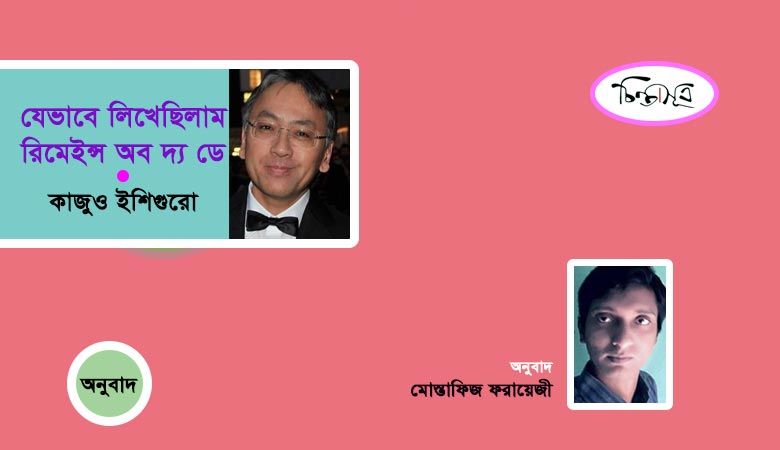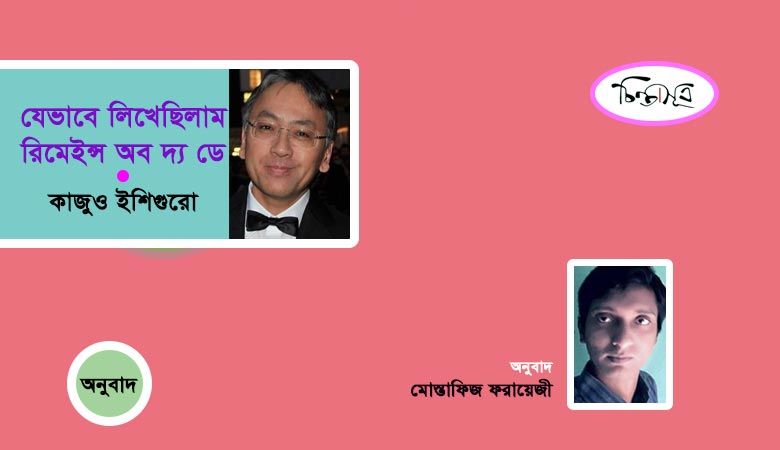 ২০১৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন জাপানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক কাজুও ইশিগুরো। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত উপন্যাস ৭টি। এরমধ্যে সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাসটি হলো ‘দ্য রিমেইন্স অব দ্য ডে’। কিভাবে তিনি মাত্র চার সপ্তাহে উপান্যাসটি লিখেছিলেন, সেই বিষয় দ্য গার্ডিয়ানে তিনি একটি নিবন্ধ লিখেছেন। নিবন্ধটি চিন্তাসূত্রের জন্য অনুবাদ করেছেন মোস্তাফিজ ফরায়েজী।
২০১৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন জাপানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক কাজুও ইশিগুরো। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত উপন্যাস ৭টি। এরমধ্যে সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাসটি হলো ‘দ্য রিমেইন্স অব দ্য ডে’। কিভাবে তিনি মাত্র চার সপ্তাহে উপান্যাসটি লিখেছিলেন, সেই বিষয় দ্য গার্ডিয়ানে তিনি একটি নিবন্ধ লিখেছেন। নিবন্ধটি চিন্তাসূত্রের জন্য অনুবাদ করেছেন মোস্তাফিজ ফরায়েজী।
অনেক লোককে প্রতিদিন দীর্ঘসময় (৮ ঘণ্টা বা তারও চেয়ে বেশি) কাজ করতে হয়। কিন্তু উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে দিনে চার ঘণ্টার বেশি লিখলে লেখার শক্তি ফিকে হয়ে আসে। আমিও এটাকে মেনে নিয়েই লিখি, কিন্তু ১৯৮৭ সালের গ্রীষ্মে আমি ভিন্ন একটি সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার স্ত্রী লর্না এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হলো।
পাঁচ বছর আগে আমি চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই সময় থেকে ১৯৮৭ সালের গ্রীষ্ম আসার আগ-পর্যন্ত আমি লেখালেখি ধীরগতিতে নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার দ্বিতীয় উপন্যাসটি জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পাল্টে গেলো। প্রকাশকদের কাছ থেকে বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাব, ডিনার, পার্টি, বিদেশে ভ্রমণ ও পাহাড়সম ইমেইলের প্রভাবে আমার লেখালিখি বিঘ্নিত হতে লাগলো। অবস্থাটা এমন হলো যে, রিমেইন্স লেখার আগের গ্রীষ্মে আমি একটা উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় লিখেছিলাম, কিন্তু একবছর পরও তার আর কোনো অগ্রগতি করতে পারিনি।
তাই লর্না আর আমি মিলে একটা পরিকল্পনা করলাম। স্থির করলাম, পরবর্তী চার সপ্তাহের ভেতর যে করেই হোক, আমার ডায়েরিটা লিখে শেষ করে ফেলব।এই বিষয়টার নাম দিয়েছিলাম ‘ক্র্যাশ’। এই ক্র্যাশের সময় আমি সকাল ৯টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু লিখতাম। সপ্তাহের সোম থেকে শনি আমার লেখালেখি চলত। দুপুরের খাওয়ার জন্য আমি এক ঘণ্টা আর রাতের খাওয়ার জন্য দুই ঘণ্টা বিরতি নিতাম। ইমেইল চেক করতাম না কিংবা ফোনের ধারে কাছেও যেতাম না। বাড়িতে কারও আসাও মানা ছিল। লর্না তার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও আমার জন্য রান্না করত। এই পন্থায় আমি শুধু খুব দ্রুত আমার কাজ করতে পারতাম, তা নয়। এমন একটা মানসিক অবস্থায় উপনীত হলাম, যেখানে বাস্তব জগতের চেয়েও কল্পনার জগৎ বেশি বাস্তবিক মনে হতে লাগলো।
তখন আমার বয়স ৩২ বছর। সম্প্রতি আমরা সাউথ লন্ডনের সিডেনহ্যামে এসেছি। এখানেই আমি জীবনে প্রথমবারের মতো নিবিড়ভাবে পড়াশুনা করেছি। একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমি আমার প্রথম দুটি উপন্যাস ডাইনিং টেবিলে বসে লিখেছি। এখানে আমি অনেক বেশি জায়গা পেয়ে রোমাঞ্চিত হলাম, আমি আমার কাগজগুলো চারপাশে যেখানে ইচ্ছা রাখতে পারতাম, দিনশেষে সেগুলো সরিয়ে ফেলার ক্ষেত্রেও বাধ্যবাধকতা ছিল না। দেয়ালে আমার প্রয়োজনীয় চার্ট ও নোটগুলো লাগিয়ে রাখতে পারতাম।
মূলত এভাবেই ‘দ্য রিমেইন্স অব দ্য ডে’ উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল। ক্র্যাশের সময়, আমি মুক্তহস্তে লিখেছি, লেখার ধরনের দিকে অত খেয়াল করিনি। সকালের দিকে আমি যেটুকু লিখেছি, বিকালের লেখাটি যদি তার সঙ্গে সাংঘার্ষিকও হতো। তবু সেদিকে নজর দিতাম না। ধারণাটা বা গল্পটা বাড়তে দেওয়াটাই ছিল প্রধান কাজ। বাজে বাক্য, জঘন্য সংলাপ কিংবা দৃশ্য তাতে ছিল, আমি সেগুলোকে থাকতে দিতাম আর তার ওপর লাঙ্গল চালাতাম।
লেখা শুরু করার তৃতীয় দিন সন্ধ্যার বিরতির সময় লর্না লক্ষ করল, আমি অদ্ভুত আচরণ করছি। রবিবারের দিন আমার লেখালেখি বন্ধ থাকতো। প্রথম রবিবারে আমি সিডেনহ্যাম হাই স্ট্রিটে হাঁটতে বের হয়েছিলাম। আমি নাকি রাস্তাটি ঢালু দেখে মুখ চেপে হেসেছিলাম। আমি এটাও বলেছিলাম, রাস্তাটা ঢালু বলে মানুষ যখন নিচের দিকে নামে, তখন হুমড়ি খেয়ে অন্যদের ওপর পড়ে। যারা ওপরে ওঠে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং টলতে টলতে চলতে থাকে। লর্না আমাকে পরে বিষয়টি বলেছিল। আমাকে আরও তিন সপ্তাহ এভাবে থাকতে হবে, এটা ভেবে লর্না চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। আমি লর্নাকে বোঝালাম, আমি ভালোই আছি। প্রথম সপ্তাহে আমি সফল হয়েছি।
চার সপ্তাহ একই নিয়মে কাজ করেছিলাম। চার সপ্তাহ শেষে মোটামুটি উপন্যাসটি লিখে শেষ করে ফেললাম। যদিও এটাকে যথাযথভাবে লিখতে আমার আরও সময় লেগেছে, কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কাল্পনিক অংশটুকু ক্র্যাশের সময়েই এসেছিল।
আমার বলা উচিত, ক্র্যাশের জাহাজে উঠেছিলাম একটা যাত্রা করার জন্য, আমি প্রচুর পরিমাণে ‘গবেষণা’ করেছিলাম যাত্রাপথে। ব্রিটিশ কর্মচারীদের দ্বারা লেখাও ব্রিটিশ কর্মচারীদের সম্পর্কিত গ্রন্থ, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অনেক ক্ষুদ্র গ্রন্থ, প্রবন্ধ, হ্যারল্ড লাস্কির ‘দ্য ডেঞ্জার অব বিইং জেন্টলম্যান’ পড়েছি মনোযোগ দিয়ে। স্থানীয় বইয়ের দোকানে হানা দিয়েছিলাম ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সালের ইংল্যান্ড সম্পর্কে জানার জন্য।
একটি উপন্যাস শুরুর সিদ্ধান্তটা আমার কাছে সবসময় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটা গদ্য লেখার আগে লেখক সেটা সম্পর্কে কতটুকু জানে? এটা শিগগিরই কিংবা দেরিতে শুরু করলে ঠিকমতো হবে না। আমার মতে, রিমেইন্সের ক্ষেত্রে ভাগ্যবান ছিলাম: ক্র্যাশটি একদম যথাসময়ে এসেছিল, সে সময় উপন্যাসটির উপাদানগুলো সম্পর্কে আমি যথেষ্ট পরিমাণ জানতাম।
রিমেইন্স সম্পর্কে পেছনে ফিরে তাকালে উৎসাহের উৎস্যগুলো দেখতে পাই। এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করছি:
১) সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে, যখন আমি টগবগে যুবক, আমি দ্য কনভারসেশন নামে একটা সিনেমা দেখেছিলাম। থ্রিলারধর্মী সিনেমাটি পরিচালনা করছিলেন ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা। এতে জিন হ্যাকম্যান নামে একটি চরিত্র ছিল, সে টাকার বিনিময়ে নজরদারি করতো। সে সেইসব মানুষের কাছে যেতো, যারা অন্য মানুষের কথা গোপনভাবে সংরক্ষণ করতে চায়। হ্যাকম্যান এ কাজে সবচেয়ে বিখ্যাত হতে চায়, কিন্তু ধীরে ধীরে তাকে একটা বিষয় তাড়া করে বেড়ায়, সেটা হলো তার ক্লায়েন্টরা তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে মানুষকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, হ্যাকম্যান চরিত্রটি স্টিভেন্স চরিত্রটির একটি প্রাক-মডেল।
২) একসময় আমি ভেবেছিলাম, আমি রিমেইন্স শেষ করে ফেলেছি। কিন্তু হঠাৎ এক সন্ধ্যায় আমি টম ওয়েটসিংগিংয়ের ‘রুবি’স আর্মস’ গানটি শুনলাম। একজন সৈন্য তার প্রেমিকাকে রেখে চলে যাচ্ছে, এমন দৃশ্যপটের একটি গীতিকাব্য এটি। গানটিতে এমন একটা মুহূর্ত আসে, যখন গায়ক ঘোষণা করে, তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি এটা শুনলাম এবং একটা বিষয় পাল্টে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি স্টিভেন্স চরিত্রে বড় পরিবর্তন আনলাম। আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম, তার দৃঢ় প্রতিবাদী চরিত্রে ফাটল ধরাতে হবে এবং একটি গোপন বেদনাবিধুর রোমান্টিজম আবছাভাবে আনতে হবে।
আর এভাবেই লেখা সম্পন্ন হলো ‘রিমেইন্স অব দ্য ডে’।