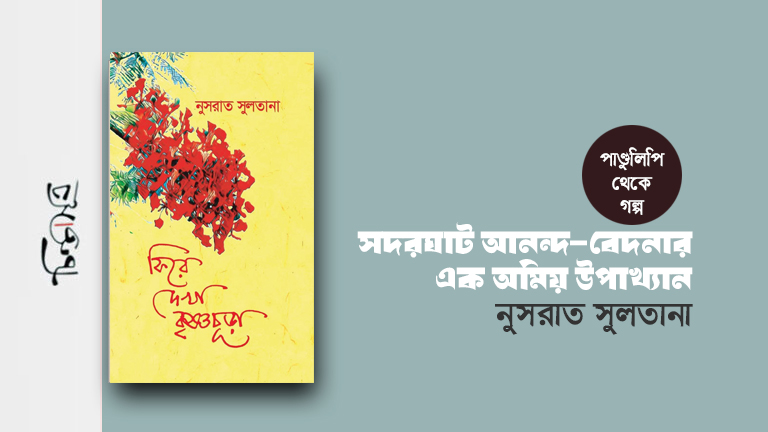বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া গ্রামে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। কীর্তনখোলা নদীর কোল ঘেঁষে গ্রামের অবস্থান। বাবা-চাচারা মোট পাঁচ ভাই। আমরা মোট সাতাশ ভাই-বোন। বাড়ির উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে বড় রাস্তা। রাস্তা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ। তার পরেই চির ষোড়শী কীর্তনখোলা। একেবারে ৪০ সাইজের বুক তার। সবসময়ই ফুলেফেঁপে থাকে। ফুলেফেঁপে ওঠা বুকেই চলে ঢাকা -বরিশালের বিলাসবহুল লঞ্চগুলো। আমাদের শৈশবে মানে ৮০’র দশকে এত বিলাসবহুল লঞ্চ আসেনি। তখন ছিল সামাদ লঞ্চ, পারাবত লঞ্চ, রিক্তা লঞ্চ। বাড়ির উত্তরদিকের রাস্তায় দাঁড়ালেই দেখা যেত নদীর বুক চিরে ঢাকাগামী লঞ্চ। আমরা হাত দিয়ে দেখিয়ে বলতাম উই যে সামাদ লঞ্চ যায়… নদীর পাড়ে যখন যেতাম লঞ্চ চলে যাওয়ার পরই আসতো সুবিশাল ঢেউ।
বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়তো তীরের দুঃখী বুকে।
আমারা পা ভিজাতাম ঢেউয়ে। তখনও নিজের চোখে সদরঘাট দেখিনি।
পঞ্চম শ্রেণীতে কেবল উঠেছি। সে বছর বৃত্তি পরীক্ষা। আব্বু স্কুলের কাজে ঢাকা আসবেন। বললাম, আমিও।
ঢাকা যাব। শিক্ষিকা মা বললেন, নিয়ে যান। আইসা ভালো মতো লেখাপড়া করবে মনযোগ দিয়া। ঠিক হল ঢাকা আসব। ব্যাগ গুছিয়ে ঢাকার উদ্দ্যেশ্যে রিক্সায় চড়ে আসলাম সদরঘাট। একপাশে ভোলা,নলছিটি, ঝালকাঠি যাবার ছোট ছোট লঞ্চ, অন্যপাশে ঢাকা -বরিশালগামী লঞ্চ। এই প্রথম দেখা বরিশাল সদরঘাট। সদরঘাটের বাইরে নিয়ে বসেছে বিভিন্ন দেশী ফল, যেমন আমড়া, বেল, চাপা কলা, সবরি কলা। টিকিট কেটে সদরঘাটের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। যতদূর মনে পড়ে তখন টিকিট ছিল দুই টাকা। আব্বুর সাথে ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখলাম হাঁকডাক – পারাবত ৬০ টাকা, সামাদ লঞ্চ ৫০ টাকা। ৫০ টাকায় ঢাকা। আশির দশকে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজন লঞ্চের কেবিনে জার্নি করতে পারত না। তারা যেত লঞ্চের ডেকে। কিন্তু আব্বু আমাকে নিয়ে ডেকে যেতে চাইলেন না। আব্বু একটা স্টাফ কেবিন নিলেন।
আব্বু বললো, চল তোরে ছাদ আর ডেক দেখাইয়া নিয়া আসি। ডেকে গিয়ে দেখতে পেলাম- বিছানার চাদর বিছিয়ে একেকটা পরিবার বসে আছে। কেউ কেউ হাঁস মুরগী নিয়ে এসেছে। পা বেঁধে রেখেছে ওদের। কেউ কাপড় দিয়ে, রশি দিয়ে নিজেদের ভাড়া করা ডেকের জায়গাটুকু ঘিরে দিয়েছে। আবার কার জায়গা কতখানি সেসব নিয়ে রেশারেশিও দেখা গেল। আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি লঞ্চের বারান্দায়। লঞ্চ থেকে বাড়ি দেখব তাই। কিন্তু হায়! নাদীর তীরবর্তী সব গ্রাম, সব বাড়ি লঞ্চ থেকে একইরকম লাগে।
সেবার ঢাকায় এসে উঠেছিলাম মহাখালী রেলগেট এলাকায়। ছোট দুই খালা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন। উনারা থাকতেন মহাখালী। খালাদের পাশেই মামার বাসা। মামার ছিল বিশাল টেইলর ব্যবসা। খালাদের বাসার পাশেই ছিল এক কহিনুর আন্টি। তার মেয়েদের সাথে স্কুলে গিয়ে হারিয়ে গেলাম। স্কুলে প্রবেশ করার অনুমতি না পেয়ে অই মেয়েদুটো বল্ল- তুমি এই এই রাস্তা দিয়ে বাসায় চলে যাও। ঠিকই এসেছিলাম কিন্তু একটা গলি ভুল করেছি। গলির মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদছি আর সবাইকে জিজ্ঞেস করছি আমার মামার নাম আবুল কালাম আযাদ। উনার বাসায় কীভাবে যাব? এটুকু মনে ছিল জলখাবার নামের ফাষ্টফুড দোকান থেকে মামার বাসা খুব দূরে নয়। এমন সময় একপশলা চৈত্রের বৃষ্টির মতো হাজির হলেন বাদশা মামা। মামার এক কর্মচারী। উনাকে দেখেই বললাম, মামা আমি আপনের সাথে বাসায় যাব। উনি বললেন তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? বাসা চিনতে পারতিছ না? চল চল বাসায় চল।
সেবার প্রথম ট্রেন দেখলাম। আব্বু শক্ত করে হাত ধরে রাখলেন যেন ট্রেনের কাঁপুনিতে ভয় না পাই। গেলাম জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সবকিছুই দুচোখ গিলত তখন গোগ্রাসে। লাল-নীল আলো, দোতলা বাস, বড় বড় শপিং মল সবই। সেজ খালা সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। যতদুর মনে পড়ে দেখেছিলাম – শাবানা-আলমগীর অভিনীত ‘পিতা-মাতা-সন্তান’।
৯৪ সালে বড় ভাই ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে। তখন ঢাকা এসে ভাইয়ের বান্ধবী শর্মি আপু, আফরোজ আপুদের সাথে কুয়েত মৈত্রী হলে থাকতাম। তখন দেখলাম সদরঘাটের তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন হয়েছে লঞ্চ। সুরভী লঞ্চে তখন বাসের মতো সোফা সিষ্টেম চালু হয়েছে। তখন সোফায় আসতাম। বরাবরই চোখে পড়ত- পায়ে ঘুঙুর বাঁধা আপাদমস্তক লাল জামা পরা চানাচুর ওয়ালাদের।
ঘুগনি বা তেল দিয়ে ঝাল ঝাল চানাচুর ভর্তার কথা মনে হলে জিভে জল চলে আসে।
৯৮ সালে আমি ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা” বিষয়ে। বরিশালের পার্ট চুকিয়ে চলে আসব ঢাকা। রোকেয়া হল
আমার আবাসিক হল। সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাস শুরু হবে। আগষ্ট -সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে চলছে দেশব্যাপী দুর্বিষহ বন্যা। বুড়িগঙ্গার দুর্গন্ধযুক্ত জলে পুরো সদরঘাট এবং রাস্তা প্লাবিত। ছোট ভাই পরশকে সাথে নিয়ে অই নোংরা জল মাড়িয়ে ভ্যানে চড়ে আসলাম রোকেয়া হল। মানুষের কী যে অসহনীয় ভোগান্তি!
ধীরে ধীরে ছয় ভাইবোন ভর্তি হয়ে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বছরে দুই ঈদে অন্তত সবার একসাথে বাড়ি ফেরা হত। ঈদে সদরঘাট লোকে-লোকারণ্য। টিকেট কাউন্টারেও প্রচন্ড ভীড়। একবার মনে পড়ে লঞ্চ প্রায় বুড়িগঙ্গার মাঝখানে কারণ তীরে আসলে লোক আরোহন ঠেকানো যাচ্ছে না। আমরা নৌকা করে গিয়ে উঠলাম লঞ্চে। আমার দুই ভাই আমাকে টেনে তুলল লঞ্চে। লঞ্চে কেবিনের সামনে, ছাদে, সিড়ি কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। তখন মনে হত ঢাকা শহরের সব মানুষের বাড়ি বরিশালে। সবাই মিলে যখন যেতাম আব্বু আগের দিন ইলিশ কিনে রাখতেন। আম্মু ইলিশ ভুনা, ভাত, ডাল রান্না করে রাখতেন। আব্বুএগিয়ে এসে অপেক্ষা করতেন নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুল ঘরে। কখনো বসে থাকতেন চায়ের দোকানে। তাঁর বুক ভরা আনন্দ তখন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছয় ছেলে-মেয়ে বাড়ি ফিরবে। এলাকার মানুষের সবার শ্রদ্ধাভাজন আবু স্যার তিনি। সবাই তাঁকে বলত- আইজগো আবু স্যারের ঘরে চান্দের আট বইবে। আব্বুর মুখে চোখে দেখা যেত পূর্ণ চাঁদের জোছনা।
আমি তখন মাস্টার্স পাস করে ফেলেছি। ছোট বোনকে উঠিয়ে দিয়েছি রোকেয়া হলের নিজের আবাসিক রুমে। আমি আর বোন বরিশাল থেকে ঢাকা যাচ্ছি। দুইবোন বসে আছি সুরভী – ৬ লঞ্চের দুই সোফায়। খাওয়া দাওয়া শেষ করে লঞ্চে থাকা টিভিতে নাটক দেখছি। মনে পড়ে নাটকে এটি এম শামসুজ্জামান অন্ত্যমিলে কথা বলতে চান কিন্তু পারেন না। লুঙ্গি পরা এক চাচা বসেছিলেন একদম পেছনের দিকের সোফায়। শামসুজ্জামান একেকটা ভুল অন্ত্যমিল বলেন
আর ভুরি ওয়ালা অই চাচা হা হা হা করে হেসে ওঠেন আর বলেন- পারে না মিলাইতে হোগার পোয় হুদাহুদি কয়। আমরা দুইবোন নাটকের চাইতে চাচার কথায় ভরপুর বিনোদন পেলাম অনেক রাত অব্দি। হেসে হেসে একজন অন্যজনের গায়ে গলে গলে পড়লাম। আজও কানে বাজে- হোগার পোয় হুদাহুদি কয়!
অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে মননে-বোধে একটা বিষয় জেঁকে বসেছিল। বিয়ে করব না। একটা মেয়ে বাচ্চা দত্তক নেব। ওকে নিয়ে দুনিয়া ঘুরে বেড়াব আর মনের মতো স্বাধীন, মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলব।
এম. এ পাস করার সাথে সাথেই পরিবারের প্রেসার – বিয়ে করতে হবে। নিজের পছন্দ থাকলে বলা যাবে। সেই অব্দি প্রেম করিনি। অপরিচিত কাউকে বিয়ে করতে কেমন গা ঘিনঘিন করছে। বিয়ে করে ফেললাম নিজের ক্লাসমেট বন্ধু আজিজ ইসলামকে। উনাদের বাড়ি সাতক্ষীরা। বরিশাল শহর থেকে বউ নিয়ে উনারা সাতক্ষীরা গিয়েছিলেন। বিয়ে হয়েছে বরিশাল কমিউনিটি সেন্টারে। আজিজ ইসলাম শ্বশুর বাড়ি যাননি। উনার শ্বাশুড়ির দাবী জামাইকে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে যেতে হবে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হয়েছিল ২২ মে ২০০৭। আমি তখন মিলিটারি ইনিষ্টিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি(এম আই এস টি)এর স্টাফ অফিসার। বিয়ের পরে অফিসার্স কোয়ার্টারে বাসা নিয়ে গুছিয়ে বরিশাল বেড়াতে যেতে যেতে আগষ্ট মাস।
প্রকৃতিতে তখন শরত ঋতু। শরতের নীলাকাশ আর সাদা মেঘের চুমোচুমি, প্রকৃতির ফুরফুরে মেজাজ বরাবর ভীষণ টানে। বিয়ের পর প্রথম প্রাণনাথকে নিয়ে যাচ্ছি বাপের বাড়ি বা নিজের বাড়ি। আমার মনের ঘরে পায়রা বাকবাকুম করে। মুশকিল অপর পক্ষ নিয়ে। আমার শ্বশুর ছেলেকে লঞ্চে যেতে দেবে না। লঞ্চ ডুবে তার ছেলে মরে যাবে। আমাকে তিনি বললেন- বউ মা আমি গাড়ি রিজার্ভ করে দিই। তোমরা গাড়ি নিয়ে যাও।
কিন্তু আমি তো যাব শরতের প্রকৃতি সাথে নিয়ে জলে ভেসে ভেসে। মাতাল বাতাস, জোছনা, সাথে পদ্মা- মেঘনা। বহু বুঝিয়ে শ্বশুর রাজি করে তার ছেলেকে নিয়ে উঠলাম সুরভী-৭ এর ক্যাবিনে। শ্বশুর তার ছেলেকে বললেন – আয়াতুল কুরসী আর লা হাওলা পড়তে। দোয়া-দরুদ পড়ে আজিজ সাহেব রওয়ানা হলেন সদরঘাটের উদ্দেশ্যে। আমাদের সাথে আমার ছোট তিন ভাইবোন। আজিজ সাহেবের মুখবায়ব দেখে মনে হয় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী। আজিজ সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস – আজ তাঁর সলিল সমাধি ঘটতে যাচ্ছে।আমরা ভাইবোনরা দেখি আর মুখ টিপে হাসি। সবাই এসে দাঁড়ালাম লঞ্চের সম্মুখভাগে। সদর ঘাট তখন লাল-নীল জরির শাড়ি পরা নববধু। আকাশে পূর্ণ চাঁদ, মাতাল বাতাস। আজিজ সাহেব বিমুগ্ধ হলেন। কিন্তু ভয় গেল না। রুমে এসে ওয়েটারকে বললাম চা দিতে, টিভি ছেড়ে দিলাম। উনি মুগ্ধ হলেন- বললেন বাহ! এত বিলাসবহুল, আরামেও জার্নি করা যায়! এই লেখা লেখার সময় জিজ্ঞেস করলাম – তুমি সেদিন কী ভাবছিলা? লঞ্চ ডুবে মরে যাবা? উনি বললেন হ্যাঁ।
আবার জিজ্ঞেস করলাম- কখন ভুল ভাঙলো? উনি বললেন, পৌঁছে।
২০১৪ সালে আম্মু একমাস জ্বরে ভুগেছিল। ছেলের বয়স তখন তিন বছর। ছেলে আর ছোট ভাইকে নিয়ে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। সদরঘাট পৌঁছাতেই আমার সবেধন নীলমনি পুত্র জাইন সাহেব বললেন, আএ (আরে) ইতনা বাড়া শিপ ক্যায়ছে! তখন হিন্দি কার্টুন “মটু-পাতলু”, ” শিবা”, “টম এন্ড জেরী” দেখে সারাক্ষণ হিন্দি বলত। লঞ্চে উঠে দৌড়ালো লঞ্চের এমাথা-ওমাথা। বরিশাল পৌঁছে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর দেখে বলে -এ পানি ক্যায়ছে আয়েগি!
উঠানের সব ইট নিয়ে ফেলে দিয়েছিল পুকুরে।
এই সদরঘাট থেকে গ্রীনলাইন ওয়াটার বাসে চড়ে বাড়ি গিয়েছিলাম ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সালে। আমার মৃত মাকে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে আসতে গেছে বড় ভাই আর সেজো ভাই। ২০১৬ অক্টোবরে আম্মু অসুস্থ হয়েছিলেন।
ছয়মাস চলে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের ভুল চিকিৎসা। এই টেষ্ট, সেই টেষ্ট আর একের পর এক পরিবর্তন করা হয় এন্টিবায়োটিক। ডিসেম্বরে নেয়া হল ব্যাঙ্গালোরের বেলভিউ হাসপাতালে। বাংলাদেশের এক্সরে প্লেট ধরেই ডাক্তার দেবীশেঠী বল্লেন- সী গট আওরতা এনিউরিজম। অথচ সেই এক্সরে প্লেটে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা দেখতে পেলেন না কিছুই। তারপর ১৪ ঘন্টার অপারেশন। ততদিনে এন্টিবডি জিরো। অপারেশনেরস্থান আর শুকাচ্ছে না। কাজ করছে না কৃত্রিম ভেইন। দেড় মাস নিষ্ফলা কঠোর লড়াই আমার লড়াকু মায়ের। মৃত্যুর শেষ অব্দি অপেক্ষা করেছেন বড় ছেলের জন্য। ১৩ ই ফেব্রুয়ারী মারা গেছেন বিকাল তিনটায়, সকালে সেজ ছেলে বলেছে- আম্মু দাদা আসতেছে। উনি বিষ্ময়ে বলেছেন – মনু এখনো আসে নাই! সে শব্দ পুরোপুরি শোনা যায়নি। গলায় কৃত্রিম খাদ্য নল বসানো। মাকে সমাহিত করতে যাচ্ছি আমরা ভাইবোন এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা। যাচ্ছি গ্রীন লাইন ওয়াটার বাসে। অই ওয়াটার বাস ছেড়েছিল সকাল এগারোটায়। একটু বেলা করে অই প্রথম সদরঘাট দেখা। কেমন থমথমে। ঠিক আমাদের স্তব্ধ হৃদয়েরই মতো। সবাই গিয়ে দাঁড়ালাম লঞ্চের পেছনে। ইঞ্জিনের ওখানে। প্রচন্ড ঢেউয়ের কিছু ওপরেই উড়ছে গাঙচিল । সবাই উপভোগ করছে। কিন্তু আমাদের চোখে সাত রাজ্যের অন্ধকার। প্রকৃতিকে মনে হল জড় পদার্থ, নির্বিকার। সে কেবল নিজের মতোই বয়ে চলে।
কারো সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় তার কিছু আসে-যায় না।
বাড়িতে পৌঁছালাম বেলা সাড়ে তিনটায়। খোলা হল মৃত মায়ের কফিন। গোসল করাতে হবে। আম্মুর দাবী ছিল দুই মেয়ে তাঁকে গোসল দেবে। যে মাকে ভয় পেয়েছি জমের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েও নদীর পাড় থেকে ফিরতাম পা টিপে টিপে। মনে হত এখনই থাপ্পড় কষে দেবে গালে। আমার সেই তুখোড়, মেধাবী, ব্যক্তিত্ববান, লড়কু মা আমার সামনে নিথর হয়ে পড়ে আছে। চোখ-মুখ ভরা বেদনা। মনে হল কাকে যেন খুঁজেছে উদাসিনী। হয়তো বা বড় পুত্র বা কন্যা। ছয় ছেলে-মেয়ের কাউকে। কেউই ছিল না যাবার মুহূর্তে। আম্মুর এমাথা- ওমাথা ফাড়া বুকটা বেলভিউ হাসপাতাল সেলাই করে দিয়েছে মোটা সুতায় বড় বড় স্টিচে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে বুক থেকে। ইচ্ছে হল- একটা চিৎকার দিয়ে আকাশটা খান খান করে ভেঙে ফেলি, পৃথিবীর সব ফুলগুলো ছিড়ে ফেলে দিই জলে। এ জীবনের কেমন পরিহাস! যে মানুষ সারাজীবন ব্যয় করলো মানুষের কল্যাণে। শিক্ষিকা, ধার্মিক মা আমার স্বার্থ কী জিনিস জানতেন না। যাহোক গোসল দিলাম দুইবোন দাফন, মিলাদ সব শেষ করে ডিমেনশিয়া আক্রান্ত বাবাকে নিয়ে ফিরলাম ঢাকায়। সেও সেই সদরঘাট হয়ে সুরভী লঞ্চে করে। সেদিনও সদরঘাট, আকাশ সবাই সেজেছিল বর্ণিল সাজে।
এর ঠিক দুবছর সাত মাস পরে আব্বু মারা গেলেন। দুই বছর আম্মু বেঁচেছিল আব্বুর মেমোরিতে। যতবার জিজ্ঞেস করেছে ততবারই বলেছি আম্মু ইন্ডিয়া হাসপাতালে। শিশুর মতো হেসে বলেছে- কেমন যাওয়া গেছে কেডা জানে! যখনই কেউ বলতে চেষ্টা করেছে খোকনের মায় মইরা গেছে। তাকেই বলেছে একটা থাপ্পড় দিমু তোরে। মরমু আমি, হে মরবে ক্যা? একদিন সব বুঝিয়ে বলার পর তিনদিন কাঁদলেন শিশুদের মতো। এরপর বিছানায় পড়ে গেলেন। কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। মৃত্যুর আগে শেষ কথা বললেন, তোর মায় কই? সেই বাবাকে অন্তিম শয়নে শুইয়ে দিয়ে আসলাম মায়ের কবরের পাশে গ্রামের বাড়ি। রিক্ত, নি:স্ব এতিম আমরা ফিরলাম জীবন যুদ্ধে সদরঘাট হয়েই।
তারপর ও গিয়েছি সদরঘাট হয়ে লঞ্চে করে বরিশাল চরবাড়িয়া গ্রামে। মায়ের চুলা জ্বলেনি, ছিলনা বাবার অস্থির পায়চারি। গরম ভাতের পাতে ওঠেনি ইলিশ। এভাবেই সদরঘাট আমার জীবনের আনন্দ-বেদনা, বিচ্ছেদ -মিলন আর জন্ম-মৃত্যুর এক অনিন্দ্য স্মারক।
শেষবার গিয়েছি ১৫ ই মার্চ ২০২৩। উপন্যাসের কাজে মুলাদী সোনামদ্দি বন্দর, কাইতমারা গ্রাম গন্তব্য। এক বন্ধুর সাথে যাবার কথা ছিল। ভি আই পি ক্যাবিন বুক করলাম। সারারাত আমাদের নদী দেখার কথা। বন্ধু গেলেন না, জানালেন শরীর খারাপ।
অথচ এই বন্ধুই জার্নি পিছিয়েছে তিনমাস। এই প্রথম একেবারে একা জার্নি করা পরিবার বা বন্ধু কেউ ছাড়া। যে আমি সবসময় বলি- আমার একাকীত্ব খুব ভালো লাগে, নিজের সাথে বাস করি তখন। লঞ্চ ছাড়ার সাথে সাথে এক দুর্মর বিষাদ ভর করলো। নদীর ঢেউ সমস্তটাই আমার হৃদয় ভেঙে চুরমার করতে লাগলো। আর মনে হল- আমি কী আমাকে চিনি না! মনে পড়ল কবি আবুল হাসানের সেই কথা- মানুষ তার চিবুকের কাছেও অচেনা। তারপর ভাবলাম- একাকীত্ব চাই বা না চাই, মানুষ মূলত ভাঙনের মতো একা!
ফিরে দেখা কৃষ্ণচূড়া
নুসরাত সুলতানা
প্রকাশক: রচয়িতা
প্রচ্ছদ : লুৎফুল হোসেন
মূল্য: ৩০০ টাকা