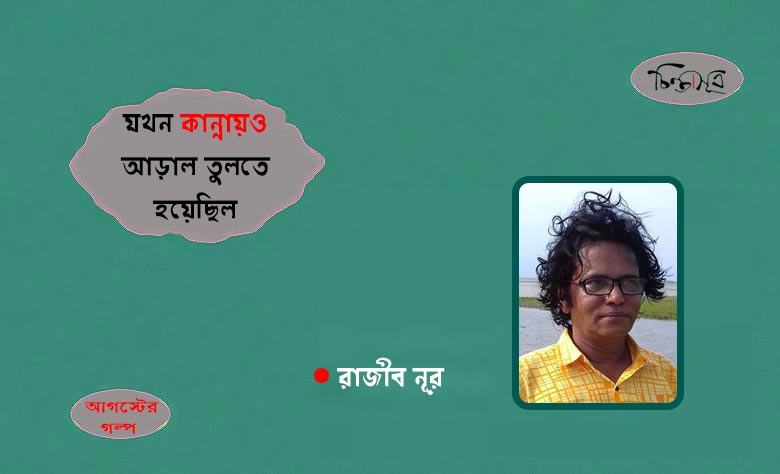 রাসেল প্রায়ই আসত আমাদের বাড়িতে। আমাদের দেয়ালের গায়ে জন্মানো পাকুড় গাছটায় টুনটুনি পাখি বাসা করলে ওর আসা বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানে ছোট্ট একটা গেট ছিল, যে গেটটা কখনোই বন্ধ করা হতো না। আমার মনে আছে, রাসেল এক সকালে একটা কাঁচি নিয়ে এসেছিল। এসেই আমাকে চুপিচুপি ডাকল। আমি তো আশ্চর্য, যে কিনা সদাসর্বদা আমার সামনে দাদাঠাকুর সেজে থাকতে ভালোবাসে, সে এমন করে ডাকছে কেন? অবশ্য দাদাঠাকুর ভাবের জন্য আমি কখনোই ওর ওপর রাগ করতাম না। আসলে আমার চেয়ে মাত্র কয়েক মিনিট আগে পৃথিবীতে আসতে পেরেছে বলে বরাবরই যে নিজেকে আমার বড় ভাই বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে, তারই বন্ধু হওয়ার কারণে সমবয়সী রাসেলকেও আমার ভাই বলে ডাকতে হতো। অবশ্য এ কারণে আমি কখনোই দুঃখ পাইনি। আমার যমজ ভাইটার ডাক নাম তারা; কিন্তু কথা বলতে শেখার সময়ে নাকি আমি ওকে তাতা বলে ডাকতে শিখেছিলাম। পরে ওর বড় ভাইগিরি ঠেকানোর জন্য ওই তাতাটাকেই তাদা বানিয়ে নেই, যা শুনতে দাদা বলে মনে হয়। রাসেলকে অবশ্য ভাই ডাকতে আমার মন্দ লাগত না; বরং এত্তো বড় মানুষের ছেলেকে ভাই ডাকাটাই আমার কাছে নিরাপদ বলে মনে হতো। আসলে শৈশবের ওই দিনগুলোর কথা আমি ঠিকঠাক মনে করতে পারছি কি না, এ নিয়ে আমার নিজেরই রয়েছে সংশয়। কাজেই আপনারা চাইলে ভেবে নিতে পারেন, বন্ধুর বাবাকে অনেক বড় বলে ভাবার মতো বিচক্ষণতা আমার ছিল না; তবে এটা আমি দিব্বি দিয়ে বলতে পারি, ওই বাড়িটিকে ঘিরে যুদ্ধের কয়েক বছর আগে থাকতে যে জনস্রোত প্রবাহিত হতে দেখেছি, তাতে বিস্মিত হওয়ার মতো জ্ঞানগম্যি আমার খুব ছোটবেলা থেকেই ছিল।
রাসেল প্রায়ই আসত আমাদের বাড়িতে। আমাদের দেয়ালের গায়ে জন্মানো পাকুড় গাছটায় টুনটুনি পাখি বাসা করলে ওর আসা বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানে ছোট্ট একটা গেট ছিল, যে গেটটা কখনোই বন্ধ করা হতো না। আমার মনে আছে, রাসেল এক সকালে একটা কাঁচি নিয়ে এসেছিল। এসেই আমাকে চুপিচুপি ডাকল। আমি তো আশ্চর্য, যে কিনা সদাসর্বদা আমার সামনে দাদাঠাকুর সেজে থাকতে ভালোবাসে, সে এমন করে ডাকছে কেন? অবশ্য দাদাঠাকুর ভাবের জন্য আমি কখনোই ওর ওপর রাগ করতাম না। আসলে আমার চেয়ে মাত্র কয়েক মিনিট আগে পৃথিবীতে আসতে পেরেছে বলে বরাবরই যে নিজেকে আমার বড় ভাই বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে, তারই বন্ধু হওয়ার কারণে সমবয়সী রাসেলকেও আমার ভাই বলে ডাকতে হতো। অবশ্য এ কারণে আমি কখনোই দুঃখ পাইনি। আমার যমজ ভাইটার ডাক নাম তারা; কিন্তু কথা বলতে শেখার সময়ে নাকি আমি ওকে তাতা বলে ডাকতে শিখেছিলাম। পরে ওর বড় ভাইগিরি ঠেকানোর জন্য ওই তাতাটাকেই তাদা বানিয়ে নেই, যা শুনতে দাদা বলে মনে হয়। রাসেলকে অবশ্য ভাই ডাকতে আমার মন্দ লাগত না; বরং এত্তো বড় মানুষের ছেলেকে ভাই ডাকাটাই আমার কাছে নিরাপদ বলে মনে হতো। আসলে শৈশবের ওই দিনগুলোর কথা আমি ঠিকঠাক মনে করতে পারছি কি না, এ নিয়ে আমার নিজেরই রয়েছে সংশয়। কাজেই আপনারা চাইলে ভেবে নিতে পারেন, বন্ধুর বাবাকে অনেক বড় বলে ভাবার মতো বিচক্ষণতা আমার ছিল না; তবে এটা আমি দিব্বি দিয়ে বলতে পারি, ওই বাড়িটিকে ঘিরে যুদ্ধের কয়েক বছর আগে থাকতে যে জনস্রোত প্রবাহিত হতে দেখেছি, তাতে বিস্মিত হওয়ার মতো জ্ঞানগম্যি আমার খুব ছোটবেলা থেকেই ছিল।
জানুয়ারির ১০ তারিখে তিনি যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এলেন, তত দিনে আমরা অনেক বড় হয়ে গেছি। কেননা, নয় মাসের যুদ্ধ আমাদের এতটাই অভিজ্ঞ করে তুলেছিল, যা পুরো নয় বছরে অর্জন করা সম্ভব নয়। তখন যাঁরা বড় ছিলেন, তাঁদের পক্ষে এটা অনুভব করা সম্ভব ছিল না; যে কারণে আমি বা তাদা যখন যুদ্ধের দিনগুলো নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে শুরু করতাম, মা রেগে গিয়ে বলত, ‘ইঁচড়ে পাকামি করতে এসো না, মাত্র পাঁচ বছরের বাচ্চা ছিলে তোমরা। এতকিছু বুঝতে পারার মতো বয়স ছিল না ওটা।’
মায়ের কথা সত্যিও হতে পারে। আজ এতকাল পর আবার পুরোনো দিনের কথা মনে করতে গিয়ে আমার মধ্যেও দ্বিধার দোলাচল শুরু হয়েছে। কাজেই রাসেল যে সকালে আমাকে ডেকেছিল, সেই সকালটাকে আমি ঠিক মতো স্মরণ করতে পারছি না হয়তো।
রাসেল কি সেদিন গেটের কাছ থেকে ইশারায় ডেকেছিল আমাকে? তাহলে আমি কোনখানটায় ছিলাম? চাইলেও আমার পক্ষে আর সেই দিনের স্মৃতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কেননা, আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানের ছোট গেটটা আর নেই। ওদের বাড়িটা ঠিক আগের মতো রয়ে গেলেও, সেটা আর বসতবাড়ি নেই; সেখানে এখন জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের বাড়িটা ভেঙে গড়া হয়েছে বহুতল এক আবাসন; ছোট্ট একচিলতে সেই উঠোনটা আর নেই। এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় এক তলার বারান্দায় বসে কিছু একটা করছিলাম। হতে পারে পড়ছিলাম রূপকথার বই, যেটা সপ্তাহখানেক আগে ডাকে করে এসেছে আমার আর তাদার জন্য। হাসু বু আমাদের জন্মদিনটার কথা ভুলে যায়নি, লন্ডন থেকে পাঠিয়েছিল এন্ডারসনের রূপকথার বইটা, যা জন্মদিনের আগেই এসে পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের হাতে। সহজসুন্দর ইংরেজিতে অনুবাদ করা ওই বইয়ের গল্পগুলো বুঝতে আমার মোটেই কষ্ট হয়নি।
রাসেলের ডাকে পড়া ফেলে উঠে এলাম। চোখের পাতা নাচিয়ে জানতে চাইলাম, কী ব্যাপার।
তামারা, তুই কি জানিস, মেয়েদের চুল না হলে টুনটুনির বাসা মজবুত হয় না।
তাই বুঝি?
হ্যাঁ, সত্যি তাই।
তুমি জানলে কোথা থেকে?
সুলতানা ভাবি ওদের বার্ডওয়াচ ক্লাবের একটা বই এনেছিল কাল, সেটা থেকেই জেনেছি।
কামাল ভাইয়ার বউ যে খেলোয়াড়, সেটা আমারও জানা ছিল; তিনি যে একজন বার্ডওয়াচারও, সেটা বোধ হয় সেদিনই শুনেছিলাম; কিন্তু রাসেল আমাকে এ তথ্য কেন জানালো, তা বুঝতে আরও কয়েক মিনিট সময় লেগে গিয়েছিল। রাসেল ওর পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাঁচি বের করার পরও বুঝতে পারিনি, ও আমার চুল কেটে দিতে চায় টুনটুনিদের, যেন বাসাটা মজবুত করে বানাতে পারে ওরা। বড়জোর একগোছা চুল হলে যা হয়, তার জন্য সে আমার লম্বা চুলগুলো কেটে বয়কাট বানিয়ে দিল।
সত্যি বলছি, আমি আমার চুলের জন্য যত না, তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছিলাম চাচির হাতে রাসেলের মার খাওয়া দেখে। আমি কিন্তু কাউকে নালিশ জানাতে চাইনি; কিন্তু আমার একরাশ ঘনকালো চুল, যা কিনা সবসময় চাচির আহ্লাদের বিষয় ছিল, সেগুলো গেল কই, চাচির এই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার মতো বুদ্ধিও ছিল না তখন। এরপর কয়েক দিন ছোট গেটের এ পাশে আসাটা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। আবার যখন এলো, তত দিনে রাসেল রীতিমতো টুনটুনি বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে; আর আমিও ওকে শোনাব বলে ভালো করে মুখস্ত করে ফেলেছিলাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টোনাটুনির গল্প। আমার কাছ থেকে টোনাটুনির গল্প শুনে রাসেল আর তাদার সে কী হাসি শুরু হতো! রাসেলের কাছ থেকে আমরা জানলাম কুড়িয়ে পাওয়া তুলা, সুতা আর মেয়েদের চুল দিয়েই টুনটুনি বাসা বানায়। শীতকাল ছাড়া অন্য যেকোনো সময় ওরা বাসা বানায়, ডিম দেয়। ডিম পাড়ার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই টুনটুনিরা ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। প্রতিদিন সকালবেলা আমরা তিনজন গিয়ে হাজির হতাম পাকুড়তলায়। পাকুড়তলা বলতে আপনারা আবার বিশাল কোনো বটগাছ ভেবে নেবেন না। যে সময়কার কথা বলছি, তার বছরখানেক আগে গাছটা জন্মেছিল মাটি থেকে কয়েক হাত উঁচুতে আমাদের দুই বাড়ির সীমানা দেয়ালের বুক চিরে। রাসেল বলেছিল, টুনটুনিরা আসলে ডুমুরগাছে বাসা বানাতে পছন্দ করে। শহরে গাছ কম বলেই পাকুড়কেই বেছে নিয়েছে।
টুনটুনির বাচ্চা দুটি দেখে রাসেলই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল। তাদা আর রাসেল মিলে ওদের বাসা থেকে উঁচু একটা টুল নিয়ে এল, রংমিস্ত্রীরা আর আগের কয়েক দিন এই টুলটাতে করেই ওদের বাড়ির দেয়ালে রং লাগানোর কাজ করছিল। একসঙ্গে তিনজনই টুলের ওপরে উঠতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলাম আমরা; ব্যথাও পেলাম। তবু আবার দেখার চেষ্টায় একজন একজন করে টুলে চড়ি এবং অন্য দুজন টুলের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। সবশেষে উঠল তাদা। উঠেই সে টুনটুনির বাসা থেকে বাচ্চা দুটি বের করে আনার চেষ্টা করতে লাগল। রাসেল চিৎকার করে উঠল, হাত দিস না, তারা। তাইলে পরে বাচ্চা দুটিকে বাঁচানো যাবে না।
এতদিন পর টুনটুনির বাসা নিয়ে খেলার ওই দিন-তারিখটা মনে রাখতে পারার কোনো কারণ ছিল না; কিন্তু আমি মনে করতে পারি। কারণ, এর মাত্র একদিন পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে ঘটনা ঘটে গেল, তা তো চাইলেও আমি কেন, আপনাদের কারো পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না।
ভোরে গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমাদের। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, আমরা বোধ হয় নৌকায় করে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি; কিন্তু সে ছিল ক্ষণিকের বিভ্রম মাত্র। আম্মা আর্তনাদ করে উঠেছিল, ওরা বোধ হয় কামালরে মেরে ফেলল। তারপর আব্বাকে বলছিল, তুমি যাও না, তুমি তো ডাক্তার, তোমারে কি যেতে দেবে না? আব্বা আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানে কোনো দিনও বন্ধ না হওয়া গেট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সেনাবাহিনীর এক লোক আব্বাকে আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল; ওই লোকটাই বোধ হয় রিসালদার মোসলেহউদ্দীন। ও এসে আমাদের বারান্দায় দাঁড়ালে আমার নাকে এসে বোটকা গন্ধ ঝাপটা মেরেছিল, যে গন্ধটাকে আমি পাকিস্তানি গন্ধ বলে ডাকি। এখনো পাকিস্তানের নাম শোনামাত্র আমি ওই গন্ধটা পাই।
পাকিস্তানি গন্ধ আসলে আমার নিজেরই একটা মনোবৈকল্যের নাম, তাই পাকিস্তানি গন্ধ বলে কী বোঝাতে চাইছি, সেটা বোধ হয় আপনাদের কাছে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। একাত্তরের যে রাতে পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে গেল, সে রাতেই আব্বা-আম্মা আমাদের নিয়ে ঢাকা ছেড়ে যায়। এর পরের নয়টা মাস আমরা ছিলাম গ্রাম-গ্রামান্তরে, মূলত নদীতে নৌকায় কাটিয়েছি আমরা ওই দিনগুলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক দিন পর সম্ভবত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় ফিরে আসি আমরা। ঢাকায় ফেরার পর জানতে পাই, বড় মামাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে একের পর এক বধ্যভূমিতে খুঁজতে লাগল আম্মা-আব্বা এবং একদিন দুপুরে মামার লাশ নিয়ে ফিরে এল। আমি সেদিন যে গন্ধটা পেয়েছিলাম পচা লাশ থেকে, সে গন্ধটাই আমার কাছে এখনো পাকিস্তানের সমার্থক হয়ে আছে।
রিসালদার মোসলেহউদ্দীন চলে যাওয়ার পরেও গন্ধটা গেল না। বমি করে ঘর ভরালেও আমার দিকে একটু মনোযোগ দিলো না কেউ। সকাল না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে মরার মতো পড়ে রইলাম সবাই। বোধ হয় বার বার বমি করার কারণে জ্ঞান হারিয়েছিলাম আমি, ঠিক জানি না, হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে থাকতে পারি। তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে, জ্ঞান হারানোর আগে শুনলাম মা বলছে, ভাই সাহেব যে কী, ভাবি আর বৌমাদের তো আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। আর ভাবিও পারেন, ওনার কলিজা ভরা সাহস। আম্মা একটু থেমে স্বগতোক্তির মতোই বলে, রাসেলটা যে কী করছে এখন।
আসলে ওই দিন ভোরবেলা আমার আম্মার পক্ষে ওই হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে অনুমান করাও সম্ভব ছিল না; কেননা, বঙ্গবন্ধুর নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর সামনে এসে কী রকম হতচকিত হয়ে পড়েছিল, সেই ঘটনা তো আম্মারই সবচেয়ে ভালো জানা ছিল। কাজেই আম্মার পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না যে, নিজ দেশের সৈন্যবাহিনীর গুটিকয়েক হঠাৎ একরাতে এসে পরিবার-পরিজনসহ বঙ্গবন্ধুকে খুন করতে পারে।
তাদা ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল। ততক্ষণে যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে। আমরা দুই ভাই-বোন গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম পাকুড়তলায়। আশা করতে ভালো লাগছিল যে কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে রাসেল। তাদা আমার মতো আশা করতে জানে না বলেই আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানের গেট আগলে দাঁড়িয়ে থাকা এক সৈন্যের কাছে জানতে চায়, তোমরা কি শেখ মুজিবকে মেরে ফেলেছ?
আমি আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, তাদা শেখ চাচাকে বঙ্গবন্ধু বললো না; অথচ যুদ্ধের পর তাঁর দেশে ফেরার দিনে আমরা যে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু বলে স্লোগান দিয়েছিলাম, তারপর থেকে আর কখনোই তাঁকে চাচা বলে ডাকিনি। এমনকি, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রাসেলও তাঁকে বঙ্গবন্ধু বলতে শুরু করে দিয়েছিল।
সৈন্যটা মহা-উৎসাহের সঙ্গে তাদার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জানালো, অল ফিনিশড।
মানে?
সব্বাইকে মেরে ফেলা হয়েছে।
রাসেলকেও? কে করেছিল এই প্রশ্নটা, বোধ হয় আমিই।
সৈন্যটা এবার বেশ স্পষ্ট করে বলল, অল অব দেম আর ফিনিশড।
রাসেলের জন্য আমার ভীষণ কান্না পেল। আমি কাঁদতে লাগলাম শেখ চাচার জন্য, চাচির জন্য, সুলতানা ভাবির জন্য…। আমি কাঁদতে শুরু করলে সৈন্যটা ভারি আশ্চর্য হয়ে যায়, কাঁদছ কেন!
আমি ভয়ে ভয়ে বলি, আমার টুনটুনি পাখির বাসাটা তোমরা ভেঙে ফেলেছ।
ততক্ষণে তাদাও টুনটুনির ভাঙা বাসাটা দেখতে পায় আর কান্নাজুড়ে দেয়। রাসেল বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আমরা তিনজন মিলে টুনটুনির বাসা ভেঙে যাওয়ায় কাঁদতাম; কিন্তু রাসেলই তো নেই, টুনটুনির ভাঙা বাসাটা একটা আড়াল তৈরির সুযোগ করে দিল আমাদের। দুই ভাই-বোনের কান্না দেখে সৈন্যটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।
তামারা আলী কাঁদছে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসির রায় হয়েছে। বোধ হয় ওর কান্না থামানোর জন্যই এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করে, ওইটাও কি রিসালদার মোসলেহউদ্দীনই ছিল?
জানি না। আসলে ভোরে যে সৈন্যটা আব্বাকে তাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেটাও মোসলেহউদ্দীন ছিল কি না, আমি জানি না। তবে তখন আবার পচা গন্ধটা পেয়েছিলাম।
রচনাকাল: আগস্ট, ২০১০


