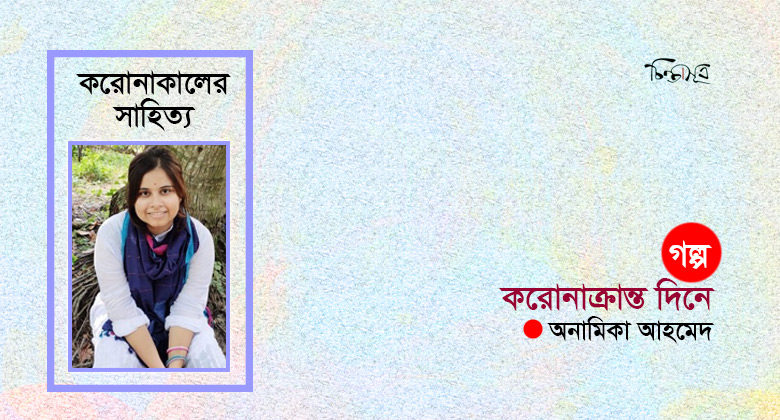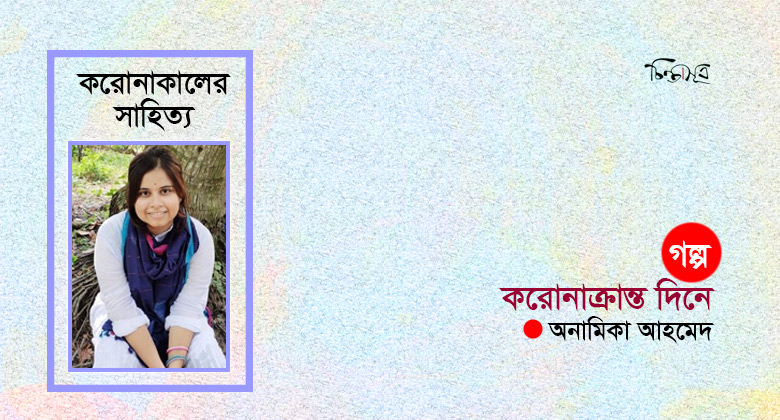 দূরত্ব
দূরত্ব
সাদিয়া স্ট্যান্ডিং টিকিটের যাত্রী। একের পর এক সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে। দুয়েক দিন পর সাধারণ ছুটি হবে। বন্ধ করে দেওয়া হবে গণপরিবহনও। তাই সবাই ছুটছে। করোনা আতঙ্কে কাঁপছে বিশ্ব। আতঙ্কটা বাংলাদেশে আসতে বরং একটু সময় নিয়েছে।
ভিড় এড়িয়ে একটা সিটের কোণা ধরে দাঁড়ায় সাদিয়া। ট্রেনের দুলুনিতে ওর ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। সিটে বসা ছোট্ট মেয়েটি একটু সরে গিয়ে ওকে বললো, ‘বতো।’
ঢাকা থেকে নরসিংদী পর্যন্ত সে দাঁড়িয়েই ছিল। তাই একটু বসতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তবে দূরত্ব রক্ষা করেই বসার চেষ্টা করে। দুজনের সিটে অচেনা একজনকে বসতে দেওয়ায় মা যে বাচ্চার ওপর নাখোশ হয়েছেন, এটা বোঝার জন্য মনোবিদ হওয়া লাগে না। তবে, না বোঝার অভিনয় করে বছর তিনেকের বাচ্চার সঙ্গে টুকটাক গল্প করতে শুরু করে সে।
ওরা সবাই নোয়াখালীর যাত্রী। সাদিয়ার সঙ্গে দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দিতে ভৈরব ছেড়ে আসার পর মেয়েকে কোলে নিয়ে বসেন মা। একটু পরে মা-মেয়ে দুজনই ঘুমচোখে সাদিয়ার গায়ে ঢলে পড়েন। অন্য সময় হলে বিষয়টিকে কিছু মনে করতো না সে। কিন্তু ওর কাছে অন্যের সঙ্গে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখাটাই বেশি জরুরি মনে হয়। তাই সে উঠে দাঁড়ায়—একটু হেঁটে আসার ভান করে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে আসার পর ট্রেনের ভিড় বেশ একটু কমে। হাঁটতে হাঁটতে সাদিয়া ভাবে—‘হায় করোনা!’ এরপর নিঃশব্দে গাইতে থাকে, ‘তোমাকে বুঝি না প্রিয়, বোঝো না তুমি আমায়, দূরত্ব বাড়ে, যোগাযোগ নিভে যায়।’
নিরাশ্রয়
নীলার চাচা কয়েক দিন ধরে বলছিলেন, চাকরিটা বোধ হয় থাকবে না। লকডাউন শুরুর পরপর চাচা যে কথাটা বলতে শুরু করেছিলেন, অবশেষে তা-ই বাস্তব হয়ে গেলো। সত্যি সত্যি চাকরিটা হারালেন তিনি। এই সেদিন বাসায় ফিরে চাচিকে জানালেন, বাসা বদলাতে হবে আমাদের। এত বড় বাসায় আর কয়েক মাস থাকতে গেলে হাতের শেষ সম্বলটাও অবশিষ্ট থাকবে না।
দাঁড়িয়ে থেকে চাচিকে লজ্জায় ফেলতে চাইলো না নীলা। তবে নিজের রুমে গিয়ে ব্যাগ গোছাতে শুরু করে। চোখ ভরে আসে কান্নায়—আবার আশ্রয় খোঁজার শুরু হলো যে!
বাসা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে নতুন বাসাটা যে ছোট হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এখনই জিনিসপত্র কমাতে শুরু করে দিয়েছেন চাচি। প্রতিদিনই কিছু না কিছু কমানো হচ্ছে। নীলা প্রতিদিন এই সব দেখে আর ভাবে, এবার কী হবে?
ওর বয়স যখন সাড়ে তিন বছর, তখন দুর্ঘটনায় মারা যায় মা-বাবা। তাদের সঙ্গে একই গাড়িতে নীলাও ছিল। সবাই বলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে সে। নীলার নিজের কাছে অবশ্য এই বেঁচে যাওয়াকে দুর্ভাগ্য বলেই মনে হয়। শুনেছে, ওর মা-বাবা দুজনই বেশ ভালো চাকরি করতেন। চাকরি শুরুর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নিজেদের জমানো টাকায় গাড়িও কিনে ফেলেছিলেন তারা। নিজেই সেই গাড়ি চালিয়ে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়েন বাবা।
মা-বাবার সঙ্গে গাড়িটিও গেছে। বড় হয়ে শুনেছে গাড়িটা ভাঙারির দোকানে বিক্রি করার অবস্থা হয়েছিল। এমন দুর্ঘটনায় সে কেমন করে বেঁচে গেছে, সেটা এক বিস্ময়। সেই থেকে সবাই তাকে অপয়া ভাবে। তবু দাদা-দাদি ওকে ফেলতে পারেননি। ওই দুর্ঘটনার পরের বছর সাতেক সে ছিল দাদা-দাদির কাছে। ওর দশম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের রাতেই মারা যান দাদা। কয়েক মাস পর দাদিও। এরপরপরই অপয়া অপবাদ আরও পোক্ত হয়। এরপর থেকে বেলা-ওবেলা ভেসে ভেসে চলছিল নীলার জীবন। আজ ফুপির বাড়ি তো কাল মামার বাড়ি। তবু সে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।
বছর চারেক হলো এই চাচার বাসায় আশ্রয় মিলেছে। চাচা নিজেই ওকে নিয়ে এসেছেন। চাচি ওকে আদর-যত্ন না করলেও অবহেলা করেননি। অনেক অবহেলা-অনাদরে বড় হওয়া নীলার কাছে তাই এই আশ্রয়টাকে স্বর্গের মতো লাগে। চাচি নিজে ওর পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হোক না সরকারি স্কুল, খোদ রাজধানীর একটি স্কুল থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। আজই নীলার রেজাল্ট হয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়ে পাস করেছে সে। চাচি বলেছিলেন, রেজাল্ট ভালো হলে ভালো একটা কলেজে ভর্তি করে দেবেন। পরিস্থিতি যে বদলে গেছে। ওর ভালো রেজাল্টে কোনো উচ্ছ্বাস নেই কারও মনে।
এরপর কী হবে—ভেবে পাচ্ছে না নীলা। ভয়ে জানতেও চাইতে পারছে না। আশা করছে, যেহেতু শুরু থেকে সে চাচাতো ভাইবোন দুটির যত্মআত্তি থেকে পড়াশোনা করানো, সব দায়িত্ব পালন করে আসছে, তাই ওকে ফেলে দেওয়া হবে না।
ভাইটি মাত্র স্কুলে যেতে শুরু করেছে। বোনটি পড়ে ক্লাস টুতে। ওরাও শুরু থেকেই অনেক আপন করে নিয়েছে নীলাকে। ওদের খেলনার কোনো কমতি নেই। তবু প্রায়ই নীলাকেও খেলনা সাজতে হয়। বেশিরভাগ সময় ওকে ভাই-বোন দুটির টেডিবিয়ার সাজতে হয়।
চাচি বাসার আসবাবপত্রের প্যাকিং করতে শুরু দিয়েছেন। নীলার চাচাতো ভাই-বোন দুটিও কী নেবে, কী নেবে না, তা বাছাই করছে। চাচি প্রমাণ সাইজের পুরনো হয়ে আসা একটা টেডিবিয়ার ফেলনার মধ্যে রেখে দিলে দুই ভাই-বোন মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা শুরু করে। দূরে দাঁড়িয়ে এই সব দেখে নীলা। হঠাৎ করেই ভাইটি বলে, তুমি নীলাকে ফেলে যাবে, টেডিবিয়ারটাও নিতে দেবে না। তাহলে আমরা খেলব কেমন করে?
দাঁড়িয়ে থেকে চাচিকে লজ্জায় ফেলতে চাইলো না নীলা। তবে নিজের রুমে গিয়ে ব্যাগ গোছাতে শুরু করে। চোখ ভরে আসে কান্নায়—আবার আশ্রয়ের খোঁজে নামতে হবে যে!
মন্বন্তর আসছে
সকাল-সন্ধ্যা একজন নার্স আসতেন দাদির সেবায়। করোনাকালের লকডাউনে তার আসা বন্ধ হয়েছে। মীরাও বাসায় আটকা পড়েছে একই কারণে। এখন মীরার দায়িত্ব দাদিকে প্রতি সন্ধ্যায় ছাদে নিয়ে যাওয়া। প্রতিদিনের মতো তারা ছাদে হাঁটছে। মীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে পড়ে। চারুকলার শিক্ষার্থী হওয়ায় ছুটি ছাড়া ওর বাড়িতে আসা হয় না বললেই চলে। মাস তিনেক আগে যখন এসেছিল, তখন মায়ের অনেক পীড়াপীড়িতেও ছাদে যাওয়া হয়নি। এবার প্রথম দিন ছাদে এসেই বিস্মিত হয়েছিল, ওদের এই ছোট্ট শহরে এমন সুন্দর ছাদবাগান ওর মায়ের পক্ষেই করা সম্ভব।
অবশ্য চুয়াত্তরে লেখা রফিক আজাদের কবিতাটি সেদিনই মা পড়ে শুনিয়েছিলেন, একটু বড় হয়ে মীরাও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পড়েছে কবিতাটা—‘ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো।’
প্রথম যেদিন দাদিকে নিয়ে ছাদে এলো মীরা, দাদি ওকে বলেছিলেন, দেখেছিস, তোর মা কেমন সুন্দর বাগান করেছে। আজ ও যখন দাদিকে নিয়ে ছাদে এলো, তখন মা ছিলেন ছাদে, তার ছাদবাগান পরিচর্যায়। মাকে ডেকে দাদি জানতে চাইলেন, সুতপা তুমি এতদিন আসনি কেন?
দাদির নিয়মিত নার্স এই সুতপা। বেশ কয়েক বছর ধরেই দাদির এমন স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। তাই মাকে দেখে তিনি সুতপা ভেবেছেন। এই যে পৃথিবীর এমন গভীর অসুখ এখন, সর্বত্র চলছে লকডাউন, সেই সবের কিছুই দাদি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু বুঝতে পারছেন, তার নার্স সুতপা আসছেন না। নার্সের সঙ্গে দাদির খুব খাতির।
মা চলে গেছেন অনেকক্ষণ। দাদিকে আজ বর্ধমানের স্মৃতিতে পেয়েছে। তিনি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে রাঢ়বঙ্গে কাটানো শৈশবের স্মৃতিচারণ করছেন। লালমাটির ওই দেশটার কথা ছোটবেলায় ওরা অনেক শুনেছে দাদির কাছে। হঠাৎ নিচে একটা চিৎকার শুনতে পায়—ভাত দেন, ভাত।
দাদি কান খাড়া করে শোনেন। তারপর বলেন, মন্বন্তর আসছে।
দাদির বয়স এখন শতবর্ষের কাছাকাছি। তার মনে গেঁথে আছে তেতাল্লিশের মন্বন্তর। তখন তিনি ছিলেন কিশোরী। মীরা ছোটবেলায় দাদির কাছে সেই সময়ের অনেক কাহিনিই শুনেছে। দাদিরা তখন কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি বর্ধমানে চলে গিয়েছিলেন। তারপর সাতচল্লিশের ভারত ভাগের পর চলে এলেন এই দেশে। মীরারও দাদির কাছ থেকে গল্প শোনার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে। ওর মনে পড়ে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ও তখন বেশ ছোট, একদিন টেলিভিশনে ‘ভাত দে’ সিনেমাটি দেখার সময় মা বলছিলেন চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের কথা। সেদিন ইউটিউবে আবার দেখতে গিয়ে ও জেনে নিয়েছে সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে ১৯৮৪ সালে। অবশ্য চুয়াত্তরে লেখা রফিক আজাদের কবিতাটি সেদিনই মা পড়ে শুনিয়েছিলেন, একটু বড় হয়ে মীরাও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পড়েছে কবিতাটা—‘ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো।’