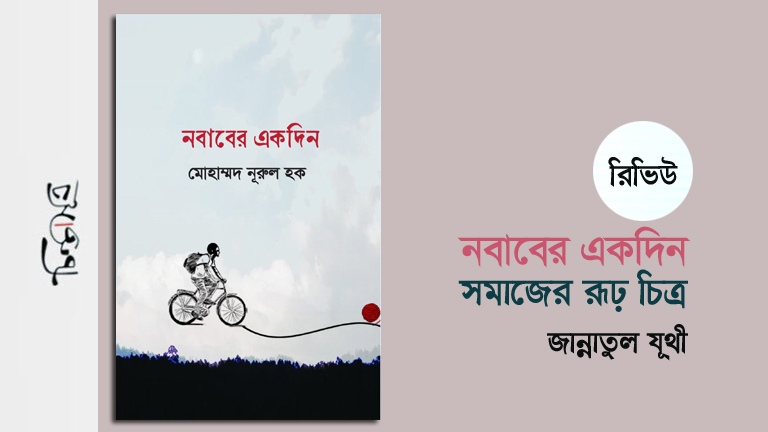বর্তমানকালে যে-সব সাহিত্যিক সৃষ্টিশীলতাকে মন থেকে লালন করেন, তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ নূরুল হক (জন্ম. ১৯৭৬) অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু শাখায় তাঁর দখল চোখে পড়ার মতো। মূলত কবি হলেও গবেষণা-প্রবন্ধেও রয়েছে তাঁর সমান বিচরণ। এর বাইরে তাঁর আরেকটি বিশেষ পরিচয় রয়েছে। তিনি একজন কথাসাহিত্যিকও। গতানুগতিকতার বাইরে এসে নিজের অভিজ্ঞতাকে তিনি গল্পের উপজীব্য করেছেন। তিনি শুধু কাহিনি বলে যান না, বরং একটি ঘটনাকে বাস্তবসম্মত করে তুলতে পরিবেশের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এই পরিবেশ ও বুননকৌশল তাঁর গল্পকে বিশেষত্ব দিয়েছে।
মোহাম্মদ নূরুল হকের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘নবাবের একদিন’। গল্পগ্রন্থের নাম চোখে পড়লেই মনে কৌতূহল জাগে। বইটিতে যেসব গল্পের অবস্থান তাদের আচার-ধর্ম-বর্ণ কী নবাবি হালের, না কি এই নবাব কোনো মোঘল বা বাদশাহী আমলের! সেই কৌতূহল কাটাতেই গল্পগ্রন্থটি হাতে নেওয়া। কিন্তু গল্পের মধ্যে প্রবেশ করতেই মন এক গভীর বেদনায় নিমজ্জিত হয়! মনে হয়েছে বইয়ের প্রত্যেক গল্পের প্রত্যেক চরিত্র আমাদের সবার চেনা-জানা। যান্ত্রিক জীবনে এই সুখেন, নবাব, পঙ্কজ প্রতিনিয়ত ঠোঁকর খাচ্ছে! তাদের টিকে থাকার লড়াই-সংগ্রাম ও সংঘাত মানুষকে জীবনের খুব কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বভাবত মানুষ নিজেই জানে না, তার জীবন কিসের জন্য! প্রিয় মানুষদের ভালোবাসায় যে জীবনকে পুরুষেরা উৎসর্গ করতে সর্বদা উৎসুক, সেই মানুষরা কি ব্যক্তির দুঃখ-কষ্টের সঙ্গী হতে পারে?
গল্পগ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্প আমাদের জীবনের প্রতি, সমাজের প্রতি, ব্যক্তির জীবনদর্শনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে! গল্পে প্রবেশ করে মনে হয়েছে জীবন শুধু বিলিয়ে দেওয়ার, না কি এই যান্ত্রিকজীবনে নিজের বলতে কিছু সঞ্চয় করা উচিত ব্যক্তির? সেই উত্তর লেখক না দিলেও পাঠকের মনে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে!
নবাবের একদিন গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প ‘একদা এক চন্দননগরে’। এই গল্পের প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন ভারতবর্ষে রাজা-জমিদার-প্রজার যুগ ছিল। কালের হিসাবে তা প্রচীনকাল থেকে উৎরে মধ্যযুগে পড়েছে। কিন্তু গল্পের প্রেক্ষাপট সময়ের ঘেরাটোপ পেরিয়ে চিরন্তনী রূপ নিয়েছে৷ প্রজার ওপর ক্ষমতাসীনের শোষণের চূড়ান্ত রূপ এই গল্পে ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের সূচনা হয়েছে পরিবেশ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। আর এই পরিবেশ বর্ণনার মধ্যে দিয়েই লেখক বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, এই চন্দননগরের শোষণ বহুকাল আগের। এখানকার নারী-পুরুষ সবাই রাজার অনুগত। যুগের পরম্পরায় এরা রাজার দাসে পরিণত হয়েছে। আরও বলা ভালো, হতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তাদের সামনে কেউ নেই, যার কাছে বিচার দেওয়া যাবে! স্রষ্টার কাছে বিচার দেবে, সে-ই ভরসাও তারা পায় না। কারণ দিনশেষে শোষণের চূড়ান্ত সীমা তাদের ললাটে লিখিত থাকে। গল্পের এ পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। সেখানে একটি বাক্য রয়েছে এমন, ‘ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্র পল্লীতে, এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।’ মোহাম্মদ নূরুল হকের ‘একদা এক চন্দননগরে’ও মনে হয় ঈশ্বরের দেখা নেই। তাই মাখন লাল বা তার ছেলে সুখেন লাল ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের শিকারে পরিণত হয়েছে।
দাসত্ব দিনে দিনে মাত্রা ছাড়িয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে! যেখানে আমরা দেখতে পাই, রুখাই রাজের অভিষেকের সময় প্রজা মাখন লালকে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে কপালে তিলক এঁকে দিতে হয়েছিল। আর বংশ পরম্পরায় তারই পুত্র দুখাইয়ের অভিষেকের দিনক্ষণ এগিয়ে আসতে থাকে। রাজার অভিষেকে তাই মাখনলালের সুদর্শন পুত্র সুখেনের ডান হাতের আঙুল কেটে তিলক দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। এর মধ্যে সুখেন দুখাই রাজের অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ। লেখক দুখাইয়ের অত্যাচারকে বোঝাতে গিয়ে মহাভারতের দুর্যোধনের সাদৃশ্য টেনেছেন। সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রই জানেন যে, মহাভারতের দুর্যোধনের দুঃশাসন কতটা পীড়নদায়ক ছিল। একসময় সুখেনকে কেউ আর খুঁজে পায় না। সুখেনকে না পেয়ে দুখাই রাজের আদেশানুসারে বৃদ্ধ মাখন লালকে ধরে নিয়ে আসা হয়। এতে একদিকে তার অভিষেকও হলো অন্যদিকে সুখেনের ওপর প্রতিশোধও নেওয়া গেলো। শেষপর্যন্ত নতুন রাজা দুখাইয়ের অভিষেকের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। হবু রাজার সম্মতি মিলতেই পারিষদের সবাই উৎসুক হয়ে ওঠে। কোতায়েলের নেতৃত্বে একদল প্রহরী মাখনকে ধরে আনে। ধস্তাধস্তিতে দুখাইরাজ সজোরে মাখনের মাথায় লাথি বসিয়ে দেয়। এরপর যতটুকু ঘটনার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা লেখকের সচেতন মনের প্রয়াস। তিনি এখানে যে দ্রোহের সুর উত্থাপন করেছেন, তা মাখনের অবচেতন মনের, না কি সচেতন মনের ভাবনা; তা লেখক স্পষ্ট করেননি। কিন্তু লেখক একধরনের সুপ্ত বা গুপ্ত বিদ্রোহী চেতনাকে তুলে ধরেছেন এভাবে:
‘আকস্মিক আঘাতে হতভম্ব মাখন। নাকের ভেতর যেন লবণ স্বাদ অনুভূত হলো। হাত দিয়ে দেখে রক্ত। তার চোখে তখন ঘনায়মান অন্ধকার। সেই ঘোলাটে চোখে একচোখা ভগবানের ভরসাশূন্য আকাশের দিকে তাকায় সে। কিন্তু ভয়ার্ত আকাশে ভগবানের কোনো সাড়া পায় না মাখন। তখনই তার মনে হয়, ন্যায়বিচারের জন্য মানুষ চিরকাল ভগবানের ওপরই ভরসা করবে কেন। কখনো কখনো কি মানুষ নিজের হাতে ন্যায়ের দণ্ড তুলে নিতে পারে না? মানুষই কি ন্যায়ের দণ্ড হাতে ভগবান হয়ে উঠতে পারে না? তার মনে দীগন্তরেখায় অপসৃয়মাণ ক্ষীণ রেখার মতো আশা জাগে, যদি সুখন সেই ভগবান হয়ে আসতো! যদি সুখন আজ প্রতিশোধ নিতো। আর তখনই তার মনে হলো, প্রহরীদের ভেতর থেকে শা করে একটি বল্লম এসে পড়লো দুখাই রাজের কপালে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো কপাল থেকে। ঢলে পড়লো দুখাই রাজ। সভায় শোরগোল পড়ে গেলো। সবাই দিগ্বিদিক ছুটছে। আর সেনাপতি পেছন ফিরে দেখে-প্রহরীদের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সুখন লাল।’ (নবাবের একদিন, পৃ. ১৪-১৫)
এই গল্পে সুখেনের যে প্রতিবাদী সত্তা, তা গল্পের প্রথম থেকেই কিঞ্চিৎ লক্ষ করা গিয়েছিল। কিন্তু দুখাইয়ের নির্দেশ তাকে মানতেই হতো। আর সুখেনের বাবা মাখন লাল ছেলেকে বুঝিয়ে দেয় সহ্য করাই গরিবের ধর্ম। দরিদ্রের প্রতিবাদের ক্ষমতা থাকে না! তাই মাখন লাল, সুখেন রাজার ভৃত্য। কিন্তু লেখক প্রতিবাদী। তাই তিনি তার চরিত্রের বেতর দ্রোহের স্বরূপ তুলে ধরেছেন শেষমেশ। যদিও সেই বিদ্রোহ অনেকটা প্রছন্ন! লেখকের প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনা মাখনের অচেতন সত্তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে!
‘নবাবের একদিন’ গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে মোহাম্মদ নূরুল হক নিজেকে ভেঙেচুরে উপস্থাপন করেছেন। এই নবাব আমাদের সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত প্রত্যেকটি পুরুষ। আমরা জানি, একজন পুরুষ পরিবারের জন্য কতটা বলিদান করেন। এই গল্পের নায়ক আসাদুল্লাহ নবাব পরিবারের চাপে চন্দননগরের এক চর থেকে বাড়তি উপার্জনের আশায় শহরমুখী হয়। তারপর নগরজীবনের রূঢ়তা তাকে ধীরে ধীরে মানসিকভাবে ভঙ্গুর করে ফেলে। একদিকে পরিবারের চাপ, অন্যদিকে বেসরকারি চাকরিতে নানা ধরনের জটিলতা নবাবের জীবন ক্রমাগত বিষিয়ে তোলে। গল্পের নবাব মূলত সংসারে সবার চাহিদা পূরণের অন্যতম হাতিয়ার। অতি সাধারণ জীবনযাপন করলেও পরিবারের চাহিদা পূরণে সর্বদা নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে নবাব। গল্পে দেখতে পাই, যখন পরিবারের চাহিদা পূরণে কিঞ্চিৎ ঘাটতি দেখা দিয়েছে, তখনই নবাবের ওপর নেমে এসেছে কথার নির্মম আঘাত! পদোন্নতি পেয়ে কোম্পানির অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর হলেও সাইকেল চেপেই অফিস করেছে গল্পের নায়ক। এজন্য বস ও সহকর্মীদের তির্যক মন্তব্যের শিকারও তাকে হতে হয়। একসময় বিনা-নোটিশেই তার সেলারি থেকে দশ হাজার টাকা কেটে নেয় কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে স্ত্রী রাশেদার রূঢ় আচরণ, ছেলে রাশেদের ইতালি যাওয়ার জন্য পনেরো লাখ টাকা জোগানোর দুশ্চিন্তা, কন্যাদের অমূলক আবদার, গ্রামের বাড়ি থেকে অসুস্থ ভাইয়ের জন্য টাকা চেয়ে মায়ের অনুরোধ; সবমিলিয়ে গল্পটিতে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর টানাপড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত গল্পটিকে নতুন রূপ দিয়েছে। নবাবের সুখের একদিন আর আসে না। গল্পে পাই,
‘নবাব মেয়ের দিকে তাকাতে চায়। পারে না। একবার চোখ যায় স্ত্রী-সন্তানের দিকে, একবার দয়াহীন-মায়াহীন ছাদের পানে। দেখে সেখানে ছাদ নয়, শূন্য আকাশের তলে কোমল ঠোঁটের মতো মসৃণ মেঘের পাপড়ি উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই মেঘের ফাঁকে দুই হাত বাড়িয়ে স্বর্গীয় দূত জিবরাইল দাঁড়িয়ে আছে। না, জিবরাইল নয়, আব্বা দাঁড়িয়ে আছে। আব্বা ডাকছে। নবাবের চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা তপ্ত জল গড়িয়ে পড়ে।’ (নবাবের একদিন, পৃ. ২৮)
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শুধু নারীই নয় আধুনিক যুগে এসে পুরুষও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। মোহাম্মদ নূরুল হকের গল্পে এটাই বেশ ভিন্ন দিক। তিনি নারীর প্রতি অবিচারকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি পুরুষনির্যানের বিষয়কেও চিত্রিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শুধু নারী নয় যুগের অববাহিকায় পুরুষও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার! কিন্তু পুরুষ অসহায়! আমরা জানি, এক্ষেত্রে দেশের আইনে নারীর জন্য সুযোগ-সুবিধা বা বিচার পাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও পুরুষ নির্যাতনের কোনো সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার কথা শোনা যায় না। এমনকি পুরুষ পরিবার-পরিজন দ্বারা নিগৃহীত হলে আইনের শরণাপন্ন হয় না। ‘মেল ইগো’ যেমন তাকে নির্যাতক হিসেবে গড়ে তোলে, তেমনি নির্যাতনের শিকারেও পরিণত করে! গল্পে দেখতে পাই, নবাব পরিবারে সুখী নয়। সে পরিবারে শুধু অর্থ-যোগানদাতা। পরিবারের মায়া-মমত্ব ভালোবাসা তার প্রতি নেই। আর এখানে যে নারী চরিত্রটি লেখক উপস্থাপন করেছেন তার নাম রাশেদা। এ সমাজে রাশেদাদের উপস্থিতি খুব একটা কম নয়। যুগ পাল্টেছে। নারী তার মায়া-মমতা-কোমলাতাকে হারিয়ে নিক্তির ভিত্তিতে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেছে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা রাশেদার নেই বরং সন্তানদের সে উসকে দেয়, যেন বাবার কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা খসাতে পারে! রাশেদা শুধু এখানেই থেমে থাকেনি! সে সন্দেহপ্রবণ নারী। স্বামী নবাবের চাকারিতে হুট করে বেতন কমে যাওয়ার প্রতি তার কোনো দুঃখ বা সহমর্মিতা নেই। উল্টো সে দোষারোপ করেছে স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আসক্তি আছে! এই গল্পে লেখক বর্তমান সময়কে খুব যত্ন করে তুলে ধরেছেন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে অবিশ্বাস, মায়া-মমতাহীন এক রূঢ়তা! যার দরুণ পরিবারগুলো ভেঙে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। নারী ও পুরুষের ভেতরের বোঝাপড়া-ভালোবাসা থমকে গেছে কালের ধুলোয়।
‘ঠাণ্ডা মার্বেল’কে প্রেমের গল্প মনে হলেও এতে সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রধান চরিত্র পঙ্কজ ও রাধা। পঙ্কজের সঙ্গে রাধার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ট্রেনে। টিকিটে একই সিট হওয়ায় খুব অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দুজনের সাক্ষাৎ হয়। অতপর একটা সুন্দর সম্পর্কের সূত্রপাতের ঈঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। গল্পের নেপথ্যে রয়েছে সমাজের করুণ ও নিষ্ঠুর সত্য। পঙ্কজ মল্লিকের চাকরির ইন্টারভিউ এবং মামা-চাচা না থাকায় চাকরি পাওয়া নিয়ে শঙ্কা, পরিশেষে সেমিনারে পরিচিত ব্যাংকার আব্দুল সালামের সুপারিশে তার চাকরি এই গল্পের প্রেক্ষাপটকে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। কাকতালীয়ভাবে ব্যাংকে পঙ্কজের সহকর্মী রাধা। ধীরে ধীরে রাধার সঙ্গে পঙ্কজের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। কারণ পঙ্কজ মল্লিক যে সাবজেক্টে পড়েছেন, তার কিছুই ব্যাংক-জবে কাজে লাগেনি। ফলে টুকিটাকি সব কাজ শিখতে হয়েছে রাধার কাছ থেকে। গল্পের মূলসুর ভিন্ন জায়গায়। সহকর্মী রাধার সম্পর্কে পঙ্কজ তেমন কিছু না জানলেও হঠাৎ লক্ষ করে রাধা অফিস ছুটির পর বসে থাকে। পঙ্কজ জিজ্ঞেস করতেই রাধার করুণ আর্তি বস তাকে থেকে যেতে বলেছেন। পঙ্কজ বসের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। তাই জোর করেই রাধাকে সেদিন অফিস থেকে বের করে আনে। রাধা তাকে শুধু এটুকু বলে তার কিঞ্চিৎ ভুলের কারণে বসের লোলুপ দৃষ্টি তার দিকে পড়েছে। কিন্তু কারণ উহ্য থাকে পঙ্কজের কাছে। এজন্য বসের রূঢ় আচরণের শিকার হতে হয় রাধাকে। অন্যদিকে বেশ কিছুদিন ধরে রাধা আর অফিসে আসে না। পঙ্কজ বেশ চিন্তায় পড়ে যায়। হঠাৎ একদিন পঙ্কজের সঙ্গে রাধার সাক্ষাৎ হয় আবার। সে জানতে পারে সংসারের অশান্তি থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে রাধা স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছে। এরপর রাধা চাকরিতে নিয়মিত হয়। দুজনের কথোপকথন বাড়তে থাকে। রাধার দুঃখ-কষ্ট আর পঙ্কজের কষ্ট মিলিমিশে একাকার হয়ে যায়। পঙ্কজও তার অসহায়ত্বের কথা জানায় রাধাকে। গল্পে পাই:
‘সব শুনে পঙ্কজ বলে, আপনি ভুল করেছেন। সংসারের কথা বাইরের লোককে বলতে হয় না। তাহলে সে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেই। ম্যানেজারও তাই করছে। দুজনের কথা বাড়তে থাকে। একসময় পঙ্কজেরও চোখ ছলছল করে ওঠে। রাধা বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকায়, ও কী, আপনার আবার কী হলো? পঙ্কজও নিজের দাম্পত্য জীবনের অশান্তির কথা বলে। কিভাবে সে টাকা উপার্জনের মেশিন হয়ে পরিণত হলো, সেই বর্ণনা দেয়। ঘরে স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। সেই সংসারে মাসে মাসে তাকে টাকা দিতে হয়। ব্যস এটুকুই। সে কখনো স্ত্রীর কাছে যেতে পারে না স্বামীর অধিকার নিয়ে। স্ত্রী তাকে ডিভোর্সও দেয় না, সেও দিতে পারে না, সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে। তার টাকায় স্ত্রী ফূর্তি করে, তার টাকায় বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে স্ত্রী ঘুরে-বেড়াতে যায়। স্বজনরা ডিভোর্স দিতে বলে। সে বুঝতে পারে না কী করবে! সব শুনে রাধা বলে, কিছু মনে করবেন না, আপনি একটা বলদ! পঙ্কজ, আহত হয় না। মলিন হাসে, হয়তো আপনার কথায়ই ঠিক। গত দশবছরে নিজেকে বলদই মনে হয়েছে। সর্বার্থেই।’ (নবাবের একদিন, পৃ. ৩৯)
ঠাণ্ডা মার্বেল গল্পে রাধার চোখকে লেখক ঠাণ্ডা মার্বেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে চোখ নির্লিপ্ত, ভাবলেশহীন! দুজনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি যখন নিবিড়ভাবে মিলিমিশে একাকার হয়েছে, তখনই পঙ্কজ তার মনের অনুভূতিকে জাহির করার চেষ্টা করেছে। আর তার উত্তর রাধার ঠাণ্ডা মার্বল সদৃশ চোখ! রাধা ও পঙ্কজ এ সমাজের প্রতিনিধি। লেখক পঙ্কজ এবং রাধার অসহায়ত্বকে তুলে ধরেছেন। সমাজের প্রথা-নিয়ম ও রীতিনীতি মানতে মানুষ নিজের জীবনকে কখন যে জড়বস্তুতে পরিণত করে ফেলে তা পঙ্কজের দিকে লক্ষ করলেই অনুমেয়। এ সমাজে রাধা ও পঙ্কজের ঘাটতি নেই। সমাজের ভেতর থেকে চরিত্রগুলো তুলে এনেছেন গল্পকার।
মোহাম্মদ নূরুল হকের প্রতিটি গল্পের স্বাদ ভিন্ন। আগের তিনটি গল্পের মতো, ‘কালো মেঘের দুপুরে’ও এক বিশেষ বার্তা লক্ষণীয়। এই গল্পে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আড়ালে এক নিদারুণ সত্য উপস্থাপন করেছেন লেখক। যোগ্যতা ও দক্ষতাকে ডিঙিয়ে মানুষ সত্যের পথে থাকতে পারে না। গল্পে অনেকগুলো চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রতিটি চরিত্র কাহিনি নির্মাণে সমান ভূমিকা রেখেছে। নাসরিন, রেবতী, শ্যামলেন্দু, রাজীব ও সুবিমলের মাধ্যমে গল্পের প্রেক্ষাপট সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সুবিমল দলের নামমাত্র প্রেসিডেন্ট। অন্যদিকে পার্টি অফিসের সেক্রেটারি শ্যামলেন্দু তথা শ্যামল। দলের নেতৃত্ব এবং দলকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সুবিমল, রাজীবরা শ্যামলের কথা মেনেই চলে। সেক্রেটারি হিসেবে একহাতে সব সামলানো শ্যামলের জন্য কষ্ট হয়ে যায়। তাই জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচন করতে চায়৷ এক্ষেত্রে প্রার্থী দুই জন। স্থায়ী কমিটির সদস্য নাসরিন। সে পরিশ্রমী, মেধাবী এবং খুবই দায়িত্বশীল। অন্যদিকে রেবতী স্মার্ট, কথা বলে বেশ গুছিয়ে। কিন্তু শ্যামল জানে নাসরিনকে দিয়ে সব সম্ভব নয়। রেবতী হলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। প্রথমত, শ্যামলের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সাড়া দিতে পারবে। দ্বিতীয়ত, তাকে দিয়ে দলীয় প্রধানের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে পারবে। ফলে শ্যামল তার ইচ্ছেনুসারে রেবতীকেই জয়েন্ট সেক্রেটারির ঘোষণা দেয়। যদিও দলের স্থায়ী কমিটির কনিষ্ঠ সদস্য রাজীব শ্যামলকে বলেই ফেলে যে, লিডার আপনি ভুল পথে এগোচ্ছেন! কিন্তু শ্যামল তার নিজের ইচ্ছেকে জাহির করতেই রেবতীকে দলের উচ্চ পদে বসায়। গল্পে পাই, নতুন জয়েন্ট সেক্রেটারি রেবতী বেশ কিছুদিন সেক্রেটারি শ্যামলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে। হঠাৎ একদিন শ্যামল আবিষ্কার করে, রেবতীর চলন-বলন-ধরণ সব পাল্টে গেছে। রেবতী নিজেই এখন কর্মসূচি-সভা-মিছিল-জনসভার প্রেস রিলিজ দিয়ে দেয়। এর মধ্যে সরকারবিরোধী আলোচনা তুঙ্গে। সুবিমল মিত্র-রেবতীসহ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের পরিকল্পনায় দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আর সরকারবিরোধী কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুরো দল দুই ভাগ হয়ে যায়। একটা পর্যায়ে সুবিমল ও শ্যামলের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। রাজীবও বুঝতে পারে দলের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে শুধু রেবতীকে জয়েন্ট সেক্রেটারির পদ দেওয়ার কারণে। সভায় রাজীব সবার উদ্দেশ্য যখন শ্যামল ও রেবতীর সব কথা ফাঁস করতে উদ্যত তখন শ্যামল উত্তেজিত হয়ে রাজীবের মাথায় চেয়ার ভাঙে! এই ঘটনাকে লক্ষ করে রেবতীর পরামর্শে সুবিমল শ্যামলকে দল থেকে বহিষ্কার করে। গল্পে পাই:
‘দরজায় দাঁড়িয়ে বের হওয়ার আগে আরেকার হলরুমের দিকে তাকায়। এবার চোখ পড়ে নাসরিনের দিকে। সে দেখে সেই চোখ স্থির। শান্ত। কোনো ক্রোধ নেই। নেই কোনো করুণার আলোড়নও। ঠা-ঠা দুপুরকেও মনে হয় মেঘাচ্ছন্ন। যেমন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে অফিসের নিচে। শেষ সিঁড়িতে নামতেই চোখে পড়ে, একঝাঁক পিঁপড়ার পিঠে একটি মৃত টিকটিকি। শ্যামলের বুক থেকে একটি গভীরতর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তাকে দেখে ড্রাইভার এগিয়ে আসে, গাড়ি বের করবো স্যার? ম্লান হাসে শ্যামল। বলে, নাহ। দরকার নেই। নেমে আসে রাস্তায়। দেখে সারি সারি প্রাইভেট কার। আছে দুই-একটা রিকশাও। সেদিকে এগোয় শ্যামল। ডাকে-ওই খালি যাবি?’ (নবাবের একদিন, পৃ. ৫৩)
গল্পের কাহিনিতে বেশ টুইস্ট রেখেছেন লেখক। শ্যামল ও রেবতী দুটি চরিত্রই লেখকের সচেতন মনের প্রয়াস। সমাজে এহেন চরিত্রের উপস্থিতি অনেক। যোগ্যতার মাপকাঠিতে নাসরিন শ্রেয়, একনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হলেও তাকে দলের কোনো দায়িত্বে রাখা হয়নি; অন্যদিকে রেবতী তার সতীত্ব লুটিয়ে দিয়ে দলের জয়েন্ট সেক্রেটারির পদে নির্বাচিত হয়। সেই রেবতীই নিজের স্বার্থে শ্যামলকে ল্যাং মারে। একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলে সহজেই বোঝা যায়, রেবতীদের চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য। রেবতী ও শ্যামলেরা দেশের-দশের জন্য কাজে নিযুক্ত হয় না। তারা বড় স্বার্থে কাজ না করে ব্যক্তিস্বার্থকে দেখে। একসময় সেই চক্রে নিজেই ফেঁসে যায়। যেমনটা শ্যামলের ভাগ্যে জুটেছে। যে নাসরিনকে ঠকিয়ে রেবতীকে কাছে টেনেছে, উচ্চপদ দিয়েছে; সেই রেবতীই শ্যামলকে পদচ্যুত করিয়েছে।
সমাজের অবক্ষয় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে ‘জতুগৃহ’ গল্পটিতে। আমরা জানি, লেখক মাত্রই সমাজের দর্পণস্বরূপ। আর মোহাম্মদ নূরুল হকের এই গল্পটি পাঠে সেটা আরও একবার প্রমাণিত হয়। ‘জতুগৃহ’ গল্পটির সূচনা হয়েছে ফ্লাশব্যাকের মধ্যে দিয়ে। গল্পের প্রথমেই লেখক আমাদের জানান দেন শেষরাতে শান্তিনগর মোড়ে ডাস্টবিনের পাশে নুপুর কামালের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ‘দৈনিক নিরপেক্ষ’ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রকিব উদ্দিনের ভাতিজি নুপুর। গল্পের এটুকু অবতারণা করেই গল্পকার আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন কদিন আগে ঘটে যাওয়া আরও একটি নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে! এই শান্তিনগরেই এক এসআইয়ের বাসা থেকে কিশোরী গৃহকর্মীর লাশ পাওয়া গিয়েছিল। পুরো শরীর পুড়ে গিয়েছিল তার। পত্রিকাগুলো শুধু গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধারের ঘটনাই উল্লেখ করেছিল। সেখানে গৃহকর্তার নাম-ধাম কিছুই প্রকাশিত হয়নি। এ নিয়ে ঘোর আপত্তি তুলেছিল দৈনিক নিরপেক্ষ পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার কবীর হাসান। কিন্তু সম্পাদকের জোর হুকুম ঘটনাটি নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি না করতে। কারণ গৃহকর্মী যে বাড়িতে কাজ করতো সেটা এক প্রভাবশালী এসআইয়ের বাসা। সব মিডিয়ার ক্রাইম রিপোর্টারকে সে কিনে ফেলেছে তাহলে কবীরের এত লাফালাফি কেন? দৈনিক নিরপেক্ষ পত্রিকার দক্ষিণ পাশের পরিত্যক্ত গ্যারেজটিতে নসিমন গাঁজা বিক্রির রমরমা ব্যবসা চালায়। এই আড্ডায় আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, দিনমজুর, সাংবাদিক, পুলিশ কনস্টেবল, এসআইসহ সব ধরনের মানুষ। কবীর তার সহকর্মীদের খুঁজতেই এই আড্ডায় ঢুঁ মারে। সেখানেই পেয়ে যায় শাকিল, সাজ্জাদ, কামালসহ হাফডজন সাংবাদিককে। তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে রাজনীতি, সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র। গল্পকার তুলে ধরেছেন এভাবে:
‘হঠাৎ রাজনৈতিক নেতার মতো ভাষণ দেয় শাকিল, শোনেন কবীর ভাই। কামাল-কবীর দুজনই তার দিকে ঘাড় ফেরায়। শাকিলের হাত উত্তোলিত, মুষ্ঠিবদ্ধ। চোখ জ্বলজ্বল করছে। আধো আলো-আধো অন্ধকারে চিতার চোখ বলেই ভ্রম হয়। দুই সহকর্মী তার দিকে তাকালে একটু থেমে এবার বলে, এই যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, এই যে শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন এসব কেন হচ্ছে জানেন? কারও উত্তরের অপেক্ষা না করেই সর্বজ্ঞের মতো নিজেই জবাব দেয়, দেশে বিরোধী দল নেই বলে। শাকিলের কথা শুনে কামাল আপত্তি জানায়, বিরোধী দল থাকা-না থাকার সঙ্গে এসব খুন খারাবির কী সম্পর্ক শাকিল? প্রশ্ন শুনে ঈষৎ হাসে শাকিল, সেই হাসি জানিয়ে দেয়, রাজনীতির পাঠ না থাকলে এমন বোকার মতো প্রশ্ন করা যায়। এরপর যেখানে থেমেছিল, সেখান থেকে শুরু করে, সম্পর্ক তো আছে। দেশের শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎসহ নিত্যপণ্যের দাম এভাবে হু-হু করে বাড়তে পারতো না। দাম বাড়ালেই বিরোধী দলগুলো আন্দোলনে নামতো। হরতাল-অবরোধ দিতো। দেশে এসব আছে এখন? এই ২০২৩ সালে এসে সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি কী করছে? দলটি আছে সত্য, কিন্তু দলটির কাজ কী? সরকার-আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা ছাড়া আর কিছু আছে? নাই।’ (নবাবের একদিন, পৃ. ৫৬-৫৭)
শাকিলের কথার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে সমাজ, দর্শন ও রাজনীতির গভীর তত্ত্ব। সমাজে তখনই অপরাধ ও শোষণের চিত্র বেড়ে যায় যখন সঠিকভাবে গণতন্ত্রের চর্চা না হয়! কোনো ভয়ই কবীরের মনকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে না। সে আসল অপরাধীকে সমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু সম্পাদকের নিষেধ তাকে ভাবিয়ে তোলে।
গৃহকর্মী সুমীর নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর কবীরের মন আরও খারাপ হয়ে যায়। সত্যকে সবার সামনে সে প্রকাশ করতে পারে না। যদিও জানে আসল অপরাধী কে! সুমী মৃত্যুর আগে বলে গেছে! এ নিয়ে কবীর শান্তিনগরে এসআই মিজানের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে। তারা সুমীর কান্নার আওয়াজ শুনডে পায়। এসআই মিজানের শালা আদম ব্যবসায়ী। সবমিলিয়ে কবীর বুঝতে পারে সুমীকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত ছিল। কবীরের বারবার মনে হয় সাগর-রুনির কথা। এছাড়া যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নিচে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় সফিক উদ্দিনকে। কবীরের কাছে অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে নুপুর হত্যার মামলার ঘটনায় অনেক করেছেন, ভালো চান তো এখানেই থেমে যান। গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লেখকের দৃষ্টি ও বুননকৌশল মনকে আকর্ষণ করেছে৷ এরপর কী ঘটতে চলেছে? খায়ের কবীরের কাঁধে হাত রেখে বলে চাকরিটাই করে যান, বেশি সাংবাদিকতা করবেন না। এর মধ্যে একটি সুখবর আসে রকিব উদ্দিন পূর্ণ সম্পাদক হন। সবাই ফুল নিয়ে রকিব উদ্দিনকে বরণের তোড়জোড় করে। সম্পাদকের পাশে বসা এসআই মিজানের শালা শিল্পপতি সাদেক খান। কবীর আর সহ্য করতে পারে না। কোথায় যাবে ভাবতে ভাবতে শাহবাগ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে পৌঁছে যায় আর তখন একটি মাইক্রোবাস ঝাঁ করে এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়। কবীর কিছু বলে ওঠার আগেই মাথায় ভারী কিছুর আঘাত পড়ে। গল্পের পরিসমাপ্তি এখানেই।
মোহাম্মদ নূরুল হক গল্পটিতে অনেকগুলো বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এখানে স্থান পেয়েছে রাজনৈতিক মতাদর্শ, গৃহকর্মী নির্যাতন, ঘুষ-দুর্নীতি, মাদক ব্যবসা, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দাপট, সাংবাদিকতার অপেশাদার আচরণ প্রভৃতি। গল্পে কবীর লক্ষ্য করে সমাজের ধ্বসে যাওয়া চিত্র। নুপুর, সুমীর হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে লেখক তুলে ধরেছেন দেশের আলোচিত হত্যাকাণ্ড সাগর-রুনির ঘটনাকে। সচেতন নাগরিক মাত্রই জানেন আইনের শাসনের কত ভঙ্গুর পরিস্থিতি! যে রক্ষক সেই ভক্ষকে পরিণত হয়েছে। এজন্য সর্বত্র দুর্নীতি, দমন-পীড়ন ও লুটতরাজ চলছে।
করোনাকালে এক নিম্নবিত্ত পরিবারের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে ‘আজমুদ্দিনের দোষ’ গল্পে। সমাজের করুণ ও নিষ্ঠুর সত্য লেখক খুব গুছিয়ে এখানে বলার চেষ্টা করেছেন। আজিমুদ্দিন নাটোরের এক মুদী দোকানী কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সে এখন ঢাকা শহরের রিকশাচালক। ২০২১ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে ঢাকার এক বস্তিতে এসে ওঠে। মেয়ে রহিমা ও বউ জমিলাকে নিয়েই আজিমুদ্দিনের পরিবার। গ্রামে মেয়ে ও বউকে রেখে আসলে হয়তো ঢাকা শহরে যতটুকু উপার্জন হয় তা দিয়ে সে ভালো মতো চলতে পারতো। কিন্তু স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে তো ফেলে আসতে পারে না। খালি হাতে যখন কমলাপুর রেলস্টেশনে নামে তখন এলাকার রিকশাচালক জাফর তালুকদারের সঙ্গে তার দেখা। এরপর কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে তেজগাঁও বস্তিতে জাফর তালুকদারের ঝুপড়িতে আসে তারা। থাকার ব্যবস্থা কোনরকম হওয়ার পর জাফরই আবার এগিয়ে আসে। দিনের বেলা যে রিক্সা জাফর চালায় সেটাই রাতের বেলা আজিমুদ্দিন চালাবে। শুধু প্রতিদিন রিকশা মালিককে দুইশত টাকা করে দিতে হবে। কথামতো জাফরের পরামর্শে আজিমুদ্দিনের টানাটানির সংসার চলতে থাকে।
ঢাকায় এসে পরিবারোর জন্য দুবেলা খাবার জোটাতে পারলেও মেয়েটাকে স্কুলে ভর্তি করতে পারে না আজিমুদ্দিন। স্কুলের বাড়তি ফি দেওয়ার ক্ষমতার আজিমুদ্দিনদের নেই। তাই গ্রামে থাকতে রহিমা ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়তে পারলেও দারিদ্র্যতার কষাঘাতে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দিতে হয়েছে। আজমুদ্দিন মনে মনে ঠিক করে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রিকশা চালিয়ে কিছু টাকা জমাবে তারপর জন্মভিটেয় ফিরে যাবে। কিন্তু সারারাত রিক্সার প্যাডেল ঘুরালেও তার ভাগ্যের চাকা ঘোরে না! একে সংসারে নিত্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই অন্যদিকে করোনাকলীন মহামারীর প্রকোপ আজিমুদ্দিনের জীবনকে তছনছ করে দেয়। ঢাকার রাস্তায় রিক্সা চালকদের মতো ছোটখাট শ্রমজীবীদের কোন সম্মান নেই, শ্রদ্ধা নেই! যাত্রীদের উপর্যুপরি খারাপ ব্যবহার আজিমুদ্দিনের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। এরই মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে রহিমা। আমরা জানি, করোনার সময়ে হাসপাতালগুলোও হটস্পটে পরিণত হয়েছিল। তাই ডাক্তারাই পরামর্শ দিয়েছিল বাড়িতে থেকে যতটা চিকিৎসা নেওয়া যায়। ফলে জাফর তালুকদারের সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়েকে সেবার বাড়িতেই রাখে আজিম। সেবারের মতো অনেক ভুগে-টুগে মরতে মরতে বেঁচে ওঠে রহিমা। রহিমার অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে জাফর মাঝে মধ্যেই রহিমাকে দেখতে আসতো। কিন্তু জমিলা লক্ষ্য করে কিশোরী মেয়ে রহিমার দিকে জাফরের কুদৃষ্টি! তাই মেয়েকে কিছুটা আগলে রাখতে চেষ্টা করে জমিলা। ঘটনা পরম্পরায় দেখতে পাই, সেসময় রহিমা বেঁচে গেলেও শেষপর্যন্ত রহিমাকে রক্ষা করতে পারেনি আজিমুদ্দিন দম্পতি। রাতে রিক্সা চালানোর সময় হঠাৎ জমিলার ফোন আসে, রহিমা প্রচণ্ড অসুস্থ। জাফরের কাছে আজিমুদ্দিন শুনেছিল তাদের নাটরেরই এক ডাক্তার ঢাকা শহরে আছে। আলম ক্লিনিকের ডাক্তার। তার হাসপাতালে নিলে টাকা-পয়সা বেশি লাগবে না। জাফরের পরামর্শ মতো আলম ক্লিনিকে রহিমাকে নেওয়া হলেও টাকা দিয়ে ভর্তি না করানোতে রহিমাকে ফ্লোরে রাখে এবং তার কোন চিকিৎসা হয় না। শেষপর্যন্ত রহিমার মৃত্যু হয়। আজিমুদ্দিন মেয়ের মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মানতে পারে না তাই ডাক্তারের ওপর চড়াও হয় কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে বাবার ভালোবাসা থমকে যায়। পুলিশ এসে আজিমুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। গল্পে পাই:
‘দারোগা যেন স্পষ্ট দেখে, রহিমার মুখের ওপর থেকে সাদা কাপড় সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। দেখে দেখে তার চোখ বিস্ফারিত হতে থাকে। আর তখনই যেন রহিমা বলে ওঠে, স্যার গো আমার বাপের কী দোষ? শব্দ কটি দারোগা আকাশবাণীর মতো শোনে বটে, কিন্তু নিজের কানকেই তার বিশ্বাস হয় না। আবার চোখকেও সন্দেহ হয়। দীর্ঘ চাকরি জীবনে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনো তাকে হতে হয়নি। তার মুখে কথা ফোটে না, হা করে তাকিয়ে থাকে রহিমার দিকে। মাথার ভেতর ঘন ঘন বেজে চলে, ‘আমার বাপের কী দোষ?’ এই প্রশ্নের যন্ত্রণা তাকে অকস্মাৎ নিশ্চল পাথরের মূর্তিতে পরিণত করে দেয়। আর তখনই হাতের মুঠোয় ধরে রাখা আজিমুদ্দিনের হ্যান্ডকাপ শিথিল হতে থাকে। কী অমোঘ আকর্ষণে দারোগার যেন পা মেঝেতে গলে যাচ্ছে, সে আর সামনে এগোতে পারে না।’ (নবাবের একদিন, পৃ. ৭৮)
‘আজিমুদ্দিনের দোষ’ গল্পে লেখক সচেতনভাবে অনেকগুলো বিষয় তুলে ধরেছেন। প্রথমত, করোনাকালীন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরমতম দুর্দশা ও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক দৈন্য তথা ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে শহর থেকে গ্রামাভিমুখী বা গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী মানুষের চিত্র; তৃতীয়ত, স্কুল থেকে রহিমার ঝরে পড়া; চতুর্থত, স্বাস্থ্যখাতে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অমানবিকতা; পঞ্চমত, জাফরের লালসা। একটি গল্প জীবনের অনেকগুলো লেসন তৈরি করে দিয়েছে। আজিমুদ্দিন চিরকালই বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত। তাদের অধিকার নেই উচ্চবিত্তের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার। তারা লাথি দেবে সেটা হজম করবে এ শ্রেণী। এই তো পৃথিবীর চিরন্তন নিয়ম। তাই আজিমুদ্দিন মেয়ের মৃত্যুর প্রতিবাদ করাতে পুলিশ তাকেই শাস্তির আওতায় আনে! ‘জতুগৃহ’ গল্পে দেখতে পাই গৃহকর্মী সুমীর হত্যার পর তার পরিবার বিচার পায়নি, ‘একদা এক চন্দনগরে’ গল্পে মাখন লাল বিচার পায়নি। কালের হেরফের হলেও এই যেন চিরন্তন সত্য নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্মই হয়েছে উচ্চবিত্তের শোষণকে মেনে নেওয়ার জন্য। তারা আল্লাহ-ভগবান বা ঈশ্বরের কাছেও যেন অবাঞ্ছিত! মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি’ গল্পের উপেনের কথা! মাত্র বিঘে দুই জমি থাকলেও বাবু বলেন সে জমি তারই হস্তে যাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ‘এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়/ আছে যার ভূরি ভূরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত/কাঙালের ধন চুরি।’ শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই নন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সব শিল্পী-সাহিত্যিকদের লেখায় ফুটে উঠেছে অন্ত্যজশ্রেণির দুঃখ-কষ্টের নিদারুণ দৃশ্য! ভাগ্য তাদের সহায় হয় না।
এই গল্পে আরও দেখতে পাই, করোনাকালে স্কুল থেকে রহিমা ঝরে পড়ার দৃশ্য! কিশোরী রহিমা প্রাণ তো হারালোই কিন্তু পৃথিবীতে যতদিন ছিল ততদিনও তার যথোপযুক্ত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়নি। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান হাল এতই শোচনীয় যে, গরীবের সন্তানের জন্য শিক্ষার পাঠ ব্যয়বহুল! অন্যদিকে ডাক্তারী পেশা অনেকটা নিলামের পেশা। চিকিৎসক আর কসাইয়ের মধ্যে বর্তমানে পার্থক্য করা খুব কঠিন! ডাক্তার সেবা দিতে প্রস্তুত নয় বরং তিনি কসাইয়ের মতো মানুষের সঙ্গে ডিল করতে ব্যস্ত। লেখক মোহাম্মদ নূরুল হকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সমাজের এসব পচা-গলা দৃশ্য এড়িয়ে যেতে পারেনি! তাইতো লেখক সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এ সমাজ অবক্ষয়ের, ঠসে যাওয়া, ভঙুর এক সমাজ! মানুষ যতদিন মনের পশুত্বকে বলি দিতে না পারবে ততদিন বাঙালি পুড়বে অঙ্গার হয়ে!
‘জঙ্গল উপখ্যান’ গল্পটিতে মোহাম্মদ নূরুল হককে আরেকটু ভিন্নভাবে চেনা যায়। তিনি উপকথার আড়ালে গল্পটি রচনা করেছেন। আমরা জানি, উপকথা হলো সাহিত্যের এমন একটি ধরন, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণী, কিংবদন্তিতুল্য সৃষ্টি, উদ্ভিদ, জড়বস্তু বা প্রাকৃতিক উপাদানকে মনুষ্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যারা মনুষ্য ভাষায় কথা বলে এবং তাদের জবানিতে গদ্য বা পদ্য ছন্দে ছোট কাল্পনিক গল্প বিবৃত হয়। এই গল্পগুলোর পরিণতিতে একটি বিশেষ নৈতিক শিক্ষাও প্রদান করা হয়। মোহাম্মদ নূরুল হকের ‘জঙ্গল উপখ্যান’ গল্পটিতে এই ফর্মের পরিপূর্ণতা লক্ষ করা যায়। এই গল্পের চরিত্রগুলো সবই পশু। পশুরাজ সিংহ, শেয়াল, বানর, হাতি, ছাগল এই গল্পের চরিত্র। গল্পে দেখতে পাই, পশুরাজ সিংহের নির্দেশ বনের সব পশুই তৃণভোজী হবে। কিন্তু শেয়ালের ঘোর আপত্তি তা নিয়ে। সে ছাগলকে বিভিন্নভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে সব পশু তৃণভোজী হলে বরং ছাগলের মতো পশু যারা প্রকৃতই তৃণ ভক্ষণ করে তাদের খাবারে ঘাটতি পড়বে। বনদেবী তাদের লালন-পালন করলেও পশুরাজের কথা মানতেই হবে। তার ব্যতয় ঘটবে না। অন্যদিকে শেয়াল ধূর্ত। সে ছাগল, বানরকে বোঝাতে সক্ষম হয় এটা তাদের জন্য অন্যায়। এই অন্যায়কে রুখতে হলে বৃদ্ধ পশুরাজকে সরাতে হবে। কিন্তু কী করা যায় সেটাই ভাবতে থাকে সবাই। একপর্যায়ে শেয়াল বানরকে বলে পশুরাজের ঘরে আগুন লাগাতে। পশুরাজের ঘরের চতুর্দিকে আগুন দিয়ে বের হতেই ছাগল লক্ষ্য করে সিংহেট গগনবিদারী মরণ চিৎকার। গল্পে পাই:
‘শেয়াল ও ছাগল শেয়ালের গুহায় চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় প্রহর গোনে, কখন বনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে, আর সেই আগুনে সিংহ পুড়ে মরবে। ভাবতে ভাবতে ছাগলের চোখে হালকা ঘুম লেগে আসে। আর তখনই সিংহের গগনবিদারি মরণ চিৎকার ভেসে আসে। সেদিকে তাকাতেই ছাগল দেখে বনের যত দূর চোখ যায়, কেবল আগুনের লেলিহান শিখা। ভেতর দিয়ে সিংহ, বুনো মহিষ, হাতি, হরিণ, শেয়াল দৌড়ে পালাচ্ছে। হঠাৎ করেই ছাগলের সামনে লাফিয়ে পড়ে বানর। তার লেজে আগুন। ছাগল দেখলো, সেই আগুন বানরটির সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার ছাগল দৌড় দেবে। ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল। ছাগলের আর পা চলে না।’ (নবাবের একদিন, পৃ. ৮৫-৮৬)
এই গল্পের মাধ্যমে লেখক চতুর মানুষের ধূর্ততার চিত্র তুলে ধরেছেন। আমাদের সমাজে শেয়ালের মতো লোকের অভাব নেই। যারা নিজের ফায়দা লাভের জন্য অন্যকে বিপদে ফেলতে সবসময় পটু। ছাগল ও বানরকে বোকা বানিয়ে শেয়াল ফায়দা লুটতে চায়। ছাগল যে তৃণের জন্য সিংহকে হত্যার পরিকল্পনায় অংশ নিলো সেই ছাগলই কালের পরিক্রমায় শেয়ালের খাদ্যে পরিণত হবে। শেয়াল মাংস খাওয়ার লোভেই গোটা পশুরাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করে৷ শেয়ালের মতো ধূর্ত ব্যক্তিদের থেকে সবসময় দূরত্ব বজায় করা উচিত নতুবা জীবনে নেমে আসবে ছাগলের মতো শ্লথ গতি!
‘আসাদের শেষদিন’ গল্পে এক নিদারুণ সত্য লেখক এখানে উপস্থাপন করেছেন। চল্লিশ বছরের সংসার জীবনে আসাদ কখনোই সুখী দাম্পত্য জীবন পায়নি। তবু বউকে ডিভোর্স দেবে সেই শক্তি ও মনোবল আসাদের নেই। সমাজের ভয়ের চেয়ে সন্তানের মঙ্গল ও অমঙ্গলের হিসাব বেশি কষেছে আসাদ। তাই অভিভাবকদের মতামতেরও গুরুত্ব সে দেয়নি। বরং বলেছে আসাদ বা রুবিনা বিয়ে করে সংসার করতেই পারে নতুন করে কিন্তু তার সন্তানদের পরিচয় কী হবে! কোথায় যাবে তারা? এই কষ্ট থেকেই দিনের পর দিন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছে আসাদ। আজ সে মৃত্যু শয্যায় প্রাণত্যাগের জন্য প্রহর গুনছে কিন্তু আসাদ লক্ষ করে স্ত্রী রুবিনা ও ছেলে রফিকের নিদারুণ অবেহলা, নিপীড়ন। একমাত্র পুত্রবধূ সুমিই তাকে প্রাপ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। সেইসঙ্গে সেবাও। এই ‘আদিখ্যেতা’ পছন্দ করে না রুবিনা। সে চায় কবে মরবে আসাদ আর সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে। আসাদের জীবনের সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে লেখক এ সমাজের করুণ ও কদর্য এক সত্য উপস্থাপন করেছেন।
আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য নারী-পুরুষ রয়েছে, যারা সম্পর্কের সুতোয় বাঁধা থাকলেও তা লোক দেখানো। সমাজের চাপে বা কখনো সন্তানের মঙ্গলের জন্য দিনের পর দিন স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যে অভিনয় করেতে দুবার ভাবছে না! ব্যক্তির জীবন যখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে তখন তার মনের মৃত্যু ঘটে! আসাদ জানে তার স্ত্রীর সঙ্গে তারই খালাতো ভাই সবুজের সম্পর্ক। তার মরণব্যাধি রোগ হয়েছে। আজই আসাদ মরলে কালই তারা ঘর বাঁধবে। কবরের মাটি শুকাতেও দেরি করবে না। কোনোদিনই রুবিনার কাছ থেকে আসাদ সম্মানের ছিঁটেফোঁটাও পায়নি। মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়ে তার মনে হয়, যখন তার ছেলে সন্তান জন্ম নেয় তখন তার শ্বশুর-শাশুড়ির মতো তার বাবা-মাও দেখতে এসেছিল। সেই নিয়ে রুবিনা ও আসাদের মধ্যে একচোট ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তারপর লোকলজ্জার ভয়ে আসাদই মুখে কুলুপ এঁটেছিল! মরণযাত্রী আসাদকে দেখতে আসে সবুজ। রুবিনার সঙ্গে চোখে চোখে কথা লক্ষ করে আসাদ। ছেলে রফিক উকিলকে নিয়ে আসে। শেষসময়ে আসাদের সম্পত্তি লিখিয়ে নিতে চায়। কিন্তু উকিল মিজানের সঙ্গে আসাদের আগেই কথা হয়ো গিয়েছিল, সেভাবে সব কাগজপত্র সিগনেচার করে আসাদ। গল্পে লেখক আসাদের মৃত্যুর করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। কিন্তু আসাদের মৃতদেহ কোথাও নিয়ে যেতে দেয় না রুবিনা। সে আগে তার সম্পত্তির ভাগ বুঝে পেতে চায়। তখনই উকিল মিজান এক ক্লাইমেক্সের অবতারণা করে, যা গল্পটিকে এক ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। গল্পে পাই:
‘প্রথম দলিলের সারমর্ম এমন, আসাদ তার পুত্রবধূ সুমিকে নিজের কন্যার মতো দেখতো। সুমিও আসাদকে বাবার মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি-সেবা করতো। তাই আসাদ তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সুমিকে দান করে গেছে। এছাড়া আরও অসিয়ত করেছে, তার মৃত্যুর পর লাশ দাফন নিয়ে কেউ যেন টানাটানি না করে। তার লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে গবেষণাকাজে ব্যবহারের জন্য দান করে গেছে। সুতরাং তার সম্পত্তিবণ্টন ও লাশ দাফন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব স্বজনদের মধ্যে আর কারও ওপর বর্তাবে না। উকিল এই পর্যন্ত বলে দম নিলো।
প্রথম দলিলের সারমর্ম শুনে সুমি নতমুখে বসে আছে। রফিক চুপচাপ, তার ছল-ছল চোখ ঘরের ছাদের দিকে। রুবিনা কেউটে সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে, কী! এত্তবড় জালিয়াতি? আমি তার স্ত্রী। তার ছেলে আছে। আমাদের জন্য কিচ্ছু নাই। সব ওই সুমিকে দিয়ে গেলো? আমি মানি না এই দলিল। রুবিনার চিৎকার থামলে উকিল বলে, আপনারা মানা-না মানায় কিছু এসে-যায় না। আসাদ আপনাদের সামনেই দলিলে স্বাক্ষর করেছে। আসাদের সম্পত্তিতে আপনার আর হক নেই। ক্ষেপে ওঠে রুবিনা, নেই মানেও উকিল বলে, নেই মানে, দ্বিতীয় দলিলে আসাদ আপনাকে তালাক দিয়ে গেছে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার সাবেক স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পায় না। আপনি কেবল দেনমোহরের টাকা পাবেন। উকিলের কথা শেষ হলে হঠাৎ ফুটো বেলুনের চুপসে যায় রুবিনা। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। (নবাবের একদিন, পৃ. ৯৫)
গল্পের মধ্যে আসাদের জীবনের নির্মমতা প্রকাশিত হয়েছে। আসাদ বেঁচে থাকতে সুখী নাহলে মৃত্যুর পর তার থেকে কেউ যেন শেষ সুখটুকু ছিনিয়ে না নিতে পারে, সে ব্যবস্থা করেছে। পরিবারের প্রতি কতটা বিতৃষ্ণা থাকলে একজন মানুষ তার জীবনকে পুরোপুরি নিঃশেষ করে দেয়! আসাদ এক নিপীড়িত স্বামী। আমাদের সমাজে আসাদেরা আইনের কাছে অসহায়। স্ত্রীর ভরণপোষণ, দেনমোহর সবই পুরুষের ওপর বর্তায় কিন্তু পুরুষ নিপীড়নের শিকার হলে তার যথোপযুক্ত বিচার সে পায় না। আসাদ পারতো জীবদ্দশায় স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে। কিন্তু সে অন্য পথ বেছে নিয়েছে। এটা একান্তই আসাদের অপারগতা। যেই সন্তানের জন্য পুরো জীবনটাকে উৎসর্গ করেছে, সেই সন্তান বাবার প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যও পালন করেনি! এ থেকে বোঝা যায়, জীবন ব্যক্তির নিজের। সে কিভাবে তার জীবন পরিচালনা করবে, সেটা একমাত্র তার দায়। শেষ সময়ে এসে আফসোস করবে, না কি যেখানে দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যুর মতো অসহনীয় যন্ত্রণার উপস্থিতি, সেখান থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে!
ছোটগল্পের শাখায় মোহাম্মদ নূরুল হকের যাত্রা নবাগতই বলা যায়। তবু কী অসাধারণ গল্পের প্লট, বুননকৌশল, ভাষার নির্মাণ! সবমিলিয়ে গল্পকার এক অনবদ্যতায় নিয়ে গেছেন প্রতিটি গল্পকে। জীবনের মূল সুর গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষ সাহিত্য পড়ে আনন্দের জন্য। কিন্তু আনন্দের গভীরে লুকিয়ে থাকে শিক্ষা, অনুভূতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা। সাহিত্যের সঙ্গে মনকে যোগ করতে পারলে তবেই তা জীবনকে বদলাতে সাহায্য করে। আর এই গল্পগুলো জীবনকে ভাবাতে শেখায়। সমাজকে বুঝতে শেখায়। অবশেষে নিজেকে প্রশ্ন করতে শেখায়! এটাই লেখকের সার্থকতা।