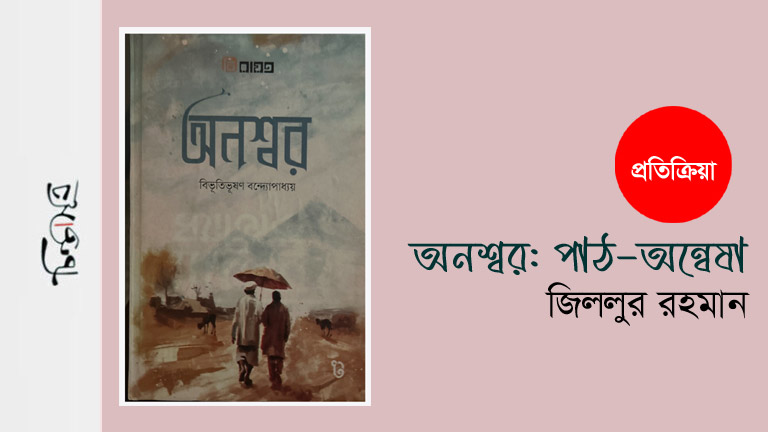গ্রাম বাংলার ইস্কুলের শিক্ষক রামলালের বয়স ষাট পেরিয়ে যাওয়ায় তার চাকরি চলে গেলে ইন্সপেক্টরের কাছে দরবার করতে যান। রামলালের চাকরি আর ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তার আইএ পাস না করা ছেলেকে ছোটদের শিক্ষকতার চাকরি দিতে আগ্রহী হন ইনস্পেক্টর । কিন্তু শ্যামলাল ভাবের জগতে বাস করে, একটা কবিহৃদয় রয়েছে তার। বাবা-মায়ের ধারণা, ছেলে অনেক বড় কিছু হবে। ইস্কুল-মাস্টারি করে রামলালের জীবন তো অর্থকষ্টে কোনো রকমে অতিক্রান্ত হলো, ছেলের জীবন এভাবে বরবাদ না করে বরং ভাগ্যের সন্ধানে তারা পিতাপুত্র চলে যায় অনেক দূরে ধুরুয়াডিহি।
এদিকে গ্রামে রেখে যায় বৃদ্ধা মা ও গরুবাছুরের সংসার। আরও একজন ছিল, ভূতি। গোপন প্রণয় দুজনের, বন্ধু রতন ছাড়া কেউ জানে না। ধুরুয়াডিহিতে দূর সম্পর্কের মামা চিকিৎসক শরৎকালীর সহৃদয় প্রশ্রয়ের কারণে ভাগ্যান্বেষণে তাদের এই যাত্রা। এত অনিশ্চয়তার মধ্যেও কবিমন জেগে ওঠে পাহাড় ও জঙ্গলের ভিন্নরকম সৌন্দর্যের অনাবিলতায়। শ্যামলালের সরল মন এবং সৎ প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হন কাঠ-ব্যবসায়ী রামজীবন। তিনি তাঁকে তাঁর নিজের ব্যবসার কাজে নিয়োগ দিতে আগ্রহী হন। সরল বাধ্য ছেলে পিতার অনুমতি নিয়ে জানাবেন বলে দ্রুত পিতা রামলালের কাছে যান।
ওদিকে শরৎকালী রামলালের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তারখানার বন্দোবস্ত করে বাজারের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ‘মঙ্গলী ভকৎ’-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, যাতে তাঁর পসার ভাল হয় সেদিকটা দেখেন। তবে এখানে পরিচয় দেবার সময় শরৎকালী রামলালকে তাঁর শালা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন, অথচ আদ্যোপান্ত গল্পটিতে রামলালের পরিচয় হলো শরৎকালীর ভগ্নিপতি। ব্যাপারটা কি ইচ্ছাকৃত না কি লেখকের ভুল তা বলা আজ অসম্ভব। যাই হোক, রামলাল বাড়ি ফিরলে শ্যামলাল তার বাবাকে ভাল বেতনে রামজীবন বাবুর অফিসে কাজ পাওয়া সম্পর্কে জানায় এবং পরদিনই যে যোগ দিতে হবে তাও বলে। এটাও সে জানায় যে বলে এসেছে তার বাবা মত দিলেই সে চাকরিতে যোগ দেবে।
বিভূতিভূষণের অসামান্য এই লেখাটি, যার নাম অনশ্বর, এখানেই শেষ করেছিলেন। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় পিতা যে সন্তানকে কবি হিসেবে মহৎ কর্মে লিপ্ত দেখতে চান, তিনি কি তাকে এরকম ব্যবসায় তদারকির বৈষয়িক কাজে নিয়োজিত হতে মত দেবেন কিনা? নাকি দেবেন? তারপর কি ভূতির সাথে শ্যামলালের সংসার হবে? এসব প্রশ্নের উদ্রেক এই লেখাটিকে একটা ছোটগল্পের ধারণার দিকে ঠেলে দেয়। না দিলেও ছয়টি পরিচ্ছেদের মধ্যে লেখাটি আমাদের চিন্তার জায়গা করে দেয় । কিন্তু আমরা দেখছি, পরবর্তীতে বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে গজেন্দ্র কুমার মিত্র সপ্তম পরিচ্ছেদের সংযোজন করেন মাত্র ৭টি বাক্য যোগ করে। এখানে তিনি ভূতির কথা এবং শ্যামলালের মা ও গ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এর আরও পরে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টম থেকে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে গল্পটির সাড়ে সমাপ্তি ঘটান। এতে শেষ পর্যন্ত শ্যামলাল অপুত্রক রামজীবনের ব্যবসার অংশীদার হন, সামান্য যে কাব্যচর্চা করতে পেরেছেন তাতে সুনেত্রা নামের আধুনিকা নারীর প্রেমে পড়ে এবং বিয়ে করে। ওদিকে ভূতির বিয়ে হয়ে যায় বয়স্ক দোজবর সম্পন্ন পাত্রের সঙ্গে। বাবাকে পাঠিয়ে গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন মাকে।
প্রশ্নটা হলো, বিভূতিভূষণও কি তাই করতেন? আর এই ১১টি পরিচ্ছেদ এত অল্প বাক্যে সমাপ্ত করার দৃষ্টান্তে মনে হলো যেন একটা জবরদস্তি করে তাকে ফুরিয়ে দেওয়া হলো । বিভূতিভূষণের লেখায় শুরুতে যে দেশভাগের পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গে দলে দলে আসার কারণে থাকার জায়গা তো আছে কর্মসংস্থানেও প্রবল ঘাটতি দেখা দিয়েছিল, যার ফলে বাঙালিরা কাজের সন্ধানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাজের সন্ধানে চলে যেতে হচ্ছিল এই পরিপ্রেক্ষিত যেন গজেন্দ্র কুমার মিত্র বা তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি।
এক বসায় এক নিঃশ্বাসে একটা বই অনেকদিন পরে পড়ে শেষ করলাম এবং একই বসায় পাঠ-প্রতিক্রিয়াও লিখে রাখলাম। এটাই বিভূতিভূষণের ভাষার শক্তি ।