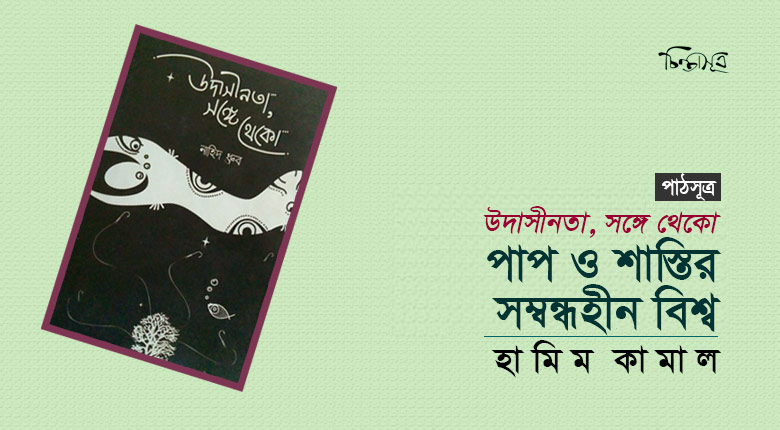 যখন ৬৩ পাতায়
যখন ৬৩ পাতায়
বিষণ্ন হয়ে পড়ছি। মনে হয় আজ নাহিদ ধ্রুবর লেখাটাই বাহিরে বৃষ্টি নামালো। ‘উদাসীনতা, সঙ্গে থেকো’ যেদিন পড়তে শুরু করছিলাম ঢাকায় সেদিন দশ ডিগ্রির কাছাকাছি শীত ছিল। অথচ যখন পাতার পর পাতা ওল্টাচ্ছি, মনে হচ্ছিল আমার চারপাশে বুঝি বর্ষা নেমেছে। আমি পড়া থামিয়ে একবার কান পেতে এমনকি বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেলাম। এর একদিন পর সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামল। ঝিরিঝিরি। আর তার দুদিন পর আজ বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে।
অনুভব করছি, উপন্যাসটা এটুকু পড়ার পর আমার নিজের উপন্যাসও হয়তো আর আগের মতো থাকবে না। কারণ আমি ভীষণ রকম আহিত হয়েছি। নাহিদের এ লেখা চুম্বক আর আমি চৌম্বক। ওর চুম্বক একেবারে আকরিক। সেখানে একটু আধটু করে খনির অনেক ধাতুর মিশেল থাকায় একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছে।
চুম্বক এখানে তার শক্তিবলয়ের উপস্থিতি রেখেছে কিন্তু বিশুদ্ধতা নিয়ে দাপট দেখাচ্ছে না। ফলে ফুলের মতো যে বলরেখাগুলো তৈরি হয়েছে দেখতে সেসব খানিক শিথিল আর ওই শিথিলতায় একটা ঘরোয়া আপন ভাব এনে দিয়েছে, উপভোগ করছি। যেমন থেকে থেকে উপন্যাসের বক্তা পাঠকের সঙ্গে কথা বলছে। ইন্টারেস্টিং।
তবে কথাগুলো ডিসাইফার করে বিশেষ কিছু পেলাম কি? একটা কথা অবশ্য ও লিখেছে যেটা যথেষ্ট ব্যঞ্জনাপূর্ণ এবং ধারার বীজ সেখানে আছে। পাঠককে বলেছে, গল্পের বক্তার নামে নিজের নাম বসিয়ে নিন।
আমাদের পুরাণে বিশ্বকর্মা জগৎ নির্মাণ করেন। আমার মনে হয়েছে এই একটা কথা উপন্যাসটার জগত নির্মাণের বিশ্বকর্মাস্বরূপ। কেননা নাম লোককে ডেকে আনে। লোক তো জগৎ। তবে এখানে একটা দুর্বলতা আছে বোধয়। একটু এগোতেই বুঝি বক্তাটি পুরুষ।
তাপসী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হলো বলেই বক্তাকে পুরুষ ভাবছি না। ভাবছি সম্ভবত বক্তার স্মৃতি ও ক্ষত ব্যাখ্যার ধরন দেখে। বিশেষ ধরনটি সঙ্গী করে বক্তা পুরুষ চরিত্রের যন্ত্রণার গভীরে যতখানি চেনা জগতের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ঢুকেছেন, নারী চরিত্রের ট্রমাগুলো ততটাই যেন শুধু উপরিতল স্পর্শ করেছে।
যেহেতু বক্তা নিজেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রমাণ করেছেন উপন্যাস জুড়ে, যা বলছি তা ওই সংবেদনশীলতার কাছে দাবি মাত্র। তারপরও বক্তার জগৎ পুরুষের জগৎ হলে বক্তাকে ছাড় দিতে পারি, কিন্তু লেখককে? নিজ নাম বসিয়ে নেওয়ার আহ্বানটা হয়ত নারী-পাঠকের কাছ থেকে অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। কারণ ওই। নাম লোক ডেকে আনে। আর লোক তো জগৎ।
যে বাক্যে উপন্যাসের জগৎ নির্মাণের এতো গুরুভার চাপানো, সেই বাক্যটি যেন আরেকটু ব্যালেন্সের যতন দাবি করছে।
এ উপন্যাসে স্থান-কাল আর সম্ভব-অসম্ভবের মাঝে কোনো দেয়াল নেই বলেই মনে হচ্ছে। ‘এই লেখাটা আমি লিখছি বা লিখছি না’, ‘এই লেখাটা আমি লিখছি এবং লিখছি না’-এমন কোয়ান্টাম অক্ষীয় খেলা অম্লান বদনে লিখে ফেলাই যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা দুষ্কর।
আমাদের সাহিত্যে এ নতুন নয়। আমরা শহীদুল জহিরকে দেখেছি, কী অমিত শক্তির সঙ্গে একে ডিল করেছেন। নাহিদ কেমন করে ডিল করেছেন, আমি দেখতে চাই। মনে হয়েছে লেখক আসলে একটা এক পাতার বিশ্ব গড়েছেন। মাত্র একটি পাতাতেই তার গড়া বিশ্বের সমস্ত বর্ণনা এঁটে যায়। উপন্যাসে একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি আছে কিন্তু যতবার পুনরায় আবৃত্তি করছি নতুন সুর বাজছে। একই কথার ভেতর দিয়ে মুক্ত হচ্ছে আলাদা আলাদা জগৎ। অথবা একই জগতের আলাদা সময়।
আমার হায়াও মিয়াজাকির হওল’স মুভিং ক্যাসেলের সেই দরজার কথা মনে পড়ছে। কবাটের পাশে বিশেষ চাবিতে মোচড় দিলে খুললেই বাইরে একেকবার একেক ভুবন হাজির, একেক কাল উপস্থিত! তবে এমন জাদুবিস্তারী প্লটে নাহিদ এরই মাঝে যা করেছেন তাকে আরো সংহত ও মনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব যদি সচেতনভাবে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গ্রহণের আরো অবকাশ পাঠকের জন্যে রাখেন।
আমার বিচারে শব্দ আর রস নাহিদের পক্ষপাত পেয়েছে। স্পর্শ, রূপ, গন্ধ একটু মনোযোগ কাড়তে চেয়ে জানালার বাইরে থেকেই কেঁদে গেছে। মাঝে মাঝে দরজা খুলে লেখক তাদের ঢুকতে দিয়েছেন। একদম বাহিরে রেখেছেন তা সত্য নয়। একটা কথা শুরুতেই বলেছিলাম, নাহিদের এ লেখা পড়ার পর আমার নিজের উপন্যাসও হয়ত আগের মতো থাকবে না। এই সূত্রেই বলি, পার্লকে বলছিলাম, বইটা পড়তে পড়তে বোধ হচ্ছে, আমি বুঝি আমার লেখককে পেয়ে গেছি।
কোনো কোনো ঐশ্বরিক শুভেচ্ছানন্দিত মুহূর্ত আছে যখন পাঠক আবিষ্কার করেন তিনি তার লেখকটিকে পেয়ে গেছেন। ‘উদাসীনতা’ আমাকে সেই বোধ এনে দিয়েছে। এই বোধ বজায় থাকুক হে মহাকাল!
যখন ১০৬ পাতায়
যে রূপ রস স্পর্শ গন্ধ শব্দ আরো বেশি করে চেয়েছিলাম নাহিদ আমাকে এবার দু’হাত ভরে তা দিলেন। আমি যে অলক্ষ্যে উপন্যাসের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছি তা অনুভব করলাম। রূপক ও হেঁয়ালি থাকলেও ঘটনা ও পরিণতি এখানে আরও পরিষ্কার, দৃশ্য আরও জীবন্ত। আর চরিত্রগুলোর সঙ্গেও আরো সখ্য হওয়ায় আমি তাদের কেয়ার করতে শুরু করেছি।
কেবল একটা গ্রাম আছে—বন্ধ্যাগ্রাম—সে চিঠি লিখল গ্রামের কুয়াকে। কুয়াটা যদিও গাঁয়ের ভেতরই, তবু সে গ্রামকে শূন্য করে দিয়েছিল। সেখানে আত্মহত্যা মহামারী হয়ে এসেছিল।
বিব্রত হয়েছি, নাহিদ একে একে তার সমস্ত বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন। আমিও বাদ পড়িনি। প্রত্যেকের মৃত্যুকাণ্ড বর্ণনা করেছে। সময়ের আগে ও পরে ভিন্ন বা অভিন্ন যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে প্রত্যেকের যাপন সমান। কোনো এক আলোহীন সরকার প্রত্যেকের সাধারণ প্রতিপক্ষ।
ক্ষমাপ্রার্থী, উপন্যাসে বর্ণিত নামগুলো আমাদের হলেও ওরা ঠিক আমরা নই। নামগুলো অবশ্যই সবার প্রতিনিধিত্ব করে। তবে আমি যদি ব্যক্তি ঔপন্যাসিকের দিকে তাকাই, তাহলে আরেক মাধুরী ধরা পড়ছে। তা উপন্যাসের বক্তাটাকে নয়, বরং লেখক ব্যক্তিটিকে উন্মোচিত করছে।
কাছের মানুষদের নাম নিয়ে আমরা সাধারণত কোনো ভাগ্যহীন রক্তাক্ত পট আঁকতে দ্বিধা করি। আমাদের দেওয়া সাজানো হতভাগ্যতার উদাহরণে কখনো আপন কারো নাম আনতে চাই না। এই ট্যাবু এজন্যে যে, পৃথিবী মত্যুসংকুল আর মায়াগর্বী আমরা আমাদের আপনজনদের নিয়ে ভীষণ তটস্থ। কোথাও কোনো কল্পিত সংকটও যেন নেইমসেইকে সত্যি না হয়ে যায়।
সেই দ্বিধা কি নাহিদের ছিল না? বাজি ধরে বলতে পারি ছিল। কিন্তু তার তোয়াক্কা না করে একেকটা বিবমিষাময় জীবনের যাপনযাত্রী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের নাম হুবহু এনে তিনি যা করেছেন তা হলো, নিজের ধমনীতে ছুরি চালিয়েছেন। আপন করা নামগুলো যেন কোনো শ্রান্তি-মৃত্যু-পরাজয়হীন সমাজে বাস করছে, এমন অভিনয় নাহিদ করেনি। লেখা তার লেখকের রক্তপাত। যতখানি সততা এ লেখায় নাহিদ অর্জন করতে চেয়েছেন, হৃদয়ের অপরিমেয় রক্তপাতে তার মূল্য পরিশোধ করলেন।
আরেকটা সত্য প্রকাশিত। তা হলো, উপন্যাসে বর্ণিত অপমৃত্যু আর আত্মহননের মহামারীময় ওই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধটা নাহিদের কতখানি কাছ থেকে দেখা। কিছু সত্য আছে বাঁকা। বাঁকা বলে, কখনো মিথ্যার মতো তাদের মান কম দিতে ইচ্ছে হয়। কখনো আবার চোখের সামনে ঘটতে থাকলেও মন তাদের সত্য বলে মানতে চায় না। সম্ভবত এমনই এক সত্য-বিপ্লব তার বিপ্লবীদের হত্যা করে। নাহিদের ‘উদাসীনতা সঙ্গে থেকো’ যার ডেমনস্ট্রেশন।
যে শাসন ব্যবস্থার নির্যাতনের রোলারে ও যে শাসকবর্গের যুদ্ধরথের তলে বক্তার মেটরা প্রত্যেকে পিষ্ট তাদের সিংহভাগ ওই ব্যাবস্থাটির শাসকদলীয় সাবেক বিপ্লবী। একটা দারুণ ছায়াসত্য নিয়ে নাহিদ এখানে ডিল করেছেন। এবং এটা গোটা উপন্যাসকে শাড়ির মতো জড়িয়ে রেখেছে। তাহলো:
পাপের সাথে শাস্তির তেমন সম্পর্ক নেই। শাস্তির সাথে শুধুমাত্র জড়িত থাকে ভাগ্য ও ক্ষমতা। এই উদ্ভাবন আমাকে ঝাঁকুনি দিয়েছে। সত্যের শরীরের ওপর যখন মহানিয়মের আলো পড়ে, তখন তার যে ছায়া পড়ে তা হয়তো সত্যের কায়া না, কিন্তু তা অসত্য না। আমার ছায়া আমি না, কিন্তু সে সত্য। উপন্যাসটার এমন দার্শনিক অ্যাডভেঞ্চার আমাকে গর্বিত করেছে। থেকে থেকে আমার কাহলিল জিবরানের কথা মনে পড়েছে। এ উপন্যাস যদি জিবরান পড়তেন, খুশি হতেন।
মনে হলো আনন্দিত হতেন হুমায়ূন আজাদও। আজাদের কথা এজন্যে বলছি, উপন্যাসে হেঁয়ালির কুয়াশায় হাত ধরে হাঁটিয়ে নেওয়ার কাজটি হুমায়ূন আজাদও নিজের মতো করে করেছেন। তবে তিনি কখনো সখনো হ্যাঁচটা টেনেছেন হাত, আমার তাই মনে হয়। নাহিদ হাতটা ধরেছে কোমলভাবে, বেশিটা জিবরানের মতোন।
হাত কোমল করে ধরলে কী হবে, পায়ের নিচে মটমট করে যা ভাঙছে তা সব বিগতপথিকদের হিউমেরাস ফিমার হাড়, বুকের পর্শুকা আর কোটরময় মাথার খুলি। এ এমন এক পথহাঁটা, হাড়ের মটমট শুনেই পাঠককে শেষাবধি পেরিয়ে যেতে হবে। পেরিয়ে যেতেই যেতেই একটা কথা মনে এলো।
মৃত্যুমুখীনতা বজায় রেখেই চরিত্রগুলোর সংগ্রামে কি আরো পার্থক্য গড়া যেত না? বোধয় শোচনীয়তার বিচিত্রতাও আরো বাড়ানো যেতে পারত। তাতে সংগ্রাম আর তার পরিণিতির ব্যাপ্তি আরো সুচারু ও বৈশ্বিক হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল। আর পলায়নপর অভিযাত্রীদল একটা স্মৃতির জাদুঘর খুঁজছে তো; স্মৃতির জাদুঘরের সূত্রে মনে পড়ল আমার মাহবুব ময়ূখ রিশাদের লেখা একটা গল্পের কথা, ‘ঝড়ের জাদুঘর’; সেখানেও জাদুঘরে থরে থরে স্মৃতিরা জমা ছিল। আমি দেখতে চাই নাহিদের জাদুঘরটা কতটা আলাদা।
শেষ করার পর
স্পর্শিয়া কিছু চিঠি পড়লাম। ভিজে ওঠার উপক্রম হয়েছিল চোখ। মানুষ লিখেছে গাছকে। আসলে গাছের চেয়ে বড় চিঠিবন্ধু আর কে আছে। এমনকি গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরলেও একটা চমৎকার চিঠি বিনিময় হয়ে যায়। চিঠির সঙ্গে গাছের অনেক মিল আছে। যেমন চিঠির শব্দ বাক্যও গাছের মতো স্থবির কিন্তু সচল। প্রাণকে কেবল ধারণই করে না, বহনও করে। এবং একেকটা গাছ বোধয় অবিকল একেকটা চিঠি। ওকে চিঠি করে প্রকৃতি সমগ্র প্রাণের কাছে পাঠিয়েছে।
যদি নাহিদ ধ্রুবও একমত হয় আমার সঙ্গে, ওর সঙ্গে ধানমণ্ডি লেকের ধারে ভীষণ আপন কোনো আড্ডা হবে। আর সেখানে শিগগির কোনো অরণ্যযাপনের পরিকল্পনা করব আমরা।
মৃত্যু আর অপমৃত্যুর ভেতর দিয়ে প্রকৃতির উৎসে ফিরে যাওয়া প্রতিটা চরিত্র গাছকে চিঠি লিখে চক্র পূর্ণ করল। কেবল একটা গ্রাম আছে- বন্ধ্যাগ্রাম- সে চিঠি লিখল গ্রামের কুয়াকে। কুয়াটা যদিও গাঁয়ের ভেতরই, তবু সে গ্রামকে শূন্য করে দিয়েছিল। সেখানে আত্মহত্যা মহামারী হয়ে এসেছিল।
উপন্যাসজুড়ে মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যুকল্প নানান রূপ ধরে আসতে দেখলাম। এবং একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে আত্মহনন। আত্মহনন সর্বব্যাপী। এই হননে নিজেকে সঁপেছে প্রত্যেকটা চরিত্র- এমনটাই মনে হলো। কেউ সত্যিই আত্মহত্যা করেছিল আর কেউ এমন পথে মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল যেন ওটা আত্মহত্যাই ছিল। তোমাকে জলে ডুবিয়ে মারব, নাকি মাঝসাগরে নামিয়ে দেবো। সাঁতরে যদি তীরে পৌঁছাতে পারো, বাঁচলে।
সেই আক্ষেপ স্মরণ করে এমন লেখার এই নাম দেওয়া। টনটনে কবিত্বজ্ঞানের কারণে নাহিদের এ লেখায় উপমার কোনো ফাঁক প্রায় চোখেই পড়েনি।
একটা জাদুঘরের সন্ধানে বক্তার সঙ্গে ছুটছিলাম। আর দেখতে অপেক্ষমান ছিলাম নাহিদের এ জাদুঘর রিশাদের জাদুঘর থেকে কতটা আলাদা। উত্তরটা পেয়েছি। স্মৃতির জাদুঘর দুটো আলাদা যদিও স্মৃতি তৈরির প্রক্রিয়ায় তারা অনেকটা এক। প্রক্রিয়াটা ট্রমা।
মানুষের স্মৃতি আটকে রাখার বড় দুটি কিলক দুই বিপরীতধর্মী তুরীয় অবস্থা। র্যা পচার আর ট্রমা। তীব্র আনন্দ, তীব্র ব্যথা। ট্রমা প্রাধান্য পেয়েছে এ উপন্যাসে।
আরেকটা পার্থক্য, বিস্তৃতির বিচারে ‘উদাসীনতা, সঙ্গে থেকো’র জাদুঘরটা ‘ঝড়ের জাদুঘর’-এর চেয়ে বড়। ব্যাপারটা ঘটেছে উপন্যাসের আঙ্গিকগত ব্যাপ্তির কারণে ঘটেনি। ঘটেছে কারণ ঝড়ের জাদুঘরে যা ব্যক্তিগত ট্রমা, উদাসীনতায় তা সামষ্টিক।
সারাপথ যে জাদুঘরের কাছে পৌঁছাব বলে দৌড়েছি, উপন্যাসে শেষে মনে হলো পুরোটা সময় আমি জাদুঘরটারই এঘর-ওঘর করেছি। যাকে খুঁজব বলে যাত্রা করেছি, পথ কেটে চলছিলাম তারই ভেতর দিয়ে। অবশ্য জায়গাটা এমনভাবে বোনা যে কারো মনে হতে পারে জাদুঘর মরিচিকার মতো কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে।
পাঠককে সাক্ষী করে কথা বলার জায়গাগুলো শেষ পর্যন্ত বাহুল্যই মনে হলো। পরের সংস্করণে এ জায়গাটা নিয়ে কাজ করার অবকাশ আছে বলেই মনে হয়।
আর ওই অভিন্ন মুহূর্তে ‘ঘটেছে/ঘটেনি’র কোয়ান্টাম অক্ষীয় খেলাটা নিয়ে বলবো, শহীদুল জহিরের উত্তরাধিকারী নাহিদ। খেলাটা এলেও তার বিশেষ ভূমিকা আমি পাইনি। কারণ আমার মনে হয়েছে দিনের শেষে উপন্যাসের গল্পটা একাধিক বিকল্প পথে পরিণতি পায়নি। এমন পরিণতি পেয়েছে যেন গল্পটা একটা ধ্রুব পথ ধরেই এগিয়েছিল।
সেক্ষেত্রে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার খেলাগুলো যদি বাক্য থেকে অপসারণও করা হয়, আমার মনে হয়, উপন্যাসটা যেমন করে শেষ হয়েছে তেমন পথেই শেষ হবে।
তবে, আমি অন্য একদিকে বিশেষ মোহিত হয়েছি। নাহিদের লেখায় বরাবর একটা আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবাদ দেখেছি। আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবাদ আদি প্যাগান বিশ্বাসগুলোকে যেন খানিক ঠাঁই দেয়। আমি নিজেও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবাদী মানুষ। তো, এর ভেতর থেকে নাহিদের ঝোঁক খানিক মৃত্যুমুখী। ওই মৃত্যুমুখী আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবাদকেই নাহিদ নিজস্ব ভাষার তুলি আর শৈলীর রং দিয়ে এ উপন্যাসে এঁকেছেন, এবারও, আমি যতটা বুঝেছি।
যেকোনো স্থায়িত্বের অনেকগুলো মূলনীতি বিপরীতে ঐক্য। এই বিপরীতে ঐক্যের সূত্র ধরেও প্রকৃতিবাদের আলাপ ভাবনার সমস্ত বিলাপে ঢুকে পড়তে পারে। আর তাই আমার মনে হয়, আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবাদের মতো মস্ত উঠান আর কোনো কিছুর নয়। নাহিদ সেই উঠানে হেঁটে হেঁটে আজ মৃত্যু লিখছে। লিখছে, ‘মৃত্যুর চেয়ে বানোয়াট আর কী হতে পারে’। সামনে হয়ত জীবন লিখবে এবং জীবন মৃত্যুর মাঝখানে যত জল আর পাথর আছে, যত শ্বাস আর আশ আছে, বাদ না যাক কিছুই। ওর এ লেখা আমাকে একটা পথরেখা দেখাল, তা আমােকে আনন্দিত করেছে। যতটা আনন্দ বুদ্ধকে নন্দিত হতে দেখলে আমার হয়।
ওর পথরেখা দেখে এমন আনন্দের গূঢ় কারণটা বলছি। ‘উদাসীনতা, সঙ্গে থেকো,’ নাহিদের প্রথম উপন্যাস। আমি তার আরও উপন্যাসের পথ চেয়ে থাকব। নাহিদের ‘উদাসীনতা, সঙ্গে থেকো’ আর রিশাদের ‘আরিমাতানোর’ এই দুই উপন্যাসে মৃত মানুষ নিজেকে ব্যক্ত করতে জীবিতের ভাষার আশ্রয় নিয়েছে। ভাষা স্মৃতির সংকেত। মৃতকে যখন স্মৃতির দ্বারস্থ হতে হয় তখন পদার্থবিজ্ঞান ‘অধি’র স্তরে প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের মানবমস্তিষ্ক সেই চাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। কী কষ্ট, কী অপমান!
আমি বিশ্বাস করি, মানুষ যতদূর কল্পনা করতে পারে, বাস্তবতার সীমাও ঠিক ততদূর। এই বাস্তব হৃদয়মস্তিষ্ক দিয়ে মানুষ অবাস্তব কিছু কল্পনা করে এ আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে যা দাঁড়ায় তা আমার আণবিক শক্তিবলয়ে আলোড়ন তোলে। আমি এই দুই উপন্যাসের ন্যারেটরদের নিয়ে আলাদা করে হয়ত কখনো কিছু লিখব।
লেখাটা সার্বিকভাবে এর প্রসঙ্গগত ও দার্শনিক গভীরতায় আমাকে শেষতক আকৃষ্ট এবং গর্বিত করে রেখেছে। আমি সচরাচর এমন লেখাই পড়তে চাই। প্রথাগত গল্প যেমন আমার খুবই ভালো লাগে, প্রথাবিরোধী এমন ঘোরাল গল্পও তেমনই আমি খুব ভালোবাসি।
এমন গল্পের অনেকটা কীর্তিকাণ্ড পাঠকের নিজস্ব ভুবনে তৈরি হয় বলে গল্পের বোঝাপড়াটা, বয়স আর পরিবেশের সমানুপাতে বাড়তে অথবা ব্যস্তানুপাতে কমতে পারে। বারংবার পাঠে এ জাতীয় লেখার অর্থ বদলে যায়। এমন লেখার আমি নাম দিয়েছি ‘বাল্মিকীয়’। পাখির ডাকের কত অর্থ হতে পারে, আর বাল্মিকীর নিজের বলা শব্দের পায়ে কিনা অর্থের সীমার শেকল পরানো- এই যে আক্ষেপ বাল্মিকী প্রকাশ করেছিলেন নারদের কাছে। সেই আক্ষেপ স্মরণ করে এমন লেখার এই নাম দেওয়া। টনটনে কবিত্বজ্ঞানের কারণে নাহিদের এ লেখায় উপমার কোনো ফাঁক প্রায় চোখেই পড়েনি।
এই বইয়ে কোনো এডাল্ট কন্টেন্ট বলতে যা বোঝায় তা নেই, তবে নিখাদ নিরপেক্ষ সব স্মৃতিকটু ট্রমা বা ছায়াট্রমা আছে যার চলৎছবি পাঠ করতে গেলে পাঠক হিসেবে অ্যাডাল্ট হতেই হবে।
উপন্যাসে ছবি
বইটির অঙ্গসজ্জায় স্থান পাওয়া নাহিদ ধ্রুবর আঁকা ছবিগুলো আমি মন দিয়ে দেখেছি। প্রথমত বেশিরভাগ ছবিতাদের পটসজ্জা বা কম্পোজিশনে চমৎকার। কিছু কিছু ছবি ভাবগভীর বলে আমার মনে হয়েছে। ছবিতে বিচিত্র সব চরিত্র এসেছেন এবং নিছক চরিত্রের ছবি হয়ে তারা বসে নেই। উদ্দেশ্য গন্তব্য পাওয়া যায় ওদের। প্রাণপ্রকৃতিও আঁচ করা যায়।
স্বপ্নভাঙা ঝড়ের দাপুটে আপটা সরাসরি প্রাণের ওপর দিয়ে গেছে। মৃত্যুদণ্ডের মতন। এবং এই দণ্ড পাপের বিপরীতে আসেনি। নিয়তির যেটুকু মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে না, দণ্ড ওই অংশে এক নিষ্ঠুর উদাসীনতার সঙ্গে নির্ধারিত হয়।
বস্তু বা প্রাণির দেহগুলোকে আকার দিয়েছে স্বপ্ন-স্বপ্ন ছোট ছোট রেখা। রেখাগুলোয় একটা শিথিল আনাড়ীপনা আছে, অনেকটা শিশুর আঁকার মতো। এটা ইচ্ছেকৃত হতে পারে। ছবিগুলোয় একটা নাহিদীয় ছাপ দাঁড়িয়ে গেছে এতে করে। বেশিরভাগ ছবিতেই নান্দনিকতা তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি বলেই মনে হয়েছে আমার। তবে কিছু কিছু ছবিতে অতিশিথিল ভাব আমি নিতে পারিনি। অন্ধকারে ভাসমান কিছু মুখের ছবির অপূর্ব একটা কম্পোজিশন আছে, দর্শনিক ভাবগভীর। কিন্তু ওই শিথিল আঁকজোখের কারণে আমার মনে হয়েছে নষ্ট হয়েছে।
আমার বিশ্বাস নাহিদ নিষ্কম্প রেখায়ও দুয়েকটা ছবি এঁকে দেখতে পারেন। তাতে ওর ক্ষমতার আরেকিটা দিক হয়ত উন্মোচিত হতে পারে আমার বিশ্বাস।
ছবিগুলো বিমূর্ত হওয়ায় লেখার শরীরের সঙ্গে না হলেও আত্মার সঙ্গে মিল কল্পনা করে নেওয়া যায়। এই সুবিধাটা পাঠক যখন নিয়েছেন, তখন হয়ত টের পেয়েছেন, লেখার ঘোরকে কেমন প্রভাবিত করতে চাইছে ছবিগুলো! ছবিগুলোও এভাবে উপন্যাসের শরীরের অংশ হয়ে উঠেছে।
আমার চোখে বিশেষ ছবিগুলো প্রথম সংস্করণের ১৮, ৫৭, ৬৬, ৭৪-৭৫, ৯৬, ১০২, ১১৩-১১৪ পাতায় রয়েছে। অবশিষ্ট ছবিগুলোর নান্দনিকতায় বেশ, কিন্তু বিমূর্ততার বিচারে ঠিক উপন্যাসের জোর বাড়ায়নি বলেই মনে হয়েছে আমার।
নাহিদের বইয়ে ওর ছবি আর লেখার এই যুগলবন্দী চালু থাকলে খুশি হবো। বড়দের বইয়ে ছবি না থাকার চল থাকলেও আমি তা মানার পক্ষে নই। উপরন্তু ছবি বিমূর্ত আর নান্দনিকতার শর্তপূরণকারী হলে তো কথাই নেই।
সার্বিক উপস্থাপন
রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন গিন্নিপনা, সেই গিন্নিপনা নাহিদের ভেতর দেখতে পেলাম পূর্ণরূপে আছে। এতো যত্নের উপস্থাপন। সিংহভাগ ছবির নান্দনিক উপস্থাপন আছে তো বটেই সঙ্গে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে মনীষীদের অপূর্ব সব উচ্চারণ। হোমার থেকে শেক্সপিয়র, গিন্সবার্গ কি এপোলোনিয়ার। হাফিজ, এমিলি, কিটস- আরো কত জনার লিখিত বাক্য। যেমন পথ দেখিয়েছে, তেমন পাঠের মন তৈরি করেছে।
আর প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদে কালোর পটে সাদায় এক অপূর্ব মানুষমূর্তি জলের নিচে জল হয়ে ভেসে যাচ্ছে। তার শরীরের এখানে ওখানে বিস্মিত চোখ। কবিতার মতো প্রচ্ছদেও সিপাহী রেজা প্রতিনিয়ত নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।
পরিশিষ্ট
চরিত্রগুলো বেঁচে থাকাকালীন ছিল নিজ নিজ প্রকৃতিমুখী। মৃত্যু তাদের প্রত্যেককে নতুন মাত্রার প্রকৃতিমুখীনতা দিয়েছে। সেখানে সবার রূপান্তরকামিতা সফল হয়েছে কিনা জানি না, তবে ওদের পরজন্ম বা পুনর্জন্ম যদি আমার সামনে মুক্ত করা হয়, বোধয় সবকজনারই বৃক্ষজন্ম দেখতে পাব।
প্রত্যেক চরিত্র কিছু স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের স্বপ্ন ভাঙা পড়েছে। স্বপ্নভাঙা ঝড়ের দাপুটে আপটা সরাসরি প্রাণের ওপর দিয়ে গেছে। মৃত্যুদণ্ডের মতন। এবং এই দণ্ড পাপের বিপরীতে আসেনি। নিয়তির যেটুকু মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে না, দণ্ড ওই অংশে এক নিষ্ঠুর উদাসীনতার সঙ্গে নির্ধারিত হয়। কেবল নাহিদীয় বিশ্বেই নয়। বোধয় নৈর্ব্যক্তিক পৃথিবীতেও এ-ই হয়।
আরও পড়ুন: অগ্নিকা আঁধার: সফল আন্দোলনের চিত্র ॥ সেলিনা হোসেন

