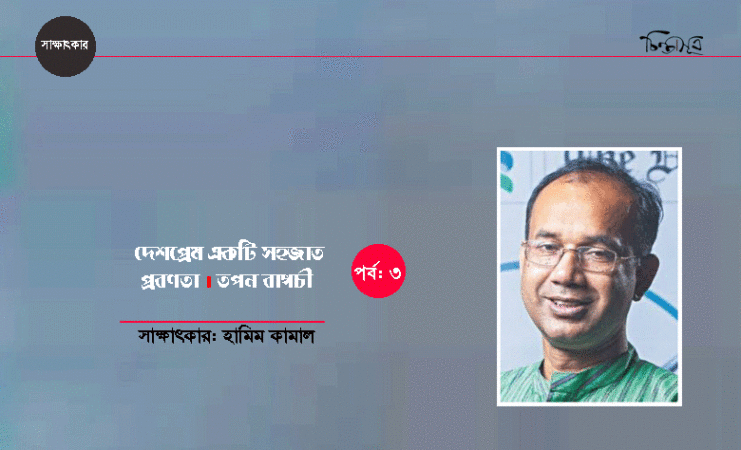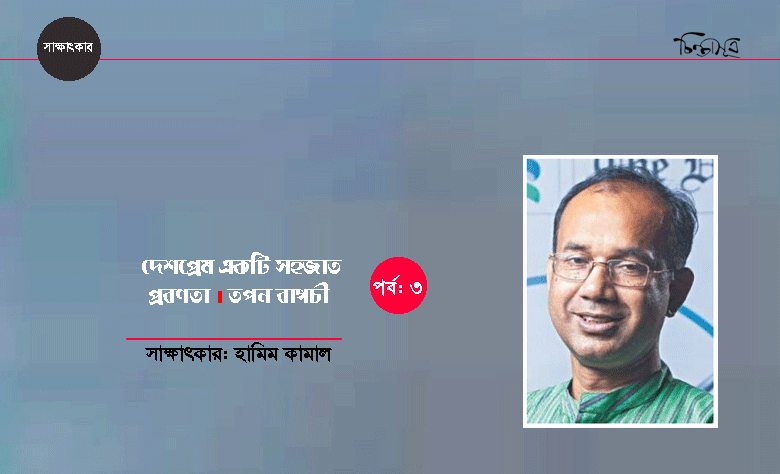[তপন বাগচী—একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তিনি ১৯৬৮ সালের জন্ম ২৩ অক্টোবর মাদারীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা তুষ্টচরণ বাগচী; মা জ্যোতির্ময়ী বাগচী। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এমএ ও পিএইচডি করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ: শ্মশানেই শুনি শঙ্খধ্বনি, কেতকীর প্রতি পক্ষপাত, অন্তহীন ক্ষতের গভীরে, সকল নদীর নাম গঙ্গা ছিল। প্রবন্ধগ্রন্থ: সাহিত্যের এদিক-সেদিক, সাহিত্যের কাছে-দূরে, চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, লোকসংস্কৃতির কতিপয় পাঠ, বাংলাদেশের যাত্রাগান : জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : চন্দ্রাহত অভিমান, নির্বাচন সাংবাদিকতা, নজরুলের কবিতায় শব্দালঙ্কার, তৃণমূল সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশ। পুরস্কার ও স্বীকৃতি: সাংস্কৃতিক খবর পদক (কলকাতা, ২০১৩), মাইকেল মধুসূদন পদক (২০১২), লিটল ম্যাগাজিন মঞ্চ সংবর্ধনা (নদীয়া ২০১০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য পুরস্কার (২০০৯), কবি বাবু ফরিদী সাহিত্য পুরস্কার (২০০৯), মাদারীপুর সুহৃদ পর্ষদ সম্মাননা (২০০৯), ফরিদপুর সাহিত্য পরিষদ সম্মাননা (২০০৯), মহাদিগন্ত সাহিত্য পুরস্কার (কলকাতা ২০০৮), এম নূরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরস্কার (২০০৮), জেমকন সাহিত্য পুরস্কার (২০০৮), অমলেন্দু বিশ্বাস স্মৃতি পদক (২০০৮), জসীমউদ্দীন গবেষণা পুরস্কার (১৯৯৬), মুনীর চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১)।
দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করার পর বর্তমানে বাংলা একাডেমির গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের উপপরিচালক। সম্প্রতি সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন তরুণ কথাসাহিত্যিক হামিম কামাল, আজ প্রকাশিত হলো তৃতীয় পর্ব]
হামিম কামাল: আসলে কি, ভাইয়ের যে উদাহরণটা আপনি দিলেন, সেখান থেকে মনে হলো, ভাই আলাদা হয়ে আলাদা ঘর করলেও, সংসার করলেও কিন্তু ফের দেখা হচ্ছে। কখনো পুনরায় এক হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ যেন তখনো থেকে যাচ্ছে, ওই সুযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না।
তপন বাগচী: এখন গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে যাওয়ায় তো দেখা হচ্ছে।
হামিম কামাল: আচ্ছা, এ ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে গ্লোবাল ভিলেজ ইমেজ।
তপন বাগচী: হ্যাঁ। এখন একইসঙ্গে অন্যান্য দেশে যারা বাঙালি আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। এই যে বলছিলাম, ঢাকায় থাকার একটা প্রবণতা আমার মধ্যে ছিল, এখন আমি অনেককে দেখেছি, চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, বলছে, আরে ইন্টারনেট ইমেইলে তো যোগাযোগ থাকবেই। আমার অনুজপ্রতীম প্রশান্ত মৃধা, খুব ভালো লেখে। তো আমি বললাম, প্রশান্ত, ঢাকায় আয়, বলে না দাদা, আমার তো সমস্যা হচ্ছে না। আমি তো লেখা যে চায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দিতে পারছি। এই গ্লোবাল ভিলেজ হয়ে পড়ার যে সুবিধাটা, এটি আর কোনও সমস্যা রাখেনি। আজকে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আমাদের এখানে আদানপ্রদান হচ্ছে। এখানকার লেখা পশ্চিমবঙ্গের প্রচুর কাগজে ইন্টারনেটের কারণে ছাপা হচ্ছে, ওখানের লেখা এখানে ছাপা হচ্ছে। আগের মতোই। এই প্রযুক্তির কারণে আবার একটা নৈকট্য তৈরি হয়ে গেছে। গ্লোবাল ভিলেজের এই ফিলসফিকাল কনসেপ্ট আমাদের আবার এক করে দিয়েছে। তো, ভৌগলিক মানচিত্রে যে কাঁটাতার এটা কোনও সমস্যা নয়।
আরেকটা বিষয় বলি, সেটি হলো, বড় সংঘাতও তো থাকে। আজকে পাকিস্তানের কথা যদি বলি, ওখানে অন্তর্ঘাত চলছে না? নেপালের মতো জায়গা, একেবারে ছোট শান্তিপ্রিয় দেশ, সেখানেও কি অন্তর্ঘাত চলছে না? আমাদের বাংলাদেশেও যে কখনো বিভাগওয়ারি কোনও ভাগ হওয়ার আন্দোলন হবে না, বিষয়টা তো এমন নয়। একসময় আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে তো বিচ্ছিন্নতাবাদি আন্দোলন ছিল। এখন বাংলাদেশে যেসব প্রশাসনিক এলাকা আছে, তারাও যদি আলাদা আলাদা রাজ্য দাবি করে, লোকসংখ্যা যখন আরও বেড়ে যাবে, তখন এরকম হতেই পারে। প্রয়োজন আর সময়ের দাবি এমন বিষয়, যখন এক হাঁড়িতে ভাত হয় না, তখন দুই হাঁড়িতে চড়াতে হয়।
হামিম কামাল: বেশ। আপনার লেখার বিষয়বস্তু কোথা থেকে পুষ্টি নিয়েছে এটা জানতে চাই। আর জানতে চাই সৃষ্টির কোন অনুষঙ্গ, কোন শাখা আপনাকে খুব কাঁপায়, ভাবায়। ওই অনুষঙ্গে আপনার নিজের কাজের কেমন পরিকল্পনা আছে।
তপন বাগচী: প্রথম যদি বলি, তো কবিতার কথা বলতে হয়। সবসময় মনে করে এসেছি, আমাদের কবিতার পূর্বসুরী যারা. সেই চর্যাপদ থেকে যদি শুরু করি, আমাদের যে হাজার বছরের পরিক্রমা— জীবনানন্দ লিখেছেন, হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি, এই হাজার বছর তো আমার সাহিত্যের ইতিহাসের হাজার বছর। এক হাজার বছর আগে চর্যাপদ লিখিত হয়েছিল। আমি সেখান থেকে যদি আমার কবিতা অভিযাত্রাপথ চিন্তা করি, দেখতে পাব আমাদের কবিতার একটা বড় স্থান জুড়ে আছে দেশপ্রেম, প্রকৃতি। এক অর্থে দেশ আর প্রকৃতি একই। আমি চেষ্টা করেছি, আমার কবিতায় আমাদের দেশের কথা, প্রকৃতির কথা, মানুষের কথা আমি বলতে পারি। কিন্তু সেই কথাটা যদি সরাসরি বলি… কবিতা সবসময় একটা অবগুণ্ঠনের মধ্যে চলছে। একটু অলঙ্কারের মধ্যে চলছে। সরাসরি কথা বলাটা কবিতায় মানায়নি কখনো। যে কারণে এখনও লালনের লেখার রহস্য আমরা ভেদ করে চলেছি, কিংবা চর্যাপদের রহস্য আমরা ভেদ করে চলেছি। এর আকর্ষণ কিন্তু ওই সবটুকু না বলা।
কবিতার ক্ষেত্রে আমি একটা সূত্র মানি। সুজন বড়–য়ার কাছ থেকে পাওয়া এ লাইন। ‘কিছুটা বলা, কিছু না বলা, না বলাটাই শিল্পকলা’। সবটুকু যদি আমি বলেই দিই কবিতায়, কিংবা সাহিত্যের মাধ্যমে তাহলে আর ওই আনন্দটুকু থাকে না। আলাপের জন্যে, তর্কের জন্যে, বুঝে নেওয়ার জন্যে বা বর্জন করার জন্যে কিছু স্পেস রাখতে হয়। এই স্পেস রাখার বিষয়টা সুচারুভাবে যে করতে পারে, তার লেখা, ওই লেখাগুলোই কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়। ওগুলোই সফল হয়। চর্যাপদে, এরপর লালন, রবীন্দ্রনাথ এঁদের রেখে যাওয়া থেকে বুঝতে পারি। একটা কথা, ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’। এরচেয়ে সহজ সরল বাক্য কিন্তু হয় না। একটি শব্দও নেই যে অভিধান খুলে দেখতে হবে। তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির একটা শিশুও এই বাক্য বুঝতে পারবে। এরপরও কেন এটা হাজার বছর ধরে টিকে আছে? কারণ এটা একটা ব্যঞ্জনাময় বাক্য। এখানে সন্তান বলতে কেবল আমার ঔরসজাত পুত্র কিংবা কন্যা নয়। এখানে সন্তান বলতে আমার প্রজন্ম। এখানে দুধেভাতে বলতে দুধ আর ভাত মেশানো খাবারের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সম্পন্ন সুষম খাবারের কথা। বলা হয়েছে মিনিমাম চাহিদা পূরণ করে এমন খাবারের কথা। স্বাস্থ্যকর খাবার। ‘যেন’ বলে একটা প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রত্যাশা শুধু আজকের কথা না। আরও হাজার বছরের প্রত্যাশা এটা।
একটা চিরন্তনতা তৈরি হয়েছে সাধারণ একটা লাইনে। আমি এরকম চিন্তা করি যে, সহজ ভাষায়, অযথা জটিলতা তৈরি না করে এরকম চিরন্তন বাক্যের দিকে সাধনা করে যাব। যেন এরকম একটা লাইন লিখতে পারি। এরচেয়ে সহজ এরচেয়ে সরল বাক্য যেমন বিরল বাংলা কবিতায়, এরকম উৎকৃষ্ট বাক্যও খুব কম আছে। আমি এরকমভাবে লিখতে চাই। তার জন্য এদের কাছ থেকেই আমি দীক্ষা নিতে চাই। কবিতা যখন একটা আধুনিক ফর্মে আসলো, রবীন্দ্রনাথ থেকে যে এ আধুনিকতা, ত্রিশের আধুনিকতা, প্রত্যেক কবি আমার অনুসরণযোগ্য এবং আমার এখানে শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ—কবিতায় যারা দেশের কথা, মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন, করেছেন বটে, কিন্তু সরাসরি নয়, ওই রূপক, ওই অলঙ্কার, ওই উপমা-উৎপ্রেক্ষা, ওসবের মধ্য দিয়ে। কবিতার অনেক টেকনিক সময়ে বদলেছে। একসময় ছিল একেবারে এক দাড়ি দুই দাড়ি দিয়ে লেখা পয়ার ছন্দ, আজ সেটি নানা রকম ছন্দে রূপ নিয়েছে। একটা সময়ে ছন্দের বাহ্যিক যে ঝঙ্কার, সেটিকে অন্তর্লীন করে ঢুকিয়ে দেয়ার যে চেষ্টা, সে চেষ্টা হয়েছে, বুদ্ধদেব বসুরা যেটা করেছেন। এখন না জেনে শুনে ছন্দছুট বাক্য লিখে অনেককে বাহবা নেওয়ার চেষ্টা করতে দেখি। আমি সেই দলে নেই।
আমি মনে করি, এখনও হাজার বছরের ঐতিহ্যের মধ্যেই আমার বাংলা কবিতার মুক্তি। এবং সেই পথে কবিতা নিয়ে হাঁটতে চাই। ছড়ার ক্ষেত্রে যদি বলি- ছড়া আমরা মনে করি বুঝি সরাসরি কথা বলে। আসলে তা নয়। সুকুমার রায়ের ‘বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে’ এটাকে অনেকে ননসেন্স রাইম বলে। ‘সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আনত/ তেড়ে মেরে ডাণ্ডা করে দিই ঠাণ্ডা’। ছোটবেলায় পড়েছি, মজা পেয়েছি, দোলা পেয়েছি। বড় হয়ে দেখি, এতো ব্রিটিশ শাসনামলের বাঙালি বাবু, যারা দালালি করতে তাদের কাছে গেছে, তারা যেমন নখদাঁতহীন নির্বীর্য মানুষ ছিল, দেশদ্রোহী ছিল, বিদেশি প্রভুদের জন্যে দেশের বিপক্ষে কাজ করেছে তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে লেখা।এবং ওই বাবুরা কিন্তু এখনও আছে। বাবুটা প্রতীকী ব্যাপার। এভাবে প্রতিটি ননসেন্স রাইম আমি যাচাই করে দেখেছি, ওগুলোর রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক মূল্য রয়েছে। ‘ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে/ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে’। পাড়া জুড়ানোর কথা বলা হলো। বর্গীর কথা বলা হলো, বহিঃশত্রুর কথা। খাজনার দেওয়ার কথা, শোষণের কথা বলা আছে। তাহলে এটা কি শুধু ননসেন্স রাইম? ছড়াও কিন্তু দীর্ঘ রাজনৈতিক মন্তব্য বহন করছে। অন্নদা শঙ্করের সাধারণ ক’টা লাইন, যতোকাল রবে… বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা, সাধারণ কথায় অসাধারণ কিছু। তবে ছড়ায় যা হয়, ছন্দ-অন্ত্যমিলকে রক্ষার ব্যাপারে একেবারেই আন্তরিক, একেবারেই শুদ্ধাচারী হতে হয়। তা অনেকেই রক্ষা করতে পারে না বলে ছড়ায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না।
আর কবিতায় এ কড়াকড়িটা নাই বলে কবিতার মতো কিছু চরণ লিখে কবিযশপ্রার্থিতার হিড়িক লেগেছে। আর এদের কারণেই কবিদের সম্পর্কে, কবিতার সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের অনেক খারাপ ধারণা আছে। কিন্তু ছড়া পড়ে আনন্দ পায়নি এমন কেউ নেই। কারণ না বুঝলেও ওই রিদমটা তাকে আনন্দ দিচ্ছে। যদি প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে নাও পারি, অন্তত ওই রিদম, দোলা, রেজোনেন্স, কম্পন যেটা তৈরি হয়, সেটা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে। ওই আনন্দটা দিতে চাই বলে কিছু ছড়াও আমি লিখেছি। ওসব রাজপথে, শহিদমিনারে, আন্দোলনে, জনসভায় পড়ার জন্য ওসব রচিত হলেও একটা সময়ে এসে আমি প্রকৃতি নিয়ে, শিশুদের ভেতর দেশপ্রেম জাগানোর জন্য লিখেছি। একটা ছড়ার বই পুরস্কৃত হয়েছিল ২০০৮ সালে, ‘মঙ্গা আসে ঘরের পাশে’ নামে। আমাদের দেশে মঙ্গার তখন প্রকোপ। ২০০৭-০৮ সালের দিকে। আমার এর আগে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকরি করার সুবাদে মঙ্গা তাড়ানোর কৌশল আমি শিখেছিলাম ওই সময়ের পরিচালকের কাছ থেকে, ড. ফরহাদ জামিল, তিনি মারা গেছেন। তার তত্ত্বটাই শেষ পর্যন্ত মঙ্গা কমালো।
তিনি ধানের একটা ভ্যারাইটির কথা বলছিলেন। যে পনের বিশদিন উত্তরবঙ্গের মানুষের হাতে কাজ থাকে না, গরুর খাবার থাকে না, মানুষের খাবার থাকে না, এমন এক ধান যদি উদ্ভাবন করা যায় যা ওই পনেরদিন আগে পাকে তাহলে মঙ্গা থাকবে না। কিন্তু তার কথা মানা হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওই তত্ত্বতেই মঙ্গা দূর হয়। ফখরুদ্দিনের আমল ওটা। মঙ্গা নিয়ে যে সমস্ত নিউজ হতো পত্রিকায়, সেগুলোকে আমি ছড়ায় রূপ দিয়েছিলাম, সেটা ‘এম নূরুল কাদির শিশুসাহিত্য পুরস্কার’ও পেয়েছিল। তাই আমি এররকম রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে, সামাজিক ইস্যু নিয়েও যেমন ছড়া লিখেছি, আবার একেবারে ছেলে ভোলানো, শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্যও লিখেছি। আমার তিন বছরের শিশু আধো আধো কথা বলে, তার কথাগুলো তার সামনে বসে ছড়ায় রূপ দিয়েছি। এভাবে ছড়া আমি নিয়েছি একেবারেই আশপাশের বিষয়গুলো থেকে।
হামিম কামাল: বেশ। শিল্পের কি আর এমন কোনও শাখা আছে যেটার প্রকাশক্ষমতাকে ঈর্ষা করেন?
তপন বাগচী: শিল্পের অনেক শাখা রয়েছে ঈর্ষা করি। আমি তো সাহিত্যের বাইরে খুব একটা কাজ করিনি। গান যেটা করি, সেটাও আমার অংশটুকু সাহিত্যেরই অংশ। যখন দেখি কেউ নাচছে, ছোটবেলার পদবলী কীর্তনের কথা মনে আসতো। নামাবলী গায়ে দিয়ে যখন নাচতে নাচতে বাঁশি বাজাতে গাইছে, কৃষ্ণকীর্তন করছে, তখন আমারও নাচতে ইচ্ছে করেছে। কোনওদিন সুযোগ হয়নি। কিন্তু নাচের শিল্পী দেখলে আমার ঈর্ষা হয়। আমি আমার গ্রামে যাত্রায় অভিনয় করেছি, কিন্তু এখনও মনে হয়, আমি যদি অমলেন্দু বিশ্বাসের মতো অভিনয় করতে পারতাম! এরকম একটা আবেগ কাজ করে। এই ঈর্ষা আসলে পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধা।
আর একা তো সব মাধ্যমে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই আমি অভিনয়ের অনেক সুযোগ থাকলেও ওই মাধ্যমে আর যাইনি, এটা কঠোরভাবে মেনেছি।
ছবি আঁকতে আমার ইচ্ছে হতো, মনে হতো একটা মানুষ দেখে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকৃতি আমি এঁকে ফেলব, কিন্তু কোনওদিন কলম ধরে চেষ্টাও করিনি। যে কোনও চিত্রশিল্পী দেখলেই আমার মনে হয়, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকে, এরা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। একটা মানুষের ছবি দেখলে আমি তাকে জীবন্ত দেখতে পাই। দেখি কাইয়ুম চৌধুরী মাত্র কয়েকটা আঁচড় কেটে একটা অবয়ব এঁকেছেন, আমি ওই আঁচড়ের মধ্যে লোকটাকে দেখতে পাই। আমি চিত্রশিল্পীদের ঈর্ষা করি। যোগ্যতার অভাবেই হোক আর যেভাবেই হোক আমি ওদিকে যেতে পারিনি। সীমাবদ্ধ জীবন, সব মাধ্যমে কাজ করাও সম্ভব নয়। সাহিত্যের মধ্যেই আমি আমাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি।
হামিম কামাল: আপনি উত্তর প্রজন্মের জন্য একটা পুষ্টি নেওয়ার ক্ষেত্র আপনার প্রতিভা, আপনার ঝোঁকের জায়গা থেকে সৃষ্টি করেছেন। উত্তরপ্রজন্মের সদস্যরা এখান থেকে নেবে, ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা করবে, এবং যে জ্ঞানটা নিলো তা তাদের পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দেবে। এটা একটা প্রক্রিয়া। আমি যেটা প্রশ্ন করতে চাইছি, একটা অভিযোগের ব্যাপারে। এখন যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের একটা অভিযোগ, আমাদের নিয়ে অনেক অবক্ষয়ের অভিযোগ আসে, দেখা যাচ্ছে যাদের ওপর তারা আঙুলটা তুলছেন তারা তাদের জীবনের শুরুতেই এমন পারিবারিক জীবন, এমন শিক্ষা জীবন পেয়েছে যা তাদের আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগেছে। আপনি লেখক হিসেবে তাদের বড় হওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে কী ভাবেন। বা ওদের বড় হওয়াটা কিভাবে বদলে দিতে চান, বা কেমন হওয়া উচিত বলে করেন।
তপন বাগচী: আমি এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ মানতে চাই। যে, সে খেলতে খেলতে, গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে, অর্থাৎ আনন্দের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষা গ্রহণ করুক। তার ওপর যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন বড় একটি বাধা তৈরি হয়। মানসিক বাধা তৈরি হয়। এটা আমাদের সময়ে যে ছিল না তা নয়, এখন তো প্রায় ৫০ বছরের কাছাকাছি আমাদের জীবন, প্রায় শেষার্ধেই চলে এসেছি, আমাদের সময়েও এই চাপ ছিল। কিন্তু এতোটা কড়াকড়ি ছিল না। আমাদের নিয়মিত বার্ষিক সংস্কৃতি, সংগীত চর্চা ছিল, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল, প্রত্যেকটি স্কুলে বার্ষিক নাট্য প্রতিযোগিতা ছিল। এর মানে আমরা পড়ালেখার ফাঁকেও শরীর ও মানস গঠনের উপকরণগুলো পেয়েছি। তো যে উপকরণগুলো ছিল, দেখতে পাই ওসব আস্তে আস্তে আমাদের সমাজ থেকে চলে গেছে।এটা একটা সংকট। এসব ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। এসব ফিরে এলে আরও দুই প্রজন্ম পর যারা আসবে, তারা অন্তত ঠিকভাবে এগোতে পারবে মনে করি।
আর অবক্ষয়ের যদি বলি, শিল্প সংস্কৃতিতে অবক্ষয়ের কথা কিন্তু শুরু থেকেই আমরা বলে আসছি। মাইকেলের সময়ের কথা যদি বলি, তিনি নাটকে, কবিতায় লিখেছিলেন— ‘অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়বঙ্গে নিরক্ষীয়া প্রাণ নাহি যায়’। অর্থাৎ সেখানেও কুনাট্য ছিল। অলীক কুনাট্য, অর্থাৎ সেখানেও নাটকের নামে ভাঁড়ামি ছিল। সেইসময়ও ছিল। আমরা যে বলব, আগেই ভালো ছিল, তা কিন্তু নয়। তবে ওই সময়ের যেগুলোকে কুনাট্য বলা হচ্ছে, সেগুলোও এখনকার অনেক নাটকের চেয়ে ভালো, এটাও সত্য। কিন্তু ব্যাপারটা প্রত্যেক সময়ে আসলে আপেক্ষিক। হতে পারে এখন আমরা যা করছি, বিশ বছর পর সেটিকেও কেউ কেউ বলবে— ভালো ছিল। আপেক্ষিক বিষয় তো, এটার কোনও স্থায়ী পরিসীমা টানা যাবে না।
হামিম কামাল: চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে যদি আসি, এখন দেখা যাচ্ছে আরেকটি বিষয়। আপনার কাজ করার বিষয় হচ্ছে ভাষা। এখন শিশুদের ওপর পরদেশি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি বিশেষ করে ইংরেজির কথা বলব। যেটা তার স্বগত ভাষা ছিল সেটাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এ বিষয়টিকে আপনি কেমন চোখে দেখেন এবং এটার পরিণতি কোন দিকে এগোচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?
তপন বাগচী: আমি মনে করি, এসমস্ত বিষয়ে অভিমত দেওয়ার মতো পর্যায়ে আমি নেই। তবে এটা যে কারণে হচ্ছে বলে আমি মনে করি, এর পেছনে রয়েছে অনিশ্চয়তাবোধ। ভাবা হচ্ছে, বাংলা ভাষা শিখে আমার সন্তান কি এ জায়গায় লড়াই করে টিকতে পারবে? ইংরেজি শিখলে সে হয়ত বাইরে যেতে পারবে। এটা অভিজাত শ্রেণির চিন্তা। অভিজাত বলতে সেই অর্থে অভিজাত না, মানে অর্থনৈতিক অভিজাত শ্রেণি। এদের হয়ত এমন একটা চিন্তা থাকে।
আর বিদেশি ভাষা যে শিখব না তা তো নয়। কিন্তু এর সময় আছে। আমাদের পাশের দেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় ভাষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে প্রথম শ্রেণি থেকেই দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি মনে করি, শুরুতেই মাতৃভাষাটা যার আয়ত্তে এলো না, তার ওপর দ্বিতীয় ভাষা যখন চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন কোনোটাই সুষ্ঠুভাবে কাজ করে না। মাতৃভাষার প্রেম জাগার আগেই অন্য কোনও ভাষার প্রেমে বাধ্য হতে হয়, কোনও প্রেমই দাঁড়াতে পারে না। সে কারণে মাতৃভাষাটা পোক্ত হওয়ার পরই সে যদি আর কোনও ভাষা শেখে, তখন বিজ্ঞানসম্মত হবে তা। আরেকটি বিষয়। যদি একটি ভাষা সে ভালো করে জানে, তাহলে অন্য ভাষা শেখাটাও সহজ হবে। বাংলাটাই যারা ভালো করে জানে না, তারা যদি ইংরেজিটা শিখতে যায়, তো সেটা একেবারেই উপরিতলের শেখা হবে। দুটি ভাষাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
হামিম কামাল: গানের প্রতি এই যে সম্মুখবর্তী ঝোঁক, এটা ধাপে ধাপে কী করে এলো?
তপন বাগচী: গান শুনে শুনে তো ভেতরে এক ধরনের সুর কাজ করত, খেলা কাজ করত। আমি আমার বোনের কথা বলব, যার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা যেমন আছে, একইসঙ্গে অনুযোগও আছে। আমার মামাতো বোন শিপ্রা বর, সে আমাকে গান শেখাতে চাইত। এটা যখন ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ি তখনকার কথা। সে গান শিখতো, আমাকে শেখাতেও চাইত। কিন্তু কোনও মতেই আমার কণ্ঠ হারমোনিয়ামের সুরের সঙ্গে মিশত না। তাই লজ্জায় আমি আর যেতাম না। এখন মনে হয়, তখন যদি ও আরেকটু জোর করত?
ও আমার ভেতর সুর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আরও একটু জোর করলে হয়ত আমি গানের দিকে যেতে পারতাম। এখন পেছনে তাকিয়ে আমার ভেতর গানের বীজ সন্ধান করলে ওই ঘটনাটিকে পাই। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে, মিছিল মিটিং শেষে যাদের সঙ্গে বসতাম, যে রুমগুলোয় আড্ডা দিতাম, সে রুমগুলো ছিল কয়েকজন শিল্পীর, যেমন সঞ্জীব চৌধুরী, পরে ‘দলছুট’ করে বিখ্যাত হন, ঢাকা কলেজের সন্তোষ ঢালী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রণজিৎ কুমার ম-ল, আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু সঞ্জয় রায়- সে গান গাইতো ভালো, সংস্কৃতে পড়ত। রাত আটটা ন’টার পরের সময়টা আমার এদের সঙ্গে কাটতো। শুধু গান শুনে যেতাম, না গাইতাম, না বাজাতাম। অনুপ ভট্টাচার্যের ষাটত জন্মদিন উপলক্ষেএকটা লেখা দিতে বললেন একদিন কবি আবিদ আনোয়ার। তখন ওনার সংগীত-সুরকার জীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে হলো তিনি তো গানের মানুষ, তাকে নিয়ে একটা গানই লিখে ফেলি। আমি তখন তাকে নিয়ে গানের মতো একটা কিছু লিখি, এটা ভালো গান হয়নি, গানের মতো করে, ব্যকরণ মেনে একটা কিছু লেখার চেষ্টা করি। আবিদ আনোয়ার এবং অনুপ ভট্টচার্য দু’জনই এর উচ্চ প্রশংসা করলেন। কিন্তু ওখানেই এটি মিলিয়ে যায়। আমার তখন একটা বিষয় মনে হতো, গীতিকাররা বুঝি কবিদের চেয়ে একটু ঊন। কম, একটু ছোট। গীতিকারদের একটু ব্যঙ্গ করা হয়, কবিদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমন ধারণা আমার ভেতর বদ্ধমূল ছিল।
একটা পর্যায়ে এসে আমি দেখলাম যে, কবিরা যেমন এরকম আত্মাভিমানে, অহংকারে গান লেখা কমিয়ে দিলো, তখন থেকে আমাদের গানের বাণীর মান কমতে শুরু করল। পঞ্চকবিরা গান লিখেছেন, সবাই বড় কবি। রজনীকান্ত, ডিএল রায়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ- সবাই কিন্তু বড় কবিও ছিলেন। এমনকি আমাদের দেশেও যদি চলে আসি, ৪৭ এর পরের কথা যদি বলি, এখানে বড় মাপের গীতিকার কারা ? কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুর রাহমানও গান লিখেছেন। এঁরা কিন্তু সবাই কবি। ষাটের দশকে এসে দেখলাম যে মাত্র দু’তিন গান লিখছেন। কারা? শামসুল ইসলাম, জাহিদুল হক এঁরা। সত্তর দশকে এসে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আবিদ আনোয়ার, নাসির আহমেদ, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল— এরকম হাতেগোনা নাম। স্বাধীনতার পর দেখা গেল যে, কবিরা আর গান লিখছেন না। অর্থাৎ গীতিকার প্রজন্মটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এটা আমার পর্যবেক্ষণ।
শামসুর রাহমান অনেকবার বলেছেন, গানে যদি কবিত্ব না থাকে, যতো ভালো সুরই দেওয়া হোক, সেটি আর টেকে না। এই যে কবিত্বটা সরে গেছে, মানে কবিরা গান লেখা থেকে সরে এসেছেন, এটা আমাকে পোড়াতো। এরপরও আমি গান লেখার সাহস করিনি। মুসা ইব্রাহীম যখন এভারেস্ট জয় করে ফেরেন, তখন আমি ‘প্রথম আলো’তে চাকরি করি। প্রথম আলো তাকে নিয়ে ছুটির দিনে ক্রোড়পত্রের একটা সংখ্যা করবে পরিকল্পনা করে। তখন আমাকে বলা হয় একটা কিছু লিখতে, আমি একটা ছড়া লিখি তাকে নিয়ে। ‘বাংলাদেশের সোনার ছেলে করল পাহাড় জয়’- এরকম। পরদিন আমাকে ফকির আলমগীর ফোন করে বললেন, ‘তপন বাগচী, আমি এটি সুর দিয়ে গাইতে চাই, আপনার কোনও আপত্তি আছে?’ আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এটি তো গান লিখিনি! এটা যে ছড়া। গান লিখলে তো আমার ব্রিজলাইন লাগবে, আমার তো অন্তরা ভাগ করা লাগবে, সঞ্চারি লাগবে। তিনি বললেন, লাগবে না। কাল মুসা আসছে, এটা সব চ্যানেলে লাইভ যাবে। তো, গানটা খুব বেশি ভালো হয়েছে বলতে পারব না, ছড়ার ওপর সুর দেওয়া হয়েছে। তবু ওটা গান পরিচয়েই প্রচারিত হয়েছে।
এরপর, পাকিস্তানের মালালা যখন আহত হয়ে হাসপাতালে, ঘটনাটা সারা পৃথিবীকে নাড়া দিল। শিক্ষার অধিকারের পক্ষে কথা বলার জন্য মালালাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, ভাগ্যক্রমে মেয়েটি বেঁচে যায়। ফকির আলমগীর বললেন, ‘মালালা নিয়ে একটা গান যদি লিখতে ভালো হতো।’ আমি তখন মালালাকে নিয়ে গান লিখি, শিক্ষার মেয়ে, শান্তির মেয়ে তোমার তুলনা নাই/ সোয়াতের মেয়ে ভগিনী আমার মালালা ইউসুফজাই। ফকির আলমগীর অনেক টিভি চ্যানেলেই গানটি গাইলেন। এবং গাওয়ার আগে আমাকে নিয়ে ছোট্ট ভূমিকা টানলেন, ‘আমার এক ছোট ভাই, তাকে বিকেলের দিকে বললাম একটা গান লিখে দিতে, সে রাতেই লিখে দিলো।’
এ কথাগুলো আমাকে খুব উদ্দীপ্ত করেছে। তখন মনে হলো যে আমি তো পারি। তিনি বললেন, ‘দেখো তুমি রুদ্রের জীবনী লিখেছ, রুদ্র কিন্তু বললেই গান লিখে দিতো আমাকে। তো তুমি গান লেখো না কেন?’ এরপর আরও বেশ কিছু গান আমি তার অনুরোধে লিখেছি। সেটি কেমন? যেমন ভুপেন হাজারিকা মারা গেলেন, তার ওপর একটা গান লিখে দিতে হলো। সুচিত্রা সেন মারা গেলেন তার ওপর লিখতে হলো। হুমায়ুন আহমেদ মারা গেলেন তার ওপর লিখতে হলো। আমি ভাবলাম এই যে উপলক্ষের গানগুলো লিখছি- ছন্দটা জানি, অন্ত্যমিলটা জানি, গানের কাঠামোটা জানি, এগুলো গান হচ্ছে কিন্তু তবু যেন এসব ঠিক গান নয়। একটা উপলক্ষকে সামনে রেখে রচিত হচ্ছে। যে কারণে সংবাদকে আমরা ঠিক সাহিত্য বলি না। আমার মনে হলো এগুলো সব সংবাদধর্মী কবিতা হয়ে যাচ্ছে। একটা বার্তা দিচ্ছে বটে, সমাজের একটা তাৎক্ষণিক দায় পূরণ করছে। এরচেয়ে নিজের মতো করে কিছু গান লেখা দরকার মনে আমার মনে হলো। তখন আমি পঞ্চকবির সমস্ত গান আমি পড়ে নিলাম। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ডিএল রায়, অতুলপ্রসাদ আর রজনীকান্ত। দেখলাম তাদের পর আধুনিক গানের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তাদের যতো গান আমি পেলাম প্রায় সব পড়ে ফেললাম।
আমাদের এখানে ভালো গান কারা লিখেছেন? মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, আবিদ আনোয়ার। আধুনিক কবিদের মধ্যে এঁরা। এঁরা কিন্তু সবাই কবি। এঁদের গানগুলো আমি পড়ে নিলাম। পড়ার পর আমি দেখলাম যে আমাদের এখানে যে গানগুলো লেখা হচ্ছে, এ গানগুলো গানের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের যে কাঠামো, যে ধারা তৈরি হয়েছে, এই আস্থায়ী, সঞ্চারী, অন্তরা, আভোগ এগুলোকে ঠিক মেনে চলা হচ্ছে না। সুরের প্রয়োজনে বাণী বসাচ্ছে। আর হওয়ার কথা ছিল, আমি যে বাণী লিখব, সে বাণী শ্রোতার কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুর বসবে। ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল। তখন আমি খুব দৃঢ়ভাবে, আমার অন্য লেখাকে কিছুটা সরিয়ে রেখেও আমি তখন গান লেখায় খুব মগ্ন হয়ে পড়লাম।
আমি জানি আমার গান যে খুব বেশি সুরে লাগবে এমন নয়, কারণ সুরকারদের সঙ্গে যে সম্পর্কটা তৈরি হয় সেটি হয়ত এ বয়েসে আমার বেশি একটা হবে না। এসব যদি আমি আরও ছোট বয়েসে লিখতাম তাদের সঙ্গে লেগে থাকতে থাকতে আমার একটা অবস্থা তৈরি হতো। কিন্তু সেই আশা আমি সেভাবে করিও না। আমি বাণীর শুদ্ধতা রক্ষায় আমার যে বিদ্যা আমি অর্জন করেছি- কাব্যবিদ্যা এবং ছন্দবিদ্যা সেসবের প্রয়োগ ঘটিয়ে কিছু সুস্থ বাণী লিখে যেতে চাই। আশার কথা এই যে, আমি লোকজ আঙ্গিকে কিছু গান লিখেছি, সে গানগুলো আমি ফেসবুকে পরিচয় হওয়া একজন শিল্পী যিনি আন্দামান থাকেন তিনি তার নয়টি গানে সুর বসিয়ে এখানে অণিমা মুক্তি গমেজ নামে এক শিল্পীকে পাঠিয়েছেন। তার নিজের করা, হারমোনিয়াম দোতারা বাজিয়ে করেছেন, সে গানগুলো অণিমা মুক্তি গমেজ কয়েকটি আসরে গেয়েছেন এবং সেসব বেশ প্রশংসিতও হয়েছে। আমার এক বন্ধু সঞ্জয় রায়, সে আমার গানগুলো দেখে বলে, ‘যদি চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের আবহ নিয়ে গান লিখতে পারিস- কমল দাশগুপ্ত যেগুলো সুর করেছে বা প্রণব যেগুলো লিখেছে ওরকম যদি হয় তাহলে আমি সুর করতে পারি।’ তার অনুরোধে ওই ধরনের কিছু গান দেওয়ায় সেগুলোতে তিনি সুর করেছেন।
অনুপ ভট্টাচার্যের মতো মুডি সুরকার— মুডি বলছি এজন্য যে তিনি লিরিক পেলেই সুর করেন না, লিরিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এরপর বসেন, তিনি আমার বেশ কিছু গানে সুর করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এরকম আরও অনেকের সহায়তা আমি পাচ্ছি। রাজন সাহা নামে আমাদের এক ছোট ভাই ইদানীং সুরকার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তার সঙ্গে একদিন বসেছি, সে আমাকে বলল, ‘দাদা, আপনার প্রতিটি গানই সুরের জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছে। তবে সেগুলো এখন বাজারে সে সুরগুলো চলছে এরকম হবে না। এরজন্যে আপনার ওরকম শিল্পীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।’
এঁদের কথাগুলো আমার ভেতর আশা জাগিয়েছে। কিন্তু আমি হতাশও হয়েছি এজন্যে যে এখনকার ট্রেন্ডের সঙ্গে আমার গান যাচ্ছে না। না গেলেও আমি আমার এ ধারার গান, শুদ্ধ ধারা লিরিক লেখার চেষ্টা আমি করে যাব। আমি অন্ত্যমিলের সঙ্গে আপস করব না, ছন্দের কাছে আপস করব না, বাংলা গানের হাজার বছরের যে কাঠামো রবীন্দ্রনাথ ঠিক করে দিয়েছেন বা পঞ্চকবি গ্রহণ করেছেন সে কাঠামোর বাইরেও আমি যাব না। কিন্তু আমাদের এখনকার যে গান, যদি বলি যে গত বছর যে একশটি অ্যালবামের গান পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে তার পচানব্বই ভাগই এসমস্ত নিয়ম মেনে রচিত হয়নি। কিন্তু সুরের কারণে, কণ্ঠের কারণে, গায়কীর কারণে অনেক গানই শুনতে খারাপ লাগেনি। কিন্তু বাণীর যে দুর্বলতা তারা বহন করে চলছে, সে দুর্বলতা যেন কোনভাবে আমার রচিত গানে না আসে।
চলবে…