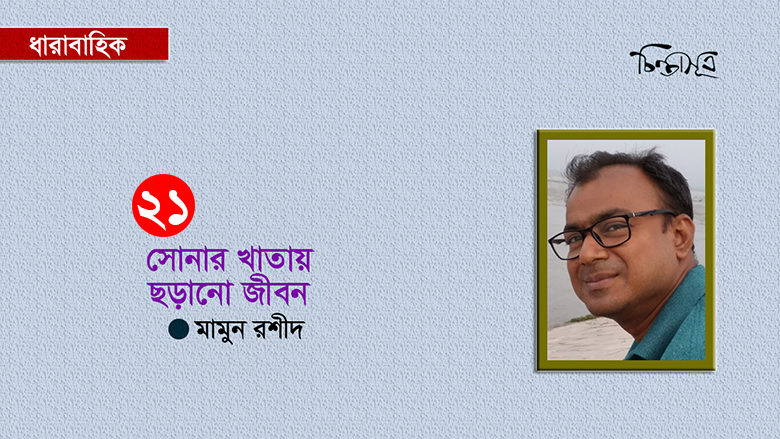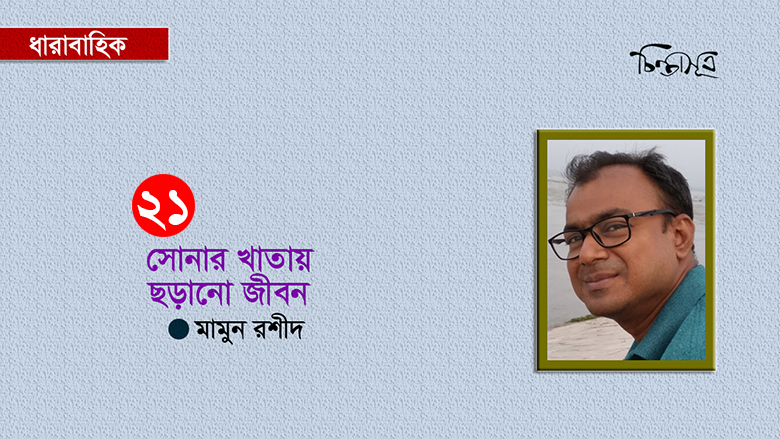
যেভাবে প্রকাশিত হই
লেখক হবো—এমন আকাঙ্ক্ষা ছেলেবেলায় ছিল কি না, মনে নেই। পড়ার আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহ এসেছে আমার মায়ের কাছ থেকে। মা বই পড়তেন। কাজের ফাঁকেও বই পড়তেন। রান্নাঘরে তরকারির ঝুড়ির ভেতরেও বই থাকতো। মা, কাজের ফাঁকে বই পড়তেন। চুলায় ভাত বসিয়ে, পাশে বসে বই পড়তেন। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসা এই দৃশ্যই আমাকে বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। যখন স্কুলের ছুটিতে নানাবাড়িতে যেতাম, তখন দেখতাম মামারাও বই পড়তেন। আমার নানাও বই পড়তেন। আর রাতের বেলা বাবা আমাদের ভাইবোনকে পাশে শুইয়ে গল্প শোনাতেন। যত রাতই হোক, অফিস থেকে ফিরতে—খেয়ে আমাদের গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন।
আর ঈদে, পার্বণে নানাবাড়ি যাওয়ার পর দেখতাম, মামারা বই পড়ছেন। দুপুরে খাবার পর, ভাতঘুমের সময়ে আমাদের পাশে শুয়ে গল্প শোনাতেন। বিনিময়ে তাদের মাথার চুল টেনে দিতে হতো। সেই থেকে আগ্রহ বইয়ের প্রতি।
আমরা যখন নানাবাড়িতে যেতাম, তখন স্টেশনে বইয়ের দোকান থেকে আব্বা আমাদের বই কিনতেন। আমরা পেতাম রূপকথার বই। আর মায়ের জন্য কেনা হতো নিহাররঞ্জন রায়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়সহ অনেকের বই। এই বইগুলোও ওই সময়েই আমি অনেক পড়ে ফেলেছিলাম। বেশ মনে পড়ে স্কুলে ভর্তির পর, তখন সবে বানান করে বই পড়তে শিখেছি, সেই সময়েই আমি রান্নাঘরে মায়ের তরকারির ঝুড়ি থেকে নিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম নিহাররঞ্জন রায়ের ‘তেরো নম্বর ঘর’। কিরিটি রায়ের কথা, সেই যে মনে গেঁথে গিয়েছিল, আজও রয়ে গেছে মগজে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধাপ পেরুনোর আগে বা পরের বছর আমার সেজমামা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, সেবা প্রকাশনী থেকে বের হওয়া চার্লস ডিকেন্সের ‘অলিভার টুইস্ট’।
আমরা খালামনির বাড়িতে যেতাম, স্কুলের ছুটিতে। খালুর বড় ভাইয়ের মেয়ে চান্দা আপা, তিনিও বই পড়তেন। পাগলের মতো। নাওয়া-খাওয়া ভুলে। খালাদের যৌথ পরিবার। বাড়িতে অনেক ছেলে-মেয়ে। দিন শেষে রাতে আমরা সব পিচ্চির দল ভিড় করতাম চান্দা আপার ঘরে। সবাইকে একসঙ্গে রেখে, আপা গল্প শোনাতেন।
পুরো হাইস্কুল লেভেলে আমাদের বাড়িতে সেবা প্রকাশনীর বই স্থান করে নিয়েছিল। কিশোর ক্ল্যাসিকের তিন গোয়েন্দা এরপর মাসুদ রানা সিরিজ, কুয়াশা সিরিজ আর এর বাইরে রোমেনা আফাজের ‘দস্যু বনহুর’-এর প্রতিটি বই চলে আসতো। বই পড়তে নিষেধ ছিল না। তবে স্কুলের পড়া শেষ করে। কিন্তু নতুন বই ঘরে এলে, সেই বই শেষ না করে অন্যকিছু পড়া আমার জন্য কঠিন ছিল। তাই পড়াপাঠ্য বইয়ের নিচে রেখে শেষ করে ফেলতাম নতুন আসা বই। এই গল্প শোনা, পড়া এবং দেখা থেকেই হয়তো আমার ভেতরে কখনো লেখার আগ্রহ জেগে উঠে থাকবে।
ঠিক কখন, কোন বয়সে লেখার আগ্রহ মনের ভেতরে দানা বাঁধলো, মনে করতে পারি না। তবে স্কুলের পাঠ্যবইয়ের যে কবিতাগুলো আমার ভালো লাগতো, সেগুলো আমি জোরে জোরে বারেবারে পড়তাম। মনে হতো, এগুলো বুঝি আমারই লেখা। গদ্য লেখা ভালো লাগলেও তা আমার, এরকম মনে হয়েছে বলে মনে করতে পারি না। তবে ভালোলাগা কবিতাকে সবসময়ই আমার বলে মনে হতো। স্কুল পেরিয়ে যখন কলেজে পা দিলাম, তখনো পাঠ্যবইয়ের কবিতার প্রতি আমার আগ্রহ হারায়নি। আমি বরাবরের মতোই ভালোলাগাগুলোকে আমার বলে মনে করতে থাকি। কলেজে পড়ার সময়েই দৈনিক পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে একদিন সাহস করে কি নিয়ে যেন একটি চিঠি লিখি। দৈনিক সংবাদের চিঠিপত্র বিভাগ আমার সেই চিঠি ছেপে আমাকে চমকে দেয়। এরপর আমি অনেক দিন চিঠিপত্র লিখেছি, নানাবিষয়ে। বাড়িতে একটি কাগজ রাখা হতো, আর গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারে গিয়ে আমি আরো তিন চারটি দৈনিক দেখার সুযোগ পেতাম। সঙ্গে তখনকার সাপ্তাহিক যায়যায়দিনের আমি ছিলাম নিয়মিত পাঠক। সেইসূত্রে চিঠি লেখার বিষয়ের অভাব হয়নি।
পরিচয় হলো চট্টগ্রামের চন্দন চৌধুরীর সঙ্গে। সেই পরিচয়ে বন্ধুতা আজও অমলিন। কত সম্পর্ক সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে গেছে। রয়ে গেছে চন্দন ও ইসলাম রফিক।
সেই শুরু। অনার্স পড়ার সময়ে কয়েকজন মিলে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল সুহৃদ নামের একটি সংগঠন। একসময় আমিও সেই দলে ভিড়লাম। আমাদের অনার্সের কয়েক বন্ধু সুহৃদে যোগ দিয়েই, একটি পত্রিকা বের করার কথা ভাবলাম। আমি ছিলাম পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। সবার লেখা যাচ্ছে, সেখানে আমার লেখা নেই। মনটাই খারাপ। কয়েক রাতের চেষ্টায় এক রাতে কবিতার মতো করে কিছু লাইন লিখলাম। পরদিন সম্পাদক সৈকত ভাইকে দেখালাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এটা দেওয়া যাবে। উত্তেজনায় আমার অবস্থা খারাপ। পত্রিকা বের হলো। সবুজ কালিতে ছাপা। ‘সুহৃদ’। কিন্তু পত্রিকা বেরুনোর পর স্বজনদের দিতে গিয়ে লজ্জায় পড়ে গেলাম। কারণ, আমার যে লেখাটা ছাপা হয়েছিল, তা আর ভালোলাগছিল না। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখেও শুধু লেখাটার কারণে লজ্জা পাচ্ছিলাম। কী লিখেছি? এই কী লিখেছি—ভাবটা এখনো আমাকে তাড়া করে ফেরে। এখনো প্রতিটি লেখা প্রকাশের পর লজ্জা পাই। প্রতিটি বই প্রকাশের পর লজ্জা পাই। তবু শুধু ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার লোভ থেকে অখাদ্য উৎপাদন করে যাই।
১৯৯৫-এর শেষে এসে লেখায় একটু মনোযোগী হলাম। মনে হতে লাগলো, লেখক হওয়া যায়। তবে এই প্রক্রিয়াকে, মানে লেখক হওয়া সহজ বিষয় ভাবিনি তখন, এখনো ভাবি না। দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য যে প্রক্রিয়ায় ভেতর দিয়ে একজন লেখককে যেতে হয়, যে কল্পনা ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়, ভাষার ওপর যে দক্ষতা প্রয়োজন, শব্দের নিয়ন্ত্রণে ঝড়েপড়া নৌকার মাঝির মতো শক্ত হাতে বৈঠা ধরতে হয়, সেই ক্ষমতা অর্জন করতে পারিনি। তবু লিখছি। লিখে যেতে চাইছি। আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে ছোটকাগজ। জীবিকার প্রয়োজনে দৈনিকে কাজ করি, তবু স্বস্তি পাই ছোট কাগজে লিখে। এখনো নিজের কাজের বাইরে ভালো লাগার বিষয়ে লিখতে আগ্রহ বোধ করি ছোটকাগজে। বগুড়া শহরে থাকার সময়ে, সেই অনার্স পড়ার দিনগুলোতে বগুড়া লেখক চক্রের নিয়মিত পাক্ষিক আসরে অংশ নিতাম। সেখানে অনেকে লেখা পড়তো, আমি পড়তাম খুবই কম। সেই আড্ডার দিনগুলো আমাকে উৎসাহী করেছে লেখার প্রতি। সেই আড্ডা থেকেই কতজনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, কতজনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে গেছে কোনো কারণ ছাড়াই। কতজনের কাছে পেয়েছি চিন্তার খোরাক, কত নতুন বইয়ের হদিস।
বগুড়া লেখক চক্রেই পরিচয় হয়েছিল ইসলাম রফিকের সঙ্গে। বয়সের সীমানা পেরিয়ে সেই পরিচয় কবে গাঢ় বন্ধুত্বে রূপ নিয়েছে, আমরা জানি না। আনন্দ-বেদনার নানা কাব্য আমাদের সম্পর্কে। ঝড়ে ও ঝঞ্ঝাটে এখনো নিভুনিভু প্রদীপের মতো টিকে রয়েছে। বগুড়া থেকে তখন অনেক ছোট কাগজ প্রকাশিত হয়। একে একে আমরাও নিজেরা ছোটকাগজ প্রকাশের দিকে ঝুঁকলাম। ইসলাম রফিকের হাতে ধরে প্রকাশ পেলো ‘দোআঁশ’, আমার হাতে ‘দ্বিবাচ্য’। তবে আমার সেই সময়ের লেখালেখি বগুড়ার কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাইরে তখনো বের হইনি। চাকরি সূত্রে ইসলাম রফিক তখন গাইবান্ধায়। একদিন জানালেন, গাইবান্ধা থেকেও বেরুবে ছোটকাগজ। তাদের হয়ে লেখা চাইলেন। আমার কয়েকটি লেখা একদিন নিয়ে গেলেন। তারপর হুট করেই বেশ কিছুদিন পর হাতে পেলাম ওয়ালী কিরণ সম্পাদিত ‘ক্রম’। সেখানে আমার একগুচ্ছ লেখা। এরপর ইসলাম রফিক আবারও লেখা নিয়ে গেলেন চিনু কবিরের কাগজ ‘ক্যাথারসিস’-এর জন্য। সেখানেও গুচ্ছ কবিতা। পরিচয় হলো চট্টগ্রামের চন্দন চৌধুরীর সঙ্গে। সেই পরিচয়ে বন্ধুতা আজও অমলিন। কত সম্পর্ক সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে গেছে। রয়ে গেছে চন্দন ও ইসলাম রফিক।
এরপর নানাসময়ে নানান কাগজে লিখেছি। এখনো ছোটকাগজ থেকে আমন্ত্রণ পেলে লিখি। লেখার আগ্রহ প্রকাশ করি। তবে ছোটকাগজের সেই বারুদভাব আর খুঁজে পাই না। সেই রাগী চেহারা আর দেখি না কোনো কাগজের ভেতরে। আমার ভেতরের বারুদ ক্রমশ নিভে যাচ্ছে বলেই কি আর কোথাও খুঁজে পাই না রাগী-বারুদ ভাব? ছোটকাগজের লেখক সুবিমল মিশ্রের উক্তি, ‘তুমি ছাপবে কি, আমি ঠিক করবো তোমার কাগজে লিখবো কি না!’ এই ভাবই আমাদের জাগিয়ে রাখতো। এখনো জাগিয়ে রাখে লেখকের অহঙ্কারে, লেখক হতে না পারার ব্যর্থতায়ও।
চলবে