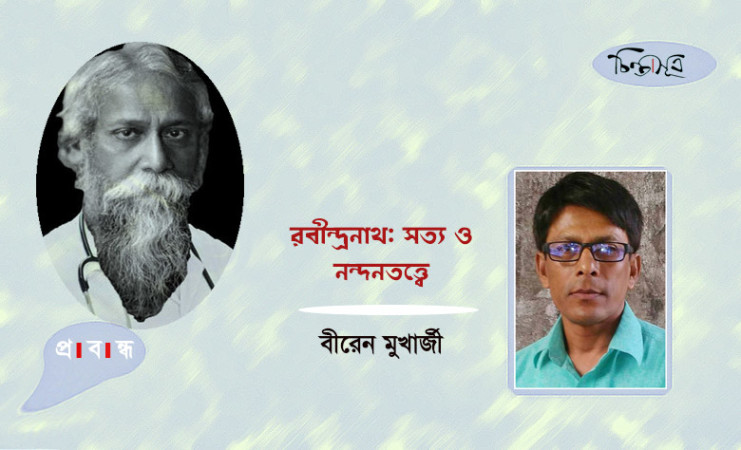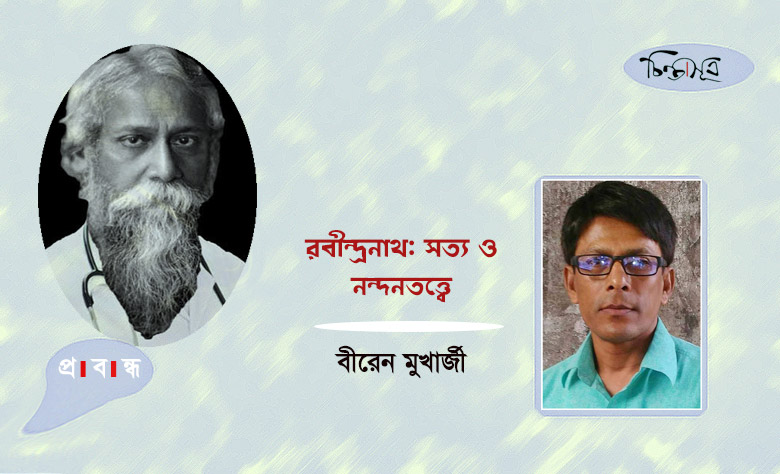 বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির, মনন ও রুচির, স্বপ্ন ও আবেগের, উৎসব ও অনুভবের, সংগ্রাম ও সংকল্পের, সংশয় ও জিজ্ঞাসার প্রধানতম নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালি মনীষার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিই নন, আজীবন যুক্তিপ্রিয় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বও। সাহিত্যের প্রতিটি স্তর রবীন্দ্রনাথের অমেয় স্পর্শে পুষ্ট হয়েছে—এ কথা সর্বজনবিদিত। সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজের অন্ধগলি থেকে মানুষকে আলোর পথে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগণ্য। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে কেউ খালি হাতে ফিরেছেন, এমন দৃষ্টান্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন যেমন তার কর্মে, নানা মাত্রায় ও ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল, তেমনি সাহিত্যভাবনার মূলেও যে নির্মল সত্য প্রতিভাত, তা হলো আনন্দ। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের যুগপৎ আত্মানুভব—তার সারকথা পরমানন্দ লাভ। সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-বিস্ময়, রাগ-অনুরাগ লজ্জা-ভয়সমেত জীবনরসের সামগ্রিক দর্শনকে উপজীব্য করে তিনি এই আনন্দযাত্রায় অভিযাত্রী। পর্যায়ক্রমে অনুভব ও বৈরাগ্যের বিবিধ প্রপঞ্চ জয় করে এমন এক স্তরে তিনি অধিষ্ঠিত, সে স্তর সার্বভৌমত্বের—সেখানে শুধু ঋষিকেই পরমানন্দে সম্ভাষণ জানানো যেতে পারে।
বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির, মনন ও রুচির, স্বপ্ন ও আবেগের, উৎসব ও অনুভবের, সংগ্রাম ও সংকল্পের, সংশয় ও জিজ্ঞাসার প্রধানতম নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালি মনীষার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিই নন, আজীবন যুক্তিপ্রিয় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বও। সাহিত্যের প্রতিটি স্তর রবীন্দ্রনাথের অমেয় স্পর্শে পুষ্ট হয়েছে—এ কথা সর্বজনবিদিত। সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজের অন্ধগলি থেকে মানুষকে আলোর পথে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগণ্য। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে কেউ খালি হাতে ফিরেছেন, এমন দৃষ্টান্ত নেই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন যেমন তার কর্মে, নানা মাত্রায় ও ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল, তেমনি সাহিত্যভাবনার মূলেও যে নির্মল সত্য প্রতিভাত, তা হলো আনন্দ। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের যুগপৎ আত্মানুভব—তার সারকথা পরমানন্দ লাভ। সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-বিস্ময়, রাগ-অনুরাগ লজ্জা-ভয়সমেত জীবনরসের সামগ্রিক দর্শনকে উপজীব্য করে তিনি এই আনন্দযাত্রায় অভিযাত্রী। পর্যায়ক্রমে অনুভব ও বৈরাগ্যের বিবিধ প্রপঞ্চ জয় করে এমন এক স্তরে তিনি অধিষ্ঠিত, সে স্তর সার্বভৌমত্বের—সেখানে শুধু ঋষিকেই পরমানন্দে সম্ভাষণ জানানো যেতে পারে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির শাশ্বত চৈতন্যকে চিন্তা ও বোধের উৎকর্ষে রূপায়িত করেছেন। ফলে সমাজের লোভী শ্রেণীর দূরভিসন্ধি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করেছেন সাধারণ মানুষ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই লোভী শ্রেণীই তৎকালে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছে সন্দেহের চোখে। তার সাহিত্যকর্মকে বিশেষ একটি ধর্মীয় শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করতেই তাক বিতর্কিত করা হয়েছে। বিস্ময়করভাবে সত্য যে, সাহিত্য, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে তার চিন্তার স্বরূপ নিয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব এখনো সমাজে প্রকট। যে কারণে উত্তরকালে এসেও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বিবেচনার আগে কে হিন্দু আর কে মুসলমান—এ বিষয়টি ষড়যন্ত্রকারীদের বিবেচনায় মুখ্য হয়ে ওঠে! সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে মানুষের মধ্যে যে গোঁড়ামি চেপে বসতে দেখা গেছে অতীতে, তার জন্য মূলত শিক্ষার অভাবকেই দায়ী করেছেন সমাজ বিশ্লেষকরা। আবার এটাও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে যে, একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন শিক্ষা ও উন্নয়নের শীর্ষে অবস্থান করছে, যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে বিশ্বকে নিমেষে হাতের মুঠোয় পাচ্ছে, তখন অজ্ঞানতার এই ডামাডোল কেন? রবীন্দ্রনাথ ও তার সৃষ্টিকর্মকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অজ্ঞানতাই কি দায়ী? হতে পারে, চক্রান্তকারীদের কাছে অজ্ঞানতা একটি পোশাক। কুশিক্ষা ও জাগতিক নানা স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবেও রবীন্দ্রনাথকে বিতর্কের বিষয়বস্তু হিসেবে টেনে আনলে, অবাক হওয়ার কিছুই থাকে না। অথচ, কিছুতেই অস্বীকার করার উপায় নেই—তিনি ‘গীতিধর্মিতা, চিত্ররূপময়তা, অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোমান্টিক চেতনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, বাস্তবচেতনা ও প্রগতিচেতনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে যে প্রেম ও আনন্দের সত্তাকে ধারণ করেছেন’, তার ভেতর সমগ্র মানবজাতির কল্যাণই প্রতিফলিত।
রবীন্দ্রনাথ মানুষ, প্রকৃতি বা জীবনদেবতার স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন—জীবনই আসলে সাহিত্য। তিনি যখন উচ্চারণ করেন, ‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে।/নির্মল করো, উজ্জ্বল করো/সুন্দর করো হে’ তখন খুব জানতে ইচ্ছে করে, এই চিরাচরিত আহ্বান কোন ধর্মের, কোন গোষ্ঠীর? লক্ষণীয় যে, এখো বাঙালি সমাজের মানুষ, ধর্মীয় কুসংস্কারের বাইরে এসে কতটুকু মানুষ, সে প্রত্যয় গড়ে না ওঠায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা প্রচারিত হচ্ছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রচর্চার ভারাসাম্যহীনতার সংকট তৈরি হচ্ছে। অথচ নির্মল সত্য এই যে, ‘শেষের মধ্যেই থাকে অশেষ’। এই বিবেচনায় জীবনের পরম শান্তির সন্ধানটুকু সাহিত্যে ব্যাপৃত করতেই জীবন পার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যারা জীবনবাদী, সত্য-সুন্দর ও নন্দনতত্ত্বের বিচারে তারা বিশ্বাস করেন—‘নিজেদের যতই উন্নতির শিখরে টেনে নিয়ে যাই না কেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রাসঙ্গিকভাবেই সামনে নিয়েই এগোতে হয়।’ অন্যদিকে গোঁড়ামির ঠুলিধারীরা রবীন্দ্রনাথের বর্জন চান সর্বোতভাবে। বিস্ময়কর সত্য যে, যতবারই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে, ততবার সব ধরনের জটাজাল ছিঁড়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন আলোর প্রত্যয় নিয়ে জেগে উঠেছেন। পুনর্বার ফিরে আসার এই শক্তি একমাত্র রবীন্দ্রসাহিত্যেই নিহিত। রবীন্দ্রসাহিত্য যে বিপুল জীবন সঘন, তা একইসঙ্গে সত্য, সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্বে বিকশিত।
প্রাবন্ধিক আহমদ রফিকের মতে, ‘শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির নান্দনিকতা নিয়ে ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার বিভিন্নতায় একাধিক ভিন্নমতের প্রকাশ মূলত ভাববাদের প্রাধান্যই পরিস্ফুট করে তুলেছে। এমনকি শুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির মতবাদে বিশ্বাসী চরমপন্থীদের বক্তব্যে এমন বিশ্বাসও ফুটে উঠেছে যে, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা বিচার্য বিষয় নয়, সৃষ্টিই বিচার্য।’ (শিল্প সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা/কালি ও কলম)। রবীন্দ্রসাহিত্যে রয়েছে নন্দনতত্ত্বের সফল উদ্ভাসন, যা নতুন করে বলার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ ভাগ পর্যন্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ১৯৩৪ সালে যখন বিহার প্রদেশে ভূমিকম্পে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়, মহাত্মা গান্ধী তখন এ ঘটনাকে ‘ঈশ্বরের রোষ’ বলে অভিহিত করেন। আর রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির এহেন বক্তব্যকে অবৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত করে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন। অথচ, সেই রবীন্দ্রনাথ, যার সাহিত্যকর্মে মানবাত্মার প্রকৃত দর্শন, জীবন ও প্রকৃতির বহুমাত্রিক ধারা প্রতিফলিত; শেষাবধি সমকালে তাকে যেমন ধর্মীয় পরাকাষ্ঠার বলয়ে স্থাপনের অপচেষ্টা করা হয়েছে, উত্তরকালেও তার মুক্তি মেলেনি। আবার রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনার অতলান্তিক অন্বেষণের জোর প্রচেষ্টাও ঠিক আশানুরূপ নয়। প্রাবন্ধিক হামীম কামরুল হকের মনে করেন, “সামাজিক জীবনে, গোষ্ঠীগত, আন্তঃশ্রেণী সম্পর্কে, রাজনীতিতে, প্রতিষ্ঠানে, মূল্যবোধে এবং আদর্শগত ধারণায় সংস্কৃতির সত্যিকারের গতিপথকে বোধগম্য করতে ‘সংস্কৃতি-অধ্যয়ন’ নতুন একটি অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের জাতি ও জনগোষ্ঠীর ভেতরে; এবং এজন্য আমাদের প্রধানতম অবলম্বন হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্পসাহিত্য।” বলা বাহুল্য, হামীম কামরুল হকের এই মতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অতলান্তিকে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে।
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনা একপাশে সরিয়ে বাংলায় জ্ঞান অন্বেষণের কথা কি আদৌ চিন্তা করা যায়? বোধ করি যায় না। তিনি যেভাবে ব্যাপ্ত বাঙালি সত্তায়, তাকে দূরে সরিয়ে রাখা মানেই জাতিকে আরও কয়েকশ বছর পেছনের দিকেই ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ হায়াৎ মামুদ রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিচিন্তার বিনির্মাণের পথটা দেখিয়ে দিয়েছেন। ১৮৯৮ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘গ্রাম্যসাহিত্য’ প্রবন্ধের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরে মন্তব্য করেন—“এই উদ্ধৃতির মধ্যে ‘সাহিত্য’ শব্দটি যেখানে যেখানে যতবার আছে, সেখানে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি স্থাপন করলেই রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিচিন্তার মানচিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।” রবীন্দ্রনাথের সেই উদ্ধৃতি খেয়াল করি :
গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্র সাহিত্যের নিম্ন-অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরে থাকতার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুলফল-ডালপালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না- তবু তত্ত্ববিদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে। (রবীন্দ্র, ১৪১৫ তৃতীয় খণ্ড : ৭৯৪)।
অস্বীকারের উপায় নেই—সংস্কৃতির এই ক্ষমতা-কাঠামোকে রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই বুঝতেন। কিন্তু তিনি সংস্কৃতির ভেতরে দিয়ে আধিপত্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা চাননি। তিনি চেয়েছেন মানুষের মুক্তি ও মানুষের চিত্তোৎকর্ষ। এ জন্যই জীবনব্যাপী তিনি সত্য ও সুন্দরের আরাধনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে/দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে’—জগতের এই আনন্দধারা থেকে সত্য ও সৌন্দর্য অন্বেষণ খুব সহজ কথাও নয়। এ জন্য যে ধ্যান ও অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন বাঙালির- সমালোচনামুখর, গোঁড়ামিতে ঠাসা বাঙালির সে অধ্যাবসায় আদৌ কি আছে কিংবা সে চেষ্টাও কি বহমান, এমন প্রশ্ন উঠে আসাও অযৌক্তিক হতে পারে না।
মৃত্যুবেদনা মানুষকে ক্ষণিকের জন্য হলেও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করে তোলে, রবীন্দ্রনাথ এ সত্য উপলব্ধি করলেও মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হওয়া উচিত নয় বলে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মৃত্যু পূর্ণতারই অংশ, ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, বিরহবেদন লাগে! তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে!’ রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যজনকভাবে শোকের মধ্যে থেকেও জীবনের জয়গান গেয়েছেন।
আজিকে তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া রব দুয়ারে- রাখিব জ্বালি আলো!
তুমি তো ভালো বেসেছ, আজি একাকী শুধু আমারে বাসিতে হবে ভালো!’
গবেষক শ্রী গুপ্ত ‘রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘মৃত্যুর মধ্যে যে শোক, সেই শোকের শত যন্ত্রণা ছাপিয়েও এই যে ঐকান্তিক প্রেম; এই প্রেমের শক্তিই আমাদের সংলগ্ন রাখে জীবনের প্রবহমানতার সঙ্গে! কবি তাই মৃত্যুর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করেননি! মৃত্যুও প্রবহমান জীবনের প্রধানতম অনুষঙ্গ! এই বোধ জাগ্রত থাকলে, শোক আমাদের পরাজিত করতে পারে না, বরং উত্তীর্ণ করে জীবনের পূর্ণতায়!’ আর জীবনের পূর্ণতার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো যুগপৎ সত্য, সৌন্দর্যে নন্দনতত্ত্ব অন্বেষা। স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যে উচ্চমার্গীয় চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি জগতের আলোকিত অনুভব আর সৌন্দর্যের উদ্ভাসন নিয়ে রচনা করেছেন সাহিত্য। প্রকৃতিরূপে নারী স্বরূপের সন্ধান করেছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন পরম সত্যকে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যেমন জীবনদর্শনের প্রতীক; তেমনি সত্য, সৌন্দর্য ও নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেরও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।