 রবীন্দ্রনাটকে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি প্রবল অনুরাগ ও নির্ভরতা লক্ষ করা যায়। তাঁর পঞ্চাশটির নাটকে ভারতীয় পুরাণের ব্যবহার থাকলেও বেশি রয়েছে বৌদ্ধআখ্যানের সরাসরি প্রয়োগ বা নবরূপায়ণের প্রচেষ্টা। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, বৌদ্ধ আখ্যানির্ভর নাটকগুলো তিনি বার বার পরিমার্জন করেছেন, পুনর্লিখন করেছেন। ‘পরিশোধ’ নাটকটি রচনার চল্লিশ বছর পরে তিনি ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যে রূপান্তর করেছেন। এ সব আচরণ বৌদ্ধ আখ্যানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতেরই প্রমাণ বহন করে। ‘কথা’ কাব্যের আখ্যান কবিতার কথা সবাই জানি যে, তা বৌদ্ধসংস্কৃতি থেকে চয়ন করা হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘সংস্কৃত অবদান সাহিত্য’ (১৮৮২) প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি বৌদ্ধ আখ্যানের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি থেকেই এর সত্যতা মেলে। তিনি বলেছেন:
রবীন্দ্রনাটকে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি প্রবল অনুরাগ ও নির্ভরতা লক্ষ করা যায়। তাঁর পঞ্চাশটির নাটকে ভারতীয় পুরাণের ব্যবহার থাকলেও বেশি রয়েছে বৌদ্ধআখ্যানের সরাসরি প্রয়োগ বা নবরূপায়ণের প্রচেষ্টা। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, বৌদ্ধ আখ্যানির্ভর নাটকগুলো তিনি বার বার পরিমার্জন করেছেন, পুনর্লিখন করেছেন। ‘পরিশোধ’ নাটকটি রচনার চল্লিশ বছর পরে তিনি ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যে রূপান্তর করেছেন। এ সব আচরণ বৌদ্ধ আখ্যানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতেরই প্রমাণ বহন করে। ‘কথা’ কাব্যের আখ্যান কবিতার কথা সবাই জানি যে, তা বৌদ্ধসংস্কৃতি থেকে চয়ন করা হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘সংস্কৃত অবদান সাহিত্য’ (১৮৮২) প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি বৌদ্ধ আখ্যানের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি থেকেই এর সত্যতা মেলে। তিনি বলেছেন:
এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ ‘কথা ও কাহিনী’র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই-সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় ‘কথা ও কাহিনী’ সেই কালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই ‘কথা ও কাহিনী’র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছে, আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমাময়, এ কী করুণায়, প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তা হলে সমস্ত দেশ জুড়ে ‘কথা ও কাহিনী’র হরির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত, তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে। আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ তা করেনি। কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মার মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। [সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা,http://rabindra.rachanabali.nltr.org/node/7380]
রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখেছেন ৫০টির বেশি। ভারতীয় উপমহাদেশের পৌরাণিক আখ্যান থেকে তিনি সারবস্তু গ্রহণ করে, কখনো কাহিনি কখনো চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি নাটক রচনা করেছেন। তবে তাঁর নাটকে বৌদ্ধ আখ্যানের তীব্র উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে রূপান্তর করেছেন নাটকে। আবার একই নাটক বার বার পরিমার্জন করেছেন। খেয়াল করার বিষয় হলো, বৌদ্ধ আখ্যান সংবলিত নাটকগুলোর ক্ষেত্রেই এই উদ্যোগ বেশি। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, বৌদ্ধআখ্যানের প্রতি তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন ‘রাজা’ নাটকটি তিনি চার বার পুনর্লিখন করেছেন। ‘পরিশোধ’নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যে। রবীন্দ্রনাথ যে সব নাটকে বৌদ্ধ আখ্যান প্রয়োগ করেছেন, তার মধ্যে সেরা নাটক হলো ‘মালিনী’ (১৮৯৬), ‘নটীর পূজা’ (১৯২৬) ও ‘চণ্ডালিকা’ (১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সব নাটকের কাহিনি গ্রহণ করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ‘অবদান সাহিত্য’ থেকে। এছাড়া ধর্মরাজ বড়ুয়ার ‘হস্তসার’ (১৮৯৩) গ্রন্থটিও তাঁর কাহিনি-চয়নে সহায়ক হয়েছে।
নাটকের বৌদ্ধআখ্যানের উৎস-সন্ধান
| রচনাকাল | নাম | কাহিনি-উৎস | মূল অবদানগ্রন্থ |
| ১৮৯৬ | মালিনী | মালিন্যাবস্তু অবদান | মহাবস্তু অবদান |
| ১৯১০ | রাজা | কুশজাতক | মহাবস্তু অবদান |
| ১৯১২ | অচলায়তন | চূড়াপক্ষাবদান | দিব্যাবদান |
| ১৯১৮ | গুরু | চূড়াপক্ষাবদান | দিব্যাবদান |
| ১৯২০ | অরূপরতন | কুশজাতক | মহাবস্তু অবদান |
| ১৯২৬ | নটীর পূজা | অবদানশতক | |
| ১৯২৯ | শ্যামা | জাতক | মহাবস্তুবদান |
| ১৯৩৩ | চণ্ডালিকা | শার্দূলকর্ণাবদান | দিব্যাবদান |
| ১৯৩৮ | নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা | শার্দূলকর্ণাবদান | দিব্যাবদান |
| ১৯৩৯ | শাপমোচন | কুশজাতক | মহাবস্তু অবদান |
এবারে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের কাহিনি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যেতে পারে।
মালিনী (১৮৯৬)
বৌদ্ধআখ্যান নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটকের নাম ‘মালিনী’। নাটকের সূচনায় এর রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায়। এর কাহিনি অনেকটা স্বপ্নে-পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি:
‘মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। কবিকঙ্কণকে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন তাঁর গুণকীর্তন করতে। আমার স্বপ্নে দেবীর আবির্ভাব ছিল না, ছিল হঠাৎ মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ ঘুমন্ত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে।
তখন ছিলুম লন্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। প্রবাসী বাঙালিদের প্রায়ই সেখানে হত জটলা, আর তার সঙ্গে চলত ভোজ। গোলেমালে রাত হয়ে গেল। যাঁদের বাড়িতে ছিলুম, অত রাত্রে দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে হঠাৎ চমক লাগিয়ে দিলে গৃহস্থ সেটাকে দুঃসহ বলেই গণ্য করতেন; তাই পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম। বিছানায় যখন শুলুম তখনো চলছে কলরবের অন্তিম পর্ব, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে।
এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।
জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের একভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতামাত্র, অন্যভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না। পালিত সাহেবকে মনের ক্রিয়ার এই বিস্ময়করতা জানিয়েছিলুম। তিনি এটাতে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য বোধ করলেন না।
কিন্তু অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল। (সূচনা, মালিনী, http://rabindra.rachanabali.nltr.org/node/2306)

স্বপ্নে-পাওয়া এই থিমের সঙ্গে যুক্ত হলো মহাবস্তু-অবদানের আখ্যান। বারানসীর রাজা কৃকির কন্যা মালিনী শ্রদ্ধা করে ভিক্ষু কাশ্যপকে। মালিনী একদিন ভিক্ষু কাশ্যপ ও তার অনুসারীদের নিমন্ত্রণ করে। এতে ক্ষুব্ধ হয় মালিনীর ব্রাহ্মণসমাজ। ভিক্ষু কাশ্যপকে নিমন্ত্রণ ও সমাদর করার অপরাধে তারা মালিনীকে নির্বাসনদণ্ড দেয়। মালিনী নির্বাসনে যাওয়ার আগে এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করে। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। মালিনীকে ভালোবাসত তার ভাই, অমাত্যবর্গ ও সাধারণ মানুষ। তাঁরা ব্রাহ্মণদের আচরণের প্রতিবাদ করে এবং মালিনীর সমর্থনে একে একে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। রাজা এই অবস্থা মেনে নিতে পারে না। তাই মেয়ে মালিনীকে বলে:
হায় রে অবোধ মেয়ে, নব ধর্ম যদি
ঘরেতে আনিতে চাস, সে কি বর্ষানদী
একেবারে তট ভেঙে হইবে প্রকাশ
দেশবিদেশের দৃষ্টিপথে? লজ্জাত্রাস
নাহি তার? আপনার ধর্ম আপনারি,
থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী
দেখে যেন নাহি করে দ্বেষ, পরিহাস
না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস
রাখ মনে মনে।
কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। মালিনী ও তার অনুসারীরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ব্রাহ্মণরা তখন রাজার কাছে বিচার ও আশ্রয় চায়। আর তরা গোপনে ভিক্ষু কাশ্যপকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সেই ষড়যন্ত্র অবশেষে বিফল হয়। ভিক্ষু কাশ্যপ বেঁচে থাকে আর অন্যায়কারী ব্রাহ্মণরা পরাজিত হয়। সংক্ষেপে এই হচ্ছে মালিনী নাটকের কাহিনি। বৌদ্ধ আখ্যান অক্ষুণ্ণ রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটকে সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর নামে দুটি পৃথক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ধর্মনাশের আশঙ্কায় হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা মালিনীকে দণ্ড দেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের এই মূঢ় আচরণে মালিনী ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু রাজাজ্ঞার বিরোধিতা করে না। নির্বাসনদণ্ড মেনে নিয়েই বলে:
শোনো পিতা-যারা চাহে নির্বাসন মোর
তারা চাহে মোরে। ওগো মা, শোন্ মা কথা—
বোঝাতে পারি নে মোর চিত্তব্যাকুলতা।
আমারে ছাড়িয়া দে মা, বিনা দুঃখশোকে,
শাখা হতে চ্যুত পত্রসম। সর্বলোকে
যাব আমি-রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির-সংসার। জানি না কী কাজ আছে,
আসিয়াছে মহাক্ষণ।
মালিনী নিজেই নির্বাসন মেনে নেয়। রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে এসে মালিনীর আত্মঘোষণা ধ্বনিত হয় এভাবে:
আসিয়াছি আজ—
প্রথমে শিখাও মোরে কী করিব কাজ
তোমাদের। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি-কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহি নি বাহিরে, দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল-কোথায় কী ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।
গৌতম বুদ্ধ যেমন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, মালিনীও তেমনি। মালিনীর চরিত্রের মধ্যে বুদ্ধের আদর্শ বিশেষত ক্ষমার বাণী প্রকাশ পেয়েছে এই নাটকে। মূর্ছা যাওয়ার আগে মালিনীর শেষ সংলাপ ‘ক্ষম ক্ষেমংকরে’ বলে ক্ষমার চরম পাঠ প্রকাশিত। যে ক্ষেমংকর একটু আগেই ধর্মপ্রাণ সুপ্রিয়কে বধ করেছে, তাকেও মালিনী ক্ষমতা করে দেয়। এই তো বুদ্ধের আদর্শ। মালিনী নাটকে ব্রাহ্মণ্যবাদকে যেমন আঘাত করা হয়েছে, তেমনি বৌদ্ধ আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। বৌদ্ধ আখ্যানকে অবলম্বন করে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক এই ‘মালিনী’।
রাজা (১৯১০) ও অরূপরতন (১৯২০)
নাটকের নাম রাজা। কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজাকে মঞ্চে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাট্যনিরীক্ষায় এটি নতুন সংযোজন। নাটকটি মহাবস্তু-অবদানের কুশজাতকের আখ্যান থেকে নেওয়া। আখ্যানের মিল থাকলে স্থান ও চরিত্রে ভিন্নতা রয়েছে। বারাণসীর রাজা ইক্ষাকুর প্রধান রানীর সন্তান হচ্ছে কুশ। কুশের চেহারা অসুন্দর হলেও অসাধারণ জ্ঞানী। তার বিয়ে হয় কান্যকুব্জের রাজার কন্যা সুদর্শনার সঙ্গে। সুদর্শনা ছিল পরমাসুন্দরী। পক্ষান্তরে কুশ এতই কুৎসিত ছিল যে, দিনের আলোয় তাকে দেখলে সুদর্শনা তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে চলে যেতে পারে। তাই কুশের মা কুশ-সুদর্শনাকে অন্ধকারগৃহে রাখার আয়োজন করে। সুদর্শনা তার স্বামীকে দেখতে চাইলে কুশের ভাইকে দেখানো হয়। এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দিনে সুদর্শনা তার স্বামীকে দেখতে পায়। স্বামীর প্রতি তার ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুদর্শনা চলে যায় বাপের বাড়ি। বিরহকাতর কুশ স্ত্রীকে দেখার আশায় কন্যাকুব্জে যায় এবং ছদ্মবেশে রাজবাড়ির রান্নাবান্নার কাজ নেয়। সুদর্শনার জন্য একে একে সাতজন পাণিপ্রার্থী আসে। কুশ তাদের সকলইে যুদ্ধে পরাজিত হয়। এতে সুদর্শনা ছদ্মবেশী কুশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুদর্শনা কুশের সঙ্গে চলে আসে। বাড়ি ফেরার পথে নদীতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে কুশ নিজেই বিস্মিত হয় এবং আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এমন সময় ঈশ্বরের কুপাবলে সে রূপবান পুরুষে রূপান্তরিত হয়। এটি বৌদ্ধ কাহিনির অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব রূপক নাটক। এই একই কাহিনীকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে ‘অরূপরতন’ (১৯২০) নাটকটি। ‘অরূপরতন’ নাটকের ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত এই কাহিনির রূপকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাটিও স্মরণ করা যেতে পারে:
সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;-নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,-সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,-এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।
অরূপরতন নাটকে সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদাদা চরিত্রদুটি নতুন সৃষ্টি। এছাড়া ‘রাজা’ নাটকটিরই পুনর্লিখিত রূপ এই ‘অরূপরতন’। ঠাকুরদা চরিত্রটি যাত্রার বিবেকের মতো। ঠাকুরদাদার কণ্ঠে আছে গান:
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে॥আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে॥
এ নাটকে ঠাকুরদাদা ছাড়াও বালকগণ, বাউল ও সুরঙ্গমাও গান গায়।
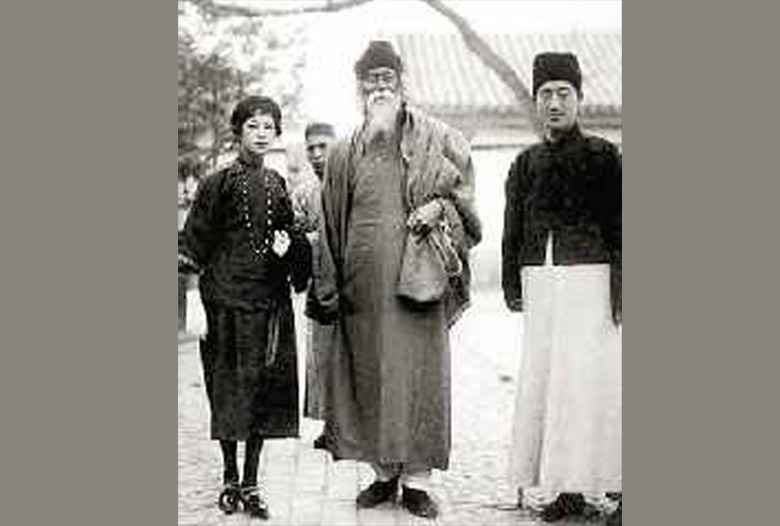
অচলায়তন (১৯১২) ও গুরু (১৯১৮)
এর আখ্যান নেওয়া হয়েছে দিব্যাবদানমালার চূড়াপক্ষাবদানের পঞ্চক-কাহিনি থেকে। এখানেও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংকীর্ণতার কথা বলা হয়েছে। এক ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও মারা যায়। একটি সন্তানও বাঁচে না। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে একটি শিশু বেঁচে থাকে। এই শিশুই এই নাটকের মহাপঞ্চক। পরে ব্রাহ্মণের ঘরে আরও একটি শিশুর জন্ম হয়। সে হলো পঞ্চক। মহাপঞ্চক প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হয়। একসময় সন্ন্যাস গ্রহণ করে সিদ্ধপুরুষ হয়ে ওঠে। কিন্তু পঞ্চক ছিল মূর্খ। সেও সন্যাস গ্রহণ করে। কিন্ত তার মূর্খতা ঘোচে না। তাই সে বিহার থেকে বিতাড়িত হয়। বিহার থেকে বেরিয়ে পঞ্চক রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। তাকে কাঁদতে দেখে ভগবান বুদ্ধ তাকে বিচারের ফিরিয়ে নেয় এবং আরেক ভিক্ষুর কাছে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। পঞ্চক অল্প সময়েই সিদ্ধিলাভ করে। পঞ্চকের পূর্বজন্মের ভালো কাজের ফল এই জন্মে ভোগ করতে পারল। এটাই এই কাহিনির শিক্ষা।
বিহারকেই এখানে অচলায়তন বলা হয়েছে। দীর্ঘদিনের সংস্কার ও অনুবৃত্তিতে অচলায়তনের শিক্ষা হয়ে পড়ে গণ্ডিবদ্ধ। পঞ্চকের এসব ভালো লাগে না। সুযোগ পেলেই সে বাইরে আসে। বাইরের আলো-বাতাস উপভোগ করে। বাইরের পৃথিবীই তার আরাধ্য হয়ে ওঠে। তাই সে বলে ওঠে:
আকাশে কার ব্যাকুলততা,
বাতাস কহে কার বারতা
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।
অচলায়তের বাইরে এসে সে দাদাঠাকুরের সন্ধান পায়। এই দাদাঠাকুর যেন যাত্রার বিবেকের মতো পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। দাদাঠাকুর ও পঞ্চকের সংলাপ:
দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।
পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মেরই না, তবু ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।
দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।
পঞ্চক। তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।
দাদাঠাকুর। আয় রে, তবে যাত্রা করি।
‘ডাকঘর’ নাটকের অমল, ‘মুক্তধারা’ নাটকের অভিজিৎ এবং ‘রক্তকরবী’ নাটকের রঞ্জনের মতো ‘অচলায়তন’ নাটেকর পঞ্চক হলো মানবাত্মার মুক্তির প্রতীক। অচলায়তন নাটকে প্রথাবিরোধিতা পথ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘জীর্ণপুরাতন যাক ভেসে যাক’ এই বাণীই প্রকাশ করেছেন এই নাটকে। এটির প্রকাশিত হলে ব্যাপক সমালোচনা হয়। প্রশংসার পাশাপাশি বিরূপ সমালোচনারও শিকার হন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ। মন্ত্র ও আচারকে বিদ্রূপ করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই অভিযোগের জবাবে অধ্যাপক ললিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:
‘নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে-পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়অ নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাতেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে।… আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত-দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই।… অচলঅয়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।’
নটীর পূজা (১৯২৬)
‘পূজারিণী’ কবিতাটির বিষয়বস্তুকেই তিনি ‘নটীর পূজা’ নাটকে রূপান্তর করেছেন। এর আখ্যান অবদানশতক থেকে নেওয়া। মগধের রাজা বিম্বিসারের জ্যোতিষ্ক নামে সুন্দর একটি প্রাসাদ ছিল। এটি তিনি এক ছেলেকে দান করেন। অন্য ছেলে অজাতশত্রু এতে ক্রদ্ধ হয়ে পিতা রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। অজাতশত্রু ছিলেন বুদ্ধবিরোধী। বিম্বিসার তার প্রাসাদকাননে বুদ্ধের উদ্দেশে একটি স্তূপ বানিয়েছিলেন। পরিচারিকারা তা পরিষ্কার করে প্রদীপ জ্বালাত। অজাতশত্রু তা বন্ধ করে দেন। দেবদত্তের প্ররোচনায় তিনি এই ঘোষণা দেন যে, বুদ্ধের প্রতি কেউ শ্রদ্ধা নিবেদন করলে তার শিরশ্ছেদ করা হবে। একদিন দাসী শ্রীমতী এই আদেশ লঙ্ঘন করে স্তূপ ধুয়ে সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। রাজার আদেশে তার শিরশ্ছেদ করা হয়। একদিন রাজা শিকারের জন্য বনে গিয়ে এক শ্রমণের সাক্ষাৎ পান। শ্রমণের উপদেশে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। শ্রমণের উপদেশে বুদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন।
বুদ্ধকে পূজার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার এই কাহিনি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন ‘নটীর পূজা’। মূল কাহিনির শ্রীমতীই রবীন্দ্রনাথের নটী। বিম্বিসার এখানে স্বেচ্ছায় সিংহাসনত্যাগী এবং ছেলের কাছে রাজ্যভার অর্পণকারী। পিতৃহন্তারক অজাতশত্রু এই নাটকে কেবলই রাজা। নাটকের শুরুতে ভিক্ষু উপালী শ্রীমতীকে ‘তুমি ভাগ্যবতী’ বলে আশীর্বাদ করলেন। এতে শ্রীমতীর মনে আত্মত্যাগের উদ্বোধন ঘটে। তার মনে গান:
নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি, কী জানি।নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে-কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি।সে-কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে-কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
“আর নয়, আর নয়।”সে-কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, “চলো দূরে,”
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।
এভাবে গানে গানে সে আত্মনিবেদনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। একসময় বুদ্ধের পূজাবেদীর সামনে শ্রীমতীর নাচের আদেশ আসে। সবাই ভাবে শ্রীমতীর আর উদ্ধার নেই। কিন্তু শ্রীমতী জানে বুদ্ধই একমাত্র ত্রাতা। তাই সে আসরে নামে। নাচে। গায়:
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্র হারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।
রত্নাবলী বুঝতে পারে না এ কেমন নাচ। গানের অর্থও সে বোঝে না। লোকেশ্বরী বাধা না দিয়ে নাচতে সাহস জোগায়। শ্রীমতী নাচে-গায়:
এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।
রত্নাবলী বলে, ‘এ কী হচ্ছে? গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ওই স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে! ওই গেল কঙ্কণ, ওই গেল কেয়ূর, ওই গেল হার! মহারানী, দেখছেন এ সমস্ত রাজবাড়ির অলংকার-এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলংকার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনই।’ লোকেশ্বরী তাকে শান্ত হতে বলে। আনন্দে তারও শরীর দুলে ওঠে। নিজের গলার হার সেও খুলে ফেলে। শ্রীমতীর নাচতে থাকে:
আমি কানন হতে তুলিনি ফুল,
মেলেনি মোরে ফল।
কলস মম শূন্যসম
ভরিনি তীর্থজল।আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা-ধরা,
তোমার চরণে হ’ক তা সারা,
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।
শ্রীমতী একে একে নটীর বেশ খুলে ফেলে। ভেতরে তার ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। তাই দেখে সকলে শংকিত হয়। পূজার ফল তো মৃত্যুদ-। রত্নাবলী স্মরণ করিয়ে দিতে চায়, ‘একেই কি পূজা বলে না? রক্ষিণী, তোমরা দেখছ। মহারাজ কী দণ্ড বিধান করেছেন মনে নেই?’
রক্ষিণী। শ্রীমতী তো পূজার মন্ত্র পড়েনি।
শ্রীমতী। (জানু পাতিয়া) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি-
রক্ষিণী। (শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া) থাম্ থাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্।
রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।
শ্রীমতী। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি-
কিংকরীগণ। সর্বনাশ করিসনে শ্রীমতী, থাম্ থাম্।
রক্ষিণী। যাসনে মরণের মুখে উন্মত্তা।
দ্বিতীয় রক্ষিণী। আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।
কিংকরীগণ। চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা।
(পলায়ন)রত্নবলী। রাজার আদেশ পালন করো।
শ্রীমতী। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।
লোকেশ্বরী। (জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে)বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিতেই সে আসনের ওপর পড়িয়া গেল। “ক্ষমা করো ক্ষমা করো’, বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধুলা লইল।
লোকেশ্বরী। (শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া) নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।(রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল)
তখন রত্নাবলী ব্যতীত সকলে উচ্চারণ করে:
সংঘং সরণং গচ্ছামি।
নত্থি মে সরণং অঞ ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।
তার পর রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান ঘটলে রত্নাবলী শ্রীমতীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে উচ্চারণ করে:
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।
এভাবে নটী শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের ত্যাগের বাণী প্রচারিত হয়। একদিনের একটি ঘটনাকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটি রচনা করেন। এটি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য রচিত হয়।

চণ্ডালিকা (১৯৩৩) ও নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮)
শার্দূল-কর্ণাবদনের কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই নাটকটি পরে নৃত্যনাট্যরূপে পরিবর্তিত হয়। নাটকের কাহিনিউৎস সম্পর্কে শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন:
‘গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।
ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দমঠে ফিরে এলেন।’
এটি মূলত জাতিভেদবিরোধী বক্তব্য প্রকাশের জন্য রচিত। হিন্দু সমাজের মধ্যে তথাকথিত জাতিভেদের ফলে যে অস্পৃশ্যতার জন্ম, রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিকে যখন তার মা তার অশুচিতা ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চায়, তখন প্রকৃতি বলে:
‘ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের-পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।’
সকল প্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে, চণ্ডাল বলে অপমানের বিরুদ্ধে কবি এখানে প্রকৃতিকে দাঁড় করিয়েছেন। এই সাহস তিনি পেয়েছেন বুদ্ধের সাম্যের বাণী থেকে। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই উচ্চারিত হয় বুদ্ধমন্ত্র:
বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো,
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর ঞানলোচনো
লোকস্স পাপুপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং॥
শ্যামা (১৯৩৯)
‘পরিশোধ’ কবিতা আর ‘শ্যামা’ নাটকের কাহিনিউৎস একই- মহাবস্তু-অবদান। তক্ষশীলার বণিক বজ্রসেনের কাছে দুর্লভ ইন্দ্রমণি হার আছে। এই হার সে কাউকে বেচবে না। সে চায় বিনামূল্যে কাউকে দিতে। সেই যোগ্য লোক খুঁজতে সে বেরিয়ে পড়ে। পৌঁছে বারণাসীতে। কিন্তু রাজার চর পিছু নেয়। বারাণসীতে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে রাত কাটানোর সময় চোর হিসেবে তাকে ধরা হয়। চুরির অপরাধে তাকে বধ্যভূমিতে নেওয়া হয়। পথে দেখা হয় রাজনটীর শ্যামার সঙ্গে। শ্যামা বজ্রসেনের প্রেমে মুগ্ধ হয়। কিন্তু শ্যামার প্রেমে আত্মহারা উত্তীয়। শ্যামার প্রেমের প্রতিদানে উত্তীয় নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়ের বজ্রসেনকে রক্ষা করে। বজ্রসেনকে নিয়ে শ্যামা দেশ ছাড়ে। বজ্রসেন নির্দোষ উত্তীয়র নির্মম হত্যার কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। শ্যামার কাছে উত্তীয়র প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা শুনে বজ্রসেন শ্যামাকে ধিক্কার দেয়। একদিন নৌবিহারের সময় বজ্রসেন শ্যামাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করে। বৌদ্ধ আখ্যান থেকে আরেকটু এগিয়ে রবীন্দ্রনাথ বজ্রসেনকে আরো মানবিক করে তুলেছেন। বজ্রসেনের মনে পাপবোধ জাগিয়ে তুলেছেন। শ্যামাকে ত্যাগ করেও বজ্রসেন আবার পাওয়ার আকাক্সক্ষা করেছেন। ডেকেছে, ‘এসো এসো এসো প্রিয়ে,/ মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।’ তার ডাক শুনে শ্যামা এসেছে। এসে বলেছে:
এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না গেল না কেন কঠিন পরান মম-
তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষমো মোরে।
কিন্তু শ্যমাকে কাছে পেয়েও বজ্রসেন শ্যামাকে আবার ধিক্কার দেয়। বলে, ‘কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে।/ যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।’ বজসেনকে প্রণাম করে শ্যামা তখন চলে যায়। কিন্তু বজ্রসেন তখন আবার বিচলিত হয়। বলে:
ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা-
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু॥’
শেষতক বজ্রসেন ভগবান বুদ্ধেরই শরণ নেয়। তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই যবনিকা ঘটে ‘শ্যামা’ নাটকের।


