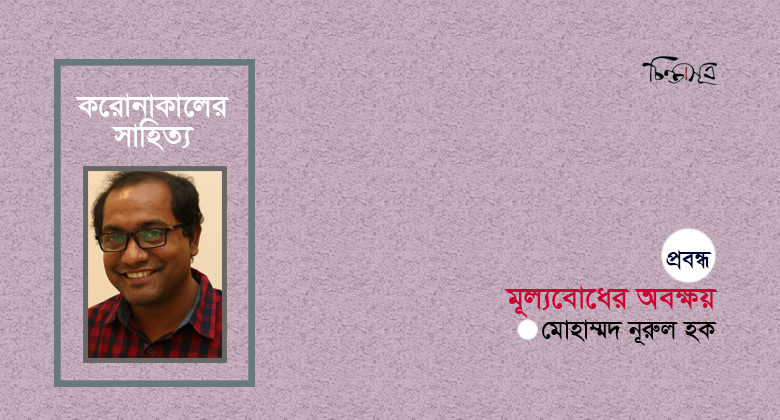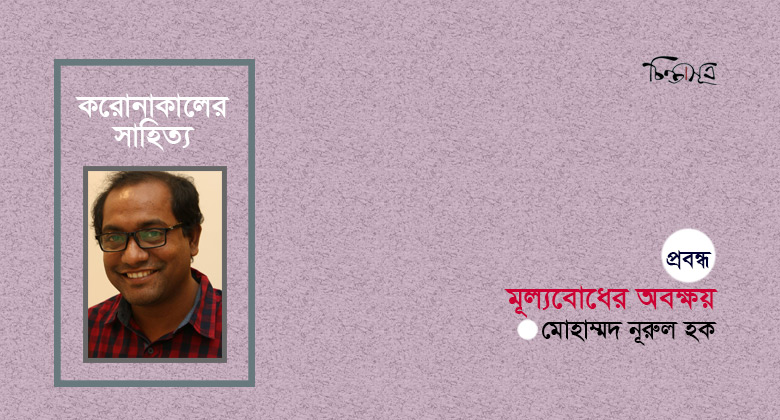 জাতি হিসেবে বাঙালির নৈতিক মান সুদৃঢ় নয়—এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। এরআগে, বলে নেওয়া ভালো, বাঙালি এক আধবার ফোঁস করে জ্বলে ওঠে সত্য। তবে সেটা ষোলোআনা বুঝে-শুনে-জেনে নয়। তাদের ঘুমন্ত দশা থেকে জাগানোর জন্য এক-দুজন দূত কিংবা বংশীবাদকের প্রয়োজন হয়। না হলে তারা যেমনটি চলছিল, তেমনটিতেই স্বস্তি বোধ করে। তারা মেনেই নেয়, দাসত্বের শৃঙ্খল। কবে কোন যুগে একজন নেতাজী সুভাষ বসু, একজন কাজী নজরুল ইসলাম তাদের আত্ম-সম্মানকে একটু জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন, সে যাত্রা তারা একটু খানি নড়েচড়ে বসেছিল, বাকিজীবন স্মৃতিরোমন্থন করে যাবে। এরই ধারাবাহিকতা বাঙালির মহত্তম অর্জন মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। একজন সমুদ্রহৃদয়-সিংহপুরুষ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতিকে না জাগালে আজও হয়তো তারা পাকিস্তানিদের শোষণকেই শাসন বলে স্বীকার করে নিতো। হাজারও নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেও ওরই নাম দিত সুশাসন।
জাতি হিসেবে বাঙালির নৈতিক মান সুদৃঢ় নয়—এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। এরআগে, বলে নেওয়া ভালো, বাঙালি এক আধবার ফোঁস করে জ্বলে ওঠে সত্য। তবে সেটা ষোলোআনা বুঝে-শুনে-জেনে নয়। তাদের ঘুমন্ত দশা থেকে জাগানোর জন্য এক-দুজন দূত কিংবা বংশীবাদকের প্রয়োজন হয়। না হলে তারা যেমনটি চলছিল, তেমনটিতেই স্বস্তি বোধ করে। তারা মেনেই নেয়, দাসত্বের শৃঙ্খল। কবে কোন যুগে একজন নেতাজী সুভাষ বসু, একজন কাজী নজরুল ইসলাম তাদের আত্ম-সম্মানকে একটু জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন, সে যাত্রা তারা একটু খানি নড়েচড়ে বসেছিল, বাকিজীবন স্মৃতিরোমন্থন করে যাবে। এরই ধারাবাহিকতা বাঙালির মহত্তম অর্জন মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। একজন সমুদ্রহৃদয়-সিংহপুরুষ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ জাতিকে না জাগালে আজও হয়তো তারা পাকিস্তানিদের শোষণকেই শাসন বলে স্বীকার করে নিতো। হাজারও নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেও ওরই নাম দিত সুশাসন।
সময় বদলেছে। রুচিরও খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আজ এই অভিযোগ করলে, খিটখিটে মেজাজের বাঙালি তেড়ে আসবে বাঁশের কঞ্চি নিয়ে। ভেবে দেখবে না, সে যার দিকে ওই মামুলি-ভঙ্গুর বাঁশের কঞ্চি নিয়ে তেড়ে আসছে, সে-ই প্রতিপক্ষের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে। বাঁশের কঞ্চি রূপকথা-উপকথায় মোক্ষম অস্ত্র হতে পারে, আজকের যুগের মারণাস্ত্রের কাছে নস্যির যোগ্যও নয়।
কথাগুলো বলছিলাম, মূলবোধের অবক্ষয় প্রসঙ্গে। আমাদের সমাজবেত্তাদের কারও কারও অভিযোগ, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য আকাশ সংস্কৃতি দায়ী। অভিযোগের ভিত্তি খুব দৃঢ় না হলেও সত্য। কিন্তু ওই সত্যটুকু আপেক্ষিক। প্রতিটি বিষয় বা প্রপঞ্চেরই যেমন ইতিবাচক দিক থাকে, তেমনি থাকে নেতিবাচক দিকও। ওই প্রপঞ্চের উপকারিতা বিচার করতে হবে এই গ্রহণ-বর্জনের কৌশলের ওপর। অর্থাৎ ব্যক্তি কী গ্রহণ করবে, কী বর্জন করবে, ওই নীতির ওপরই নির্ভরশীল সমাজের প্রতিটি বিষয়। নাটক বা সিনেমানির্মাতা একটি সমাজকে যেভাবে দেখেন, যেভাবে দেখতে চান, তিনি শিল্পকর্মটি সেভাবে তৈরি করেন। যেভাবে সমাজ গঠনের স্বপ্ন শিল্পী দেখেন, সেভাবে তৈরির জন্য, ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোও তিনি চিত্রায়িত করেন। এখন বিবেচনা করতে হবে, কোনটা গ্রহণ করা হবে, কোনটা বর্জন করা হবে। যেমন সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবির হীরক রাজা যখন যে নিয়ম চালু করেন, তা মানতে রাজ্যের সবাইকে বাধ্যও করেন। যারা অমান্য করবে, তাদের সবাইকে যন্তরমন্তর ঘরে নিয়ে মগজ ধোলায় করে ছেড়ে দেওয়া হবে। এটা একটা প্রথাগত নিয়ম। অর্থাৎ রাজা বা শাসক যা চাইবেন, তার জন্য কিছু নিয়ম করবেন। সে নিয়ম অনুসারে তিনি শাসন কাজও চালাবেন।
আর সময়-রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে একদা-এক রাজার রাজ্যে বলেই। অর্থাৎ নিপীড়িত জনতাও প্রকাশ্যে ও সোজাসুজি অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদ করতে ভয় পেয়েছে। তাই যখনই কোনো দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চেয়েছে, তখনই গল্প-কল্পকাহিনীর অবতারণা করেছে।
শিল্পীকে, সচেতন সমাজকে দেখতে হবে, ওই নিয়ম কী করে রোধ করা যায়। ‘হীরক রাজার দেশে’ টোলের পণ্ডিত আর গোপী গাইন, বাঘা বাইন দেখিয়েছেন, হীরক রাজার অর্থে-স্বার্থে তৈরি যন্তমন্তর ঘরে হীরক রাজারও মগজ ধোলায় সম্ভব। এ দৃষ্টান্ত থেকে এটা পরিস্কার হলো-যত পরাক্রমশালী শাসকই হোক না কেন, জনতার একটি বিশেষ অংশ এবং বাস্তবতা উপলব্ধি করতে জানেন, এমন কিছু ব্যক্তিত্বের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ওই পরাক্রমশালীর দোর্দণ্ড প্রতাপশালীর দম্ভও মুহূর্তে ভেঙে চুর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া যায়।
আবার ঋত্বিক ঘটকের ‘যুক্তি তক্ক আর গল্প’ ছবিতে দেখানো হয়েছে, শিক্ষিত-অর্ধপাগল বুদ্ধিজীবী নীলকণ্ঠ। মধ্যবয়সে স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। সে সংসারের প্রতি উদাসীন। সারাক্ষণ মদে আসক্ত। কিন্তু আশ্রয়ের সন্ধানে ফেরা আরও দুই তরুণ-তরুণী এবং এক সমবয়সীর দায়ভারও নিজের কাঁধে তুলে নেয়। নিজেই বাউণ্ডুলে, কিন্তু সমাজকে দিতে চায় নৈতিক শিক্ষা। দেশপ্রেম তার অকৃত্রিম। কিন্তু দেশের জন্য কী করতে হবে, এ বিষয়ে নেই কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। দেশ-সমাজ দূরের কথা, নিজের সংসার টিকিয়ে রাখার মতো প্রস্তুতি, মানসিক শক্তিও তার নেই। সে নীলকণ্ঠই আবার প্রকাশ্যেই নকশালপন্থীদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে।
এ দুটি ছবির প্রসঙ্গ টানার একটিই উদ্দেশ্য, সমাজে পচন ধরেছে বহু আগে। মানুষ যা বিশ্বাস করে, তা কাজে পরিণত করে না। আর যেকাজগুলো সে করে, তার সব সে প্রকাশ্যে স্বীকার করে না। সর্বত্রই তার ভণ্ডামি। প্রাচীন পণ্ডিতরাও জানতেন ধনার্জনের চেয়ে জ্ঞানার্জনই শ্রেয়। কিন্তু তারা প্রবাদ প্রচার করলেন, জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ধনার্জন শ্রেয়। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ যা কিছু অর্জনের রয়েছে, সবই থাকবে সমাজপতিদের কব্জায়। পতিতজনে ধন-সম্পদ দিয়ে কী করবে, তাই সে জ্ঞানার্জন করবে। আর ওই ঠুনকো জ্ঞানের গরিমায় ধনীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করবে।
টোলে-পাঠশালায়-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে, ‘ধনার্জনের চেয়ে জ্ঞানার্জন শ্রেয়’। মজার ব্যাপার হলো, এই শিক্ষা পুঁজিপতিদের সন্তানরাও প্রথমে, শৈশবে গ্রহণ করে সত্য। কিন্তু দরিদ্রের সন্তান যেমন সবধরনের গুরুবাক্য শিরোধার্য মানে, পুজিপতির সন্তানরা সেভাবে মানে না। তারা প্রতিটি লেসন, বাসায়, বাড়িতে ফিরে বাবা-কাকা-দাদার সঙ্গে শেয়ার করে। তখন বাবা-কাকা-দাদারা তাদের ভুল ধরিয়ে দেন। বলেন, পণ্ডিতের কাজ পণ্ডিত করেছে। পণ্ডিত যা শিখেছে, যা বিশ্বাস করেছে, তাই তোমাকে লেসন দিয়েছে। তুমি ওসব বিশ্বাস করতে যেও না। আবার ভুল করেও তুমি পণ্ডিতের ভুল ধরিয়ে দিও না, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। সাধারণ মানুষ, গরিব, হতদরিদ্ররা, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা সচেতন হয়ে উঠবে। তখন আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে টানাটানি করবে। অতএব শিক্ষাগুরু তোমাকে যা শেখাবে, তুমি তা শেখার ভান করবে, কিন্তু মানবে না। একারণেই একই প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার্জন করার পরও কৃষকের সন্তান মামা-কাকা ধরে বড় জোর কেরানির চাকরিটা পায়, আর পুঁজিপতির সন্তানরা শিল্পকারখানার চেয়ারম্যান-এমডি-ডিরেক্টর হয়। পৃথিবীতে মিথ্যার কী যে কদর, ভাবতেই অবাক লাগে। মিথ্যাবাদীরা যুগে যুগে মানুষকে শিখিয়েছে-ধনার্জনের চেয়ে জ্ঞানার্জন শ্রেয়। কথাটা যে কত বড় ভাঁওতাবাজি, যুগেযুগে জ্ঞানী আর ধনীদের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়। একজন ধনী লোক ইচ্ছা করলে, শতশত জ্ঞানীর মাথা কিনতে পারেন, পারেন তাদের দাস বানিয়ে রাখতে। জ্ঞানীদের দিয়ে নিজেদেও প্রশস্তিও রচনা করাতে পারেন ধনীরা। কিন্তু সহস্র জ্ঞানী মিলিত হয়েও একজন ধনীকে বশ করতে পারেন না। আসলেই জ্ঞানার্জনের চেয়ে ধনার্জন শ্রেয়। এর বিপরীতে যত তথ্য আছে, সবই মিথ্যা।
বাঙালির স্বভাবের অস্বচ্ছতা সুপ্রাচীন। রূপকথা-উপকথা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো পর্যালোচনা করলে এ বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে। প্রায় একই সময়ে বসে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী, টোলের পণ্ডিতেরা সমাজপতিদের অর্থে স্বার্থে প্রবাদ-প্রবচন রচনায় মগ্ন। অন্যদিকে অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য, রূপকথা রচনা করে নিজেদের ক্ষোভ-প্রতিবাদ প্রকাশ করতো। রূপকথা-উপকথাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মানবচরিত্রগুলো কোনো দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কোনো নীতিকথা বলছে না। করছে না কোনো প্রতিবাদও। মানবচরিত্রগুলো যত নীতিকথা, ন্যায়বোধ-এ সবের ধারণা পায় ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির মতো পশুপাখির কাছে। সেসব গল্পে, উপকথায় কোনো মানুষকে তেমন অত্যাচারী হিসাবে দেখানো হয়নি সহজে। অত্যাচারী হিসাবে দেখানো হয়েছে সাধারণত রাক্ষসখোক্কসদের। আর সময়-রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে একদা-এক রাজার রাজ্যে বলেই। অর্থাৎ নিপীড়িত জনতাও প্রকাশ্যে ও সোজাসুজি অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদ করতে ভয় পেয়েছে। তাই যখনই কোনো দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চেয়েছে, তখনই গল্প-কল্পকাহিনীর অবতারণা করেছে।
যখন এসব চিত্র একজন সদ্য শিক্ষাজীবন পার হয়ে আসা ব্যক্তি দেখে, তখন নিজের পঠন-পাঠনের সঙ্গে বাস্তবতাকে সে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করে। আর তখনই দেখে, তার বিদ্যার্জনের সমস্ত আয়োজন ছিল ভুলে ভরা। সে যা শিখেছে, কিছুই বাস্তব জীবনে কাজে লাগছে না। এখানে মেধার মূল্য নেই, চাকরি পেতে হয় ঘুষ আর মামা-কাকার খুঁটির জোরে।
বর্তমানও বাঙালির স্বচ্ছ নয়। আজকের যুগে বিনয়ের স্থান ভাঁড়ামি আর প্রশংসার স্থান দখল করে নিয়েছে স্তূতি। বিনয়ীকে এখন আনস্মার্ট এবং দৃঢ়চিত্তের সত্যবাদীকে গোঁয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ। এ সমস্যা অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রকট। প্রতিটি মানুষ তার শৈশবে যা শেখে, পরিণত বয়সে সেই বিষয়-আশয় আর অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জগতের কোনো মিল খুঁজে পায় না। ফলে প্রচুর পঠনপাঠন থাকা সত্ত্বেও একেবারে আনপড়া কোনো একজনের সঙ্গে অস্তিত্বের লড়াইয়ে তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়।
শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার টেক্সট ও কন্টেন্টের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের মিল খুব সামান্যই। যেটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তার সিংহভাগই সাংঘর্ষিক। পুথিগত বিদ্যা ও শিক্ষকদের বাতলে দেওয়া পথের সঙ্গে পেশাগত জীবন কিংবা কর্মজীবনে কোনো মিল খুঁজে পায় না আজকের তরুণ। ফলে সে হয়ে পড়ে সমাজের প্রতি, নিজের প্রতি ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীন। শিক্ষকসমাজের প্রতিও।
সততা-সত্যবাদিতা এখন বোকামি হিসেবে গণ্য। সৎ-কর্মনিষ্ঠ-পরিশ্রমী মানুষের মূল্য সমাজে কমে এসেছে। করপোরেট কালচারের নামে এক ধরনের স্নবরি আচরণের প্রকাশ দেখা যায়। যা ব্যক্তিত্ববানকে খাটো আর চাটুকারিতা-মেরুদণ্ডহীনতাকে প্ররোচিত করে। এ কারণে সমাজে সততার মূল্য কমেছে। তরুণরা সততার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। কারণ, সততা, কর্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম ও ব্যক্তিত্ব মানুষকে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বিপরীতে স্নবরি, মিথ্যাচার, চাটুকারিতা যেকোনো মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পক্ষে সাহায্য করে। এ কারণে ছাত্রজীবনে যতই নৈতিকতার পাঠ মানুষ গ্রহণ করুক, পেশাগত জীবনে এসে ওসব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।
পেশাগত জীবনে এসে ব্যক্তি দেখে তার চারপাশি স্তূতি আর মিথ্যাচারের বেসাতি। যে যত চাটুকার-মিথ্যাবাদী, সে তত সফল। এটি সরকারি-আধাসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত-বেসরকারি চাকরি ক্ষেত্রে যতটা সত্য, রাজনৈতিক অঙ্গনেও ততটা। সেখানেও দেখি ভয়ানক মিথ্যাচার-চাটুকারিতা। রাজনীতিবিদরা যখন কোনো মঞ্চে-জনসভায় বক্তৃতা করেন, তখন তারা দলীয় প্রধানের প্রশংসায় রীতিমতো মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয় দেন। তাদের স্তূতির ধরন দেখলে মনে হয়, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসায় মগ্ন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমন একটা স্বভাব গড়ে উঠেছে যে, তাদের বক্তৃতা শুরুই করতে হয়, সকল প্রশংসা দলীয় প্রধানের বলেই। দলীয় প্রধানের ইচ্ছার বাইরে পৃথিবীর একটি পাতাও কোথাও নড়ে না। পৃথিবীতে কোনো শস্য উৎপাদিত হয় না, মায়েরা সন্তান প্রসব করেন না, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে চুমু খায় না। কবিরা ভুলে যায় কবিতার পঙ্ক্তি। পাখিরা গান ভুলে মৃত্যুর প্রহর গোনে। আর দলীয় প্রধানরা যখন ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন সমস্ত পৃথিবী আবার জেগে ওঠে।
এছাড়া আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি থাকে জনকল্যাণের। তারা সভা, সেমিনার, মঞ্চে; এমনকী পারস্পরিক আলোচনার সময়ও জনসেবার কথা বলেন। বাস্তবে, তারা জনকল্যাণের চেয়ে পারিবারিক-আত্মীয় কল্যাণেই ব্যস্ত থাকেন। যখন এসব চিত্র একজন সদ্য শিক্ষাজীবন পার হয়ে আসা ব্যক্তি দেখে, তখন নিজের পঠন-পাঠনের সঙ্গে বাস্তবতাকে সে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করে। আর তখনই দেখে, তার বিদ্যার্জনের সমস্ত আয়োজন ছিল ভুলে ভরা। সে যা শিখেছে, কিছুই বাস্তব জীবনে কাজে লাগছে না। এখানে মেধার মূল্য নেই, চাকরি পেতে হয় ঘুষ আর মামা-কাকার খুঁটির জোরে।
মূলবোধের অবক্ষয় ঠেকাতে চাইলে, প্রথমে সমাজ থেকে মিথ্যাচার দূর করতে হবে, আর এজন্য সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। কিন্তু সে পরিবর্তনটা করবে কে?
বাদ থাকলো, সাহিত্য-সংস্কৃতি। এখানের চিত্র অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে বীভৎস। সাহিত্যিকেরা যা বিশ্বাস করে, তা বলতে চায় না। যা বলে, তা নিজেই বিশ্বাস করে না। তবু মিথ্যাচারে ভরিয়ে তোলে পাতার পর পাতা। তারা অধিকাংশ সময় ব্যয় করে, পরস্পরের স্তূতি কিংবা নিন্দায়। সততার সঙ্গে সমালোচনার সাহস তাদের নেই। এর কারণও স্পষ্ট। সাহিত্যিকেরা বেশির ভাগই সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গেও তারা সম্পৃক্ত। তাদের সাহিত্যকর্ম শিল্পোত্তীর্ণ হোক বা না হোক, তাদের অধীনস্থরাও যদি লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন, তবে নানা প্রসঙ্গে বসের কাজের সপ্রশংস আলোচনা করতে তারা বাধ্য। তাদের প্রশংসা তখন কেবল বসের রচনার বিষয়বস্তুতে আর সীমাবদ্ধ থাকে না। গড়িয়ে পড়ে ব্যক্তিগত, পেশাগত জীবনেও। বসের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে, অধীনস্থদের পেশাগত পদোন্নতি থেকে শুরু বদলি, ইনক্রিমেন্ট প্রভৃতি।
শুরুতে বলেছিলাম, আমাদের সমাজবেত্তাদের কারও কারও অভিযোগ, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য আকাশ সংস্কৃতি দায়ী। কথাটার মধ্যে সত্য তো নেই, বরং উল্টো ‘উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে’ চড়ানোর অপষ্টো আছে। চরাচরের প্রতিটি ঘটনার ভেতর দুই ধরনের বিষয় রয়েছে। একটি ইতিবাচক, অন্যটি নেতিবাচক। ব্যক্তি কোন দিকটা গ্রহণ করবে, এটা নির্ভর করবে তার রুচির ওপর। আকাশ সংস্কৃতি থেকে শিল্পটা গ্রহণ না করে, ক্ষতিকারক দিকগুলো বর্জনের রুচি গড়ে না তুললে, তার দায় আকাশ সংস্কৃতির, না কি সমাজের? মানুষ যখন কোনো ফল খায়, তখন আসলে কী খায়? কমলা বলতে, নিশ্চয় এর কোয়াগুলো, আসলে রসটুকুই, যা থাকে খোসার নিচে, আর লিচু বলতে বিচির ওপরের সাদা রসালো অংশটুকু, যা থাকে খোসার নিচে। মানুষ নিশ্চয় কমলা বা লিচুর নামে ফলটির বিচি কিংবা খোসা খায় না। খাওয়ার সময়েই তারা ঠিক করে নেয়, কী খাবে, আর কী বর্জন করবে। এখন কেউ যদি লিচুর বিচি চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে, বিরসমুখে বলে লিচু মিষ্টি নয়, তেতো, তাকে সমাজ কী বলবে? তার মানসিক সুস্থিরতা নিয়ে কি সমাজ প্রশ্ন তুলবে না? এ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাক্ষ্য নেওয়া যাক। ‘দর্শনের দারিদ্র্য’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘যাঁরা দর্শন চর্চা করেন তাঁদের শ্রেণী-চরিত্রই দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই শ্রেণীর আলস্য ও পরিবর্তনভীরুতাই বড় হয়ে ফুটে আছে দর্শনে। আরোহনের বন্ধুর পথে না-গিয়ে দর্শন যে চলেছে অবরোহণের মসৃণ পথ ধরে তার প্রধান কারণ বোধ করি শ্রমবিমুখতা। দ্বিতীয় কারণ সব সময়ে উপরমুখো তাকানোর অতিপুরাতন সমাজ-সমর্থিত অভ্যাস। যুক্তির দারিদ্র্য ঢাকার চেষ্টা হয় কাব্যের পোশাক গায়ে চড়িয়ে। আর পরাধীনতার দীর্ঘ ঐতিহ্য। ওপরওয়ালাই সব করেন এবং করবেন, মারবেন কিম্বা রাখবেন। ওপরে আছেন কর্তা, তারো ওপরে আরো বড় কর্তা, তারা বলবেন তাই গ্রাহ্য। এই পরিবর্তনশীলতা মানুষকে দার্শনিক করে না, কর্তাভাজা করে।’
সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য কোনো সংস্কৃতি বা তরুণ সম্প্রদায় দায়ী নয়। দায়ী মূলত পচে যাওয়া, পুরনো ধ্যান-ধারণার শিক্ষাপদ্ধতি, সমাজপতি, পুঁজিপতি এবং অতি অবশ্যই পুঁজিপতিদের অর্থে-স্বার্থে লালিত-পালিত একশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ। যারা কেবল অর্থের বিনিময়ে পুঁজির অনুকূলে নীতিবোধ তৈরি করে প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। মূলবোধের অবক্ষয় ঠেকাতে চাইলে, প্রথমে সমাজ থেকে মিথ্যাচার দূর করতে হবে, আর এজন্য সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। কিন্তু সে পরিবর্তনটা করবে কে?