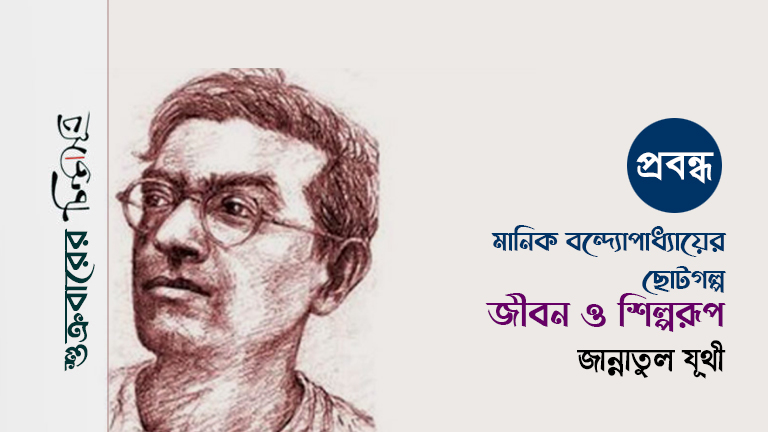মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক জীবনশিল্পীর নাম। জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-নিষ্ঠুরতা, আদিমতা, জৈব তাৎপর্য গল্পে স্থান দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকের মতো প্রতিনিয়ত জীবনের অনুসন্ধান করেছেন। এ কারণেই তিনি বাংলার বাস্তববাদী কথাশিল্পী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অসাধারণ শব্দ চয়ন, ভাষার প্রয়োগ, গল্পের অটুট বন্ধন রক্ষিত হয়েছে বিশেষভাবে। যেমন মানুষের লিবিডো চেতনার কথা বলেছেন তেমনই সমাজের মানুষের লড়াই, দুঃখ- যাতনা নিয়েও কথা বলেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের কাহিনিতে ভিন্ন মেজাজ এনেছেন। যা আগে কেউই তাঁদের গল্পে তুলে ধরেননি। আর এ কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জগতে একক অধিশ্বর। সাহিত্যের জগতে কালজয়ী এই লেখক চির অমলিন হয়ে থাকবেন।
প্রাগৈতিহাসিক গল্পগ্রন্থটি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম গল্প প্রাগৈতিহাসিক। নামগল্পটির প্রধান চরিত্র ভিখু ও পাঁচী। এছাড়া এই গল্পে স্থান পেয়েছে আরও কিছু পার্শ্বচরিত্র। পেহ্লাদ, ভরত, বসির, বিন্নু মাঝি, বৈকুণ্ঠ সাহা।
গল্পের সূচনা হয়েছে আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুন্ঠ সাহার গদিতে ভিখুর ডাকাতির দৃশ্য দিয়ে। এগারো জনের একটি ডাকাত দলের মধ্যে একমাত্র ভিখুরই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা লাগলেও সে পালাতে পেরেছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরে মাথা-ভাঙা পুলের নিচে পৌঁছে অর্ধেক শরীর কাদায় ডুবিয়ে শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকিয়ে থাকলেও রাতে আরও নয় ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে উপস্থিত হয় তার পরিচিত পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ি চিতলপুরে। কিন্তু পুলিশের তৎপরতা লক্ষ করে পেহ্লাদ তাকে মাইল পাঁচেক উত্তরে বনের মধ্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। একদিকে কাঁধের জখম, অন্যদিকে বনের মধ্যে জীব-জন্তুর উৎপাত তবু প্রাণ রক্ষার্থে ভিখুকে কিছুদিন গা ঢাকা দিতেই হয়। বনের মধ্যে ভিখুর অসহয়নীয় জীবনের কথা উঠে এসেছে গল্পে। দিনে দিনে তার কাঁধের ব্যথা অসহনীয় হয়ে আসে। কিন্তু হঠাৎ কয়েকদিন পেহ্লাদের খবর মেলে না। কুটুমবাড়ির বিবাহোৎসব থেকে ফিরে পেহ্লদের ভিখুর কথা মনে হয়। তখন ভিখুর শরীরের বেগতিক অবস্থা দেখে পেহ্লাদ তার বোন জামাই ভরতকে সঙ্গে নিয়ে ভিখুকে তার বাড়িতে স্থান দেয়। এমনই শক্ত প্রাণ যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পেয়েই ভিখু একমাসের মধ্যেই মুমূর্ষু অবস্থা কাটিয়ে ওঠে। কিন্তু কাঁধের জখমের জন্য ডান হাতটি তার আর ভালো হলো না। গাছের মরা ডালের মতোই অকমণ্য হয়ে পড়ে রইলো। হাতের কারণে ভিখুর শরীরের জোর কিছুটা কমলেও মনে কামনার রস একটুও কমেনি। তাই যেই পেহ্লাদ তাকে আশ্রয় দেয় তার বউয়ের ওপরই ভিখুর চোখ আঁটকে যায়। গল্পে লেখক দৃশ্যটার বর্ণনা তুলে ধরেছেন এভাবে, `কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্দীর মেয়ে দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।’১
সেইরাতে ভিখু এবং পেহ্লাদের মধ্যে বেশ হাতাহাতি ও গালাগালি হয়ে গেলো। এবং ভিখু পেহ্লাদের বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু দুপুররাতে হঠাৎ পেহ্লাদের ঘর জ্বলে ওঠে এবং বাগ্দীপাড়ায় বিষম হইচই শুরু হয়। পেহ্লাদ সব বুঝতে পারলেও পুলিশের কাছে ধরা খাওয়ার ভয়ে ভিখুর নামও মুখে আনলো না। এ পর্যায়ে গল্পে আসে নতুন মোড়। চিতলপুরের গ্রামের পাশে নদীতে জেলেডিঙ্গি চুরি করে নদীর স্রোতে ভেসে ভোর ভোর মহাকুমা শহরের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ায় ভিখু। এখনেই গড়ে ওঠে তার নতুন বাস। গাছের মতো মরা ডান হাতটি দেখিয়ে সে ভিক্ষা করতে শুরু করে। মাসিক আট আনায় বিন্নু মাঝির বাড়ির পাশে ভাঙা চালাটা ভাড়া নেয়। সুখেই দিন কাটছিল ভিখুর কিন্তু বিন্নু মাঝির সুখী পরিবার দেখে ভিখুর মনে আদিম কামনার জন্ম হয়। তার স্মৃতিরোমন্থনের সুখস্বপ্ন অন্তরের পীড়া বৃদ্ধি করে। নারী সঙ্গীহীন জীবন ভিখুর কাছে নিরস লাগতে শুরু করে। গল্পে পাই,
নারী-সঙ্গীহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে। তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কী আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পালাইয়া বেড়াইয়া আর বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল।২
বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলা দায়ের কোপে দুভাগ করে দিয়ে আসছে যেই ভিখু আজ তাকে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইতে হয়। কেউ কেউ ভিক্ষা না দিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে যায়। তবু ভিখুকে শুধু অসাড় হাতটার জন্য সব সহ্য করতে হয়। কিন্তু সব সহ্য হলেও নারী সঙ্গীহীন জীবন ভিখুর জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। কিন্তু সামান্য ভিক্ষার টাকায় তার কাছে কেউই থাকতে রাজি হবে না সে নিজেও জানে। তারই পাশে ভিক্ষা করে পাঁচী নামের এক নারী। ভিখুর চেয়েও সে বেশি রোজকার করে। আর এই রোজকার বেশি করার কারণ তার পায়ের ঘা। ওখুধ দিলে ঘায়ের জায়গাটি শুকিয়ে যাবে কিন্তু ভিক্ষা বেশি পাওয়ার জন্য সে এটি আরও বেশি দগদগে করে বের করে রাখে। পাঁচীর প্রতি কিছুটা নজর গেলেও তার পায়ের ঘা-টিকে ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি ভিখু। কিন্তু যখন আরেক ভিক্ষুক বসিরের সঙ্গে পাঁচী থাকতে শুরু করে তখন ভিখুর ইর্ষা হতে শুরু করে। এবং একদিন পাঁচীকে নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বের জেরেই রাতের অন্ধকারে বসিরের কুঁড়ে ঘরে তাকে নির্মমভাবে খুন করে। ঘুমের মধ্যে সরু শিক তার মুখে বিদ্ধ করে। পাশে শায়িত পাঁচী জেগে গিয়ে গোঙাতে শুরু করলে পাঁচীকেও হত্যার হুমকি দেয়। পরবর্তীকালে পাঁচীর সহোযোগিতায় বসির মিঞার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে রাতের অন্ধকারেই তার গ্রাম ত্যাগ করে সদরের উদ্দেশে পা বাড়ায়। পাঁচীর পায়ের ঘা থাকায় তাকে পিঠে ঝুলিয়েই চলতে শুরু করে ভিখু। গল্পের শেষে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে,
ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথে দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।৩
কাহিনির কেন্দ্রে ভিখু। তার জীবনকে কেন্দ্র করেই এ গল্পের গতি-প্রকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিখুর চরিত্রকে লেখক আগাগোড়া এক আবেশে জড়িয়ে দিয়েছেন। যেন লেখকের ভালোবাসা ছেয়ে রেখেছে ভিখু চরিত্রটিকে। কোথাও তার গর্জন কমেনি। এমনকি কাঁধের আঘাতে মুমূর্ষু ভিখু আবার আদিমতম নেশায় জেগে ওঠে। পেহ্লাদের বউকে কাছে পেতে চায়। কিন্তু সেখান থেকে এসে সে আবারও পাঁচীর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। পায়ের ঘা সারিয়ে তোলার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে যখন বসিরের সঙ্গে থাকতে শুরু করে তখনও যৌন তাড়োনা তাকে সঞ্চারিত করেছে। সে শুধু চেয়েছে নারী সঙ্গ। মনের মতো নাহলেও সামান্য উপার্জনক্ষম ভিখুকে একমাত্র পাঁচীই তৃপ্ত করতে পারে। এখানে ভিখুর ভালোবাসার চেয়ে নারীদেহ কামনায় বেশি তাকে তাড়িত করেছে। কাহিনি ও গল্পের প্লট নির্মাণেও লেখক থেকেছেন নির্মোহ। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুরই বর্ণনা দিয়েছেন। দুটি প্রধান চরিত্রের সন্নিবেশে এত চমকপ্রদ গল্প উপহার দেওয়া একমাত্র জীবনশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। কল্লোলীয়দের অবাধ যৌনতার ভাবনা ও প্রভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হয়তো এ গল্পে খানিক ছুঁতে পেরেছে। যদিও জীবনের সত্য রূপকেই তিনি সর্বদা ধরতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,
প্রাগৈতিহাসিক- এ ডাকাত ভিখুর ক্রম- পরিণাম নির্ভুল বাস্তবতা এবং অসামান্য বলিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। ভিখুর কাহিনি যতই বীভৎস হোক- চরিত্রটির প্রতি লেখকের একটি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আগাগোড়াই অনুভব করা যায়। তাই দুর্দান্ত ডাকাতের ডান হাতটা বল্লমের ঘায়ে মরা ডালের মতো শুকিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সে অপরাজিত।৪
প্রাগৈতিহাসিক গল্পের আদ্যোপান্ত পাঠে মানবের আদিমতম কামনা, বৃত্তি, যৌনতা, ক্ষুধাতৃষ্ণার রূপ ফুটে উঠেছে। ভিখু এবং পাঁচীর পরস্পর সামনের দিকে চলার ইঙ্গিতে লেখক প্রাগৈতিহাসিক জীবনের ছাপ এঁকে দিয়েছেন। যার মধ্যে দিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে কালের পর কাল তাদের সন্তানের মধ্যেও এই তাড়না রেখে যাবে। আদিমতম বৃত্তিই প্রাগৈতিহাসিক। পোশাক পরা মেকি সভ্যতার আড়ালে মানবের মনে বয়ে চলা আদিমতম বৃত্তি ভিখু, পাঁচী, বসির মিঞা, বিন্নু মাঝি সবাইকে তাড়িত করেছে।
‘গল্পের নামের তাৎপর্য স্পষ্ট এবং লেখক শেখুম অনুচ্ছেদে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভিখু চরিত্রই নামের সঙ্গে জড়িত। ভিখু যেন গল্পের প্রাগৈতিহাসিক এক মানুষ। তার আদিম জৈববৃত্তি, তার হিংসা, জিঘাংসা বৃত্তি, তার লোভ-লালসা, ঈর্ষা, যৌন – ভাবনা সবই চরমতম, প্রধান অর্থে যেনবা দুই মেরুস্থিত। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতোই ভিখুর যাবতীয় তৎপরতা গল্পে নিহিত।৫
আতসীমামী ও অনন্যা গল্পগ্রন্থে ‘আত্মহত্যার অধিকার’ গল্পটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি ১৯৩৫ সালের আগস্টে প্রকাশিত হয়। এই গল্পের প্রধান চরিত্র নীলমণি। আরও স্থান পেয়েছে নীলমণির স্ত্রী নিভা, মেয়ে শ্যামা, ছেলে নিমু, নিভার কোলের ছেলে খোকা, সরকার বাড়ির বড় ছেলে, তার অসুস্থ পিসেমশাই এবং শ্যামার কুকুর ভুলু। গল্পটিতে দরিদ্র, হতভাগ্য, দুর্দশাপীড়িত নিম্নবিত্তের এক রাত্রির করুণ জীবন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সামর্থ্যহীন নীলমণির পরিবারের ঝড়ের রাতে মাথা গোঁজার সামান্য আশ্রয়টুকুও ছিল না। ঘরের পুরোনো চাল যথাসময়ে সংস্কার করার অর্থনৈতিক অক্ষমতা ফুটে উঠেছে এ গল্পে। সেইসঙ্গে অসহায়, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের অসহনীয় জীবনের আড়ালে আত্মমর্যাদা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।
প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে সারাদিন কষ্টে কাটালেও রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির উপদ্রবে ঘরে থাকার উপক্রম থাকে না নীলমণির পরিবারের। আর সেই আত্মাভিমান গিয়ে জমা হয় ক্রোধে। স্ত্রী নিভা যখন সরকার বাড়ি গিয়ে ঝড়ের রাতটুকু কাটিয়ে আসার প্রস্তাব দেয় তখন পাগলা কুত্তার মতো খেঁকিকে ওঠে নীলমণি। তার মনে হতে থাকে স্ত্রী তার অপারগতাকে ব্যঙ্গ করতেই যেন সরকার বাড়ি যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কারণ এর আগেও তাদের সরকার বাড়ি আশ্রয় নেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। তবু কেন নিভার এই অপমান হজম করে আবারও আশ্রয় নেওয়ার বাসনা? এদিকে এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে ঘরে একটুও দাঁড়ানোর মতো জায়গা না থাকলেও ছেলে নিভু বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। সেই ঘুমও যেন নীলমণির কলিজাটাকে দুখণ্ড করে দিচ্ছে। লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে,
মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায়, ঘরের ও কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তার সীমা থাকে না। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের জলস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ার আর কী মানে হয়? এর চেয়ে ও যদি নাকী সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভালো ছিল। এ সহ্য হয় না।৬
নীলমণির অপারগতা যেন বিদ্ধ করে তাকেই। কেনোই বা পরিবারের জন্য দুবেলা দুমুঠো ভাত আর একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই নিশ্চিত করতে পারেনি সে। মনে মনে সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে থাকে। কিন্তু যখন মেয়ে শ্যামার বিকারহীন চেয়ে থাকা, স্ত্রী নিভার ছোট খোকাকে নিয়ে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজার অবিরাম চেষ্টা চোখে পড়ে তখন তার অথর্ব শরীরেও জেগে ওঠে ক্রোধ। শ্যামার কুকুর ভুলুকে যখন নীলমণি মারতে উদ্যোত হয় তখন বাবার লাঠি ধরতেই মেয়ের ওপর চড়াও হয় সে। একসময় শ্যামাকে আঘাত করে। কিন্তু তার জন্য কোন মন খারাপ হয় না। কারণ জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, শোক, মৃত্যু, শোকের অভাব নেই তাদের। সে আত্মগ্লান্তিতে দগ্ধ হতে থাকে আর মনে মনে ভাবে,
সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছে করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুখুলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখ ফিসফিস করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুসমন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তার এই ভাঙা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোনার ওই ভাঙা বাক্সটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝমঝম করিতে থাকে – টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।৭
অবচেতন মনে ভেবে চলা হাজারো চিন্তা এসে ভিড় করলেও ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষা তাদের মেলে না। তাই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একসময় নিজেই যেমন নিভাকে ধমক দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিল ঠিক তেমনই প্রস্তাব করে বসে সরকার বাড়ি রাতটুকু কাটিয়ে আসার। কারণ নীলমণি নিজেও জানে এই রাত তাদের কোনমতেই পার হবে না। ফলে এই রাতেই গায়ে চট জড়িয়ে ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিয়ে সরকারি বাড়ি গিয়ে ওঠে। এক পায়ে ভর করে কাঁদার মধ্যে যতই নীলমণি চলতে চায় ততই তার, হয় পা নয়তো লাঠি আঁটকে যায়। মেয়ের সাহায্যে কোনরকমে পার হয়ে তারা গিয়ে উপস্থিত হয় সরকার বাড়ি। সরকার বাড়ির বড় ছেলের উপেক্ষা মিশ্রিত দাক্ষিণ্য মেলে। তবে যে ঘরে তারা আশ্রয় পায় সেখানে নোংরা চট পেতেই রাতটুকু কোনরকমে কাটিয়ে দিতে চায়। নীলমণির স্বস্তি মেলে সরকার বাড়ির বড় ছেলের পিসেমশাইও সে ঘরেই স্থান পেয়েছে এ কারণে। তবে তিনি রোগে শীর্ণ দেহ নিয়ে এককোণে একটি ছোট্ট চৌকিতে মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। গল্পে পাই, ‘পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল, ‘খুব মোটাসোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের চেহরা এমন হয়? চার বছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটাও কানা, এত লোককে নিচ্ছে, আমায় চোখে দেখতে পায় না।’৮
নীলমণির পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। আর পিসে মশাইয়ের সেটুকু আছে কিন্তু সুখ নেই। এ যেন এক আজব লীলা। সবার দুঃখ-কষ্ট ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু সবাই-ই এক লীলাচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই কোনদিন শেষ হয় না। পিসেমশাই তার অসুস্থ শরীরকে ভালো করার তাগিদে অসংখ্য ডাক্তরের স্মরণাপন্ন হয়েছে। অন্যদিকে নীলমণি তার পরিবারকে মাথা গোঁজার ঠাঁই নিশ্চিত করতে ব্যর্থ। দুই চিত্র যেন একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন লেখক। তবু আত্মহত্যার অধিকার তাদের নেই। তাইতো নীলমণির মনে হয়েছে বেঁচে থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেই নিষ্প্রয়োজনীয়তাই জীবনের জন্য বড় প্রয়োজন হয়ে ওঠে। নিঃসম্বল ক্ষতবিক্ষত মানুষের নিরূপায় হাহাকারের মনোভঙ্গি গল্পের নামকরণে সার্থক হয়ে উঠেছে।
আত্মহত্যার অধিকার গল্পটি সবদিক থেকে চরমভাবে ভেঙে- পড়া, পর্যুদস্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের অসহায়ভাবে বাঁচার কাহিনী, প্রয়োজনের জীবনের অস্তিত্বটুকু কোনরকমে টিকিয়ে রাখার কাহিনী। এর কাহিনী-অংশ সেই পরিবারের গৃহকর্তার আত্মনিগ্রহের চিত্রে বিশিষ্ট।৯
এক বর্ষণমুখর প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের টিকে থাকার লড়াই মানবজীবনের চিরন্তন বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবনে দুঃখ-কষ্ট, জরা আসতেই পারে তবে মানুষের দায়িত্ব তাকে সমাধান করা। বৃদ্ধ পিসেমশাই, নীলমণি, নিভা, শ্যামা সাবাই একটি সুন্দর সকালের প্রতীক্ষায়। ‘… তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মতো শাঁ শাঁ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।’১০
মোট বারোটি গল্প নিয়ে সরীসৃপ গল্পগ্রন্থটি ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থের শেষগল্প সরীসৃপ নামগল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বনমালী, চারু, পরী। এছাড়া গল্পটিতে আরও কিছু চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রামতারণ চারুর শ্বশুর, চারুর ছেলে ভুবন, বনমালীর মা হেমলতা, কনক, পদ্ম ঝি। গল্পটির সূচনা হয়েছে চারুর শ্বশুর রামতারণের প্রকাণ্ড তিন তলা বাড়িকে কেন্দ্র করে। রামতারণ এবং চারুর পাগল স্বামীর মৃত্যুর পর বাড়ি দেখভালের সমস্ত দায় এসে পড়ে চারুর ওপর। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি পাটের দালাল বনমালীর হস্তগত হয়। চারুর যখন বিয়ে হয় তখন তার সতেরো বছর বয়স এবং বনমালীর পনেরো। শ্বশুর রামতারণের অভ্যেস ছিল তার বন্ধু, প্রতিবেশী, মোসাহেব বনমালীর বাবাকে নিয়ে ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে রাত কাটানো ও ফুর্তি করা। তবে যাওয়ার আগে চারুর সতীত্বের ওপর অবিশ্বাস থাকায় তার পাগল পুত্রের বধূ চারুকে পাহারা দেওয়ার জন্য বনমালীকে রেখে যেতো। চারু প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী ফলে শ্বশুরের এই চাতুর্য সে বুঝতে পেরেছিল। বনমালীকে রাতে পাশের ঘরে শুইয়ে পাগল স্বামীর সামনে শোবার ঘরে দরজা খুলে রাখণ। বাবার ভয়ে চারুর স্বামীও বাধা দিত না। স্বামী, শ্বশুরের মৃত্যুর পরে সব সম্পত্তিদেনার দায়ে বনমালীর হাতে চলে যায়। চারুর নিজের বলতে থাকার মধ্যে আছে এক সন্তান ভুবন। সেও জড়বুদ্ধি। তাকে নিয়ে চারু তাদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িতেই থাকে। যেভাবেই হোক চারু ভুবনের জন্য এই আশ্রয়টুকু ছাড়তে চায় না। তার মৃত্যুর পর বুদ্ধিহীন ছেলেকে কে দেখে রাখবে এই চিন্তায় চারুর দিবানিশি এক হয়। এর মধ্যে হঠাৎ বনমালী, তার মা হেমলতা শহরের বাস উঠিয়ে এই বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করে। সেখানে এসে উপস্থিত হয় চারুর সদ্য বিধবা বোন পরী। কোলের সন্তানকে নিয়ে বোনের কাছে শেষ আশ্রয়টুকু চায়। যদিও চারু তাতে আপত্তি জানায় কারণ তার আর সেই অবস্থা নেই। নিজের জড়বুদ্ধি ছেলেটির মাথার ছাঁদ চলে যাক সেটাও চারু চায়নি। এখানেই আসে গল্পের ক্লাইম্যক্স। চারুর সঙ্গে শুরু হয় বনমালীর সম্পর্ক। গল্পে পাই, ‘বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না। ভাবে, কী মেয়ে বাবা! ও দেখছি সর্বনাশ করে ছাড়বে!’১১
গল্পের নায়ক বনমালী তার দুপাশে দুই প্রধান নারী চরিত্র চারু ও তার ছোট বোন পারু। বাড়িতে আশ্রয়ের জন্য একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই নিশ্চিত করার জন্য দুই বোনই বনমালীর জালে নিজেকে জড়িয়েছে। চারুর প্রৌঢ়ত্বকে উপেক্ষা করে সে ধরা দিয়েছে পরীর কাছে।
চারু ভাবিতে লাগিল, একী মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া লইল যে তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারাজীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে।১২
বনমালী বহুদিন থেকেই চারুকে এ বাড়ি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে। কিন্তু বনমালী যাই বলুক মুখের ওপর সরাসরি কিছু বলতে পারে না এই যা চারুর ভরসা। বহুদিনের প্রচেষ্টায় চারুকে শেখুক তীর্থে পাঠাতে সক্ষম হয় বনমালী। পদ্ম ঝিকে কটা টাকা দিয়ে নিজের জড়বুদ্ধি ছেলের দেখার ভারার্পণ করে তীর্থ যায় চারু। সেখানে গিয়ে পরিচয় হয় কনক নামের এক বউয়ের সঙ্গে। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে করে তীর্থে এসে ধরনা দিচ্ছে। কলেরা হয়ে সেখানেই বউটির মৃত্যু হয়। তার কাছে চারুর বাটি ছিলো। মনে মনে বিধাতার কাছে পরীর মৃত্যু কামনা করে। যাতে বউটির মতো পরীরও কলেরায় মৃত্যু হয় সেলক্ষে বউটির কাছে থাকা বাটির একদানা ভাত এনে পরীকে খাওয়ায়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কলেরায় চারুরই মৃত্যু ঘটে। বোনের মৃত্যুর পর পরীর জীবনও থমকে পড়ে। চারুর মৃত্যুর পর হঠাৎ ভুবনের ওপর বনমালীর ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে দেখে পরীর ঈর্ষা শুরু হতে থাকে। তাই সে জড়বুদ্ধি বোনের ছেলেকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসে। গল্পে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,
দরাজহাতে অনেকগুলি নোট কাউন্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল। যা যা বলেছি মনে আছে, ভুবন? কাল বিকালে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ি থামবে সেইখানে নেমে যাবি।১৩
পরী ভুবনকে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশে যাত্রা করালেও বনমালীর কাছেও তার রাণীর মতো জায়গা হয়নি। বরং আপদ ভেবে তাকেও ওপর তলার ঘর থেকে ক্ষেন্তি ঝিয়ের ঘরের পাশে থাকতে দেয়। বনমালীর মা যখন ভুবনের খোঁজ নেওয়ার প্রস্তাব করে তখন বনমালী বলে, আপদ গেছে যাক।
সরীসৃপ গল্পে জৈবকামনার হীনতম আত্মকেন্দ্রিক চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। বনমালীর প্রতি দুই বোন চারু এবং পরীর কারোরই মনের আকর্ষণ ছিল না। দুজনেই নিজের এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে ধরা দিতে চেয়েছে। কিন্তু চারু যৌবনে চায়লেই বনমালীকে বশে আনতো পারতো কিন্তু সে তা করেনি। তবে সম্পত্তি হারিয়ে বারাবর বনমালীকেই যেন আপন করে পেতে চেয়েছে। যাতে সন্তানের মাথার ছাঁদ টুকু চলে না যায়। অন্যদিকে বিধবা পরী বনমালীকে তার কচি রূপে আটকে ফেলে। কিন্তু বনমালী শিকারী। সে মাছ শিকারে টোপ কতটুকু ব্যবহার করতে হয় জানে। তাইতো পরী ভোগ করার পর তাকে উচ্ছিষ্টের মতো আশ্রয় দিয়েছে ঝিয়ের পাশের ঘরে। যৌন মনস্তত্ত্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটের মিশ্রণে গল্পটির এক দারুণ রূপদান করেছেন লেখক। সরীসৃপ গল্পে মানব মনের কুৎসিত কদাকর রপের প্রকাশ ঘটেছে। মানুষ অর্থ এবং শরীরের কাছে অসহায়। চারু যৌবনে শরীরকে দূরে রাখতে পারলেও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা দূর করতে বনমালীকে প্রৌঢ় বয়সে এসে নতুনভাবে কাছে টানার আকুতি জেগেছে। সন্তানের মাথার ছাঁদ যেন না যায় সেদিকে যেমন তার আগ্রহ তেমনই পরীকে কাছে ঘেঁষতে দেখে নিজেকে কেন আরও আগে বনমালীর জীবনে সঁপে দেয়নি সে নিয়ে আক্ষেপ দেখা গেছে। আবার পরীর জীবনেও একই চেতনা তাকে গ্রাস করেছে। তবে পরীর অতি লোভাতুর চোখ সবকিছুকে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছে।
বনমালীকে আয়ত্ত করবার জন্যই দুই বিধবা বোন চারু এবং পরীর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার কদর্য -কুটিলতার দ্বিতীয় নিদর্শন আছে কিনা সন্দেহ। সরীসৃপ যেন নরকের কাহিনী। হিংসার যন্ত্রণায় পরীকে কলেরার জীবাণু খাইয়ে চারুর হত্যা চেষ্টা, পরীর স্বার্থপরতা ও নির্লজ্জ লালসা-অন্তর্জ্বলায় নিজের সন্তানের গলা টিপে ধরা, অবিশ্বাস্য মিথ্যার বেসাতি, চারুর ছেলেকে নিশ্চিত মৃত্যুতে পাঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি বনমালীর শয়তান সুলভ নির্বিকল্প কঠিনতা, বোধ হয় গল্পের স্রষ্টাকেও পর্যন্ত আতঙ্কিত করে তুলেছিল!১৪
রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, ‘সভ্যতার বাইরের খোলস যত বর্নোজ্জ্বলই হোক না কেন, তার ভিতরের রূপ কত বিকৃত ও অসুস্থ, তিনি তা নির্মমভাবে উদঘাটিত করেছেন।’১৫
সরোজমোহন মিত্র বলেছেন, ‘আমাদের সমাজ ও সভ্যতার কৃত্রিম অন্তরালে কত বিষাক্ত কুটিলতা সরীসৃপের মতো বিরজমান এ গল্পে তা দেখানো হয়েছে।’১৬
বীরেন্দ্র দত্তের মতে, ‘বনমালীর মতো অবিবাহিত মধ্যবয়সী পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই বোনের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যে মনের জগতের উন্মোচন – তা যৌন বিকৃতির পশুসুলভ দিকের পোষকতা করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সভ্য মানুষের মনের গভীর থেকে এসব বৃত্তির যে প্রকাশ হওয়া, তা সভ্যতার নির্মোকে মানব চরিত্রের নিষ্ঠুর বৈপরীত্যকে দেখায়।’১৭
বনমালী সরীসৃপের মতো বিষধর ফণার শিকার দুই বোন। আবার বনমালীকেও শিকারে পরিণত করতে চেয়েছে চারু-পারু। কিন্তু পাটের দালাল বনমালী ধূর্ত এবং স্বার্থবাদী ফলে সে নিজের যতটুকু গ্রহণীয় তার বাইরের অংশ উচ্ছিষ্টের মতো ছুঁড়ে ফেলেছে। এখানে মানব মনের এক অদৃশ্য দিক তুলে ধরেছেন লেখক। সমাজে বনমালীর মতো মানুষের অভাব নেই। যারা নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে চারু, পরীদের ব্যবহার করে। আবার পরীর মতো স্বার্থান্ধ মানুষ এতটাই অন্ধ হয়ে পড়ে যে ন্যূনতম মনুষ্যত্ব খুইয়ে বসে। ভুবনের মতো জড়বুদ্ধি ছেলের প্রতি তার এতটুকু মায়াও প্রকাশিত হয়নি।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বৌ’ গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে মানুষের বিশেষ পেশা, বয়স, স্বভাব, সাংসারিক হতাশা, রোগগ্রস্ততা, বিকলাঙ্গ স্বভাবÑএসবকে ভিত্তি করে মোট ১৩টি গল্প সংকলিত হয়। ‘কুষ্ঠ-রোগীর বৌ’ এই গল্পগ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প। মাত্র ২টি চরিত্রের সমন্বয়ে গল্পটির অনবদ্য রূপ দিয়েছেন লেখক। যতীন ও মহাশ্বেতা স্বামী-স্ত্রী। যতীনের বাবার অঢেল সম্পত্তি। তবে সেই সম্পত্তি গড়ে উঠেছে অসৎ উপায়ে। এই বিষয়টিকে যতীনের বাবা দেখেছেন এভাবে,
কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ করো। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাংকে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে। ধনী হওয়ার এ ছড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।১৮
সুতরাং যতীনের বাবা অনন্যোপায় হয়েই মানুষের সর্বনাশ করে কিছু টাকা জমিয়েছিল। জীবনের আনাচে-কানাচে যতীনের বাবার প্রতি যে অভিশাপ জমা হয়েছিল সেটাই যতীনের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। বাবার টাকাগুলো ভালো করে ভোগ করার আগেই মাত্র আঠাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আর্বিভাব হয়। স্ত্রী মহেশ্বেতা স্বামীর আঙুলে কী হয়েছে বুঝতে পারে না প্রথম পর্যায়ে।
যতীনের হাত নেড়ে চেড়ে আঙ্গুল চুম্বন করতে গিয়ে যতীনের প্রতি তার ভালোবাসার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। সে বলে, তুমি সুন্দর বলেই তো আমার ধাঁধা লাগে! তোমাকে ভালোবাসি, না, তোমার চেহারাকে ভালোবাসি বুঝতে পারি না। শুধু কি তাই গো? হুঁ, তবে আর ভাবনা কী ছিল! দিনরাত কীরকম ভাবনায় – ভাবনায় থাকি তোমার হলে টের পেতে। ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে!১৯
যতীনের কুষ্ঠরোগ দিনে দিনে প্রকাশিত হলো। ডাক্তার এর কোনো উপায়ন্তর করতে পারে না। বাড়ির সদর থেকে অন্দরে একটি ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যতীন। একমাত্র মহেশ্বতা ছাড়া আর কারোর সেই ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ষোল টাকা ভিজিটের ডাক্তার, বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার সবাই মূলত রোগীর কুষ্ঠ রোগের প্রতি ইঙ্গিত করে। একশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার তাকে ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাঁচতে একঘরে রাখার পরামর্শ দেয়। তবে সে পরামর্শ মহাশ্বেতা কতটা মানবে সে বিষয়ে ডাক্তার সন্দিহান! কারণ মহেশ্বতার রোগগ্রস্ত সন্তানের ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটেছে। পূর্বেই সন্তানের মৃত্যু এবং স্বামীর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে যতীনের কাছ থেকে মহাশ্বেতার দূরে সরে আসা। কুষ্ঠরোগ, সন্তানহারা পিতার সন্দেহপরায়ণ মন মহেশ্বেতার নতুন সম্পর্কের প্রতি ঈঙ্গিত দুজনের মাঝে দেওয়াল তুলে দেয়।
জীবন যাপন প্রথার আকস্মিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সীমা না থাকলেও পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বিসর্জন দিলেও মহাশ্বেতাকে সে ছাড়তে পারে না। তার মনে হতে থাকে জীবনটা এতকাল ভাগাভাগি করে এসেছে তারা। আজ যদি কদর্য রোগটাও মহাশ্বেতা গ্রহণ করতো তার কিছু বলার থাকতো না। স্ত্রীকে সবসময় কাছে ডাকে। কাছে রাখতে চেষ্টা করে। মহাশ্বেতা তাকে গল্প পড়ে শোনাক, কথা বলুক, পাশাপাশি বসে গান শুনুক সবসময় তাকে ঘিরে থাকুক যতীনের বাসনা এমন হলেও মহাশ্বেতা আগেই মন থেকে মরে গিয়েছিল। রোগগ্রস্ত সন্তানের মৃত্যুর অপবাদ মহাশ্বেতাকে যতীনের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সেখানে নতুন করে যুক্ত হয়েছে কুষ্ঠরোগ। যতীন মহাশ্বেতার দূরে সরে যাওয়ার যত আভাস পায় ততই তার ওপর চড়াও হতে থাকে। স্বামীর সন্দেহ যখন তুঙ্গে, বিকৃত হতে থাকে তখন মহেশ্বেতা হয়ে পড়ে যন্ত্রের মতো।
আর ঈশ্বরবিমুখ যতীন একসময় দেবতার দর্শনে কামাখ্যায় চলে যায়৷তার অনুপস্থিতিতে মহাশ্বেতাও স্বামীর জন্য কালীঘাটে ভিখারিদের মধ্যে দান-ধ্যানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেখানেই আবিষ্কার করে একাধিক কুষ্ঠরোগীর। পরবর্তী সময়ে একুশ জন কুষ্ঠীরোগীর সেবায় মহেশ্বেতা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। যতীন এ সম্পর্কে জানতে চাইলে সে ঈশ্বর প্রদত্ত বাণীর কথা বলে। এই কুষ্ঠরোগীর সেবার মধ্যেই মিলবে যতীনের মুক্তি। ফলে স্বামীর মাঙ্গালার্থেই যে মহাশ্বেতা কুষ্ঠরোগীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। মহাশ্বেতার প্রপঞ্চনা যতীনের অজনা থেকে যায়। গল্পে পাই, ‘সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালোবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠ রোগাক্রান্তগুলিকে ভালোবাসে।’২০
মার্কসবাদ নির্ভর মানবতাবাদের ধ্যান- ধারণা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের মুক্তি ঘটে সমগ্রতায়। তেমনই এই গল্পে মহাশ্বেতার মুক্তি ঘটেছে আর্তের সেবায়। একদা স্বামীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা, মমত্ব থাকলেও আজ নেই। আজ যতীনের মহশ্বেতাকে বড্ড বেশি প্রয়োজন কিন্তু মহাশ্বেতার মন থেকে সরে গেছে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। যতীনের থেকে পাওয়া অশ্রদ্ধা, সন্দেহই যেন মহাশ্বেতার মনের মাঝে দেওয়াল তুলে দিয়েছে। কুষ্ঠরোগীর বৌ গল্পে মানব মুক্তির দিক প্রকাশিত হয়েছে। সব কষ্ট-দুঃখের অবসান ঘটেছে কুষ্ঠরোগীর সেবার মধ্যে। গল্পে লেখক সমাজে কুষ্ঠরোগীর অবস্থান, দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব কলহের মনস্তাত্ত্বিক রূপ তুলে ধরেছেন। মাত্র দুটি চরিত্রের মনের জটিল টানাপড়েন গল্পটির মাঝে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যুবক স্বামী যতীন এবং তার সুস্থ যুবতী স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপড়েন, জটিলতা, সম্পর্কের বদল এবং উত্তরণে গল্পের প্লট নির্মিত। মানুষের দ্বন্দ্ব – জটিল মনকে আঁকতে চেয়েছেন লেখক। এ সম্পর্কে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন,
কুষ্ঠরোগীর বৌ গল্পের নামেই প্রমাণ হয়ে যায়, গল্পের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও চরিত্র হল মহাশ্বেতা। তার চরিত্রনির্মাণে তার মনোলোকের যে অসামান্য চমৎকারিত্বপূর্ণ বিবর্তনচিত্র লেখক এঁকেছেন, বাংলা ছোটগল্পে এই জাতীয় চরিত্র-কাঠামো দ্বিতীয়রহিত। মহাশ্বেতা আমাদের গভীর বিস্ময় জাগায়। এরকম একটি ইস্পাতকঠিন নারী চরিত্র বাংলা ছোটগল্পের ধারায় নিশ্চিত অমূল্য সংযোজন। গল্পের প্রথম দিকে যতীনের কুষ্ঠ হয়েছে এমন বিশ্বাস যখন এতটুকুও হয়নি, সন্দেহও জাগেনি সে বিষয়ে, তখনকার স্বামীর সামান্য অসুখ ভেবে মহাশ্বেতার যে প্রেমস্বভাব প্রকাশের সারল্য ও রোমান্টিক অন্তরঙ্গ দাম্পত্যের আবেগধর্ম, তা চরিত্রের ব্যক্তিত্বের এক মধুর লাবণ্যকে তুলে ধরে। তার অসুখ সারবার যুক্তি প্রেমিকা স্রীর অকৃত্রিম মনোবাসনার অনুগ।’২১
স্বামীর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়া, ডাক্তারের অপমান, স্বামীর সন্দেহ মহাশ্বেতা ক্রমশ নির্বিকার করে তোলে। কুষ্ঠ এমন এক ব্যাধি যা ছোঁয়াচে জেনেও স্বামীর কাছ থেকে সরে গিয়ে মহাশ্বেতা আরও একুশ কুষ্ঠরোগীর সেবা করেছে। মূলত কুষ্ঠরোগের জন্যই যে মহাশ্বেতা স্বামীর কাছ থেকে সরে গেছে এমন নয় বরং নিজের প্রতি প্রচণ্ড অপমান সহ্য করতে না পারার ফলেই মহাশ্বেতা সরে গেছে। মহেশ্বেতা মরে গেছে অন্যায় অপঘাতে যন্ত্রণা পেয়ে। সেই মরে যাওয়া দৈহিক নয় মানসিক। যার ফলে স্বামীর পাশে থেকে তাকে সুস্থ না করে অপরিচিত একুশ রোগীর আত্মীয় হয়ে উঠেছে। যার দ্বারা সে অপমানের গলারোধ করতে চেয়েছে।
কুষ্ঠরোগীর বৌ গল্পটিতে বিষয় হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃহত্তর মানবতার বাস্তব ভিতরে সার্বজনীন রূপাবয়ব। যে মার্কসবাদে বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরবর্তী আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের দীক্ষা দেয়, উনিশশো চুয়াল্লিশের আগের এই রচনায় তারই যেন ভূমিকা রচিত হতে দেখি। এখানে কোনো তত্ত্ব নেই, মানবতার ভাবনা সৃষ্ট চরিত্রের অভ্যন্তর থেকেই প্রকাশ্য হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু জটিল মনস্তত্ত্বের রূপকার নন, তিনি বাস্তব সত্যে দীপিত জীবনভাগ্যের রূপকার। তাঁর মানব সম্পর্কের ভাবনা মৃত্তিকাপ্রেমে বলিষ্ঠ।২২
গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক বিশেষভাবেই সার্থকতা অর্জন করেছেন। কুষ্ঠরোগী যতীন এবং তার স্ত্রী মহাশ্বেতার দ্বন্দ্ব – জটিল মনের আশ্রয় হয়ে উঠেছে কুষ্ঠরোগীদের সেবা। ফলে দুদিক বিবেচনা করলে গল্পের নামকরণ কুষ্ঠরোগীর বৌ সার্থক। যতীনের কুষ্ঠরোগ তার দেহেই নয় তার মনেও যে মনের বাইরে প্রবেশ করেছে মহাশ্বেতা। তাইতো মানবতার ধর্মেই তার মুক্তি মিলেছে।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদপোড়া’ গল্পগ্রন্থটি ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে মোট দশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। এর প্রথম গল্প ‘হলুদপোড়া’। এই গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন অমলেন্দু দাসগুপ্ত। ১৯৪৫ সালে অনূদিত গ্রন্থটির নাম দেন ‘ইঁৎহঃ ঞবৎসবৎরপ’। এই গল্পটি ভিন্ন ঘরনার। আপাতদৃষ্টিতে এটি ভৌতিক গল্প বা অলৌকিক রসের গল্প মনে হলেও লেখক এখনে ভূত- সংস্কারের বিষয়ে নজর দিয়েছন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কমিউনিস্টে বিশ্বাসী লেখকের হাত থেকে এ ধরনের গল্প পাঠককে খুব চমকিত করে। তবে ভিন্ন ধারার এগল্পে লেখকের একটা ভৌতিক সাসপেন্স কাজ করেছে। প্রতিটি মুহূর্তে একটি চাপা উত্তেজনা পুরো গল্পে। পূর্বসুরীদের অতিপ্রাকৃত গল্পের আমেজ থেকে একেবারেই ভিন্ন এ গল্পটি। সত্যি সত্যি পাঠকও হারিয়ে যায় এক শিহরণের জগতে। হলুদপোড়া গল্পে একটি টানা কাহিনির উপস্থিতি নেই। গল্পের প্রথমেই দেখতে পাই কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে পরে গাঁয়ে দুটো খুন হয়। একজন মাঝবয়সী জেয়ান মদ্দ পুরুষ যার নাম বলাই চক্রবর্তী। অপর জন ষোল- সতের বছরের একটি রোগা মেয়ে নাম শুভ্রা। সে গ্রামের ধীরেনের বোন। বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল। গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিলা সে বিষয়ে গ্রামের সবাই সন্দিহান। আবার এই দুটো খুনের মধ্যে কোন যোগসাজশ আছে কিনা সেটাও কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। গ্রামের মাঝে এই ঘটনা নিয়ে বেশ একটা হইচই ভাব। যে গ্রামে বিশ-ত্রিশ বছরের কেউ জখম পর্যন্ত হয়নি সেখানে হঠাৎ এমন খুনের ঘটনা তাও আবার একটি পুরুষ এবং একটি নারী। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনি মোড় নিয়েছে। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকের মনেও একসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করে দিয়েছেন। যার ফলে কাহিনির মধ্যে ঢুকে পড়তে পাঠকের কোথাও হোঁচট খেতে হয় না।
বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী ভাইপো নবীন চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে স্ত্রী দামিনীকে নিয়ে একেবারে সপরিবারে গ্রামে এসে হাজির হয়। ঠিক একুশ দিনের মাথায় নবীনের স্ত্রী দামিনীর ওপর ভূতের ভর হয়। শুভ্রার দাদা ধীরনকে গ্রামের স্কুলের মাস্টার এবং না-পাস করা ডাক্তারও। দামিনীর এরূপ অবস্থা দেখে বন্ধু ধীরেনকে ডেকে পাঠায় নবীন। বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড় হলেও দুজন এক স্কুলে পড়ার সুবাদে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব রয়েছে। ফলে ধীরেন যখন দামিনীর বেগতিক দেখলো তখন পাস করা বড় ডাক্তার কৈলাসকে দেখানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু গ্রামের বড়রা দামিনীর সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ উঠানে আছড়ে পড়ে দাঁতে দাঁত লাগার জন্য কবিরাজ ডাকার পরামর্শ দেয়। এবং কুঞ্জ কবিরাজ আগে এসে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। কুঞ্জ রোগীর অবস্থা দেখে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে দামিনীর নাকের কাছে ধরে। আর তখনই দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে। গল্পে এক শিহরণ জাগানো বর্ণনা দিয়েছেন লেখক,
‘কে তুই? বল, তুই কে?
‘ আমি শুভ্রা। আমায় মেরো না।’
‘চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?
‘হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমায় মেরো না।’
‘নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, ব্যাপার বুঝলেন কর্তা?’
উঠান থেকে বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, ‘ কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছ? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট করে।’
কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।’’২৩
কুঞ্জ ওঝার ভূত তাড়ানোর প্রক্রিয়া শেষ হতে না হতেই এসে উপস্থিত হয় কৈলাস ডাক্তার। কুঞ্জ অন্য একটি প্রতিক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার চলে আসায় সে সুযোগ আর পায় না সে। কুঞ্জের আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুড়ে দিয়ে কৈলাস তাকে শাসাতে থাকে। এবং খুঁটিতে বাঁধা দামিনীর চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে বলাইয়ের দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দেয়। প্যাঁট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে ঘুমের ওখুধ দেয়। দামিনীও ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিনের মতো বিষয়টির শেষ হলেও ভর সন্ধ্যেবেলা দামিনীর এমন স্বীকারোক্তি সারা গ্রামের মানুষের মনের গভীরে ভূতের বিশ্বাসকে চেপে বসায়। এই বিশ্বাস ক্রমেই যুক্তিবাদী ধীরেনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। ধীরেনের বউ শান্তি সূর্যাস্তের আগেই সমস্ত কাজ সেরে ঘরে ঢুকে পড়তো। সমস্ত গ্রামটা একটা ভূতুড়ে রাজ্যে উপনীত হয় মৃত্যুর রহস্যকে কেন্দ্র করে। তবে দামিনীর স্বীকারোক্তি সবার দ্বিধা দূর করে। ধীরে ধীরে ভূতের ভয় ধীরেন, শান্তি সবাইকে ভূতাক্রান্ত করে ফেলে। উপায় খুঁজতে গ্রামের ক্ষেন্তিপিসির কথায় শুভ্রার আত্মা যাতে না আসে তার জন্য শান্তি কাটা বাঁশের দুপাশ পুড়িয়ে শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দু’প্রান্ত ঠেকিয়ে পেতে দেয়। একদিন শান্তির অলক্ষে সন্ধ্যেয় ধীরেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ফেরে নিজের বিকৃত কণ্ঠ, ঠোঁট আর চিবুক পর্যন্ত গড়ানো রক্তমাখা মুখ নিয়ে। বোঝা গেলো ধীরেনকেও ভূতে ভর করেছে। কুঞ্জ ওঝা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকে ধরতেই স্বীকার করে, সে বলাই চক্রবর্তী, শুভ্রার খুনি। গল্পের শেষ এখানেই।
মূলত গল্পে ধীরেন, শান্তি, দামিনী, নবীন, কুঞ্জ, কৈলাস, পঙ্কজ ঘোষাল, ক্ষেন্তিপিসি প্রভৃতি চরিত্রের মনস্তত্ত্বের সক্রিয়তাকে দেখাতে চেয়েছেন লেখক। গল্পের শুরুতে দামিনীর ওপর ভূতের ভর এবং শেষে ধীরেনের ওপর ভূতের ভর প্রকৃতপক্ষে তাদের মানসিক উত্তেজনার ফল। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একটি গ্রামের চিত্র এটি। যেখানে কুঞ্জের মতো ওঝা সবার মানসিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। সহজ-সরল গ্রামের মানুষের মাঝে একধরনের আতঙ্ক আগে থেকেই ছিল সেটাকে আরও উস্কে দিয়েছে কুঞ্জ। গ্রামীণ সমাজে মানুষের মাঝে কুসংস্কার এবং ঝাড়-ভুকে বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন লেখক। গ্রামের মানুষের সহজ-সরল বিশ্বাসের কাছে কৈলাস ডাক্তারের পরামর্শ ধোপে টেকেনি। এমনকি শিক্ষিত স্কুলের মাস্টার, গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার খ্যাত ধীরেনও প্রচলিত ধারণাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। দামীনির ওপর ভূতের আচড় বলে যখন গ্রামবাসী একজোট তখনও ধীরেন কৈলাস ডাক্তারকে দেখানোর জনয় বন্ধুকে অনুনয় বিনয় করেছে। পরবর্তীতে এই ভূতগ্রস্ত ভীতির কারণে তার মধ্যে একধরনের মানসিক বিকার পরিলক্ষিত হয়েছে।
এ সম্পর্কে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন,
মানুষের মনই সবচেয়ে বাস্তব, কঠিন প্রত্যক্ষ বাস্তব। মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ফ্রয়েডের ভূমিকা অবশ্যই বিস্ময়কর। মনের গভীরের জটিল অন্ধকারে তার বিস্ময়কর রহস্য কোনো কালেই স্থায়ী সমাধানে মুছে যাবার নয়। অন্তরলোকে মানুষকে ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে যায়। তার অন্ধকার পরিবেশ কখনো কখনো মানুষের নিজেকেই ভুলিয়ে দেয়। মানুষের উন্মাদগ্রস্ততা সেও তারই এক শোভনীয় রূপ! মনের গভীরেই সচেতন সভ্যতার পরিপন্থী বিকার জন্ম নেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মনের রহস্যেই এনেছেন ‘হলুদপোড়া’ গল্পের নায়ক থেকে শুরু করে সমস্ত গ্রাম্য মানুষের রহস্যময় সক্রিয়তার অসঙ্গতিপূর্ণ দিকগুলি। আর এখানেই আমাদের মতে, সৃষ্টির অনন্যতার শ্রেষ্ঠত্বের সূত্রে মিলে যায়।’২৪
ধীরেন চরিত্রের মধ্যে ক্রমশ পরিবর্তন এসেছে। শুভ্রাকে যে বলাই চক্রবর্তীই খুন করেছে এমন একটি ঈঙ্গিত পুরো গল্পে আচ্ছন্ন। গ্রামের মানুষ অন্ধের মতো মেনে নিয়েছে। লৌকিক সংস্কার ফুলে-ফেঁপে ধীরেনকেও বশ করে ফেলে। তখন তার ভেতরের যুক্তি -বিদ্যা-বুদ্ধি সরে যেতে থাকে। ধীরেনের ভাবনা ছিল মানবতার। সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা বোন শুভ্রার পিছল কাঠের সিঁড়ি বানানোর চিন্তার মধ্যে। কিন্তু গুজব তাকে ক্রমশ গ্রাস করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ক্লাসের ছাত্ররা, মথুরবাবু, স্ত্রীর তৈরি বাড়িতে ভুতুড়ে পরিবেশ, ক্ষেন্তিপিসির ভূত তাড়াবার টোটকা ধীরেনের পাশে একটা অচেনা দেওয়াল তুলে দেয়। তাইতো গল্পের শেষে ধীরেন নিজেকে বলাই চক্রবর্তী এবং শুভ্রার খুনি হিসবে আখ্যায়িত করে। গল্পের এই প্রচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে লেখকের বিজ্ঞানমনস্ক, মার্কসীয়, ফ্রয়েডীয় মন হঠাৎ ভূত সংস্কারের দিকে কেন মনোযোগী হলেন তা ঠিক বোঝা যায় না।
বস্তুত, গল্পটি মানসিক বিসর্পিলতার একটি ভয়াল নিদর্শন। ধীরেনের শোকার্ত মন, আত্যন্তিক ভাবপ্রবণতা, ‘ জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের ‘ একটা অসুস্থ আবেগ- তাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই প্রেতাশ্রিত করে তুলেছে। গ্রাম- জীবনের সাধারণ কুসংস্কারও এ ব্যাপারে অনেকখানি আনুকূল্য করেছে বলা যায়। কিন্তু ভৌতিকতার পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখকের কৃতিত্ব গল্পটিকে বিকেন্দ্রিত করেছে- Communication এবং False indication উদ্দীষ্ট সিদ্ধান্তের বিপরীতেই পাঠকের মনকে পৌঁছে দিয়েছে।
সমুদ্রের স্বাদ গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণটি বের হয় ১৯৪৫ সালে।গল্পগ্রন্থের নামগল্প সমুদ্রের স্বাদ – এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্ন- মধ্যবিত্তের স্বাদ বা ইচ্ছের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলা, অনাদি। কেরানির মেয়ে নীলার খুব শখ সমুদ্র দেখার। তাদের প্রতিবেশী বলাই দাদার বাড়ির সবাই পুরী ঘুরতে গিয়েছিল। কলকাতার সাহেব কাকার ছেলে বিনুদাও বিলাতে গিয়েছিল। তখন সমুদ্রের বুকেই সে অনেকদিন কাটিয়ে দেয়। প্রতিবেশীদের কাছে গল্প শুনে সমুদ্রের সুনীল মাধুর্যে হারিয়ে যায় নীলা। তারও খুব ইচ্ছে হয় জীবনে সে সমুদ্রের এই অপূর্ব মাধুরী দেখবেই। কিন্তু বাবার টানাটানির সংসার। সেখানে মেয়েকে সমুদ্র দেখতে নিয়ে যাওয়া বেশ শক্ত। তবে নীলার মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি ছিল তাকে একবার সমুদ্র দেখাবেই। ফলে নীলার কেরানি বাবা তার সব সমস্যা পায়ে ঠেলে নীলার মাকে নিয়ে সমুদ্রে বেড়াতে যায়। সামর্থ্যের অভাবে মেয়ের আকুল আবেদন থাকলেও তাকে সঙ্গে নিতে পারেনি নীলার বাবা। বাবা, মায়ের সমুদ্র যাত্রার নানাগল্প শুনে নীলার চোখ ফেটে জ্বল আসে। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বাপের আদুরে মেয়ের সমুদ্র দেখা হলো না। আর বাপ সমুদ্র দেখে আসলো। নীলা কান্না শুরু করে। মেয়েকে প্রবোধ দিতেই নীলার বাবা তাকে প্রতিজ্ঞা করে পুজোর সময় যেমন করেই হোক তাকে সমুদ্র দেখাবেই। কিন্তু সমুদ্র দেখানোর আগেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যায় নীলার বাবা। গল্পে পাই-
“সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার বদলে পূজার সময় নীলাকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বলাই বাহুল্য যে, এবার সমুদ্র দেখা হইল না বলিয়া নীলা কাঁদিয়া আোখ ফুলাইয়া চোখের জলের নোনতা স্বাদে আর সবকিছুর স্বাদ ডুবাইয়া দিল না, কাঁদিল সে বাপের শোকেই। কেবল সে একা নয়, বাড়ির সকলেই কাঁদিল। কিছুদিনের জন্য মনে হইল, একটা মানুষ, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বয়সের বিশেষ একটা মানুষ, চিরদিনের জনয় নীলার মনের সমুদ্রের মতো দুর্বোধ্য ও রহস্যময় একটা সীমাহীন কিছুর ওপারে চলিয়া গেলে, সংসারে মানুষের কান্না ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না।’২৫
নীলার বাবার মৃত্যুর পর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার মা ভাইয়ের বাড়ি চলে যায়। যদিও মৃত্যুর পর পরই নীলার মা ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে অরাজকতা বাড়াতে চায়নি। বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে বিদায় করেই ভায়ের আশ্রয়ে থাকতে চেয়ছিল কিন্তু নীলার মামার কথা মেয়ে তাদের অরক্ষণীয়া নয়। বাপ মরেছে একটা বছর কাটলে তবেই বিয়ে। নীলার দুই মামার পরিবারে দারিদ্র্যতার ছায়া আরও তাদের গ্রাস করতে থাকে। মামার ঘরে নীলা গলগ্রহের শিকার। মামাতো ভাইবোনেরা দুবেলা খায়, স্কুলে পড়ে, খাবার পাশাপাশি বাড়তি যত্নে দুধ, পিঠা, পায়েস পায়। কিন্তু নীলা বা তার দুটি ভাই দুবেলা পেট পুরে ভাতটুকুও পায় না। মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য নীলাকে খুব কষ্ট দেয়। এ নিয়েও মায়ের কাছে মামীদের নালিশের শেষ নেই। কিন্তু সব কষ্টের মধ্যেও নীলার সমুদ্র দেখার স্বাদ কমে না। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সমুদ্র দেখার বাসনা লালন করতে থাকে। হঠাৎ নীলার বিয়ে হয়ে যায় অনাদি নামে সদর হসপিটালের এক কম্পাউন্ডারের সঙ্গে। সংসারের জীবনেও অভাবের ছায়া। স্বামীর পরিবারে গিয়ে সহসাই নীলার মন খারাপ থাকে। অনাদিকেও সে কখনও কিছু বলে না। সমুদ্রের গল্প শুনলেই সে কেঁদে ভাসায়। পাশের বাড়ির কানুর মায়ের সমুদ্রে বেড়ানোর গল্প নীলাকে কষ্ট দেয়। নিম্ন- মধ্যবিত্তের স্বাদ পূর্ণ করেছেন লেখক-
বাহিরে গিয়া অনাদি দেখিতে পায়, দরজার কাছে বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া নীলা বঁটিতে তরকারি কুটিতেছে। একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপটপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।’২৬
এখানেই গল্পের ইতি টেনেছেন লেখক। নীলা, অনাদি, নীলার কেরানি বাবা সবই নিম্ন- মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। যার স্বাদ আছে কিন্তু সাধ্য নাই। নীলা আজীবন স্বপ্ন বুনেছে সমুদ্র দেখবে। বলাই দাদাদের বাড়িতে যে গল্প তার মনোভুবনে দাগ কেটেছিল শেষ পর্যন্ত সামাজিক -অর্থনৈতিক কারণে তা পূরণ হয়নি। বাবার কাছে স্বপ্ন পূরণ হয়নি বলে স্বামীর কাছে স্বপ্নের সমুদ্র দেখার বায়না করবে সটিও হয়ে ওঠেনি টানাপড়েনের সংসারে। তার চেয়ে বড় কথা সামজিক বাধার কারণেও বাবার কাছে যে আবদার অনায়েসে রেখেছে স্বামীর কাছে গিয়ে থমকে গেছে। সমাজে নারী জীবনের প্রতিবন্ধকতাও দেখিয়েছেন লেখক। মানব মনের জটিলতা, সামজিক – অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা সব একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন লেখক। নিম্ন-মধ্যবিত্ত নীলার তাই সমুদ্রের কৌতূহল কখনোই শেষ হলো না। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন- আকাঙ্ক্ষা বেদনাকে প্রতীকায়িত করেছেন গল্পাকার। যার ফ্রেমে বন্দি হয়েছে নীলা, অনাদি। অর্থনৈতিক দৈন্য মধ্যবিত্তের জীবনে অভিশাপ। স্বাদের সঙ্গে সাধ্যের সঙ্কুলান যেন হয়েই ওঠে না মধ্যবিত্ত, নিম্ন- মধ্যবিত্তের। সমাজের এই শৃঙ্খল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে না মধ্যবিত্ত মানুষ। ফলে সমাজের বেড়াজালে তাকে আষ্টেপৃষ্টে নীলা, অনাদি হয়েই কাটাতে হয়। সব স্বপ্নই স্বপ্ন হয়েই থেকে যায় বেশিরভাগক্ষেত্রেই। তাই নীলা চোখের জলের নোনতা পানিতে সমুদ্রকে ছুঁতে চেয়েছে। সমুদ্রের নীল জলের থেকে লবণ কীভাবে আসে সেই প্রশ্নের উত্তর না পেলেও তার অবাধ্য মনকে সে নোনতা স্বাদটা দিয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ‘‘বৃহত্তর মহত্তরেরই আর এক রূপ ‘ সমুদ্রের স্বাদ ‘। মধ্যবিত্ত সংসারে নীলার মতো অনেক মেয়েই সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে- যে সমুদ্র মুক্তি – যা মহাজীবন, খাঁচার পাখি নীল আকাশে যে মুক্তির স্বপ্ন দেখে; কিন্তু অনিবার্যভাবেই সেই সমুদ্র জীবনের বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন, সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ গণ্ডির হতাশা ও বেদনায় পরিণাম লাভ করে।’’২৭
গোপকীনাথ চৌধুরী বলেছেন,
“… মধ্যবিত্ত ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে নীলার মনে সমুদ্র দেখার আকাঙ্ক্ষা, তার কাছে যা এক রোমান্টিক পিপাসার মতো তা কোনদিনই বাস্তবে চরিতার্থতা পায় না। এই আকাঙ্ক্ষার আর্তি এবং তার অপূর্ণতার বেদনায় নীলার মনোজগৎ যেমন পাঠকের সামনে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে – অন্যদিকে এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অন্তারালের কঠিন অর্থনৈতিক প্রশ্নটিকেও পাঠকের সামনে উদ্যত করে তুলতে ভোলেননি সমাজ- বিজ্ঞানমনস্ক লেখক। গল্পের একেবারে শেষে নীলার চোখের জলের নোনতা স্বাদের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের স্বাদ পাওয়ার করুণ মর্মস্পর্শী ব্যঙ্গচেতনার এক অপরূপ সঙ্গতি দান করেছেন।২৮
সমালোচকগণ বিশেষভাবেই তুলে ধরেছেন নীলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের করুণ কাহিনি। নীলার স্বপ্ন এবং স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনি প্রতিটি নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের জীবনের। গৃহাবদ্ধ নারী জীবনের অধিকাংশের অপূর্ণ সাধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
সমুদ্রের স্বাদ গল্পগ্রন্থের একটি গল্প বিবেক। গল্পটিতে নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র ঘনশ্যাম। এছাড়া গল্পটিতে স্থান পেয়েছে ঘনশ্যামের মুমূর্ষু স্ত্রী মণিমালা, তাদের বড় ছেলে সন্তু, মেয়ে লতা। নিখিল ডাক্তার, ঘনশ্যামের দুই বন্ধু – অশ্বিনী ও শ্রীনিবাস, অশ্বিনীর চাকর পশুপতি।
গল্পটির শুরু হয়েছে হতদরিদ্র ঘনশ্যামের স্ত্রী মণিমালার অসুস্থতার চিত্র দিয়ে। মুমূর্ষু মণিমালাকে বাঁচাত হলে একজন ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার কিন্তু সেই সামর্থ্য ঘনশ্যামের নেই। তবু মণিমালার অসুখের বাড়াবাড়ি দেখে ছেলে সন্তুকে ডাক্তার আনতে পাঠায়। মনে মনে পরিকল্পনা করে মণিমালার হাতের রুলিটা বেঁচে কিছু টাকার জোগাড় করবে। ডাক্তারের দেখা শেষ হলে তখন তাকে বুঝিয়ে বলবে এবং সকালে গিয়ে তার টাকাটা পরিশোধ করলেই হবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সন্তু ফিরে এসে জানায় মায়ের মুমূর্ষু অবস্থার কথা শুনে নিখিল ডাক্তার চারটে টাকা সঙ্গে করে তবেই তাকে ডাকতে যাওয়ার কথা বলেছে। হতবুদ্ধি ঘনশ্যাম কোনই উপায়ন্তর করতে পারে না। কোথায় টাকা পাবে, কিভাবে মণিমালার চিকিৎসা হবে। বহুকালের পুরোনো পোকায় কাটা সিল্কের জামাটি পরেই তার বড়লোক বন্ধু অশ্বিনীর কাছে ক’টা টাকা ধার করতে বের হয়। এর আগেও অশ্বিনীর বাজে ব্যবহার সে হজম করেছে। মণিমালাকে চিকিৎসাবিহীন মরতে দেওয়া চলে না। বিধায় যতই অপমান – অসম্মান হোক মণিমালাকে বাঁচাতে অশ্বিনীর স্মরণাপন্ন তাকে হতেই হয়। অশ্বিনীর বৈঠকখানায় পৌঁছে তিন জন অপরিচিত লোক দেখে ঘনশ্যাম দমে যায়। তবুও মনে সাহস নিয়ে বসার ঘরেই অশ্বিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তবে জনহীন ঘরে অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি দেখে হঠাৎ করেই ঘনশ্যামের মন পরিবর্তন হয়ে যায়। নিজের দুর্দশার কথা ভেবে অনেক ইতস্তত করে একসময় ঘড়িটি পকেটে ভরে ফেলে ঘনশ্যাম। যখন ঘর থেকে বের হয় তখন অশ্বীনির চাকর পশুপতির সঙ্গে ঘনশ্যামের সাক্ষাৎ ঘটে। প্রতিনিয়তই ঘনশ্যামের মনের মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার উৎকণ্ঠা প্রবল হতে থাকে। এই বুঝি অশ্বিনী ঘড়ির খোঁজ করতেই বাড়িতেই সরগোল শুরু হবে। আর তৎক্ষনাৎ পশুপতি ঘনশ্যামকে বসার ঘর থেকে বের হতে দেখেছে বলে দেবে। বারবার তার মনে হয় এখনও কেউ বুঝতে পারেনি কোনভাবে ঘড়িটি আগের জায়গায় রেখে আসবে কিনা। আবার ভাবতে থাকে এর আগে অশ্বিনীই তাকে বলেছে চাকরটার হাতটান আছে।
এরূপ ভাবতে ভাবতেই একঘন্টা পর মিনিট পাঁচেকের জন্য অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হয় ঘনশ্যামের। কোনরকম কথা না বাড়িয়ে ঘনশ্যামের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে পাঁচ টাকার একটি নোট বের করে ছুড়ে দেয়। আর পশুপতিকে ডেকে একটি কাপড় কাচা সাবান দিতে বলে। গল্পে লেখক ঘনশ্যামের হতদরিদ্র অবস্থাকে তুলে ধরেছেন এভাবে,
এই বাবুকে একখণ্ড সাবান এনে দাও। জামা কাপড়টা বাড়িতে নিজেই একটু কষ্ট করে কেচে নিও ঘনশ্যাম। গরিব বলে নোংরা থাকতে হবে? পঁচিশ টাকা ধার চাহিলে এ পর্যন্ত অশ্বিনী তাকে অনন্ত পনেরটা টাকা দিয়াছে, তার নিচে কোনদিন নামে নাই। এ অপমানটাই ঘনশ্যামের অসহ্য মনে হইতে লাগিল। মণিমালাকে বাঁচানোর জন্য পাঁচটি টাকা দেয়, কী অমার্জিত অসভ্যতা অশ্বিনীর, কী স্পর্ধা! পথে নামিয়া ট্রাম-রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ঘনশ্যাম প্রথম টের পায়, তার রাগ হইয়াছে। ট্রামে উঠিয়া বাড়ির দিকে অর্ধেক আগাইয়া যাওয়ার পর সে বুঝিতে পারে, অশ্বিনীর বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষে বুকের ভিতরটা সত্যই তার জ্বালা করিতেছে। এ বিদ্বেষ ঘনশ্যাম অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ জিরাইয়া রাখিবে। হয়তো আজ সারাটা দিন, হয়তো কাল পর্যন্ত।২৯
ঘনশ্যামের একটা বৈঠকখানা আছে। একটু স্যাঁতসেঁতে এবং ছায়ান্ধকার হলেও সেখানেই প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে শ্রীনিবাস চোখ বুজে শুয়ে পড়ে। ঘনশ্যামের দেখা পাওয়ামাত্রই টাকার কোন যোগাড়যন্ত্র হলো কিনা জানতে চায়। শ্রীনিবাসও ঘনশ্যামের মতোই হতদরিদ্র। তার ছেলে খোকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে দিনদিন। হাতে টাকা-পয়সা না থাকায় সেও ভালোমতো ডাক্তার দেখাতে অক্ষম। দুভাগ্যের এই বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দুই বন্ধুকেই নির্বাক করে দেয়। অনেক দিনের বন্ধু তারা। সব মানুষের মধ্যে তারা দুজন খুব কাছাকাছি। হয়তো তাদের অবস্থা একই তাই তাদের মধ্যে এত ভাব। শ্রীনিবাস বউয়ের গয়নার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল বেঁচে ছেলের ডাক্তার খরচ কোনরকমে যোগাড় করেছে। সেখান থেকেই দশ টাকার একটি নোট ঘনশ্যামের হাতে গুঁজে দেয় শ্রীনিবাস। একই অবস্থায় থেকেও তার এই উদারতার জন্যই নিজেই বেশ লজ্জা পেয়ে হকচকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। কিন্ত কিছুক্ষণ পরেই শ্রীনিবাস ফিরে আসে ঘনশ্যামের বাড়ি। তার পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে গেছে। রাস্তা, ঘনশ্যামের বাড়ি অনেক খোঁজাখুজির পরও যখন মানিব্যাগের কোন হদিস পাওয়া গেলো না তখন পূর্বের দশ টাকা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয় শ্রীনিবাস। এই পরিস্থিতিতে ঘনশ্যামের বারবারই মনে হতে থাকে শ্রীনিবাসের ব্যাগটা সে ফিরিয়ে দিতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে সে মজা করতেই পারে। এই অভাবনীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-
শ্রীনিবাস চলিয়া যাওয়ার খানিক পরেই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যামের সর্বাঙ্গে একবার শিহরন বহিয়া গেল। ঝাঁকুনি লাগার মতো জোরে। শ্রীনিবাস যদি কোনো কারণে গা ঘেঁষিয়া আসিত, কোনরকমে যদি পেটের কাছে তার কোন অঙ্গ ঠেকিয়া যাইত! তাড়াতাড়িতে শার্টের নিচে কোঁচার সঙ্গে ব্যাগটা বেশি গুঁজিয়া দিয়াছিল, শ্রীনিবাসের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরিয়া খোঁজার সময় আলগা হইয়া যদি ব্যাগটা পড়িয়া যাইত! পেট ফুলাইয়া ব্যাগটা শক্ত করিয়া আটকাতেও তার সাহস হইতেছিল না, বেশি উঁচু হইয়া উঠিলে যদি চোখে পড়ে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি আলগাভাবে শার্টের পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া কতক্ষণ ধরিয়া চা খাইয়াছে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, অশ্বিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তো একবারও হয় নাই। সেইখানেই ভয় ছিল বেশি। তার ব্যাগ বাহির করিয়া দেয়, শ্রীনিবাস নিছক তামাশা মনে করিবে। তাকে চুরি করিতে দেখিলেও শ্রীনিবাস বিশ্বাস করিবে না সে চুরি করিতে পারে।কিন্তু কোনরকম পকেট ঘড়িটির অস্তিত্ব টের পাইলে অশ্বিনী তো ওরকম কিছু মনে করিত না।৩০
শ্রীনিবাস চলে যাওয়ার পর অশ্বিনীর সোনার ঘড়িটির কথা বারবার মনে হতে থাকে ঘনশ্যামের। এদিকে মণিমালার শরীরেরও অবনতি হয় আরও। ডাক্তার গম্ভীর মুখে মণিমালার ব্রেন কমপ্লিকেশনের খবর দেয়। সময়মতো দু- চারটা ইনজেকশন পড়লে হয়তো ধীরে ধীরে মণিমালা সুস্থ হয়ে উঠতো কিন্তু এখন সে সম্ভাবনাও নাই। ঘনশ্যামের কাছে এখন টাকার অভাব নেই। সোনার ঘড়ি বিক্রি করলে সে অনেক টাকা পাবে। তাছাড়া শ্রীনিবাসের মানিব্যাগটাও তার কাছে। ফলে এখন মণিমালার বেঁচে উঠতে তো কোন সমস্যা নেই। ভাবনায় হারিয়ে যায় ঘনশ্যাম। আবার ভাবতে অশ্বিনী হয়তো তার হারানো ঘড়িটির খোঁজ করছে। এমনও হতে পারে সে পুলিশে খবর দিয়েছে।
পরদিন অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা করার বাহানায় আবার তার বাড়িতে যায় ঘনশ্যাম। গতকালের চুরি করা ঘড়িটি যথাস্থানে রেখে বের হয়ে পড়ে ঘনশ্যাম। গল্পের শেষ এখানেই।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্ন- মধ্যবিত্তের জীবন জটিলতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, মনস্তাত্ত্বিক দিক একত্রে দেখিয়েছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র ঘনশ্যাম। দরিদ্র, অসহায়, নিরীহ একজন মানুষ। তার বন্ধু শ্রীনিবাসও ঘনশ্যামের মতোই অসহায়, দরিদ্র। খোকার যায় যায় অবস্থায় বউয়ের সঞ্চিত শেষ সম্বলটুকু বেঁচে শ্রীনিবাস টাকা সংগ্রহ করে। সেই টাকা থেকে তারই মতো অসহায় বন্ধু ঘনশ্যামকে সাহায্য করতে দশ টাকার একটি নোট হাতে গুঁজে দেয়। নিজের অতি কষ্টের টাকা হলেও শ্রীনিবাসের মধ্যে মনুষ্যত্ব, বিবেক তাকে তাড়িত করেছে। তাই শুধু নিজের সন্তানের চিকিৎসা নয় বরং বন্ধু পত্নীর জন্যও তার মন কেঁদেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ঘনশ্যাম তার মানিব্যাগটা সরিয়ে ফেলে। এবং তার বিবেকও তাকে বেশ প্রশ্রয় দেয়। শ্রীনিবাসের সরলতা, বিশ্বাস আছে বলেই সে ব্যাগটা নিতে পারে। শ্রীনিবাসের মতো অসহায় দরিদ্র মানুষ জানলেও বন্ধুর চুরি করা বিশ্বাস করবে না বিধায় মানিব্যাগটা সে লোপাট করেছে। বন্ধু তাকে পুলিশে সোপর্দ করার কথাও ভাববে না। সর্বোপরি শ্রীনিবাসের মতো একজন হতভ্যাগ্য, হতদরিদ্র, দুর্দশাপন্ন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব না থাকলেও ঘনশ্যামের কিছুই যাবে, আসবে না। হয়তো এসব চিন্তা তাকে মানিব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে বড়লোক বন্ধু অশ্বিনীর অঢেল সম্পত্তির মালিক। পতিপত্তির অভাব নেই। তার সোনার ঘড়ি চুরি করে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়েছে ঘনশ্যাম। এই বুঝি সে অশ্বিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত অশ্বিনীর ঘড়ি সে চুপিসারে যথাস্থানে রেখে এসেছে। পরস্পর দুটি ঘটনা বেশ নাড়া দেয়। মানুষের মনস্তত্ত্বকে বোঝার জন্য এরচেয়ে বেশি গভীরে হয়তো ঢুকতে হয় না। যেখানে শ্রীনিবাসের ওটুকুই শেষ সম্বল সেখানে ঘনশ্যাম নির্বিকার কিন্তু যেখানে অশ্বিনীর এতটুকু খোয়া গেলে কিছুই হবে না তবু তার প্রতি সমর্পণ! কারণ অশ্বিনী সম্পদশালী। তার সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ ঘটলে ঘনশ্যামের কোনমতেই চলবে না। বলা যায় না, বরলোক বন্ধুর প্রয়োজন সর্বদাই হতে পারে। কিন্তু শ্রীনিবাসের মতো চালচুলোহীন মানুষের কী প্রয়োজন তার? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এত জীবনঘনিষ্ঠ দুটো ঘটনার সম্মিলনে মানুষকে বুঝতে শিখিয়েছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক, গবেষক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,
‘বিবেক’ গল্পের ঘনশ্যাম যখন বড়লোক বন্ধুর চুরি-করা ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির গোপন অনুপ্রেরণায় নিজের বিবেককে নিরুঙ্কুশ করে, অথচ সেই সঙ্গে দরিদ্র, নিরুপায়, পরম হিতকামী সমগোত্রীয় বন্ধুর মানিব্যাগ চুরি করতে তার বাধে না- তখন মধ্যস্বত্বভোগীর স্ববিরোধের রূপটি চূড়ান্তভাবেই অভিব্যক্ত হয়।৩১
চরম সংকটে পতিত দুজন একই বৃত্তের মানুষ একে অপরের সঙ্গে প্রতারণা করছে। আত্মমর্যাদাবোধ, বিবেকের সন্ধান মেলে না সেখানে। কিন্তু বড়লোক বন্ধুর কাছে সামান্য অপমানিত হওয়ার ভয়, পুলিশে সোপর্দ করতে পারে আশঙ্কায় ঘনশ্যাম জড় সড় হয়েছে। দরিদ্র বন্ধুর প্রতি অন্যায় -অবিচার, বিবেকহীন থেকেছে আবার তার প্রতি ভরসাও করেছে। যেটা বড়লোক বন্ধুর ক্ষেত্রে রাখতে পারেনি। বিষয়টিকে দুভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বলছেন,
‘ঘনশ্যামের বিবেকও বন্ধুত্বের খাদ। ধনী অশ্বিনীর অবজ্ঞা পেয়েও তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখার আগ্রহ, তাই ঘনশ্যাম চুরি ঘড়িটি ফেরত দিল, গরীব শ্রীনিবাসের প্রতি বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, তার পুত্রের জনয় মমতা সবই ঘনশ্যামের বিবেকের এলাকার বাইরে সব মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত এই শ্রেণি এখন দিগভ্রান্ত।৩২
আপিম গল্পটি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির প্রকাশ। এ গল্পের চরিত্রগুলো যথাক্রমে হরেন, নরেন, বিমল, মায়া, অমলা, কালিদাসী, সবিতা, মাধুরী। গল্পটির সূচনা হয়েছে একটি পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে। প্রত্যেকদিন সকালে এ বাড়ির বর্তমান কর্তা নরেনই মোটামুটি বাজারটা সেরে ফেলে। কিন্তু আজ সকালে উঠে নরেন একগাদা অফিসের কাজ নিয়ে বসেছে। ফলে বাজার যাওয়ার মতো যথেষ্ট সময় তার হবে না। এদিকে নরেনের ছেলে বিমল সেও কোনদিন বাজারের মুখদর্শনও করেনি। মা মায়া যখন তাকে বাজারে যাওয়ার জন্য সাধতে লাগলো বিমল বেশ ব্রিবত হয়। কুলকিনারা না পেয়ে নিরুপায় হয়ে মায়া বাড়ির ঝি কালিদাসীকেই শেষমেশ বাজারে পাঠায়। বাড়ির সব কাজ কালিদাসী করলেও এই একটি কাজে মায়া কখনও তার সাহায্য চায়নি। আজ এত নিরুপায় হলো যে তাকেই পাঠাতে হয়। কালিদাসীর মুখের হাসোজ্জল ভাব দেখেই মায়া বুঝতে পারে কালিদাসী এখন থেকে পয়সাও সরাবে। আবার মাছ-তরকারি থেকেও কিছু কিছু সরিয়ে ভিন্ন একটা পুটলি বাঁধবে। মায়ার কাছে এসে একসঙ্গে তার বাজারটাও করে আসার বাহানা দেবে।
মায়ার সংসারে আরও আছে নরেন বড় দাদা হরেন, তার মেয়ে অমলা। বড়ির বড় বউয়ের মৃত্যুর পর ভাশুর তার আপিম ধরেছে। কাজকর্ম করে না। ঘরের মধ্যে থাকে আর আপিম খায়। সংসারটা এখন নরেনকেই চালাতে হয়। দশটার সময় কালিদাসীর বাজার কর তরিতরকারি-মাছ মুখে গুঁজে নরেন অপিসের উদ্দেশে বের হতেই হরেনের ডাক পড়ে। দাদা টাকা চাইতেই সে মুখের ওপর স্পষ্ট জানিয়ে দেয় মাসের শেষ তার কাছে কোনো টাকা নেই। দাদার মুখের ওপর এমন কথা কোনদিনই বলেনি নরেন। কিন্তু টানাটানির সংসারে দাদার আপিমের বাড়তি খরচা যোগাতে সে পারবে না। মধ্যবিত্তের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে,
টাকা তো নেই দাদা। মাস কাবার হয়ে এল, আমি সামান্য মাইনে পাই,
একেবারেই নেই? আনা চারেক হবে না?
নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল,’ না, একটি পয়সাও নেই। আপিমের জন্যে তো? আপিমটা এবার তুমি ছেড়ে দাও দাদা।৩২
নরেনের কাছে হতাশ হয়ে বিমলের কাছে টাকা চায়লে সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হতে হয় হরেনকে। এদিকে ভাগ্যের বদল ঘটাতে নরেন মাঝেমাঝেই টিকিট কেনে। পকেটের শেষ সম্বলটুকুও হঠাৎ যদি ভাগ্যের চাকা ঘোরে সে আশায় নিঃশেষ করে। হরেন মিত্র আগে বড় চাকুরে ছিল। সংসারের হাল তখন সম্পূর্ণ তার ওপরই ছিল। কোনদিন নরেনকে ভাবতে হয়নি। কিন্তু আজ হরেনের আপিমের নেশা তাকে কষ্ট ভুলাতে সাহায্য করলেও সংসারটাকে রসাতলে ঠেলে দেয়। বিমল কলেজে জ্যাঠার জেরেই সবিতা, মাধুরীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পেরেছে।
সংসারের দুর্দশায় চুপ থাকলে হরেনের চলে না। পরিবারের কর্তা সে যদিও আজকাল নরেনই সব দেখাশুনো করে তবু সকালে নরেনের অসহায় অবস্থা হরেনকে পীড়িত করে। কাজের সন্ধানে বের হয় সে। কাজ পেয়েও যায় হরেন। রাতে নরেনের হাতে পাঁচ টাকা গুঁজে দেয় হরেন। টাকা কয়টা পেয়ে বাজার করার দুশ্চিন্তাটা তার মাথা থেকে তখনকার মতো যায়। সে আবারও ভাবতে বসে আজ দুটাকা দিয়ে টিকিট কিনেছে। যদি সেটাতে হাজার পঞ্চাশেক টাকা তবে কী মজাটাই না হবে। চোখ বুজে কল্পনায় তার মন উতলা হয়ে ওঠে।
এদিকে নরেনের পুত্র বিমল সবিতার সঙ্গে কেমনভাবে আরও ভাবটা জমে ওঠে সে কল্পনায় বিভোর। কলেজ থেকে সবিতার সঙ্গে গাড়িতে ফিরতে গিয়ে হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যদি তারা পাশাপাশি দুটি বেডে থাকতো। সবিতার কিছু হয়নি। সবিতাকে বাঁচাতে গিয়ে তার গুরুতর আঘাত লেগেছে। কল্পনায় গল্প গড়ে তুলতে থাকে বিমল। এতেই তার সুখপাখি ধরা দেয় যেন। আবার ছেলের আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে থাকতে দেখে মায়ার মনে হয় এ পর্যন্ত ছেলে ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে। এবার যদি একটু রাত জেগে পড়াশোনা করে ভালো করে। মেডেল পায়, বৃত্তি পায়, ছেলে তার মস্ত বড় চাকরি করবে। ঘরে একটি টুকটুকে বউ আসবে। গল্পের শেষ হয়েছে এভাবে,
বাড়িতে আপিম খায় একজন, কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখে সকলেই। হরেনের পনের বছরের মেয়ে অমলা পর্যন্ত কাকিমার চোখ এড়াইয়া এতরাতে খোলা ছাতে একটু বেড়াইতে যায়- ছাতে গিয়ে নানা কথা ভাবিতে তার ভালো লাগে।৩৩
গল্পের এক অনবদ্য কাহিনি নির্মাণ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যবিত্তের জীবনে স্বপ্নটাই সব। তাদের বেঁচে থাকা স্বপ্নকে বুকে নিয়ে। প্রতিনিয়ত দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে চলে এই এক স্বপ্নের জোরে। আজ না হয় কাল তাদের ভাগ্য ফিরবেই। নরেন, অমলা, মায়া, বিমলের মতোই বুকের মাঝে স্বপ্নকে প্রতিনিয়ত একটু একটু বৃদ্ধি করতে থাকে। স্বপ্নহীন মানুষ পৃথিবীতে নেই। প্রত্যেকেই তার নিজের অবস্থান থেকে আরও একটু সুখের আশায়, ভালো থাকার আশায় স্বপ্ন দেখে চলেছে। সন্তানকে নিয়ে মায়ের যেমন স্বপ্ন, প্রেমিকের স্বপ্ন প্রেমিকাকে নিয়ে, পরিবরের কর্তা স্বপ্ন পরিবারিক অবস্থার উন্নতি, শিক্ষার্থীর স্বপ্ন কিভাবে সে পড়াশোনায় ভালো করবে, একটি মস্ত বড় চাকরি করবে প্রভৃতি। স্বপ্নটাই সত্যি। স্বপ্নটাই বেঁচে থাকার প্রেরণা। আর নরেন, মায়দের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্তের একমাত্র স্বপ্নের সঙ্গেই বসবাস। তাই প্রত্যেকেই আশায় বুক বেঁধেছে। হরেনও স্বপ্নকে জয় করতে কাজে ফিরেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাই এতটা জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলতে পেরেছেন ছোটগল্পগুলো। মধ্যবিত্ত জীবনচেতনার অন্ধকার প্রান্তগুলোর বিকাশ ঘটেছে এই গল্পে। এ সম্পর্কে ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,
মধ্যবিত্ত ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে, সেই মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষও তিনি। আর এই সমাজের কৃত্রিমতার মুখে রঙ মাখার মতো উৎকট জৌলুস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছিল পোশাক পরা মেকী সভ্যতার আড়ালে যে আদিম স্বভাব আছে, তাকে বিকৃত ও ভ্রষ্টতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস আছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার যথাযথ সত্যতা চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন।৩৪
মধ্যবিত্তের জীবনচেতনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ গল্পটি। গল্পের পাত্র-পাত্রী সমানভাবে সক্রিয়। কোন একটি চরিত্র ধরে এ গল্পের নায়ক বা নায়িকা বলে চলে না। তবে নরেন পরিবারের কর্তা মারফত এগল্পের কেন্দ্রে যেন তারই অবস্থান বেশি। যদিও প্রতিটি চরিত্রের বিকাশ গল্পে সমানভাবে ঘটিয়েছেন লেখক।
“আজ কাল পরশুর গল্প ” এই গল্পগ্রন্থটি ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার গন্ধ তখনও বাংলার প্রান্তর থেকে মুছে যায়নি। চারিদিকে বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবে ক্ষয়প্রাপ্ত মানুষ, সমাজ, সভ্যতা। বিশ্ব যুদ্ধের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন চলছিল দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। চারিদিকে হাহাকার চললেও একটি শ্রেণি রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছে পরিণত হয়। মুনাফাখোর, মজুতদার, চোরাকারবারি, গরিবের পেটে লাথি মেরে তাদের মুখের খাবারটুকু পর্যন্ত তারা শোষণ করেছে। পুঁজিপতিদের দিনে দিনে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে আর দরিদ্ররা না খেতে পেয়ে পথে-ঘাটে মরে পড়ে থেকেছে। দুর্নীতি, ঘুষ, ধর্ষণ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের এক নোংরা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল বিশ্ব। ভারতবর্ষও এই অরাজকতা থেকে রক্ষা পায়নি। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একমুঠো খাবার জোটেনি। যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরা। পৃথিবীর সব যুদ্ধেই নারীরা সম্মান হারিয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে, হত্যার শিকার হয়েছে। নারীদের করে তোলা হয়েছে ভোগের সামগ্রী। গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিশ্বযুদ্ধের দামামা ছুঁয়ে গিয়েছিল। তাঁর মনের ওপর এতটাই প্রভাব পড়েছিল বিভিন্ন গল্পের উপাদানে তিনি বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমাজ জীবনকে তুলে ধরেছেন। “আজ কাল পরশুর গল্প” গড়ে উঠেছে এমনই একটি যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের সমাজ জীবনের কাহিনি নিয়ে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামপদ, মুক্তা৷ এছাড়া গল্পটিতে স্থান পেয়েছে গিরিবালা-গিরি, ঘনশ্যাম দাস, সাধনা,সুরমা, শঙ্কর, বনমালী, করালী, নন্দী, ফণী, সুদাস, গোকুল, নিকুঞ্জ।
গল্পের সূচনা হয়েছে মানসুকিয়ার গ্রামে। চালচুলাহীন রামপদ ঘরের দাওয়ায় বসে নিজের রাঁধা ভাত, শোল মাছ খেতে বসেছে। এমন সময় দেখতে পায় খালের ঘাটে নৌকা থেকে তিনজন মেয়ে ও একটি ছেলে নামছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সুরমা, সাধনা, মুক্তা। এই তিন নারীর মধ্যে মুক্তা রামপদের বউ। গ্রামে তাকে ঢুকতে দেখেই পাড়া- মহল্লায় সোরগোল পড়ে যায়। বুড়ো সুদাস, নিকুঞ্জ, গোকুল সবাই কানাকানি করতে থাকে। কেন আবার ফিরে এলো মুক্তা। তার গ্রামে ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে মধু কামারের বউ গিরির মা একেবারে সামনে এসে পথ আটকায় তার ফোলা-ফাঁপা শরীর নিয়ে। মধু কামার বছর খানেক নিরুদ্দেশ। তার মেয়ে গিরিও কিছুদিন আগে উধাও হয়েছে। কিন্তু গিরির মায়ের তেজ কমেনি। মুক্তাকে দেখেই তার মন বিষিয়ে ওঠে। তার দিকে খেঁকে ওঠে,
ক্যান লা মাগী? গিরির মা মুক্তাকে শুধোতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দিয়ে, ‘ ক্যান্ ফিরেছিস গাঁয়ে, বুকের কী পাটা নিয়ে? ঝেঁটিয়ে তাড়াব তোকে। দূর অ দূর- অ! যা!৩৫
মুক্তার সঙ্গে থাকা সুরমা গিরির মাকে থামাতে গিয়ে গালের চোটে এক হাত পিছিয়ে আসে। গিরির মায়ের চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাড়ার মানুষদেরও সুবিধা হয় মুক্তাকে কদর্য চোখে ঘুরে ঘুরে দেখার এবং নানারকম বাজে মন্তব্য করার। সব বাধা পেরিয়ে সমাজকর্মী সুরমা, সধনা, মুক্তাকে তার স্বামী রামপদের হাতে তুলে দেয়। সব ভুলে তাদের আবারও সংসার করার কথা বলে সুরমা। কিন্তু রামপদের মধ্যে জড়তা, ভয় কাজ করে। তার বউকে গ্রহণ করতে সমস্যা না হলেও সমাজ তাকে শাসিয়েছে। রামপদ বলে,
সমাজ তাকে শাসিয়েছে, বৌকে ঘরে নেওয়া চলবে না। নিলে বিপদ আছে। সমাজ মানে ঘনশ্যাম দাস, কানাই বিশ্বাস, নিধু নন্দী, লোচন কুমার, বিধু ঘোষ, মধু নন্দী- এরা কজন। ঘনশ্যাম একরকম সমাজপতি এ অঞ্চলের চাষাভুষোদের, অর্থাৎ চাষি গয়লা কামার কুমোর তেলি ঘরামি জেলে প্রভৃতির। সেই ডেকে কাল ধমক দিয়ে বারণ করে দিয়েছে রামপদকে। অন্য কজন উপস্থিত ছিল সেখানে। একটু ভয় হয়েছে তাই রামপদর। একটু ভাবনা হয়েছে।৩৬
তবু সুরমা বলে কয়ে দুটি খাওয়ার ছলে মুক্তাকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়। বাইরে যা ঘটে ঘটুক, ওদের মধ্যে একটু বোঝাপড়া হওয়া চায়। গ্রামের আরেকজন কর্মী শঙ্কর। গ্রামের অবস্থা সেই ভালো জানে। তার সঙ্গেও সুরমা, সাধনাদের পরামর্শ করা দরকার। কীভাবে মুক্তাকে সংসারমুখী করা যায় সমাজকর্মীদের উদ্যোগেই সে অসৎ জীবন থেকে ফিরে এসেছে। এগারো মাসের অঘটনের জন্য দায়ী মুক্তার ভাগ্য। সাত মাসের ছেলে না খেয়ে মরেছে। রামপদ তখন বিদেশে। সন্তান হারানো মা দিনের পর না খেয়ে থেকেছে তখন গ্রামের কেউ আসেনি। তখন মুক্তা সদরে চলে যায়। বউকে রামপদ গ্রহণ করতে চাইলেও মানসুকিয়ার চাষাভুষো সমাজে গোলমাল বেধে যায়। ঘনশ্যামই আন্দোলটা জাগিয়ে রাখে। কারণ অসহায়ের ওপর পীড়ন করা সহজ। সবাই যাকে ত্যাগ করে, যার পক্ষে কেউ থাকে না তার ওপর যতখুশি অত্যাচার করা যায়। মিলেমিশে অসহায় মানুষটাকে পীড়ন করতে ভালোবাসে সবাই। ঘনশ্যামেরা একজোট হয়ে মুক্তাকে ঘরে তোলার বিরোধীতা করে। এদিকে ঘনশ্যাম গিরিবালার কাছে রাত পার করে। গিরি তাকে অনুরোধ করে মুক্তাকে সমাজে ফেরাতে যেন কেউ বাধা না দেয়। তা নাহলে গিরিও সমাজে মায়ের কাছে ফিরতে পারবে না। গিরি তাই মুক্তার সঙ্গী। গ্রামের শালিস বসে। মুক্তাকে সমাজে ফিরিয়ে নিতে সবার আপত্তি। গিরি, বনমালী, শঙ্কর সবার মুখের ওপর প্রতিবাদ করে। বনমালী বলে রামপদের বউ কোন অপরাধ করেনি। কিসের বিচার তার? গিরিও মুক্তার পক্ষ নেয়। নানারকম যুক্তি দেয়। প্রতিবাদের মুখে পড়ে ঘনশ্যাম নামমাত্র একটা প্রাচিত্তির করার কথা বলে। গিরি, বনমালী আবারও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মুক্তা রামপদের ব্যাপারটাও চাপা পড়ে গেলো। গিরিও তার মায়ের কাছে ফেরে সুযোগ বুঝে। গল্পের কাহিনি এখানেই শেষ করেছেন লেখক। তবে কাহিনির আড়ালে লেখকের সমাজ সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের মানুষের জীবন কিভাবে বাঁকা পথে হারিয়ে গিয়েছিল তারই রূপ ফুটে উঠেছে গল্পটিতে।
দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল ছোবলে রামপদ, মুক্তার সংসার টেকে না। অর্থের অভাবে সন্তানের মৃত্যু, নিজে দিনের পর দিন না খেয়ে পড়ে থেকেছে। একসময় ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জড়িয়ে পড়েছে যৌনকর্মে। সমাজগর্হিত কাজে জড়িয়ে মানুষের অপবাদের শিকার হয় মুক্তা। স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা মুক্তার সংসারে ফেরার পথ বন্ধ করে দেয়। গল্পে দুটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত. দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনজীবনে মুক্তাদের নিরাপত্তাহীন জীবন।
দ্বিতীয়ত. ঘনশ্যামের মতো কালোবাজারি, উঠতি পুঁজি পতিদের ভণ্ডামী। বিশ্বযুদ্ধের দামামায় মুক্তারা হারিয়ে গেছে সহজ-সরল জীবন থেকে। গৃহস্থ জীবনের বদলে কুল মর্যাদা হারিয়ে অনেককেই বেছে নিতে হয়েছে অসৎ পন্থা। একটু বেঁচে থাকার আশায়। সমাজকর্মীদের সহোযোগিতায় সংসারে ফিরতে চায়লেও বাধ সেধেছে ভণ্ড সমাজপতিরা। ঘনশ্যাম যে কিনা নিজেই গিরিবালার কুটিরে রাত কাটায় সে নিজের বিচার না করে হতদরিদ্র, অসহায় রামপদকে শাসিয়েছে। বউকে ঘরে তুললে তাকে একঘরে করা হবে। প্রতিনিয়তই জীবন-মৃত্যুর দরকষাকষি চলেছে। সেখানে নারীর সম্ভ্রম, নারীর অহংকার মুখ থুবড়ে পড়েছে। সামান্য খড়-কুটো আঁকড়েও মানুষ বাঁচার আশা ত্যাগ করে না। মুক্তাও জীবনের প্রয়োজনে অন্যপথ বেছে নিয়েছিল। মূলত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ-ধর্মের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে মুক্তাকে সংসারে ফেরত দিয়ে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বুকে আশা জাগিয়েছেন।
বিশ শতকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আর এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রত্যক্ষ যোদ্ধা নাহলেও ভারতবর্ষ যুদ্ধের দামামা থেকে রক্ষা পায়নি। ফলে সমকালে ঘটে যাওয়া নানাবিধ অভিজ্ঞতা, সমস্যা, সংকট উঠে এসেছে সাহিত্যকর্মে। তারই ধারাবাহিকতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন “যাকে ঘুষ দিতে হয় ” গল্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর সমাজে ছড়িয়ে পড়া স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়া, রেশন কন্ট্রোল, চাল-কেরোসিন- বস্ত্র সংকট, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মজুতদারি, দ্রব্য মূল্য গুদামজাত করে রাখা, নারীর সম্ভ্রমহানি, নৈতিক অবক্ষয়, চুরি- ডাকাতি প্রভৃতি স্থান পেয়েছে সমকালে রচিত সাহিত্যে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমাজকে তুলে ধরতে লেখক সৃষ্টি করেছেন একাধিক গল্পের। এর মধ্যে একটি অন্যতম গল্প যাকে ঘুষ দিতে হয়। এ গল্পের প্রধান চরিত্র মাখন, সুশীলা, দাস সাহেব, ঘনশ্যাম।
বিশ শতকের নব্যপুঁজিপতিরা পুঁজি সংগ্রহে এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে নারীদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতেও তারা দ্বিধা করেনি। হোক সে বউ বা প্রেমিকা। পণ্যকে যেমন নিলামে তোলা হয় ঠিক তেমনই একশ্রেণির মানুষ পুঁজিপতি হয়ে উঠতে ঘরের সম্ভ্রমও নির্দ্বিধায় লুটিয়ে দিয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাখন পরীক্ষায় ভালো পাস করা গরিবের ছেলে। মাত্র একশ টাকার সামান্য মাইনের চাকরি করতো। চাকরিকালীন বউ সুশীলার কত কটুবাক্য শুনেছে সে। কত অবজ্ঞা, অবহেলা, অপমান, লাঞ্ছনা- বঞ্চনার শিকার হয়েছে মাখন। কিন্তু আজ সে মোটর হাকিয়ে চলে। গাড়ির ড্রাইভার ঘনশ্যামের আস্তে মোটর চালানো দেখলে আজ সে সহ্য করতে পারে না। সুশীলার সুখের সংসার। মাখনের হঠাৎ এত পদন্নোতি ভাবাই যায় না। সুশীলার জীবনে এখন অপার শান্তি। তাদের হঠাৎ আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এভাবে—
তিন বছর আগে মাখনকেও তো এমনভাবে ঝুলতে ঝুলতে কাজে যেতে হতো। স্বামীর অতীত সাধারণত্বের দুর্দশা আজ বড় বেশি মনে হওয়ায় ট্রাম- বাসের বাদুর- ঝোলা মানুষদের প্রতি উত্তপ্ত দরদ জাগে সুশীলার। মাখন সিগারেট ধরিয়ে এপাশে ধোঁয়া ছেড়ে ওপাশে সুশীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রায় সবিনয় নিবেদনের সুরে বলে, ‘কে ভেবেছিল আমরা একদিন মোটর হাঁকাব?’৩৭
মাখন, সুশীলার আজকের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে দাস সাহেবের বৌদলতে। একশো টাকার চাকরি ছেড়ে দাস সাহেবের সহোযোগিতায় ঠিকাদারি করে অবৈধ পথে বিপুল অর্থের মালিক হয়েছে। তিন বছরেই ভাগ্যের চাকা পাল্টে ফেলেছে। মাখনের বড় হওয়া, টাকা রোজগার করার ক্ষমতাকে তরান্বিত করেছে সুশীলার অর্থলিপ্সু স্বভাব। মাখন যেমন টাকা দুহাতে কামিয়েছে তেমনই ঘুষও দিতে হয়েছে দাস সাহেবকে। শুধু কী টাকার ঘুষ দিয়েই সে ক্ষান্ত থেকেছে? সুশীলাকেও তো দিতে হয়েছে। দাস সাহেবের নোংরামি টের পেলেও মাখন এবং সুশীলার জীবনে টাকার গুরুত্ব এত বেশি যে সেদিকের ভারটা কনট্রাক পাইয়ে দিয়ে মিটিয়ে দিয়েছে দাস সাহেব।
ঘুরতে বেরিয়ে দাস সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটে তাদের। তখনও দাস সাহেবের কুনজর থেকে রক্ষা পায় না সুশীলা। পুঁজির নেশায় মাখন এবং সুশীলা এতটাই বিবেকশূন্য হয়ে পড়ে যে কনট্রাক হাতিয়ে নেওয়াই তাদের আসল উদ্দেশ্যে। সেখানে চরিত্র বিকাতেও তাদের সমস্যা হয় না। তাইতো পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হলে দাস সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় দুজনে। দাস সাহেব বিয়ে করেননি, আত্মীয়স্বজনও থাকেন না কাছে। মস্ত বাড়িতে একাই থাকেন। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেতেই খানিক বাদে কনট্রাকের কথায় আসে দাস সাহেব। তার একান্ত কামনা দ্রুত মাখনকে কাজে পাঠিয়ে দিয়ে সুশীলার সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠ সময় পার করা। তাই বাহানা করে কনট্রাকের জন্য হাওয়ার্ড সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পাঠায় মাখনকে।
গল্পে লেখকের অনবদ্য অভিজ্ঞতার সঞ্চারণ ঘটেছে। কথায় আছে, টাকার জন্য কাঠের পুতুলও হা করে। গল্পের নায়ক মাখন এবং সুশীলার টাকার প্রতি প্রবল নেশা। আত্মসম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়ে হলেও মোটর হাঁকিয়ে সমাজের বুকে সদর্পে নিম্নবিত্তের বুকে লাথি মেরে চলায় তাদের কাজ। তাইতো গাড়ির চালক ঘনশ্যাম বাবুর হুকুমকে বেদবাক্য মনে করে। নগরায়নের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে তার আত্মমর্যাদা ভুলতে বসেছে। ধনসম্পদ গড়ে তুলতে নিজের মান-সম্মানের দিকেও ফিরে তাকায়নি। এই গল্পের চরিত্র মাখন এবং সুশীলা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আর দাস সাহেব ভণ্ড, অসৎ, দুর্নীতি পরায়ণ মানুষ। টাকা দিয়ে নারীর সম্ভ্রম কেড়ে নিতেও তাদের বিবেক কাঁপে না। বিনা স্বার্থে মাখনের উপকারে সে আসেনি। নিজের লালসা চরিতার্থ করতেই মাখনকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। আর মাখনও চুপ থেকেছে মুখে টাকা গুঁজে দিয়ে। নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রমের চেয়ে টাকা তার প্রিয়। তাইতো স্ত্রীকে অন্যের ঘরে রেখে যেতে কিঞ্চিৎ বিব্রত হলেও প্রতিবাদ করেনি।
“আজ কাল পরশুর গল্প” নামের গল্প সংকলনটির দ্বিতীয় গল্প দুঃশাসনীয়। এটি বাংলা তেরশো তিপান্ন সালের বৈশাখে প্রকাশিত হয়। গৃরনৃথটির ষোলটি গল্পের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাকলীন সমাজ, পরিবেশ, অর্থনীতি, মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। দুঃশাসনীয় গল্পের মোড়কে লেখক মন্বন্তরকালীন অসহনীয় বস্ত্রসংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন। পুঁজিপতিদের ঘরের মেয়েরা যখন নিত্যুনতুন শাড়ি পরে ঘুরছে সেখানে গ্রামের সাধারণ নারীরা ছায়ার সঙ্গী। রাতের অন্ধকারে কেবল ঘর থেকে বের হয়। পালাক্রমে একটুকরো কাপড় পরে নদীর ঘাটে স্নানে যায়। এই অসহনীয় সংকট হৃদয়- মনে কষ্টের সঞ্চার করে। এরই ধারাবাহিকতায় দুঃশাসনীয় একটি কালোত্তীর্ণ গল্প। সমাজের দর্পণ। এই গল্পে লেখক লেখার এক অন্য ভুবন তৈরি করলেন। গোটা গ্রাম জুড়ে বস্ত্রসংকটের কারণে নারীরা সব ছায়ামূর্তি জীবনে বাধ্য হয়।
গল্পের সূচনা হাতিপুর গ্রামে। যারা জানে না এ গ্রামের স্বাভাবিক দৃশ্য তারা হঠাৎ সন্ধ্যার পর গাঁয়ে ঢুকলে ভয়ে আঁতকে উঠবে। দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু তার ওপর চারদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চারণ চোখে পড়ে। নারীরা সব জীবিতের জগৎ পার হয়ে ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছেছে। জমকালো ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে তাদের গা ঢাকা দিতে হয়। অন্ধকারের দিন তবু সুবিধা কিন্তু যেদিন হঠাৎ তারাকার আলো ওঠে সেদিন নারীদের কষ্টের শেষ থাকে না। রাত্রির আবছা আঁধার, কুরু সভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা। অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন বস্ত্রের অসহনীয় সংকট দৃশ্য,
সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আমগোপন করে থাকে। কোনো কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ- ভাই স্বামী- শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না- স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জায়। কোনো বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে -মাসি, খুড়ি, পিসি, মেয়ে, বোন, শাশুড়ি, বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে-এক-একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয়, কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।৩৮
এমন অবস্থার জীবন্ত রূপ এঁকেছেন লেখক। টানা কাহিনি এখানে নেই। একাধিক খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে একটি অনবদ্য গল্প এটি। ভোলা নন্দী কোমরের ঘুনসির সঙ্গে দুআঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতি ধুতিখানা মেয়েদের দান করেছে। তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য। ওই একটিমাত্র ধুতি কাপড় পালাক্রমে বদল করেই ভোলার বউ ঘাটে যায়, ভোলার মেজ ছেলে পটলের বউ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়৷ নারীদের এমন অসহনীয় জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস মেনে নিতে পারে না কেউ। বৈকুন্ঠ মালিক লঘু পরিহাসে স্ত্রী মানদার উলঙ্গ থাকার দুঃখকে হালকা করতে চেষ্টা করে। গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ- কুনের ছাউনির দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে। দাসু কামারের মেয়েটাও ওদের সঙ্গে। সধবা মেয়ে ধোপদস্তুর সাদা থান পরেছে। সুযোগ বুঝে রঘু বিন্দীর সঙ্গেও উদ্দেশ্যমূলক কৌতুক করতেও ছাড়ে না। ভূতি উলঙ্গ অবস্থায় তার বারো বছরের ছেলে কানুর হাসির কাছে শুকনো দুচোখের জ্বালা সামলাতে পারে না৷ গল্পের সব শেষে আসে রাবেয়া ও আনোয়ার। স্বামীড ওপর রাবেয়া ক্ষোভ ফেটে পড়ে। কেন তাকে ছায়া হয়ে বেড়াতে হবে? কাপড় না পেলে তার মরণই ভালো। এমন জীবন সে চায় না। একটুকরো কাপড় নেই শরীর ঢাকার। কেমন স্বামী সে ধিক্কার দেয় এদিকে আনোয়ার তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। একটু ধৈর্য ধরতে বলে। কিন্তু ঘোষবাবু, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা নিত্য-নতুন শাড়ি কোথায় পায় রাবেয়া প্রশ্ন করে। আর তার স্বামীই শুধু কাপড় পায় না। আজিজ এবং সুরেনের কালোবাজারি গ্রামের মানুষ বোঝে না। তারা ওপর ওপর ভরসা দিয়ে চলে,
আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশশ চাষি ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াইশ ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের কাপড় জোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উসকানি জুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গ। সতের মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশ তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেকশ গাঁট ধুতি শাড়ি জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস।৩৯
ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের কোটা তারা যা আদায় করেছে। এবার কাপড়ের জন্য আর তাদের ভাবতে হবে না। মনোহর শা-র প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করলেও হাতিপুরের সবাই আশায় বুক বেঁধেছে। কাপড় আসলে তাদের দুঃখ কাটবে। আশা ছেড়ে দিয়েও বা উপায় কী। দুজন সদরে কাপড়ের জন্য গিয়েছিল। গাঁয়ের সব লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে থাকে হয়তো ছায়ামূর্তিরা বাইরের আলো দেখতে পারবে। কিন্তু কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরি রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যায়। আজিজ, সুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ ড্রাইভারের পাশে বসা। সুরেন ঘোষের ইশারায় লরিটা জোরে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এদিকে কাপড় না নিয়ে গেলে আজ রাবেয়া আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে। আনোয়ার খুব চিন্তায় পড়ে যায়। আজ সে বাড়ি যাবে কোন মুখ নিয়ে। গ্রামে রসুল মিয়ায় দালানে এক ঘন্টা ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে। অবশেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। রসুল মিয়া কদিন পর তাকে একখান শাড়ি দেবেন। এই ভরসায় আনোয়ার বাড়ি ফেরে। লজ্জায়, ঘৃণায় মানবজন্ম থেকে রাবেয়া মুক্তি খোঁজে। যে স্বামী পরার কাপড় দিতে পারে না, শরীরের নগ্নতা ঢাকতে পারে না, তার সঙ্গে বিছানায় শুতে ঘেন্না লাগে রাবেয়ার। ঠাণ্ডা মাথায় রাবেয়া তাই অন্ধকারে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় পুুকুরের জলে জীবন শেষ করে দেয়। এখানেই গল্পের শেষ হয়। লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে,
আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইট- পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁটে পুকুরের জলের নিচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।৪০
গল্পের চরিত্র সংখ্যা অসংখ্য। গ্রামের নারীদের লজ্জা নিবারণের জন্য যেটুকু কাপড়ের দরকার তার কোনটাই দিতে পারে গ্রামের কোন পুরুষ। মানদা, পাঁচী, শিউলি, ভূতি, রাবেয়ার কাহিনি চোখে জল এনে দেয়। নারীর এত দুর্বিষহ জীবন সাধরণের সহ্যসীমার বাইরে। বাস্তব কাহিনির আদলে হলেও সমাজের কীটদের জন্য ঘৃণা জাগে মনে। কাপড়ের সংস্থান থাকার পরও যারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মা-বোনদের রেখেছে উলঙ্গ। আবদুল আজিজ, সুরেন ঘোষদের মতো কালোবাজারি, চোরাকারবারিরা যুদ্ধের বাজারে দরিদ্র মানুষদের শোষণের তীব্রতা দেখিয়েছে। মুখের অন্ন যেমন কেড়ে নিয়েছে। তেমনই লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড়ও তাদের দেয়নি। কিন্তু তাদের বাড়ির মেয়েরা নিত্য- নতুন বাহারি শাড়ি পরে ঘুরেছে গ্রামে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন বোদ্ধা শিল্পী। সমাজের এরূপ অসহনীয় চিত্র তাঁর কলমে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। ভূতি, রাবেয়ারা তৎকালীন সমাজের যাতাকলে পিষ্ট নারীর প্রতীক।
গল্পের চিরাচরিত প্রথা ভেঙে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক অভিনব কায়দায় সমাজের কদর্য দিককে ছোটগল্পের উপাদান করেছেন। বিশেষ কোন নায়কের সন্ধান তিনি করেননি। লেখক এখানে সমগ্র মানুষের দুঃখ গাঁথা তুলে ধরেছেন ফলে কোন একজন ব্যক্তিকে ফোকাস করেননি। এ সম্পর্কে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন-
দুঃশাসনীয় গল্পের পটভূমিতে আছে প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজ। সে সমাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -সমকালীন তেতাল্লিশের মহামন্বন্তরের অব্যবহিত পরবর্তী, আবার এই মহাকালের সঙ্গেই গভীর সূত্রবদ্ধ বস্ত্রসংকট। এমন মন্বন্তরের মতো এই বস্ত্রসংকটও মানুষেরই তৈরি করা- যেসব মানুষ লোভী, স্বার্থপর, আত্মপরায়ণ, অমানবিক থেকেই শাসক- শোষকদের দালালের কাজ করে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালেই জন্ম নেওয়া, শাসকদলের নিজেদের স্বার্থেই তৈরি হওয়া এবং তাদের নিজেদেরই অর্থলিপ্সাকে এরই মধ্যে কুশলতায় পরিতৃপ্ত করতে সবরকম চক্রান্তে উৎসাহী। এই যে মানুষগুলি, এই যে শাসন- ব্যবস্থার বুর্জোয়া অর্থনীতির বনিয়াদ, এ সবই তথ্যের সত্য৷ ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে কঠিন সত্য যাচাই হয়ে। যে কোন সময়ের সমাজ যখন গোষ্ঠীস্বার্থের তথা মঙ্গলের জন্যই গড়ে ওঠে, ব্যক্তিস্বার্থ থেকে গোষ্ঠীর বড় উত্তরণে তার সবরকমের দায়-দায়িত্ব বর্তায়, সেখানে শাসকশ্রেণী ও তার ফড়িয়াদের তৎপরতা স্বার্থে বিপরীত হলেই সমাজের মূল তাৎপর্য ও লক্ষ্যই যায় বদলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য গল্পে সেই সমাজের এক দুঃসময়ের বাস্তব রূপ ও মানুষদের নিয়েছেন।৪১
মহাভারতে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল আর এযুগে দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ করে আবদুল আজিজ, সুরেন ঘোষেরা। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃশাসনীয় গল্পের নামকরণ সার্থক। মন্বন্তরের অব্যবহিত পরবর্তীকালে বস্ত্রসংকট মানবসৃষ্ট। তার নেপথ্যে ছিল তৎকালীন বুর্জোয়া শ্রেণি, দালাল, মুনাফাখোর, মজুতদার, কালোবাজারিরা।
স্বাধীনতা পূর্ব অবিভক্ত বাংলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ তেভাগা আন্দোলন। দরিদ্র কৃষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষে তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়। একদিকে জমিদার, জোতদারেরা তাদের দাবি ছাড়তে চায়নি অন্যদিকে কৃষকদের ন্যায্য দাবির প্রয়াস চলতে থাকে। ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে বাংলার কৃষক সমাজ। রোদ-জলে ভিজে যারা ফসল ফলায় সেই কৃষকেরা বঞ্চিত হয় তাদের ন্যায্য পাওয়া থেকে। লাভবান হন জমিদার, জোতদার শ্রেণি। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস দিনাজপুর জেলার আটোয়ারি থানার রামচন্দ্রপুর গ্রাম থেকে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। সমস্ত ঠাকুরগাঁও মহকুমার ভাগচাষিরা ধান কেটে নিজের গোলায় তুলতে শুরু করে। তাদের কণ্ঠে স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে। জান দেব তবু ধান দেব না। জোতদার, পুলিশ, লাঠিয়ালদের রুখে দিতে গ্রামবাসী সবাই একজোট হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ জানুযারি পুলিশের গুলিতে দিনাজপুর জেলার আদিবাসী ক্ষেতমজুর জমিরউদ্দীন এবং শিবরাম তেভাগা আন্দোলনে প্রথম শহিদ হন। আন্দোলন আরও বেগবান হয়। আন্দোলনের মুখে স্বাধীন ভারতে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর, নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ বিজ্ঞাপ্তি করে তেভাগা আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেন। পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখেন ” হারানের নাতজামাই”; “ছোট বকুলপুরের যাত্রী” গল্প দুটি। গ্রামের দরিদ্র, শোখিু, অত্যাচারিত মানুষের চেতনার স্তরে জেগে উঠেছিল বিদ্রোহ। প্রতিরোধের অভিনবত্বে কিভাবে শাসকের ভ্রুকুটি থেকে রক্ষা পেল কৃষক নেতা ভুবন তারই ভিত্তিতে গল্পটি অনবদ্য রূপ পেয়েছে।
হারানের নাতজামাই এক অনবদ্য গল্প। সাহসী ময়নার মায়ের উপস্থিত বুদ্ধিতে কৃষক নেতা ভুবন কিভাবে পুলিশের হাত থেকে সে যাত্রায় রক্ষা পায় সেই রোমাঞ্চকর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে গল্পে। গল্পের সূচনা হয়েছে কনকনে শীতের রাতে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে কৃষকরা ঘুমে অবচেতন। পালা করে মেয়েরা জেগে ঘরে ঘরে ঘাটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল। এই মাঝ রাতে গ্রামে পুলিশ হানা দেয়। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই আর শ্রীপতি। তার গোপনসূত্রে খবর পেয়েছে কৃষকনেতা ভুবন আজ সালিগঞ্জ গাঁয়ে দাওয়াত খেতে এসেছে। তারা ঠিক খবরটাই নিয়ে এসেছে। এবং বাড়ির চারপাশ পুলিশ, জোতদারের লোকজন ঘিরে ফেলেছে। সরাসরি তার হারানের মেয়ে ময়নার মায়ের ঘরে হানা দিয়েছে। গ্রামের লোকজন একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে। কিছুতেই তারা তাদের নেতা ভুবনকে নিয়ে যেতে দেবে না। পুলিশও চড়াও হয়ে ওঠে। ময়নার মার উপস্থিত বুদ্ধি এ সময় ভুবনকে রক্ষা করে। মেয়ে ময়নাকে নতুন কাপড় পরে সদ্য বিয়ের কনে সাজতে বলে। এদিকে ভুবনকেও শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়। ময়নার মা তাড়াতাড়ি করে বুড়ো হারানকে বুঝাতে সক্ষম হবে না ভেবে আঙুলের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলে। ঘরের বাইরে এসে ময়নার মা বলে ঘরে তার নতুন জামাই এসেছে। মেয়ে জামাই ও মেয়ে ময়না বাইরে এসে ময়নার মায়ের শেখানো অনুযায়ী অভিনয় করতে লাগলো। পুলিশ, জোতদারের লোকেরা বোকা হয়ে যায়। ময়নার আলুথালু চুল দেখে পুলিশের দারোগা মন্মথর নেশার মতো মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে,
ময়নার রঙিন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথর, পিঁচুটির মতো চোখে এঁটে যায় ঘোমটা- পরা ভীরু লাজুক কচি চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি. এ. পাস মন্মথর কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আফসোস হয় যে জোয়ান মর্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এস স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার আলুথালু বেশ।৪২
পাড়ার দুজন বুড়োকে এনে শনাক্ত করায়। ভুবন চুপচাপ গোবেচরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দারোগা মন্মথ শেষমেশ হারান বুড়োকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু মায়নার মা বলে হারান বুড়ো বদ্ধ কালা। দারোগার সামনেই জোর করে ঘরে যেতে বলে ভুবন এবং ময়নাকে। তারা ঘরে গিয়ে ঝাপ ফেলে দেয়। সে যাত্রায় ময়নার মায়ের উপস্থিত বুদ্ধিতে ভুবন রক্ষা পায়। পরদিন সকালে গ্রামে রটে যায় ময়নার মার দুঃসাহসিক কাজ। প্রশংসা হয় সর্বত্র। মুখে মুখে কথা পৌঁছায় হাতিনাড়ার জগমোহনের কাছে। সেই ময়নার স্বামী। জগমোহন শ্বাশুড়ির এই কর্মকাণ্ডের জনয় মেয়েকে আর ঘরে তুলবে না বলে শাসায়। পর পুরুষের সঙ্গে সে ঘরে ঝাপ দেয়। ময়নার বিরক্ত হয়। জামাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে। জোতদার, দারোগার সঙ্গে লড়াই করে চলে কিন্তু অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সঙ্গে পারে না। ময়নার মা বলে ওঠে বাপের সঙ্গে মেয়ে ঘরে ঝাপ দিয়ছে তাতে কী হয়েছে? ভুবন মণ্ডল তাদের দশ গ্রামের বাপ। সে না থাকলে কৃষকরা না খেয়ে মরতো। সব ফসল জমিদার, জোতদারের পেটে যেতো। লেখক গল্পে এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন এভাবে,
‘ বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্ম দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধরইা কই, বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।’৪৩
এদিকে পুলিশ ময়নার ভাইকে ধরে হাজতে দিয়েছে। পরদিন সন্ধ্যাবেলা পুলিশের কানে কথা পৌঁছাতেই তারা ময়নার মায়ের বাড়ি ঘেরাও করে। ঘরে নতুন জামাই দেখে মন্মথ কটুবাক্য বলে। জগমোহন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। এসময় বাড়ির সবাইকে হারানকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দিতেই গ্রামের সবাই জমায়েত হয়। ধীরে ধীরে জমায়েত বাড়তে থাকে। শুধু এ গ্রামের নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ জড় হয়। এ যেন মানুষের সমুদ্র। ‘‘ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারান সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ‘ ছোঁড়া গেল কই? কই গেলো? হায় ভগবান!’’৪৪
লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের ইতি টেনেছেন এখানেই। কাহিনির সূত্রপাত সালিগঞ্জ। ময়নার মায়ের অপ্রতিরোধ্য মনের শক্তিকে ভেঙে দিতে পারেনি শাসক শ্রেণি। তেভাগা আন্দোলনের সময় কৃষক শ্রেণির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষকরা তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করতে সমর্থ হয়। জোতদার, পুলিশের হিংস্র আচরণেও দমে যায়নি আন্দোলন। কৃষক নেতা ভুবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে এসে সাধারণ জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে পড়ে মন্মথ দারোগা। ময়নার মায়ের উপস্থিত বুদ্ধি ও ত্যাগ স্বীকার গল্পটিকে দিয়েছে অভিনব মাত্রা। তেভাগা আন্দোলনে গ্রামের নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সবার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ যেকোনো অন্যায়কে প্রতিহত করতে পারে সহজেই। হারানের নাতজামাই গল্পে কৃষক নেতা ভুবনকে ধরতে যখন পুলিশ, জোরদারের চ্যালারা এসেছে তখন সবার সম্মিলিত প্রতিবাদ মন্মথ দারোগাকে থমকে দেয়। তার সাহস হয়নি সন্দেহের জেরে ভুবনকে গ্রেপ্তার করার। আবার জগমোহনের আগমনেও পুলিশ সাধারণ জনতার কাছে হার মানে। তেভাগা আন্দোলনের সময় সাধারণ জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। পুলিশের আক্রমণ, অত্যাচারও তাদের থামাতে পারেনি। গল্পটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন,
কঠিন প্লটের বন্ধনে কাহিনীবৃত্তটির দুটি ভাগ- প্রথম ভাগে আছে ময়নার মায়ের সঙ্গে ভুবন মণ্ডল, ময়না, মন্মথ, বৃদ্ধ হারাণ ; দ্বিতীয় ভাগে আছে ময়নার মা ও জগমোহন। দ্বিতীয় ভাগে নকল জগমোহনকে দেখে পুলিশ চলে গেলে আসে আসল জগমোহন – হারাণের নাতজামাই। স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে রাতকাটানোর নোংরা অপবাদ শুনে ক্ষুব্ধ জগমোহন শাশুড়ির কাছে এলে, কাহিনির যে দ্বিতীয় ভাগের শুরু তার মধ্যে ময়নার মায়ের চরিত্রের ক্লাইম্যাক্স ও চরিত্রটির স্বভাবে ক্রমশ ব্যক্তি – মা থেকে বিশ্ব- মায়ের স্বভাবে উত্তরণের রচিত হয়ে যায়।৪৫
ময়নার মায়ের সকরুণ মানবতাবোধে কৃষক সম্প্রদায়ের নেতা ভুবন মণ্ডল রক্ষা পায়। বাঙালি দরিদ্র ঘরের মা হিসেবেও ময়নার মায়ের দুঃখের অসহায় চিত্রটি তুলে ধরেছেন লেখক। গল্পের নামের ক্ষেত্রে লেখকের সচেতন দৃষ্টি লক্ষণীয়। কাহিনি অনুযায়ী নাম হতে পারতো ময়নার মা কিন্তু সেখানে কাহিনিটাই ঢাকা পড়ে যেত। কারণ ভুবন মণ্ডলকে জামাই সাজিয়ে পুলিশ, জোতদারকে বোকা বানানো অপরদিকে প্রকৃত জামাই জগমোহনের তোপের মুখে পড়েও পুলিশ জব্দ হয়েছে। ফলে নামের ক্ষেত্রে সরস কৌতুকের ভাবে গল্পটির অনবদ্য রূপ তুলে ধরেছেন লেখক।
ছোট বকুলপুরের যাত্রী ১৩৫৬ (১৯৪৯) সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত একটি গল্পগ্রন্থ। এই গল্পগ্রন্থের ছোট বকুলপুরের যাত্রী শ্রেষ্ঠ নামগল্প । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তিপান্নর মন্বন্তর এবং তেভাগা আন্দোলনের কাহিনি নিয়ে রচিত গল্প এটি। এই গল্পে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের সে সময়কার গ্রামের চাষীদের প্রতিরোধ চিত্র। সর্বহারা, শোখিু, নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ গল্পের কাহিনি বলতে তেমন কিছুই নেই তবু এক অনবদ্য গল্প এটি। এখানে তৎকালীন সমাজে চাষীদের উৎপীড়নের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। ছোট বকুলপুর নামক ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামের মেয়ে আন্না। বাপের বাড়ির এলাকায় পুলিশী সন্ত্রাসের কারণে বউ আন্নার উৎকণ্ঠা ফলে স্বামী দিনমজুর দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ি ছোট বকুলপুরে যাত্রা।
গল্পের সূচনা হয়েছে সন্ধ্যাবেলা একটি লেট করা ট্রেন থমথমে স্টেশনে এসে থামে। অল্প কয়েকজন যাত্রী প্লাটফর্মে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে। সবাই শঙ্কিত এবং স্তব্ধ। ট্রেন থেকে নেমেই সবাই যে যার মতো গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। গভীর রাতে ট্রেনে যাওয়ার জন্য কিছু যাত্রী অপেক্ষা করছে। তবে যারা ট্রেন থেকে নামছে সবাই দ্রুত পদে বেরিয়ে যাচ্ছে। অন্য সময় হলে স্টেশনের সামনে বাজার থেকে কেউ কেনাকেটা করে কিন্তু আজ সেসবের কিছুই চোখে পড়ে দিবাকরদের। একদল সেপাই প্লাটফর্মে যাত্রীর অভাব পূরণ করেছে। তাদের উপস্থিতির কারণ নতুন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। স্টেশন- সংলগ্ন একটি কারখানায় ধর্মঘট হওয়ার সময় ধর্মঘটী শ্রমিকদের তিনজন নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রমিকেরা প্রচণ্ড বাধা দিলে পুলিশের গুলি চলে, রক্তপাত হয়। তাই স্টেশন থমথমে। এসবের মধ্যে দিবাকর দাস, স্ত্রী আন্না এবং ছোট শিশুটিকে কোলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে ছোট বকুলপুর গ্রামে যাওয়ার জন্য গরুর গাড়ি খোঁজ করে। ঘোড়ার গাড়িও থাকে কিন্তু কোনকিছু না পেয়ে গরুর গাড়ি ঠিক করে। এই রাতে দিবাকরের স্ত্রী- পুত্র নিয়ে ছোট বকুলপুরে যাওয়ার কথা শুনে গাড়োয়ানরা অবাক হয়। কেউই আজ ও পথে যেতে রাজি হয় না। ছোট বকুলপুর পৌঁছাতে রাত হবে জেনেই তারা রওনা দিয়েছে। তবে রাত করে মেয়েছেলে আর শিশু নিয়ে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে ঘোড়ার গাড়ির আশাটা ছিল৷ শেষমেশ ভরসা গরুর গাড়ি। সেও গ্রামের মাথায় যাওয়ার আগে নামিয়ে দেবে। গাড়ির গাড়োয়ান গগন ঘোষ কমলতলা পর্যন্ত যেতে রাজি হয়। তবু তাদের প্রায় আধ মাইল হাঁটতে হবে পুরো দেড় ক্রোশ হাঁটার চেয়ে সে অনেক ভালো। গ্রামের সাধারণ খবর, ঘনিষ্ঠতর বিবারণ, অনেক নতুন খবর গগনের কাছে জানা যায়। দূর থেকে তারা শুনতে পাচ্ছিলো ছোট বকুলপুরের অবস্থা শোচনীয় কিন্তু বাপ- ভাইয়ের জন্য আন্নার মনটা ছটফট করতে থাকে। প্রথমদিকে গাঁয়ের ওপর খুব অত্যাচার হয়েছিল কিন্তু গাঁয়ের লোক আটঘাট বেঁধে এমন জেঁকে বসেছে যে এখন ঘোষ বা চৌধুরীদের কোন লোক অনন্ত দু- ডজন রাইফেল ছাড়া ছোট বকুলপুরে ঢুকতেই সাহস পায় না।
এ অঞ্চলে ঘন বসতি। গায়ে গায়ে লাগানো বড় বড় গ্রাম। তবু এখন সন্ধ্যারাতেই রাস্তায় লোক চলাচল নেই। গ্রামে লোকের গা ঢাকা দেওয়ায় চলার পথ ভুতুড়ে রূপ নিয়েছে। ছোট বকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতেই সাত- আটজন গাড়িটি ঘিরে ফেলে। কে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে প্রশ্ন করে তারা।
দিবাকর, আন্না, গগন গাড়োয়ান বেশ বিড়ম্বনায় পড়ে। তল্পিতল্পা খুলে দেখো জেয়ানরা। তারপর দিবাকরের পকেট চেক করতেই একটি কাগজ মোরানো পানের পুটলি পায়। তিনটি পান অবশিষ্ট তাতে। তিন জনের মুখে চলে যায় তা। পান চিবোতে চিবোতে একজন লণ্ঠনের আলোয় কাগজ ধরতে সেখানে বড় হরফের ” ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি” লেখা দেখে। প্রমাণ তাদের হাতের মুঠোয়। গল্পে পাই-
এই ইস্তেহার পেলে কোথা?
ইস্তেহার? ইস্তেহারের তো কিছু জানি না! চার পয়সার পান কিনলাম, পানওলা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।’
‘ পানওয়ালা জড়িয়ে দিলে না তুমি ভেবেচিন্তে পান কিনে ইস্তাহারটাতে জড়িয়ে নিলে?
কেন তা কেন করতে যাব?
আর ঢং না করে এবার আসল নাম বলো দিকি।’
দিবাকার আর আন্না পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।৪৬
গল্পের কাহিনি এখানেই শেষ। গল্পে দিবাকর গোবেচারা নিরীহ মানুষ। তার স্ত্রী আন্নার বাপ- ভাইয়ের খোঁজ নিতে তারা বকুলপুরে যাওয়ার জন্য বের হয়। কিন্তু গ্রামের প্রান্তে পৌঁছাতেই সাত- আটজন সদস্য তাদের জব্দ করে। তাদের ধারণা বকুলপুরের যাত্রী সেজে তাদের চোখকে ধুলো দেওয়া হচ্ছে। এরা সাধারণ মানুষ নয়। আন্না, দিবাকরের জিনিসপত্র সন্ধান করে যখন কোনকিছু মেলেনি তখন একটি পানের সঙ্গে আসা কাগজ নিয়ে তারা সন্দেহের তীর তাক করে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ওপর জমিদার, জোতদার, পুলিশী শাসন- শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি তুলে না ধরলেও রাজনীতির উত্তাপ তাঁর গল্পে পরিস্ফুট। একদিকে কৃষক শ্রেণি অন্যদিকে জমিদার, জোতদার শ্রেণির কড়া শোষণ। তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কৃষক সমাজে যে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় সেই তোপের মুখে পড়ে জমিদার, জোতদারেরা। পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে যতই এই দুর্বল, নিরন্ন, হতভাগ্যদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চেয়েছে একজোট হয়ে সব শোষণের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে তারা। ছোট বকুলপুর একসময় শোখিু হলেও এখন তারা সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার বুজে নিয়েছে। এ সম্পর্কে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন,
সংগ্রামী শ্রমিক- কৃষকদের সমাবেত একতার স্পৃহাই বড় জীবন গঠনের মূল ভিত্তি। স্বাধীনতা – উত্তর বাংলাদেশের বিশেষ সময়ের রাজনীতি ভাবনা, সাম্যবাদের শিক্ষা বাস্তব সত্য ঘটনা এ গল্পের শিল্পে নিখুঁত হওয়ার উপযোগী তাপ সঞ্চার করেছে। যে উত্তাপে খাদ- মিশ্রিত সোনা গলে গিয়ে কেবল সোনাটুকুই সামনে আনে জহুরি স্বর্ণকারদের কাছে, ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী ‘ গল্পে সামগ্রিক অবয়ব অর্থাৎ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ সেই সোনার আভাস দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সাহিত্য-শিল্পী-স্বর্ণকার। একই গল্পে দুই আন্দোলন-শ্রমিক ও কৃষক- এদের শত্রু দালালদের চিনিয়ে দিয়েছেন, আর আশ্চর্য, এরা সকলেই স্বাভাবে একই! শেষ পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের বিষয়- চেতনায় যে নিজস্ব একটি জীবনাদর্শন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়েছিলেন , এই গল্প তা প্রমাণ করে।৪৭
দুটি চরিত্রের সমন্বয়ে তৎকালীন সমাজকে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা একজন গুণী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। ছোট বকুলপুরের যাত্রী আন্না এবং দিবাকর। গল্পের কাহিনি যেহেতু তাদের যাত্রাকে কেন্দ্র করে ফলে গল্পের যথার্থ নামকরণ করেছেন।
‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ পড়তে গিয়ে দিবাকর আর আন্নার সঙ্গে লেখক অভিন্নসত্তা হয়ে যান। গণ-সংগ্রাম এবং পুলিস-গোয়েন্দাতন্ত্রের এই অপূর্ব গল্পটির সূচনা, গতি ও পরিণতির সঙ্গে কেবল লেখকই অগ্রসর হন না; আামদেরও একচিত্ত করে দেন।৪৮
মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প শৈলজ শিলা। এই গল্পটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রমী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধত্তোর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের বিজ্ঞানমনস্ক প্রতিফলন ঘটেছে। দাম্পত্য জীবনের বাইরে কুটিল সম্পর্কে জীবনের রূঢ়তম বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে । মানুষের মনের গহীনে প্রবেশ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পশুজাত অবদমিত সত্তাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজের অনাবৃত রূপকেই নগ্ন করেছেন তিনি। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় কথক যিনি দাদু রূপেই চিহ্নিত তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিধবা পিসির খোশামোদ করা। মাসি মরে যাওয়ার পর তার জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। কোন কাজ না পাওয়া বন্ধুদের উপদেশে একবার বিয়ে করার জন্যও মনস্থির করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পাত্রী পছন্দ হলেও মনের সঙ্গে মিল হয় না। তাই কথক চরিত্রের আর বিয়ে করা হয়ে ওঠে না। হঠাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে দার্জিলিং এবং টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার জন্য কয়েকদিনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ হাত ফসকে কুড়ি ফিট আন্দাজ একটি গাছের গুঁড়িতে আটকে সেবার কোনরকমে জীবনটা রক্ষা পায় দাদুর। কিন্তু সেখানে কথক দাদুর সঙ্গে ঘটে গেলো এক অভাবনীয় ঘটনার। গাছের ওপর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে তার চোখ আটকে যায় আরও ত্রিশ গজ তফাতে পাহাড়ে। সেখানে একটি উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপানো। নিকটে এক বাঙালি ভদ্রলোক বসে আছে। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই পাশে গুহার মধ্যে এক যুবতীকে দেখে কথক। সে তখন জগৎ আলো করা সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে বাঙালি ভদ্রলোককে এবার স্ত্রীটিকে লোকালয়ে নেওয়ার কথা বললে ভদ্রলোক আঁতকে ওঠে। যুবতী মেয়েটি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দশ ঘন্টাই কেঁদে কাটায়। গল্পের কথক তিনি বুঝতে পারেন ভেতরে কোন গোলমাল আছে। দিনদশেক বাদে কথক সব বুঝতে পারেন। গল্পে লেখক প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন এভাবে-
দিন দশক বাদে কিন্তু সব সরল হইয়া গেল। খাদ্য ও দুগ্ধের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিয়া দেখি কচি মেয়েটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে, মা – বাপ কাহারো চিহ্ন পর্যন্ত নাই! মেয়েটার কাছে একটা চিঠি পড়িয়াছিল। যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি ভীষণ। আমার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া নামধাম না দিয়া লোকটি রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছে। যুবতীটি নাকি লোকটির স্ত্রী নয়, বালবিধবা কন্যারত্ন। পাপটাকে যাহাতে গুহাতেই মরিতে দিয়া পালাইয়া গিয়া জগতের কল্যাণ করি, শেষের দিকে এরূপ একটা অনুরোধও জানানো হয়েছে।৪৯
পনের বছর পরে ভূমিকম্প। বাৎসল্যের সিমেন্ট দিয়ে যৌবনের শক্ত গারদ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সব চৌচির। মেয়েটির নাম শিলা। আর কথক এখন দাদু। নাতনিকে খুব কষ্ট সৃষ্টে মানুষ করেছেন। পরম যত্নে লালন পালন করেছেন। নাতনি যেন তার চোখের মণি। একসময় শিলাকে সবাই বিয়ে দেওয়ার কথা বলে। সুন্দরী নাতনিকে দাদুই কেন বিয়ে করছে না বলে মিত্তির, সান্যালেরা ঠাট্টা করতে শুরু করে। একসময় শিলাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ভূপেন নামের এক পাত্রের কথা বলে সান্যালেরা। ভূপেনের কথা শুনতেই শিলার দাদু আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। শিলাও ভূপেনকে পছন্দ করে। ভূপেন মাঝে মাঝে চুপিসারে দেখা করে শিলার সঙ্গে। ভূপেন ভালো মাইনের চাকরি জোগাড় করে বিয়ের প্রস্তাব দিলেও দাদু রাজি হয় না। এর মধ্যে একদিন পাহাড়ি সেই বাঙালি ভদ্রলোক খোঁজে খোঁজে কথকের কাছে উপস্থিত হয়। কিন্তু কথক রূপী দাদু বাঙালি ভদ্রলোককে এড়িয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে তারপর বাড়ি ফেরে। একদিন বর্ষা ব্যাকুল দ্বিপ্রহরে দাদু তার পুরু তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ ঠোঁট দিয়ে শিলার হাসিখুশি মুখ চিরকালের জন্য মুছে দেয়। দাদু মনে করে শিলা ঘুমিয়েছে তাকে চুম্বন করতেই ধরা পড়ে। গল্পের এ পর্যায়ে লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে-
কত কথাই বলিতে পারিতাম। দাদামশাই নাতনির ঠোঁটে চুম্বন করিয়াছে, ইহার কত সঙ্গত ব্যাখাই ছিল। চুম্বন যে লভ- রাইট এর সভ্য সংস্করণ এ কথ আজও যে জানে না দুই-চারিটা সস্নেহ বাণী বলিয়া কত সহজেই তাহাকে ভোলানো যাইত। কিন্তু সে সব কিছু না করিয়া আমি দিলাম ছুট।৫০
ষোলো বছরের পরিশ্রম করেও দাদু প্রিয়ার মন খুঁজে পেলো না। ভূপেনের সঙ্গে শিলার চোখাচোখি, লুকিয়ে কথা বলা এসব দাদু পছন্দ করেন না। একদিন পঁয়তাল্লিশ উর্ধ্ব দাদু শিলাকে নিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে গ্রামের বাস চুকালো। শিলাকে একান্ত করে পাওয়ার বাসনা দাদুর মনকে বারবার বিগলিত করেছে। এই ষোল বছর সে এত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছে। অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য? শিলার সঙ্গে রক্ত সম্পর্কহীন প্রতিপালক বাধ্য হয়েই তাকে মানুষ করে। প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলেও শীলার রূপে ধীরে ধীরে মাতাল হয় দাদু। তার মনে লালসার বীজ জন্ম নেয়। কাছে পেতে চায় শিলাকে।
গল্পে এর বর্ণনা এসেছে এভাবে,
আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়ে কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই ইহার মধ্যে আমিও নাই শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি অনন্ত প্রেম, পশুপাখি মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে- প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীরানক। দু-দিন পরে আমরা যখন শূন্যে মিশাইব এ প্রেম তখনো পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে।৫১
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শৈলজ শিলা’ গল্পটি এক অন্য ধাঁচের গল্প। ফ্রয়েডের লিবিডো চেতনা দেখা দিয়েছে। দাদুর জীবনের চরম সত্য হয়ে উঠেছে তার অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা । মানুষের অনাদিকালের কামনা লিবিডো চেতনাকে ঘিরে। চিরন্তন কামনায় অবদমন সত্য হলেও মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা পশুত্ব যখন বেরিয়ে আসে তখন তা কখনও কখনও কদর্য হয়। দাদু শিলাকে গহীন পাহাড়ে ফেলে না এসে কাছে রেখেছে। মানুষ করে তুলেছে সযত্নে। যখন কথক শিলাকে কলে তুলে নেয় তখন দাদুর যুবক বয়স। ষোল বছর লালন- পালন করা শিলা তার পঞ্চাশোর্ধ দাদুর বুকে আশ্রয় নিতেই পারে। শিলাকে মানুষ করতে গিয়ে দাদু সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হননি। মনের মাঝে শিলাকেই তার পত্নী রূপ দিয়েছেন। নাতনি যত বড় হয়েছে তার রূপের ছটায় দাদু ততই মজেছেন। তার মধ্যের এরূপ বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য শিলার জন্য ভালো পাত্র পেলেও সে তাকে বিয়ে না দিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে। বিবাহের মাধ্যমে অন্য পাত্রের হাতে তুলে না দিয়ে ত্রিশ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও এই প্রৌঢ় দাদু শিলাকে ভোগ করতে চায়। বাহুপাশে আবদ্ধ করে নিজের কামনা চরিতার্থ করার প্রয়াস করে। মানুষের অদম্য কাম চেতনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নবরূপে দান করেছেন। একদিকে শিলা এবং তার রক্ত সম্পর্কীহীন প্রতিপালক দাদু অন্যদিকে বাঙালি ভদ্রলোক এবং তার বালবিধবা মেয়ে। এ গল্পে দুই নারীই তার ভরসা, ভালোবাসার জায়গায় যৌনতাকে দেখতে পেয়েছে। বাঙালি ভদ্রলোক নিজের বাল্যবিধবা মেয়ের পেটে ভ্রুণের জন্ম দিয়ে পাপ বলে পাহাড়ে রেখে যায়। অন্যদিকে সেই মেয়ে শিলাকে মানুষ করে দাদুও তার কামনা চরিতার্থ করতে চেয়েছে। মানব মনের গভীরে লুকিয়ে থাকে এক অদম্য পশুত্ব। লালসার চোখ। সেই লালসার চোখেই রূপবতী নানতিকে বিছানায় নেওয়ার বাসনা। প্রৌঢ়ের অস্বাভাবিক প্রেম নিবেদন শিলার মুখের হাসিকে মলিন করে দেয়। কিন্তু দাদু তার যুক্তি তুলে ধরেছে পাঠকের উদ্দেশে,
হে পাঠক হে পাঠিকা, কৈফিয়ত আমি দিব না। শুধু কয়েকটা কথা বলি। শিলাকে নিয়া আমি যে আদি কাব্য রচনা করিতে চাই, ত্যাগের কাব্য তার চেয়ে বড় এ কথা মানা আমার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভূপেনের হাতে শিলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্যঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুশি হন, কিন্তু তাহাতে আমার কী লাভ? কেনই বা শিলাকে আমি ছাড়ব! বিলাইয়া দিবার জন্যে এত কষ্ট এত যত্নে আমি ওকে মানুষ করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণরক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভূপেনের অধিকার বেশি কেমন করিয়া? আপনারা ন্যায় বিচার করিবেন! আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, শিলাকে আমি ভালোবাসি। আমার যেমন প্রকৃতি আমার ভালোবাসাও তেমনি। দেড়শ কোটি মানুষের মধ্যে আমি যেমন মিথ্যে নই, আমার এই ভালোবাসাও তেমনি মিথ্যা নয়।৫২
কত মহাজ্ঞানী, শক্তিশালী, অসম সাহসের অধিকারী লেখক হলে এমন বিদগ্ধ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব। মানুষের অব্যক্ত কথা কত অবলীলায় বলে ফেললেন মানিক। চিরন্তন যৌনতার কথা এত পরিষ্কার করে খুব কম লেখক তুলে ধরেছেন। মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা অদম্য কামনায় পিষ্ট করে শিলাকে আগলে রাখতে চায় দাদু। গল্পের শেষটি আরও চমক দেয় পাঠকের মনে। এতটা স্পষ্ট জীবনের রূপায়ণ! দাদুর অভিব্যক্তি বোঝে শিলা। ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে সে। কিন্তু দাদুর আত্মপক্ষ সমর্থন। শিলার কাছে জানতে চাশ তার ভয় লাগে কিনা? শিলা জানায় চব্বিশ ঘন্টায় তার ভয় করে। দাদুর অতি সরল তবে বিস্ফোরক প্রতিউত্তর, তবে দরজা খোল। ভয় মিটিয়ে নে।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার শৈলজ শিলা গল্পটির নামকরণ করেছেন শিলার নামানুসারে। শিলার জন্ম যেহেতু পর্বতের গুহায় সেদিক থেকে গল্পের নামকরণ সার্থক। আবার দাদুর কামনার নাগপাশ থেকে সে পর্বতের মতোই নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। সেদিক বিবেচনায়ও গল্পটির নামকরণ যথার্থ। নামকরণের যুক্তিটি অনেকটা লেখক নিজেই যেন তুলে ধরেছেন,
নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দুই হাতে বুক চাপিয়া শুইয়া পড়ি। শৈলে যার জন্ম, শিলা যার নাম, সে শিলার মতো শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিরকাল রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভবিয়া মাথা গরম হইয়া ওঠে।৫৩
মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প সিঁড়ি। মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন বাস্তবতার কদর্য রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এ গল্পের পাত্র-পাত্রীরা স্বার্থান্বেষী জীবনের আড়ালে আবেগ, কামনাকে হাতিয়ার করেছে৷ বেঁচে থাকার লড়াইয়ে যৌবনকে চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তঃসারশূন্য, হিংস্র ও পাশবিক জীবনের নগ্ন রূপ ফুটে উঠেছে এ গল্পে। প্রকৃত ভালোবেসে নয় বরং কিছু পেতে কিছু দেওয়ার মধ্যে তাদের কামনাকে প্রশমিত করেছে। নিম্ন- মধ্যবিত্ত যাদের একবেলা পেটপুরে খাওয়া জোটে না সেই নারী যৌবনকেই তার প্রেমিক নামের ভণ্ডের সামনে মুলোর মতো ঝুলিয়ে রেখেছে। এ গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভদ্রতার মুখেশের আড়ালে ভণ্ডামি, ইতরতা, ছলনা, কদর্যতা, কুটিলতাকে বিশ্লেষণ করেছেন।
গল্পের সূচনা হয়েছে একটি বাড়ির সিঁড়িতে ওঠার কাহিনিকে ঘিরে। একতলার উত্তর প্রান্ত থেকে দোতালা আর তিনতলার মধ্যে দিয়ে একটি সিঁড়ি তেতালার খোলা ছাদে গিয়ে পৌঁছেছে। এই খোলা ছাদে উঠতে বেশ কষরতই করতে হয়। তবে মহামানবরা একটু আগেই পৌঁছে যান। সেক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটু সরস কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি মহামানব বলতে যারা দু-তিন সিঁড়ি একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠে তাদের কথা বলেছেন। তবে গল্পের নায়িকা ইতির বাঁ পা-টি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি ছোট। তাই তার পক্ষে এ সম্ভব নয়। আর মেয়েরা সাধারণত মাহামানব হয়ও না। এ গল্পের নায়ক মানব। ইতির সঙ্গে তার মিষ্টিমধুর সম্পর্ক। যদিও সে সম্পর্কের অন্তারালে রয়েছে জৈবিক চাহিদা। মানব চল্লিশ বছর বয়সের অবিবাহিত পুরুষ। ইতির প্রতি তার মনের টান কতটুকু সে বুঝে ওঠা একটু দুঃসাধ্যই বটে। তবে ইতিও ওসবের ধার ধারে না। তার শুধু বাড়িটায় থাকতে পারলেই হবে। মা- কুষ্ঠ রোগী ভাই নিয়ে কোনরকমে মানবের তিন তলা বাড়িতে ভাড়া থাকে তারা। কিন্তু তিন-চার মাসের ওপর বাড়িভাড়া বাকি। মানবের এই বাড়িতে আরও কয়েক ঘর ভাড়া থাকে। একমাত্র ইতিদের ক্ষেত্রেই সে ভাড়া বাকি রেখেছে। নাহলে তো কবেই বাস গুটিয়ে যেতে হতো। আর ইতিও নিজের যৌবনের মোহে আঁটকে রেখে মানবের কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করতে চায়।
তেতালার বারান্দায় বছর খানেকের ছেলে কোলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে গিয়ে ইতি, মানব থতমত খেয়ে যায়। মেয়েটি নরেনের বউ। মধ্যবিত্ত পরিবারের অস্বচ্ছলতা তার চোখে-মুখে। এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর স্বাধীনতাহীন জীবনের প্রতি ঈঙ্গিত দিয়েছেন। নরেনের ছোট ভাই এসেছে বেড়াতে। তার খাতির- যত্ন আত্তির কোন কমতি না থাকলেও নরেনের বউয়ের কোন সম্মান নেই সেখানে। এত করার পরও তারা খুঁত ধরতেই ব্যস্ত। বৌদির কাছে দশটাকা চাইলেও তার দেওয়ার ক্ষমতা নেই। মেয়েটির এরূপ পরিস্থিতির জন্যও তাকে দায়ী করা হবে। কিন্তু সে তো আর রোজগার করে না। অভাবের সংসারে যেটুকু যা আছে সব স্বামীর হাতে। ইতির ছাদে যাওয়ার প্রসঙ্গে মেয়েটি জানতে চাইলে ইতি ভাড়ার টাকা দিতে গেছিলো সেটিই জানায়। ইতির কাছে মানব জানতে চায়, সত্যি সে ভাড়ার টাকা দিতে এসেছে কিনা! ইতি তখন মানবের কাছে আরও কিছু টাকা ধার চায়। এ প্রসঙ্গটি লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে,
সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মানব বলে, ‘ তোমাদের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি আছে।’
হ্যাঁ।’
মানব রসিকতা করে বলে, ‘ অন্য কোন৷ ভাড়াটে হলে কবে তুলে দিতাম।’৫৪
মানবের কথায় ইতির বেশ মন খারাপ হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাদের মান-অভিমান চলতে থাকে। স্ত্রী চরিত্রের আরো দুটো দিক আবিষ্কার করতে মানব নরেশের বৌ এর কথা বলে। তার প্রসংশা করতেই ইতির মুখে কালো ছায়া। তার যে পোড়াকপাল এমন কারো নেই। মানবের দিকে তাকিয়ে বাপ- মা- ভাই- বোনদের জন্য তার আফসোস হয়। নাহলে ইতির মতো সুখী কে আছে? এমন রাজরাণী কে। আবারও সিঁড়ি তাদের পথচলা। সিঁড়িতে চলতে চলতে ইতি ভোল বদলায়।
দোতালায় সুধার সঙ্গে দেখা হতেই তেতালায় নরেনের বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে গিয়েছিল বলে ইতি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন লেখক। সুধা এবং নগেন। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো নয়। এ বাড়ি সুধা একাই থাকে। সে হাসপাতালের নার্স। আজ তার ডিউটি নেই তাই বাড়িতে। স্বামী নগেনকে ফিরে আসার জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একার সংসারে নারী হয়ে কীইবা তার করার আছে। মানবের কাছে দশ টাকা চাইতে পাঠিয়েছে ইতির মা। টাকাটা নিয়ে ইতি ঘরে প্রবেশ করতেই গল্পের ক্লাইমেক্সে পৌঁছে পাঠক,
…মেয়ের পদমূলে চোখ রেখে বলে, ‘তোর গায়ে রক্ত কিসের লো ইতি?’
ইতি নিশ্চিতভাবে বলল, পাঁচড়া চুলকে ফেলেছি।’
মানব বলে, তোমার পাঁচড়া হয়েছে ইতি?’
প্রশ্ন শোনবামাত্র ইতি বিনা ভূমিকায় খেপে যায়। আর্তনাদ করার মতো বলতে আরম্ভ করে, হ্যাঁ হয়েছে, একশটা হয়েছে। কী করবে তুমি? ঘেন্না করবে? করগে যাও, কে তোমার ঘেন্নাকে কেয়ার করে? দেখছ না ভাইয়ের গায়ে পাঁচড়া, জান না ভাইকে আমি কোলে নিই? পাঁচড়া হবে না তো কী হবে আমার?
তাড়াতাড়ি কুঁজোটা নামিয়ে রাখতে সেটা গড়িয়ে উঠানে পড়ে ভেঙে যায়। মানব সেদিকে চেয়েও দেখে না।
‘ ঘরে যাও ইতি, সুধাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ‘
বলে একেবারে তিন – চারটা ধাপ ডিঙিয়ে মহামানবের মতো মানব উপরে উঠতে আরম্ভ করে।”৫৫
চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে এখানেই গল্পটির শেষ করেছেন লেখক। ইতি গরিব ঘরের দরিদ্র মেয়ে। বাবা- মা- ভাই- বোনের টানাটানির সংসারে কোনরকমে টিকে আছে। আর সে কাজে সহোযোগিতা পেয়েছে চল্লিশ বছরের অবিবাহিত বাড়িওয়ালা মানবের কাছ থেকে। মানবের স্নায়ুতে যৌন অনুভূতি সঞ্চার করে পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি দিয়ে থাকতে পারে ইতিরা। কিন্তু তার সেই যৌনতার আড়ালে নগ্ন জীবন সেখানে ইতির কোন ভবিষ্যৎ নেই। কোন পরিণাম নেই। শুধু ভাড়া না দিয়ে কিভাবে দিন গুজরান করা যায় সে লক্ষেই তার সম্পর্ক। নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারীর বর্বর জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। মানুষের অসহায়ত্ব, বর্বরতা, যৌনতা ভালোবাসার মোড়কে আবদ্ধ। যেখানে আছে শুধু দুজনের স্বার্থসিদ্ধি। মানব চায় ইতি তার মনোরঞ্জন করুক। আর ইতি ভাড়া না দিয়ে, মাঝে মাঝে টাকা ধার নিয়ে সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা তাদের নেই। ব্যক্তিস্বার্থ এখানে বড় হয়ে উঠেছে। ভালোবাসা নামক শব্দটি তাদের স্বার্থের ধাঁধায় অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। নারী জীবনের অসহায় দুঃসহ চিত্রকে দেখাতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সিঁড়িকে রূপকে বেঁধেছেন। সিঁড়ি দিয়ে মানুষ ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে ওঠে। তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। এখানে সিঁড়ি দিয়ে ওটার চিত্র নিরূপণে লেখক ইতির জীবনের সিঁড়ি করেছেন মানবকে। আবার অপরপক্ষে মানবের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে পরিপুষ্ট করতে ইতিকে সিঁড়ি করেছেন। গল্পের নামকরণ এ অর্থে যথার্থ।
মানবের আত্মনিবেদন এবং প্রণয়াভিনয়ের মধ্যে ছিল স্বার্থ। তাই যখন ইতির পাঁচড়ার সন্ধান পায় তখন দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে তেতলায় উঠতে থাকে। সে যেন নিচে নেমে গিয়েছিল, তাকে শুধরে নিলো! মানব এবং ইতি মাত্র দুটি চরিত্রের সন্নিবেশে মানব জীবনের অমোঘ সত্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্থ – সামজিক সমস্যা এবং যৌনতাকে কেন্দ্র করে মানুষ তার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে কখনও কখনও আশ্রয় নেয় কপটতার। এ সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,
“সিঁড়ি গল্পেও আর এক দিক থেকে ‘সরীসৃপেরই’ অনুরণন শোনা যায়। এই গল্পের বাড়িওয়ালা মানব মূলত বনমালীরই স্থূল এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ‘সরীসৃপে’র শেষের পংক্তিগুলিতে তবু লেখকের তিক্ততা খানিকটা আভাসিত হয়েছে- কিন্তু ‘ সিঁড়ি ‘র স্রষ্টা জল্লাদের মতো যান্ত্রিক এবং নৈর্ব্যক্তিক। অক্ষম নিরুপায় ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে টাকা পাওয়ার উপায় না থাকলে তার স্ত্রী- কন্যার দেহের মাধ্যমে বাড়িওয়ালার ক্ষতিপূরণ আদায় করাবার কুৎসিত কাহিনী বিদেশি সাহিত্যেও পড়েছি- কিন্তু মিতভাষণ ও ইঙ্গিতময়তার এই গল্পে যে পাশবতার বিন্যাস ঘটেছে তার তুলনা দুর্লভ। তবে ‘সরীসৃপের’ পরীর চাইতে ‘ সিঁড়ি’র খোঁড়া মেয়ে ইতি শেষ মুহূর্তে কিছুটা আত্মসম্মানের পরিচয় দিয়েছে- সুধার পরিণামের মধ্য দিয়ে ইতির বিদ্রোহ- সম্ভবত সাময়িক বিদ্রোহ- অন্তত একটা নিরুপায় ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ এই গল্পে রেখে যেতে পেরেছে।”৫৬
প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭) গল্পগ্রন্থের একটি অসাধারণ গল্প চোর। গল্পটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জৈবিক তাড়ানা মানব মনের আদিমতম কামনা। মানুষ এই কামনাকে প্রশমিত করতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বকে মস্তিষ্কে ধারণ করেছিলেন বিশেষভাবে। ফলে তাঁর প্রথমদিকের গল্পগুলোতে ফ্রয়েডীয় চেতনা জেঁকে বসেছে। জৈবিক তাড়নার বশবর্তী তাঁর এ পর্যায়ের গল্পগুলোর নায়ক, নায়িকারা।
চোর গল্পটির প্রধান চরিত্র মধু। সে রাতের আঁধারে মানুষের বাড়ি চুরি করে জীবন- জীবিকা নির্বাহ করে। তার বউ কাদু। বউয়ের শখ-আহ্লাদ পূরণের জন্য মধুকে আরও বেশি করে পয়সা জোগাড় করতে হয়। কাদু সুন্দরী। পণ দিয়ে সে বিয়ে করেছে কাদুকে। নিজে রাতের আঁধারে চুরি করলেও বউকে কষ্টে রাখতে চায় না মধু। দুটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই গল্পে আরও স্থান পেয়েছে রাখাল, তার স্ত্রী- কন্যা, রাখালের বড় ছেলে পান্নাবাবু।
গল্পটি সূচনা মধ্যরাতের এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে। বাইরে হঠাৎ বৃষ্টির তাড়া দেখে গোয়ালপাড়ার মধুর বেশ চিন্তা শুরু হলো। শরীরে এখন নেই। সবেমাত্র কালকেই একটু জ্বরটা নেমেছে। শরীরে এখনও ভালো করে বল নেই। বৃষ্টির শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেলে ছেঁড়া কাঁথাটা শরীরে জড়িয়ে সে বিছানায় উঠে বসে। তার মুখের চিন্তার ছাপ। আজ হঠাৎ জল নামলো। শরীরে একটুও পথ্যি পড়েনি। কিন্তু ঝড়-জলের রাতে তো বেরও হতে পারবে না। তবে এই রাতে চুরি করার সুবিধা আছে। ঝড়-বৃষ্টিতে কেউ সহজে বেরুতে পারে না। সবাই ঘরে খিল এঁটে ঘুমোয়। মধুর সিঁদ কাটার বিশেষ দরকার। হাতে তেমন পয়সাও নেই। এদিকে কাদুর মুখটা হাঁড়ি হয়ে আছে। চুরি যখন করে তখন খুব ভালো মতো তার দিন কাটে। কিন্তু মাসের শেষে তার আর কাদুর খুব কষ্টে কাটে। বৈধ উপায়ে আজ পর্যন্ত একটি টাকাও সে উপার্জন করেনি। কোন রকম নীতির ধার মধু ধারে না। পয়সার জন্য করতে পারে না এমন কাজ নেই। সে শিশুর গলার হার ছিনিয়ে নিয়েছে, মেলায় জুয়াড়ি সেজে দরিদ্র কৃষকের টাকায় ভাগ বসিয়েছে, পকেট কেটেছে, দূর গ্রামে গিয়ে পিতৃদায় উদ্ধারের জন্য বাড়ি বাড়ি ভিক্ষাও করেছে। তার এভাবে ভালোয় দিন কাটে। কিন্তু হটাৎ শরীরটা অসুস্থ হয়ে পকেটের টাকাও প্রায় শেষ। আজ ঝড় জলের রাতেই তাকে বেরুতে হবে। কাদুর শখ- আহ্লাদ মেটে না। হঠাৎ তার মুখ ঝামটা শুনে মধুর আরও কষ্ট হয়। সে বাড়ি থেকে বরিয়ে পড়ে। ঝাঁপ খুলে বেরুতে গিয়ে কাদুর মুখে সে কত কথা না শোনে। অন্য হলে আজ কাদুর সুখের সীমা থাকত না। আর মধু তাকে কী দিয়েছে জীবনে। এই হাহাকারে বাইরের জল- ঝড় আরও গতি পায়।
একদিকে কাদুর মুখ ঝামটা, অস্বাভাবিক আচরণ অন্যদিকে মধুর মনে চিন্তার উথাল- পাথাল ভাবনা। কয়দিন আগেই নগদ টাকা নিয়ে রাখাল মিত্তির বাড়ি এসেছে। তার বাড়িটি কাঁচা। আবার টাকা রাখার সিন্দুকও নেই। মধুর লোভ হওয়াতে সে কদুকে তার বাড়ি ঝিয়ের কাজ করতে পাঠিয়েছিল। রাখালের স্ত্রী স্বামী বাড়ি আসলে স্বামীসেবার সুবিধার জন্য ঝি রাখে। মধু সে সুযোগে কাদুকে খবর আনতে পাঠায়। কোথায় টাকা রাখে। কোনদিক সদর দরজা। বাড়ির কোনদিকে সিঁদ কাটালে সুবিধা। মধু রাখাল মিত্তিরের বড় ছেলে পান্নালালকে বেশ ভয় করে। সে তাগড়াই জোয়ান। ঝিয়ের কাজ করতে গিয়ে খোঁজটুকু নিয়ে পরে কাজে না গেলেও চলবে বলে কাদুকে জোর করেই মোটামুটি সে বউকে রাজি করে। কিন্তু কয়দিন পর কাজ ছাড়তে বললে কাদু আর কাজ ছাড়ে না। নানরকম বাহানা বানায়। মাঝখানে একদিন মধুর কাছে রাখালের বড় ছেলে পান্নাবাবু এসে অদ্ভুত প্রস্তাব দেয়। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টির বর্ণনা করেছেন এভাবে,
রাজু কাল শ্বশুরবাড়ি যাবে মধু। তোমার বউকে সঙ্গে দিতে হবে। বেশিদিনের জন্য নয়, ধর- এই দিন পনের।’
মধু রাজি হয় নাই।
কিন্তু রাখালের মেয়ের ঝি হইয়া তাহার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জনয় কাদুর উৎসাহ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। যাওয়ার অনুমতি না পাইয়া দুদিন কাদু তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে নাই।৫৭
দশ টাকার ছুতা দিয়ে কাদু দুঃখ পেতে থাকে। গল্পের শেষে লেখক এই ধোঁয়াসার খোলাসা করেছেন। কাদুর এবং মধুর মধ্যে তখন থেকেই কেমন জানি দুরত্ব। মধুর অসুস্থ শরীরে সে সিঁদ কাটতে পারেনি। কাদু এবং মধুর মান- অভিমান- অভিযোগের পালা শেষ হতেই মধু বেরিয়ে পড়ে রাখাল মিত্তিরের বাড়ির উদ্দেশে। বৃষ্টি ধরে আসলেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মধু চুরির জন্য বেরিয়ে পড়ে। যেতে যেতে সবচেয়ে জরাজীর্ণ বাড়িটি দেখে তার মনে হয় এ বাড়ির বউটি সাতদিন না খেয়ে থাকলেও মনে হয় স্বামীকে এই ঝড়-ঝঞ্ঝার রাতে বেরুতে দিত না। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলে। সামনে কুমারপাড়ার ঘাট। সেখানে কিছু নৌকা ভেড়ানো। একটি নৌকা ছইয়ের মধ্যে আলো জ্বলছে দেখে মধু অবাক হলো। কিছুদূর এগিয়ে নৌকার মধ্যে পান্নাবাবুকে দেখে মধু বেশ চমকিত হলো। কিন্তু তার মনে প্রশান্তিও কাজ করে। তাহলে রাখাল মিত্তিরের বাড়ি চুরি করতে তার বেশ সুবিধা হবে। অন্ধকার রাতে সন্তর্পণে সে গ্রামে প্রবেশ করে। রাখাল মিত্তিরের বাড়িতে সিঁদ কাটতে গিয়ে তার মেয়েকে দেখে মধুর মন এলোমেলো হয়ে পড়ে। নানাবিধ স্বপ্ন তার চোখে ভাসে। ওই সুডোল দেহ আর ঠোঁট যদি তার হতো সেসব ছেড়ে দিয়ে সৎ পথে উপার্জন করতো। আর দশটা মানুষের মতো ডাল, ভাত খেলেও সুন্দর মতো বেঁচে থাকতো। রাখালের বিবাহযোগ্যা মেয়েটি তার সারা শরীর মনে শিহরণ জাগায়। হয়তো এই মেয়ের বিয়ের জন্যই রাখাল টাকা রেখেছে। সে যদি মধু হতো। লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে মধুর জীবন রূপায়িত হয়েছে এভাবে,
চোরের জীবন বড় একা। ওদের আপন কেহ নাই। কবির মত, ভাবুকের মত, নিজের মধ্যে ওরা লুকাইয়া বাস করে। যে স্তরের অনুভূতি ওদের থাক, যে রুক্ষ প্রাচীন সীমানার মধ্যেই ওদের কল্পনা সীমাবদ্ধ হোক, ওদের অনুভূতি, ওদের কল্পনা ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র, পরিবর্তনশীল। অনেক ভদ্র লোকের চেয়ে ওরা বেশি চিন্তা করে। জীবনের এমন অনেক সত্যের সন্ধান ওরা পায়, বহু শিক্ষিত সুমার্জিত মনের দিগন্তে যাহার আভাস নাই। কবির নেশা নারী, চোরের নেশা চুরি। আসলে ও দুটো নেশায় মানসিক উর্বরতা বিধানের পক্ষে সমান সারবান।৫৮
মধু সব আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটিয়ে শেষমেশ রাকলের বাড়ির চুরিটা সেরেই ফেলে। সে যে নরকে বাস করে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি পায় না রাখালের মেয়েটাকে দেখে তার বারবার মনে হতে থাকে। তার দুর্গন্ধযুক্ত ঘর, টাকা দিয়ে কেনা হীনচেতা নারী, তার লোভ ও ভয়ে তার একটানা জীবন এখন অসহনীয়। সেও তো রাখলের মতো স্ত্রী- পুত্র- কন্যা নিয়ে বাস করতে পারে। ঘুমন্ত কিশোরীকে ভালোবেসে সে নতুন জীবন যদি পেতো। ভাবনার ঘোর কাটে একসময় সে বাড়ির পথে হাঁটা শুরু করে। আজ সে অনেক কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরবে। কদুকে সুখী করবে। ঘাটের পথে আসতেই নৌকা নেই। মধুর একটু খটকা লাগলো। কিন্তু আজ তার আনন্দের দিন। এত ভাবলে চলে না। তাই বাড়ি ফিরতেই তার তাড়া। বাড়ির আঙিনায় পা দিয়ে থমথমে বাড়ি। কোথাও কদুর দেখা নেই। ঘরেও সে ঘুমিয়ে নেই। কোথায় গেলো কদু? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি শেষ করেছেন চমক দিয়ে,
মধুর মনের উত্তেজিত আনন্দ সহসা নিঝুম হইয়া গেল। টাকা ও নোটে ভরা বালিশের খোলটি পায়ের কাছে মাটিতে পড়িয়াছিল। সেদিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল আবার তাহার জ্বর আসিতেছে। সহসা মধু বীভৎস হাসি হাসিল। রাখালের ঘরের দিকে চলিবার সময় যে যুক্তি দিয়া নিজের চৌর্যবৃত্তিকে সে সমর্থন করিয়াছিল সেই কথাটি হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।৫৯
গল্পের এখনেই ইতি টেনেছেন লেখক। তাঁর চোর গল্পটি এক অনবদ্য গল্প। মধু চুরি করে অর্থ উপার্জন করে। সে রাখালের ঘরে চুরি করেছে শেষমেশ। কিন্তু রাখালের ছেলে পান্নাবাবু তার ঘরেও সিঁদ কেটেছে। চুরির পথ ভিন্ন হলেও কে না চুরি করে। মধুর জীবন সংগ্রাম কদুকে ভালো রাখার জন্য। লোভ, লালসা, জৈবিক তাড়নায় কদু মধুর অলক্ষ্যে পান্নাবাবুকে সঙ্গী করেছে। মধু উপেক্ষিত হয়েছে। কাদুর রূপে মজে চড়া পণ দিয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু স্বামীর প্রতি কাদুর মধ্যে ভালোবাসা নেই। স্বামীকে ভালোবেসে আগলে রেখে তাকে সৎ পথে আনার তাড়না নেই। কাদু নিজের স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত থেকেছে। রূপোর গয়না কিভাবে সোনার গয়নায় স্বামী তাকে খুশি করতে পারবে সে তাগাদা দিয়েছে। কিন্তু স্বামীর অসুস্থ শরীরে তার প্রতি কোন মমত্ববোধ পরিলক্ষিত হয় না। কাদু অতি স্বার্থন্বেষী, লোভী। রূপের মোহে জড়িয়ে সে মধুকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু মধুর ঘরে সুখের বদলে দুঃখের সংসার। চার বছর কাটানোর পর তার মনের কোণে জমেছে ক্ষোভ। একটু ভালো থাকার ইচ্ছেয় নিজের আখের গুছিয়ে চম্পট দেয় কাদু। পান্নাবাবু মধুর বুকে সিঁদ কেটেছে৷ সেই তো মধুর থেকে বরং বেশি চোর। এ সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,
চোর গল্পে চোর মধুর পাপকে ছাপিয়ে আরো বড় পাপ করেছে রাখালের ছেলে পান্নাবাবু। মধুর চুরি করতে হয় বাঁচার প্রয়োজনে- আর রাখালের ছেলে তার স্ত্রী কাদুকে অপহরণ করে লালসার তাড়নায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিটি এই গল্পে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : ‘ জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।’ উপরতলার মানুষ আর মাটিঘেঁষা মানুষের চৌর্যবৃত্তির পার্থক্য এই গল্পে অতিপ্রতক্ষভাবে ধরা দিয়েছে। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ভবিষ্যৎ পরিণতির একটি প্রচ্ছন্ন আভাস ‘ ‘প্রাগৈতিহাসিক ‘ বা ‘চোর’ জাতীয় গল্পে সংকেতিক হয়েছে।৬০
কথাসাহিত্যাঙ্গনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্বিভাবকালে অনেকেই সাহিত্যজগতে তাঁদের স্থান পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ছাত্র মাত্র। এ সময় হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে প্রথম গল্প ‘আতসী মামী’ পাঠিয়ে দেন বিচিত্রা পত্রিকায়। তখনকার দিনে বিচিত্রা একটি জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প আতসী মামী। কাকতালীয়ভাবে হলেও এরপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য জগতে আপন রাজত্ব গড়ে নিয়েছেন একের পর এক পাঠকগুণমুগ্ধ উপন্যাস, গল্প রচনা করে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ এবং কল্লোলগোষ্ঠী থেকে অন্য ধারায় সাহিত্যকে দেখার চেষ্টা করলেন। যে কথা আগে কেউ বলেননি, সে কথা বলতেই যেন এলেন তিনি।
ছাত্রাবস্থা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রবল ভালোবাসা ও ঝোঁক ছিল। ফলে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে তিনি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নতুনভাবে উপন্যাস, গল্পে মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানচেতনার মাধ্যমে মানবমনের অন্তর্নিহিত জটিলতার অনুসন্ধান করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সিগমুন্ড ফ্রয়েডের গ্রন্থ অনুশীলনের মাধ্যমে নর-নারীর চেতন-অবচেতন সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। প্রথম পর্যায়ের গল্পে দেখা যায় তার প্রকাশ। ফ্রয়েড যেমন জীবনের শেষ পর্যায়ে অবৈজ্ঞানিক অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তাঁর অনুসারীরাও অন্য পথের সন্ধানে নামেন। প্রথম পর্যায়ে মানিক ফ্রয়েডীয় হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মার্কসীয় ভাবনার সন্ধান করেছেন।
জননী, দিবারত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি উপন্যাসে নর-নারীর হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করে তাদের কামনা-বাসনা, জীবনের জটিলতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সহরতলি উপন্যাসের মাধ্যমে প্রথম মার্কসীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে। নতুন দ্বার উন্মোচিত করেন। মানুষের অন্তর্গত দিক থেকে বহির্জগতে প্রবেশ করেন লেখক। পুঁজিপতি ও মেহনতি মানুষের দ্বন্দ্ব রূপায়ণ করেনে। শুধু উপন্যাসেই নয়, গল্পের ক্ষেত্রেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই ভাগে বিভাজন করা যায়। ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয়।
প্রাগৈতিহাসিক গল্পগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি গল্পই নর-নারীর লিবিডো চেতনাকে দেখনোর চেষ্টা করেছেন লেখক। শৈশবে মাতৃহীনা লেখক নিজেতেই সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, সাংসারিক টানাপোড়েন, মায়ের অসুস্থতা, মৃত্যু, বাড়ি বিক্রি, পিতার প্রতি ভাইদের অবহেলা সব এসে জড়ো হয় লেখকের জীবনের পাতায়। আর এসব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে তার কালজয়ী উপন্যাস, গল্পের চরিত্র।
প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখু, পাঁচীর আদিমতম কামনাকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ভিখু ডাকাত দলের সর্দার থেকে রাস্তার ভিখারী, পেহ্লাদের বউয়ের প্রতি ভিখুর জৈবিক আকর্ষণ, বিন্নু মাঝির সুখী জীবন ভিখুর জীবনকে অর্থহীন করে তোলে। একসময় যে নিজের মর্জি মতো নারীকে ভোগ করেছে। ডাকাতি করতে গিয়ে নির্জীব হাত তবু জৈবিক চাহিদার পথ রুদ্ধ হয় না। আদিমতম তাড়নাকে পরিপূর্ণ করতেই বসিরকে হত্যা এবং পাঁচীকে নিয়ে পলায়ন। অন্ধকারের মতো তাদের সন্তানের মাংসল দেহেও এই আদিমতম লিপ্সা প্রাগৈতিহাসিক হয়ে থাকবে।
আত্মহত্যার অধিকার, সমুদ্রের স্বাদ, আপিম, বিবেক, আজ কাল পরশুর গল্প, চোর, সিঁড়ি প্রভৃতি গল্পে নিম্ন- মধ্যবিত্তের দুঃখ- দারিদ্র্য পীড়িত জীবনের অসহনীয় বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। শৈলজ শিলা, সরীসৃপ, যাকে ঘুষ দিতে হয়, কুষ্ঠ- রোগীর বৌ প্রভৃতি গল্পে উঠে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক গল্পের মতো মানুষের আদিমতম কামনা। দুঃশাসনীয় গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃত্রিম বস্ত্র সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। এই গল্পে দেখানো হয়েছে যুদ্ধের বাজারে দালাল, মুনাফাখোর, মজুতদারদের আঙুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হওয়া আর সাধারণ জনগণের দুর্বিষহ চিত্র। রাতের অন্ধকারে নারীরা ছায়ামূর্তি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দিনের আলোতে তারা আসতে পারে না। কিন্তু ঘোষ, আজিজদের পরিবারের মেয়েরা নিত্য- নতুন শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়োডীয় চেতনা ছেড়ে মার্কসের অর্থনৈতিক অসমতা, নিরন্ন মানুষের পক্ষে কথা বলা, শোষণ, বঞ্চনা নিয়ে কথা বলেছেন হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী প্রভৃতি গল্পে। কৃষকদের ওপর জমিদারী শোষণের মুখে ১৯৪৬ এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাংলার জনগণ আন্দোলন করে। যা ইতিহাসে তেভাগা আন্দোলন নামে আখ্যায়িত। উৎপাদিত ফসলের দুই- তৃতীয়াংশ ভাগচাষী পাবে। জমির মালিক এক- তৃতীয়াংশের বেশি আদায় করতে পারবে না। তেভাগা আন্দোলনের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী গল্প দুটি। কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে পড়ে মন্মথ দারোগার নাজেহাল অবস্থা এবং ময়নার মার উপস্থিত বুদ্ধি সবমিলে অনবদ্য গল্প এটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবনে বাংলা সাহিত্যকে দু হাত ভরে দিয়ে গেছেন। তাঁর মনন, মেধা, সাহিত্য সাধনার একাগ্রতা দিয়ে রচনা করেছেন কালোত্তীর্ণ সাহিত্য।
তথ্যসূত্র:
১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৩
২। তদেব, পৃ. ৫
৩। তদেব, পৃ. ১০
৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা, কবি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৫৫
৫। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৭৩২
৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ২০
৭। তদেব, ১৯
৮। তদেব, পৃ. ২৫
৯। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৭২৬
১০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ২৬
১১। তদেব, পৃ. ৩৫
১২। তদেব, পৃ. ৩৬
১৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৪৭
১৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প- বিচিত্রা, কবি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৫০
১৫। সাহেদ মন্তাজ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরালে কথকতা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২, পৃ. ১৫৬
১৬। তদেব,পৃ. ১৫৬
১৭। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৭৯৬
১৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৫০
১৯। তদেব, পৃ. ৫১
২০। তদেব, পৃ. ৬০
২১। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৮১৩
২২। তদেব, পৃ. ৮১৫
২৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৬৪
২৪। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৭৭৯
২৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৬৮
২৬। তদেব, পৃ. ৭৩
২৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প- বিচিত্রা, কবি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৪৯
২৮। সাহেদ মন্তাজ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরালে কথকতা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২, পৃ. ১৯৬
২৯। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৭৭
৩০। তদেব, পৃ. ৭৯
৩১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা, কবি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৫৮
৩২। সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ২১৫
৩২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৮৫
৩৩। তদেব, পৃ. ৮৯
৩৪। ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত যুগলবন্দী, গল্পকার: তারাশঙ্কর-মানিক, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ০১
৩৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৯১
৩৬। তদেব, পৃ. ৯২
৩৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ১০১
৩৮। তদেব, পৃ. ১১১
৩৯। তদেব, পৃ. ১১৩
৪০। তদেব, পৃ. ১১৫
৪১। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৭৬৯
৪২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ১৩২
৪৩। তদেব, পৃ. ১৩৬
৪৪। তদেব, পৃ. ১৩৭
৪৫। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৭৪৬
৪৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ১৫১
৪৭। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, নবম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৯, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পৃ. ৭৬১
৪৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা, কবি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৬০
৪৯। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠগল্প, অবসর, অষ্টম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, অবসর, ঢাকা, পৃ. ১১৯
৫০। তদেব, পৃ.২০২
৫১। তদেব, পৃ. ২০৪
৫২। তদেব, পৃ. ২০৪
৫৩। তদেব, পৃ. ২০৫
৫৪। তদেব, পৃ. ২৯৯
৫৫। তদেব, পৃ. ৩০২
৫৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা, কবি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৫০
৫৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৩৭, পৃ. ১৮
৫৮। তদেব, পৃ. ২৪
৫৯। তদেব, পৃ. ২৮
৬০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প-বিচিত্রা, কবি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৫৫