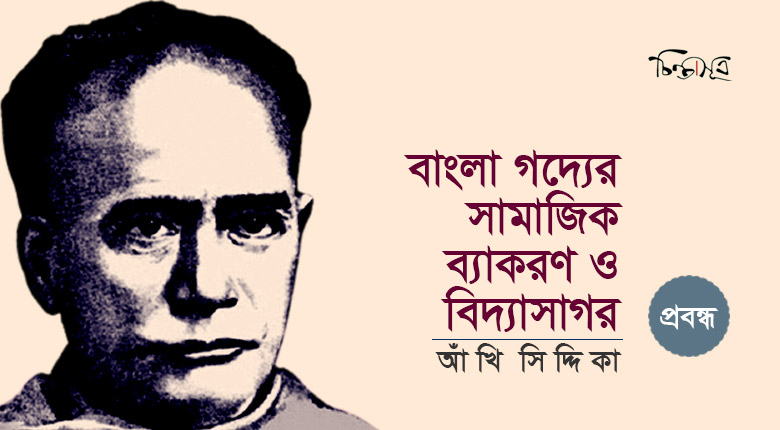 প্রবন্ধের শুরুতেই প্রমথনাথ বিশির একটি উক্তি উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেছেন, ‘বাংলা গদ্য সংসারের নিত্য চলাচলের ওপর এসে পড়েছে। এতকাল যা মন্থরভাবে চলছিল, কয়েকজন বলবান মাল্লার গুণের টানে বা সরকারি সাহায্যের পালের বাতাসে এবারে তা হাজার বৈঠার ক্ষিপ্র তাড়নে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বৈঠাওয়ালাদের প্রধান ঈশ্বরগুপ্ত, আর হালে অবশ্যই আছেন মনীষী রামমোহন। গদ্য সাহিত্য ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের বাহন। এইসব মাঝিমাল্লাদের সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, দিল্লির বাদশার খেতাবপ্রাপ্তি সত্ত্বেও রামমোহন মধ্যবিত্ত ছাড়া কিছু নয়। বহুজন কর্তৃক বহুতর প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষায় এসেছে নমনীয়তা; তাতে ঢুকেছে নতুন শব্দসম্ভার তাদের ইঙ্গিত ও স্মৃতির পরিমণ্ডল দিয়ে, বেশ বুঝতে পারা যায় যে অনেকগুলো কলমের প্রচেষ্টায়, তাদের মধ্যে আনাড়ির কলমের সংখ্যাও কম নয়, ভাষার কর্দম উত্তমরূপে মথিত হয়েছে, এবারে মূর্তি গড়ে তুললেই হয়, এলেই হয় শিল্পী। এলেন বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বিদ্যাসাগর।’
প্রবন্ধের শুরুতেই প্রমথনাথ বিশির একটি উক্তি উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেছেন, ‘বাংলা গদ্য সংসারের নিত্য চলাচলের ওপর এসে পড়েছে। এতকাল যা মন্থরভাবে চলছিল, কয়েকজন বলবান মাল্লার গুণের টানে বা সরকারি সাহায্যের পালের বাতাসে এবারে তা হাজার বৈঠার ক্ষিপ্র তাড়নে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বৈঠাওয়ালাদের প্রধান ঈশ্বরগুপ্ত, আর হালে অবশ্যই আছেন মনীষী রামমোহন। গদ্য সাহিত্য ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের বাহন। এইসব মাঝিমাল্লাদের সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, দিল্লির বাদশার খেতাবপ্রাপ্তি সত্ত্বেও রামমোহন মধ্যবিত্ত ছাড়া কিছু নয়। বহুজন কর্তৃক বহুতর প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভাষায় এসেছে নমনীয়তা; তাতে ঢুকেছে নতুন শব্দসম্ভার তাদের ইঙ্গিত ও স্মৃতির পরিমণ্ডল দিয়ে, বেশ বুঝতে পারা যায় যে অনেকগুলো কলমের প্রচেষ্টায়, তাদের মধ্যে আনাড়ির কলমের সংখ্যাও কম নয়, ভাষার কর্দম উত্তমরূপে মথিত হয়েছে, এবারে মূর্তি গড়ে তুললেই হয়, এলেই হয় শিল্পী। এলেন বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বিদ্যাসাগর।’
উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণে বিদ্যাসাগর অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)-এর ভূমিকা বা এমনভাবে যদি বলি উনিশ শতকের বাংলাদেশ ধন্য হয়েছিল যেসব বরণীয় মানুষ ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে, সেসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আজও তিনি। যুগ ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড আক্রমণের মুখেও একটি ব্যক্তিত্বের কথা আমরা কোনোক্রমেই তার নাম ভুলতে পারি না। যে ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য যুগ যুগান্তরেও ক্ষীণ হয়নি; আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যিনি বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।
মানসিকতার উদারতায়, সমাজ সংস্কারের তৎপরতায় আর পাণ্ডিত্যের গভীরতায় তার যে চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা এদেশের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার সফল কর্মবহুল জীবন যেমন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে ছিল গুরুত্বপূর্ণ, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ছিল তেমনি বিশিষ্টতার অধিকারী। বিশেষ করে বাংলা গদ্যে ছন্দবোধ, প্রবাদ প্রবচনের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবহার এবং তিনিই প্রথম বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে গদ্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। যা তাকে ‘বাংলা গদ্যের জনক’ হিসেবে বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এমন সব সত্যিই সাহিত্যের বর্ণনা অবশ্যসম্ভাবী। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণে বিদ্যাসাগর এভাবে বললে তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও ঈশ্বরচন্দ্রের ভুমিকা আলোচনার দাবি রাখে। তাই বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বলতে হলে সেই সময়ের আগের ও তৎকালীন সময়ের সমাজ ও গদ্যের ধারবাহিকত চিত্র কিছুটা আলোচনার দাবি রাখে।
১৭৭৮। হলহেড নামে একজন ইংরেজ ‘A Grammer of the Bengal Language’ দিয়ে বাংলা গদ্যের গোড়া পত্তন করলেন ভারতীয় উপমহাদেশে। তারপরই বাংলা গদ্য হামাগুড়ি দিয়ে আসতে শুরু করলো বাংলাসাহিত্যে, কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় সমাজের প্ল্যাটফরমে অর্থনীতি’র কাঁধে ভর করে ঔপনিবেশিকতার যুগে ঔপনিবেশিক হয়ে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথপ্রদর্শক আরেকজন ইংরেজ মিশনারি উইলিয়াম কেরি, তিনিই হয়ে গেলেন বাংলা ভাষায় গদ্যচর্চার পথিকৃৎ।১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার কাল থেকে, বাংলা গদ্যরচনার গুরুতর প্রচেষ্টা শুরু। তবে বিদেশি পৃষ্ঠপোষকতা আর তার আগের দেশি প্রচেষ্টার মধ্যে সুনীতিকুমার একটা সময় সাধনের প্রয়াস পান, Out of the large number of forms, dialectical, and archaic, which prevailed in Middle Bengali, specially in the verb, documentary and epistolary Bengali of the three centuries 1500-1800 was evolving a standard language for prose, in which only a few recognized forms were used; and the documentary and epistolary Bengali, based as it was on the speech of the 15th century, or it may be, of the 14th, was adopted as the Language of ordinary prose composition, when the advent of western learning brought in a sudden demand for a prose style. তবে পুরনো বাংলা গদ্য বলতে যে শুধু দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র বোঝায় না, সেকথা আরেকবার মনে করিয়ে দেন সুকুমার সেন (১৯৩৪)। বৈষ্ণব সাধকদের নিবন্ধের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবের সম্ভাবনা প্রাচীন সাহিত্যে অসম্ভাবিত ছিল, কেননা ইহার আবেদন তত্ত্ববোধে এবং যুক্তিজ্ঞানে।’ এই ধারণা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কৃতিত্বে অতিরিক্ত বিশ্বাস যে পুরোনো বাংলা গদ্য সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট মনোযোগী হতে দেয়নি। গদ্য বা গদ্যরীতি ও গদ্যসাহিত্যের পার্থক্যের ধারণাও অনেকের মনে কাজ করেছিল। তাছাড়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলো এক করার চেষ্টাও হয়নি, তেমন করে উপাদান-সন্ধানের কাজও হয়নি। সুতরাং প্রাক্-উনিশ শতকী বাংলা গদ্য সম্পর্কে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি।
চিঠিপত্র লেখা এবং দলিল-দস্তাবেজ লেখার প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের সূত্রপাত। দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সংস্কৃতি ও পার্সি; এই দুই ভাষার প্রভাবে পরিকীর্ণ। আদি সাহিত্যিক গদ্যে কথ্যভাষার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এলাকার কথ্য ভাষা প্রতিফলিত যেমন, ‘‘ফ্লান্দিয়া দেশে এক সিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল। লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতামাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাত্রে পৌঁছিল। তাহার এক বইন আছিল; তাহার পন্থে লাগাল পাইল; ভাইয়ে বইনরে চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল, ‘তুমি কী আমারে চিন?’ ‘না, ঠাকুর’ বইনে কহিল। সে কহিল, ‘আমি তোমার ভাই।’ ভাইয়ের নাম শুনিয়া উনি বড় প্রীত হইল। ভাইয়ে ঘরের খবর লইল, জিজ্ঞাস করিল, ‘আমারদিগের পিতামাতা কেমন আছেন?’ বইনে কহিল, ‘কুশল।’ দুইজনে কথাবার্তা কহিল।’’
গদ্য জনতার কাছে আসেনি, আসেনি জনতাও গদ্যের কাছে। কারণ জনতা মানে কৃষক শ্রেণী, নীলচাষি শ্রেণী। তারাই সংখ্যায় অধিক। তারা আসেনি। এটা তাদের সমস্যা। তাই রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্তদেব মহাশয়রা মধ্যবিত্ত স্বার্থ রক্ষায় পৃথকীরণ করেন তাদের ভাষা ব্যবহারের মাত্রাজ্ঞানকে।
এমন অবস্খার পরপরই সাহেব-শাসিত কলকাতায় যে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠলো তাদের নিয়ে শুরু হলো নতুন চিন্তা-চেতনা,সৃষ্টির আলোড়নে নবজাগরণ। এরা ছিল কৃষককুলের ঠিক একটু ওপরের শ্রেণী।জাতীয়তাবাদী অনুভুতির ও চেতনার যে বিকাশকে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল তা আসলে ভ্রান্তই ছিল, তা ছিল মুৎসুদ্দী শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ। কলকাতাকে বৃটিশ পুঁজিবাদের পরিপোষক হিসেবেই ব্যবহার করেছিলো সুকৌশলে আর ইংরেজ বিতাড়নের নামে যে জাগরণ তৈরি হয়েছিল, তা আসলে ইংরেজ বিতাড়ন নয়, বরং ইংরেজকে রাজনীতি, অর্থনীতির মূল ছেড়ে দিয়ে তার ছত্রছায়ায় সমাজকে বাঁচানোর চেষ্টা। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সেই চোখে ঠুলি লাগিয়ে অন্ধের পথ চলার মতো। দেশীয় কুটির শিল্পকে গোড়া থেকে উঠিয়ে, উদ্বৃত পুঁজিকে শিল্পে ব্যবহার না করে, উৎপাদিত পণ্যের বাজারে কাঁচামাল ও খনিজ পদার্থকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবে। এই কাণ্ড কখনো রেনেসাঁর মিত্র হতে পারে না। বরং উলটো যাত্রা। সামন্তবাদকে নিগড়ে উঠিয়ে পুঁজিবাদের পত্তন ত্বরান্বিত করার ধান্দা ছিল তৎকালীন ইংরেজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগকারী ফেউদের। ইংরেজ শাসন মস্ত এক ব্যবসায়িক জাল ফেললো দেশজুড়ে, পাল্টে যেতে লাগলো অর্থনীতির চেহারা, সমাজের তক্তপোষ, এসে গেলো রেল, ডাক, তার। স্থাপিত হলো ইংরেজ প্রশাসনিক কেন্দ্র। বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলো কেন্দ্রীয় শাসনের কব্জাভুক্ত হলো। পাল্টে গেলো শিক্ষা পদ্ধতি। শিল্পরুচি আর সংস্কৃতি, সাহিত্যে, নৈতিকতায় পদ্যের সুর কেটে বেরিয়ে এলেো গদ্য।
ইংরেজ আসার আগে এদেশে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছিল কবিতা, গীতল, পদ্য। দলিল-দস্তাবেজে যে গদ্য একসময় ব্যবহার হয়েছে তাকেও গদ্য বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাকে ‘গদ্যবোধশক্তি’। অবশ্য ইংরেজ আসার পূর্বে গদ্যের জন্য যে কোলাহল অর্থাৎ যোগাযোগ, আদান-প্রদান, সামাজিকতা প্রয়োজন ছিল, তা ছিল না। কবিতা একা একা থাকতে পারলেও গদ্য সমাগম চায়।
দরিদ্রকে আরও দরিদ্র, ধনীকে আরও ধনী করা অনিবার্যভাবে সমাজে এক বৈষম্যের জোয়ারে নিজ স্বার্থ বজায় রেখে উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য লেখকরা প্রায়ই সবাই সাময়িক পত্রের মাধ্যমে একটি ঘরানা তৈরি করলেন মানুষের কাছে যাবেন চিন্তা করে। কিন্তু কোন মানুষের কাছে তারা যাবেন, সকল মানুষ না কিছু মানুষ। সকল মানুষের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল না রাখা সম্ভবও নয়। তাই কিছুটা আত্মপ্রেমে, দেশপ্রেমের লেবেল লাগিয়ে নেতাদের মতো এগিয়ে এলেন তারা। রামমোহন, বঙ্কিম, ভূদেব, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর , কালী প্রসন্ন সিংহ, এমন অনেকেই যতিবিহীন গদ্য শুরু করলেন।
প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত ‘আলালের ঘরে দুলাল’ বাংলা ভাষায় রচিত আদি গদ্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এটি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থের ভাষা ‘আলাল ভাষা’ নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে কথ্যরূপী গদ্য একটি পৃথক লেখ্য রূপে দেখা দেয়, ‘রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড়ো ঢিলে দেন-হচ্ছে হবে-খাচ্ছি খাব-বলিয়া অনেক বেলায় স্নান-আহার করেন-তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন-কেহ বা তাস পেটেন-কেহ বা মাছ ধরেন-কেহ বা তবলায় চাঁটিদেন-কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন-কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভালো বুঝেন-কেহ বা বেড়াতে যান-কেহ বা বহি পড়েন। কিন্তু পড়াশুনা অথবা সৎ কথায় আলোচনা অতি অল্প হইয়া থাকে। হয়তো মিথ্যা গালগল্প কিংবা দলাদলির ঘোঁট, কি শম্ভু তিনটা কাঁঠাল খাইয়াছে এই প্রকার কথাতেই কাল ক্ষেপণ হয়। বালীর বেণীবাবুর অন্য প্রকার বিবেচনা ছিল। এদেশের লোকদিগের সংস্কার এই যে স্কুলে পড়া শেষ হইলে লেখাপড়া শেষ হইল। কিন্তু এ বড়ো ভ্রম, আজন্ম মরণ পর্যন্ত সাধনা করিলেও বিদ্যার কূল পাওয়া যায় না, বিদ্যা চর্চা যত হয় ততই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে। বেণীবাবু এ বিষয় ভালো বুঝিতেন এবং তদনুসারে চলিতেন। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহকর্ম সকল দেখিয়া পুস্তক লইয়া বিদ্যানুশীলন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে চোদ্দ বৎসরের একটি বালক-গলায় মাদুলি-কানে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটি গড় করিল। বেণীবাবু এক মনে পুস্তক দেখিতেছিলেন বালকের জুতার শব্দে চম্কিয়া উঠিয়া দেখিয়া বলিলেন, ‘এসো বাবা মতিলাল এসো- বাটির সব ভালো তো ?’ মতিলাল বসিয়া সকল কুশল সমাচার বলিল। বেণীবাবু কহিলেন- অদ্য রাত্রে এখানে থাকো কল্য প্রাতে তোমাকে কলিকাতায় লইয়া স্কুলে ভর্তি করিয়া দিব। ক্ষণেক কাল পরে মতিলাল জলযোগ করিয়া দেখিল অনেক বেলা আছে। চঞ্চল স্বভাব- এক স্থানে কিছু কাল বসিতে দারুণ ক্লেশ বোধ হয়- এজন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া বাটীর চতুর্দিকে দাঁদুড়ে বেড়াইতে লাগিল- কখন ঢেঁস্কেলের ঢেঁকিতে পা দিতেছে- কখন বা ছাতের উপর গিয়া দুপদুপ করিতেছে-কখন বা পথিকদিগকে ইঁট-পাটকেল মারিয়া পিট্টান দিতেছে ; এইরূপে দুপ-দাপ করিয়া বালী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল-কাহারো বাগানে ফুল ছেঁড়ে-কাহারো গাছের ফল পাড়ে-কাহারো মট্কার উপর উঠিয়া লাফায়- কাহারো জলের কলসী ভাঙিয়া দেয়।’’
ওপরের গদ্যে যে চিত্র্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যে শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তাতে স্পষ্টত তৎকালীন সমাজ ও অথর্নীতির প্রেক্ষাপট চিত্রিত হয়। অলস, কলকাতার মাতাল, বাটপার মনুষ্যদেহী পশুর ছবি, রুচিতে চেতনায় গ্রাম্য গড্ডলিকায় ইংরেজ-শিক্ষিত বাঙালীর অবস্থানই এসেছে এই গদ্য সাহিত্যে। কালী প্রসন্নে অবশ্য যতি এসে গেছে, “পাড়া গেয়ে দুই-একজন জমিদার প্রায় বারোমাস এখানে কাটান। দুপুর বেলা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডী গানের ছেলেদের মতো চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, দশবারোজন মোসাহেব সঙ্গে. বা জানের ভেড়য়ার মতো পোশাক, গলায় মুক্তার মালা; দেখলেই বোঝা যায় বনগাঁর শিয়াল রাজা।”
গদ্যচর্চার ভেতর দিয়ে স্বীকৃতি পাচ্ছেন ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোকদের পরিচয়টা কী? উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বিযুক্ত, জনজীবন বিচ্ছিন্ন, রুচির ব্যপারে নিরাপোস আবার আত্মসচেতনও বটে। যার পরিচয় ওপরের উদ্ধৃতিতে প্রাপ্য। এই শ্রেণীর আত্মীয়তা ছিল ইংরেজের সঙ্গে। তাই জানা যায় রাজারামমোহনের বাড়িতে ইংরেজরা বাইজীর নাচ দেখতে এসেছিল। তার র্বুজোয়া কর্ম স্পৃহা ও সংস্কারের উৎসাহ প্রায় হাত ধরাধরি করে চলেছিল। ম্যাক্স মুলার সাহেব তার সর্ম্পকে বলেছিলেন, ‘a great man, because of unselfishness, honesty and boldness’। তিনি সজ্জন হলেও ধনসম্পতির মালিক ছিলেন প্রচুর। আর কোম্পানির সঙ্গে সর্ম্পক না থাকলে তা সম্ভবও ছিল না। রাজা রামমোহন একা নন, এমন উদাহরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে শব্দগুচ্ছের আধিক্যের রচনা কেবল ভারী হয়ে উঠবে।
মুলত গদ্যের ভাষা, শব্দে, ছবিতে উঠতি পুঁজিবাদ আর বানিজ্যীকরণের চিত্র দেখা যায়, যা পদ্যে সম্ভব ছিল না। পদ্যের আফিমে যে দুলকি চাল আছে তাতে এই সমাজের চেহারার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল না, পয়ার বা পদ্য ভেঙে গদ্য এলো ঠিকই কিন্তু তাতে রইলো শ্রেণী শাসনের শিকল, যা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বার্থের ইটের তৈরি দালান। রবীন্দ্রনাথ যদিও সাহস করে বলেছিলেন, ‘বিদেশী শাসনামলে যদি এমন কোন জিনিসের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা লইয়া বাঙালী যথার্থ গৌরব করিতে পার, তা বাংলা সাহিত্য। তাহার প্রধান কারণ , সাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই।’
সাহিত্য নেমক খাক আর না খাক সাহিত্যিক খেয়েছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘না খেয়ে গত্যন্তর ছিল কি, অন্য কোন নুনের সরবরাহ তো ছিলো না বাজারে।হ্যাঁ খেয়েছেন এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে খাওয়ার পর নিমকহারামি যে করেছেন এমন অপবাদ তাঁদের সর্ম্পকে দেওয়া কঠিন। সাহিত্যের স্বাদে তাই নুন লেগেছে, ইংরেজের গুনের নুন।’
বাংলা ভাষাকে বোঝা, আর বুঝতে পারাটা ব্যবসা ও ধর্মের প্রয়োজনে, তাই ১৭৭৮ সালে হলহেডের বই ছাপানোর তাগিদে উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা এলো, যেখানে ইংল্যান্ডে ছাপাখানার প্রচলন হয় ১৪৭৭ সালে। প্রায় তিনশ বছর পর ভাষার ব্যাকরণের পেছনে রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যাকরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের শুরু হলো। ইংরেজের ব্যবসানীতির ছাপ সুলভ না হলেও গদ্যে ছাপ রেখেছিল কমা, সেমিকোলন, যতি, বিস্ময়বোধক চিহ্ন, বাগবিধি, শব্দ, বাক্যগঠন, এমনকি যোগাযোগ ব্যবস্থার শব্দসমুহ ঢুকে পড়েছিল গদ্যে। যেমন আজকের গদ্যে ব্যবহার হচ্ছে এসএমএস, চ্যাট, ফেসবুক, ভাইবার, আরও অনেক শব্দসম্ভার। তেমনি তৎকালীন গদ্যে চড়ক, বান্ডিল, বক্কোন, ফেটিং গাড়ি, টমটম, কমোড ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার গদ্যের ভেতর আসন গেড়েছিল। তবে গদ্য জনতার কাছে আসেনি, আসেনি জনতাও গদ্যের কাছে। কারণ জনতা মানে কৃষক শ্রেণী, নীলচাষি শ্রেণী। তারাই সংখ্যায় অধিক। তারা আসেনি। এটা তাদের সমস্যা। তাই রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্তদেব মহাশয়রা মধ্যবিত্ত স্বার্থ রক্ষায় পৃথকীরণ করেন তাদের ভাষা ব্যবহারের মাত্রাজ্ঞানকে। রামমোহনের গদ্যে তাই বুদ্ধির ঝলক থাকলেও হৃদয় ছিল না, হৃদয় আসতে গদ্যে চল্লিশ বছর লেগেছিল, তা এসেছিল বিদ্যাসাগরের হাতে।
বিদ্যাসাগরের পূর্বে ও সমসাময়িককালে বাংলা গদ্যচর্চার পরিসীমা ব্যাপক হয়ে উঠলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যতিত এইসব প্রচেষ্টায় অন্য কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তৎকালীন সমস্ত গদ্য রচনাকারীর মধ্যে বিদ্যাসাগরের অবদান গদ্যের কাঠামো গঠনে এবং বাক্যের ভারসাম্য স্থিরীকরণে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।
বাঙালির পদ্যের হৃদয় তাই বড় অসহায় ছিল, গদ্য তাকে মুক্তি দিতে পারেনি। কারণ সে নিজেও ছিল অর্থনীতি আর মুৎসুদ্দির খাঁচায় বন্দি। শ্র্রেণী বৈষম্যের পাহারায় গদ্য যখন দিশেহারা অস্থির, তখন তাকে স্থির রূপ দিতে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী। মাইকেল মধুসূদনের মতে, ‘প্রাচীন ঋষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্মশক্তি এবং বাঙালি মায়ের হৃদয় দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠিত।’
১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা শেষ হওয়ার পর সে বছরই ২৯ ডিসেম্বর মাত্র একুশ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদে আবৃত হন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৭ সালে স্থাপন করেন সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি নামে একটি বইয়ের দোকান। এই বছরই এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় হিন্দি বেতাল পচ্চিসী অবলম্বনে রচিত তার প্রথম গ্রন্থ বেতাল পঞ্চবিংশতি। বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সমঅংশীদারিত্বে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেন তিনি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য এই বছরই নদিয়ার কৃষ্ণনগরে আসেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। ১৮৪৯ সালে মার্শম্যানের হিস্ট্রি অব বেঙ্গল অবলম্বনে রচনা করেন বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থখানি। বন্ধু ও হিতৈষীদের সহযোগিতায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্যে স্থাপনা করেন সর্ব্বশুভকরী সভা। সংস্কৃত কলেজের দ্বার সব বর্ণের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৩ সালে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যাকরণ কৌমুদী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। পরের বছর ব্যাকরণ কৌমুদী তৃতীয় ভাগ ও কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম অবলম্বনে তার রচিত শকুন্তলা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব প্রথম পুস্তক প্রকাশিত। এই বছরের এপ্রিল মাসে বাংলা নববর্ষের দিন যুগান্তকারী বাংলা শিশুপাঠ্য বর্ণমালা শিক্ষাগ্রন্থ ‘বর্ণপরিচয়’ প্রকাশিত হয়। বিধবা বিবাহ আইনসম্মত করতে ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ সরকারের কাছে বহুস্বাক্ষর সংবলিত এক আবেদনপত্রও পাঠান। ২৭ ডিসেম্বর আরেকটি আবেদনপত্র পাঠান বহু বিবাহ নিবারণ বিধির জন্য। ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয় সোমপ্রকাশ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনার নেপথ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট অবদান ছিল। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত এটিই প্রথম পত্রিকা, যাতে রাজনৈতিক বিষয় স্থান পেয়েছিল। ১৮৬০ সালে ভবভূতির উত্তর রামচরিত অবলম্বনে তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ সীতার বনবাস প্রকাশিত হয়। কথিত আছে, বইখানি তিনি রচনা করেছিলেন মাত্র চারদিনে। ১৮৬৪ সালের জুলাইয় ইংল্যান্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত করে। খুব কম ভারতীয়ই এই বিরল সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় তার পরিমার্জিত আখ্যান মঞ্জরী পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।
সামিজিক ব্যকারণে বিদ্যাসাগরে ভুমিকা সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস ‘বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ‘১৮২৯ হইতে ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ এক যুগকাল সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ সাহিত্য, বেদান্ত, অলংকার, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া এই সংস্কারমুক্ততা অর্জন করিলেন, তৎকালে প্রচলিত জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে এই উদারতার বীজ কোথায় কেমনভাবে তাহার মনে উপ্ত হইল, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও তাহার রহস্য আমাদিগকে অভিভূত করে।’
তাহার গদ্যে মধুরসঙ্গীত ধ্বনিত হতো। ছন্দ আর প্রবচনে ভরপুর গদ্য ছিল সঙ্গীতের মতো সমুধুর। ‘এই সেই জনস্থান-মধ্যবৰ্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহান্ন শিখরদেশে আকাশপথে সতত-সমীয় সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে মিষ্ণু শীতল ও রমণীয়–পাদদেশে প্ৰসন্ন সলিল৷ গোদাবী তরঙ্গ বিস্তাৱ করিয়া—প্রবলবেগে গমন করিতেছে’ (সীতার বনবাস)।
তার অধিকাংশ গদ্যে সামাজিক ব্যাকরণীকরণ যা এক প্রকার সমাজ সংস্কারকের মনোবৃত্তি সহজেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তদুপরি বিষয় ও আদর্শের দিক বিচারে বিদ্যাসাগরের রচনাবলী বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্য সৃষ্টির যৌথ প্রচেষ্টা তার রচনাবলীর পেছনে কাজ করেছে, সেসব বিষয়ের ওপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ঋজুপাঠ (১৮৫৩), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), ব্যাকরণকৌমুদী (১৮৫৩), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ) (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১), নি®কৃতি লাভ প্রয়াস (১৮৮৮), পদ্যসংগ্রহ (১৮৮৮), সংস্কৃত রচনা (১৮৮৯), শ্লোকমঞ্জরী (১৮৯০), বিদ্যাসাগর চরিত (১৮৯১), ভূগোল খগোল বর্ণনম (১৮৯২), বেনামী রচনা: অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা (১৮৮৪), রতপরীক্ষা (১৮৮৬)।
তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, শিশু শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করলেই জাতীয় জীবনে মননশীলতা বিকাশর সুযোগ আসবে। তাঁর বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, বর্ণপরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি। সংস্কৃত শিক্ষার জন্যও তাঁর উদ্যোগ কতিপয় গ্রন্থে রূপ লাভ করেছে।
বিদ্যাসাগরের সমাজসম্পর্কিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ এবং ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার’ উল্লেখযোগ্য।গ্রন্থ দুটির প্রত্যেকটিতে দুটি করে খণ্ডের মাধ্যমে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা এবং বহুবিবাহ প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করার জন্যে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বলিষ্ঠ মতবাদ প্রকাশ করেছেন। এসব গ্রন্থের অনুসারী হিসেবে বেনামীতে ‘কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য’ রচিত। এছাড়া ‘অতি অল্প হইল’, ‘আবার অতি অল্প হইল’, ‘ব্রজলিবাস’, ‘কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণ’ ‘বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা’ এবং ‘কস্যচিৎ উপুক্ত ভাইপো-সহচরষ্য’ ও ‘রত্নপরীক্ষা’ উল্লেখযোগ্য।
দেশের শিক্ষিত লোকদের সামনে সৎসাহিত্যের আদর্শ তুলে ধরতে পারলে জাতীয় জীবন সুন্দর রূপে গড়ে তোলা সহজতর হবে বিবেচনায় নিয়ে তিনি অন্য ভাষার সাহিত্য থেকে কয়েকটি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি গ্রন্থ ‘বৈতাল পচ্চিসী’ থেকে অনুবাদ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নামক সংস্কৃত নাটক থেকে অনুবাদ ‘শকুন্তলা’, মহাভারতের কিছু অংশের অনুবাদ ‘মহাভারত’ (উপক্রমণিকা ভাগ), ভবভুতির ‘উত্তর রামচরিত’ নাটকের অংশ বিশেষ এবং বাল্মীকির ‘রামায়ণ’ অবলম্বনে রচিত ‘সীতার বনবাস’, সেক্সপিয়রের Comedz of Errors অবলম্বনে রচিত ‘ভ্রান্তিবিলাস’ উল্লেখযোগ্য রচনা। তার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক রচনা হিসেবে ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’ ক্ষুদ্র নিবন্ধ এবং স্বরচিত ‘বিদ্যাসাগর চরিত’ গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।
তিনি বাংলা সাধুভাষার গদ্যরীতিকে পুর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। জড়তা ও দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্য প্রথমবারের মতো তার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’তে প্রকাশ পেয়েছে। এর পরবর্তী রচনাবলীতে তার ভাষা ক্রমে ক্রমে সরলতা ও স্নিগ্ধতা লাভ করেছে। সাহিত্যের বাহন হিসেবে গদ্যের রসালো উপযোগিতা বিদ্যাসাগরের রচনায় প্রথম লক্ষ্য করা যায়। পদ্যের মতো গদ্যেরও যে একটা নিজস্ব তাল বা ছন্দ আছে, বিদ্যাসাগর তা আবিষ্কার করেন। বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর মধ্যে অনুবাদ জাতীয় গ্রন্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। বিশেষত তার সাহিত্যকীর্তি প্রকাশক গ্রন্থগুলো অনুবাদ মাত্র। তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে তার সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশের অবকাশ ছিল না। বরং হিন্দি সংস্কৃত ইংরেজি থেকে তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী অনুবাদ হলেও তাকে বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আসলে ভিন্ন ভাষার কাব্য ও নাটককে উপাখ্যানে রূপান্তরিত করতে গিয়ে তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাকে নিছক অনুবাদক হিসেবে মনে করা যায় না। অনুবাদের বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে তার মৌলিকতা পরিদৃশ্যমান। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের হাতেই হয়েছে। তার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে সাহিত্যিক গদ্য বিচিত্র রূপে ক্রমপরিণতির পর্যায়ে উন্নীত হয়। অমার্জিত বঙ্গভাষাকে বিদ্যাসাগরই সুসংগত মার্জিত রূপ দান করেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ‘বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পী এবং তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।’
বাংলা গদ্যের অবয়ব-নির্মাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। গদ্যের অনুশীলন পর্যায়ে সুশৃঙ্খলতা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনিপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যরীতিকে তিনি উৎকর্ষের এক উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করেন। তারই বলিষ্ঠ প্রতিভার যাদু স্পর্শে বাংলা গদ্য কৈশোরকালের অনিশ্চয়তাকে পশ্চাতে ফেলে পূর্ণ সাহিত্যিক রূপের নিশ্চয়তার মধ্যে স্থান পায়, গদ্য তার অস্থির গতির কাল অতিবাহিত হয়ে স্থিরতার পর্যায়ে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগরের পূর্বে ও সমসাময়িককালে বাংলা গদ্যচর্চার পরিসীমা ব্যাপক হয়ে উঠলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যতিত এইসব প্রচেষ্টায় অন্য কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তৎকালীন সমস্ত গদ্য রচনাকারীর মধ্যে বিদ্যাসাগরের অবদান গদ্যের কাঠামো গঠনে এবং বাক্যের ভারসাম্য স্থিরীকরণে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের অনেক আগেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব হলেও বিদ্যাসাগরই উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যকারণে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে শিল্পরসসমন্বিত ভাষাভঙ্গিমা প্রথম প্রয়োগকর্তার গৌরব তারই প্রাপ্য।
সমকালীন গদ্য লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যের জটিলতা দূর করে তাকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর বিদ্যাসাগর সেই গদ্যরীতির মধ্যে লালিত্য সঞ্চার ও নমনীয়তা এনে ভাষারীতি হিসেবে গদ্যের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে গৌরবময় অগ্রগতি সাধন করেন। তিনি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রবাহ অনুধাবন করে বাক্যে স্বাভাবিক শব্দানুবৃত্তির রূপ দিয়ে গদ্যরীতিতে পরিমিতিবোধ সৃষ্টি করেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন লেখকদের মধ্যে যে সুষম বাক্যগঠনরীতির নিদর্শন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে না, তা নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে বিদ্যাসগর যেমন সচেষ্ট ছিলেন, তেমন আর কাউকে দেখা যায় না। সে জন্য বাংলা গদ্যশৈলীর উদ্ভবের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে লেখনী ধারণ করা সত্ত্বেও তাকে ‘বাংলাগদ্যের জনক’ বলা হয়ে থাকে।
প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট গদ্যরীতির প্রভাবেই পরবর্তী সময়ে বাংলাগদ্যের পরিণত রূপের সৃষ্টি হয়।
একদিকে সব রকম জীর্ণতার অবসান কামনা, অন্যদিকে নবজীবনের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্খা এই দ্বৈত তাগিদে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তার প্রচেষ্টার ফল যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল বাংলাদেশের বিদ্যমান ইতিহাস তার সাক্ষ্য। তাই উনিশ শতকের ৩য় ও ৪র্থ শতকের প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলন, যেমন-বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য ও বহু বিবাহ রোধ, ইংরেজি শিক্ষা এবং মাতৃভাষা শিক্ষায় ইত্যাদি প্রত্যেকটি সামাজিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংগ্রহণ করেন। এতে তার সমাজ সংস্কারক দৃষ্টি উজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হয়। তার শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষাসংস্কার ও অন্যবিধ সংস্কারমূলক কাজের ব্যাপকতা তার এ পরিচয়টিকে নিঃসন্দেহে সত্যতর করে তুলেছে। নবীন শিক্ষার্থীদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা, সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে রচিত বাদ-প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গামূলক রচনার পিছনেও কাজ করেছে এই সংস্কারক মন। আবার এই সংস্কারক মনই জাতীয় মানসের যথাযথ বিকাশের প্রয়োজনে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাংলা গদ্য ভাষার নবনির্মাণে ও নতুন বাংলা সাহিত্যের ভিত রচনায় ব্রতী হতে।
সমাজ সংস্কারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই ব্যয় করেছেন কুসংস্কার-অপসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর সংস্কারমূলক কাজে। তদুপরি বাংলা ভাষার বিশেষ করে বাংলা গদ্যের মানোন্নয়ন এবং গদ্যকে সব মানুষের ভাব প্রকাশের যথার্থ ও পরিমার্জিত বাহন হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি।
বাংলা গদ্যের মধ্যে ছন্দবোধ ও ছন্দ আবিষ্কার করে বিদ্যাসাগর ভাষাকে নবরূপে গড়েছিলেন। তাছাড়া, বাংলা প্রবাদপ্রবচনের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবহার বিদ্যাসাগরের রচনা তথা প্রাথমিক পর্যায়ের গদ্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। প্রবাদের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গ রচনাকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হয়েছিল। বাংলা গদ্যে স্বাভাবিক যতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি সুষম বাক্যগঠনরীতির প্রবর্তন করেন। দাঁড়ি কমা প্রভৃতি বিরামচিহ্ন তিনিই প্রথম ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন।
বিদ্যাসাগরের প্রতিভার সার্থক সমঝদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথার্থ মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ‘ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারের কতগুলি বক্তব্য বিষয় পুরিয়া যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। বাংলা ভাষাকে পূর্ব প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।’
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের অনেক আগেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব হলেও বিদ্যাসাগরই উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যকারণে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে শিল্পরসসমন্বিত ভাষাভঙ্গিমা প্রথম প্রয়োগকর্তার গৌরব তারই প্রাপ্য। বাংলা পরিণত গদ্যরীতির উন্নয়নে বিদ্যাসাগরের প্রভাব তাই অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।
দোহাই:
১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন সমাজ।
২। রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৩। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ: সিরাজুল ইসলাম চৌধূরী
৪। হুতোম পেঁচার নকশা: কালী প্রসন্ন সিংহআরও পড়ুন: মোহাম্মদ নূরুল হকের প্রবন্ধ: যুক্তির শৃঙ্খলা ও শিল্পের দায় ॥ আজিজ কাজল

