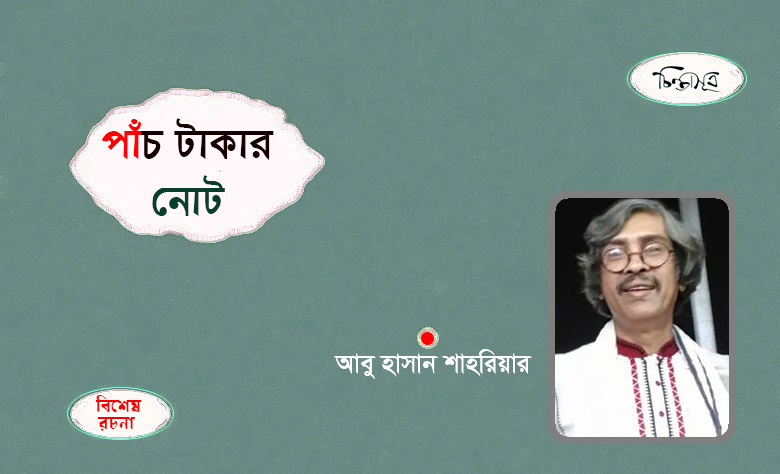অধুনালুপ্ত দৈনিক মুক্তকণ্ঠের ব্রডশিট ৮ পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক সাহিত্য সাময়িকী ‘খোলা জানালা’য় শামসুর রাহমান, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, রশীদ করীম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন সরকার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন আজাদ, সেলিম আল দীন, মোহাম্মদ রফিক, সুস্মিতা ইসলাম, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, জয় গোস্বামীসহ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কবি-লেখকদের লেখা যেমন নিয়মিত ছাপা হতো, দুই বাংলার সম্ভাবনাময় তরুণ ও নবীনতম কবি-লেখকের লেখাও বাদ যেত না। মূল দৈনিকটির সম্পাদক ছিলেন কে. জি. মুস্তাফা। আমার সম্পাদনায় ‘খোলা জানালা’ বেরুতো শুক্রবার। আমাদের তারুণ্যে কবি আহসান হাবীব সম্পাদিত দৈনিক বাংলার সাহিত্য সাময়িকীতে একটি লেখা ছাপা হলে যেমন কোনও তরুণের কাছে তা লেখকস্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হতো, ‘খোলাজানালা’ও তার সময়ের তরুণদের কাছে ঠিক একইরকম ছিল। এটা আমার কথা নয়, অনেককে বলতে শুনি।
সম্পাদনার পাঠ কবি আহসান হাবীবের কাছ থেকে নিয়েছিলাম। তার সান্নিধ্যে জেনেছিলাম, সাহিত্য সম্পাদককে সম্পর্কবিচারী হলে চলে না; হতে হয় গুণবিচারী। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত কলকাতার ‘দেশ’ পত্রিকা থেকেও শিখেছি অনেক কিছু। সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে কত কী মহার্ঘ পাঠই না আছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘কল্লোল যুগ’ বইটিতে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকা শামসুর রাহমানসহ অনেক কবিকে তারুণ্যে প্রাণনা জুগিয়েছে। যে-পত্রিকার অনুসরণে বুদ্ধদেবের ‘কবিতা’, হ্যারিয়েট মনরো সম্পাদিত জগদ্বিখ্যাত সেই ‘Poetry’ পত্রিকার দু-চারটি সংখ্যাও ততদিনে দেখার সুযোগ ঘটেছে। স্বভাষা-বিভাষার অনেক মুনি-ঋষির কাছ থেকে পাঠ নিয়ে জেনেছি—একজন সাহিত্য সম্পাদকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—সম্ভাবনাময় নবীন লেখককে খুঁজে বের করে সারস্বত সমাজের সামনে তুলে ধরা এবং তরুণ লেখকদের চলার পথ মসৃণ ও প্রতিষ্ঠাদীর্ঘ করা। তার মানে এই নয়, অগ্রাহ্য করতে হবে প্রবীণ লেখকদের। চিন্তার তারুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি, এমন বয়সী লেখকরাই পাঠককে আকৃষ্ট করেন বেশি। প্রথিতযশা অগ্রজদের পাশে নিজের লেখা দেখে উৎসাহিত হওয়ার সুযোগ থাকে নবীন লেখকদেরও। ৮ পৃষ্ঠার ‘খোলা জানালা’ ঠিক এরকমই একটি সাহিত্য সাময়িকী হয়ে উঠেছিল। ছোটকাগজের অনেক আত্মমর্যাদাশীল কবি-লেখকই—যারা তখন বড়কাগজে লিখতেন না—সাগ্রহে লেখা পাঠানো শুরু করেন এই সাময়িকীতে। ছোটকাগজ প্রসঙ্গ আসায় শিহরণ-তোলা একটি অভিজ্ঞতা কথা মনে পড়ে গেল। বাঙলা ভাষার একদা বিখ্যাত ছোটকাগজ ‘কৃত্তিবাস’-এর সম্পাদক হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ই অধিক পরিচিত। সুনীলের প্রবাসকালে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় কাগজটির একাধিক সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন। ‘খোলা জানালা’য় পশ্চিমবঙ্গের অনেক কবি-লেখকের লেখা ছাপা হলেও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তখনও আমার যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। একদিন ডাকযোগে তার একটি অভিমানী চিঠি পেলাম। সঙ্গে কবিতাও। অভিমানের কারণ, তার কাছে লেখা না-চাওয়া। আর সঙ্গের কবিতাটি ছিল আমার জন্য না চাইতেই পাওয়া এক অমূল্য রতন। ‘খোলা জানালা’ প্রাসঙ্গিক এমন অজস্র গল্প আছে আমার স্মৃতিশালায়। তিক্ত স্মৃতিও আছে দুটি-একটি। ভালো কিছু করতে গেলে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও যুক্ত হয়। জোটে অযোগ্যের আস্ফালন ও ছোটখাটো অকৃতজ্ঞতা। এগুলো উপেক্ষা করতে হয়।
_____________________________________________________________________
আমার একমাত্র ছোটগল্পের বই ‘আসমানী সাবান’-এর প্রায় সব গল্পেরই প্রথম প্রকাশ আহসান হাবীবের সম্পাদনায়। আমার ছোটগল্প তিনি পছন্দ করতেন। বলতেন— ‘কবি হতে এসেছ তুমি, কিন্তু ছোটগল্প ছেড়ো না। ’
_____________________________________________________________________
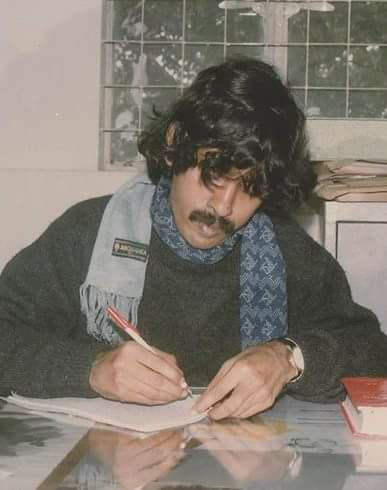
আহসান হাবীব যখন দৈনিক বাংলার সাহিত্য সম্পাদক, শামসুর রাহমান তখন মূল দৈনিকের সম্পাদক। হাবীব ভাই বসতেন দৈনিক বাংলা ভবনের চতুর্থ তলে। শামসুর রাহমানের ঘর ছিল দোতলায়। হাবীব ভাইকে কবিতা দিতে হলে শামসুর রাহমান সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠে আসতেন। বিনম্র শ্রদ্ধায় কবিতা তুলে দিতেন সাহিত্য সম্পাদকের হাতে। লেখকের অনুমতি ছাড়া লেখায় কোনও পরিবর্তন আনতেন না হাবীব ভাই। এ প্রসঙ্গে নিজের দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। একবার আমার একটি ছোটগল্প প্রকাশের আগে গল্পটির নাম নিয়ে হাবীব ভাই দ্বিধায় পড়েছিলেন। আমাকে ফোন করে দেখা করতে বললে আমি পরদিনই তার কাছে যাই। উল্লিখিত ছোটগল্পের নাম দিয়েছিলাম ‘ছন্নছুট’। আমাকে দেখেই আহসান হাবীব বলেছিলেন— ‘‘জানি, তোমার যৌগ-শব্দসৃষ্টির প্রতি ঝোঁক আছে। ‘ছন্নছুট’ও তেমন। কিন্তু যেহেতু অভিধানে ‘ছন্নছাড়া’ শব্দটি আছে, সেটাই দেবে কি না ভাবো।” আমার সবিনয় উত্তর ছিল—“হাবীব ভাই, ‘দলছাড়া’কে যদি ‘দলছুট’ বলা যায়, ‘ছন্নছাড়া’কে কেন ‘ছন্নছুট’ বলা যাবে না?” আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। আর কিছু জানতে না-চেয়ে গল্পটি প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটিও একটি শব্দ নিয়ে। অন্য এক বিখ্যাত দৈনিকের সাহিত্য সম্পাদক আমার এক ছোটগল্পের একটি শব্দে আপত্তি তুলেছিলেন। শব্দটি যৌগ নয়, মৌল; অভিধানেই আছে— ‘ব্যত্যয়’। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ‘ব্যত্যয়’ মানে কী? বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলাম—‘ব্যত্যয় মানে ব্যতিক্রম।’ তিনি সঙ্গে-সঙ্গে অভিধান খুলেছিলেন। শব্দটি পেয়েও গিয়েছিলেন সেখানে। এ সময় আমার সমবয়সী এক কবিকে নিয়ে ওই সাহিত্য সম্পাদকের ঘরে ঢোকেন অগ্রজ এক কবি। তারা ঢুকতেই সাহিত্য সম্পাদক তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তারা ব্যত্যয় শব্দের মানে জানেন কি না। দুজনের কেউই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ফলত সাহিত্য সম্পাদক ভাবগম্ভীর গলায় আমাকে বলেছিলেন—“এখানে আমরা চারজন মানুষ আছি; তিনজনের কাছেই ‘ব্যত্যয়’ শব্দটা অপরিচিত। তোমার গল্পটা আমার পছন্দ হয়েছে; তুমি যদি ‘ব্যত্যয়’ বদলে ‘ব্যতিক্রম’ করে দাও, তাহলেই ছাপাতে পারি।” আমি রাজি হইনি। গল্পটা তার কাছ থেকে ফেরত নিতে-নিতে বলেছিলাম—‘‘ধরে নিন আপনাদের তিনজনের পকেটে হাজার টাকা আছে; আমার পকেটে মাত্র পঞ্চাশ। কিন্তু পাঁচ টাকার নোটটা আপনাদের কারও কাছেই নেই, যা আমার আছে। আমার ‘ব্যত্যয়’ ওই পাঁচ টাকার নোট।” তারপর সেখান থেকে সটান চলে এসেছিলাম দৈনিক বাংলায়। হাবীব ভাইয়ের হাতে গল্পটি তুলে দিয়ে একটু আগে ‘ব্যত্যয়’ নিয়ে আমার ব্যত্যয়ী অভিজ্ঞতার কথা বলতেই তিনি জিগ্যেস করেছিলেন—‘কোন মূর্খ সম্পাদকের কাছে গিয়েছিলে তুমি?’ পুরো ঘটনা খুলে বলতেই তিনি ওই বৈঠকেই আমার ছোটগল্পটি তাকে পড়ে শোনাতে বলেন। ঠিক পরের সপ্তাহেই সেটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক বাংলার সাহিত্য পাতায়।
উল্লেখ্য, হাবীব ভাইয়ের হাত দিয়ে আমার প্রথম প্রকাশিত লেখাটি কবিতা হলেও তিনি আমার বেশ কয়েকটি ছোটগল্প ছেপেছিলেন। আমার একমাত্র ছোটগল্পের বই ‘আসমানী সাবান’-এর প্রায় সব গল্পেরই প্রথম প্রকাশ আহসান হাবীবের সম্পাদনায়। আমার ছোটগল্প তিনি পছন্দ করতেন। বলতেন— ‘কবি হতে এসেছ তুমি, কিন্তু ছোটগল্প ছেড়ো না।’ কবিতার পাশাপাশির আমি যে কিছু গদ্যও লিখি, তার প্রাণনা হাবীব ভাইয়ের সেই পথনির্দেশনা।
আমাদের তারুণ্যে সাহিত্য-সম্পাদনা ছিল বটতুল্য উচ্চতার একটি কাজ। ‘ব্যত্যয়’ শব্দের মানে-না-জানা ‘মূর্খ’ সম্পাদকেরও অনেক পড়াশোনা ছিল। হালের কোনও দৈনিকে শামসুর রাহমানের মতো সম্পাদকও দুর্লভ, আহসান হাবীবের মতো সাহিত্য-সম্পাদকও বিরল। সাধে কি কালজয়ী ভাষাচিত্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার শার্টের হাতা গোটাতে-গোটাতে প্যারিসফেরত বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন বদমাশ পত্রিকাওয়ালাদের পেটাতে যাবেন বলে? আরেক কিংবদন্তী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তো সন্তোষকুমার ঘোষকে পিটিয়েই আনন্দবাজার পত্রিকার চাকরি ছেড়েছিলেন। তাদের ক্ষোভের পেছনেও ছিল কোনও না কোনও পাঁচ টাকার নোটের গল্প। গল্পগুলো সারস্বত সুতোয় বোনা বলে সাহিত্যের পাড়াপ্রতিবেশী। প্রতিটি গল্পই এক-একটি পাঁচ টাকার নোট।