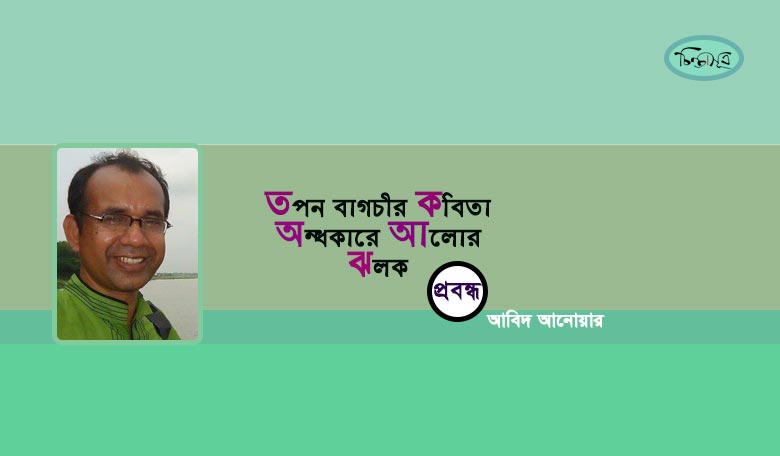 তপন বাগচী তাঁর সাহিত্যচর্চায় দুই দশক পথ অতিক্রম করেছেন। এরই মধ্যে তিনি উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন কবিতায়, প্রবন্ধে, সাহিত্য-সমালোচনায় ও গবেষণাধর্মী নিবন্ধ রচনায় এবং শিশু-সাহিত্যে। কবিতায় যে প্রসাদগুণ, ছড়ায় যে হাস্যরস ও ছন্দনৈপুণ্য, প্রবন্ধ ও সাহিত্য-সমালোচনায় যে বিশ্লেষণধর্মিতা, গবেষণায় যে অনুসন্দ্বিৎসা অভিনিবেশী পাঠকের কাম্য তার সবই রয়েছে তপন বাগচীর রচনাকর্মে। তাঁর প্রবেশলগ্নেই বাংলা একাডেমি, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কইভ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছে কবিতাবিষয়ক মুল্যবান আলোচনা ও জীবনীগ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি (যাত্রা) ও চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা-অভিসন্দর্ভ এবং অনেক সম্পাদিত গ্রন্থ। যারা এ সম্পর্কে অবহিত তাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করবেন সার্বিক বিবেচনায় তিনিই তাঁর প্রজন্মের শ্রেষ্ঠতম বহুমাত্রিক লেখক।
তপন বাগচী তাঁর সাহিত্যচর্চায় দুই দশক পথ অতিক্রম করেছেন। এরই মধ্যে তিনি উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন কবিতায়, প্রবন্ধে, সাহিত্য-সমালোচনায় ও গবেষণাধর্মী নিবন্ধ রচনায় এবং শিশু-সাহিত্যে। কবিতায় যে প্রসাদগুণ, ছড়ায় যে হাস্যরস ও ছন্দনৈপুণ্য, প্রবন্ধ ও সাহিত্য-সমালোচনায় যে বিশ্লেষণধর্মিতা, গবেষণায় যে অনুসন্দ্বিৎসা অভিনিবেশী পাঠকের কাম্য তার সবই রয়েছে তপন বাগচীর রচনাকর্মে। তাঁর প্রবেশলগ্নেই বাংলা একাডেমি, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কইভ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছে কবিতাবিষয়ক মুল্যবান আলোচনা ও জীবনীগ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি (যাত্রা) ও চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা-অভিসন্দর্ভ এবং অনেক সম্পাদিত গ্রন্থ। যারা এ সম্পর্কে অবহিত তাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করবেন সার্বিক বিবেচনায় তিনিই তাঁর প্রজন্মের শ্রেষ্ঠতম বহুমাত্রিক লেখক।
এ-লেখায় আমি কেবল তাঁর কবিতা নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণের প্রয়াস চালিয়েছি। একটি বিশেষ কারণে তাঁর কবিতায় ছন্দ-প্রকরণের বিষয়টিকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বের চোখে দেখেছি। তাঁর প্রজন্মের অধিকাংশ কবিই অক্ষম গদ্যকেই কবিতার প্রধান (কেউ কেউ একমাত্র) বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এ-কারণে পাঠক সম্প্রদায় তাদের কবিতাকে অপাঠ্য বলে প্রায় বর্জন করেছেন বলা যায়। এই পটভূমিতে তপন বাগচী’র কবিতা আমাদের আশান্বিত করে। আধুনিক কবি হয়েও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটিও গদ্যকবিতা লেখেননি; জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব বসু নগণ্যসংখ্যক গদ্যকবিতা লিখেছেন; নবাগতদের হাতে আঙ্গিকের নৈরাজ্য দেখে শামসুর রাহমান শেষ বয়সেও বলে গেলেন ‘সনেটে প্রত্যাবর্তন আমার একধরনের প্রতিবাদ’ (জনকণ্ঠ সাময়িকী, ২৩ অক্টোবর ১৯৯৬); আল মাহমুদ বলেছেন, ‘যে কবি ছন্দ জানে না, সে কিছুই জানে না’ (ইনকিলাব সাহিত্য, ৩ অক্টোবর ১৯৯৭)। এ সবের অর্থ বুঝতে অক্ষম বলে কিংবা নিজেদের অপারগতার কারণে তপন বাগচীর সহযাত্রীদের প্রায় সবাই যাচ্ছেতাই আঙ্গিকে লিখে কবিতার বারোটা বাজাচ্ছেন।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটিও গদ্যকবিতা লেখেননি; জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব বসু নগণ্যসংখ্যক গদ্যকবিতা লিখেছেন; নবাগতদের হাতে আঙ্গিকের নৈরাজ্য দেখে শামসুর রাহমান শেষ বয়সেও বলে গেলেন ‘সনেটে প্রত্যাবর্তন আমার একধরনের প্রতিবাদ’; আল মাহমুদ বলেছেন, ‘যে কবি ছন্দ জানে না, সে কিছুই জানে না’।
এ পর্যন্ত তপন বাগচীঁর কবিতার বই বেরিয়েছে মোট পাঁচটি। প্রথমটি ‘কেতকীর প্রতি পক্ষপাত’ বেরিয়েছে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির বইমেলায়। ১৯৯৬ সালেরই জুন মাসে বেরোয় দ্বিতীয় কবিতার বই ‘শ্মশানেই শুনি শঙ্খধ্বনি’, যা ছিল বাংলা একাডেমির তরুণ লেখক প্রকল্পের শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁর অনুশীলনের ফসল। এর পর ২০০৫ সালে ‘অন্তহীন ক্ষতের গভীরে’ এবং ২০০৭ সালে ‘সকল নদীর নাম গঙ্গা ছিলো’ নামের আরও দু’টি কবিতার বই। ২০১০ সালে প্রকাশিত ‘নির্বাচিত ১০০ কবিতা’ নামের বইটি পূর্বোক্ত বইগুলো থেকে চয়িত ১০০ কবিতার একটি সংকলন এবং এই বইতে সংকলিত কবিতা নিয়েই আমার বর্তমান লেখাটির আয়োজন।
আধুনিক বা উত্তরাধুনিক যে-নামেই চিহ্নিত হোক, কবিতার বিবর্তন কোনো উন্নাসিকতার ফসল নয়, বরং আবহমান ধারায় একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সংঘটিত হয়ে চলেছে—এ সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ বোধ তাঁর ভেতরে কাজ করছে বলেই কবিতা ও কবিতাবিষয়ক আলোচনায় তপন বাগচী বিশিষ্টতার দাবিদার। তাঁর অধিকাংশ সহযাত্রীর এলোমেলো অর্থহীন রচনাকে উদ্দেশ করে তাই নিম্নোক্ত ব্যঙ্গাত্মক পংক্তি রচনা করতে পেরেছেন তিনি:
লিখুক, তাদের লিখতে দিন
তাদের এখন লেখার সময়
ভরতে হবে কাগজ খাতা
হোক তা চনা, নয় তো গোময়।
* * *
লিখলে ছাপা হবেই কোথাও
এত্তো কাগজ, বিশাল মাঠ
পাঠ বাড়ে না, কেবল বাড়ে
লেখক কবির আপন ঠাট।
[লিখুক, লিখতে দিন]
নিজের লেখা সম্পর্কে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী না-হলে এতটা প্রত্যয়ের সঙ্গে কেউ এমন ভাবনা প্রকাশ করতে পারেন না। বলছি না এটি তাঁর একটি উৎকৃষ্ট রচনা, যা তাঁর অধিকাংশ কবিতার শৈল্পিক বাচনভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু তপন বাগচীর অধিকাংশ সহযাত্রীর রচনাকর্ম সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে ও এ সবের অসারতা বিষয়ে পাঠককে অবহিত করার নিমিত্তে ছড়ার আঙ্গিকে লেখা তাঁর এই কবিতার কয়েকটি পংক্তির উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক মনে করেছি।
আমাদের কবিতার বর্তমান দৈন্যদশার জন্য দায়ী গত শতাব্দীর আশির দশকে সূচিত একটি প্রবণতা। প্রতাপশালী আমলা থেকে শুরু করে সমাজের ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ (এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান) অনেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন সে-সময়ে। নামজাদা কথাশিল্পী ও চিত্রশিল্পী, সিনেমার নায়ক-নায়িকা, টেলিভিশনের কর্তাব্যক্তি, বয়স্ক অধ্যাপক—সবাই কোমর বেঁধে কাব্যচর্চায় মেতে উঠলেন এবং অনেক সম্পাদক নানা চাপে ওদের কবিতা ছাপতে বাধ্য হলেন। এই ফাঁকে অনেক সম্পাদক নিজেও কবিতাচর্চায় মেতে উঠলেন। উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করা যাবে: যখনই কোনো কবি যশপ্রার্থী ব্যক্তি কোনো কাগজের সাহিত্য পাতার দায়িত্ব পেয়েছেন, তাঁর কবিতা অন্য সময়ের তুলনায় নিজেরটাসহ নানা পত্র-পত্রিকায় বেশি ছাপা হয়েছে। ষাটের দশকের কবি মোহাম্মদ রফিক-এর একটি পঙ্ক্তি ‘সব শালা কবি হবে’ সারাদেশে তখন আলোচিত হয়েছিলো। এর পরের অবস্থা আরও ভয়াবহ। তপন বাগচী‘র উপরোক্ত বক্রোক্তি এইসব কবি ও কবিতার প্রতি নিক্ষিপ্ত।
শিল্পসাহিত্যে নতুনত্বের সাধনা একটি চলমান প্রক্রিয়া, কিন্তু মূল থেকে বিচ্যূত হয়ে লাফ দিয়ে নতুনত্বকে আলিঙ্গন করা যায় না। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, ‘শিল্পসাহিত্যে নতুনত্ব একটি জীবিত বৃক্ষের ডালপালা বিস্তারের মতো: মূলকে অবলম্বন করেই যার বিস্তৃতি ও বিকাশ। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার জনকেরা নতুনত্বে প্রয়াসী হয়েও এই বোধে জারিত ছিলেন যে, আবহমান বাঙলা কবিতার শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো আধুনিকতার চর্চাই ফলবতী হবে না। তাই, তাঁরা কবিতার ভাষা বদলে দিলেও প্রাকরণিক বিশুদ্ধতার সঙ্গে কোনো আপস করেননি। রবীন্দ্রযুগে, এমনকি মধ্যযুগে সূচিত প্রকরণের বাইরে যাননি বা শত চেষ্টা করেও যেতে পারেননি তাঁরা। বিশ-শতকীয় আধুনিকতার আদি জনক বোদলেয়র নিজেও ছিলেন সপ্তদশ শতকে প্রবর্তিত প্রকরণের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত। এক কবি-বন্ধুর একটি কবিতার একটি পঙক্তিতে সামান্য ছন্দ-পতন দেখে শেষ বয়সেও তিনি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।
সদ্যসমাপ্ত বিশশতকের নব্বইয়ের দশকে এসে আমাদের কবিতা যখন অন্তহীন নৈরাজ্যে নিপতিত, তখন তপন বাগচী’র মতো কবির আবির্ভাব আমাদের আশান্বিত করে, যখন দেখি বুদ্ধদেব বসুর অমোঘ কথাটিই প্রকাশ করেছেন তিনি তাঁর একটি কবিতার শেষাংশে এভাবে:
সহজে যায় না মানা শিল্পপ্রতারণা
পথকেই পথ দেয় পথের ঠিকানা
(পথের হিসেব)
পথই ভিন্ন পথের ঠিকানা বাতলে দেয়—এই বোধে যিনি জারিত তাঁর পথ হারাবার ভয় নেই। তাই তপন বাগচী তাঁর প্রজন্মের পথহারাদের দলে ভিড়ে যাননি। প্রাকরণিক বিশুদ্ধতাকে মান্য করেই তাঁর কবিতা নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছেন। একটি বইয়ের শিরোনামে এবং এই শব্দগুচ্ছে ধৃত বিশ্বাসের সাথে লগ্ন কবিতা লিখে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে হুমাযুন আজাদও পুনর্ব্যক্ত করে গেছেন একই গুরুবাক্য ‘পেরোবার কিছু নেই’। দশকের গণ্ডি পেরিয়ে আবহমান বাংলা কবিতার সঙ্গে যুক্ত হবে তপন বাগচী’র কবিতা, এই আশা অমূলক নয়।
কবিতার আলোচনায় আমি বিষয়বস্তুকে গুরুত্বহীন মনে করি। ফুল নিয়ে যেমন অসুন্দর কবিতা রচিত হতে পারে, তেমনি মল নিয়ে হতে পারে উৎকৃষ্ট কবিতা। কোনো কবির শক্তিমত্তা বোঝানোর জন্য তার নির্মাণ-কুশলতাই প্রকৃত নিরিখ। তবুও বলে নিচ্ছি: তপন বাগচী তাঁর কবিতায় ধারণ করেছেন সমকালীন প্রসঙ্গের চেয়ে বেশিমাত্রায় নান্দনিকতা ও শাশ্বত জীবনকে (নর-নারীর প্রেমও যার অনিবার্য উপাদান)। কিছু সমকালীন, এমনকি রাজনৈতিক প্রসঙ্গও, বিবৃত হয়েছে শিল্পিত উচ্চারণে।
তপন বাগচী’র প্রধানতম বিষয় নান্দনিকতা তথা শিল্পকলার নানা অনুষঙ্গ এবং মিথ ও সাহিত্য-ঐতিহ্য যে-পাত্রে পরিবেশিত হওয়ার যোগ্য, তেমন ক্ল্যাসিকধর্মী আঙ্গিকও তিনি বেছে নিয়েছেন। ছন্দ-অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ গাঢ় উচ্চারণ তার কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে।
কবিতার আলোচনায় আমি বিষয়বস্তুকে গুরুত্বহীন মনে করি। ফুল নিয়ে যেমন অসুন্দর কবিতা রচিত হতে পারে, তেমনি মল নিয়ে হতে পারে উৎকৃষ্ট কবিতা। কোনো কবির শক্তিমত্তা বোঝানোর জন্য তার নির্মাণ-কুশলতাই প্রকৃত নিরিখ। তবুও বলে নিচ্ছি: তপন বাগচী তাঁর কবিতায় ধারণ করেছেন সমকালীন প্রসঙ্গের চেয়ে বেশিমাত্রায় নান্দনিকতা ও শাশ্বত জীবনকে (নর-নারীর প্রেমও যার অনিবার্য উপাদান)। কিছু সমকালীন, এমনকি রাজনৈতিক প্রসঙ্গও, বিবৃত হয়েছে শিল্পিত উচ্চারণে।
অক্ষরবৃত্তীয় রচনা এই কবির ভাবনা প্রকাশের প্রধান বাহন। ১৪ মাত্রার আদিপয়ার (অক্ষরবৃত্ত) প্রায় তিরোহিত হয়ে উঠেছে সাম্পতিক কবিতায়। তিনি তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন বলা যায়। আলোচিত গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশ (একশ’টির মধ্যে চব্বিশটি) কবিতা ১৪ মাত্রার আদিপয়ারে রচিত। ‘অনন্ত অসুখে’, ‘একবিংশী’, ‘কৃষি-প্রকৌশল’, ‘পৃথিবী’, ‘চাঁদোয়া’, ‘তেজী’, ‘রঙিলা’, ‘দ্রোহ’, ‘জীবনের নৈশগাড়ি’ সিরিজ কবিতার পাঁচটি, ‘অধিকার’, ‘পথের হিসেব’, ‘বিকেলনামা’, ‘ঋতুমতী’, জীবিকা’, ‘শেয়ালেরা’, ‘শিল্পযাত্রা’, ‘নদীকাহিনী: এক’, ‘যাত্রাকাহিনী: তিন’, ‘নিবিড় বৃষ্টিতে আজ’, এবং ‘ভিজে ভিজে আমি আজ’ কবিতাগুলোয় রয়েছে ১৪ মাত্রার আদিপয়ারের বহুবিচিত্র প্রকাশভঙ্গি। এই বৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসেবে ‘শেয়ালেরা‘ কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধার করা যাক:
আমাদের খামারের চারপাশে কাল
পাল পাল শেয়ালের ঘোরাফেরা দেখি
এ কী! তারা গান গায় সমবেত সুরে!
দূরে নয়, খুব কাছাকাছি লোকালয়।ভয় কি মোটেই নেই মানুষ ও আলোর?
ভোর নয় সন্ধ্যা নয় বিকেলের ছায়া—
মায়া নেই, নাকি তারা বন্ধু মানুষের!
এর কোনো সুজবাব দারুণ অচেনা।
এই কবিতার প্রথম স্তবকটিতে চার মাত্রার মাত্রাবৃত্তীয় চাল সুস্পষ্ট। এমনকি ‘ভয় কি মো/টেই নেই/মানুষ ও আ/লোর?/’ এ ধরনের মধ্যখণ্ডন দেখিয়ে বাকিটুকুও চার মাত্রার মাত্রাবৃত্তে স্ক্যান করা যায় কিন্তু ‘সন্ধ্যা নয়’ পর্বটিতে এসে মেনে নিতে হয় কবিতাটি ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে রচিত। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হলো বহু পঙক্তির শেষ শব্দের সাথে মিল রেখে পরবতী পঙক্তির প্রথম শব্দটি বেছে নেওয়া হয়েছে, যেমন ‘কাল/পাল’, ‘দেখি/এ কী’, ‘সুরে/দূরে’, ‘আলোর/ভোর’, ‘ছায়া/মায়া’, মানুষের/এর’ ইত্যাদি। এসব শক্তিমান কবিদের কাজ।
‘পথের হিসেব’ থেকে ইতোপূর্বে উদ্ধৃত কবিতাংশের সঙ্গে ১৪ মাত্রার আদিপয়ারে রচিত কবিতা থেকে আরও কিছু উদ্ধৃতি:
চাঁচর চুলের মেয়ে গোপন ক্ষুধায়
চুম্বনের ঘ্রাণ মাখে মুখের ভূগোলে
চরকাবাজির স্রোতে ভেসে যাই একা
চকসা আকাশ থেকে অদৃশ্যের কোলে।
(চাঁদোয়া)তকমার লোভে কবি চিতায় না বুক
তেজী তিনি তথাগত লেখে তমসুক।
(তেজী)প্রাণ যদি নদী হয় স্বচ্ছ কুশিয়ারা
ফেনিল সাগরে ছোটে অনন্ত মিছিল
কীর্তিনাশা বুক হবে শোণিতের ধারা
সুফলা যুবতী যেন ডাকাতিয়া বিল।
(দ্রোহ)একদিন এইসব পুরোনো দলিল
পুড়ে হবে ভস্মসাৎ ব্যর্থ হাহাকারে
তবুও সমুদ্রগামী আমাদের আশা
রা পাবে নামমুদ্রা কালের বিচারে।
(জীবনের নৈশগাড়ি: দুই)
উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোয় শুধু ছন্দ নয়, অন্ত্য্যমিল ব্যবহারেও তপন বাগচী’র পটুত্ব এবং বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যে ধরনের অসমমাত্রিক মিল আধুনিক পাঠকের কাম্য, তার উদাহরণ এ গুলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আদিপয়ারে রচিত কবিতায়ও ভূগোলে(৩)/কোলে(২), বুক (২)/তমসুক (৪), কুশিয়ারা (৪)/ধারা (২), মিছিল (৩)/বিল (২), হাহাকারে (৪)/বিচারে (৩)’—এ সব অসমমাত্রিক অন্ত্যমিলের ব্যবহার কবির আধুনিকতা ও শক্তিমত্তার পরিচয়বাহী।
১৪ মাত্রার আদিপয়ারের পর রয়েছে ১৮ মাত্রার পয়ারের প্রাধান্য—সংখ্যায় ১৭টি: ‘অন্তরী’, ‘শুদ্ধস্রোত’, ‘শঙ্খধ্বনি’, ‘তৃষ্ণা’, ‘ষোড়শী’, ‘নদীকাহিনী: দুই’, তিন ও চার’, ‘কবি ত্রিদিব দস্তিদার’, ‘অপ্রাপ্তির আলো’, ‘যাত্রাকহিনী: এক ও দুই’, ‘শামসুন্নাহার: দুই’, ‘অসুন্দর নাচে’, ‘জবান’, ‘শাহবাগ: এক’, ‘চোখ রোদ্দুরের দিকে’। তবে চূড়ান্ত বিবেচনায় ‘নৌকাকাণ্ড’ কবিতাটিকেও ১৮-মাত্রার পয়ার হিসেবে গণ্য করা যায় কারণ ১২-পঙক্তির এই কবিতার শেষ পংক্তিটি কেবল ১৪ মাত্রার। তাহলে এই আঙ্গিকের কবিতার সংখ্যা হয় ১৮টি।
২২ মাত্রার পয়ার ছন্দে রচিত হয়েছে ‘বোধঘুড়ি’, ‘জন্মদিনে’, ‘যাত্রাকাহিনী: পাঁচ’, যাত্রাকাহিনী: দশ’, এবং ‘কবিরা ব্রাহ্মণ হয়’—এই ছয়টি কবিতা। গদ্যাক্রান্ত— ধ্বনি শ্রুত হলেও ‘ভারতবর্ষের কবি’ কবিতাটিও ২২-মাত্রার চালে বিন্যস্ত।
‘এই শহরে’, ‘কবিতার আতুড়ঘরে’, ‘কেমন আছি কোথায় আছি’, ‘বৃষ্টি’, ‘ফাগুন-স্মৃতি’, ‘ঢেউয়ের ফণায়’, ‘পদচ্ছাপ’, ‘বর্ষাপাড়ায়’, ‘লিখুক, লিখতে দিন’-এই ১০টি কবিতা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। স্বরবৃত্তে রচিত হলেও ‘ঋণমঙ্গল‘ কবিতাটিতে আছে পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্তীয় দোলা। গুটিকয়েক পর্বে ব্যতিক্রমের কারণেই এটি স্বরবৃত্তীয় হয়ে উঠেছে। জীবনের নৈশগাড়ি: তিন‘ শিরোনামের কবিতাটি মিশ্র ছন্দে লেখা: প্রথম দুই স্তবক ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে আর শেষ স্তবক ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে।
৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লেখা ’কেয়া-কাঁটা’, ’আবাহনী’, ‘যাত্রাকাহিনী: সাত’ এবং ‘চাষাবাদ’—এই চারটি এবং ৭-মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লেখা ‘তোমার সঙ্গীত’ এবং ‘শুধু জল’—এই দু’টি বাদ দিলে বাকি কবিতার অধিকাংশই রচিত হয়েছে ১৪, ১৮ কিংবা ২২ মাত্রা-অভিমুখী মুক্তক ছন্দে। ‘অভিমুখী” শব্দটি দিয়ে আমি বুঝাতে চাইছি পঙক্তিবিন্যাসের মূল প্রবণতাকে।
’এখানে মানুষ’, ইচ্ছের ভ্রূণ’, ‘আকাশ, পদ্মা ও চাঁদের যৌবন’, ’দধীচির হাড় চাই’, ‘সোনালি অসুখ’, ’খোলাবাজার’, ‘শাহবাগ: দুই’, ‘ছিলার মতো ফুল ফুটেছে’, ‘অপোয় আছি’, ’উন্নয়ন-গবেষণা’, ‘যাত্রাকাহিনী: ছয়’, ‘সাংস্কৃতিক সমীক্ষা’ এবং ‘সকল নদীর নাম গঙ্গা ছিলো’—এই ১৩টি কবিতা গদ্যছন্দে রচিত। এই কবি ছন্দ-প্রকরণে দক্ষ বলেই টানাগদ্যের একটি বাদে অন্যগুলোতে রয়েছে অন্তর্লীন ছন্দের দোলা। তাই এগুলোর রচনারীতিকে ‘গদ্য’ না-বলে ‘গদ্যছন্দ’ বলা যেতে পারে।
মধুমতী নদীর জলের মিষ্টিস্বাদ
এখনো রয়েছে কি না জানি না
কীর্তিনাশা তার নাম
সার্থক করেছে জানি অরে অরে
(সকল নদীর নাম গঙ্গ ছিলো)ফুলবাড়িতে কালো কালো ফুল ফুটেছে
খানপুরে, ছোট বুকচি আর গোলাপপুরে ঘুরে
আমি দেখেছি সেইসব ফুলের গন্ধ ঝুলে আছে
(ছিলার মতো ফুল ফুটেছে)
সমপঙক্তির বৃত্তীয় ছন্দে রচিত কবিতায় তো বটেই, অসমপঙক্তিবিশিষ্ট (মুক্তক) কবিতার অধিকাংশেও মিল প্রয়োগে তপন বাগচী’র পারদর্শিতা লক্ষণীয়:
এই হাসি এই গান, বুকের রক্তমাখা এই রঙতুলি
ছুঁয়ে যায় যথারুচি ঠোঁট, চোখ, বুকের মহিমা
বাকি থাকে অভিমান, প্রণয়ের বীমা
কী করে পূর্ণ করি সময়ের ঝুলি?
(বোধ)যেখানে সুলভ সাক্ষী রাজপথ, মিছিলের মুখ;
অঙ্গীকারে মূর্ত হয় প্রাণের স্লোগান
পথের প্রাচীর গড়ি নির্বিকার, মানি না পণিনি
শুধু করি অনিকেত জীবনের গান
(কেতকী ও রাধাচূড়া)
এখানেও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে ‘রঙতুলি/ঝুলি’, ‘মহিমা/বীমা’, ‘স্লোগান/গান’ এসব আধুনিক অসমাত্রিক মিল প্রয়োগে এই কবির দক্ষতা।
সমিল স্বরবৃত্তে রচিত আমাদের কবিতার অধিকাংশই সমমাত্রিক মিলবিশিষ্ট। কেবল বড় মাপের কবিরাই পেরেছেন স্বরবৃত্তীয় রচনায় অসমমাত্রিক মিল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখাতে। এ ক্ষেত্রে তপন বাগচী’র পারদর্শিতার একটি উদাহরণ:
তোমার কথা জাপটে ধরে এক সকালের স্মৃতি
সরল সুখে সুবাস ছড়ায় প্রণয়ের উদ্ধৃতি. . .
‘উদ্ধৃতি‘ শব্দটির মধ্যখণ্ডন লক্ষ করার মতো। স্বরবৃত্তীয় রচনায় এ ধরনের অসমমাত্রিক মিল প্রয়োগ খুবই বিরল এবং কেবল শক্তিমান কবিরাই তা পেরেছেন এবং পারেন।
উপরোক্ত পরিসংখ্যান সাক্ষ্য দেয়: তপন বাগচী সব ধরনের ছন্দ এবং মিল প্রয়োগে দক্ষ হলেও অক্ষরবৃত্তীয় সনেটীয় আঙ্গিকের প্রতি রয়েছে তাঁর প্রবল পক্ষপাত। শব্দের অনুষঙ্গ এবং গাঢ় উচ্চারণও এই অনুজ্ঞাকে সমর্থন করে।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ‘আমার বিবেচনায় কবি-প্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র ছন্দ-স্বচ্ছন্দ্য, এবং মূল্যনির্ণয় যেহেতু মহাকালের ইচ্ছাধীন আর অর্থগৌরবের আবিষ্কর্তা অনাগত সমধর্মী, তাই সমসাময়িক কাব্যজিজ্ঞাসার নির্বিকল্প মানদণ্ড ছন্দোবিচারু।’ গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে ছন্দহীনতার নৈরাজ্যে তপন বাগচী’র মতো একজন কবির আবির্ভাব অভাবনীয় হলেও একারণেই কাঙ্ক্ষিত ছিল এবং এই কবি সেই আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি পূরণ করে চলেছেন।
অবশ্য, কবিতায় বাক-বিভূতি কেবল ছন্দ-মাধুর্য্যের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু কবিতাকে কবিতা হয়ে ওঠার জন্য ছন্দ একটি আবশ্যিক উপাদান—এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ-লেখায় উল্লেখিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ ও হুমায়ুন আজাদ-এর অভিমতে। তবু, কারও কাব্যকৃতির মূল্যায়ন পূর্ণ হয় না যদি অন্তত ছয়টি প্রতিতুলনাজাত অলঙ্কার: উপমা-উৎপ্রক্ষা-রূপক-প্রতীক-সমাসোক্তি-অন্যাসক্ত এবং এর সঙ্গে চিত্রকল্প ও মিথকল্প ব্যবহারে তার শক্তিমত্তা আলোচিত না-হয়। আমি কবিতার আলোচনায় যে-ধরনের উপাত্ত-নির্ভর বিশ্লেষণের প্রয়াসী, তাতে প্রতিতুলনাজাত অলঙ্কার নির্মাণে এই কবির সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা তুলে ধরার জন্য বৃহত্তর পরিসরে অচিরেই ভিন্ন একটি লেখার কথা ভেবে রেখেছি। বলে রাখা যায়: এ-বিষয়েও তপন বাগচী দখল করে আছেন তাঁর প্রজন্মের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসনটি। লক্ষ করা গেছে: প্রচলিত উপমা-উৎপ্রক্ষা ও প্রতীকের চেয়ে এই কবি শব্দ ও বাক্যস্তরের রূপক, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত, এমনকি অতিশয়োক্তির মতো অবহেলিত অলঙ্কার নির্মাণে বেশি উৎসাহী। এইসব অবহেলিত সোনা আহরণ করে তিনি তাঁর কবিতাকে নিজস্ব কায়দায় সমৃদ্ধ করে তুলছেন।
আমার বিবেচনায় কবি-প্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র ছন্দ-স্বচ্ছন্দ্য, এবং মূল্যনির্ণয় যেহেতু মহাকালের ইচ্ছাধীন আর অর্থগৌরবের আবিষ্কর্তা অনাগত সমধর্মী, তাই সমসাময়িক কাব্যজিজ্ঞাসার নির্বিকল্প মানদণ্ড ছন্দোবিচারু। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে ছন্দহীনতার নৈরাজ্যে তপন বাগচী’র মতো একজন কবির আবির্ভাব অভাবনীয় হলেও একারণেই কাঙ্ক্ষিত ছিল এবং এই কবি সেই আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি পূরণ করে চলেছেন।
শব্দস্তরের রূপক, সমাসোক্তি, অন্যাসক্ত ও অতিশয়োক্তির কিছু উদাহরণ (এর অনেকগুলো একান্তই মৌলিক): ‘তুমুল কেতকী’, ‘উলঙ্গ দুপুর’, ‘সোনালি অসুখ’, ‘রূপালি দহন’, ‘নবীনা সকাল’, ‘ধূসর আগামী’, ‘অহঙ্কারী সবুজ’, ‘জলৌকা-পরান’, ‘প্রণয়ের বীমা’, ‘সমযের ঝুলি’, ‘সবুজ রোদে’, ‘পেশির ফলক’. ‘বুকের মহিমা’, ‘বরফের অভিমান’, ‘লোহিত ক্ষরণ’, ‘অনন্ত শাওন’, ‘সাহসের শিখা’, ‘প্রত্যয়ের টীকা’, ‘অনিকেত জীবনের গান’, ‘ইচ্ছের ভ্রূণ’, ‘লাজুক ছায়া’, ‘রাতের মায়াবী কাঁধ’, ‘দেহের জমিন’, ‘দৃষ্টির ঢেউ’, ‘প্রতীক্ষার চক্রব্যুহ’, ‘পিশাচের অট্টহাসি উড়ছে হাওয়ায়’, ‘মিহিন বাতাস’, ‘জলের মিছিল’, ‘দিঘল চুলের মেঘ’, ‘বোধর ঔরসে’, ‘অলঙ্কৃত শাখা’, ‘উপমিত পাতা’, ‘বোধের নাটাই’, ‘বিচলিত বোধিদ্রুম’, ‘আমার বোধিরা হাঁটে’, ‘হৃদয়-দ্রাঘিমা’, ‘বিরহ-সাগর’, ‘ঢেউয়ের ফণা’, ‘মৃত্তিকার গলনালী’, ইত্যাদি, ইত্যাদি।
এই কবির অলঙ্কারহীন অনেক সরল উক্তিও কেবল শিল্পিত প্রকাশভঙ্গির কারণেই ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে:
যে যাবে সে যাবে, তাতে দুঃখ কেন বুকে
আমি তো সুখেই আছি অনন্ত অসুখে
(অনন্ত অসুখে)প্রিয়তমা. তুমি তোমার কোমল হাতে
ছুঁয়ে দাও এই তৃষিত হুদয়কোণ
যতটা সময় রেখেছি কবিতাখাতে
পূর্ণতা পাক শব্দের হরিজন
(আবহনী)
কবিতাখাতে আরও সময় বরাদ্দ করতে হবে তপন বাগচীকে। বহুমাত্রিকতার নিচে কবিতা যেন চাপা পড়ে না-যায় (যেমন পড়েছে আশির দশকের এক শক্তিমান কবি আনিসুল হকের কবিতা কথাসাহিত্য, নাট্যচর্চা ও সাংবাদিকতার ধামার নিচে)। দেখা যাবে: প্রিয়তমার কাছে আর কোমল হৃদয়কোণ ছুঁয়ে দেওয়ার জন্য এমন করুণ আকুতি জানাতে হবে না; বঞ্চিত, তৃষ্ণার্থ পাঠককুল মুখিয়ে আছে এমন সান্দ্র উচ্চারণের প্রকৃত কবিতার জন্য। তাদের আশীর্বাদেই এই ‘শব্দের হরিজন (!)’ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে কিংবা ইতোমধ্যে করে ফেলেছে।


