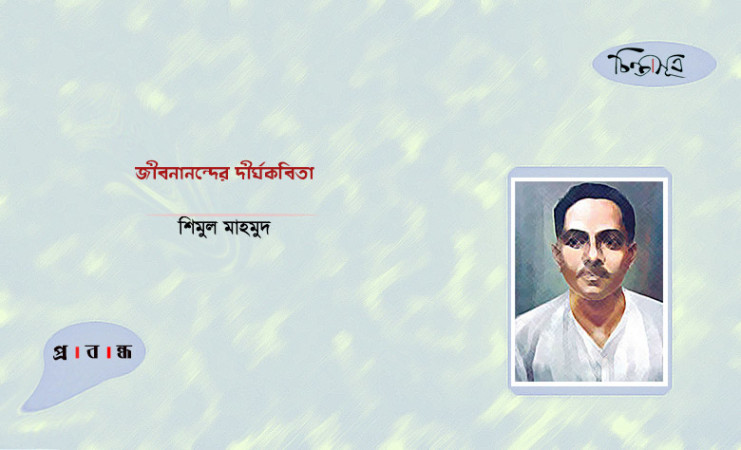সাহিত্য তার উপাদান সংগ্রহ করে জীবন ও জগৎ থেকে। এই জীবন ও জগৎ দীর্ঘকবিতার কাঁচামাল। কবি এই কাঁচামালকে প্রতিভার রসে জারিত করে যে জারক রস সৃষ্টি করেন, তা দীর্ঘকবিতার জীবনরস; জীবনীশক্তি। ক্রমাগত পরিচর্যার ফলে, শব্দ বিন্যাসের কলাকৌশলে অর্থাৎ নিছক কারিগরি দক্ষতার কারণেও কেউ পদ্য বা ছড়া লিখে ফেলতে পারেন। হয়তো বা কেউ কেউ গীতিকবিতাও লিখে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘকবিতার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। মানব জীবনের বহুবিচিত্র তাৎপর্য ও অভিজ্ঞতাসমূহকে উন্মোচিত ও বিশ্লেষিত করে দর্শন-নির্ভর প্রজ্ঞায় দীর্ঘকবিতাকে স্থিত করতে হলে প্রতিভার পাশাপাশি প্রয়োজন কবিত্ববীজ। সঙ্গে বিশাল মানব জীবনকে অন্তর্চক্ষু দিয়ে বিশ্লেষণের এক অস্বাভাবিক ক্ষমতা; যা কিনা সাধারণ লেখকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
সাহিত্য তার উপাদান সংগ্রহ করে জীবন ও জগৎ থেকে। এই জীবন ও জগৎ দীর্ঘকবিতার কাঁচামাল। কবি এই কাঁচামালকে প্রতিভার রসে জারিত করে যে জারক রস সৃষ্টি করেন, তা দীর্ঘকবিতার জীবনরস; জীবনীশক্তি। ক্রমাগত পরিচর্যার ফলে, শব্দ বিন্যাসের কলাকৌশলে অর্থাৎ নিছক কারিগরি দক্ষতার কারণেও কেউ পদ্য বা ছড়া লিখে ফেলতে পারেন। হয়তো বা কেউ কেউ গীতিকবিতাও লিখে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘকবিতার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। মানব জীবনের বহুবিচিত্র তাৎপর্য ও অভিজ্ঞতাসমূহকে উন্মোচিত ও বিশ্লেষিত করে দর্শন-নির্ভর প্রজ্ঞায় দীর্ঘকবিতাকে স্থিত করতে হলে প্রতিভার পাশাপাশি প্রয়োজন কবিত্ববীজ। সঙ্গে বিশাল মানব জীবনকে অন্তর্চক্ষু দিয়ে বিশ্লেষণের এক অস্বাভাবিক ক্ষমতা; যা কিনা সাধারণ লেখকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
জীবনানন্দ দাশ সাধারণ লেখক নন। তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি দীর্ঘকবিতাতে এসে স্ফূর্তি লাভ করেছে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর মতো শুধু নয় অথবা একজন ফটোগ্রাফারের মতো শুধু নয় বরং একজন চিত্রশিল্পী যেভাবে রঙের সাহায্যে জীবনের ছবি আঁকেন জীবনানন্দ দাশ তাঁর শব্দরাশি দিয়ে চিত্রকর যা পারেন না সেই না পারা অনুন্মোচিত অভিব্যক্তির ছবি আঁকেন দীর্ঘকবিতার শরীরে। তিনি শুধু মানুষ নয়, মানুষের অভিজ্ঞতা-প্রজ্ঞা-দর্শন বীক্ষণ আর প্রতিবেশের যথাযথ উপস্থাপনায় তাঁর কবিতাকে গতি দান করেন। সৃষ্টি করেন চলমান ছায়াছবি। যেখানে প্রতিবেশ নিজেই এক অর্থবহ ভাষা, উপলব্ধিজাত মেসেজ ও ইঙ্গিতবাহী চূড়ান্ত মননজাত এক স্বয়ম্ভূ শিল্প। এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের শব্দগুলো তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে না। কবি শব্দকে শাসন করতে জানেন। সুতরাং কবি শব্দ দ্বারা প্রতারিত হন না। ফলে কবির উপলব্ধিজাত চেতনা সরাসরি শব্দে স্থানান্তরিত হতে সক্ষম। কবি যা দেখতে পান, অথচ যা আমাদের চোখে অদৃশ্য, তাকে কবি কবিতায় উপস্থাপন করতে সক্ষম। এই গুণটি দীর্ঘকবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
জীবনানন্দ দাশের ধূসর পাণ্ডুলিপি-র ‘কয়েকটি লাইন’ কবিতাটিতে দীর্ঘকবিতার কিছু লক্ষণ সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। বলা সম্ভব এই কবিতার ভেতর রয়েছে দীর্ঘকবিতার বীজ, যা শেষ পর্যন্ত লিরিক হিসেবে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করলেও দীর্ঘকবিতা হিসেবে সফল হয়ে ওঠেনি। আসলে এটি দীর্ঘকবিতা নয়। যদিও গোটা কবিতাটি ১৭৮ টি পঙ্ক্তির সমন্বয়ে রচিত। দীর্ঘকবিতা হিসেবে কবিতাটির প্রধান দুর্বলতা, কবিতাটির সমস্ত শরীর জুড়ে রয়েছে আমিত্বের প্রকাশ। রয়েছে ‘আমি’ চরিত্রের চূড়ান্ত পদচারণা। যা কিনা দীর্ঘকবিতার বিশাল ব্যাপ্তি নির্মাণের অন্তরায়। কবি গীতিকবিতার মতোই এখানে আত্মমগ্ন অহমের দাস।
কবিতার শুরুটা খুব নীরবে নিভৃতে আরম্ভ হয়ে ক্রমান্বয়ে আত্মকথনে আত্মলীন হতে হতে রূপকথার পথ ধরে কবি তার প্রেমিকার নিকট পৌঁছে গিয়েছেন। তারপরও কবি নিরাসক্ত। কবি উৎসবের গান শোনাতে প্রস্তুত নন। প্রস্তুত নন, ব্যর্থতার গান শোনাতে। শুধু বারবার তাঁর ঘুম ভেঙে যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের জাদুস্পর্শে। অন্ধকার। নিঃসাড়তার অন্ধকার। অথচ রাতভর নক্ষত্রের আলো ঝরে পড়ে যেখানে, সেখানে পৃথিবীর কানে কানে শস্য গান গেয়ে ওঠে। কবি তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে ঠাণ্ডাফেনা ঝিনুকের মতো চুপচাপ আত্মগত লীন। আর মাঠে মাঠে ঘাসেরা নিবিড় হয়ে আরও গভীর হয়ে বেড়ে ওঠে। বেড়ে ওঠে ভালোবাসার ভাষা। তারপর স্মৃতি এবং ক্লান্তি। কবি ক্রমাগত নিজের ভেতর আত্মগত লীন হতে হতে একান্ত নিজের অনুভূতির কাছে, ভাষার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং ১৭৮ পঙ্ক্তির কবিতাটি শেষ হয়। পাঠকও কবির আবেগের সাথে নিজ জগতের আবেগের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।
এই যে একান্ত আবেগে সমর্পণ, যা শুধু কল্পনার নভোচারী, যা শুধুই রূপতৃষ্ণায় হাবুডুবু খায়, তা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার তাৎপর্য ধারণ করে; দীর্ঘকবিতার নয়। একইভাবে ‘অনেক আকাশ’ কবিতাটিতে দীর্ঘকবিতার অনুষঙ্গ ও ব্যাপ্তি থাকলেও ‘পরস্পর’ কবিতার মতো তা দীর্ঘকবিতার আবেদন পুরোমাত্রায় ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। বরং ‘পরস্পর’ কবিতাটিকে দীর্ঘকবিতা হিসেবে বিবেচনায় আনলে এর ভেতর পাওয়া যায়, রূপকথা। রূপকথার মধ্য দিয়ে কবি ভালোবাসার গল্প বলার ছলে পক্ষান্তরে প্রতারক পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন। ফলে কবিতার শেষে গিয়ে কবি বলেন, ‘সব বাসি,—সব বাসি—একেবারে মেকি!’
কবিতার শুরুতেই একজন ঘুমন্ত নারীর ছবি। যে মেয়ে নিঃসাড় পুরীতে একাকী এক পালঙ্কে শুয়ে আছে। পাহাড়ের পাড় ঘেঁষে এই প্রাসাদ। পৃথিবীর সমস্ত রূপের যোগফলের ঊর্ধ্বে এই রমণীর রূপ। কবি গল্প শোনাতে থাকেন,
তারে আমি দেখেছিগো,— সেও চোখ বুজে পড়েছিলো;
মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাত দুটি বুকের উপরে তার রয়েছিলো উঠি!
গতিহীন নিথর সেই রমণীর দেহ। পাথরের মতো সাদা তার শরীর। এই রমণীর যেন কখনো ছিল না কোনো হৃদয়। অথবা ছিল, যা কবির জন্য নয়। সুতরাং কবি তাকে জাগাতে পারেন না। অর্থাৎ পজেটিভ শক্তিকে, শুভ শক্তিকে কবি জাগাতে পারছেন না। পৃথিবীর প্রতিটি হাত যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছে। তবুও কবি আশাবাদী, হয়তো সে জেগে উঠবে। হয়তো তখনই জেগে উঠবে সেই শুভ শক্তি যখন কবির প্রেমিকা গিয়ে তাকে স্পর্শ করবে। অর্থাৎ পৃথিবীর তাবৎ প্রেমিকার মধ্যে ক্রিয়াশীল ইতিবাচক শক্তি।
কবিতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, কোনো এক পরিচিত কুমারের কাছে গল্প বলছে কেউ। গল্পের পাত্র পাত্রিদের দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে কুমার, ‘তারপর, কহিল কুমার, আমিও দেখেছি তারে,— বসন্তসেনার মতো সেইজন নয়,— কিম্বা হবে তাই।’ আর এদিকে নদীর শিয়রে নবমীর জোছনা ঝরে পড়ছে। অনাদিকাল প্রবাহমান পদ্মা-ভাগীরথী-মেঘনা। দেশ থেকে দেশে, ভূমি থেকে ভূমিতে, অচীনপুরে বয়ে চলে নদী। আর তারার আলো, নিবু নিবু জোছনায় পথ দেখে দেখে ভেসে চলে নদীর সাথে। সেই নক্ষত্রময়ী নদীর বুকে আরও একটি চরিত্র কান পেতে শুনতে থাকে শব্দ। শব্দেরা ভাষা বোনে। সেই ভাষা মাঘরাতে অথবা ফাল্গুন অতিক্রম করে ছুটে চলে সময়ের অনাবিল গহ্বরে।
ভাষার আহ্বানে শীতের রাতে ঘুম ভেঙে যায়। খসে পড়ে চোখের ঘুম। আর জমানো ফেনার মতো নদীর কিনারে শীতের কুয়াশা নিজেই একটি স্বয়ম্ভূ চরিত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে থাকে প্রকৃতি ও মানুষ। মানুষের নীরব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর চলে যায় বসন্তের দেশে, জীবনের দেশে, যৌবনের দেশে। অতঃপর একজন মানুষ রাত জাগে আর একজন মানবী শুধুই ঘুমায়। ঘুমিয়ে থাকে পৃথিবীর বিবেক। আহা ভাসমান কুয়াশা। হাতির দাঁতের তৈরি মূর্তির মতো শুয়ে থাকে কুয়াশা। শুয়ে থাকে শুভ শক্তি। শুয়ে থাকে পবিত্র প্রিয়তমা নারী,— ‘শুয়ে আছে,— শুয়ে আছে,— শাদা হাতে ধবধবে স্তন রেখেছে সে ঢেকে!’— অতঃপর কাহিনি অসমাপ্ত থেকে যায়। তীব্র ইঙ্গিতবহ বক্তব্যকে উস্কে দিয়ে কাহিনি অসমাপ্ত থেকে যায়।
অসমাপ্ত গল্প আমাদের মনে আকাক্সক্ষা জাগায়। কল্পনার স্নায়ুকে করে তোলে ক্ষুরধার। শুধুই ছবি ভেসে ওঠে মগজে। মগজ ভাববার অবকাশ পায়। অথচ বিশ্রাম পায় না মগজ। মগজ জটিল মেটাফরে ভাষারাশিদের সরলীকরণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কী কথা বলতে চায় পৃথিবীর বহমান বাস্তব দৃশ্যাবলী? অতঃপর আমরা খুঁজতে শুরু করি ঘুমন্ত সেই নারীর মুখ। দিনের আলোয় মুছে যায় সব। অথচ খুঁজতে থাকি আমরা,—হৃদয়ে এক বিশাল তৃষ্ণার মতো ক্ষত নিয়ে মানুষেরা অনুসন্ধানরত সেই শুভ শক্তির। কুমারের গল্প বলা শেষ হলো।
এ অবস্থায় আরও একজন আরও একটি রূপকথা বলা শুরু করে। উত্তর সাগরের গল্প। সেখানে কেউ নেই। শুধু জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ। উঁচু নিচু পাথরের খাঁজ, পাহাড়; সেখানে জেগে ওঠে কেউ। অতঃপর ঘুম যায় ওরা। সাগরের ফেনার মতন ওরা শীতল, সাদা। ওরা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে সাগরের ঢেউয়ের মতো… ঢেউয়ের মতো তারা ঢলে পড়ে। আবছায়া চরিত্রদুটো প্রতীকী ইঙ্গিত নিয়ে, প্রতীকী তাৎপর্য নিয়ে ক্রমাগত উন্মোচিত হতে থাকে। ওরা মূর্তি পায়। চেনা যায় ওদের। ওরা জলকন্যা। ঠাণ্ডাসাদা ওদের স্তন। জলকন্যাদের চোখমুখ ভিজে আছে ফেনার শেমিজে। পিছল ওদের শরীর। আর,— ‘কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল চাঁদের বুকের থেকে ঝরে উত্তর সাগরে! পায়ে চলা পথ ছেড়ে ভাসে তারা সাগরের গায়ে,’— ওদের পায়ে কাঁকড়ের আঘাতে কোনো রক্ত চিহ্ন ফুটে ওঠে না। রূপের মতো ওদের চুল ঝিকমিক করে উত্তর সাগরে।
বারবার কবিতার শরীরে এই জলকন্যাদের দৃশ্য ভেসে উঠতে দেখা যায়। পাঠকের মনে মাদকতা জাগে। ইমেজ প্রসারিত হতে থাকে। কাচের গুড়ির মতো শিশিরের জল, চাঁদ, উত্তর সাগর— অতঃপর পাঠকের ভয়ানক তৃষ্ণা জাগে; উত্তর সাগরে ছুটে যাবার তৃষ্ণা। কল্পনা তীব্র হয়। অতঃপর অন্তর্চক্ষু স্বাধীন হয়। শীতের শেষে বসন্ত আসে। একজন কবি তন্ময়, সৌখিন। নিশ্চয় এই গল্পের ভাষা বোঝার মতো একজন কবি জন্ম নেবেন আমাদের দেশে। আমরা শুধু বলে যাই পরীর মতো এক ঘুমানো মেয়ের কথা। হীরের ছুরির মতো শরীরের ঐশ্বর্য ওর হয়ে ওঠে আরও ক্ষুরধার। আহা, ওর কাছে কেউ নেই আজ। মেঘের মতো চুলের ঢেউ পালঙ্কের ধারে এলিয়ে আছে। আহা, ধূপের ধোয়ার মতো সেই চুলরাশি সেই পরীর ভেতর নীরব।
আর সেই ঘুমন্ত মেয়ের চারপাশে হাড়ের স্তূপ। রাজ-যুবরাজ আর যোদ্ধাদের হাড়ের পাহাড়। ইতিহাসের পর ইতিহাসের চিত্রপটজুড়ে আত্মাহুতি। যুদ্ধ। যুদ্ধজয়ের ইতিহাস। অথচ তারপরও চলমান সমাজ সেই শুভ শক্তির ইঙ্গিতবহ প্রতীকী মেয়েটিকে জাগাতে অক্ষম। বিবেক ঘুমিয়ে আছে। লম্বা একটা যুগ। লম্বা একটা শতাব্দী। লম্বা একটা মানব প্রজন্মের গোটা বিবর্তিত সময় জুড়ে বিবেক ঘুমিয়েই থাকে। সুতরাং আমরা শুধু রূপকথার রূপসীর ছবি নিয়েই তৃপ্ত থাকি। এই ছবি একে একে এসে দেখে যায় প্রত্যেকে। দেখে যায় একজন কবি। স্বপ্ন, জাদু, মায়াবী জগৎ, গল্প-রূপকথা; যেন রূপকথা নয়, তেপান্তরের মাঠ; আহা গল্প নয়, সবটুকুই মানুষের কথা, মানুষের হৃদয়ের কথা, ঘুমন্ত হৃদয়ের কথা। ফ্যান্টাসি চিত্রকল্পের আলোকে এই রূপকথাগুলোতে প্রকৃত প্রস্তাবে মানব মনের অনুন্মোচিত চিরন্তন আকাক্সক্ষারই প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। যা জীবনানন্দের দীর্ঘকবিতার অর্থমাত্রার সীমানাকে ধাপে ধাপে ছড়াতে ছড়াতে একটা সার্বিক সারবক্তব্যের কাছে পৌঁছে দেবার অবকাশ পায়।
সুতরাং কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ দাশ লাল রোদে ঝলমল এমন এক দিনের ছবি আঁকেন এবং সেসাথে সবজির গানে গানে সহজ সাবলীল এমন এক প্রাকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যে, সেই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে ভেঙে যায় সেই ঘুমন্ত শুভ শক্তির ইঙ্গিতবহ প্রতীকী নারীর ঘুম। যাকে ইতিহাসের সহস্র যুদ্ধও কখনো জাগাতে পারেনি। এবং সেই মেয়ে, ছেড়া করবীর মতো মেঘের আলোকে মায়াবী ঘরে জেগে ওঠে পালঙ্কের ওপর। আহা সবজির গানের প্রাকৃত স্বাধীনতার এমনই তাৎপর্য! বিস্ময়!
‘ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি, দেখিলাম তবু চেয়ে-চেয়ে এ ঘুমানো মেয়ে,’— এই মেয়ে যেন গোটা পৃথিবীর প্রতিভূ। মানুষের দেশের মতো এক সমগ্র দেশ নিয়ে হৃদয়ে, বসে আছে মেয়ে। রূপ ঝরে পড়ে। তবু যারা সৌন্দর্যের মিথ্যে আয়োজনে ব্যস্ত, আফসোস তাদের জন্য। আফসোস সেই মিথ্যে সৌন্দর্যের স্বর্গ নির্মাণে ব্যস্ত যারা তাদের নির্বোধ আত্মার জন্য। যে যৌবন ছিঁড়ে ফেঁড়ে যায়, সেই যৌবনের জন্য আফসোস। একদিন এই সুন্দর নর আর নারীরা আয়নার প্রতিবিম্বে নিজেদের চেহারা দেখে ভয়ে কুঁচকে উঠবে। ওরা শরীরের ঘুণ রেখেছে ঢেকে। ব্যর্থতা লুকিয়ে রেখেছে বুকে। অনিবার্য ক্ষয়; অব্যাহত দিন আর রাত্রি। অথচ আমরা জড়াগ্রস্থ নির্বোধ মানুষেরা তো পারতাম সেই ঘুমন্ত রমণীকে জাগিয়ে তুলতে। যার মুখ শুভ সৌন্দর্যের জ্যোতিতে ঐশ্বর্যময় এক অবিনশ্বর মূর্তি। অথচ হায় সেই নারীটিও একদিন,— ‘দেখেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ, চোখে ঠোঁটে অসুবিধা,— ভিতরে অসুখ! কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে!’
এই মহাবিশ্বের যাবতীয় শুভ শক্তিকে একে একে শুষে নেয় দেবতা গন্ধর্ব-নাগ-পশু ও মানুষ। এ পর্যায়ে এসে কবিতাটি যথার্থ অর্থে দীর্ঘকবিতার মর্যাদা লাভ করে। চূড়ান্ত তাৎপর্য নিয়ে যে সত্যভাষ্যের জগৎ এখানে উন্মোচিত হয়েছে তা পাঠকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রজ্ঞার জগৎকে চলিষ্ণু করে তোলে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রাগৌতিহাসিক কাল থেকে দেবতাদের অংশগ্রহণ। পৃথিবীর কোনো মিথই তাৎপর্যহীন নয়। চূড়ান্ত সত্যের জগৎকেই মিথ উন্মোচিত করে। দেবতা গন্ধর্ব, অশুভ শক্তি নাগ আর মানুষ স্বয়ং পৃথিবীর আয়ু, সৌন্দর্যের আয়ু ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। অবশেষে পৃথিবীর এই পাঁচ হাজার কোটি বছর পর আমরা পেয়েছি এক কুৎসিত রুগ্ন পৃথিবী। তবুও আমরা অপেক্ষায় থাকি। পরী নয় অথবা ঠিক মানুষও নয়, সেই মেয়েটির জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকি। হয়তো সে আসবে। প্রেমিকের ভালোবাসার স্পর্শে বিশ্বাস জাগে; হয়তো আসবে সেই রূপকথার মেয়ে। অথচ দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে শুধু বাসি চাঁপাফুল।
ব্যক্তিগত আবেগ নয় অথবা শুধুই ফ্যান্টাসি রোমান্টিক ইমেজ নয়। বরং ফ্যান্টাসি রোমান্টিক ইমেজের আশ্রয়ে বহমান মানব সভ্যতার চিরন্তন আকাক্সক্ষা যে নান্দনিক পিপাসার আহ্বান জানায় তারই উন্মেষ, বিবর্তন ও ব্যর্থতার গল্প বুনন করেছেন কবি; কবিতাটিতে। ফলে কবিতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভাব উচ্ছ্বাসে আটকে না থেকে একটা সার্বজনীন ভাববক্তব্যে উন্নীত হয়ে পাঠককে জীবন জীজ্ঞাসার মুখোমুখিতে দাঁড় করিয়ে দেয়; যা দীর্ঘকবিতার একটি অন্যতম লক্ষণ। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, দীর্ঘকবিতার রূপক-উপমা-চিত্রকল্পগুলো প্রত্যেকেই স্বয়ম্ভূ। এই চিত্রকল্পগুলো নিজেরা মিলেমিশে চরিত্র হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় এবং এই চরিত্রসমূহের আশ্রয়ে ঘটনাপ্রবাহের যোগসূত্র নির্মিত হয়ে নতুন তাৎপর্যে উন্নীত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিটি রূপক-উপমা-চিত্রকল্পের তাৎপর্য শুধুমাত্র প্রতিঅর্থমাত্রাই সৃষ্টি করে না বরং তা গতিশীল চিত্রকল্পের সাথে সাথে ক্রমাগত প্রত্যক্ষভাবে কাহিনির ঐক্যসূত্র রক্ষা করে অর্থ-তাৎপর্যকে কাহিনির সমান্তরালে উপস্থাপন করে।
ফলে রূপক অথবা প্রতীক অথবা উপমা যাই বলি না কেন ওরা স্বয়ম্ভূ ব্যঞ্জনামাত্রা লাভ করে; যা কিনা কবির প্রকাশযোগ্য বক্তব্যকে সরাসরি ভাষায় অর্থাৎ কবিতার শরীরে স্থানান্তর করতে সক্ষম। যেমন আলোচ্য কবিতাটিতে কবি-চরিত্র নিজেই একটি প্রতীক এবং যার রয়েছে অবশ্যই তাৎপর্যধর্মী বক্তব্য ও ঘটনার সাথে যোগসূত্র। কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে একজন ঘুমন্ত নারী। এই রমণীও একটি প্রতীকী বিন্যাস। যে কিনা গোটা কবিতার মেসেজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যে সৃষ্টি করেছে অর্থময় রূপকল্প। বুনন করেছে ঘটনার ধারাবাহিকতা। উস্কে দিয়েছে কাব্যভাষার ইঙ্গিতধর্মী সম্ভবনাকে। এমনকি সে শুধু প্রতীকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা কবিতার ভাববক্তব্যকে যৌগিক প্রতিবেশে উন্মোচনে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে পাঠক বিভ্রান্ত হয় না এবং দীর্ঘকবিতার বিশাল প্রেক্ষাপটে পাঠক হাবুডুবু খায় না; বরং এই চিত্রকল্পটি জটিল মেটাফরে ও জটিল মোটিভে রচিত হলেও একটা মায়ার জগতের মধ্য দিয়ে, বলা সম্ভব ম্যাজিক-রিয়ালিজম কৌশলে পাঠককে কবিতার সাথে সমাজ বাস্তবতার যোগসূত্রটিকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। ফলে প্রতীকটির ধারাবাহিক উপস্থিতি শুধুই চিত্রময়তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হয়ে বিষয়নির্ভর ও অর্থবহ বক্তব্যের সূত্র ধরে অগ্রসর হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।
সুতরাং এ কবিতাটি নিছক ভালোলাগার ছবিমাত্র নয়; বরং পাশাপাশি তা পাঠককে ভাবাতে শেখায়; পাঠককে নিয়ে যায় সাফারিং-এর পর্যায়ে। এই যে সাফারিং, এই যে ক্লাইমেক্স, যা কিনা দীর্ঘকবিতার লক্ষণ বহন করে। অথচ এই সাফারিং তথা সাফারিং-এর মধ্য দিয়ে যে ক্যাথারসিসের সূত্রপাত ঘটে তা সম্ভব হয়ে থাকে ট্রাজিডি অথবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে। কিন্তু দীর্ঘকবিতার জগতে পাঠক যদি সত্যিকার যোগ্যতা নিয়ে ভ্রমণ করতে সক্ষম হন, তা হলে অবশ্যই তাদের চিন্তার জগতে এক ধরনের সাফারিং ক্রিয়াশীল হবে; হওয়া সম্ভব। যে অভিজ্ঞতা আমরা ওক্টাভিও পাজ, কাহ্লিল জিবরান, টি. এস. এলিওট, গীন্সবার্গ অথবা এমনি আরও অসংখ্য কবির দীর্ঘকবিতা পাঠে পেয়ে থাকি। এই সাফারিং-এর সাথে সাথে পাঠকের মধ্যে একটা দায়ভার, একটা অপরাধবোধ, এক ধরনের কষ্ট দানা বাঁধতে থাকে। ফলে সচেতন এক মহাকালের চরিত্র নিয়ে পাঠকের মগজে বিবেক ক্রমাগত ক্ষত সৃষ্টি করতে থাকে। পাঠক মুক্তি পায় না। এবং যেহেতু বহমান মানব প্রজন্মের রূপকল্প হচ্ছে দীর্ঘকবিতা। এই রূপকল্পের স্বরূপ উপলব্ধির কারণেই পাঠক মুক্তির পরিবর্তে আবারও ফিরে আসে জীবনেরই কাছে। ফিরে আসে অজস্র অমীমাংসিত প্রশ্নের কাছে।
যেমন, ‘অবসরের গান’ কবিতায় এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন ঐশ্বর্যকে অঙ্কন করা হয়েছে, চাষ করে যারা ক্ষুণ্নিবৃত্তি করে। কার্তিকের ক্ষেত। ভেসে আসে মাঠভরা ফসলের ঘ্রাণ। ভোরের রোদের চোখে শিশিরের প্রতিভাস। এই প্রতিভাসের স্পর্শে পেকে ওঠে ধান। অজস্র ফসলের ঐশ্বর্য। পেঁচা আর ইঁদুরের গন্ধ। চারিদিকে ছায়া-রোদ-খুদ-কুঁড়ো-কার্তিকের উৎসব। এই উৎসবমুখর দৃশ্য অবলোকনে পেশাজীবী মানবগোষ্ঠীর চোখের ক্ষুধা তৃপ্তি লাভ করে; কর্ণগহ্বর হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ। — ‘পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।’
কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়, একটি সমঝদার চরিত্র যে কিনা শ্রমজীবী মানবগোষ্ঠীর ঐশ্বর্য দর্শনে আত্মমুখর হয়। সে দেখতে পায় প্রসবোন্মুখ ফসল। হয়তো শীত এসে এই পোয়াতি ফসলের সৌন্দর্য কেড়ে নেবে। তবুও নতুন ফসল জেগে থাকে রাতভর। মাঠেমাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা রোদ। গোলাভরা ফসল; কৃষকের তৃপ্তি। ভাঁড়ারের রস। রসের ঘনত্বে মদ প্রস্তুত হয়। মদ প্রস্তুতকৃত ভাঁড় ছড়া বাঁধে। ওরা শ্রমজীবী মানুষ আনন্দ উৎসবে ভুলে থাকে রাজ্য-জয়ের কথা অথবা সাম্রাজ্যের ছবি। বরং অনেক মাটির তলে যে মদ ঢাকা ছিল তার শীতলতা শুষে নিয়ে তরতাজা হয় ওরা। ওরা মৈথুনে মৈথুনে মাটির সম্ভাব্য চূড়ান্ত ঐশ্বর্য আহরণ করে। আর দৃশ্যপটে ভিড় করে আইবুড়ো মেয়ের দল। কিন্তু এমন এক ঐশ্বর্যময় রাজ্যপটে অনুর্বর বন্ধ্যা রমণীগণের পদচারণা কেন?
এই প্রশ্নকে সামনে রেখে দীর্ঘকবিতার প্রেক্ষাপট জটিলতা লাভ করে। লাভ করে দীর্ঘকবিতার আবহ। সৃষ্টি হয় গল্পের পরিবেশ। যেখানে মাঠের পর মাঠ ফলবন্ত ঐশ্বর্যে টইটম্বুর অথচ সেখানকার রমণীরা বন্ধ্যা। এবং মাঠের পর মাঠ জুড়ে নিস্তেজ রোদ। সেই রোদে নাচের আয়োজন। শুরু হয় হেমন্তের প্রগাঢ় উৎসব। হাতে হাত ধরে গোল হয়ে সকলে নৃত্য করে। ফলন্ত ধানের গন্ধে ভরে ওঠে সকলের নৃত্যরত দেহ। এই দেশে রাগ নেই। নেই কোন হিংসা রিরংসা। অথচ ছোট্ট সময়। ভালোবাসার মতো বেশি সময় নেই ওদের হাতে। ছোট ছোট অলস আহ্লাদের সময়। ভেসে আসে দূরের নদীর মতো অচেনা ঘ্রাণ। অবসাদ। ওদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে আসে। অবসন্ন হয়ে আসে হাত। ফলন্ত শস্য কর্তনের সময় ফুরিয়ে আসে। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে শান্ত সাদা বিকেল। থেমে যায় গেঁয়ো চাষাদের নৃত্য উৎসব। মৃত শেফালি ফুলের বিছানা। ঘাসেরা সাদা হয়ে গেছে। আকাশ হয়েছে শুধুই ধবল। সেখানে শ্যামল মেয়েদের আনাগোনা নেই। ভিড় করে পাড়াগাঁর আইবুড়ি মেয়েদের দল। শেষ হয় দীর্ঘকবিতার প্রথম অধ্যায়।
দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। অন্ধকার। কোটর থেকে পেঁচারা বাইরে আসে। ইঁদুরেরা গর্তে ফিরে যায়। চাষারা ফিরে গেছে মাঠ থেকে। কারা যেন গান গায়। প্রেম আর পিপাসার গান। পাড়াগাঁর সেইসব ভাঁড়, যুবরাজ-রাজাদের মতো যাদের দেহের অস্থি মিশে গেছে মাটির তলে; অনেক অন্ধকারে পৃথিবীর তলে। পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো যাদের ছিল না কোনো ভয় অথবা শঙ্কা। কোনো প্রণয়ীর জন্য ওরা বাধেনি কোনো ছড়া। চাষাদের মতো ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘামে ওদের সময় কাটেনি। আজ শুধু অনেক মাটির নিচে কোনো এক নাম না জানা সম্রাটের অস্থির সাথে ওদের দেহের অস্থি মিশে একাকার।
এখানে যুদ্ধ নেই। শুধুই পাঁচফুট জমিন। ওখানে নেই কোনো দিনের আলো। মাটিতে মিশে যাওয়া সেইসব গেঁয়ো কবি, সেইসব পাড়াগাঁর ভাঁড় এই অন্ধকারে আবার উঠবে কি জেগে? আর আশ্চার্য এইসব গেঁয়ো কবিদের মৃত দেহের অস্থি-মজ্জা-রস শুসে নিয়ে বেড়ে ওঠে ক্ষেতের ফসল। অর্থাৎ কবি সৃষ্টিশীল মানবগোষ্ঠীকে অর্থাৎ শিল্প এবং শিল্পীকে উৎপাদনের সাথে, উৎপাদনের হৃদপি-ের সাথে ভয়ানক হার্দ্যকি উত্তাপে সংযোজিত করলেন। কবি এখানে কবিচরিত্র, চরিত্রগুলোর মৃতচিত্রকল্প অর্থাৎ শিল্পী জীবনের বিনিময়ে ফসলের বেড়ে ওঠা, অর্থাৎ মৃতদেহ থেকে ফসল জন্মের যে অভিজ্ঞান উপস্থাপন করলেন তা শ্রমজীবী চাষিদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রমঘন সংগ্রামের একটি জীবনবাদী চিত্র উপহার দেয়। সঙ্গে উপস্থাপন করে তাৎপর্যমুখী বক্তব্য।
প্রজ্ঞাশীল পাঠক এ পর্যায়ে এসে আত্মমগ্ন হন। লাভ করেন অনুন্মোচিত সত্যভাষ্যের দৈববাণী। কেননা সেইসব মৃত কবিদের মস্তিষ্ক অন্ধকার মাটির নিচে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে স্বপ্নে ওদের মাথাগুলো অদ্ভুত ইশারায় নড়ে ওঠে। এবং মৃত কবিদের এই নড়ে ওঠার সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে অন্ধকারের মশা এবং নক্ষত্রের ঝাঁক। শহর-বন্দর-বস্তি আর মানুষের কারখানা থেকে দেশলাইয়ের আলো জ্বেলে ফিরে আসে সেই সংবাদ। যে সংবাদে শরীরে অবসাদ নামে। মানুষ ভুলে যায় হৃদয়ে জ্বরের তপ্ততা। এবং
শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধরে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই মরে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন।
অতপর চাষাবাদ নয় বরং কী এক অভিমানে চাষারা সকলে জমি উপড়ায়ে ফেলে চলে গেছে। ওদের নতুন লাঙলগুলো পরিত্যক্ত। অথচ পুরোনো সেই ঐশ্বর্যের পিপাসা জেগে উঠেছে আবার মাঠের ওপর। মহাকালের সাক্ষ্যবহনকারী পেঁচা উদয় হয় দৃশ্যপটে। এরপর ফটোগ্রাফের মতো কিছু টুকরো টুকরো ছবি; কিছু অভিব্যক্তির প্রকাশ এবং উদার আহ্বান,— ‘দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।’ — এখানে মেঠো পথে থেমে থেমে ভেসে চলে আকাশের চাঁদ। চাঁদের অবসর অনেক। অবোধ আহ্লাদ ওর। আমাদের সময় শেষ হয়ে এলে পশ্চিমের পানে যেতে যেতে এই মেঠো চাঁদখানা হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জাগরণ তোলে; জাগরণ তোলে কামনা, কামনার গান। শেষ হয় দ্বিতীয় অধ্যায়।
এ পর্যন্ত দৃশ্য অবলোকনে পাঠক নিজেকে গুছিয়ে নেন। প্রস্তুত করে নেন নিজের সত্তাকে। দীর্ঘকবিতার উদার আহ্বানে সাড়া জাগাবার মতো নিজেদের মগজের কোটরগুলোকে শানিয়ে নেন খানিক। অতঃপর মনোনিবেশ করেন তৃতীয় অধ্যায়ে, অন্তর্গত সত্তার সাথে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিতে। পাঠক দেখতে পান প্রবাহমান কালের বুকে শুয়ে আছে একখানা সনাতন ফসলের মাঠ। ভাঁড়ার ঘরে পূর্ণতার আহ্বান। সুতরাং পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই। কৃষকেরা ফিরে আসুক এই মাঠে। দূর কোনো মাঠের খোঁজে যাবার মতো ওদের অবসর নেই। এমনকি অবরোধ-ক্লেশ-কোলাহল শোনার মতো ওদের সময় নেই। ওরা জানতে চায় না কোন ভাঁড় ওদের রাজ্যের রাজা সেজে বসে আছে। অথবা কোথায় কোন নতুন বেবিলন ভেঙে হলো চুরচুর। অথবা ওরা দেখতে চায় না ইতিহাসে জেগে থাকা সৈনিকদের মশালের আগুন। —‘দামামা থামায়ে ফেল— পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ।’
তীব্র স্যাটায়ার। পাঠক উজ্জীবিত হন। শ্লেষ মিশ্রিত বক্তব্য কবিতাকে ধারালো করে তোলে। পক্ষান্তরে ঘোষিত হয় কর্ষণরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর স্বাধীন জীবনাচারের বাণী। অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত,—‘জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।’— অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় কুটিল চিন্তা থেকে এই মানবগোষ্ঠী মুক্তি লাভ করলো। সুতরাং শান্তি। অথচ ‘ক্যাম্পে’ কবিতায় আমরা দেখতে পাই হরিণ শিকারের দৃশ্য। গতি এবং সৌন্দর্যকে হত্যার মর্মকথা। সভ্যতার কূটাভাষ। বন্দুকের শব্দ। হরিণমাংস ভক্ষণ। মাংসাসী মানবগোষ্ঠী। ওখানে চিতার চোখের হিংস্রতা। একখানা শর্ট ফিল্ম। অতঃপর মানব জন্মের সারকথা। কে একজন ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে জীবন ভাবনায় বিভোর। মৃত হরিণের মতো ওর জীবন, আমার জীবন, আমাদের জীবন। যদিও বসন্তের জোছনায় আমরা অবগাহনরত। তথাপি চূড়ান্ত অর্থে গতি আর সৌন্দর্য হত্যা পক্ষান্তরে মানব সভ্যতাকেই হত্যা; মানুষের জীবনকেই হত্যা। এবং ‘জীবন’ কবিতাতে মানব জীবনের উপলব্ধি আরও ভয়ানক প্রগলভা লাভ করে। লাভ করে অনিবার্য দর্শনচেতনা।
৩৪টি খণ্ডে এই দীর্ঘকবিতাটি একটি পূর্ণদৈর্ঘ ছায়াছবির মর্যাদা লাভে সক্ষম। প্রতিটি দৃশ্য এক একটি সিকোয়েন্সে গুচ্ছ গুচ্ছ গতিশীল চিত্রকল্প ধারণ করে স্বয়ম্ভূ গতিরেখায় বক্তব্যকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়েছে। যদিও কবির স্বগত উপস্থিতি কবিতার শরীর জুড়ে ক্রিয়াশীল তথাপি কবিতাটি শেষাবধি দীর্ঘকবিতার মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়ে উঠেছে। এই কবিতায় পৃথিবী নিজেই একটি চরিত্র। প্রধান চরিত্র। রূপক চরিত্র। দীর্ঘকবিতার রূপকগুণ কবিতার অব্যক্ত বক্তব্যকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে দেয়। বিশাল পৃথিবীর বুকের ভেতর অজস্র তাৎপর্যময় চরিত্র তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়া সমাপন করে। সৃষ্টি করে গল্পের ধোয়া, অনুষঙ্গ, বক্তব্যের প্রতিভাস ও চিরন্তন অনুকল্পসমূহ। প্রতিটি ঋতু এই কবিতাতে স্বয়ম্ভূ বক্তব্য নিয়ে জীবন্ত চরিত্র হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছে। অবচেতনে এক ধরনের নাটকীয় টানাপোড়েন। এই নাটকীয় ইমেজ সৃষ্টির অবকাশ দীর্ঘকবিতাতে যথেষ্ট পরিমানেই বিদ্যমান থাকে। এবং এতে দীর্ঘকবিতা গতিশীল হয়ে ওঠে; হয়ে ওঠে জীবন্ত ছায়াছবি। ফলে প্রতিটি চিত্রকল্পের মাঝে পাঠক আপাত অর্থের অতিরিক্ত অর্থমাত্রার ইঙ্গিত লাভ করে। ফলে কবিতার ভাব-ঐক্য আরও খানিকটা ছড়িয়ে পড়ে; প্রগাঢ়তা লাভ করে। পরিণামে বক্তব্য আর নিছক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গুরুত্ববহ মেসেজে উন্নীত হয়।
এই যে ভাষাকৌশল যা গীতিকবিতাতেও অবশ্যই ক্রিয়াশীল কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে অলঙ্কারের অর্থতাৎপর্য নিজস্ব অর্থমাত্রায় সীমাবদ্ধ থাকে অপরপক্ষে দীর্ঘকবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় অলঙ্কারগুলো দীর্ঘকবিতার বিশাল অর্থব্যঞ্জনাকে আশ্রয় করে অর্থমাত্রাকে বিবিধ চরিত্রে ক্রিয়াশীল করতে গিয়ে আপাত অর্থের সাথে সুদূরবিস্তারি অর্থমাত্রায় ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে। যেমন ‘জীবন’ কবিতাতে শস্যের কীটের প্রসঙ্গ একটি পৃথক রূপকল্প সৃষ্টি করেছে; যা কৃষকজীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত; চাষাবাদের চিত্রকল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেসাথে কীটনাশক হচ্ছে অপশক্তি রহিতকরণে ব্যবহার্য; অথচ বিপরীত ব্যবহার যেমন জীবন নাশেও ব্যবহার্য। অথচ এখানে এমনই এক কীটনাশকের ব্যবহার করা হচ্ছে যার দ্বারা পোকামাকরের মৃত্যুর আগেই মানব মনের ভেতরে যে রহস্যঘেরা অব্যক্ত স্বপ্ন রয়ে গেছে তারই মৃত্যু ঘটছে; আর এই মৃত্যু বিষয়ক অনুষঙ্গের সাথে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর গতিশক্তি, বরফ, শীত, আগুন বিবিধ অনুষঙ্গ।
আলোচ্য ‘জীবন’ কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবরের মুখ কথা বলছে। যা আপাতভাবে মিথ্যা অর্থাৎ অসম্ভব। কিন্তু শিল্পের সত্যের কাছে এর গূঢ়ার্থ ভয়ানকভাবে পাঠককে ভাবায়। পাঠক আন্দোলিত হন। পাঠক শিহরিত হন। পাঠক বুঝতে পারেন, দীর্ঘকবিতার জাদুমন্ত্রে কবরের মুখও জীবন্ত হয়ে উঠেছে; যে গুণটি মিথ্যা জগতের পরিবর্তে প্রকৃত সত্য জগতের রহস্য উন্মোচন করে দিচ্ছে। যেমন— ‘নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা,— মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা,’— দেখা যাচ্ছে নির্জন ঢেউয়েরও রয়েছে জীবন্ত কর্ণগহ্বর; যেখানে রয়েছে মানব মনের পিপাসা এবং সেখানে মানব জীবনের মৃত্যুসম বেদনাজাত ভাষা ক্রিয়াশীল।
অদ্ভুত কৃৎকৌশলে এক্ষেত্রে অবচেতন বিষয়ের ওপর চেতন জীবনের গুণারোপ করে মানব জীবনের টানাপোড়েনজাত রহস্যের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। যা দীর্ঘকবিতার ব্যঞ্জনায় আপাত অর্থব্যঞ্জনাকে অতিক্রম করে অধিকতর দীর্ঘ অনুভূতিতে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। কবিতাপাঠে বিষয়টি ক্রমাগত পরিষ্কার হয়ে আসে। অর্থাৎ অলঙ্কারের তাৎক্ষণিক ব্যঞ্জনাতে দীর্ঘকবিতা সন্তুষ্ট নয়। দীর্ঘকবিতা তাৎক্ষণিক অর্থসৌন্দর্যকে চাবি হিসেবে ব্যবহার করে মাত্র এবং পাঠকের কাজ সেই চাবির সাহায্যে কবিতার রুদ্ধ ভাষাসৌন্দর্যের মুক্তি দিয়ে অপার অর্থবৈভবের জগতে প্রবেশ করা। অতঃপর পরিভ্রমণ। পরিভ্রমণে দেখা যায়, মৃত্যুর মতো মানুষের মন ঘুমিয়ে আছে। —‘মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন।’ কবিতা শেষ হয়। আর সেসাথে তৈরি হতে থাকে পাঠকের মনের গভীরে মানব জীবনের রহস্যঘন অমীমাংসিত প্রশ্নের পাহাড়। একটা বিশাল পাহাড়ের মতো পাঠকের মনের গহীনে কবর খুড়তে থাকে মৃত্যুচেতনা। মানব মনের চিরন্তন চেতনা ক্রমাগত পাঠকমনে দানা বাঁধতে থাকে; ক্রমাগত চিত্রিত হতে থাকে। তারপরও বলতে হবে, এই নাতিদীর্ঘ ছায়াছবিটি শেষাবধি মৃত্যুময় কবর থেকে জীবনকে ছিনিয়ে এনে আবারো পৃথিবীর বুকে দাঁড় করিয়ে দেয়।
জীবনানন্দ দাশ এমন একজন কবিপ্রতিভা যিনি নগর জীবনের প্রাচুর্যময় সৌন্দর্যের পাশাপাশি আজীবন অন্ধকারে নিমজ্জিত নিস্প্রভ ক্ষয়িষ্ণু মানুষের দলা পাকানো সৌন্দর্যের ভেতর আত্মমগ্ন হয়েছেন। তিনি বোদলেয়ারের মতো বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক পার্থিব বস্তুর বেঁচে থাকার পেছনে রয়েছে মানুষের আত্মার জগৎ এবং জন্ম। এসব রহস্য বুঝে, ব্যাখ্যা করে একমাত্র কবিদেরই দ্বারা আধ্যাত্মিকতার উঁচু মেরুতে পৌঁছানো সম্ভব। এই কাব্যিক আধ্যাত্মিকতার উঁচু মেরুতে পৌঁছার সিড়ি হচ্ছে দীর্ঘকবিতা। সৌন্দর্যের অনুসন্ধান এবং আত্মিক বিশ্বাসের অনুসন্ধান; এই দুই বিষয়ই জীবনানন্দের নিকট সমান্তরাল। যা কিনা লাভ করা সম্ভব তীক্ষè প্রজ্ঞার সাহায্যে; অনুদ্ঘাটিত রহস্যের ভেতর।
এক্ষেত্রে সৌন্দর্য অবশ্যই আত্মিক বাস্তবতা; যাকে একমাত্র কবিতাতেই ধারণ করা সম্ভব। সৌন্দর্য বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করে না। শিল্পীকেই সৌন্দর্যের ভেতর প্রবেশ করতে হয়। সৌন্দর্য আগুনের শিখা; শক্তির দীপ্তি; আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অভিঘাত। যদিও আপাত পঙ্কিল বিষয় থেকেও এই কাব্যিক আধ্যাত্মিকতার উদ্ভব হওয়া সম্ভব তথাপি কবি জীবনানন্দ দাশ কখনোই বোদলেয়ারের মতো কদর্যতার ভেতর সৌন্দর্যকে দেখেননি বরং তিনি কদর্যতা থেকে সৌন্দর্যকে মুক্তি দিয়ে প্রবাহিত করেছেন কবিতার শরীরে ও আত্মায়। এই সৌন্দর্য নির্মাণ তাঁকে কাব্যিক আধ্যাত্মিকতার জগতে উন্নীত করেছে। এই আধ্যাত্মিকতা যেন আগুনের গভীরতা; যেন প্রকৃতির প্রগাঢ়তা; যা থেকে শিল্পের তাপ উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হয় দীর্ঘকবিতার নূর বা জ্যোতি। যার তাপে একজন কবি মহান হয়ে ওঠেন। ফলে দীর্ঘকবিতা নিছক কবিতামাত্র নয় বরং তিনিই দীর্ঘকবিতার কবি, যিনি কাব্যিক আধ্যাত্মিকতার জন্ম দিতে সক্ষম।
কবিতা যখন পূর্ণতা লাভ করে, কবিতার পূর্ণতায় যখন দর্শন প্রতিবিম্বিত হয় তখন সমস্ত শিল্প এসে জড়ো হয় কবিতাতে। যেমন চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য— সবই একই উপলব্ধিতে একই ভাষা প্রকাশ করে। একই সংকেত প্রকাশ করে। যা কিনা সম্ভব হয়ে ওঠে দীর্ঘকবিতার ক্ষেত্রে। শিল্পের আর কোনো মাধ্যমে এ বিষয়টি এতটা সফলতা পায় না। এক্ষেত্রে দীর্ঘকবিতা পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে অবশ্যই। অর্থাৎ দীর্ঘকবিতা চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও সাহিত্যের রসকে একীভূত করার ক্ষমতা ধারণ করতে সক্ষম।
জীবনানন্দের প্রতিটি কবিতাতেই চিত্রকলার ব্যবহার অনস্বীকার্য। একইভাবে জীবননান্দের দীর্ঘকবিতা ‘সিন্ধুসারস’-এ চিত্রকলার উপস্থিতি ক্রমাগত উন্মোচিত হতে হতে গোটা কবিতা জুড়ে অবশেষে সিন্ধুসারস চরিত্রটি একটি স্থাপত্যে স্থিতি লাভ করে। সঙ্গীত এখানে সঙ্গীত শ্রবণের বীক্ষণ নিয়ে ধরা দেয় না। সঙ্গীত নয় বরং সঙ্গীতরস আস্বাদনের তাৎপর্য নিয়ে কবিতা অনুরণন তোলে পাঠকের মস্তিষ্কে। সেসাথে কবিতার বিষয়বক্তব্য, চিত্রকলার প্রকাশযোগ্যতা, অর্থতাৎপর্য ও ইঙ্গিতধর্মীতাকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলে ভাস্কর্যের মর্যাদায় উন্নীত করলেও সঙ্গীতসুর নয় বরং সঙ্গীত শ্রবণের ফলাফল কবিতাটিকে জাগিয়ে রাখে; নন্দনরসসহ বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং কবিতামধ্যে বলা সম্ভব, —‘সমুদ্রের নীল জানালায় আমারই শৈশব আজ আমারেই আনন্দ জানায়।’
‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থটির দীর্ঘকবিতাগুলোতে যোগ হয়েছে সমাজবাস্তবতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য সেসাথে দৈনন্দিন জীবনাচার। যদিও জীবনানন্দের প্রায় সবগুলো কবিতা সম্পর্কেই এ কথা বলা সম্ভব। তথাপি এই গ্রন্থের সমাজদর্শনের মধ্যে রয়েছে একটু ভিন্ন মাত্রা। যেমন ‘বিভিন্ন কোরাস’ কবিতায় পাওয়া যায়, মানুষের আয়ুরেখা, মৃত্যুরেখা, হৃদয়ের চোখ, দুর্যোগের রাত, তৃপ্তি, উঁচু নিচু দেয়াল, বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা, নৃসিংহের আবেদন, সাধারণ মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব, ভোট, জনমতামত, গ্রন্থপাঠ, নগরীর রাজপথ, মৃতদেহ, আতঙ্ক, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদফসল, স্বর্গবিশ্বাস, জীর্ণ নরনারী, ভীত মুখশ্রী, বিষ্ময়, বক্তৃতা, করতালি, পরিত্যক্ত ক্ষেতের ফসল, নগরীর নাভির ভেতরে ভোর নামে, কলরব, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ, অন্ধকার সংসার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, স্মিতচক্ষু নাবিক, ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময় অর্ধনারীশ্বর, বঙ্গোপসাগর, নাবিকের লিবিডো। উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল, ধোঁয়া, রক্ত। উনিশশো তেতাল্লিশ সাল, উনিশশো চুয়াল্লিশ উৎক্রান্ত পুরুষ, কামানের গোলার ঊর্ধ্বে নীলাকাশ, ভারত সাগর, রিরংসা, অন্যায়, আবারো রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষা, আবারো ভয় এবং স্বাধিকার আন্দোলন, উপনিবেশ শাসনের শৃঙ্খল, ভারতবর্ষ, মানব প্রজন্ম। একইভাবে ৫৪ পঙক্তির ‘সময়ের কাছে’ শিরোনামের দীর্ঘকবিতাতে পাওয়া যায়,
নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেলিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই;
কোথাও আঘাত ছাড়া— তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
পার্সি ধর্ম প্রচারক জরথুস্ত্র। যিনি জন্ম নিয়েছিলেন উর্মি হ্রদের তীরে। তিরিশ বছর বয়সে তিনি ঘর ছেড়ে বের হলেন। গেলেন আরিয়া প্রদেশে। দশ বছর একাকি জীবন যাপন কালে পাহাড়ে পর্বতে রচনা করলেন ‘জেন্দাবেস্তা’ গ্রন্থ। যাকে ধর্ম গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। দার্শনিক ফ্রেডারিক নীটশে জরথুস্ত্রকে নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ ঞযঁং ঝঢ়ধশব তধৎধঃযঁংঃৎধ। সাহিত্যকীর্তি হিসেবেও গ্রন্থটি মূল্যবান। জরথুস্ত্রের দার্শনিক প্রজ্ঞা ও সত্যের জগতে কবি জীবনানন্দ দাশ বিশ্বাসী। জরথুস্ত্রের মতই কবি পীড়িত তাঁর আপন জ্ঞানের প্রাবল্যে। দিব্যচোখে কবি পাঠ করেন ইতিহাস ও সমাজকে। রচনা করেন ‘ইতিহাসযান’ কবিতা। রচনা করেন ‘মহাত্মাগান্ধী’-র মতো সত্যভাষ্যে উজ্জ্বল একটি দীর্ঘকবিতা। ইতিবাচক বক্তব্য নিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছে। অতঃপর সাম্প্রতিক সমাজ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কবিতাটি অগ্রসর হয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ এসেছে, স্থান লাভ করেছে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞানের প্রসঙ্গ। মানুষকে ঘিরে রয়েছে সাম্রাজ্য, রাজ্যের কোটি দীনহীন সাধারণ জনগণ, পীড়িত কখনো বা রক্তাক্ত। আত্মঘাতী মানুষের গল্প। অসম্ভব রকম লৌকিক পৃথিবী।
তারপর ঢের দিন কেটে গেছে—
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হয়ে গেছে;
যেই সব বড়-বড় মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিল
তাদের অন্তর্দান সবিশেষ সমুজ্জ্বল ছিল, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যে সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হয়েছে—
সহিষ্ণুতায় ভেবে সে সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত;
এরপর মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র বিশ্লেষিত হয়েছে। কবিতার সত্য-সৌন্দর্যে মহাত্মা তাৎপর্য লাভ করেছে সমকালের চারিত্র্য লক্ষণের সাথে সমান্তরালে। উল্লেখ করা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর সত্য এবং শান্তি নামক বিষয় দুটোর মর্মকথা। প্রসঙ্গক্রমে কবিতাতে স্থান পেয়েছে মানুষের সহজাত রিপুতাড়িত আকাক্সক্ষার কথা। সুতরাং মানুষও রক্তাক্ত হতে চায়। অথচ এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে মহাত্মা গান্ধী বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করেছেন; শুভ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন। অগ্রসরমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ফলাফলের আলোকে তিনি মানব সমাজের স্বরূপকে উন্মোচনের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। অথচ তারপরও চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে। মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে। বিজ্ঞান নিজেও প্রতারক শাসক। বিশ্বাস তিরোহিত। প্রেম ও শান্তির জন্য, কল্যাণের জন্য যে নন্দনতত্ত্ব, যে গভীর জ্ঞান তা আজ উপেক্ষিত, মৃত। এরপরও আমরা জ্ঞানপাপে আত্মমগ্ন হই। প্রতিদিনই শিক্ষা গ্রহণ করি। অথচ পৃথিবী প্রতিনিয়তই রক্তাক্ত। নন্দন এখানে ব্যর্থ। —‘তবু এই বিলম্বিত শতাব্দীর মুখে যখন জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিল, যখন পৃথিবী পেয়ে মানুষ তবুও তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে, আকাশে নক্ষত্র সূর্য নীলিমার সফলতা আছে, —তবু মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই, শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই।’
পৃথিবীর কোথাও কোনো প্রেম নেই। শুধুই রক্তাক্ততা। প্রার্থনা করার মতো বিশ্বাসের গভীরতা নেই কোথাও। তথাপি মানুষের যে আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা যেন ফিরে আসতে শুরু করেছে মহাত্মা গান্ধীকে আশ্রয় করে। কেননা মানব সমাজের শেষ পরিণতি শুধুমাত্র গ্লানি নয়; হয়তো বা মৃত্যুই সব নয়; হয়তো বা কোথাও প্রেম আছে, শান্তি আছে, প্রগতিশীল মানুষও আছে। সেই কাক্সিক্ষত সমাজে একজন স্থবির মানুষও অগ্রসর হবার সুযোগ লাভ করে। পথ থেকে পথান্তরে এগিয়ে যায় সময়ের কিনারা ধরে, এগিয়ে যায় দূরতর অন্তঃস্থলে। সেখানে সত্য আছে, আলো আছে, আছে সত্যকে আবিষ্কার করার মতো সুযোগ। আমরা আজকের শতাব্দীর মানুষ অবশ্যই সফলকাম হবো,‘জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়।’ এমন এক মহাপৃথিবীর রূপরেখা অঙ্কন সম্ভব একমাত্র দীর্ঘকবিতাতে। দীর্ঘকবিতার প্রকরণ সেই ধারণ ক্ষমতা নিয়েই গড়ে উঠেছে।
‘যাত্রা’ কবিতার বিষয়বস্তু জাহাজযোগে সমুদ্রযাত্রা। কবিতাটি গল্পের ইমেজ নিয়ে দীর্ঘকবিতার স্বাদ দিতে সক্ষম; সক্ষম হয়েছে আঙ্গিক ও বিষয়বক্তব্যে। কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতিটি দীর্ঘকবিতার ক্যানভাসই বিশাল। অসংখ্য চরিত্রের প্রতিভাসে অসংখ্য ঘটনা ইঙ্গিত-তাৎপর্যে কখনো বা মাত্রাবৃত্ত আবার কখনো বা অক্ষরবৃত্তের বলয়ে রচিত হয়েছে। অক্ষরবৃত্তের ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনতা ভোগে বিশ্বাসী। যা কিনা দীর্ঘকবিতা লেখার স্বার্থে সম্ভব হয়ে উঠেছে। কেননা দীর্ঘকবিতা ছন্দের স্বাধীনতা ভোগের মধ্য দিয়ে নতুন ছন্দের জন্ম দিতে ইচ্ছুক। উদাহরণ হিসেবে ‘যাত্রা’ শিরোনামের দীর্ঘকবিতাটির কথা প্রাসঙ্গিক। কবিতার দ্বিতীয় পঙক্তি,‘কোথাও প্রাণের কল্যাণ-সূর্যালোক আছে?’
এক্ষেত্রে পর্ব ও মাত্রা বিন্যাস = ৬ + (৯—১)। অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে এক মাত্রা কমিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। লক্ষযোগ্য, গোটা কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কবি পয়ার এবং মহাপয়ারের গুণাবলি ভোগ করার পাশাপাশি স্বাধীনতাও ভোগ করেছেন পুরোমাত্রায়। যেমন সপ্তম পঙক্তিতে তিনি প্রথমে চারমাত্রার পর্ব নিয়েছেন অতঃপর দশমাত্রার। অর্থাৎ তিনি মুক্তক ছন্দের দিকে ধাবিত হয়েছেন। কিন্তু মুক্তক ছন্দেও তিনি আটকে থাকতে রাজি নন। অথবা মুক্তক ছন্দের রীতি অনুসারে অন্ত্যমিল কবির জন্য অপরিহার্য নয়। তিনি অন্ত্যমিল গ্রহণ করেননি। যেহেতু তিনি লিখছেন দীর্ঘকবিতা। সুতরাং ভাববক্তব্য অনুসারে স্বাধীনতা গ্রহণ অনিবার্য।
অতএব ৮ম পঙক্তির ১ম পর্বে রয়েছে ৭ মাত্রা, যা কিনা টেনে ৮ মাত্রা হিসাবে পাঠ করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দীর্ঘকবিতার ক্ষেত্রে পর্ববিন্যাস রক্ষার জন্য কখনো মাত্রা কমিয়ে বা কখনো মাত্রা বাড়িয়ে কবিতাপাঠ অনিবার্য নয়; বরং অনিবার্য পাঠ কৌশল হল কবিতার অর্থানুসারে পাঠ গ্রহণ; অর্থাৎ দীর্ঘকবিতার পর্ববিন্যাস ও মাত্রা রক্ষা করা হবে অবশ্যই কবিতার বক্তব্য ও অর্থের ওপর ভিত্তি করে। যেমন ৯ম পঙক্তিতে রয়েছে ৭ মাত্রার একটি মাত্র পর্ব; যার শেষে একটি ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করে অর্থের সাথে মাত্রা সাম্যতা রক্ষা করা হয়েছে। একইভাবে ১৫তম পঙক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে,‘শান্তি চায় নীল মহাসাগরের ভোরের আলোয়’।
অর্থাৎ পর্ববিন্যাস অর্থানুসারে = ৪ + ৮ + ৬ , কখনোই মহাপয়ারের রীতি অনুসারে ১০ + ৮ হিসাবে পাঠযোগ্য নয়। একইভাবে ১৯তম পঙক্তিতে রয়েছে ১২ + ২ এবং ২০তম পঙক্তিতে ১০ + ৪ সেসাথে ২১তম পঙ্ক্তিতে ৪ + ৭; অবশ্য এই ৭ মাত্রার সাথে একটি ড্যাশ যুক্ত হয়েছে। ২৩ তম পঙ্ক্তিতে দেখা যাচ্ছে, — ‘ডেকে পাইচারি করে একা। একা। একা।’
অর্থাৎ ১ম পর্বের মাত্রা ৯; যা কিনা ১০ মাত্রায় উচ্চারণ করা যেতে পারে। কিন্তু পরের দুটি পর্বের প্রতিটিই ২ মাত্রার মর্যাদা লাভ করেছে। একইভাবে ২৯ তম পঙ্ক্তির ১ম পর্বটি ৭ মাত্রার; ৩৪ তম পঙ্ক্তির ১ম পর্ব ৪ মাত্রার এবং ৩য় পর্ব ৭ মাত্রায় উচ্চারিত হয়েছে। ৩৫ তম পঙ্ক্তির মাত্রাবিন্যাস = ২ + ৪ + ৪ এবং ৩৭তম পঙ্ক্তির মাত্রাবিন্যাস = ৮ + ৭ + ৬; অর্থাৎ ৩৭তম পঙক্তিতে উচ্চারণের টোন ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখি হয়ে উঠেছে। কিন্তু ৩৮তম পঙ্ক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে ৬ + ৬ + ৪ + ৬ বিন্যাসের গতি বা লয় এবং ৪৪তম পঙ্ক্তির মাত্রাবিন্যাস = ৮ + ৬ + ৩; অর্থাৎ শেষে অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। যা কিনা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দেখা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে ছন্দের স্বাধীনতা গ্রহণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে কবিতার অর্থগত সৌন্দর্য রক্ষার প্রয়োজনে। একইভাবে পাওয়া যাচ্ছে ৪৯তম পঙ্ক্তিতে,‘যাত্রী মরে গেছে— নতুন যাত্রীর দল তারপর’।—অর্থাৎ পর্ববিন্যাস = ৭ + ১১। ৫৩তম পঙ্ক্তিতে পাওয়া যায়,‘মরে যেতে হবে— যাত্রী, তবু চলো’।
অর্থাৎ মাত্রাবিন্যাস = ৬ + ২ + ৪। ৫৭তম পঙ্ক্তির মাত্রাবিন্যাস = ১১ + ২ + ১০। ৫৮তম পঙ্ক্তির মাত্রাবিন্যাস = ৭ + ৯ + ৬। ৫৯তম পঙ্ক্তির মাত্রাবিন্যাস = ৯। ৬০তম পঙ্ক্তির মাত্রাবিন্যাস = ৮ + ৯। একইভাবে কোথাও পাওয়া যাবে ৭ + ৭ + ৯ অথবা কোথাও অপূর্ণ পর্ব অথবা কোথাও ৭ +১১ অথবা ৬ +১১ ইত্যাদি এবং কবিতার সর্বশেষ পঙ্ক্তি, ‘মৃত্যুশীল— মৃত্যুর নিঃশেষ নেই— নেই— যাত্রী চলেছে।’—অর্থাৎ মাত্রাবিন্যাস = ৪ + ৮ + ২ + ৫।
যেহেতু দীর্ঘকবিতায় নির্দিষ্ট একটি মাত্র মোটিভ থাকে না বরং দীর্ঘকবিতা অসংখ্য মোটিভ নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে সেহেতু মোটিভ অনুসারে ছন্দের গতি অগ্রসর হবে এটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় নির্দিষ্ট মেসেজ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে; কিন্তু মনে রাখতে হবে দীর্ঘকবিতায় নির্দিষ্ট একটি মাত্র মেসেজ নয় বরং একাধিক মেসেজ যৌথভাবে কবিতায় ক্রিয়াশীল থাকে।
শুধু ছন্দের ক্ষেত্রে নয় বরং সার্বিক অর্থে দীর্ঘকবিতায় কবিতার প্রচলিত নির্দিষ্ট ফর্মের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার প্রবণতা লক্ষ করা সম্ভব। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালের দীর্ঘকবিতায় বিষয়টি স্পষ্ট। এক্ষেত্রে দীর্ঘকবিতা একইসাথে একাধিক ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা ভোগ করতে চায় যদি তা বিষয় উপযোগি হয়ে ওঠে। কেননা ব্যবহারিক জীবনেও মানুষ মনের ভাব উপযুক্ত অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষার সাথে উর্দু-হিন্দি-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার শব্দ-শব্দাংশ, বাক্য-বাক্যাংশ ব্যবহার করে থাকে। শুধু ভাষা ব্যবহারেই নয় বরং ছন্দের ক্ষেত্রেও দীর্ঘকবিতায় একাধিক তাল-লয় ব্যবহার করতে দেখা যায়।
ভাবের ঐক্য গীতিকবিতার একটি সুসংহত লক্ষণ; যা মানতে দীর্ঘকবিতা বাধ্য নয়। দীর্ঘকবিতা একাধিক ভাববস্তুর সম্মিলনে জটিল মেটাফর ও মোটিভের সৃষ্টি করে। যা কিনা আপাতভাবে ভাবের ঐক্যতা রক্ষা না করলেও দীর্ঘকবিতা পাঠশেষে এক ধরনের অনুন্মেচিত ভাব ঐক্যের অনুরণন ধ্বনিত হয়। অর্থমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ঐক্যমাত্রার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যা সার্বিক কবিতার ভাবঐশ্বর্যের আলোকে প্রতিভাসিত হয়ে থাকে। এর কারণ দীর্ঘকবিতা যেহেতু খ- খ- বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্প তৈরি করে অগ্রসর হয় এবং চিত্রকল্পগুলোর যোগফলে যেহেতু তৈরি হয়ে থাকে বক্তব্য ও ইঙ্গিতধর্মী উপলব্ধিজাত নান্দনিক প্রজ্ঞা সেহেতু সার্বিক অর্থে কবিতার ভাব ঐশ্বর্য নির্দিষ্ট মোটিভে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়।
তবে মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে দীর্ঘকবিতা ছন্দের ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করলেও কাব্যগুণধর্মে, রসবিচারে, বক্তব্যধর্মে, চিত্রময়তা ও রূপকল্পে, জটিল মেটাফরের বন্ধনে এ জাতীয় কবিতা অবশ্যই উপযুক্ত ভাষা নির্মাণ করে থাকে; যা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসন তথা বিবিধ বিষয় বৈচিত্র্যের সংশ্লেষণে আবর্তিত; যা পাঠককে এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ ভ্রমণের আহ্বান জানায়।
শব্দের অপরিহার্য বিন্যাসে, সুর-লয়-তালে, দীর্ঘকবিতার একটি শরীরী অস্তিত্ব থাকলেও এই কবিতার তাৎপর্য বাহ্যিক নয় বরং তা উপলব্ধিজাত। ফলে লিরিকের মতো ছন্দের সুর-লয় ও শব্দবিন্যাসই দীর্ঘকবিতার একমাত্র অপরিহার্য শর্ত নয়। এমনকি অপরিহার্য শর্ত নয় কবির একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ। বরং আবেগ এক্ষেত্রে পরিশ্রুত; যা কোনোক্রমেই আর ব্যক্তিগত থাকে না। লিরিকের অন্যতম শর্ত, ছন্দের দোলা। দীর্ঘকবিতার ছন্দেও দোলা থাকতে পারে, তবে তা অপরিহার্য নয় বরং তা কবিতার মেজাজ অনুসারী। অর্থাৎ তা কবিতার ভাববক্তব্যকে অনুসরণ করে। ছন্দ রক্ষার্থে এক্ষেত্রে কবিতার ভেতর জোর করে শব্দ বা পদ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না; অথবা মাত্রা ছাটাই করার প্রয়োজন পড়ে না।
চিত্রকর রঙের বিন্যাসে তার ভাববক্তব্যকে অর্থময় করে তোলেন ক্যানভাসে। আর কবি রঙ নয় বরং শব্দবিন্যাসে যে কাজটি করে থাকেন তা চিত্রকরের চিত্র অপেক্ষাও অধিক শিল্প সৌন্দর্য ধারণে সক্ষম। কিন্তু সেই ধারণকৃত সৌন্দর্যকে আহরণ করতে হলে কবিতা রচনার মতো দীর্ঘকবিতা পাঠও এক মূর্ত সৃজনী অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ দীর্ঘকবিতার পাঠককেও কবির অন্তকরণ দিয়ে নন্দনরস আস্বাদনে প্রবেশ করতে হয় কাব্যজগতে। পাঠকের রুচি-মেধা-মনন ও প্রজ্ঞানুসারে কবিতা নিজ অর্থমাত্রাকে পাল্টে ফেলার এক স্বয়ম্ভূ ক্ষমতা রাখে। সুতরাং কবিতা স্বয়ং সৃষ্টিশীল। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কবিতার ব্যঞ্জনামাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি-সংশ্লেষ-বিশ্লেষ ঘটে। সুতরাং একখানি কবিতা লেখা হয়ে যাবার পর তার ওপর কবির আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কবিতা হয়ে ওঠে এক স্বয়ম্ভূ শিল্প।
এই স্বয়ম্ভূ শিল্প সম্পর্কে বেকন তাঁর ‘অ্যাডভান্সমেন্ট অব লার্নিং’ নিবন্ধে বলেছিলেন, গদ্য বা পদ্য যে কোনটাই কবিতার বাহন বা ভাষা হতে পারে। দীর্ঘকবিতা এই গদ্য বা পদ্য উভয় স্বাধীনতা ভোগে বিশ্বাসী। ওয়াড্র্সওয়ার্থ ‘প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাড্স’-এ গদ্য ও কবিতার ভাষার মধ্যে তেমন কোনো বিভাজনরেখা মানতে চাননি। তিনি ‘ডিকশন’ ও ‘মিটার’কে নিছক আলঙ্কারিক মাধুর্যের জন্যই প্রয়োজনীয় বলে মত দিয়েছেন; তবে তা অপরিহার্য নয়। বরং গদ্য ভাষায় কবিতার শক্তিশালী শরীর গঠন সম্ভব। কেননা কবিতা সম্পূর্ণরূপে ছন্দের ওপর নির্ভরশীল নয়। দীর্ঘকবিতা এই সম্ভবনাকে সাহসের সাথে যাঁচাই করে দেখতে উৎসাহী। সুতরাং দীর্ঘকবিতা হতে পারে সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন সংযোজন। যার রয়েছে অসম্ভব রকমের সম্ভবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ। যা শিল্পের একাধিক মাত্রাকে আত্মস্থ করে কবিতাকে লিরিকের সীমিত সীমা থেকে মুক্ত করতে পারবে বলে ভাবা সম্ভব।