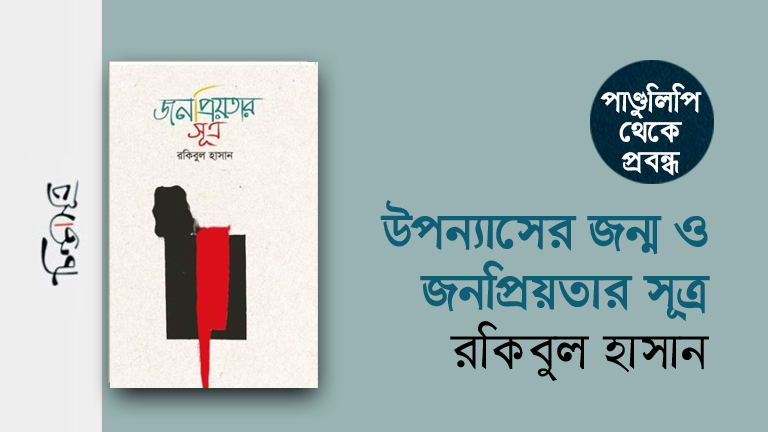আধুনিক পৃথিবীর মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার সাহিত্য-রূপ উপন্যাস।১ কিন্তু উপন্যাসের জন্মকাল নিয়ে নানামাত্রিক আলোচনা আছে। সেসব আলোচনাতে সঠিক সময়কাল নিয়ে মতবিরোধও আছে। উপন্যাসের জন্মের সঠিক সময়কাল নির্ণয়ে এখনো মতবিরোধ নিষ্পন্ন হয়নি। উপন্যাসের সঠিক অবকাঠামো তৈরির আগে অনেককাল ধরেই উপন্যাসের-স্টাইলে কিছু রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো উপন্যাস না হলেও উপন্যাসের ইঙ্গিত বহন করে। ইতালির বোকাচ্চিওর দেকামেরন, ইংল্যান্ডের চসারের ক্যান্টারবারি টেলস্, ফ্রান্সের রাবল্যের গারগানতুয়া ও প্যাঁতাগ্রুয়েল এবং স্পেনের মিগুয়েল দ্য সেরভান্তেস’র ডন কিকসট্ দ্য লা মাঞ্চা-এই পাঁচটি গ্রন্থ সেই নিদর্শন বহন করে। এ পাঁচটি গ্রন্থের কোনোটিই যথার্থ উপন্যাস নয়। কিন্তু উপন্যাসের ইঙ্গিত গ্রন্থগুলোতে লক্ষণীয়। উপন্যাসের বীজবপন মূলত এ গ্রন্থগুলোতে নিহিত। আর এ গ্রন্থগুলোর চারজন লেখকই ছিলেন ইউরোপের প্রথম আধুনিক শিল্পী। এসব লেখক তাঁদের গ্রন্থে ‘মধ্যযুগীয় রোমান্সের অবিশ্বাস্য কল্পলোকের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় শৌর্যবীর্য ও অবাস্তব জীবনকে তীক্ষè ব্যঙ্গের শরাঘাতে ও যুক্তির নির্মম খোঁচায় বাস্তবভূমিতে ধরাশায়ী করা হয়েছে। ইউরোপের মানুষের সামনে এঁরা এক নতুন পৃথিবীর ছবি তুলে ধরলেন।’২ উপন্যাসের ইঙ্গিত দিয়ে যে-সব গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে, সে-সবের উপর দাঁড়িয়ে উপন্যাস সৃষ্টির পথ এগিয়ে গেছে আরো খানিকটা পথ। আর তা অবকাঠামোগতভাবে যেমন, তেমনি বিষয়বস্তুতেও। বিশেষ করে উপন্যাসের প্রাথমিক সূচনা লক্ষ্য করা যায় ষোলো, সতের ও আঠার শতকে। এটি ঘটে স্পেন ও ফ্রান্সে। বিষয়বস্তুতে যুক্ত হয় বিজ্ঞান-কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চার-উপাখ্যান, রম্য ও প্রেম। এসবের ভেতর গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায় বাস্তবচেতনা, মানবসম্পর্ক ও সংসারমুখিতা। যেখানে ঘোষিত হয়েছে বুদ্ধির মুক্তি ও যুক্তির জয়। আর এর মূলমন্ত্রক ছিলেন ‘ফ্রান্সে মিশেল দ্য মঁতেন, ভোলত্যের, রুশো, দিদেরো এবং স্পেনে লেসেজ। এঁদের রচনায় মানুষের আত্মবিশ্বাসের কথা প্রথম উচ্চারিত হয়। বিজ্ঞানকে মানুষের জীবনকে উন্নত করতে এবং রহস্যময় অধ্যাত্ম স্বর্গের পরিবর্তে স্পষ্টরূপে ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেতনাবোধ তৈরি করে। এর মাধ্যমেই ইউরোপের মানুষের জীবনে ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’;এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ইউরোপের জীবনের দিগন্ত আরো প্রসারিত হয়। বিশেষ করে শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং এশিয়া-আমেরিকার জলপথের সন্ধান এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। আর উপন্যাসের জন্ম ঘটে মূলত তখনই।
আঠারো শতকে শিল্পবিপ্লব ঘটে, আবিষ্কার হয় মুদ্রণযন্ত্রের। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে উদ্ভব ঘটে সাময়িক পত্রিকার এবং এটি দ্রুত প্রসারতা লাভ করে। এতে করে উপন্যাসের ব্যাপারটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসে বিষয়বস্তুর যেমন দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তেমনি ঘটতে থাকে উপন্যাসের কাঠামোগত পরিবর্তন। এই ধারাতে জন্ম ঘটে বানিয়ানের পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস (১৬৭৮), ডানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশো (১৭২৭), জনাথান সুইফটের গালিভারস্ ট্রাভেলস (১৬২৭)। এ উপন্যাসত্রয়ে নতুন বিষয় হিসেবে যুক্ত হয় বাস্তব জীবনের গল্প; উপন্যাসের ভিত্তি তৈরিতে যা অবিশ্বাস্য এক ভূমিকা রাখে। উপন্যাসের পথ উন্মুক্ত হয় মূলত এখান থেকেই। বিশেষত এই তিনটি গ্রন্থের মাধ্যমে। এ ধারাতেই আবির্ভূত হন রিচার্ডসন, ফিলডিং, স্মোলেট ও স্টার্ন। রিচার্ডসনের পামেলা (১৭৪০), ক্লারিসা হার্লো ও স্যার চার্লস গ্রান্ডিসন, হেনরি ফিলডিং’র জোসেফ অ্যান্ড্রুজ (১৭৪২), ও টম জোন্স (১৭৪৯), এস্মালেটের রোডরিক র্যান্ডম (১৭৪৮), পেরিগ্রিন পিকল (১৭৫১) ও হামফ্রি ক্লিঙ্কার (১৭৭১) এবং স্টার্নের ট্রিস্ট্রাম স্যান্ডি (১৭৬০-৬৭) ও আ সেন্টিমেন্টাল জার্নি (১৭৭৩);ইংরেজি সাহিত্যে এগুলো ছিল প্রাথমিক উপন্যাস। এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল ত্রিশ বছর সময়কালের মধ্যে। ইংরেজি উপন্যাসের বুনিয়াদী ভিত্তি মূলত রচিত হয় এঁদের হাতেই। ইংরেজি উপন্যাস-সাহিত্যের স্থপতি হিসেবেও এঁদেরকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এঁদের হাতের ইংরেজি উপন্যাসের মজবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর উনিশ শতকে ইংরেজি উপন্যাসের বিকাশের দুর্দান্ত এক সময়কাল। উনিশ শতক হয়ে ওঠে উপন্যাসের শতক। গোটা পৃথিবী জুড়েই উপন্যাসের বিশাল রাজত্ব গড়ে ওঠে। উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক ‘স্বর্ণশতক’ হিসেবে অভিহিত হতে পারে। উনিশ শতকে উপন্যাসের যে বিকাশ ঘটেছিল এবং যেসব মহাশক্তিশালী ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অন্য আর কোনো শতকে তা আর সম্ভব হয়নি। এসব বিখ্যাত ঔপন্যাসিক উপন্যাস-সাহিত্যকে সেসময় এতো সমৃদ্ধ করে গেছেন, পরবর্তীতে তাঁদের এ ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা-বিকাশের ধারাতেই উপন্যাস পথ হেঁটেছে। যা আজো এক অপার বিস্ময় হয়ে আছে। ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডে উনিশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীখ্যাত বিভিন্ন ঔপন্যাসিক। ফ্রান্সের সেসময়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্তাঁধাল, বালজাক, আলেকজান্ডার ডুমা, জর্জ সাঁ, ভিক্টর হুগো, গুস্তাব ফ্লোবের, এমিল জোলা, আলফাঁস দোদে বিশেষভাবে উলে¬খযোগ্য। ইতালিতে আবির্ভূত হন জিওভান্নি ভের্গা। স্পেনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোসমারিয়া দ্যা পেরেডা, হুয়ান ভালেরা, বেনিতো পেরেজ গালদোস। রাশিয়ার নিকোলাই গোগোল, ইভান তুর্গেনেভ্, লিও টলস্টয়, দস্তভয়েস্কি, আন্তন চেখভ। ইংল্যান্ডের জেন অস্টেন, ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, জর্জ মেরিডিথ, টমার্স হার্ডি, ব্রন্টে ভগিনীত্রয় এবং আমেরিকার নাথানিয়েল হথর্ন ও হানমেন মেলভিল। এসব বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির ওপর নির্ভর করে বিশ শতকে উপন্যাস জনপ্রিয় সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ শতকের উপন্যাসের বিশেষ দিক ছিল লেখকের আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটি। সেসময়ে বিখ্যাত সব লেখকেরা উপন্যাসকে তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন। জীবননিষ্ঠা, জীবনজিজ্ঞাসা, সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবতার ভিত্তির ওপর উপন্যাসের নতুনমাত্রা জন্মলাভ করে। পাঠকের কাছেও যা নতুন আস্বাদনে পরিণত হয়। সেই কারণে পাঠকের আগ্রহমাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের জনপ্রিয়তার প্রথম দিকটি এ পর্যায়েই চিহ্নিত হয়।
বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই। দীর্ঘদিন বাংলা উপন্যাসে পাশ্চাত্য সাহিত্য বেশ শক্তভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে ইংরেজি উপন্যাসের অনুকরণে বাংলা উপন্যাসের সফল যাত্রা ঘটে। সময়কাল হিসেবে আঠারো শতকের ইংরেজি উপন্যাসকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি। একথা স্বীকার্য যে, বাঙালির নিজস্ব সম্পদ লোকসাহিত্য, রূপকথা, উপকথা, কিস্সা-গল্প, বীরত্ব-কাহিনি নির্ভর হয়ে সেসময় উপন্যাস নির্মিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশশাসনের একটি পর্যায়ে নগরজীবনের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটতে থাকে। ভারতবর্ষ তথা বাঙালি সমাজবাস্তবতায় পুঁজির প্রতিক্রিয়ায় নাগরিক উপকরণের সূত্রপাত ঘটতে থাকে বৃটিশশাসনের গোড়া থেকেই নানাভাবে। মুসলমানদের যে বাস্তবতা তৈরি হয় তা অনেকাংশে উপেক্ষিত ও অবহেলিত জীবনপ্রয়াস। সমাজ-অর্থনীতি বা অনাদৃত পরিবেশে কোনোভাবেই আধুনিকতার সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা সম্পন্ন হয়নি। পুঁজির প্রবাহের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ঘটেনি। বিপরীতে হিন্দু মধ্যবিত্ত ইংরেজ সহযোগিতা বা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়সমূহ সহজাত বাস্তবতায় গ্রহণ করে। ফলে এ সম্প্রদায়ের ভেতরে যোগ্য ব্যক্তি তথা দক্ষ নেতৃত্ব তৈরি হয়। নবজাগরণের প্রবাদপুরুষ হিসেবেই তারা পরিগণিত হতে থাকেন। তাছাড়া মেধা ও যোগ্যতার কমতি ছিল না এসকল মনীষীদের। ভারতবর্ষ তথা বাংলার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পথিকৃৎরূপে তারা পরিগণিত হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ সকল মনীষীর হাতেই সমাজ সংস্কার, নগরভিত্তি বা রূপায়ণ পুনর্গঠিত হওয়ার ঘটনা শুরু হতে থাকে। তবে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে পুরোপুরি মুসলমানরা সংশ্লি¬ষ্ট হতে পারেনি। ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’র (১৭৯৩) ফলে বঙ্গদেশের ভূমিব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সংখ্যার হিসেবে বাঙালি মুসলমান জমিদার বাঙালি হিন্দু জমিদারের চেয়ে কখনই বেশি ছিল না। ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই সংখ্যা আরো হ্রাস পায়। কারণ, এই নতুন ব্যবস্থায় সাধারণভাবে পূর্বতন জমিদারেরাই জমিদারি হারিয়েছিলেন। কিন্তু পুরনো হিন্দু জমিদারের বদলে যেভাবে নতুন হিন্দু জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, বাঙালি মুসমানদের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। কেননা, ভূমিতে বিনিময়যোগ্য অর্থের সংস্থান তাদের ছিল না। ফলত তাদের মধ্যে এভাবেই সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির সংখ্যা কমে যেতে থাকে । যার জন্য পুরো ব্যাপারটাই এরকম দাঁড়ায় যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নতির অর্থই হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের অধোগতি।’৩ ফলশ্রুতিতে মুলমান নেতৃত্ব তৈরি হয়নি। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সচেতনতাও গড়ে ওঠেনি। একারণে, সাংস্কতিকভাবে তারা থেকে যায় নিরাবলম্ব। যাবতীয় বিষয়-ব্যবস্থাপনায় ধরা পড়ে অসংলগ্নতা। আধুনিকতা অর্জনের পথে মুসলমানদের ঘটে অমোচনীয় বিপর্যয়। ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির পাদপীঠে তাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের অসহায়ত্বই প্রতিপন্ন হয় । ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাকে ঘিরে যে সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশ বিরাজমান ছিল সেখানে মুসলমানরা প্রকৃতার্থে বিচ্ছিন্নই থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকদের নানামাফিক মন্তব্য থাকলেও প্রকৃত সত্য এই যে, বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও প্রসারের সামূহিক বাস্তবতায় মুসলমানদের কোনো কৃতি পরিলক্ষিত হয় না। গদ্যের নির্মিত ও অর্জিত আধুনিকতার সঙ্গে মুসলমানরা জড়িত থাকতে পারেননি বলা চলে। সেক্ষেত্রে তারা তৈরিও ছিলেন না। এছাড়া ধর্মীয় শাস্ত্রাচারে বা সংস্কার বিশ্বাস তাদের এতই বদ্ধমূল করে রেখেছিল যে, সেখানে আধুনিকতার বিবিধ উপাদানসমূহকে গ্রাহ্য করতে তারা কিছুতেই সক্ষম ছিলো না। বস্তুত ধর্মের রীতি-নীতি আর আধুনিকতার সঙ্গে তাদের বিরোধ ও বাধা দুটোই ছিল। ফলে আধুনিকতা অর্জনের পথে তারা কিছুতেই এগোতে পারেনি। গদ্য উৎপত্তির এ পর্বে যখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) মতো লেখকরা সামাজিক নকশাধর্মী রচনাসমূহে মনোনিবেশ করেছেন এবং কথাসাহিত্যের বাস্তবতা উন্মোচিত হচ্ছে বা পথ তৈরি হচ্ছে তখন মুসলমানরা এসব থেকে দূরে স্থিত আছেন। তারা মূল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত। ধর্মোন্মাদ বা প্রতিক্রিয়াশীলতার বেশে খোলাফায়ে রাশেদিনের রাজ্যকে পুনরাবর্তন বা ফিরে যাওয়ার জেহাদে শামিল হতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ পর্যায়ে বেশ কিছু কারণ চিন্তাবিদদের দর্পণে উঠে আসে। যেমন, মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, প্রত্যন্ত গ্রামে স্থিতি, নাগরিক সংস্পর্শ না থাকা, কুসংস্কার আর শাস্ত্রীয় ধর্মের মধ্যে নিজেদের রক্ষণশীল মনের আশ্রয়, আধুনিকতার সঙ্গে ধর্মের বিরোধ, ইংরেজি শিক্ষার অবহেলা ইত্যাদি। ফলে গদ্যরচনার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য উপাদান আবিষ্কারে তারা অনুপস্থিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। গদ্যের অস্তিত্বের ভেতরে যে নগরায়ণ ভাবনা, আধুনিকতার উন্মেষ, প্রগতিচেতনার উত্থান, ব্যক্তিচরিত্রের উন্মোচন, প্রতিরোধী ও সাহসী চরিত্র সৃষ্টি, সংস্কার বা দ্বিধাকে অস্বীকার করে প্রকৃত সত্যের প্রকাশ তৎপরতা সবকিছুই এগিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু সেটি মুষ্ঠিমেয় শিক্ষিত হিন্দুর ভেতরে চললেও তা জনপ্রিয়তার দৃষ্টিতে সম্মুখগামী হতে পারেনি। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কিছু স্কেচধর্মী নাটক যেমন রচিত হয়, তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনুবাদ হয় এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পুননির্মাণও চলতে থাকে। এ পুনর্পাঠে সাহিত্যে উন্মোচিত হতে থাকে নতুন জীবন-বীক্ষা। সেখানে সমাজ সংস্কার বা শাস্ত্রীয় ধর্মাচার বিপুলভাবে ভাঙনের মুখে পড়ে। যুক্ত হয় জীবনের আলোকিত ও উন্মত্ত সত্যসমূহ। এ পরিপ্রেক্ষিতেই সামাজিক নকশার ভেতর থেকে শিল্পপ্রয়াসের বার্তা উন্মোচিত হতে থাকে ।
হ্যানা ক্যাথেরিন ম্যুলেন্স’র ফুলমনি ও করুণার বিবরণ রচনা করলেও সেটি উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের খ্যাতি অর্জন করলেও সার্থক উপন্যাস হিসেবে মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। বাংলা উপন্যাসের সফল যাত্রা শুরু হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) হাতে। তিনি বাঙালির নিজস্বতাকে পাশ কাটিয়ে ইতিহাস ও রোমান্সনির্ভর উপন্যাস রচনা করেন। বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসে এই বিষয় স্পষ্ট। এক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, ও মৃণালিনী উলে¬¬খযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন, সেখানেও রোমান্সনির্ভরতা স্পষ্ট। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী ও ইন্দিরা সামাজিক উপন্যাস হলেও রোমান্সপ্রধান উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বাংলা উপন্যাসের আদর্শ-ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও শিল্পিত রূপটি প্রথম খুঁজে পান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর হাতেই বাংলা উপন্যাস মুক্তি পায়। সমাজ-রাজনীতি-আর্থনীতি-বাস্তবতা সবকিছু অবারিতভাবে উপন্যাসে উঠে এল। উপন্যাসের যে কাহিনিগদ্য সেটি বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম উপন্যাসে প্রযুক্ত করলেন। বাংলা উপন্যাসের এই সফলস্রষ্টা সফল হয়েছিলেন দুটো কারণে। এক. সমাজ ভাঙনকে উপন্যাসে স্পষ্ট করে, দুই. ‘ব্যক্তি’ মানুষকে জীবন সম্ভাব্য প্রকরণে তুলে এনে। এখনও যেহেতু বাংলা উপন্যাস অদ্যাবধি এমন শর্তকে অঙ্গীভূত করেই এগিয়ে চলেছে। সমালোচকরা কথাসাহিত্যের আলোচনায় এমন শর্তকেই প্রমাণিত জ্ঞান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাব আছে । বিশেষত ওয়াল্টার স্কটের কথা আমরা সবাই জানি। প্রধানত বঙ্কিমকে ‘বাংলার স্কট’ বলার যে আখ্যা সেটি এ কারণেই এসেছে। তবে উপন্যাসের পাশ্চাত্যরীতি বঙ্কিম যতোই গ্রহণ করুন না কেন দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রবণতা তিনি অস্বীকার করেননি। আর তা করলে বঙ্কিম উপন্যাস এতো জনপ্রিয় হতো না । হয়তো শিল্পসিদ্ধিও পেত না। বঙ্কিম সমসাময়িক অনেকেই উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু কেউই তেমন জনপ্রিয় হননি অথচ বঙ্কিমের জনপ্রিয়তা উত্তুঙ্গস্পর্শী। ‘বঙ্কিম উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে সেকালের সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা-জটিলতা।’৪ নানা রকমের উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঐতিহাসিক-সামাজিক-পারিবারিক-রাজনৈতিক উপন্যাস। এসব উপন্যাসে নতুন আত্মপ্রত্যয় ধ্বনিত হয়। জীবনের রোমাঞ্চ ও রোমান্টিকতা সম্পর্কে দেয়া হয় নতুন প্ররোচনা। এসব উপন্যাসে বঙ্কিম জীবন সমাজ ও সামগ্রিক বিশ্বাসকে সত্যে পরিণত করেন। তবে এটা সত্য যে, বঙ্কিমের উপন্যাসের জীবনরূপায়ণ সে সময়ে খুব সহজ কাজ ছিল না। কারণ সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্নতা, কুসংস্কার, ও শাস্ত্রীয় রীতি;তাঁর সময়ে ছিল উন্মুখ। এগুলো শিল্পরচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই ছিল দ্বিধা এবং বাধার দ্যোতক। যে দ্বিধাগ্রস্ত সময়ে তিনি উপন্যাস লিখতে উদ্যত হন তখন তাঁর জীবনও ছিল সংশয়পূর্ণ। কিন্তু অদম্য শিল্পক্ষুধা তাঁকে প্রণোদনা যোগায়। বিশেষত পাশ্চাত্য উপন্যাসগুলো তাঁকে নানাভাবে উদ্দীপিত করে। বঙ্কিমের প্রায় সব উপন্যাসেই ইতিহাসের আঁচড় আছে । ইতিহাসের প্রতি যতোটা অনুরাগবশত তার চেয়ে বেশি ছিল নিজের উপন্যাস লেখার জন্য তীব্র উৎসাহ। ইতিহাসকে পটভূমি হিসেবে রেখে তিনি কাহিনিগদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর রচিত প্রায় সব উপন্যাসে ইতিহাস আছে এবং এর ভেতর দিয়ে তিনি পৌঁছতে চেয়েছেন।
আবেগভক্তির নির্বিচার তোষণপরিচর্যা অস্বীকার করে জীবনের উল্লাসকে ধারণ করত। এতে করে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবীক্ষার ক্ষেত্র সার্থক ও বিস্তৃত হয়। উপন্যাসে উঠে আসে জগৎসিংহ, প্রতাপ কিংবা গোবিন্দলালের মতো এক একটি বিরাট চরিত্র। একইরূপে রোহিণী, কুন্দনন্দিনী, আয়েশা অপরূপ উল্লাসিত জীবনের পরিবাহী। এসব চরিত্রের রূপায়ণ ও জীবনগাঁথা পাঠকদের কাছে দুঃখ-সুখের প্রস্রবণ খুলে দেয়। ভেতরের আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বনিষ্ঠা পাঠকদের কাছে বিস্ময়ের অবাদক্ষেত্রও প্রস্তুত করে। পাত্র-পাত্রীরা সমাজশৃঙ্খলের বন্ধন ভেঙে জীবনকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেখেছিল। প্রচলিত সমাজ-সংস্কারকে অস্বীকার করেছিল। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রটি এ জায়গাতেই চিহ্নিত। আর ইতিহাস অবলম্বী হওয়ার কারণে সেটি আরও বিস্তার লাভ করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন:
ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকরা ইতিহাসের যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, দৈনিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধে যেভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, বঙ্কিম তাহা পারেন নাই। তবে বঙ্কিমের সপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপীয় আদর্শ অনুকরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, এবং স্বাভাবিক বাধা সত্ত্বেও তিনি যতটা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভারই পরিচয়। স্থানে স্থানে তিনি কেবল প্রতিভাবলেই কোন অতীত যুগের ঠিক প্রাণস্পন্দনটি ধরিয়াছেন, বা কোন ইতিহাস-বিখ্যাত পুরুষের আসল ব্যক্তিত্বটুকু ফুটায়া তুলিতে পারিয়াছেন, ইহা প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও অনুভব করা যায়। ‘চন্দ্রশেখর’-এ জনসন্ ও গলস্টন্ প্রতাপের গৃহদ্বারের রুদ্ধ কপাটে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই পদাঘাতই ভারতে প্রথম যুগের ইংরেজদের বলদৃপ্ত, মদগর্বিত আত্মাভিমানের যেন মূর্ত বিকাশ;এই এক পদাঘাতই শত শত লিখিত প্রমাণ অপেক্ষা সুস্পষ্টতরভাবে তাহাদের প্রকৃতির আসল রহস্যটি আমাদের নিকট প্রকাশ করে। ‘মৃণালিনী’তে মুসলমান বিপ্লবের পর বক্তিয়ার খিলিজির সম্মুখে প্রভুদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক পশুপতির যে বিবেকভীরু, কর্তব্যবিমূঢ়, অর্ধ-অনুশোচনা-অর্ধ-আত্মপ্রসাদমিশ্রিত ভাব তাহা ঠিক ঐতিহাসিক সত্য না হউক, উচ্চঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনার পরিচয় দেয়। ‘রাজসিংহ’-এ আরংজেবের যে কুটিল, ভাব গোপনদক্ষ, হাসির আবরণের মধ্যে বজ্রকঠিন প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তা আধুনিক ঐতিহাসিকও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রমাণনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারের দ্বারা ইতিহাসের একেবারে মর্মস্থানে গিয়া হাত দিয়াছেন, সমস্ত জটিল ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে যুগবিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের আসল স্বরূপ টানিয়া বাহির করিয়াছেন।৫
এরূপে বঙ্কিম-উপন্যাসের সামগ্রিক রূপটি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু উপন্যাসেই নয় বাংলা গদ্যকে সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভাগুণে পণ্ডিতি ও আলালি-হুতোমি রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে সরল ও সরস গদ্যের উদ্ভাবন করেন। ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২) নামক সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেন। সাহিত্য-সমালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা, ধর্ম ও দার্শনিক আলোচনা, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, ব্যঙ্গ-সাহিত্য;এর সবই তিনি প্রবর্তন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবলে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তাঁরাই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ বাংলা সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বাংলায় তুলনামূলক সাহিত্যসমালোচনারও তিনি পথিকৃৎ। তবে তাঁর প্রধান পরিচয় ঔপন্যাসিক হিসেবে এবং তিনি বাংলা সাহিত্যে ‘সাহিত্য সম্রাট’ হিসেবে পরিচিতি। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ প্রভৃতি। মূলত তিনিই আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি ব্যাপকভাবে পাঠকনন্দিত লেখক ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস সমৃদ্ধ হলেও তাতে রোমাঞ্চ সংযোগ করে বাঙালি পাঠকদের গভীরভাবে দীর্ঘকাল মুগ্ধতার সঙ্গে ধরে রাখতে সক্ষম হন।
প্রসঙ্গত বঙ্কিম সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৯৯১), দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) প্রমুখ উপন্যাস লিখলেও তা তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনি। যদিও প্রায় একই রীতিতে ইতিহাসের ধারায় তাঁরা উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু জীবন-বীক্ষার তারতম্যে তাঁরা উপন্যাসে তেমন তাৎপর্যবহ মাত্রা দিতে পারেননি।
বঙ্কিমের পরে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রপর্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবানুভূতি ও শিল্পচেতনা বিবর্তনধর্মী। সৃজনশীলতা, নব নব ভাবকল্পনা ও রূপচেতনার দ্বারা তিনি একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস রাজর্ষি ও বউঠাকুরানীর হাট বঙ্কিম-প্রভাব বেষ্টিত। বাংলা উপন্যাসে শক্তিশালী নতুন বাঁক নেয় রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি উপন্যাসের মাধ্যমে। তাঁর গোরা (১৯৯০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), নৌকাডুবি (১৯০৬) প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের বহুবিস্তৃত পথ খুলে দেয়। বিষয় হিসেবে যুক্ত করে বহুবিচিত্রতা। রাজনীতি, দার্শনিকতা, মুক্তি, সর্বজনীনতা, ভ্রাতৃত্ব, বর্ণ, শ্রেণিবৈষম্য, ঐতিহ্য, আধুনিকতা, নগর আভিজাত্য, গ্রামীণজীবন, ঔপনিবেশিকতা, জাতীয়তাবাদ, বঙ্গভঙ্গ, জাতিপ্রেম, সমাজ ও প্রথাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক, জটিল পারিবারিক সমস্যা; বহু বিষয়নির্ভরতা লাভ করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। যা বাংলা সাহিত্যের জন্য স্বর্ণখচিত অভিনব ঘটনা ছিল। বাংলা উপন্যাসের নতুন আর একদিক উন্মোচন হয় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।
এই সময়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা উপন্যাসে আর এক রাজপুত্র হয়ে ওঠেন। বাংলা উপন্যাসকে তিনি নিয়ে গেলেন আরো অনেক দূর। একেবারে সাধারণ পাঠকের দোরগোড়ায়। বিষয়বস্তুতে যোগ করেন নতুনত্ব। সাধারণ মানুষের স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা-আতিশয্য তাঁর উপন্যাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দেশপ্রেম দায়িত্বশীলতায় অসামান্য সৃষ্টিশীলতায় তাঁর উপন্যাস আর এক অভিনব নতুন বাঁক তৈরি করে। তাঁর দেবদাস (১৯১৮), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০), পথের দাবী (১৯২৬) অসাধারণ সৃষ্টি। এসব উপন্যাস বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে নতুনমাত্রা এনে দেয়। তাঁর সামাজিক উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সে যুগের মতো এ যুগেও এমনভাবে বহমান যে, ভারতীয় প্রায় সব ভাষায় সেগুলো অনূদিত, এমনকি চলচ্চিত্র ও মঞ্চনাটকেও রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর রচনায় বাঙালির নিত্যদিনের সুখদুঃখময় জীবনযাত্রা, বাংলার পল্লিসমাজ এবং সর্বোপরি বাংলার নারীচরিত্র অপরূপ মাধুর্যে ফুটে উঠেছে। সমাজের অন্যায়, অবিচার ও দুর্বলতা তিনি তীক্ষ্ন ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ভাষায় আবেগ সঞ্চারে এবং বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে শরৎচন্দ্রের অসামান্য অবদান রয়েছে। সামাজিক সংস্কার ও নীতিবোধের প্রশ্নকেই তিনি তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) রত্নদীপ, রমাসুন্দরী, জীবনের মূল্য, সিন্দুর কৌটাসহ মোট ১৪টি উপন্যাস লিখলেও তাঁর আসল পরিচয় পাওয়া যায় মূলত ১০৮টি ছোটগল্পে। তাঁর ছোটগল্পের আঙ্গিকনৈপুণ্য উল্লেখ করার মতো। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। তাঁর উপন্যাস পথের পাঁচালী, অপরাজিত, চাঁদের পাহাড়, আরণ্যক, ইছামতী, মৌরীফুল, অশনি সংকেতসহ প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাস ব্যাপক পাঠকনন্দিত ছিল। উপন্যাস-সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও শিল্পসুষমায় নতুন এক ধারা তিনি তৈরি করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও অশনি সংকেত অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরি করে বিশ্বখ্যাতি ও বহু পুরস্কার-সম্মাননা লাভ করেন। বিভূতিভূষণ প্রায় ২০টি গল্পগ্রন্থ, কয়েকটি কিশোরপাঠ্য উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি রচনা করেছেন। পল্লিপ্রধান বাংলার গার্হস্থ্য জীবন ও পল্লিপ্রকৃতির অপূর্ব কাব্যিক বর্ণনা তাঁর রচনার বিশেষত্ব। প্রকৃতির শান্তস্নিগ্ধ ও মমতাভরা রূপ বর্ণনার মাধ্যমে মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ তাঁর রচনায় প্রধান হয়ে ওঠে।
জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) কবি হিসেবে খ্যাতিমান। সেকারণে বর্তমান সময়ে তাঁর উপন্যাস নিয়েও পাঠকের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মূলত এটা তাঁর কবিখ্যাতির কারণেই। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) কবি হিসেবে বিশিষ্টতা অর্জন করলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেও শক্তিমত্তার পরিচয় রেখেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের যাপিতজীবন নিয়ে লেখা তাঁর তিথিডোর পাঠকপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তৎকালীন উপন্যাস-সাহিত্যে শক্তিধর প্রতিভা। বাংলার পল্লী অঞ্চলের সহজ-সরল কৃষক, মাঝি ও গায়েনের প্রাণের মূল্য তিনি অপরিসীম দরদের সঙ্গে উপলব্ধি করেন। রাঢ়ের রুক্ষভূমির স্পর্শ, শ্রমজীবী মানুষের কাহিনি বর্ণনা এবং সুতীব্র আত্মানুসন্ধান তাঁর উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পোৎকর্ষ দিয়েছে। তাঁর গণদেবতা (১৯৪২) ও পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪) উপন্যাস দুটিতে পল্লিজীবনের বৈচিত্র্যমণ্ডিত কাহিনি মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই বৈচিত্র্য, বিশালতা এবং সামগ্রিকতায় এ দুটিকে বলা হয় পল্লিজীবনের মহাকাব্য। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুও পল্লিপ্রধান।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মানবজীবনকে দেখার রীতি একান্ত নিজস্ব। মনোনিবেশের মাধ্যমে মানবজীবন ও মানবপ্রকৃতির গোপন রহস্য আবিষ্কার তাঁর রচনার আদর্শ। পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) ও পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা। এতে তাঁর মানসবৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর উত্তরজীবনের রচনায় মার্কসবাদী মতাদর্শ এবং দলীয় মতের তীব্র সমর্থন দেখা যায়।
এ যুগে শক্তিমান আরও অনেক কথাসাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের অবদান অসামান্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬Ñ১৯৫৭)। একেবারে ভিন্ন ধরনের বিষয়কে উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করে তাঁর সময়কালে অনেকটাই নিন্দিত হলেও কালের যাত্রায় পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে তাঁকে সত্যিকারের জীবনঘনিষ্ঠ ও অধুনিক কথাসাহিত্যিক হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯৩৫) উপন্যাস-সাহিত্যে নতুনমাত্রা তৈরি করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের সৃষ্টিকর্মে বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে উপস্থাপন শৈলীতে নিজস্ব স্টাইল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। যে কারণে পাঠকের কাছে তাদের উপন্যাস বিশেষ মর্যাদায় স্থান করে নিতে পেরেছে। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল।
এখনকার বাস্তবতা অনেক জটিলতর; পুঁজির প্রকোপ আর পণ্যের দাপট আজ নানামুখী, মানুষ আজ বিবিধ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। তথ্যপ্রবাহ বা যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রচণ্ডতা তৃতীয় বিশ্বের হতদরিদ্র দেশগুলোকে অনেকরকম সমস্যায় ফেলেছে। বিশেষত একদিকে সমাজ বিভক্তি যেমন বৈষম্য বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে মানুষকে ভোগ আর অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ, নিয়মহীন পুঁজির অবাধ প্রবেশ। এ পরিস্থিতিতে শিল্প হিসেবে উপন্যাস কী করতে পারে কিংবা তার দায় কী! তাছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপন্যাস একটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। প্রথমেই যে শর্তের কথা উল্লেখ করেছি উপন্যাসের জন্য সেটা আজকাল মোটামুটি সব উপন্যাসেই সাধারণ বিষয়। কেননা আমরা যে সময়ের মুখোমুখি, একজন লেখক সে সময়ে অনিবার্যভাবেই এমন প্রস্তাবনার মধ্যে বসবাস করেছেন। সেজন্য সময়ের জটিলতাই শিল্পীকে এরূপ প্রকরণকে বেছে নিতে উদ্যোগী করে তুলেছে। তবে এটাও সত্য যে, এর ভেতরেই জীবনের বীক্ষা নানাজনের কাছে নানাভাবে নিরীক্ষিত হচ্ছে, উঠেও আসছে। যা সত্য ও বিবর্তনের নিরিখে দিকচিহ্নধারী তা নিশ্চয়ই আস্বাদনযোগ্য। কালের বিচারেও নিশ্চয়ই তা প্রতিষ্ঠা পাবার যোগ্য। আর উপন্যাসে জনপ্রিয়তার শর্তসমূহও তার মধেই নিহিত। কারণ, কাহিনিগদ্যে যে রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার ও অপরিমেয় জীবনবোধের সন্ধান থাকে তা অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে নিয়ে আসা দুরূহ। উপন্যাস সে শর্তপূরণে সক্ষম বলেই তার জন্ম এবং সিদ্ধি অবাধ ও জনপ্রিয়। এভাবেই বাংলা উপন্যাস জীবন-সমাজ-রাজনীতি-আর্থসামাজিকসহ বহুমাত্রিক বিষয়-আশয় ধারণ করে বিকাশের ধারায় এগিয়েছে। এ ধারায় অবদান রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঔপন্যাসিক। এ প্রবন্ধে মূলত পূর্ববাংলার মুসলিম ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার সূত্র নির্ণয়ের প্রয়াস থাকবে।
উপন্যাস বাস্তব জীবনের চিরায়ত উচ্চতর-শিল্প। তার সাথে জনপ্রিয়তা যুক্ত। বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির লগ্ন থেকেই জনপ্রিয়। যে আখ্যানের জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকতো, তা হলো ভঙ্গুর সমাজে নারীর জীবনাকাঙ্ক্ষা আর সমাজ প্রতিরোধে বেড়ে ওঠা ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। সেখানে খুব দ্রুত এগিয়ে যান বিষাদ-সিন্ধুর লেখক মীর মশাররফ হোসেন। পরে তা আরও বিকশিত হয়। যে মুসলিম লেখকগণ সমাজ-ধর্মে রক্ষণশীল ছিলেন তারাও উপন্যাসে পরিবার, সমাজ, জীবন নিয়ে প্রভূত চরিত্র সৃজন করেন।
আধুনিক পৃথিবীর মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার সাহিত্য-রূপ উপন্যাস। এখানে আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয় পাশ্চাত্য প্রভাবে। বাংলা উপন্যাসের সফল যাত্রা শুরু হয় বঙ্কিমচন্দ্র’র (১৮৩৮-১৮৯৪) হাতে। তিনি ইতিহাস ও রোমান্সনির্ভর উপন্যাস রচনা করেন। বাংলা উপন্যাসের আদর্শ-ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পায় বঙ্কিমের হাতে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুটি উপন্যাস রাজর্ষি ও বউঠাকুরানীর হাট বঙ্কিম-প্রভাবিত। বাংলা উপন্যাস নতুন বাঁক নেয় চোখের বালি উপন্যাসের মাধ্যমে। বাংলা উপন্যাসের নতুন আর এক দিক উন্মোচন হয় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যোগ করলেন নতুন মাত্রা। তবে বঙ্কিম উপন্যাসের সামগ্রিক রূপটি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।
বঙ্কিমী ধারার লেখক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)। মীর মশাররফ হোসেন অসাধারণ জীবনচেতনার বৃহত্তর সমাজ কাঠামোকে উপন্যাসে আনেন। তাঁর উপন্যাসের কাহিনিকেন্দ্রে থাকেন বঙ্কিমচন্দ্র। গদ্যে তিনি কখনোই বঙ্কিমী-রীতি ছাড়েননি। অনেক ঔদার্য ও উন্মুক্ত জ্ঞানে তিনি বাংলা গদ্যরীতিকে উপন্যাসের কাহিনিতে প্রবিষ্ট করান। তবে এমন দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছিল মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিজীবন থেকে। অনেক র্স্পশকাতর আখ্যান রচনায় তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর মানবতাবাদের শর্তসমূহ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাতেও এরকম ভাষাপরিক্রমায় প্রাঞ্জল তিনি। আমার জীবনী (১৯০৮) বা কুলসুম জীবনীতেও (১৯১০) তার বহুবিধ প্রমাণ মেলে। মীর মশাররফ হোসেন পারিবারিক জীবনেও এরূপ প্রতিশ্রুতি পালন করেন। পরিবেশের দায়বদ্ধতায় উপন্যাসের ক্ষেত্রটি তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন। নিজ ধর্ম ও মুসলিম আনুগত্যের প্রেরণা তিনি অর্জন করেন বাল্যকালেই। কিন্তু সেটি বিশেষ কোনো কাল পরিবৃত্তি বা স্বধর্মের-কাঠামোতে আটকান না, হয়ে ওঠেন জীবনভাষ্যের পূর্ণাঙ্গ রূপকার। বিষাদ-সিন্ধু শুধু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, একটি ধর্মনিঃসৃত আখ্যানও বটে। বিচিত্র ভাবনার পরিবৃত্তে এটির অবলোকন চলে অনেককালব্যাপী। মীর মশাররফ হোসেন বঙ্কিম অনুসৃত রীতিতে উপন্যাস রচনা করেন এবং সেখানে বঙ্কিমী পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সামনে এগোতে থাকেন।
মুসলিম লেখক হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের জনপ্রিয়তা শতবর্ষের পরেও আকাশচুম্বী। উপন্যাস রচনায় তিনি অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর কারণ, মুসলমানদের উগ্রতা ও সংস্কারচেতনা বিপুলভাবে তৎকালীন আর্থ-সামজিক পরিপ্রেক্ষিতে বজায় ছিল। তাঁদের নানারকম দ্বন্দ্ব বিরাট জটিলতা সৃষ্টি করে। একমাত্র মীর মশাররফ হোসেন নিজে মুসলমান হয়েও বাঙালিয়ানা বা জাতিতাত্ত্বিক বীক্ষায় নিজের আত্মপরিচয়ের সম্মানটি অর্জন করতে পেরেছিলেন। অসম্ভব উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সাহিত্যের পুরাতাত্ত্বিক দস্তুরটি তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন। সেজন্য বিষাদ-সিন্ধুর মতো মহাকাব্যিক উপন্যাসও তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন এবং তা জনপ্রিয়তার তুঙ্গস্পর্শী লাভ করেছিল। ভারতবষের্র মুসলমানদের বিকশিত হওয়ার পথ নানাভাবে অবমুক্ত হলেও বাঙালির অস্তিচেতনা নিয়ে তখনও গণমানুষের মধ্যে সংকট কাটেনি। এ পর্যায়টিতে তাঁরা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষাপূর্ণ ছিলেন। প্রধানত ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেখানে বাঙালি মুসলমান হিসেবে মীর মশাররফ হোসেন অনেক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তা অর্জন করলেও বাঙালি মুসলমানরা নানা সমস্যায় আচ্ছন্ন থাকেন। তাদের কিছু বাধা ছিল; যেখান থেকে তাদের সংশয়ও দানা বেঁধে উঠেছিল। বিশেষজ্ঞ মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:
ইংরেজ বিরোধিতার বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রয়াস সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেও তা ছিল প্রধানত সামন্তকেন্দ্রিক। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। সাঁওতাল বিদ্রোহও প্রায় তাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের শেষদিকে সংগঠিত হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও তৎপুত্র দুদুমিয়া (১৮১৯-১৮৬০)-র নেতৃত্বাধীন ফরায়েজি আন্দোলন কিংবা ওহাবি বিদ্রোহের চরিত্র ইংরেজবিরোধী হলেও ধর্মীয় শুদ্ধতা ফিরিয়ে আনাই ছিল এর লক্ষ্য। এসব সশস্ত্র ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের যৌক্তিক পরিণতি পাবার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বললেই চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দেখা যায় এইসব সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছে। তার পরিবর্তে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বুর্জোয়া ছকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সূচনা করে। এই সূচনা পর্বের পূর্বের পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষিত বাঙালির ভেতরে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে এবং তা তাদের আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছিল।৬
এছাড়া ধর্মীয় শাসনের সঙ্গে জাগতিকতার বা মানবীয় দিকসমূহের তথাকথিত পার্থক্য, রক্ষণশীলতার বিপরীতে দাঁড়ানো, শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ ইত্যাকার কারণে অধিকাংশ গণমানুষ ঘরে-বাইরে বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্যরা মীর মশাররফ হোসেন যেমন এগিয়েছেন স্বীয় প্রতিভাবলে (প্রসঙ্গত অনেক নাট্যকারও বটে) কিন্তু তেমনটা নন। প্রকৃতঅর্থে তখন সে পরিবেশটি ছিল না, সৃষ্টি হয়নি কোনো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ফলে মুসলমানরা জেহাদে অংশ নেয়, মফস্বলে থেকে নানামুখী বিষয়ে ইন্ধন যোগায়। একাধারে উনিশ শতকীয় দ্বিধা অন্যদিকে সাংস্কৃতিক শূন্যতা উপনিবেশবাদী শাসনকর্তাদের সুযোগ এনে দেয়। তাদের হাতে যা লেখা হয় তা নিছক চালচিত্র বা জীবনের সরল বৃত্তান্ত। কখনোবা তা সমাজরীতি পরিস্রুত গতানুগতিক জীবনচিত্র। ফলে জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রটি একটি বাস্তবতা থেকেই তাঁদের নিকট অধরা রয়ে যায়। তবে যেমনটি উল্লেখ করা গেছে যে, একমাত্র মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন ব্যতিক্রম। কারণ, বাঙালি মুসলমানদের গতানুগতিকতার বদলে বড়শিল্পী হিসেবে তিনি জায়গা খুঁজে নেন। সেক্ষেত্রে তাঁর শিল্পচেতনার প্রকৃত ক্ষেত্র বা দস্তুরকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু পরবর্তী মুসলিম লেখকদের মধ্যে অনেকেই তেমন অগ্রসর হতে পারেননি। একদিকে তাদের ব্যক্তিজীবনে যেমন ছিল অসহায়ত্ব, শূন্যতা অন্যদিকে তেমনি সমাজের নির্ধারিত বাস্তবতাও ছিল;যা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁর উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), গাজী মিঞার বস্তানি (১৮৯৯) বিখ্যাত গদ্য রচনা। রত্নবতী (১৮৬৯) তাঁর উপন্যাস। সময়-কাল বিবেচনায় এ উপন্যাসটিও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।
‘বাঙালী মুসলমান লিখিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস’৭ লিখেছেন চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী (১৮৫০-১৯০০)। তাঁর উপন্যাস প্রেমদর্পণ (১৮৯১)। তবে এ উপন্যাসে মুসলিম জীবনাগ্রহ তেমন নেই যতোটা আছে হিন্দুসমাজের চালচিত্র। গ্রামীণ সমাজের দলাদলি, বেশবাস, আচার-আচরণ, ভেদ-বিভেদ এখানে বর্ণিত। সবকিছুই চালচিত্র আকারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গভীর সমস্যার শিল্পিত রূপ এ উপন্যাসে নেই। তবে তাঁর উপন্যাসে সমাজ-সম্প্রাদয়ের অন্ধকার দিকটি ঠিকই পাওয়া যায়। উদাহরণ: ‘অবিবাহিতা নামটি ঘুচিলেই নীচবংশ মধ্যে স্বীয় পতির বিনা সংশ্রবেও যদি সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান, সেই অবিবাহিতা নামটি ঘুচানকারীর সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে।’৮
মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) কবি হিসেবে পরিচিত হলেও উপন্যাস-রচনাতেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর জোহরা (১৯১৭) পাঠকনন্দিত উপন্যাস ছিল। সে-সময়কালের মুসলিম সমাজচিত্র উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য। তাঁর আর একটি উপন্যাস দরাফ খান গাজী (১৯১৯)। শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) এর লায়লী মজনু (১৯০৪) শিল্পোৎকর্ষ সমৃদ্ধ উপন্যাস না হয়েও এর ভাগ্যে পাঠকপ্রিয়তা জুটে যায়। লায়লী-মজনু’র (কায়েস) অমর প্রেম-কাহিনি মানুষের কাছে চির পরিচিত। এর আবেদন চিরন্তন ও সর্বজনীন। যে কারণে এ উপন্যাস সহজেই পাঠকপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। পরিচ্ছন্ন ও আবেগময় ভাষার কারণেও উপন্যাসটি পাঠকের সমাদর লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পরূপটি প্রেমদর্পণ-এর মতো এ উপন্যাসেও অনুপস্থিত হলেও তাঁর গাম্ভীর্য ও সৌষ্ঠবপূর্ণ কাব্যময়ী ভাষা প্রশংসনীয়:
যদি প্রেম করিয়াই থাকি,;যদি মজিয়াই থাকি, তবে লাঞ্ছনা কর কেন? শ্যাম কুঞ্জোপবনে পুষ্পময়ী লতার ন্যায় আবেগে আন্দোলিত হইয়া প্রণয়-জ্বালায় যদি রমণীগণ এতই ব্যাকুল হয়, আর পুরুষ-বৃক্ষই যদি প্রকৃত লতাকে বক্ষে ধারণ করিবার অধিকার পাইয়া থাকে, তবে পবিত্র প্রেম, স্নিগ্ধ ভালবাসা, প্রাণ জুড়াইবার এ সাধ, এ পোড়া পৃথিবীতে এত ঘৃণা কেন? বুঝিলাম—তোমাদের চক্ষু দৃষ্টিহীন; হৃদয় ভ্রমান্ধ।৯
উপন্যাসে প্রকৃত রূপটির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এক্ষেত্রে ইসমাইল হোসেন শিরাজী’র (১৮৮০-১৯৩১) নাম বিশেষভাবে উলে¬খনীয়। তাঁর উপন্যাস হলো: তারাবাঈ (১৯০৮), ঈশা খাঁ বা রায়-নন্দিনী (১৯১৫), ফিরোজা বেগম ( ২য় সং ১৯২৮) ও নূরুদ্দিন (২য় সং ১৯২৮)। শিরাজীর উপন্যাসে সমাজের ভেদবিচারের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র অনুসরণে কিংবা প্রতিকারের ভিত্তিতে তিনি উপন্যাস রচনা করেন। এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে তারাবাঈ (১৯০৮) উপন্যাসের কথা। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল রায়-নন্দিনী। বিশেষ করে সেকালের মুসলিম সমাজ এ উপন্যাসটিকে তাদের আত্মমর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করতো। শিরাজীর ভাষায় শক্তি ছিল। যেমন, রায়-নন্দিনী (১৯১৬) উপন্যাস থেকে উদাহরণ যেতে পারে:
অধম আমরা, মূর্খ আমরা, অদূরদর্শী আমরা, তাই মর্হরম-পর্ব দেশ হইতে উঠিয়া গেল। জীবন্ত ও বীরজাতির উৎসব কাপুরুষ, অলস, লক্ষ্যহীনদিগের নিকট আদৃত হইবে কেন? বীর-কুল-সূর্য অদম্যতেজা হযরত ইমাম হোসেনের অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ ও স্বাধীনতাস্পৃহার জ্বলন্ত ও প্রাণপ্রদ অভিনয়, প্রাণহীন নীচচেতা স্বার্থান্ধদিগের ভালো লাগিবে কেন? পেচকের কাছে সূর্য, কাপরুষের কাছে বীরত্ব, বধিকের কাছে সঙ্গীত, অলসের কাছে উৎসাহ কবে সমাদর লাভ করে? যখন বাঙ্গালায় মুসলমান ছিল, সে মুসলমানের প্রাণ ছিল-বুদ্ধি ছিল-জ্ঞান ছিল-তেজঃ ছিল-বীর্য ছিল; তখন মহররম উৎসবও ছিল।১০
এভাবে মহররমের উপযোগিতা ও প্রচলিত বিয়ের বিষয়টি তিনি উপন্যাসে আনেন। এতে করে জাতীয় চেতনার স্বরূপও উল্লে¬খনীয় হয়ে ওঠে। তাতে হিন্দ-মুসলমান বলে কিছু নয়, গুরুত্ব পেয়েছে প্রকৃত ধারার ঐতিহ্যিক আদর্শ। যেটি প্রত্যেক বড় লেখকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবে প্রধানত জাতীয় চেতনার পরিপ্রেক্ষিতটিই তিনি উপন্যাসে তুলে আনেন। তবে মুসলিম নায়ক আর হিন্দু নায়িকার আন্তঃপ্রণয়ের চিত্রে তিনি মুসলমানদের গৌরবান্বিত করে তোলেন। প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসে এরূপ প্রণয়ের চিত্র বর্ণনা করেছেন তিনি। এরূপ চিত্র একইভাবে মোজাম্মেল হক-এর (১৮৬০-১৯৩০) জোহরা (১৯২৭), শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী’র (১৮৯৫-১৯৪৫) বঙ্কিমদুহিতা (১৯১৭) উপন্যাসেও পরিলক্ষিত। সেখানে বঙ্কিম উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় কাহিনি বিন্যস্ত করা হয়েছে। জোহরায় বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার প্রভাবে রোমাঞ্চের আধিক্য ঘটেছে। সমাজচিত্রটিও নির্মিত হয়েছে কপালকুণ্ডলার অনুসৃতে। একসময় মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের মতামত বা ইচ্ছে কোনো মূল্য বহন করতো না। জোর করে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে পরিবারের পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হতো। এতে নারীর জীবনে দুঃসহ বেদনার যে করুণ পরিণতির জন্ম হতো এ উপন্যাসে সে চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটির পাঠকপ্রিয়তা লাভে নায়িকা জোহরার মর্মন্তুদ কাহিনি মূল শক্তি। তবে এ উপন্যাসের ভাষাশৈলীটি প্রশংসনীয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিরাজী এ ধারা থেকে বের হয়ে এসে রচনা করেন নূরউদ্দিন (১৯২৩)। এ উপন্যাসে হিন্দুর অতীত অত্যাচারের কাহিনি তিনি প্রবন্ধের মতো করে বর্ণনা করেন। তাঁর ফিরোজা বেগম (১৯২৩) উপন্যাসেও প্রায় একইভাবে সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের কাহিনি বিধৃত। এসব অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতনের কাহিনি বর্ণনা করে শিরাজী সেকালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। অন্তত মুসলমানদের নিকট। প্রধানত সামাজিক বিষয়াশ্রিত এসব ব্যাপার অনেকের মনোযোগের কারণ যেমন হয়েছিল তেমনি সাংস্কৃতিক সচেতনতার দিকটিও প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।
শিরাজীর সময়কালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর (১৮৮০-১৯৩২) উপন্যাসে নতুনমাত্রা হিসেবে যুক্ত হয় পর্দাপ্রথার অন্ধকারে নারীসমাজের অবরুদ্ধতা ও অশিক্ষা এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার মন্ত্রবীজ। এ চেতনাপ্রসূত থেকেই তাঁর মতিচূর (১ম খণ্ড ১৯০৬, ২য় খণ্ড ১৯২১), অবরোধবাসিনী (১৯২৮), পদ্মরাগ (১৯২৮) প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হয়েছে। তাঁর সব উপন্যাসেই প্রধান উপজীব্য পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমান নারীদের দুর্দশনার চিত্র এবং জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমেই নারী শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে পদ্মরাগ উপন্যাসের মূল মেসেজ এটি। অবরোধবাসিনী উপন্যাসে পর্দাপ্রথার ভয়ঙ্কর অন্ধকারের নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হয় কুসংস্কারের ভয়ালস্বরূপটি, উচ্চারিত হয় নারীমুক্তির মন্ত্র; উদিত হয় জাগরণের আলোকবার্তা। অবরোধ-বাসিনী থেকে উদাহরণ: ‘আমাদের ন্যায় আমাদের নামগুলি পর্যন্ত পর্দানর্শিনা। মেয়েদের নাম জানা যায় কেবল তাহাদের বিবাহের কাবিন লিখিবার সময়।’ ১১
বাঙালি মুসলমানদের যে অবিসংবাদিত রূপ, সেটি কাজী আবদুল ওদুদের পর্বে বহমান। বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবস্থান। উপন্যাস-সাহিত্যেও তাঁর পদচারণা রয়েছে। তিরি নদীবক্ষে (১৯১৯) উপন্যাস লেখেন। নদীবক্ষে একটি ফ্ল্যাট উপন্যাস। উপন্যাসের যে বাস্তবতা বা জীবনাগ্রহ দরকার তা কিছুতেই তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়নি। আর তা স্বাভাবিকও ছিল না । অথচ তাঁর সাহিত্যরুচি ও জীবন সম্পর্কে আগ্রহ ছিল তুলনারহিত। তাঁর উপন্যাসে শিল্পের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে ভালোমন্দ বা সুখদুঃখচিন্তার লেখকরা অর্জন করতে পারেন খুব স্বল্প পরিমাণে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা মীর মশাররফ হোসেন তাদের পূর্বপুরুষ হলেও তারা অনেক বেশি পরিমাণে তাঁদের চেতনার জগৎটি অর্জন করতে পারলেও উচ্চমাত্রার শিল্পশক্তির প্রমাণ রাখতে পারেন নি। তবুও উপন্যাস রচনার পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। উপন্যাসে যে সত্যমিথ্যা বা সুখদুঃখ নির্ধারণই মূল বিষয় নয়, সমাজের ভেতরে সংগ্রাম ও দীক্ষা, জীবনীশক্তির স্ফূর্তিপ্রণোদনা অবশ্যম্ভাবী সেটি এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পায়। মননশীল প্রবন্ধের লেখক হিসেবে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাস সরলা (১৯১৮), পথহারা (১৯১৯), রায়হান (১৯১৯), প্রীতি উপহার (১৯২৭) ও বাসর উপহার (১৯৩০)। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসে নৈতিকতা, আদর্শ, ব্যক্তিত্ব, মানবতাবাদ এসব দিক উপস্থাপিত হয়েছে। আবদুল মালিক চৌধুরীর স্বপের ঘোর (১৯২৩), আবদুল ফাত্তাহ কোরেশীর সালেহা (১৯২৪), মোহাম্মদ শাহজাহানের নিমকহারাম (১৯২৫), আপন-হারা (১৯২৫), সৈয়দ আফতাব হোসেনের অশ্রুরেখা (১৯২৭), মোহাম্মদ সানাউল্লাহর মুত্যুপথে (১৯৩৭) কিংবা বন্দে আলী মিয়া’র ঘূর্ণিহাওয়া (শেষলগ্ন পরবর্তী পববর্তিত নাম, এখন সংস্করণের প্রকাশকাল পাওয়া যায় না) বা বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (১৯৩১) প্রভৃতি উপন্যাসে আদর্শভিত্তিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। রক্ষণশীলতা বা উদারতার দৃষ্টান্ত বা জাতপাতের ভেদবিভেদ এ লেখকদের উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা পাঠকের জনপ্রিয়তার সূত্রটি নির্ধারণ করে। ঘূর্ণিহাওয়া উপন্যাসে পল্লীর নিস্তরঙ্গ জীবনচিত্র ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উপস্থাপিত হয়েছে। শিলাইদহ পল্লী অঞ্চলের মুসলমান পরিবারের নিখুঁতচিত্র অঙ্কন এবং কাব্যধর্মী ভাষা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ উপন্যাসের পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে মূলসূত্র হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। পল্লী-জীবনচিত্র ও পল্লী-প্রকৃতির নানা উপমা-সমৃদ্ধ করে নারীর রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনায় লেখক দক্ষ শিল্পী।
গায়ের রঙটা কল্মিলতার মতো শ্যামল এবং হাতগুলো শাপ্লার ডাঁটার মতন ছড়া ছড়া। মাংসে ফোলা মুখে দুইটি ভাসা ভাসা চোখ;এমন চমৎকার যে, উহার দিকে একটিবার মাত্র তাকাইলে দৃষ্টি স্ন্গ্ধি হয় এবং আরও একবার তাকাইতে ইচ্ছা করে। সারাদেহে যৌবন রসে-ভরা ডালিমের মত ফাটিয়া পড়িবার রকম হইয়াছে।১২
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে উপন্যাসে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও নাটকীয় ঘটনার সংস্থান, সেইসঙ্গে কাব্যিক ভাষা ও হৃদয়স্পর্শী সংলাপ প্রয়োগ এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ হৃদয়বত্তার পরিচয় গ্রন্থটিকে বিশেষ তাৎপর্য দান করে। তাঁর পাঠকপ্রিয়তার মূলসূত্রটিও এখানে গ্রথিত। উপন্যাসের নায়িকা খ্রিস্টান তরুণী মালবিকার প্রেম-প্রীতি ছেড়ে নায়ক মুসলমান যুবক ফরিদ স্বর্গে যেতেও রাজি নয়। ধর্ম-বর্ণ এমনকি পরকালের লোভনীয় স্বর্গের চেয়েও দেশীয় খ্রিস্টান তরুণী মালবিকা তার কাছে মূল্যবান। হৃদয়ঘটিত প্রেমই এখানে সবচেয়ে বড় শক্তি, যেখানে বড় সত্য হয়ে উঠেছে মানুষÑমানুষের হৃদয়বত্তা। তবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রথম অসাম্প্রাদায়িকতা তথা হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রসঙ্গটি নিয়ে আসেন বিশেষভাবে। তাঁর উপন্যাস রায়হান কিংবা পথহারা গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের চরিত্ররা চায় সম্প্রীতির ভেতর দিয়ে মানুষ দিন অতিবাহিত করুক। এর কারণ হিসেবে মানবতাবাদই প্রবিষ্ট হয় কাহিনিতে। দুই সম্প্রদায়ের অন্তঃসর্ম্পক নিয়ে নানা রকম মন্তব্য ও প্রস্তাব রচিত হয়। এ প্রসঙ্গে রায়হানকে তুলে আনলে দেখা যায়:
দুই বিরুদ্ধ জাতির মধ্যে সখ্যত স্থাপন অসম্ভব। বিবাহ প্রথা ছাড়া কোনোকালে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রণয় হয় নাই;অথচ হিন্দু মুসলমানের প্রণয় না হলে চলে না। কারো কাছে আমি আমার মত প্রচার করে বেড়াচ্ছি না। যে চিন্তা সহজভাবে খেলার মতো আমার মাথায় আসে তাই বলতে যাচ্ছি।১৩
রায়হান এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং আদর্শবানরূপে রচিত। একে আপন জীবনাদর্শে তৈরি করেছেন লেখক। হিন্দু-মুসলমানের সমস্ত সংস্কার অতিক্রম করে লেখক একটা সমুন্নতিতে পৌঁছাতে চেয়েছেন এমন চরিত্রের ভেতর দিয়ে। পথহারাতেও এমন দৃষ্টান্ত স্থাপনে ব্রতী হয়েছেন লেখক। এখানে হিন্দু মহিলার চরিত্র এমনভাবে অঙ্কন করেন যা একটা সময়ে অমলিন দৃষ্টান্ত। বাঙালি হিন্দুকে তিনি ‘উন্নত’ এবং ‘চিন্তাশীল’ আখ্যা দিয়েছেন। এরূপে আমরা অসাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্তরূপে বিংশ শতাব্দীর শুরুকে চিহ্নিত করতে পারি এবং এমন মন্তব্য পাওয়া একজন লেখকচিত্তকে পেয়ে যাই। তবে মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩) এক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। পীরপ্রথা বা পীরদের ক্ষমতা, কৌশল বা আধিপত্য নিয়ে তিনি বেশকিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর গরীবেব মেয়ে (১৯২৩), পরিণাম (১৯২৭) ও প্রেমের সমাধি (১৯২৮) উপন্যাসে পীরের মর্যাদার প্রশ্নটি উঠে এসেছে। এ লেখক প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়ে যান এসব উপন্যাস রচনা করে। প্রাসঙ্গিকভাবে নিশ্চয়ই আনোয়ারা’র (১৯১৪) কথা বলতে হয়। এসব উপন্যাসে ধর্মচর্চা, মুসলিম রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, আদেশ-উপদেশ-নির্দেশ অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করেছেন। এসব উপন্যাসে ধর্মচর্চার বিষয় পারিবারিক জীবনাগ্রহে ব্যক্ত করেছেন। এভাবে মুসলিম ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রটি রচিত হয়। জাত্যাভিমান ও বংশপরিচয়ের বিষয়ে নজিবর রহমান তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস আনোয়ারায় বলেন:
সকলের মূলেই এক আদম। তবে কার্যবশতঃ সংসারের বড় ছোট হইয়া গিয়াছে। আমাদের মোগল পাঠান শেখ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের মূল ইহাই। ফলতঃ বংশমর্যাদা সব দেশে, সব কালে সৎ-অসৎ কার্যফলের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। আমরা সম্ভ্রান্ত শেখ বংশোদ্ভব। যে বংশে আমি বিবাহ করিয়াছি, তাহাও সম্ভ্রান্ত শেখ। আপনার বাপ-দাদারাও বুনিয়াদি শেখ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। সুতরাং বংশের গৌরব করা আপনার উচিৎ নয়।১৪
আনোয়ারার স্বামী নূরল এস্লাম সৎমাকে উদ্দেশ্য করে এরূপ সচেতন উক্তি করেন যেটি তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে লেখকের মনেরই আজ্ঞা। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য: ‘মনে হয়, বংশের আভিজাত্যের লেখকের কিছুটা আস্থা ছিল।’১৫ পর্দাপ্রথা, ধর্মনিষ্ঠা বা বংশমর্যাদা সম্পর্কে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের স্পর্শকাতর দৃষ্টিচেতনাই তাঁকে পাঠকপ্রিয়তা দিয়েছিল। তবে মোহাম্মদ নজিবর রহমান বহুবিবাহ ও তালাক প্রসঙ্গে কিছুটা রক্ষণশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। আনোয়ারায় আছে ‘সতীর সর্ব্বস্ব পতি,/ সতী শুধু পতিময়, বিধাতার প্রেমরাজ্যে সতত সতীর জয়।’১৬ গরীবের মেয়ে বা পরিণাম-এ নজিবর রহমান তালাক সমর্থকে মন্তব্য করেন। তবে ঔপন্যাসিকের এসব মন্তব্য অনেকটা সমাজধারণাপ্রসূত। এরূপ ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অমূলক ছিল না। তবে সমস্ত রক্ষণাশীলতাকে এড়িয়েই নজিবর রহমান বাংলা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ অভিধা পেয়ে যান। বোধ করি, জনপ্রিয়তার বিষয়টিতে তাঁর রক্ষণশীল মনের সমর্থনই পাঠকদের অনুগামী হয়। তবে নজিবর রহমানের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মনোভাব খুব বেশি ছিল। চাঁদ-তারা বা হাসান গঙ্গা বাহমানির বিষয় বঙ্গদেশের বাইরে হলেও বঙ্গীয় সংস্কৃতির ভাবনাই সেখানে পরিস্রুত।
মোহাম্মদ নজিবর রহমান এ উপন্যাসে মুসলিম শাসনের প্রতিও দৃকপাত করেছেন। তাঁর প্রেমের সমাধি উপন্যাসেও বিদ্যমান। হিন্দু-মুসলমান দুই বান্ধবের সখ্যের বিষয়টিও এখানে প্রতিফলিত। সমসাময়িক সমাজের চিত্রটি তিনি চমৎকার করে পরিবেশন করেছেন। সেখানে বিভিন্ন বর্ণভেদ বা ছুঁৎমার্গের নানারকম বিষয় তাৎপর্যমণ্ডিত করে তিনি উপন্যাস তুলে এনেছেন। সমাজের যাবতীয় প্রক্রিয়া ও দ্বন্দ্বাত্মক বিষয়গুলোর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাসের যে চারিত্র্য সেটি তিনি তাঁর রচনার মধ্যে উদ্ভিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলন। ব্যক্তি ও সমাজদ্বন্দ্বের ভেতর থেকেই উপন্যাসের আলেখ্য রচিত হয়। মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আনোয়ারা কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে মোহাম্মদ কোরবান আলী রচনা করেন মনোয়ারা উপন্যাস। এটিও সে-সময়কালে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) নজরুল-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান কবি। তবে তিনি মরুর কুসুম, রিক্তা, কাঁটাফুল, পথের দেখা, সোনার কাঁকন প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করলেও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যতি অর্জন করতে সক্ষম হননি। কাজী নজরুল ইসলামেরও (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রধান খ্যাতি কবি হিসেবে। ‘বিংশ শতকে মুসলমানদের মধ্যে একাধিক বিস্ময়কর প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল, নিঃসন্দেহে নজরুল ছিলেন তাঁদের মধ্যে সেরা।’১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এ সময়পর্বে উপন্যাস লিখে জনপ্রিয় না হলেও যে বিপ্লব চেতনার ‘আইকন’রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন সেটাই গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে। কুহেলিকা (১৯৩১) উপন্যাসে ধর্মবিষয়ে রসিকতা আছে। সমকালীন বিপ্লবীদের চেতনাও এখানে পরিস্রুত। যেটির ভেতরে নির্ধারিত জনপ্রিয়তার অনলবর্ষী উচ্চারণ।
আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হূন মেরেছে। আরবী ঘোড়া মেরেছে চা’ট কাব্লিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরানি মেরেছে ছুরি, তুরানি হেনেছে তল্ওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পতুগিজ-ওলন্দাজ দিনেমার ফরাসি;ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকি ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু;যার জোরে এত মারের পরও এ-জাত মরেনি;তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজী!১৮
প্রারম্ভিকদিকে রচিত নজরুলের পত্রোপন্যাস বাঁধন-হারা উপন্যাসে আবেগদীপ্ত ভাষা প্রেম ও প্রত্যয়ের দীপ্তিতে প্রকটিত। নজরুলের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে তাঁর অবিসংবাদিত কবিখ্যাতি যুক্ত ছিল। তিনি প্রেম ও বিদ্রোহের কবি, সুতরাং তাঁর রচনায় প্রেম-বিদ্রোহরে যে বার্তা নির্ঘোষিত তার গুণেই সমকালের বা একালের পাঠকদের তা আকর্ষণ করেছে। নজরুলের ব্রত ছিল হিন্দু-মুসলমানের সর্ম্পকের উন্নতি এবং বর্ণ-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানবতার আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া। নবযুগ গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধে এসব কৃতির স্বীকৃতি মেলে। সেটি তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও কার্যকর। নজরুল সমসাময়িক সময়ে একজন ‘ক্রেজ’ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। সেটি তাঁর উপন্যাস রচনার পরিবেষ্টনে অমোঘরূপে কার্যকর ছিল। মৃত্যুক্ষুধা বা কুহেলিকার মতো উপন্যাস এক্ষেত্রে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
নজরুলের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে যেমন তাঁর অবিশ্বাস্য কবিখ্যাতি, ঔপন্যাসিক হিসেবে জসীমউদ্দীন-এর (১৯০৩-১৯৭৬) জনপ্রিয়তা লাভের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি প্রায় একইধারায় পর্যবসিত। জসীমউদ্দীন উপন্যাস বোবাকাহিনী (১৯৬৪) প্রকাশের বহু আগেই তিনি কবি হিসেবে খ্যাতিমান। বোবাকাহিনী রচিত হয়েছে মুসলমান কৃষকদের জীবন-কাহিনি নিয়ে। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে গ্রামের সাধারণ এক কৃষক আজাহের তার পুত্রকে ডাক্তারি পড়িয়ে নতুন স্বপ্নে বিলাত পাঠায়। স্বপ্ন আর সংগ্রামের নিখুঁত গ্রামীণ জীবনচিত্রে উঠে এসেছে বোবাকাহিনীতে। উপন্যাসটিতে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে গ্রাম-জীবনের সামগ্রিক চিত্র। সেই কারণে তাঁর বোবাকাহিনী বিষয়বস্তু, ভাষা, সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র, আনন্দ-বেদনা-দৈন্য, সুখ-দুঃখ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নানাবিধ কারণেও পাঠকনন্দিত হওয়ার গৌরব লাভ করে। কিন্ত একথা অস্বীকার করা যায় না পাঠকের কাছে বোবাকাহিনী প্রথমে যে গুরুত্ব লাভ করেছে তা গুণগতমানে নয়, কবি জসীমউদ্দীনের উপন্যাস হিসেবে।
ধর্মীয় বিষয় ও জীবনাচারকে কেন্দ্র করে রচিত হয় এম এ হাশেমের আলোর পরশ (১৯৫৩) উপন্যাস। প্রাচীন আরবে মুসলিম-নির্যাতন, নও-মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস, কষ্টবরণ ও নির্বাসন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসীদের সমাজে নারীর দুর্দশা ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থের পটভূমি। গ্রন্থটিতে ভাষাশৈলী ও চিত্রকল্প নির্মাণে লেখক পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তিনি ভাষার জোরে নরক-চিত্র বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ উপন্যাসটি ব্যাপকভাবে পাঠকনন্দিত হয়েছিল। আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)-এর চৌচির (১৯৩৪) উপন্যাসেও মুসলিম জীবনাগ্রহের পরিচয় বিধৃত। জনপ্রিয়তার ধারায় এটিও একটি অবস্থান রচনা করে। যদিও মুসলিম সমাজে পাঠকপ্রিয়তা সে অর্থে গণনা করার সুযোগ কম তবুও ঐতিহ্যিক আরাধ্যে এটি অগুরুত্বপূর্ণ নয়। শৈলীটি পরীক্ষার জন্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে: ‘সেই নিস্তব্ধ নিশীথে তাহার অন্তর মথিত করিয়া ধ্বনিত হইল: প্রভো! জন্মান্তরে, পরলোকে মানুষের আরও জীবন আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, নবজীবনে, জন্ম-জন্মান্তর আমাকে পাওয়ার অবসান থেকে মুক্তি দিয়ো। না পাওয়ার উন্মুখ প্রতীক্ষার ক্ষুধাই যেন আমার সহায় হয়।’১৯ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের কথা আছে তাঁর জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে বৃহত্তর সামাজিক পটভূমি অনুপস্থিত, ব্যক্তি মানুষের উপলব্ধি বাস্তবায়নের পথ ধরে উপন্যাসটির কাহিনি নির্মিত হয়েছে। তাঁর রাঙ্গাপ্রভাত (১৯৫৭) উপন্যাসের পটভূমি দেশবিভাগের বিক্ষুব্ধ সময়কাল। মানবতার জয় ঘোষণা ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানবতার স্থান এ উপন্যাসের মূল ভিক্তি। তাঁর উপন্যাস মানবতাবাদী, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ধারণ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিমানুষের উপলব্ধির বাস্তবায়নের বিশেষ প্রেক্ষিতে রচিত। জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারা এবং সময়কাল ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিবেচনায় আবুল ফজলের এ উপন্যাস গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলা উপন্যাসে জনপ্রিয়তার ধারায় ঔপন্যাসিক আকবর হোসেন (১৯১৭-১৯৮১) গুরুত্বপূর্ণ। সমাজজীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে একজন সুদক্ষ শিল্পীর মতো তিনি তাঁর উপন্যাসে এঁকেছেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর নেতাদের চরিত্রচিত্রণের প্রেক্ষাপটে তিনি উপন্যাস রচনা করে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নর-নারীর অবৈধ প্রণয়ের ফসল হিসেবে মাতৃগর্ভে যে ‘অবাঞ্চিত’ সন্তানের আগমন ঘটে তার জন্যে সমাজ জীবনে নারী কীভাবে লাঞ্ছিত হয় তার বাস্তবচিত্র অবাঞ্চিত (১৯৫০) গ্রন্থ। রমজান প্রেসিডেন্টের মতো অত্যাচারী সামজপতি সুন্দরী তরুণী শাহেদাকে বিয়ে করতে না পেরে তার পিতা জয়নালের মতো আদর্শবান মানুষকে কীভাবে অত্যাচারের স্টিম রোলার পিষ্ট করে ঠেলে দেয় নির্মম মৃত্যুর দিকে, কীভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সমাজজীবনে কলঙ্কিত করতে পারে নিষ্পাপ শাহেদাকে, রশিদের মতো আদর্শবান যুবককে কীভাবে শিকার হতে হয় নিষ্ঠুর বলিয়া আর অত্যাচারী পিতার মিথ্যে আভিজাত্য অহমিকা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে রমজান প্রেসিডেন্টের যৌবনময়ী তরুণী কণ্যা মঞ্জু—তা কি পাইনি (১৯৫১) উপন্যাসে অত্যন্ত সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। জমিদার এনায়েত খান রাঙাবউকে কামাগ্নি বাহুতলে পিষ্ট করতে না পেরে তার আদর্শবান স্বামী ওমর মাস্টারকে চাবুকের নির্মম আঘাতে হত্যা করে। অত্যাচার, শোষণ আর নিপীড়নের স্টিম রোলার চালিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের উপর। এদের সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে অসহায় সাধারণ নারীর ক্ষুধার যন্ত্রণায় একমুঠো খাবারের আশায় দেহ বিক্রির মতো নিকৃষ্ট উপায় বেছে নেয়। এসব চিত্রিত হয়েছে ঢেউ জাগে (১৯৬১) উপন্যাসে। এ উপন্যাসে আদর্শ ও আদর্শহীনতার সংগ্রাম গুরুত্ব পেয়েছে। দেশকাল, আর্থ-সামাজিক ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি নানা চরিত্রের উত্থান-পতন, নৈতিকতা, স্থূলতা, অবক্ষয় তুলে ধরেছেন লেখক। একই সঙ্গে ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে যে ভণ্ডামি ও নষ্ট মানসিকতা বিদ্যামান তা তাৎপর্যপর্ণ হয়ে উঠেছে। লেখক অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে এসব তুলে ধরে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। দু’দিনের খেলাঘরে (১৯৬৫) উপন্যাসে মেহেরার মতো চরিত্রহীনা নারীরা হীনস্বার্থের কারণে কূটকৌশলে সুখী সমৃদ্ধ পরিবার ভেঙে চুরমার করে দেয়। দুষ্টক্ষত (১৯৮৯) উপন্যাসে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ থেকে ১৯৭৫ পযর্ন্ত সময়কাল আন্দোলন-সংগ্রাম, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নৈতিক অবক্ষয় স্থূলতা ও নগ্নতাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রিকজীবনের নানা ঘটনা বিকৃত হয়েছে। নতুন পৃথিবী (১৯৭৪) উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের নেতা বলে পরিচিত একশ্রেণির নেতাদের প্রকৃত স্বরূপ। সাধারণ মানুষের মুক্তির নামে এরা সংগ্রাম করলেও মূলত এসব নেতার মূল উদ্দেশ্য থাকে সাধারণ মানুষের রক্ত আর লাশের উপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে অর্থবিত্তের মালিক হওয়া। আকবর হোসেন অতীব জীবননিষ্ঠ বলেই তাঁর রচনাগুলো আমাদের চেনা পরিবেশ আর এখানে লালিত মানুষের অকৃত্রিম আবহে সৃষ্টি। ফলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনাসম্ভার। ভাষা ও রচনারীতির ক্ষেত্রেও তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছে। ভাষার জোরে তিনি অনেক অস্বাভাবিক ঘটনাকেও বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর সেরা কৃতিত্ব ভাষায়। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজম্ব একটি স্টাইল তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন অলঙ্কার প্রয়োগে তাঁর ভাষার মাধুর্যতার প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আকবর হোসেনের উপন্যাসের প্রধান চমক যেন তাঁর ভাষাতেই। প্রতিটি গ্রন্থের প্রাণবন্ত ও চমৎকারিত্বের মূলে তাঁর স্বচ্ছ, জোরালো এবং কাব্যময়ী ভাষা। ভাষার গাঁথুনিতে তিনি একজন দক্ষ শিল্পী। তাঁর মতো এমন আবেগময়ী ভাষা খুব কম লেখকই সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আর সেকারণে তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা পাঠকের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এসব চরিত্র যেমন দেশকাল, সমাজ ও পারিবারিক নানা আবহে তৈরি, তেমনি চিনিয়ে দেয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ, সংগ্রাম, রাষ্ট্রিক জীবনব্যবস্থা, সমাজে বিরাজমান নানা কুসংস্কারসহ বিভিন্ন দিক। এসব বিচার-বিবেচনায় আকবর হোসেনের উপন্যাসের চরিত্ররা সার্থকতা লাভ করেছে। সচেতন শিল্পী হিসেবে আকবর হোসেন এভাবেই জীবনের সত্যকে পাঠক সমীপে প্রকাশ করেন। এজন্য সেকালে অনেকেই তাঁর রচনাকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু‘ শেষ পর্যন্ত শ্লীল-অশ্লীলের ঊর্ধ্বে সাহিত্যের সামর্থ্যে তাঁর উপন্যাস লাভ করেছে অত্যুঙ্গ জনপ্রিয়তা। বাংলা কথাসাহিত্যে একজন শক্তিমান ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি পেয়ে যান পূর্ণায়ত প্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের পুরোধা কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন: ‘সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দিক আলোচনা করে লেখক বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ ও জোরালো, মনোবৃত্তি আধুনিক এবং উদার আর ঘটনা সমাবেশ স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক মনে হলেও মোটের উপর বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়ে লেখক সামাজিক সমস্যা এবং মানসিক দ্বন্দ্ব বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন।’২০ শুধু তাঁর একটি উপন্যাসই নয়, সব উপন্যাসে তিনি যে জীবনের সূত্র কাহিনির মধ্যে উন্মোচন করেছেন তা একাধারে দ্বান্দ্বিক এবং সংক্ষুব্ধ প্রত্যয়তাড়িত। আকবর হোসেনের এ উপন্যাসসমূহ জনপ্রিয় হওয়ার অপর কারণ উঠতি নগরের মধ্যবিত্ত জীবনকে প্রকাশ করবার তাণ্ডব থেকে।
আকবর হোসেনের জনপ্রিয়তা উত্তুঙ্গস্পর্শী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) পরেই তাঁর জনপ্রিয়তা। এর মূলে আমরা দেখতে পাই, সমাজবিন্দুর ক্ষেত্রগুলোকে তিনি বিশেষ উদ্দীপনাদায়ী শৈলীতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর শৈলীই পাঠককে বেশি টানে। তাছাড়া আকবর হোসেনের উপন্যাসের বিষয় নর-নারীর প্রেম-রোমাঞ্চ, মধ্যবিত্ত টানাপোড়েন, রাজনৈতিক আখ্যান কিংবা সাম্যবাদী চেতনাদর্শ। এসব বিষয় নিয়ে অনেকেই উপন্যাস রচনা করলেও আকবর হোসেন প্রাত্যহিক নায়ক-নায়িকাদের ভেতরের সংকট ও দ্বিধা দোলাচলতার মনস্তত্ত্ব উপস্থাপন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বাংলা কথাসাহিত্যে বাঙালি মুসলিম লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এরূপ আন্তঃসর্ম্পক ও ভেতরের দ্বন্দ্বকে পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করতে সক্ষম হন। উপন্যাস যে বৃহত্তর জীবনের আখ্যান এবং জীবনের যাবতীয় ও সামগ্রিক সম্ভাব্যতার রূপায়ণ, সেটি আকবর হোসেনের মতো লেখক দ্রুত রপ্ত করে ফেলেন। তিনি শুধু ঔপন্যাসিক নয়, একটা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নিয়েও বাংলা উপন্যাসে আবির্ভূত হন। সেখানে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব কিংবা ভেতরের ক্ষোভ-হতাশাকে উপন্যাসের বিষয় করেছেন ।
সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেও উপন্যাসও লিখেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাস মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪) ও নতুন সকাল (১৯৪৫)। হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯) রচিত নদী ও নারী গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে নদীভিত্তিক আরও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস রয়েছে। বিশেষ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম, সমরেশ বসুর গঙ্গা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৯৪-১৯৫০) রচিত ইছামতি (১৯৪৯), কাজী আবদুল ওদুদ-এর (১৮৯৪-১৯৭০) নদীবক্ষে (১৯১৮), তারাশঙ্করের কালিন্দী (১৯৪০), সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে (১৯৭১), আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলি, সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬) উল্লেখযোগ্য। নদীকেন্দ্রিক দরিদ্র মানুষের জীবন-সংগ্রাম এ উপন্যাসের মূল বিষয়। ‘নদী ও নারী এখানে একাকার;যাবতীয় চিন্তনে ও সংগ্রামে, ভাষার জঙ্গমতায় লেখকের এ উপন্যাস হয়ে উঠেছে প্রাণপ্রাচুর্যময়।’২১ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে শক্তিমান লেখক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)। বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে আঙ্গিকগতভাবে তিনি উপন্যাসে নতুনত্ব আনতে সক্ষম হন। শব্দ চয়নেও তাঁর নিজস্বতা রয়েছে। বাংলা উপন্যাসকে তিনি আরও অনেকটা এগিয়ে নিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর জননী (১৯৬১) বিখ্যাত উপন্যাস। বনীআদম (১৯৪৩) ও ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২) তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস জাহান্নম হইতে বিদায় (১৯৭১), নেকড়ে অরণ্যে (১৯৭৩), দুই সৈনিক (১৯৭৩), জলাঙ্গী (১৯৭৪)। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাস পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০), সমাগম (১৯৬৭), আর্তনাদ (১৯৮৫), রাজসাক্ষী (১৯৮৫), পিতৃপুরুষের পাপ (১৯৮৬) প্রভৃতি। শওকত ওসমান বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন কথাশিল্পী। তাঁর জননী উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করতে পেরছে। বিভাগোত্তরকালে রচিত এ উপন্যাসটি গ্রামীণ পটভূমিভিত্তিক প্রান্তিক তৃণমূল মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত হয়েছে। ক্ষুধা-দারিদ্রের কাছে দরিদ্র মানুষেরা কীভাবে পরাজিত হয়, কীভাবে তাদের সম্ভ্রম-সম্মান ক্ষুধা-দারিদ্রের কাছে বলি হয়, এসব বাস্তবতা যেমন আছে, তেমনি আছে দরিয়া বিবি ক্ষুধার কাছে সতীত্ব সম্ভ্রম সম্মান হারালেও, মাতৃত্বকে তিনি ধারণ করেছেন সবার ঊর্ধ্বে। সমাজ-ধর্ম সব কিছুকে উপেক্ষা করে শাশ্বত মাতৃত্বকে স্থান দিয়েছেন সকলের ঊর্ধ্বে। সমাজ-ধর্ম-মানসিক নানামাত্রিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত দরিয়াবিবি নিজেই ধাত্রী সেজে নিজের অনাকাক্সিক্ষত সন্তানকে জন্ম দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে নিজে আত্মহত্যা করে। ‘দড়ির ফাঁসের দিকে দরিয়াবিবি তাকাইল। সারাজীবনের কত উদ্বেগ, কত সংগ্রামজনিত ক্লান্তি ওইখানে ঝুলাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।’২২ দরিয়াবিবির কাছে নিজের জীবন, সমাজ-ধর্ম এসবের থেকে মাতৃত্বই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। যে সত্য শাশ্বত। এখানেই উপন্যাসের বিশিষ্টতা। এটি বাংলা সাহিত্যে অসামান্য একটি রচনা।
ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক উপন্যাস রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮)। তাঁর পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪) সুবৃহৎ কলেবরের উপন্যাস। পাঠক সমাদৃত হয়েছিল এটি। তাঁর অন্য উপন্যাসগুলো পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৪৭), মুক্তি (১৯৪৮), প্রপঞ্চ (১৯৮০), দেয়াল (১৯৮৬), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০) ও ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩)। ‘শুদ্ধ মননশীলতা রুচি ও সমাজ-সন্দিগ্ধ স্বচ্ছ চেতনায় আবু জাফর শামসুদ্দিন বাংলাদেশের উপন্যাসের রুচি ও দিগন্তকে গড়ে দিয়েছেন। সেটা নিছক জনপ্রিয়তার জন্যে নয়; স্থায়ী ও দীর্ঘায়ত ঐতিহ্যের আলোকবর্তিকা হিসেবে।’২৩ বাংলা উপন্যাসের শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে ইতিহাসকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও তিনি ইতিহাসের সঙ্গে অতিমাত্রায় রোমাঞ্চ যুক্ত করেছিলেন। পাঠক কয়েক দশক তাতে বুঁদ হয়েছিলেন। এ বৃত্ত ভাঙতে অনেক সময় লেগেছে রবীন্দ্রনাথের। এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রভাব স্পষ্টত। এরপর দীর্ঘপথ এগোলেও উপন্যাসের বিষয়বস্ত হিসেবে ইতিহাস খুব বেশি বিবেচিত হয়নি। বিশেষ করে মুসলমান লেখকরা আরো পিছিয়ে ছিলেন। এক্ষেত্রে বলা যায় অগ্রগামী হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন আবু জাফর শামসুদ্দিন। তিনিই ইতিহাস-ঐতিহ্যকে প্রধান উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করেছেন।
বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অত্যন্ত শক্তিমান ও নিরীক্ষাপ্রবণ একজন কথাশিল্পী। ‘বিভাগোত্তর সাহিত্যে মুসলিম লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শিল্পের গোড়ায় প্রকৃতঅর্থে জলসিঞ্চন করতে পেরেছিলেন।’২৪ তাঁর উপন্যাস লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) ও কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র বিখ্যাত উপন্যাস লালাসালু। গ্রামীণ জীবনযাপন, সহজসরল দরিদ্র মানুষের জীবনযাপন, ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও ভীতি এসব নিয়ে গড়ে উঠেছে লালুসালু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্বের ধ্বংসলীলা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ;এসব কারণের একটা অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে এদেশের মানুষের জীবনকাল। সেসময়ে ক্ষুধা-দারিদ্র আর ধর্মপ্রীতিও ছিল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অবলোকন করেছিলেন এদেশের মানুষের নানামাত্রিক এই জীবনচিত্র। তিনি দেখেছিলেন ধর্ম ও দরিদ্র মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে একশ্রেণির মানুষ কীভাবে অর্থশালী হয়ে উঠছে এবং সমাজে প্রতিভূ বিরাজ করছে। এই বাস্তবতা থেকেই লিখলেন কালজয়ী উপন্যাস লালসালু। এ সমাজে দিনহীন মজিদ ধর্মকে পুঁজি করে কীভাবে অর্থশালী হয়ে উঠতে পারে, কীভাবে সমাজের ক্ষমতার চাবুকটা নিজের হাতে তুলে নেয়;শোষণের এ স্বরূপটি অসাধারণ এক শিল্পসৃষ্টি হয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র লালসালু। একই সঙ্গে সৃষ্টি করলেন নারীর দ্রোহরূপ, মজিদের সকল ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পদাঘাত জমিলার।
আবুল মনসুর আহমেদের (১৮৯৭Ñ১৯৭৯) জীবন-ক্ষুধা (১৯৫৫) সময়কাল বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিক-প্রাবন্ধিক আবুল মনসুর আহমেদ জীবন-ক্ষুধা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিকে গ্রহণ করেছেন। আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) রচিত সূর্য-দীঘল বাড়ি (১৯৫৫) বিখ্যাত উপন্যাস। সমসাময়িক সমাজবাস্তবতা এ উপন্যাসের বিষয। নারীর স্বাধিকার চেতনার ব্যাপারটি জোরালোভাবে এ উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামীণজীবনের শেকড়ে চিরায়তভাবে স্থান করে নেয়া কুসংস্কার, জনশ্রুতি, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াই এ উপন্যাসের মূল বিষয়। বাংলা উপন্যাসে শিল্পচর্যা এবং পাঠকপ্রিয়তা লাভে এ উপন্যাসটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বেদুঈন সামাদ (১৯২৬Ñ২০০১) জনপ্রিয় কথাশিল্পী । তাঁর বেলাশেষে (১৯৫৬) ও দুই নদী এক ঢেউ (১৯৬০) বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া তাঁর অন্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য;নিষ্পত্তি (১৯৬০), পথে যেতে যেতে (১৯৫৮), ধূম নগরী (১৯৬৭), নিবিড় ঘন আঁধারে (১৯৭৩) প্রভৃতি। মধ্যবিত্ত-জীবনকে নানাভাবে খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করে পাঠকপ্রিয়তা পান তিনি। মুসলিম নারীদের মধ্যে যাঁরা সে-সময় উপন্যাস-সাহিত্যচর্চায় আত্মনিবেদিত ছিলেন, জোবেদা খানম ( ১৯২০-১৯৮৯) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জন্মসূত্রে তিনি লালন-মীর মশাররফ-আকবর হোসেনের কুমারখালীর মাটির সন্তান। আকবর হোসেন ও জোবেদা খানম প্রায় সমসাময়িক। দুজনেই পাঠকপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। আকবর হোসেনের মতো তিনিও প্রেম-রোমাঞ্চকেই উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। অভিশপ্ত প্রেম (১৯৫৯), দুটি আঁখি দুটি তারা (১৯৬৩), অনন্ত পিপাসা (১৯৬৭) জোবেদা খানমের জনপ্রিয় উপন্যাস। শহীদ আশরাফের অপরাজিতা একসময় পাঠকমহলে সুপরিচিত ছিল। নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২) গবেষক-প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও উপন্যাস রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৯), এক পথ দুই বাঁক (১৯৫৮) তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সমাজ-সংস্কৃতি আর্থ-রাজনীতিকে তিনি উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিলেও নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনই তাঁর উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে। কন্যাকুমারী (১৯৬০) লিখেই খ্যাতি পেয়েছিলেন আবদুর রাজ্জাক (১৯২৬-১৯৮১)। তাঁর অন্য উপন্যাস বঁধুয়ার লাগিয়া (১৯৬৮)। আবদুর রাজ্জাকের উপন্যাসে মধ্যবিত্তের ভোগবাদ, মূল্যবোধহীনতা, নৈতিক অবক্ষয় ও মনস্তাত্ত্বিকতা নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২Ñ২০০৯) বাংলা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ও মেধাবী কথাশিল্পী। তাঁর প্রথম দিকের রচনা তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০)। গবেষকের ভাষায়, ‘এ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ক্লান্তি-প্রসন্নতা, হতাশা-ক্ষোভ, নৈরাশ্য-গ্লানি সবই প্রতিরূপিত। কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে প্রেম ও যৌনতার অঙ্গীভূত জীবন। যার মূলে আছে ব্যক্তিচরিত্রকে বিশে¬ষণের প্রয়াস।’২৫ উপন্যাসটিতে তিনি প্রেমকে নানা কৌণিকভাবে বিশে¬ষিত হয়েছে। সেই নিমিত্তে এ উপন্যাসে চারটি প্রেমের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। জাহেদের সঙ্গে ছবির প্রেমের সম্পর্ক, জোবেদার সঙ্গে গড়ে উঠেছে অহিদের সম্পর্ক, জামিল চৌধুরীর সঙ্গে মীরা এবং মুজতবা ও তিনার প্রেমের সম্পর্ক মূলত নানা কৌণিক থেকে তৈরি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো এ সম্পর্কগুলোর একটি আর একটির সঙ্গে কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেনি। এক একটি সম্পর্ক নিজস্ব গতিতে এগিয়েছে। এর ভেতর দিয়ে তিনি প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতেই বেশি আগ্রহী হয়েছেন। প্রেম শরীরনির্ভর নাকি মননির্ভর;চিরকালীন এই জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্ব এখানেও লক্ষণীয়। তবে ঔপন্যাসিক এখানে যেমন প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনি এর একটি সমাধানেও তিনি উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। ‘ঔপন্যাসিক নারীর বিচিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তাঁর অভিপ্রায় ও শিল্পের দায় প্রশমন করেছেন।’২৬
গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক হাজার বছর ধরে (১৩৭১ ব.) জহির রায়হানের অসাধারণ সৃষ্টি। এ উপন্যাসে একদিকে নারীর সংস্কার, অনুশাসন, নিপীড়ন-নির্যাতন যেমন উঠে এসেছে, তেমনি তুলে ধরা হয়েছে পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূজারি দাপট। হাজার বছর ধরে কাহিনিপ্রধান একটি উপন্যাস। কাব্যিক ভাষা উপন্যাসটির একটি বড় শক্তি। তাঁর অন্য উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭ ব.), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫ব.), বরফ গলা নদী (১৩৭৬ব.), আর কতদিন (১৩৭৭ব.), তৃষ্ণা (১৩৮২ব.) ও কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২ ব.)। শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) শক্তিমান কথাশিল্পী। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস সংশপ্তক (১৯৬৫) ও সারেং বৌ (১৯৬২)। দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রবিধৌত অঞ্চলের মানুষের সংগ্রামমুখর জীবন এ উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসটি পাঠকমহলে সমাদৃত। ‘ইতিহাসবোধ ও সংগ্রামী জীবনচেতনার শিল্পরূপ’ হলো শহীদুল্ল¬া কায়সারের সংশপ্তক। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বৈপ্ল-বিক ধারায় উপন্যাস রচনা করে যে কজন কথাশিল্পি খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার অন্যতম। এ ধারারই উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী সত্যেন সেন, জহির রায়হান, আবু রুশদ, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। এঁদের উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল¬ব নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সংশপ্তক এ ধারার এক অসামান্য সৃষ্টি। শহীদুল্লা কায়সার আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস-গল্পের স্রষ্টা। তাঁর উপন্যাস;কৃষ্ণচূড়া মেঘ, দিগন্তে ফুলের আগুন, কুসুমের কান্না, চন্দ্রভানের কন্যা, কবে পোহাবে বিভাবরী। এসব গ্রন্থের কথা স্মরণে রেখেও বলা যেতে পারে, বহুমাত্রিক লেখক শহীদুল্ল¬া কায়সার অন্য আর কোন উপন্যাস-গল্প বা অন্য আর কোন সৃষ্টির স্রষ্টা না হলেও শুধু সংশপ্তকই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে উচ্চতর এক মর্যাদায় আসীন করে রাখতো। এ উপন্যাসে তিনি তাঁর শিল্পদক্ষতার সবটুকু সামর্থ্যরে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। একইসাথে পারিবারিক জীবনচিত্র, প্রেম-দ্রোহ, রাজনীতির নানাকৌণিক মেরুকরণ, সমাজদর্শন সর্বোপরি সুস্থ ও সুন্দর নতুন এক সমাজের স্বপ্নবীজ রোপিত হতে দেখি, ‘চিন্তা করিস নে রাবু, আমি ফিরে আসব। আমি আসব।’ এই ফিরে আসা শুধু ব্যক্তি জাহেদের ফিরে আসা নয়, চেতনা ও আদর্শেরও ফিরে আসা;যার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে এক নতুন সমাজ। উপন্যাসটির যেখানে শেষ, প্রকৃত অর্থে সেখান থেকেই যেন নতুন জীবন, নতুন প্রত্যয়, নতুন দৃঢ়তায় ঘুরে দাঁড়ায়। যেন শেষের ভেতরই শুরুর উৎসব।
সংশপ্তক উপন্যাসের ক্যানভাস দীর্ঘ। সমাজজীবন, যাপিত ধর্ম, রাজনৈতিক আদর্শ, শ্রেণিবেষম্য, পুঁজির হিংস্র ছোবল, নষ্টদের দখলকৃত সমাজের কদর্য রূপ, সুন্দর ও আদর্শের জন্যে অমীমাংসিত সংগ্রামÑসমাজ ও রাষ্ট্রিকজীবনের নানামাত্রিক বিষয় এতো নিখুঁতভাবে খুঁটে খুঁটে শহীদুল্লা কায়সার তুলে এনেছেন, যা আমাদের ভাবিত করে, বিস্মিত করে একইসাথে অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ধারায় এ কারণেই সংশপ্তকের স্থান সুউচ্চ ও কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্যাদার পর্যায়ভুক্ত বলেই বিবেচিত হতে পারে। বাঙালির জীবন সংগ্রাম-সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি নানাকৌণিকভাবে এর আগে সেভাবে অন্য কোনো উপন্যাসে এত দীর্ঘ ক্যানভাসে ধরা পড়েনি। শহীদুল্ল¬া কায়সার ব্যক্তিজীবন অভিজ্ঞতাপ্রসূত সমাজ-সমকাল ও নিজস্ব চেতনা-আদর্শগতভাবেই যে এ উপন্যাসের ক্যানভাসে বহু ধরনের রঙ দিয়েছেন, যে রঙে এক একরকম জীবন জীবন্ত হয়ে ওঠে আমাদের সামনে;যেসব জীবন আমাদের চেনা—এ সমাজেরই। সংশপ্তক উপন্যাসটির কাহিনির সময়কাল ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়কালে এদেশে রাজনৈতিক পটভূমির নানামাত্রিক পরিবর্তন সুস্পষ্ট। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কাল থেকে শুরু করে যুদ্ধোত্তর সময়কাল, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও বিভক্ত এবং বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের আগ পর্যন্ত এ উপন্যাসের সময়কাল নির্দিষ্ট হলেও ভাষা-আন্দোলনের অগ্নিরূপটি তখন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতোই ফণা ধরে উঠেছে। বলা যায়, তের বছরের বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক যে জীবনসত্য তা এ উপন্যাসে শিল্পসুষমায় সত্যালোকে ধরার প্রয়াস রয়েছে। উপন্যাসটি মূলত: উপকূলবর্তী বাকুলিয়া-তালতলি গ্রাম এবং কলকাতা ও ঢাকা শহরকেন্দ্রিক। শুরুটা গ্রামেই-বাকুলিয়াতেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছর তিনেক আগে এ উপন্যাসের কাহিনি শুরু। এরপর এ উপন্যাসের কাহিনিতে যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ এবং ভাষা-আন্দোলনের অগ্নিবাতাস। গ্রাম-বাংলার কয়েকটি পরিবারের জীবনচিত্রের ভেতর দিয়েই এই সময়কাল, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রেমভাবনা, পুঁজির প্রকোপ, ধর্মের অসারতা, উঠতি ধণিক শ্রেণিক অনৈতিকতা ও নষ্টামিপনা এবং এসবের ভেতর থেকেই আবার সমাজে নতুন জাগরণের দীপ্তচেতনার আলোকরশ্মি ফুটে উঠেছে। কাহিনির সূচনা গ্রামে হলেও কাহিনির প্রয়োজনেই বাঁক খাওয়া নদীর মতো কাহিনি গড়িয়েছে কলকাতা মহানগরীতে, ঢাকা শহরের বুকেও। শেষটা ঘটেছে আবার গ্রামে।
শহীদুল্লা কায়সারের ভাষারীতি ও চারিত্র্যে তাঁকে শুধু কথাশিল্পী হিসেবেই নয়, একজন নিরীক্ষাপ্রবণ সুদক্ষ ভাষাশিল্পী হিসেবেও অভিহিত করা যায়। আর এ বিবেচনাতেই সংশপ্তক হয়ে উঠেছে চেতনা-অগ্নিস্পর্ধিত শিল্পজীবনভাষ্য। মুসলিম সমাজের খুঁটিনাটি চিত্র এমনভাবে তিনি শিল্পিতভাবে তুলে ধরেছেন, তাদের প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামের ছবির ছিটেফোঁটাও বাদ পড়েনি। ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রিক জীবনের নানামাত্রিক জটিলতা বিশেষ করে বিদ্রোহ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত-পীড়ন কী অবিশ্বাস্য বিশ্বস্ততার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন শিল্পমান সমুন্নত রেখে। আর এ কারণেই তাঁর শিল্প-সামর্থ্যরে সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে উঠেছে সংশপ্তক।
রশীদ করীম (১৯২৫—২০১১) ঔপন্যাসিক হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর উত্তম পুরুষ (১৯৬১), প্রসন্ন পাষাণ (১৯৬৩), আমার যত গ্লানি (১৯০৭৩), প্রেম একটি লাল গোলাপ ( ১৯৭৮) প্রভৃতি পাঠকমহলে সমাদৃত। মহান মুক্তিযুদ্ধ, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বাংলাদেশের সমাজ-সমকাল, প্রেম-দ্রোহ তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১) রচিত রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩) অসামান্য এক উপন্যাস। মহান মুক্তিযুদ্ধ এ উপন্যাসের বিষয়। বিশেষ করে একাত্তরের এপ্রিল থেকে জুন উপন্যাসটির রচনাকাল। তাঁর অন্য উপন্যাস নীড় সন্ধানী (১৯৬৮), নিষুতি রাতের গাথা (১৯৬৮)। সেলিনা হোসেন (জ. ১৯৪৭-) খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক। অসংখ্য উপন্যাসের স্রষ্টা। বাংলা উপন্যাস-ধারাকে সমৃদ্ধকরণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মুসলিম নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে প্রধানতম কয়েকজনের মধ্যে তিনি অন্যতম একজন। ‘তাঁর উপন্যাসে রাজনৈতিক সময় বা আন্দোলন অধিকতর পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করে। নারীর শাশ্বত দৃষ্টি, সনাতন আদর্শ বজায় থাকে তাঁর লেখায়।’২৭ নারী-যুগের প্রতিনিধি হিসেবেও তিনি বর্তমানকালে অভিহিত। তাঁর উপন্যাসে নারী নানামাত্রিকভাবে উপস্থাপিত। নারী-সমাজের প্রবল প্রতিনিধি হিসেবেই যেন দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর উপন্যাসে সেই সত্য বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন গবেষক সেলিনা হোসেনকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, ‘এই যে নারী-যুগের প্রতিনিধি, মানুষের প্রতিনিধি, বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় সামনের সারিতে চলমান, ইনি আজ আমাদের কথাসাহিত্যের এক সুদক্ষণা সারথি।’২৮ সেলিনা হোসেনের উপন্যাস যাপিত জীবন (১৯৮১), হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), চাঁদবেনে (১৯৮৪), পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬), কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯), কালকেতু ও ফুল্লরা (১৯৯২), খুন ও ভালোবাসা (১৯৯০), ভালোবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২), মগ্ন চৈতন্যে শিষ (১৯৭৯) নিরন্তর ঘণ্টাধ্বণি (১৯৮৭), উত্তর সারথি (১৯৭১), মোহিনীর বিয়ে (২০০২), মর্গের নীলপাখি ( ২০০৫), পূর্ণ ছবির মগ্নতা (২০০৮), লারা (২০০০) প্রভৃতি। সেলিনা হোসেন উপন্যাসে দেশভাগ, পাকিস্তানের দুঃশাসন, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাসখ্যাত বিভিন্ন সংগ্রামী ও বিপ্ল¬বী নারীচরিত্র, অবহেলিত-লাঞ্ছিত নারীদের জীবনচিত্রণ যেমন তিনি উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি চর্যাপদের কাহ্নপা ও শবরীও তাঁর উপন্যাসের বিষয়। বিষয় হয়ে ওঠে ফুল্ল¬রাও। শেকড় ও ঐতিহ্য-অনুসন্ধানী কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন তাঁর সৃষ্টিশীলতায় বিবিধ-নিরীক্ষায় নিজেই নিজের বৃত্ত ভেঙেছেন বারবার। তাঁর সৃষ্টি কথাশিল্পে এক নতুন দিক্বলয়ই শুধু তৈরি করে না, নিজস্ব একটি জগৎও তৈরি করে দেয়। ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংগ্রাম-বিপ্লব-প্রেম-দ্রোহ-বঞ্চনা-অধিকার সবকিছুকে তিনি শিল্পের রশ্মিতে বেঁধে অসাধারণ শিল্পকর্ম সাধন করেন। বাংলা উপন্যাসের ধারাকে বিষয়-বৈচিত্র্যে ও শিল্প-প্রকরণে সমৃদ্ধকরণে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।
দিলারা হাশেম (১৯৪৩—২০২২)) ঘর মন জানালা ( ১৯৬৫) উপন্যাসের জন্য সুপরিচিতি লাভ করেন। এ উপন্যাসটি একসময় পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। নাজমার জীবনের নানা বাঁক, দায়িত্বশীলতা, ভালোবাসার স্বপ্নভঙ্গ, ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অসম সম্পর্ক স্থাপন, প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দেয়া, ছোটবোনের জন্যে আত্মত্যাগ;এ উপন্যাসের উপজীব্য। বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনে লেখক যথেষ্ট সাহসী। শরীরী কামবাসনা যেমন সাবলীলভাবে এ উপন্যাসে উপস্থিত, তেমনি অর্থনীতি একটা সমাজ কিংবা পরিবারকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তার স্পষ্ট ছবি এ উপন্যাস। মানুষের বাঁচাটাই যে বড় সত্য, যে-কোনো ভাবেই সে বাঁচতে চায়, যেভাবে নাজমা সর্বক্ষেত্রে পরাজিত হলেও বাঁচার লড়াই ঠিকই সে ধরে রাখে, যেখানে আত্মসম্মান বিকিয়ে দিয়ে দ্রুত সাফল্যের সিঁড়ি ধরতে চেয়েছে। সেটি সে করেছেও। চাকরিতে দ্রুত উন্নতির ক্ষেত্রে তা লক্ষণীয়। পরিবারের অর্থনৈতিক দৈন্য-সমাজের ভেতর বাহির-নাগরিক জীবনের কদর্যতা-একাকীত্ব-যৌনতা-ব্যক্তি জীবনে বহুমুখি ঘাত-প্রতিঘাত ঘর মন জানালায় শিল্পশৈলীতে উপস্থাপিত। লেখকের গদ্যটা বেশ চমৎকার। যে কারণে পাঠক তৈরিতে তাঁর পথটা বেশ সুগম হয়েছে বলে অনুমিত। দিলারা হাশেমের অন্য উপন্যাস একদা এবং অনন্ত (১৯৭৫), স্তব্ধতার কানে কানে (১৯৭৭), আমলৌকির মৌ (১৯৭৮)। মধ্যবিত্ত পরিবারের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, বঞ্চনা-উপেক্ষার যন্ত্রণা এবং সবকিছুর পরও জীবনকে এগিয়ে নেয়া, জীবন-সংগ্রামে নিরন্তর লড়াই তাঁর উপন্যাসের বিশেষ মাত্রা বহন করে। সমাজ-পরিবারের নির্মম ও রূঢ় বাস্তবতাকে ঘিরেই তাঁর উপন্যাস নির্মিতি লাভ করে।
মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনদ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের মানুষের আত্মিক সংকট, প্রেম-পরকীয়া, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্যে বিখ্যাত জনদের জীবনভিত্তিক কাহিনি;এসব বিষয়কে উপজীব্য করে উপন্যাস লিখেছেন হাসনাত আবদুল হাই (জ. ১৯৩৯-)। তাঁর সুপ্রভাত ভালবাসা (১৯৭৭), মহাপুরুষ (১৯৮২), নভেরা (১৯৯৫), সাঁতারু ও জলকন্যা (১৯৯৯) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) বাংলা সাহিত্যে শক্তিমান ঔপন্যাসিক। তাঁর অসংখ্য উপন্যাস ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। শিল্পমানেও তাঁর উপন্যাস অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। তাঁর গদ্য কাব্যিকগুণে অসাধারণত্ব লাভ করে। একারণে তাঁর উপন্যাস পাঠকের কাছে বিশেষ মর্যাদা বহন করে। তাঁর অনুপম দিন (১৯৬২), নিষিদ্ধ লোবান (১৯৮১), এক মহিলার ছবি (১৮৫৯), জনক ও কালো কফি (১৯৬২), সীমান ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৩), অন্য এক আলিঙ্গন (১৯৮২), এক যুবকের ছায়াপথ (১৯৮৭), নারীরা (১৯৯৯) প্রভৃতি উপন্যাস মুসলিম-রচিত উপন্যাসের ধারাকেই শুধু সমৃদ্ধ করেনি, বাংলা উপন্যাসে অসামান্য অবদান হিসেবেও বিবেচিত। ‘প্রধানত বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্রম-উত্তরণ ও রূপান্তরের পর্বটি অঙ্কন করেন সৈয়দ শামসুল হক। এক্ষেত্রে শহর কিংবা গ্রাম দুই’ই তাঁর বিষয়বন্দি হয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে ক্রমবিকশিত মধ্যবিত্তের মনোজগত, বিকারগ্রস্ততা, যৌনতা, অচরিতার্থতা, স্ববিরোধিতা বিচিত্রভাবে নিরীক্ষিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।’২৯
হুমায়ুন আজাদের উপন্যাস বোদ্ধা ও মুক্তচিন্তার পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, প্রথাবিরোধী চিন্তা, অসুস্থ রাজনীতি, যৌনতা, আমলাদের চরিত্রবিন্যাস, নারীর স্বাধীনতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার নানা বিষয়কে তিনি উপন্যাসে তুলে এনেছেন। তাঁর উপন্যাস ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল (১৯৯৪), সবকিছু ভেঙে পড়ে (১৯৯৫), মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ (১৯৯৬), পাক সার জমিন সাদ বাদ (২০০৪) প্রভৃতি।
শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) যদি উত্তরের খেপ (১৯৯১) রচনার আগে-পরে আর কোন উপন্যাস নাও লিখতেন, তাহলেও শুধু এই একটিমাত্র উপন্যাসের জন্যেই বাংলা উপন্যাসে তাঁর আসন স্থায়ী হয়ে থাকতো। যদিও তাঁর আরো বিখ্যাত উপন্যাস রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে শওকত আলী বিখ্যাত কথাশিল্পী। তাঁর ওয়ারিশ (১৯৮৯), দলিল (২০০০), সম্বল (১৯৮৬), গন্তব্য অতঃপর (১৯৮৭), ভালোবাসা কারে কয় (১৯৮৮), যেতে চাই (১৯৮৮), বাসর ও মধুচন্দ্রিমা (১৯৯০), বসত (২০০৫) প্রভৃতি। ঔপন্যাসিক হিসেবে রাবেয়া খাতুন বিশিষ্ট। তাঁর অনেক বিখ্যাত উপন্যাস রয়েছে। মধুমতী (১৯৬৩), রাজারবাগ শালিমারবাগ (১৯৬৯), ফেরারী সূর্য (১৯৭৫), মেহের আলী (১৯৮৫), মন এক শ্বেত কপোতী (১৯৬৫), অনেকজনের একজন (১৯৮৬), জীবনের আর এক নাম দিবস রজনী (১৯৮০) প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস।
জনপ্রিয়তার রাজপুত্র হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)। মুসলমান লেখকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ নজিবর রহমান এবং আকবর হোসেনের পর হুমায়ূন আহমেদ বাঙালি পাঠকসমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাঠকসৃষ্টিতে হুমায়ূন আহমেদ নিজেকে অসামান্য করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাস ব্যাপকভাবে পাঠকনন্দিত। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যা পাঠক হৃদয়কে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধকেও তিনি উপন্যাসের বিষয় করে অসাধারণ উপন্যাস জোছনা ও জননীর গল্প (২০০৪) লিখেছেন। হুমায়ূন আহমেদ ব্যাপক পাঠকনন্দিত হলেও তাঁর উপন্যাসের অবকাঠামো ও শিল্পমানে শৈথিল্য আছে। তাঁর নন্দিত নরকে (১৯৭৩), শঙ্খনীল কারাগার (১৯৭৩), শ্যামল ছায়া (১৯৭৪), আমার আছে জল (১৯৮৫), আগুনের পরশমনি (১৯৮৬), এইসব দিনরাত্রি (১৯৮৬), কোথাও কেউ নেই (১৯৯০), অয়োময় (১৯৯০), মিসির আলীর অমীমাংসিত রহস্য (১৯৯২), হিমু (১৯৯৩), জলজোছনা (১৯৯৩), শ্রাবণ মেঘের দিন (১৯৯৪), লীলাবতী (২০০৫), লেলুয়া বাতাস (২০০৬) প্রভৃতি উপন্যাস অবিশ্বাস্যরকম পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এখনো ব্যাপকভাবে তাঁর উপন্যাস পঠিত হচ্ছে। তিনি নিজেই বিশাল এক পাঠকসমাজ সৃষ্টি করে অনন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
‘বাংলাদেশের উপন্যাসে অনিবার্য ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩Ñ১৯৯৭)।’৩০ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬)। ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনীতি, শ্রেণিদ্বন্দ্ব, প্রেম-বাৎসল্য-মাতৃত্ব-কামনা-বাসনা, পুঁজিবাদ, পাকিস্তানের স্বপ্ন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তেভাগা, সংখ্যালঘু সঙ্কট, হিন্দু-মুসলিম মনস্তত্ত্ব উপন্যাসের বিষয় করেছেন তিনি।
রিজিয়া রহমান (১৯৩৯Ñ২০১৯) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উত্তর পুরুষ (১৯৭৭), বং থেকে বাংলা (১৯৭৮), সবুজ রক্ত (১৯৮১), ধবল জ্যোৎস্না (১৯৮১), অলিখিত উপন্যাস (১৯৮০), প্রেম আমার প্রেম (১৯৮৫), ঝড়ের মুখোমুখি (১৯৮৬) প্রভৃতি। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিচিত্র। পর্তুগিজ, বাংলাদেশের জাতিত্ব ও নৃতত্ত্ব, চা বাগানের কাহিনি, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নীলচাষ বিভিন্ন বিষয় উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করে তিনি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন।
জনপ্রিয়তার বিচারে হুমায়ূন আহমেদের পরেই যে নামটি আসে, তিনি ইমদাদুল হক মিলন (জ. ১৯৫৫)। বাংলা উপন্যাসে তাঁরও রয়েছে বিশাল পাঠকগোষ্ঠী। জনপ্রিয় ধারার ঔপন্যাসিক হলেও ইমদাদুল হক মিলন উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্ণয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সতর্ক ও সচেতন। শিল্পমানেও অনেক উপন্যাসেই দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। সুবৃহৎ কলেবরের নূরজাহান তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসে তাঁর শিল্পমেধার অসাধারণত্ব লক্ষণীয়। কালোত্তীর্ণ উপন্যাসের মর্যাদায় এ উপন্যাসটি অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস ও রাধা ও কৃষ্ণ (১৯৮২), ভালোবাসার পাশেই (১৯৮৯), উপনায়ক (১৯৯০), প্রতিনায়িকা (১৯৮৮), পরকীয়া (১৯৮৯), রূপনগর (১৯৮৮), ভালোবাসা ভালো নয় (১৯৮৯), প্রিয়দর্শিনী (১৯৯১), মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস (১৯৮৯), লাইলী (১৯৯১) প্রভৃতি পাঠকপ্রিয় উপন্যাস। শহীদুল জহির অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসের ঢংটি আলাদা। তাঁর উপন্যাস সে রাতে পূর্ণিমা ছিল (১৯৯৫), মুখের দিকে দেখি (২০০৬) প্রভৃতি। এ সময়ে আনিসুল হক (জ. ১৯৬৫) উপন্যাস রচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে তাঁর উপন্যাস। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস মা (২০০৩)। বলা যায়, তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের একটি বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিস্তৃত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদ ও তাঁর মায়ের জীবনের মর্মস্পর্শী ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। আয়েশামঙ্গল (১৯৯৮) ও যারা ভোর এনেছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।
আতা সরকার (জ. ১৯৫২) বহুদিন ধরে উপন্যাস লিখছেন। বহুমাত্রিক লেখক হলেও ঔপন্যাসিক হিসেবেই সুপরিচিত তিনি। বাংলাদেশের সাহিত্যসমাজে আতা সরকার বর্তমানে বিশিষ্ট একটি নাম। ছোটগল্পকার হিসেবেও তাঁর অবস্থান শক্ত। আতা সরকারের উপন্যাসের ধরন, বিষয়বস্তু, দর্শন, সমাজ-কালচেতনা, শিল্প এবং দর্শনের ব্যাপারটি স্পষ্ট এবং সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ থেকেই এসবের সৃষ্টি ঘটেছে তা অনুমানযোগ্য। কারণ দেশ-রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ না থাকলে এ ধরনের উপন্যাস লেখা সহজতর নয়। তিতুর লেঠেল (১৯৮৭), আপন লড়াই (১৯৮৮), একদা অনঙ্গ বউ (১৯৯০), চারদিক বৃষ্টি (১৯৯০) এবং সোনাই সরদারের ঢাকা অভিযান (২০০১) প্রভৃতি উপন্যাস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আতা সরকারের উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে রাজনীতি, দেশাত্ববোধ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রেম-দ্রোহ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পারিবারিক নানান অসংগতি স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস বিশেষ কিছু মেসেজকেন্দ্রিক নির্মিত। তাঁর উপন্যাসে জীবনদর্শন আছে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে, রাজনীতির নির্মম ভয়াবহতা, মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, টানপোড়েন, প্রেম-অভিমান, আত্মদংশন-আবেগ আছে। তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে অত্যন্ত সচেতন এবং কোনো উপন্যাস রচনার আগেই মস্তিস্কে যেন এটি সাজিয়ে নেন। তারপর প্রসব করেন সযত্নে, সাবধানে। সেকারণে তাঁর উপন্যাসে মূল বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে অনেক উপকাহিানর সংযুক্ততা ঘটে। যা একবারেই বাস্তবতা থেকে সংগৃহিত। যেন স্পর্শ করেই তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা আমাদের সমাজেরই লোক, আমাদের অত্যন্ত চেনা;তবে এই চেনা লোকগুলোরই কেউ কেউ সাংঘাতিকরকম ভয়ঙ্কর, আর কেউ আমাদের কল্যাণকামী, দেশ-জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ। এ থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি, আতা সরকারের উপন্যাসের বিষয়বস্তু কল্পনাপ্রসূত নয়; তাঁর দেখা-জানা-চেনা-অভিজ্ঞতাপ্রসূত, কখনো ইতিহাসাশ্রিত।
বর্তমানে জাকির তালুকদার (জ. ১৯৬৫) উপন্যাস সাহিত্যে জনপ্রিয় একটি নাম। তাঁর মুসলমানমঙ্গল পাঠিকনন্দিত উপন্যাস। এছাড়াও তাঁর পিতৃগণ, হাঁটতে থাকা মানুষের গল্প উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মনি হায়দার (জ. ১৯৬৮) ঔপন্যাসিক হিসেবে এ সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর আমার বীনু খালা, একািট খুনের প্রস্তুতির বৈঠকের পর, নায়ক ও নায়িকারা, মেয়েটি সমুদ্রে ডুবে যেতে চেয়েছিল, কিংবদন্তির ভাগীরথী প্রভৃতি উপন্যাস পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
মুসলিম ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আরো অনেক লেখকই আছেন, অনেক তরুণও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস লিখছেন। তাঁদের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধির ধারায় এঁদের অনেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে ভূমিকা রাখতে পারছেন। এঁদের স্মৃষ্টিকর্ম প্রবহমান রয়েছে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মুসলিম লেখকদের সফল যাত্রার পথিকৃত মীর মশাররফ হোসেন। এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেক মুসলিম লেখক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অনেক লেখকের নাম আনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁদের অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা উপন্যাসের বিকাশে তাঁদের বিশেষ অবদান সবসময়ই স্বীকৃত হবে।
বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় উপন্যাসের ঐতিহ্য নির্মাণে মুসলিম ঔপন্যাসিকবৃন্দ অনেকটা পথ অতিক্রম করেছেন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, the aesthetic and the intellectual, the desire for beauty and the desire for truth৩১ নির্মাণে আসে জনপ্রিয়তা এবং সেটি একটি লক্ষ্য । এক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেন থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে উপন্যাসধারা রচিত হয়েছে তা একক বা শুধুমাত্র কোনো বিশেষ ধর্মের লেখকের হাতে নয়, বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে তা বয়ে চলছে। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার কথা অপরিহার্যভাবে স্মরণযোগ্য। জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রটি নির্ধারণে প্রধানত রচনার সৌকর্য, চরিত্র চিত্রণের মুন্সিয়ানা কিংবা জীবনদর্শনের ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। বিষাদ-সিন্ধু কেন জনপ্রিয় তা তার আবহ পড়লেই জানা যায়।
জনপ্রিয়তার সুরটি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। একইভাবে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কারণও অনুসন্ধান করলে তাঁর সাহিত্য ভাবাবেগ, উচ্ছৃখলতা কিংবা আবেগের সুনির্দিষ্ট প্রবাহ বিশে¬ষণে আসে। যেমন, হুমাযুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) বলেন:
শরৎচন্দ্র যে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক, এ কি এমনিই হয়েছে! বাংলাদেশে তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে এবং তাঁর চেয়ে আর কারুকে সে এত ভালোবাসতে পারেনি। তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে যে ক্রটি আছে, তার কল্পনা যে স্থানে স্থানেদুর্বল হয়ে পড়ছে, তাঁর মধ্যে যে ভাববিলাসিতা স্থান পেয়েছে, মাঝে মাঝে বুদ্ধিও দীপ্তিতে যে তাঁর বিচারবোধ ঘোলাটে হয়ে গেছে, এসবই সত্য। কিন্তু তাঁর এবস ত্রুটির কথা আমরা ভুলে যাই, বাংলাদেশ ও তার জনসাধারণের প্রতি তাঁর অন্তরে গভীর দরদের কথা ভেবে। সত্যিই তিনি বাংলাদেশকে ভালোবেসেছিলেন, আর বাংলাদেশও তাঁকে তেমনি ভালোবেসেছে।… তিনি নতুন করে বাংলাদেশকে আবিষ্কার করেছিলেন সাধারণ মানুষের জন্যে এবং সেই আবিষ্কারের মধ্যে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তাঁর মধ্যেই প্রথম উদ্ঘাটিত হয়ে উঠেছিল কি বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তিনিই প্রথম এটা হৃদয়াঙ্গম করেছিলেন যে বাঙালী জীবনের বাহ্যিক একঘেয়ামীর অন্তরালে প্রেম ও বিতৃষ্ণা, আশা ও নৈরাশ্য, সুখ ও দুঃখ কি-ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে।৩২
এভাবেই একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের মানদণ্ডটি চেনা সম্ভব। জনপ্রিয়তার সূত্রটিও সেভাবেই অগ্রসর হয়। বাংলা উপন্যাসে মুসলিম লেখকদের মধ্যে মীর এ পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী । এরপর নজিবর রহমান এবং পরবর্তীতে আকবর হোসেন। কিন্তু এঁদের বাইরেও অনেক মুসলিম লেখক উপন্যাস রচনা করলেও তেমনভাবে উপন্যাসের ক্ষেত্রটিতে পৌঁছাতে সক্ষম হননি। কারণ, আগেই বলা হয়েছে বাঙালি মুসলমানদের উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সংস্কার ও বিশ্বাসে যেমন আড়ষ্টতা তেমনি ভাষা বিষয়েও ছিল তাদের অস্পষ্টতা। এসব পেরিয়ে নজিবর রহমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বেশ জনপ্রিয় হন আনোয়ারা রচনার জন্য । এর ভেতর দিয়ে জনপ্রিয়তার ধারাটি নজরে আসে। আনোয়ারা মুসলিম পারিবারিক জীবনাগ্রহ নিয়ে রচিত কিন্তু সে উপন্যাসে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তির ভেতরের প্রবৃত্তি, নানারকম সম্ভাব্যতার বিচার পাঠকের সামনে নিয়ে আসে। এর পর ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রতিক্রিয়াশীলতার সাহিত্য করেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে উপন্যাসের যুগ। সমাজ ভেঙে গেছে, একান্নবর্তী পরিবার বিচ্ছিন্ন, গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরমুখো, নাগরিক আস্বাদ, রাজনীতি বিষয়ে হয়েছে সচেতন, নির্বাচন করছে নিজস্ব নেতা ইত্যাদির ভেতরে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনা জন্ম নিয়েছে। ‘মূলত আধুনিক যুগেই জন্ম এবং আধুনিকতার যুগ মহিমায় উপন্যাসের পরিপুষ্টি বলেই এখানে অভিব্যক্ত চরিত্রাবলি যুগের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে মূর্ত হতে পেরেছে।’৩৩
ফলে উপন্যাস জনপ্রিয় হবে বা উপন্যাসের মতো ফর্ম পাঠকের আগ্রহের বস্তু হবে তা আর নতুন কী। সে পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে শরৎচন্দ্র অন্যদিকে মুসলিম বাঙালিরা উপন্যাস রচনায় এগিয়ে আসতে পারলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁদের শিল্পক্ষুধাও ছিল প্রবল। ফলে উপন্যাসের যুগে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়ে বাঙালি মুসলমানরাও হিন্দুদের পাশাপাশি অনেকটা নিজেদের চিনে নিতে সক্ষম হলেন। সে কারণেই তাঁদের লেখায় আড়ষ্টতা থাকলেও প্রেম, যৌনতা, রাজনীতি, শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। একইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রতিক্রিয়ার উপন্যাস লিখে বেশ জনপ্রিয় হলেন। আর আকবর হোসেনের প্রচণ্ড সততার সঙ্গে জীবনের ভিতর পর্যবেক্ষণে সমাজের ভেতরের স্বরূপকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে পরীক্ষায় নামলেন। উপন্যাসকে শিল্পবোধে আরো অনেক পথ এগিয়ে দিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন, শহীদুল জহির প্রমুখ। আর জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে আকবর হোসেনদের উত্তরসূরী হয়ে ওঠেন হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, আনিসুল হক প্রমুখ। অনেক মুসলিম লেখক সমাজের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, এখনো লিখছেন। সামাজিক বৈষম্য, বংশাভিমান, ভেদবিরোধী ব্যাপার, পীরপ্রথা, অলৌকিকতা, ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃৃতি, অস্পৃশ্যতা, ধর্মান্ধতা, অবরোধ, নারীনির্যাতন, প্রণয়বীক্ষা এমন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিংশ শতাব্দীর মুসলিম লেখকরা নানা মাপের উপন্যাস লিখে জনপ্রিয় হয়েছে। পরকীয়া, ধর্মান্ধতা, মনস্তত্ত্ব বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হয়েছে মুসলিম লেখকেদের উপন্যাসে। এরপর বিষয়বস্তুতে রাজনীতি, ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কুসংস্কার, যৌনতা, নারীর অধিকার, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক উপন্যাসের বিষয় করে জনপ্রিয়তা অর্জনে মুসলিম লেখকদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতাব্দীতেও সেই ধারাবাহিকতায় প্রবহমান রয়েছে উপন্যাস সাহিত্যে। এর ভেতর দিয়েই চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা—উপন্যাসে নিশ্চয় বাঁক পরিবর্তন ঘটবে, যুক্ত হবে আরো নতুন নতুন বিষয়, শিল্পে আসবে আরো অভিনবত্ব। জনপ্রিয়তায় আরো বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে উপন্যাস সাহিত্য।
তথ্যনির্দেশ
১.অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ৯
২.তদেব, পৃ. ৯
৩. জুলফিকার মতিন, সমাজ ও সাহিত্য : আধুনিকতা অর্জনের ধারা, (ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৬৯
৪. শ্রীভূদের চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৯৮৫), পৃ. ১৮৭
৫. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ,(কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি., ১৯৮৭),পৃ.৪৬-৪৭।
৬. জুলফিকার মতিন, সমাজ ও সাহিত্য : আধুনিকতা অর্জনের ধারা, (ঢাকা: ২০০১), পৃ. ১১।
৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮), পৃ. ২১।
৮. হুমায়ুন কবির খোকন, সম্প., শিল্পকণ্ঠ, ঈদসংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, ঢাকা, পৃ.১৪৮।
৯. শামসুন নাহার জাহান, সম্পা., শেখ ফজলল করিম রচনাবলী, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ৩৫।
১০. আবদুল কাদির, সম্পা., শিরাজী রচনাবলী, উপন্যাস খণ্ড, (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ৮৭।
১১. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, অবরোধ-বাসিনী, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬), পৃ. ৩৯।
১২. আলাউদ্দিন আল আজাদ, সম্পা., বন্দে আলী মিয়া রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৯৭।
১৩. আবদুল কাদির সম্প., ‘রায়হান’, লুৎফর রহমান রচনাবলী, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭২), পৃ. ২৪৭-২৪৮।
১৪. মোহাম্মদ নজিবর রহমান, আনোয়ারা, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা,২০০৫, পৃ. ৫২।
১৫. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), পৃ. ২৮৯।
১৬. মোহম্মদ নজিবর রহমান, ‘উৎসর্গপত্র’, আনোয়ারা।
১৭. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান, (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৩), পৃ. ২৫৪।
১৮. কাজী নজরুল ইসলাম, কুহেলিকা, তৃতীয় সং., (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪১৬), পৃ.১৬।
১৯. আবুল ফজল, চৌচির, (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৭৭), পৃ. ৬৭।
২০. ড কাজী মোতাহার হোসেন, অবাঞ্ছিত, ঊনবিংশ সং. (ঢাকা: জাহাঙ্গীর ব্রাদার্স, ১৯৯৩), ‘ভূমিকা’।
২১. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯), পৃ. ১৫৪।
২২. শওকত ওসমান, জননী, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ২০০৬।
২৩. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৫৬।
২৪. তদেব, পৃ. ১৫৬।
২৫. তদেব, পৃ. ১৭৩।
২৬. শাফিক আফতাব, পাঁচ দশকের বাংলা জনপ্রিয় উপন্যাস, (ঢাকা: গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন, ২০১৫), পৃ. ৭১।
২৭. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৯৭।
২৮. চন্দন আনোয়ার, সম্পা., ‘গল্পকথা’ (সেলিনা হোসেন সংখ্যা), রাজশাহী, ২০১৫, পৃ. ৫৩।
২৯. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৭৭
৩০. তদেব, পৃ. ২১৪।
৩১. Robert Scholes & Robert Kellogg, The Nature of Narattive, Oxford University Press, London, ১৯৬৮, ঢ়.১০৫.
৩২. হুমায়ুন কবির, শরৎসাহিত্যেও মূলতত্ত্ব, উত্তরণ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৫।
৩৩. অনীক মাহমুদ, আধুনিক সাহিত্য: পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২৪।