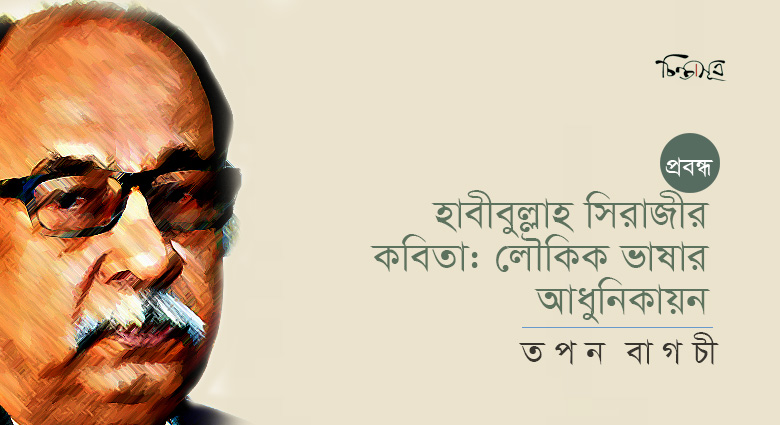 নতুন শতকের এসে কবিতার বইয়ের নাম হয়, ‘মুখোমুখি’ (২০০১), ‘হ্রী’ (২০০৫), ‘জো’ (২০১৭), সুভাষিত (২০১৯), ‘ঈহা’ (২০১৯)। রবীন্দ্রকাল পেরিয়ে তিরিশি আধুনিকতার পরে একশব্দের কাব্যনামে আধুনিকতা বজায় রাখা রীতিমতো ঝুঁকির বিষয়। সেই ঝুঁকিটিই গ্রহণ করেছেন কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী।
নতুন শতকের এসে কবিতার বইয়ের নাম হয়, ‘মুখোমুখি’ (২০০১), ‘হ্রী’ (২০০৫), ‘জো’ (২০১৭), সুভাষিত (২০১৯), ‘ঈহা’ (২০১৯)। রবীন্দ্রকাল পেরিয়ে তিরিশি আধুনিকতার পরে একশব্দের কাব্যনামে আধুনিকতা বজায় রাখা রীতিমতো ঝুঁকির বিষয়। সেই ঝুঁকিটিই গ্রহণ করেছেন কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী।
‘জো’ কাব্য আমার হাতে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘তুমি তো আমাগো ফরিদপুইরা, ভাষাডা খেয়াল কইর্যা পইড়ো। দেইখো ঠিক আছে কি না।’ ‘আবিষ্কার’ প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান থেকে বছর চারেক আগে। কবি আবু হাসান শাহরিয়ারকে উৎসর্গ করা এই কাব্য ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। পল্লিকবি জসীমউদ্দীন ফরিদপুরের আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিংবা তার কাব্য থেকে আমরা যে আঞ্চলিক শব্দ পাই, তা ফরিদপুরের, কিন্তু গোটা একটি কাব্য তিনি আঞ্চলিক ভাষায় লেখেননি।
অথচ হাবীবুল্লাহ সিরাজী ‘জো’ লিখেছেন ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষায়। কেবল ভাষা-ই নয়, আঞ্চলিক বিষয়-অনুষঙ্গও ফরিদপুরের। তার চেয়ে বড় কথা আঞ্চলিক তথা গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেও এটি আধুনিক কাব্য। এই শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা খুব কম কবিরই থাকে! সিরাজীর আছে সেই ক্ষমতা। আরেকটি কথা, উত্তরাধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে যারা গলদঘর্ম হয়েছেন, তারা এই কাব্যকেও তাদের টেক্সট হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।
নদীমাতৃক বাংলাদেশে পালগুড়া শব্দটি দারুণ প্রতীকী। কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী তাই শব্দটিকে দস্তুরমতো প্রয়োগ করতে পেরেছেন। জীবন যে দমেরই খেলা, কবি তা জানতেন।
৫০টি কবিতা। শিরোনাম ক্রমানুসারে বর্ণভিত্তিক। অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দুও বাদ যায়নি। অবাক করা বিষয় হলো, এটি কেবল কবিতার ক্রম-প্রকাশক নয়, তিনি কবিতার বিষয় ‘অ’ বলেই নাম রেখেছেন‘অ’। বিসর্গ নিয়ে কবিতা লিখেছেন বলেই কবিতার নাম হয় (ঃ)। বইয়ের বাইরে বাংলাভাষার প্রতিটি বর্ণকে নিয়ে কবিতা লেখার কৃতিত্ব মনে হয় একমাত্র হাবীবুল্লাহ সিরাজীর। ‘অ’ নিয়ে তার কবিকাংশ উদ্ধার করা যেতে পারে:
দোয়াত উল্টাইয়া গেলে স্বরে-অ তাকায়,
মধুসূদন আইস্যা যদি দুয়ারে খাড়ায়;
আসমান বইল্যা কথা, পঞ্চবটি রইল পাতা
কপোতাক্ষে ফাইস্যা গ্যাছে রাবণের মাথা।
(পৃ. ০৭)
প্রতিটি কবিতাই ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত। আঞ্চলিক ভাষার শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে তিনি প্রথাসিদ্ধ ছন্দ বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক উচ্চারণের শিথিলতা, সংকোচনতা ও প্রসারণতাকে কাজে লাগিয়েছেন। আর অনিবার্য আঞ্চলিক শব্দটি পর্বমধ্যে ধারণ করতে গিয়ে তিনি মধ্যখণ্ড করেছেন অজস্রবার। এসবই তার সচেতন প্রয়োগ। কাব্যের প্রথম চারচরণের পর্ববিন্যাস করে দেখানো যেতে পারে:
দোয়াত(অ) উল্/টাইয়া গেলে/ স্বরে-অ তা/কায়, ৪+৪+৪+১
মধুসূদন/ আইস্যা যদি/ দুয়ারে খা/ড়ায়; ৪+৪+৪+১
আ(আ)সমান/ বইল্যা কথা,/ পঞ্চবটি/ রইল পাতা/ ৪+৪+৪+৪
কপোতাক্ষে/ ফাইস্যা গ্যাছে/ রাবণের(অ)/ মাথা। ৪+৪+৪+২
এই কবিতা স্বরবৃত্তে পাঠ করতে পারি। আঞ্চলিক উচ্চারণের শিথিলতাকে কাজি লাগিয়ে আমরা একে অক্ষরবৃত্তেও পাঠ করতে পারি ভিন্ন বিন্যাসে। যেমন পরে ‘আ’ কবিতাটিই:
স্বরে-আ লইয়্যা ঘাড়ে/ দাবডাইলে পালা ৮+৬
নানা ভাণ্ড গয়রহ/ পবেন বেতালা ৮+৬
চলনে-বলনে ঠাট/ উদলা সিনান ৮+৬
পালগুরা ধইরা আছে/ গুরুর আসান। ৮+৬
(আ, পৃ. ৮)
আমরা এই কাব্যের আলোচনায় ছন্দের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে কিংবা এড়িয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকেও আধুনিক কবিতার কাতারে প্রকাশ করতে কবি কতটা মূলানুগ হয়েছেন, সেটি বোঝাতেই এই প্রচেষ্টাটুকু নিতেই হলো।
দেখুন ‘পালগুরা’ শব্দটি। তার সমসাময়িক দশকের আরেক শক্তিমান কবি হুমায়ুন আজাদ তার ‘নৌকো’ কবিতায় লিখেছেন, ‘পালগুড়া ধরে আছে বায়ুমন্ত্র, গতি প্রগতিতে কাঁপে সন্মুখ গলুই / দীর্ঘ জলে ভেসে যায় শিল্পময় তীক্ষ্ণ তীব্র ক্ষিপ্র রুই মাছ।’ আবার আব্বাসউদ্দীন আহমেদের কণ্ঠে শুনতে পাই, ‘আমার দয়ালগুরু বইস্যা আছে পালগুরারই নিচে’।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে পালগুড়া শব্দটি দারুণ প্রতীকী। কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী তাই শব্দটিকে দস্তুরমতো প্রয়োগ করতে পেরেছেন। জীবন যে দমেরই খেলা, কবি তা জানতেন। তাই তিনি সহজেই বলতে পারেন:
পাঁচ নম্বর স্বরের লগে বইস্যা আছে তিন
উই যদি পোকা হয় তয় মুইও মানুষ
ভুস হইয়া আছি, দম গ্যালেই ঠুস
কাজী সাবে ধরাইবেন সইলত্যা ছাড়া কুপি
(উ, পৃ. ১১)
এখানে সইলত্যা ছাড়া কুপিকে না চিনতে পারলেও ‘দম গ্যালেই ঠুস’ ঠিকই বুঝতে পারি। তার আগেই তার আত্মবিনয় ঝরে পড়ে ‘উই যদি পোকা হয় তয় মুইও মানুষ’ কথার মাধ্যমে।
লালনের অচিন পাখির সন্ধান এখনো থামেনি, এমনকি জীবনানন্দের ‘রোদের গন্ধ’ টের পেতেও আমাদের অনেক সময় পার করতে হয়েছে, হাবীবুল্লাহ সিরাজীর অনেক কবিতার অর্থ বুঝতেও হয়তো আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতে পারে। সেই দায় তো কবির নয়।
লক্ষ করতে পারি এই কাব্যে আরে বেশ কয়েকটি কবিতায় তিনি মৃত্যুচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। পরিকল্পনা করে তো আর কেউ মরণের কবিতা লেখে না! ঘোরের মধ্যে এসেই যায় হয়তো:
১.
পতন ফতুর হইলে ধাক্কা মারে ঊ
হুমড়ি খাইয়া দেহখান পড়নের কালে
জনমের বাসনায় মাটি ডাইক্যা তারে কয়, হউক
তারপরও বিষয়-নিষ্পত্তি বড় বেতালা-বিষম
(ঊ, পৃ. ১২)২.
জসীমেরে কও একটা ঠিকা ঝি দিক
এ-র গতরে ত্যাল ঢাইল্যঅ রানব পুঁইশাক
লালে খাইব আর দ্যাখত কালা চোর
ডালিম গাছের তলে বান্ধান কব্বর!
((এ, পৃ. ১৪)৩.
যয়টা পোকার তয়টা মজলে ঘাস
বদলায় না ত’ লাশগলা হাঁসফাঁস
বাঁশের মাঁচায় মানা তোলে যদি খাল
আঁইটা রইটা ভাবেন শরৎকাল
(শ, পৃ. ৪৬)৪.
চন্দ্রে বিন্দু দিয়া চিতায় উঠলে জাল
তিতাসে ঝাঁপাইয়্যা পড়ে বর্ণের ছাওয়পাল
জুইতমতো রইতমাছ কাটতেছিল দাও
আউল্যা প্যাটে ধাক্কা মারে রই;-বিষ্টির ভাও
(ঁ, পৃ. ৫৬)
হাবীবুল্লাহ সিরাজীর এই কাব্য একেবারেই ভিন্ন স্বাদের। তিনি যে আধুনিক শব্দবন্ধে নিজস্ব এক কাব্যভাষা তৈরি করেছেন, এই কাব্যে তারাই স্বতন্ত্র উত্তরণ। লৌকিক ভাষাকেই তিনি আধুনিক অর্থে রূপদান করেছেন। তার সময়ের আরেক প্রধান কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ‘মৌলাধুনিকতা’ নামে যে প্রস্তাববনা তৈরি করেছিলেন, হাবীবুল্লাহ সিরাজীর কাব্যে পাই, তারই প্রায়োগিক শিল্পরূপ।
এই কাব্যের অনেক রূপকের অর্থ আমি বুঝে উঠতে পারিনি। অনেক প্রতীক রয়ে গেছে অধরা মাধুরী হয়ে। কিন্তু তিনি যে নতুন এক স্পন্দন সৃষ্টি করতে পেলেছেন, সেটি টের পাই। লালনের অচিন পাখির সন্ধান এখনো থামেনি, এমনকি জীবনানন্দের ‘রোদের গন্ধ’ টের পেতেও আমাদের অনেক সময় পার করতে হয়েছে, হাবীবুল্লাহ সিরাজীর অনেক কবিতার অর্থ বুঝতেও হয়তো আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতে পারে। সেই দায় তো কবির নয়। আমি ঠিক বুঝতে পারি, পাঠক হিসেবে আমাদের আরেকটু প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হলে হলে তার কবিতার পাঠও আমরা গ্রহণ করতে পারবো ঠিকমতো।
হাবীবুল্লাহ সিরাজী কবি। তার সময়ে উল্লেখযোগ্য কবি। জসীমউদ্দীনের যেমন ‘নকশীকাঁথার মাঠ’, সৈয়দ শামসুল হকের যেমন ‘পরানের গহীন ভেতর’, আল মাহমুদের যেমন ‘সোনালি কাবিন’, মুহম্মদ নূরুল হুদার যেমন ‘শুক্লা শকুন্তলা’, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর যেমন ‘মানুষের মানচিত্র’, কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজীরও তেমিন ‘জো’। লৌকিক ভাষার আধুনিক কাব্যরূপায়ণ হিসেবে এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

