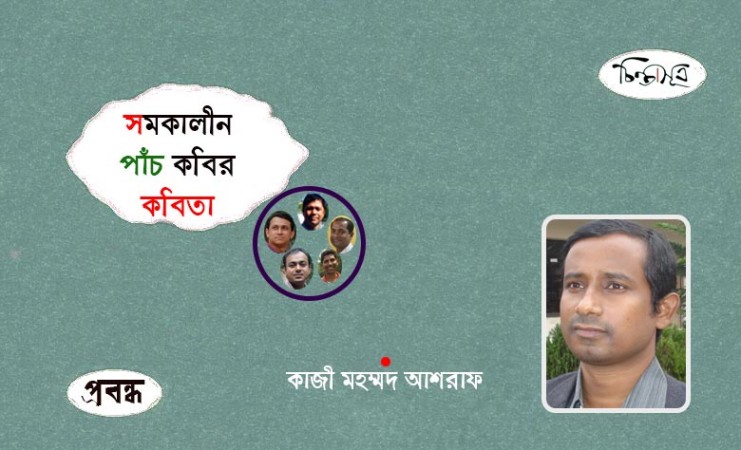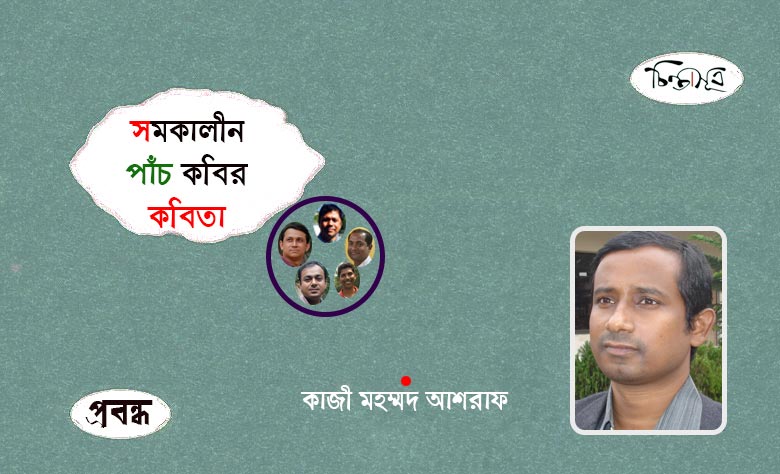একুশ শতকের সতেরো বছর চলে গেল। নতুন যুগের নতুন প্রজন্মের অনেক কিছুই নতুন। সাহিত্যের শাখাপ্রশাখা এর মধ্যে নতুন ফুলে-ফসলে ভরে উঠেছে। যতই ভরে উঠুক চিরন্তন বিষয়গুলো চিরন্তনই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ বা রবীন্দ্র-নজরুল-উত্তর আধুনিক কবিদের সাহিত্যের আদর-কদর কিছুই কমেনি। বরং প্রযুক্তির সুবিধায়, পুঁজির বিকাশে অতীতের অনেক কবির অখ্যাত, অজ্ঞাত রচনাবলিও এখন বাজারে উন্নত কাগজে ছাপা মোটা মোটা বই হয়ে বাজারে আসছে। এতে অধুনালুপ্ত বা বিলুপ্ত সাহিত্যের পরিমাণ কমে আসছে। সবই এখন বাজারে চলে আসার পথে আছে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে পিডিএফ ফাইল হয়ে পুরনো, দুর্লভ, বিলুপ্ত গ্রন্থাবলিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। পাঠকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কম্পিউটারে, ল্যাপটপে, নেটবুকে, ইবুক রিডারে; এমনকি মোবাইল ফোনের সেটে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে, পড়া যাচ্ছে। যে প্রজন্মকে আমরা বইবিমুখ বলি, তারাই তো এসব কাজে সম্পৃক্ত। এই তরুণরাই তো এসব ফাইল তৈরি করছে, ইন্টারনেটে আপলোড করছে, ডাউনলোড করছে, কপি করছে, শেয়ার করছে, সেভ করছে। তাহলে তারা কি পড়ছে না? না পড়লে প্রযুক্তির দৌড়ের এই ব্যস্ততম সময়ের ছেলেমেয়েরা কেন এসবের পেছনে সময় দিচ্ছে?
আবার নতুন প্রকাশকরা অজ্ঞাত, অখ্যাত বইপ্রকাশে ঝুঁকিও নিচ্ছে। ভারী ভারী বই অবলীলায় দেশের মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা হয়েই বইমেলায় চলে আসছে। রেয়ার বই হিসেবে এগুলোর প্রতি কৌতূহলী পাঠকের আকর্ষণও আছে। এখন আর তরুণরা পুরনো বইয়ের সন্ধানে কোনো প্রবীণ পাঠকের স্মৃতি, ব্যক্তিগত লাইব্রেরি বা কোনো বড় লাইব্রেরিতে যেতে আগ্রহী নয়। তাই বলে তারা বইবিমুখ হয়ে যায়নি। তারা প্রথমেই গুগলে সার্চ করে নেয়। না পেলে অনলাইনেই বন্ধুদের তার প্রয়োজনের কথা জানায় এভাবে শেয়ারিং হচ্ছে।
এভাবেই বইয়ের জগৎ বড় হচ্ছে। পাঠক সমৃদ্ধ হচ্ছে। লেখকদের পূর্বপ্রস্তুতি বা প্রিভিয়াস স্টাডির বোঝাও বড় হচ্ছে। এসময় যারা লিখছেন, তারা ক্ষীণদৃষ্টি নিয়ে পাঠের জগতে আসেন না। তবে ফেসবুকের মাধ্যমে সবাই তার নিজের কথা, কবিতা, ছবি, গান, গল্প, আবৃত্তি, ভিডিও ইত্যাদি সহজেই প্রকাশ করতে পারছেন। অনেকে ধারাবাহিক উপন্যাসও লিখছেন। স্বয়ম্প্রকাশিত এসব শিল্প সুসম্পাদিত না, সম্পাদিতও না। এগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই বর্জ্য। সব বর্জ্যই বর্জনযোগ্য, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে অনেক সময় মূল্যবান চামচ, চাকু বা ঘরের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু চাবি, আঙটি ইত্যাদি ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, সে বিষয়টি মাথায় রাখলে মূল্যবান, প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষণযোগ্য বস্তু নিজেরাই সঞ্চয়ে রাখতে পারি।
প্রকাশনার খরচ বেড়ে যাওয়া ও সম্পাদকদের পীর-মুরিদি সিলসিলার জটিলতায় অনেক তরুণই তার নতুন কবিতাটি নিয়ে পাঠকের কাছে যেতে পারছেন না। তাই বিকল্প ব্যবস্থায় ফেসবুকে নিজেই তা পোস্ট দিয়ে বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন। এটা খারাপ কিছু না। অনেক প্র্রবীণ লেখকও এই পথে এসেছেন বা আসছেন। প্রবীণদের অনেকে নিজে প্রযুক্তি বোঝেন না, ফেসবুক চালাতে পারেন না বলে নাতিনাতনি বা এই বয়সী তরুণতরুণীর সহযোগিতা নিয়ে চলে আসছেন পাঠক তথা ফেসবুক বন্ধুদের কাছে।
প্রযুক্তি বা প্রকাশনার সুবিধার এই যুগে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা প্রচুর। এদের মধ্য থেকে বাছাই করা কঠিন কাজ। প্রকাশিত গ্রন্থ বা ফেসবুকে বেশি অ্যাক্টিভ কবিদের কবিতা থেকে কষ্ট করে হলেও বেছে নিতে হয়।
এই আলোচনার লক্ষ্য— নতুন শতকে আবির্ভূত হয়েছেন এমন ৫ জন কবির কবিতা। তবে এখানে নতুন যুগের এই কবিদের কবিতার প্রধান প্রধান প্রবণতা চিহ্নিত করা, অঙ্গীকার আবিষ্কার করা বা নির্দিষ্ট মাপকাঠি দিয়ে ঠিকবেঠিক দেখার সুযোগ নেই। তবে একটি সাধারণ ধারণায় প্রবণতাগুলো দেখে নেওয়া যাবে।
॥দুই॥
১. এ সময়ের কবিরা শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের কবিতার পথ ছেড়ে নতুনত্বের প্রয়াসীরা জয় গোস্বামীর কাব্যরীতির দিকে ঝুঁকেছেন। এর প্রধান কারণ একঘেয়েমি থেকে মুক্তি। পূর্বজদের কবিতা নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু দিতে পারছিল না। এ সময়ের কবিদের তুলনায় এক প্রজন্মের পরের কবিরা অধিক প্রভাবশালী। তাই শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার বা উৎপলকুমার বসুর কাব্যরীতি থেকে সরে আসেন তরুণরা। পরের যুগের কবিদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকে আবুল হাসানের কিছু কবিতা। অন্যদের একেবারেই কম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরের প্রথম প্রজন্মের ও পরের প্রজন্মের কবিদের পথ থেকে একেবারেই সরে আসেন নতুন শতাব্দীর কবিরা। একমাত্র জয় গোস্বামীকে তরুণরা গ্রহণ করেন, তাই চেনাও সহজ হয়।
২. কবিতার শরীরে পরিবর্তন। যেমন: সাধুরীতির ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের ব্যবহার। এর কারণ লোকভাষারূপ তৈরি করে দেখানো। এ পদ্ধতিটা লোকভাষারূপ তৈরির প্রচেষ্টা। তবে সব কবির হাতে সাধুচলিত রীতির মিশ্রণ সার্থক হয়নি। অনেকের কবিতা পড়লেই বিরক্তির উৎপাদন হয়।
৩. কবিতাকে মুক্তি না দিয়ে খাঁচা থেকে বের করে যেন তাড়িয়ে দেওয়া। কবিতার শরীরকাঠামো ও ভেতরের অন্ত্রসমূহ এতটাই নতুনরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে যে, কবিতাকে পুরনো কাঠামোর খাঁচা থেকে বের করে যেন মুক্তি না দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকের কবিতা পড়ে এটাই মনে হয়। কোনও কিছুই আর তাদের হাতে থাকেনি। যেন সবটাই কবির নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তারা বুঝি শুধু কতগুলো অর্থহীন শব্দ সাজিয়ে সে শব্দগুচ্ছকে কবিতা বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন। তাদের কবিতা ভাবাবেগের শব্দ স্রোত ছাড়া আর কিছুই না।
৪. অব্যয়পদের ব্যবহার কমানো। যেথা, সেথা ধরনের সর্বনাম অনেক আগেই বাংলা কবিতা থেকে বিদায় হলেও কবিতার পঙ্ক্তিতে অনাবশ্যক অব্যয়পদের ব্যবহার এ সময়ের কবিতায় কমে এসেছে। তাই, যদি, কিন্তু, এবং, হয়তো, তবু ইত্যাদি বাক্যের জন্য প্রয়োজনীয় পদগুলো কবিতা থেকে অনেকটা দূর হয়েছে।
৫. বস্তু-অবস্তুর পার্থক্য হ্রাস করা। নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ ও উপস্থাপনায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করার জন্য কবিরা বস্তু ও অবস্তুর পার্থক্য কমিয়ে আনেন।
৬. নরত্বারোপ করা। বস্তু, বিষয় এবং অন্যপ্রাণীকে মানুষ, মানুষের বন্ধু কিংবা কথা বলা প্রাণী হিসবে ব্যক্তিত্ববান করে তোলা নতুন কাব্যরীতির অংশ।
৭. বাক্যরীতি থেকে বেরিয়ে শব্দকে স্বাধীনতা দান করা। যেমন: আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতার শর্ত লঙ্ঘন করা। এ সময় এসে কবিতার পরিভাষা ভেঙে নতুন করে গড়ে ওঠে। ইংরেজিতে অর্থপূর্ণ শব্দের সমষ্টিকে বলা হয় সেনটেন্স আর কবিতার বাক্যকে বলা হয় লাইন। তেমনি বাংলায় গদ্যের জন্য অর্থপূর্ণ শব্দের সমষ্টিকে বাক্য বলা হলেও কবিতার জন্য নির্ধারিত হয় ‘পঙ্ক্তি’ কথাটি। এর পরেই প্রশ্ন ওঠে সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো সার্থক পঙ্ক্তির জন্য শর্ত কি না। তরুণ কবিরা অস্বীকার করেন সেই ব্যাকরণগত শর্তসমূহকে। তাই বাক্যের উদ্দেশ্যবিধেয়, কর্তাকর্মক্রিয়া কিংবা আকাঙ্ক্ষা-আসত্তি-যোগ্যতা পদক্রমরীতি ভেঙে যায়। ফলে কবিতা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে থাকে। অনভ্যস্তের কাছে অপরিচিত মনে হয় বলে কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।
৮. পুরনো ধারার কবিরা এ সময় শামসুর রাহমান-আল মাহমুদীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্যাঁচালকেই কবিতা বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। এরা গৌণ হয়ে পড়েন। কবিতার মূলধারা থেকে দূরে থেকে কিছু কবি এ সময়ও সেই পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে, প্রেমের সাধারণ নাগরিক রূপ নিয়েই লেখেন। কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ঘটনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগতভাবেই উপস্থাপন করেন। এসব ঘটনার নান্দনিকতা অতি সামান্য, প্রায় নেই বললেই চলে। এসবে পাঠকের অংশগ্রহণ নেই। নতুন অর্থ, ব্যঞ্জনা কিছুই নেই। ফলে এরা দ্রুত গৌণকবি বলে চিহ্নিত হন। নতুন বিষয়বস্তু নতুন প্রকাশভঙ্গি দাবি করে। এরা সে দাবি অগ্রাহ্য করেন।
৯. ইংরেজি অথবা অন্য বিদেশি কবিতার পাঠকেরা ইংরেজি মাধ্যমে কবিতার ছন্দ ধরতে না পেরে ফ্রি ভার্স বা মুক্তক বা গদ্য ধরে নিয়ে প্রিপজিশন এবং আর্টিকেল ব্যবহার কমিয়ে বাংলায় ঐরূপ একটি গদ্য কাব্যভাষারীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বাক্যের শর্ত অস্বীকার করার পরে বিভক্তি ব্যবহারও হ্রাস পায়। এর ফলে কবিতা আরও অপরিচিত বলে মনে হতে থাকে পাঠকের কাছে। এ কারণে অনেকের কবিতা পড়লে বিদেশি কবিতার অনুবাদ বলে মনে হয়।
১০. নির্বিচারে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার। দক্ষ-অদক্ষভাবে নতুন শব্দবন্ধ বানানোর প্রয়াস। রবীন্দ্রযুগে বাংলা কবিতার শরীরজুড়ে দেখা গেছে সন্ধিবদ্ধ শব্দ। নজরুলের যুগে এসে দেখা যায় সমাসবদ্ধ পদের সমাহার। মাঝখানে কমে গিয়েছিল, নতুন শতাব্দীতে সমাসের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বাড়তে থাকে। সন্ধি ও সমাসের নির্দিষ্ট নিয়ম না জানার কারণে অদক্ষ হাতে তৈরি সমাসবদ্ধ পদগুলো হাস্যকর মনে হয়।
১১. প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন নতুন মিশ্র ক্রিয়াপদের ব্যবহার। কম্পিউটার-ইন্টারনেট মোবাইলসহ প্রযুক্তির সহজ ও সুলভ বিষয়গুলো জীবনযাপনের অনিবার্য অংশ হয়ে পড়ায় বাংলা প্রতিশব্দ বা পরিভাষা গড়ে ওঠেনি। চেষ্টা করলেও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তাই কবিরাও সহজভাবেই বিদেশি শব্দগুলো ব্যবহার করেন।
১২. লোকজ শব্দ ও অনুষঙ্গের ব্যবহার। বিশেষ করে বাউল মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণ। তবে বাউলতত্ত্বের দুরূহতা অনেককে বিভ্রান্তও করেছে। বাউল, সূফি, মারফতি, ভান্ডারি, বয়াতী, বৈষ্ণব ইত্যাদি মতবাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মীয় এমনকি মার্কসীয় পরিভাষা যুক্ত করে এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতির ধারণা ও ব্যবহার চোখে পড়ে। তাত্ত্বিক জ্ঞানের গভীরস্তর চোখে না পড়লেও তত্ত্বের উপরিস্তর বেশ চোখে পড়ে।
১৩. ইতিহাসের নানা উপকরণের ব্যবহার। এ বিষয়েও যথেচ্ছাচার কানে লাগে। ইতিহাস-ঐতিহ্য-কিংবদন্তি সব কিছু একাকার করে ফেলায় অনেকের কবিতায় এর নিরর্থক ব্যবহার ঘটে। সার্থক ব্যবহার সামান্য। জীবনানন্দের ঐতিহাসিক বা ঐতিহ্যচেতনা থেকে কবিতাকে জীবনানন্দীয় মার্গে উন্নীতকরণের প্রয়াস সবার ক্ষেত্রে সার্থক হয়নি। ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার তথ্যবিভ্রাটও ঘটে।
১৪. ফুল-ফল-নদী-পাখি-বৃক্ষ-পাহাড়-মেঘ-চন্দ্র-সূর্যের মতো অতি ব্যবহৃত উপাদানের নতুন ব্যহার। এসব শব্দ আগের রূপে আর ব্যবহার করেন না নতুন কবিরা। তারা এগুলো নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপন করেন।
১৫. বিমানবিক বিষয় ও বস্তুর সঙ্গে আত্মীয়তাসূচক সম্পর্ক রচনা। কবির আত্মীয়তা শুধু সামাজিক আত্মীয়তার বন্ধনের নিয়মে চলে না। নতুন কবিতায় এসব বিষয় উঠে এসেছে। কবিতা, মেঘ, নদী, পাহাড় বা কষ্টকে ভাই-বোন-বন্ধু-পিতা-মাতা ইত্যাদি আত্মীয়তাসূচক শব্দের বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যায়।
১৬. অনাত্মীয় বিষয় ও বস্তুকে সম্বোধন ও সম্ভাষণরীতি। নতুন আত্মীয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্বোধন করে বা সম্ভাষণ জানিয়েও কবিতা লেখেন কবিরা।
১৭. বিদেশি শব্দের ব্যবহার। বিশ্বায়নের ফলে কাব্যভাষায় শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুদ্ধতা রক্ষা করা এখন আর সম্ভব নয়। তরুণ কবিরা বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেন অনায়াসে। কিন্তু তারা বিষয়টা সহজভাবেই করেন। এজন্য শ্রুতিকটু জবরদস্তি করেন না।
১৮. শব্দালঙ্কারের ব্যবহার হ্রাস পেয়ে অর্থালঙ্কারের ব্যবহার বৃদ্ধি। ছন্দ, অনুপ্রাস ইত্যাদি শব্দালঙ্কার এ সময়ের কবিতায় কমে গেছে। বাংলাদেশের কবিতায় ছন্দ প্রায় দেখাই যায় না। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন কবির কবিতায় এখনো ছন্দ-অনুপ্রাস কানে লাগে। তবে অর্থালঙ্কার বেড়ে গেছে সবখানে। বলা যায় এখনকার কবিতার মূল কাঠামোটিই উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প দিয়ে গঠিত।
১৯. অর্থহীনতা। নতুন শতকের কবিতায় অর্থহীনতা একটি অভিযোগ। কবিতার নতুন শারীরকাঠামো এবং ভিন্ন মানসের কারণে, পঙ্ক্তিগঠনে অর্থনির্দিষ্টতার বাক্যিক শর্ত ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বলে অনেকের কাছে কবিতা অর্থহীন মনে হয়। এটা পাঠকের অপ্রস্তুতি। কিন্তু কোনও কোনও কবি অর্থহীনতাকেই নতুন কাব্যভাষা বা কাব্যপ্রাণের প্রবণতা বলে মনে করেন। তাদের মাথা শিল্পীর মতো সমৃদ্ধ নয় বরং কারিগরের মতো হাতের দক্ষতা আছে। নতুন কবিতার গতিপ্রকৃতি না বোঝার ফলে এমনটি হয়েছে।
২০. বিরামচিহ্নের ব্যবহার কমানো। বিরামচিহ্ন বাক্যের অর্থনির্দিষ্টতার শর্ত পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। এটি কবিতার পঙ্ক্তির জন্য সর্বদা অনিবার্য নয়। যেখানে বিরামচিহ্নের ব্যবহার না করলেই নয় সেখানেই ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় যতি, ছেদ ইত্যাদি ছন্দের রীতি অনুসারে পর্ব এবং পর্বাঙ্গের ভিত্তিতেই চলে, সেখানে বিরামচিহ্ন লাগে না। এ বিষয়টা আগের কবিরা জানলেও রীতিটা পরিবর্তন করার সাহস পাননি বা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তরুণরা এ বিষয়ে সাহসী কাজ করেছেন।
॥তিন॥
জাকির জাফরান
জাকির জাফরানের বেশিরভাগ কবিতাই প্রেমের। তিনি আবেগের সমকালীন ভাষ্য রচনা করেন। কখনো প্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কখনো না পাওয়ার হাহাকার, কখনো হারানোর বেদনা কাব্যরূপ দেন। পৃথিবীর কবিতার সবচেয়ে পুরনো বিষয়টাই প্রেম। প্রেমের অনুভূতি চিরন্তন। যতদিন মানুষ আছে ততদিন আবেগ থাকবে, প্রেম থাকবে। প্রেমের কবিতাও থাকবে। কিন্তু প্রত্যেক কবির নিজস্ব ভাষা, ভাষ্য কিংবা প্রেমের ভাষণ থাকে। থাকে নিজস্ব উপস্থাপনা পদ্ধতি। এই নতুনত্বই প্রত্যেক নতুন কবিকে পুরনোদের ভিড়ে জায়গা করে দেয়। সবার প্রেমের কবিতা যদি একই রকম হতো, তাহলে পৃথিবীতে একটি মাত্র কবিতা থাকত। আর সবাই সেটাই পড়ত। দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায়, জাতিতে জাতিতে কত কবিতা লেখা হচ্ছে এর মধ্যে কোনো না কোনো টেকসই ক্ষমতা থাকে, না হয় টিকে না।
জাকির জাফরানের ‘চিঠি’ কবিতায় দেখি, বাবার সঙ্গে কিশোর মন অঙ্ক শেখার মধ্য দিয়ে বিরহের যাতনা আপন করে নিচ্ছে। বাবা শেখাচ্ছিলেন, ডালে বসা দুটি পাখি থেকে শিকারির গুলিতে একটি মরে গেলে কয়টি থাকে? কবির মন সেই বেঁচে থাকা পাখিটির নিঃসঙ্গতাকে আপন করে তার সাথে চলে যায়। এ কবিতায় ‘আমি’ সর্বনামটি পাখির রূপকে আর ‘তুমি’ আছে স্মৃতি হয়ে।
‘অশ্রুলীন’ কবিতায় দেখা যায় প্রেমের পাওয়ানা পাওয়ার দোলাচলে দুলছে কবির মন ও কবিতার শব্দগুলো। এ কবিতায় প্রেমিকের কল্পনার তীব্রতা যেমন আবেগ সৃষ্টি করেছে, তেমন কবির কল্পনার তীব্রতা থেকেও সৃষ্টি হয়েছে শিল্পসত্য। শুরুতেই কবি জানান,
তুমি আসবে না জেনেও বৃষ্টি হল সারারাত।
এখান থেকেই দুলুনির শুরু।
তুমি ভালোবাসবে না জেনেও এক উদভ্রান্ত বালক
প্রণয়ের পতাকা ওড়ালো কাল সারাটা বিকেল
এর পরে জানাচ্ছেন কিশোর বালক সূর্যাস্ত টেনিসের পিছু ছুটতে গিয়ে সন্ধ্যার পালক ছিঁড়ে ফেলেছে। একটি শালিক দিনের শেষে কুলায় না ফিরে সারাটা সন্ধ্যা খড়কুটো কুড়িয়েছে। যদিও শালিক জানত তার প্রেমিকা তাকে ভালো বাসবে না। পাশাপাশি দুটি গাছের মতো দূরত্ব নিয়েও কত দূর। এখানে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নেই কিন্তু উপেক্ষার বেদনা বড় তীব্র। ‘লাল আকাশ’ কবিতাটি শুরু হয়েছে অতীতের গল্প দিয়ে। কিন্তু সেই গল্প থেকেই বেরিয়ে আসে প্রবাদপ্রতিম দুটি পঙ্ক্তি।
তরমুজ কাটলে দু’ভাগ হয়ে পড়ে থাকে লাল আকাশ।
কিন্তু হৃদয় দু’ভাগ হলে মাথার ওপরে কোনো আকাশ থাকে না।
এ কবিতায় বিচ্ছেদের বিরহ প্রবল শোক তাপ নিয়ে আছে। না পাওয়া, হারিয়ে যাওয়াই এখানে মুখ্য। কবি স্পষ্ট ভাষাতেই জানান,
আজ তুমি নেই
আমি আলো আঁধারির মধ্যে বসে কাঁদলাম।
‘দুঃখ’ কবিতায় কবির স্বপ্নহন্তারক রূপে উপস্থাপিত হয়েছে বাঘ। বাঘ এখানে শুধু স্বপ্নবিনাশই করে না, কবির হৃদয় ক্ষতবিক্ষতও করে। কবি দেখেন তার দুঃখের গল্পে কেবল বাঘের ছড়াছড়ি। প্রেমিকার রক্তের রঙ অত্যধিক লাল। তার ভাষার অন্য কোনো দেশ আছে কি না—এ প্রশ্ন কবির মনে ঠেলে ওঠে। নিষ্ঠুর শ্লোকের মতো মানুষ বা পাখিদের ভাষা থেকে পৃথক সে ভাষা। ‘স্টেথো’ কবিতায়ও চলে যাওয়ার কথা। এখানে প্রেমিকার চলে যাওয়া ছাই থেকে জন্ম নেয় পাখি। ফিনিক্স পাখির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। প্রেমিকা চলে গেলেও প্রেম চলে যায় না। প্রেম পুনর্জীবন লাভ করে। আবার সে অনন্ত আকাশে উড়তে শেখে। একই নামের দ্বিতীয় কবিতায় কবির হৃদয় প্রতীক্ষায় থাকে ‘কোনোদিন চিঠি না আসা দ্বীপের মতো’। সেখানে ফার্ন উদ্ভিদ সেজে বসে থাকা ভালো মনে করেন কবি। থানকুনি পাতার সমাজ বা ফার্নের সমাজ আমাদের চেনা পরিবেশে বড় অনাদর আর অবহেলার জায়গা। উপমা দুটি চমক নিয়ে কবিতায় বসে গেছে। এমন প্রতীক্ষা দেখা যায় ‘খেলা’ কবিতায়। আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো সামান্য একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর সহযোগে পরাবস্তব ঘোর সৃষ্টি করা হয়েছে ‘একদিন আমি আর মফিজ’ কবিতায়। মশারির ভেতরে মানুষ আর মশা। মশার রক্তাক্ত কামড়গুলো যেভাবে মানুষকে জাগিয়ে দেয়, তেমনি কবির স্মৃতি প্রিয়ার ভালোবাসা ও রক্তাক্ত চুম্বনগুলো জাগিয়ে তোলে। ‘পায়ে বাঁধা দুটি সর্বনাম’ কবিতায় পায়ে বাঁধা সর্বনামে মন মজে গেছে। হয়তো কবি আমি আর তুমির কথাই বলেছেন। তবে কবি তুমিকে জড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে ভোলেননি। প্রেমিকাকে জড়িয়ে থাকলে কৃষিসভ্যতায় জড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতা লাভ করেন।
বিস্তৃত অনাগ্রহের প্রতি উড়ে আসে মেঘ
তোমাকে জড়িয়ে ধরে মনে হল ধান
মনে হলো উৎসব
‘দ্বিরালাপ’ কবিতাটিতে বিচ্ছেদ নেই আছে মিলনের ভাষা।
…তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে রাত
চুল খোলো রাত্রিসহোদরা
যুদ্ধক্ষেত্র প্রসারিত হোক
এখানে দেখি প্রেম থেকে তীব্র কামনা। সবশেষে মেঘের ভেতর বিমান বাংলাদেশের প্রবেশ করার উৎপ্রেক্ষাটি মিলনাত্মক এ কবিতাটির ঔৎকর্ষ বাড়িয়ে দিয়েছে। ‘অস্তিত্ব বিষয়ক’ একটি ছোট কবিতা। কবি শিরস্ত্রাণ পরে প্রেমিকার সামনে এসেছেন। দুই চোখে দুটি পাখির রূপকে আসলে কবি দূরদৃষ্টিরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবি যাকে কামনা করেন তাকে না পেয়ে অন্য কোনো দিক থেকে কবির হৃদয় নয় শুধু পেশাগত দিক উল্লেখ করে বিয়ের প্রস্তাব এলে কেমন লাগার কথা? সেই অনুভূতিই তুলে ধরেছেন ‘বিয়ে, প্রীতিধারা’ কবিতায়। ‘সংবেদনা’ কবিতায় আছে অসম প্রেমের ইঙ্গিত। বইখাতা হাতে তরুণী এসে রুলকরা খাতার মতো বিশাল আকাশে আশ্রয় খোঁজে। ‘একটি মাছ ভালোবাসে একটি পাখিকে।’ জলচর আর খেচরের মধ্যে যেন গড়ে ওঠে অসম প্রেম। ‘জল’ কবিতায় আছে অকারণে ভালোবাসার কথা। অপরপক্ষের চোখে কোনো অক্ষর নেই বলে কবি বুঝেই নিচ্ছেন সেখানে অক্ষর নেই মানে ভাষা নেই, ভাষা না থাকলে ভালোবাসাও থাকে না। গভীর আলিঙ্গনের দূরত্ব বাড়ে এই মহান সত্যের প্রকাশ কত সাবলীলভাবে এখানে উচ্চারিত হয়েছে। হৃদয়ের গভীরে যদি আশা জেগে ওঠে তাহলে যেন কবিকেও ডেকে নেয় তার প্রিয়তমা সেই আহ্বান করা হয়েছে বার বার।
‘প্রিয়ঝু’ সিরিজের কবিতাগুলোতে আছে স্মৃতিকাতরতা, নিঃসঙ্গতা, প্রতীক্ষা। আর আছে জীবনের ব্যর্থতার গভীর গ্লানি। কিছু কিছু কবিতা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা। উদ্দেশ্য প্রণোদিত কবিতায় স্মৃতিকাতরতা এবং কামনা নির্দিষ্ট হয়ে যায় পাঠকের কাছে। সর্বজনীনতার অভাবে এগুলো আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তবে জাকির জাফরানের কবিতা সে সমস্যা থেকে অনেকটাই উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, তিন নম্বর কবিতায়:
মেঘে মেঘে শতাশ্রু যে আমি
প্রত্যাগমনের পথে দাঁড়িয়ে রয়েছি একা
‘শীত’ কবিতায় অতিথি পাখির রূপকে আছে প্রিয়া। স্পর্শের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখার কামনাও আছে। ‘সান্নিধ্য’ কবিতায় প্রিয়ার সান্নিধ্যে যাওয়ার ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। অমারজনীতেও যেখানে জনঅসন্তোষ নিয়েও ফুল ফুটে থাকে।
‘আমি’ কবিতায় আগুনের রূপক হয়ে কবি আছেন শুকনো পাতার নিচে। তার ওপরে আছে শুকনো পাতা অথচ সেখানে আগুন জ্বলে না। এই ব্যর্থতাই এখানে পাঁচ লাইনের ছোট্ট কবিতাটির শব্দমালা সৃষ্টি করেছে।
আমার এ জীবন নকশা
বৃথা যায় প্রভু
শুকনো পাতার নিচে আজ
চাপা পড়ে গেছি
আমি আগুন আগুন।
‘আগন্তুক’ কবিতায় কবি স্পষ্টভাবে আগন্তুককে জানাচ্ছেন যে, তার প্রিয়াই শত বেদনার উদ্ভাবক। তাকে আসতে দেখে মনে মনে অসংখ্যবার শামুক হয়ে গেছেন। শামুক হয়ে গেলেও ভেতরের অগ্নিকা কিন্তু নিভে যায়নি। ভেতরের অগ্নিকাণ্ডের দিকে চোখ রেখে তিনি আহ্বান করেন: ‘দেখে যাও, বেঁচে আছি গালপল্পহীন’।
‘আফিম’ কবিতায় প্রিয়ার আফিম মেশানো চোখের দৃষ্টিতে আছে অনেক মাস্তুল। এখানে ‘মাস্তুলে ভরা’ বলা হলেও আমাদের চোখে ভাসে ছোট বড় অনেক পাল টানানো সামুদ্রিক জাহাজ। এই যে প্রিয়ার দূরগামী চোখ। সে চোখে নিশ্চয়ই আছে কামনার আহ্বান, বাসনার গান। কে আগে কাকে আহ্বান জানাবেন তিনিই হবেন প্রথম ডাকহরকরা। সেখানে নেশা থাকলেও ভরসা নেই। তাই কবি তাকে আহ্বান করেন। কাছে ডাকেন।
চন্দন চৌধুরী
চন্দন চৌধুরী বহুমাত্রিক প্রতিভা। ছোটগল্প, অণুগল্প, প্রবন্ধনিবন্ধসহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় সমান বিচরণ করেন। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক ব্যঙ্গ একটি সফল নান্দনিক দিক। রাজনৈতিক কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি লেখেন না। কারো প্রতি পক্ষপাত এমনকি বিপক্ষপাতও দেখা যায় না। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর, এই ঘনসংখ্যার দেশে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক নেতাদের শঠতা, প্রতারণা, সন্ত্রাস, অভিনয়প্রিয়তা ইত্যাদি দেখে এবং সহ্য করে তাদের প্রতি জন্মানো বিরক্তি, ঘৃণা ও অবিশ্বাস উঠে আসে তার কবিতায়। তিনি নতুন নতুন শব্দ সমবায়ে ও অলঙ্কারে সে সব নেতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ করেন। ‘হাসি কালারপ্রিয়’ কবিতায় শুরুতেই তিনি লিখেছেন: ‘নেতাদের হাসি দেখে কুয়াশা জমে বেশ্যার চোখেও।’
পরে আবার তিনি লেখেন,
এই সব জেনেও নেতাদের হাসি দেখে বড় ডর ডর লাগে
ঢের সংকোচে নিজের হাসিটা জিন্সের পকেটে ভরে
হাঁটা দিয়েছি দূরে
চন্দন চৌধুরীর কবিতায় আরেকটি বিষয় বড় বড় কোম্পানির বস কালচার। এই বসদের স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ইত্যাদি ব্যঙ্গভাষায় কাব্যরূপ লাভ করে। আবদুল গনি হাজারীর হাতে যেমন আমলাদের নিয়ে বিদ্রুপ কবিতা লিখিত হতে দেখেছি, চন্দনের কবিতায় দেখি শীর্ষ ধনী ও পুঁজিপতিদের অফিসের কর্মকর্তাদের। চন্দন কোনো সমাজতত্ত্ব হাতে নিয়ে লেখতে বসেন না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, যা তিনি উপলব্ধি করেন তাই লেখেন। ‘হ্যালো বস’ কবিতায় লিখেছেন:
সেই বদ লোক, যে পুরুষাঙ্গটিকে সিরিঞ্জের মতো ব্যবহার
করে কখনো মাতাল চাকু
তার কাছে দেহ রেখে কত নারী বিদেশভ্রমণে যায়
কত নারী শুনে বজ্রব্যাকুল গান
এই বদ লোকটির সঙ্গে কবির সম্পর্ক কী? সমাজে তো এমন কত ধরনের লোকই বাস করে। কে রাখে তাদের ভেতরের খবর? পেশাগত কারণে এ ধরনের বদলোকের সাক্ষাৎকার নিতে হয় কবিকেই। এই লোকদের ক্ষমতা অসীম। তারা প্রায় আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এরা অনেক তরুণের প্রেমিকাদেরকে এরা সবল পুরুষাঙ্গের ক্ষমতায় ও লাভের লোভে বশীভূত করে রাখে। অনেক তরুণের বেদনা, বিষণ্নতা ও সিজোফ্রেনিয়ার কারণও। ক্ষমতার উচ্চতার কারণে অনেক বিরহকাতর প্রেমিকের গোপন অস্ত্র তাদের বিদ্ধ করার জন্য শহরজুড়ে হেঁটে বেড়ায়। এদের গোপন শত্রু অনেক। আর এই শত্রুতার কারণ ক্ষমতা। তাদের ক্ষমতাসিন্দুকের রহস্য কবি উন্মোচন করেন এভাবে:
হ্যালো বস, এই সমাজ বাঁচাতে, অন্তত আপনার সিন্দুক খুলে
কিছু যোনি সাপ্লাই দিন
সকল প্রেমিক তরুণের কাঙ্ক্ষিত যোনি এইসব ক্ষমতাবান ব্যক্তির গোপন সিন্দুকে বন্দি করে রাখা আছে। আর সমাজ বাঁচাতে, তরুণতের বাঁচাতে সেখান থেকে মুক্তি দিতেই হবে যোনিদের।
‘আরোগ্যনিবাস’ ও ‘শেখা’ কবিতা দুটিতে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ভালো বিদ্রুপ আছে। প্রথমোক্ত কবিতায় আরোগ্যনিবাসে মাতালের চিকিৎসা হয়। সেখানে একদিন এক নেতা আসতেই দ্রুত সদর দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। একজন মাতাল চিৎকার করে বলে, “বেহায়া আর বাটপারের চিকিৎসা হয় না এখানে।” আর পরের কবিতাটিতে শিশু বাবার সঙ্গে হাত ধরে হাঁটে মহানগরীর পথে বাবা এটা সেটা দেখান। শিশু দেখে, শিশু শেখে। অবশেষে:
শিশুটি যখন আঙুল তুলে সংসদ দেখায়
বাবা বলেন, ওটা দেখো না, ওটা দেবতার ঘর
গণমানুষের কবর
রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের এবং তাদের মোসাহেবরা তাদের দেবতুল্য বানিয়ে রাখেন। কবি এ কারণেই দেবতার ঘরের প্রতিতুলনা করেছেন গণমানুষের কবরের সাথে। চমৎকার এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। ‘সুখ’ কবিতায় লিখেছেন,
সুখ হলো মন্ত্রীর মেয়ে
টাকা দেখেই যে দু’পা ফাঁক করে
‘লিঙ্গ’ কবিতায় নষ্ট সমাজের, নষ্ট পুরুষদের লিঙ্গের রোগব্যাধি নিয়ে লিখেছেন। বীজ, বংশধর, সবখানে মড়ক। বীর্যের বেশে টপটপ করে ক্ষত বেয়ে পড়ে মৃত্যুপুঁজ। এই সমাজের নেতাদের লিঙ্গের খবর কী তাহলে?
আমাদের নেতাদের গনোরিয়া
সিফিলিসে ভরে গেছে সংসদ
‘শিক্ষা’ কবিতায় জানান, প্রাচীনকালে বাবারা ছেলেদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাতেন। মধ্যযুগে শেখাতেন ধর্মবিদ্যা। আধুনিক যুগে বলতেন বিজ্ঞান চর্চার কথা। মহাকাশে অভিযানের কথা। কিন্তু এখনকার প্রকৃত বাবা বলেন,
অঙ্ক কষে বলতো খোকা
কত টাকা হলে একজন মন্ত্রী হওয়া যায়
‘নগ্ন’ কবিতায় দেখা যায় সংসদের সামনে এক উলঙ্গ পাগলী মনের আনন্দে নাচছে, গাইছে। তখন একজন নেতা পাজেরো গাড়ি থেকে বের হওয়া পরে তাকে দেখেই পাগলী লজ্জায় নিজের চোখ ঢেকে ফেলে।
চন্দন চৌধুরীর কবিতায় দার্শনিকতা এসে নিজেকে ভেঙে ফেলে। এটা তার সাহিত্যের এক স্পষ্ট শনাক্তিকরণ চিহ্ন। তাঁর গল্পেঅণুগল্পেও এটা ঘটে। নিজের বিভিন্ন সত্তা পৃথকভাবে দেখা দেয়। এটা যদিও পাশ্চাত্যসাহিত্য থেকে আমদানি নয়। মধ্যযুগের শেষের দিকের বাউলসাহিত্য থেকেই শুরু। ‘সে আর লালন এক সাথে রয় লক্ষ যোজন ফাঁক রে’ থেকেই এই আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মবিভাজন দেখে আসছি। আধুনিকতার যুগে শামসুর রাহমানের কবিতায় একটি কঙ্কালের সঙ্গে হাঁটার অনুষঙ্গ দেখেছিলাম। আধুনিকতা পেরিয়ে উত্তরআধুনিকতার কালে চন্দন চৌধুরীর কবিতায় দেখি আরো নতুনভাবে বিষয়টি ঘটে। ‘কারণ’ কবিতায় দেখি:
তবু আমাকেই আমি আমার সহস্র হাতে জাপটে ধরে রাখি,
সময় যেভাবে নিজেই বেঁধে রাখে সময়কে।
‘দূর সম্পর্ক’ কবিতায় নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে কবি প্রেমিকার ভেতরে প্রবেশ করেন। সেখানে বসেই তিনি ধ্যানমগ্ন হন। দু’জনের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভব করেন না তিনি। না করারই কথা। কারণ তিনি জানান, ‘দূর বলে কিছু নেই, তোমার ভেতর বসে ধ্যান করছি যখন।’
এ কবিতায় কবি নিজেকে গ্যালারির ভাস্কর্যের মতো বহুমাত্রিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ কবিতা থেকে আরো ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলে ধরেছেন ‘সর্বাংশ’ কবিতায়। চন্দ্র, সূর্য এমনকি ছায়াপথ জুড়েই কবি আছেন বলে অনুভব করেন। কবির নিজের অংশই বিস্তার করে আছে পরম পর্যন্ত। নিজেকে দেখতে পান অজস্র ‘আমি’র সমাহারে। লিখেছেন:
তুমি আমি মিলে যে অজস্র এক আমি, সেই আমিটাই জন্মদাতা।
সেই আমিটাই সূর্যকে জন্ম দিয়েছি, পৃথিবীকে জন্ম দিয়েছি, সমস্ত
কিছু আমারই মধ্যে অন্তর্লীন।
‘তুমি দিয়ে তৈরি’ কবিতায় জানান, ভাবতেই ভালো লাগে ট্রেনের সব বগিতে শুধু তুমি আর আমিতে ভরা। কবি নিজেকে কত ‘তুমি’ দিয়ে তৈরি দেখতে পান। বিশ্বপ্রকৃতির অনিবার্য অংশরূপে কবি নিজের অস্তিত্ব অনুভব করেন। মধ্যযুগের পারস্যের দার্শনিক জালালুদ্দিন রুমী এবং আরব দার্শনিক ইবনুল আরাবির মতো অতিবর্তী ধারণা চন্দনের দর্শন। যিনি নিজেকে শুধু বাংলাদেশ নামক একটি দেশের ভয়াবহ দূষিত পরিবেশের রাজধানীর নাগরিক হিসাবেই দেখেন না। ‘পরিমাপ’ কবিতায় দেখি যেন পারস্যের কবি হাফিজের মতো দৃঢ় সুফিবাদী উচ্চারণ: ‘দেখো, জীবন একজন মানুষেরই সমান, তথাপি একটি চুম্বনের মুহূর্ত থেকেও অসংখ্য জীবন কত ছোট। ‘
জীবনের বাইরে মানুষের কোনো আকার নেই। জীবন আর মানুষ সমান আয়তনের এ কথাটাই চন্দন ভীরভাবে উপলব্ধি করেন। নাগরিক জীবনের অনুভব প্রতিটি কবির স্বতন্ত্র। চন্দন চৌধুরীর কবিতায় নাগরিক জীবনের জন্য, সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসার জন্য তাঁর ত্যাগ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বলা হয়ে থাকে আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের জীবনে ত্যাগ নাই। কিন্তু এই কবি তা দেখিয়েছেন। কবিতার নাম ‘শুধুমাত্র সাধারণ’; এখানেই তিনি জানান, শুধু সাধারণ হওয়ার জন্য কবি গতির নিয়ম তৈরি করেন, ভেতরের অপার সৌন্দর্য ছুঁড়ে ফেলেছেন অসীম শূন্যে। নিজের ভেতরের সুধা সঞ্চিত না রেখে ছড়িয়ে দিয়েছেন। লাবণ্যকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন।
সাধারণ হওয়ার জন্যই নিজের ভেতরটা উড়ে গেল বাইরে, এবং পৃথিবীতে তৈরি হলো যাবতীয় সম্পর্ক, আর এই সাধারণ হবার আশায়ই আমি মাথা গুঁজলাম ঘাসের ভেতর, আমার ওপরই পড়ুক জগতের সব পায়ের বেদনা।
কবিতা সম্পর্কেও যেন ভাষ্য রচনা করেন কবি। ‘জন্ম’ কবিতায় জানিয়েছেন,শব্দ কবির কাছে শৈশবের লাটিম। কবিতার জন্য তিনি নিরীহ উরুর কাছে প্রার্থনা করতে চান না। তিনি এই মতের বিরোধী। তিনি অনুপ্রেরণাবাদী কবি নন। কারো কাছ থেকে অনুপ্ররণা পেয়ে পেয়ে কবিতা রচনা করার পক্ষপাতি নন তিনি। কবির কাছে প্রতিটি ভাবনা একেকটি চিরুনি। প্রতিভাপ্রার্থনা করে কবিতা লেখা তাঁর কাছে কপট পিপাসামাত্র। কিন্তু নারীর শান্ত বুকে প্রার্থিত শব্দ নড়ানচড়া করলে জেগে ওঠে পৃথিবীর প্রাণপুঞ্জ। কবিতাটির শেষ পঙ্ক্তিতে অকপট জানিয়েছেন, ‘হরিণীর সমস্ত পেয়েও আমি সম্ভোগ শিখিনি, অথচ তার গর্ভেই জন্ম নিয়েছে আমার সমস্ত কবিতা।’
এখানে এসেই বোঝা যায় কবি নারীর কাছে কী প্রার্থনা করেন। তিনি কবিতা চান, কিন্তু তিনি অতীতের জ্যেষ্ঠ কবিদের মতো নারীপটানো কবিতা রচনা করতে চান না। ‘জীবনসূত্র’ কবিতায় নাগরিক যন্ত্রণা সহজ সরলভাবে তুলে ধরেছেন। জীবন স্রফে ১০০ মিটার দৌড়। তবে কবি জীবনকে এই কঠিন এবং প্রচ নাভিশ্বাস ওঠা গতিশীল বলেই নেতিবাচকভাবে থেমে থাকেননি। জীবন সন্তানের মতো তাকে জন্ম দিতে হয় বার বার
‘রোমাঞ্চ ও শীতের শহরে’ সিরিজের কবিতাগুলোতে নগরজীবনের নানা দিক কাব্যরূপ লাভ করেছে। তিনি নগরীর আলোর ঘূর্ণিতেও হিজলগাছ দেখতে পান। সিরিজের চার নম্বর কবিতায় লেখেন,
প্রেম একটা ভ্রাম্যমাণ সেতু—এ দিয়েই দেওয়া যায়
আকাশগঙ্গা পাড়ি
তবে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বও তিনি ভোলেন না। একটা ডুবন্ত ট্রেনের রূপকে নিজেকে উপস্থাপন করেন তিনি। প্রেমিকাকেও মনে করেন সেই ট্রেনের স্বল্পসময়ের যাত্রী। শেষরাতের বাতাসে পাতার মতো উড়ে যাবার কথা তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সেই পাতাটি কিন্তু বিচ্ছিন্ন কোনো পাতা না। অন্য পাতাদের মাঝখানে ছিল দেবদারু গাছে। ছয় নম্বর কবিতায় পরাবাস্তবতার ভেতর দিয়ে শহরটাকে পাগলের চোখ থেকে টেনে বের করে নিতে চান। সাত নম্বর কবিতায় দেখি, জেলেপাড়া থেকে আগুন কিনে আনেন নগরপদ্মের দামে। সেখানে জলের গন্ধ মুছে যায়নি। আট নম্বর কবিতায় দেখি, শহুরে বাতাসে কবির গ্রামের ভাই মারা যায়। ভাই শব্দটি এখানে কবির দ্বিতীয় সত্তাকেও বোঝাতে পারে। নয় নম্বর কবিতায় লিখেছেন,
কেননা এ নগরে মেঘেদেরও কর দিতে হয়
পাখি মৌমাছিদেরও
এগারো নম্বর কবিতায় প্রেমিকার বাড়িকে শহুরে ধানক্ষেত বলে অভিহিত করে ধানকে গৃহলক্ষ্মী গেরস্ত বাড়ি করে তুলেছেন। প্রেমিকার অস্তিত্বই তার কাছে ধানের গরম। ধান নিয়ে কবির একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতাও আছে ‘ধানবউ’নামে। বিচ্ছেদের শিল্পরূপ কতটা নান্দনিক হতে পারে একটি মাত্র পঙক্তিতে দেখা যায়।
ও আমার ধানবউ
বল তোরে খেয়ে গেল কোন টিয়াপাখি
ধানের অনুষঙ্গ চন্দন চৌধুরীর আরো কবিতায় আছে। ‘কইন্যা বুদ্ধিমান’ কবিতায় চুলের সমানুপাতে ধানের পরিমাণ বলেছে কইন্যা। ‘পাখিজন্ম’ কবিতায় তিনি লিখেছেন, ‘শব্দচেতনার দিনে উদাসী সাম্পান ভরে কেই নিয়ে যায় আমাদের বেটে রাখা ধান।’, ‘ডাহুকমঙ্গল’ কবিতায় আবার রাজনীতি এসেছে। সেখানে জলপাই রঙের নঞর্থক দিক তুলে ধরেছেন। ‘অলীক বীক্ষণ’ কবিতায় লিখেছেন, ‘ওই দূরে গলিটার মোড়ে একখ ছায়াবিন্দু আামকে ডাকছে বুঝি সিভিলের বেশে।’
চন্দন চৌধুরীর ‘যাবে হে মাঝি দিকশূন্যপুর’ এবং ‘স্বাধীনতা’ কবিতাদুটি অনেক বেশি নান্দনিক। প্রথমোক্ত কবিতায় অচিনদেশের যাত্রী হওয়ার কথায় যেন নাগরিক জীবনের অনিশ্চয়তা, ঔপনিবেশিক বেনিয়ার ভাষা, ইতিহাসচেতনা, অতীতের অশ্বখুরের আওয়াজ সব কিছু দিয়ে কবিতাটি যথেষ্ট ঋদ্ধ করা হয়েছে। ‘স্বাধীনতা’ কবিতায় সেই চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম। এ কবিতায় আমাদের ঐতিহাসিক ভুলগুলোর ইশারা আছে। সাম্প্রতিক নাগরিক কিংবা গ্রামীণ জীবনের সমস্যাগুলোর অতীতবীজের কথাই বলেছেন কবি। আর এরই পরিণতি ‘কবিসন্তরণে’ কবিতাটি। এই দেশে, এই শহরে এই সভ্যতায় বাস করতে হলে যে কত ঘাম, শ্রম, ক্লান্তি নিয়ে বাস করতে হয় তারই উপসংহার এই কবিতা। ‘জীবনসূত্র’ কবিতায় যে লিখেছিলেন জীবন ১০০ মিটার দৌড়, এখানে আরো শিল্পীত বুননে কথাটি বলেছেন,
জুতার তলাকে আগেই উৎসর্গ করেছি রাস্তার নামে
এই জীবন তো আসলে আমাদের না আমাদের রাস্তার। চন্দন এই কথাটিই লিখেছেন।
মামুন রশীদ
মামুন রশীদের ব্যক্তিস্বভাব কবিতায় উঠে আসে, আবার বিপরীত কথাগুলোও অবচেতনে শিল্পরূপ পায়। মনের ঘরের গোপন অভিলাষগুলো দিয়েই তো গড়ে ওঠে কবিতার সাতমহলা। কবিতা রচনা শুধু অভ্যাসের বিষয় না তাঁর কাছে। কবিতারচনার শ্রম দিয়ে তিনি উঁচু কোনো সৌধ রচনা করতে চান। তাই তিনি লেখেন ‘একটু একটু দূরে’ কবিতায়:
একটু একটু করে মানুষ আমাকে মনে রাখুক
…
পুরনো স্মৃতিতে কিছু না কিছু
ফেলে আসি, ভাবি, এইসব স্মৃতিচিহ্নে
মানুষ আমাকে জানুক
মানুষ একজন কবিকে মনে রাখবে এটা কবির উচ্চাভিলাষ নয়। কবিতা জানতে হলে কবিকে জানতে হয়। বস্তু শুধু তার নিজের সময়েই অবস্থান করে। বস্তু থাকে তাঁর ভর ও আয়তন নিয়ে। বস্তুটি ধ্বংস হয়ে গেলে চারপাশ থেকে অন্য বস্তু বেগবান হয় শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য। এই কারণে শিল্পজগতের মানুষেরা, শিল্পীরা নিজের শূন্যস্থানে নিজের শিল্পকর্ম দিয়ে ভরাট করে রাখতে চান।
মামুন রশীদের কবিতায় প্রেমের বিচ্ছেদ বেদনা এবং বিরহের শোকতাপও দেখা যায়। ‘আমাকে মনে আছে’ কবিতায় দেখা যায়,
দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে আমাকে রেখে
রাজহংসীর মতো নীলিমাকে পেছনে ফেলে
হেলে দুলে অদ্ভুত এক স্বপ্নসীমার
সন্ধানে, আর কখনোই ধরতে না পারা
দূরত্বে—ঠিক ঠিক শান্তির আবাসে দিয়েছ উড়াল।
বিরহের কবিতা এবং গানের চিরন্তন ধারাই যেন এটা। কবিকে শিল্পীকে ছেড়ে তার প্রেয়সী সুখের সংসারে প্রবেশ করে। ‘প্রবাস’ কবিতায় দেখি
মুকুরে প্রতিফলিত মুখ কখনো সত্য বলে না
তবু সেই সত্যে আস্থা রাখি বার বার
সত্যিই তো আমরা জানি আয়না সর্বদা সত্য উপহার দেয় না। আমরা যারা আত্মসচেতন মানুষ, আমরা যাদের আয়না মনে করি তারাও সঠিকভাবে আমাদের সত্য দেয় না। তবু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সেখানে আস্থা রাখতে হয়। কবিতার শেষে দেখা যায় ঘুড়ির রূপকে কবিমন আকাশে ওড়ে ঠিক সেই আয়নার প্রতিবিম্বের আস্থার মতো।
‘পুরীর সমুদ্র দেখিনি’ কবিতায় শুরুতেই কবি জানান, তিনি পুরীর সমুদ্র দেখেননি। তবু পুরীর সমুদ্র কবির কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা কবির প্রেমিকার উপমা। সেখানকার বালুকাবেলায় আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ভাঙন আর শব্দ কবির কানে এবং বুকে। ‘স্থিরতা কি কারও ধাঁচে থাকে’ কবিতায় সত্যিই কবির প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যায। অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও গন্তব্যহীনতা মানবিক বোধকে যেভাবে ভাবিত করে, তাড়িত করে আর কিছু সেভাবে করে না। কারণ এগুলোর মধ্যেই মানুষের অস্তিত্ব। এর ভেতরেই বাস করে মৃত্যুচিন্তা নামক কালোগর্ত। কবি বলেন, ‘তাকে আজ কি দিয়ে বাঁধি? কোন যতিচিহ্নে?’ এই যতিচিহ্নের উপমাটি অভিনব। এর অনিবার্যতাও আছে। যতিচিহ্নেই নির্ধারিত হয়, কে কোথায় কতক্ষণ অবস্থান করে।
মামুন রশীদের ‘চিড়িয়াখানা’ সিরিজের কবিতাগুলোর বুনন ঘন। এর মধ্যে আছে বাস্তবতা আর পরাবাস্তবতার ঘোর। প্রচলিত বাকভঙ্গিতে অর্থহীনতার মতো মনে হয়। কিন্তু পদক্রম ভেঙে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সেখানে আছে নান্দনিকতার নতুনত্ব। এসব কবিতায় বাঘ, সিংহ, শাখামৃগ, পায়রা, শেয়াল, সাপ, কুকুর, খরগোশ, হরিণসহ অনেক প্রাণীর প্রসঙ্গঅনুষঙ্গ আছে। এগুলোর ভেতর লুকিয়ে আছে সেমেটিক ধর্মের মিথ ময়ূর, সাপ ইত্যাদি। আদি মানবের আদিপাপের লুপ্ত নিদর্শন। এগুলোর সাথে কবি একাত্মতাও দেখতে পান। এক নম্বর কবিতায় লিখেছেন,
চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে পড়া বাঘ, যার সঙ্গে গতকাল
দেখা— প্রথমে ভেবেছিলাম কাগজের। পরে দেখি না, অবিকল
আমারই গলায় কথা বলে।
‘সময়’ কবিতায় কবি সময় সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন, সময় বলে কিছু নেই। বন্ধ খামের ভেতরে বয়ে বেড়ানো শূন্যতা শুধু।
মামুন রশীদের কবিতায়ও নিজেকে ভাঙতে দেখা যায়। এই ভাঙনকে কবি নিজেই ‘দ্বৈতবাদ’ বলেছেন। ‘মানুষ বা আত্মা বা এরকম কিছু’ কবিতার শুরুতেই লিখেছেন, মানুষ মূলত দ্বিখণ্ডিত। এই দ্বিখনের সংখ্যাটি নিচের দিক থেকে— মানে অদ্বৈতবাদ থেকে সর্বোচ্চে দুই, নাকি বহুত্ববাদ থেকে কমে এসে দুইয়ে স্থির এই প্রশ্নটা কবিতা পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বার বার জাগে। মনে হয় নিচের দিক থেকে দুই। মান অদ্বৈতবাদ থেকে দ্বৈতবাদের জন্ম। কারণ তিনি এ কবিতায় মানুষের দেহকে অস্বীকারের মতো করে ‘শরীর হলো কাঠামো’, ‘শরীর হলো অভিশাপ’, ‘শরীর মূলত ক্লীব’ ধরনের পঙ্ক্তিতে উল্লেখ করেছেন। মানবদেহকে এ ধরনের অস্বীকারের মধ্য দিয়ে টিকে যায় শুধু আত্মা। আর দেহ যদি আত্মা থেকে পৃথক ধারণায় প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে দ্বৈতবাদ ঘুরে ফিরে অদ্বৈতবাদে পরিণত হয়। সব শেষে বলেছেন,
শরীর হলো অভিশাপ। শরীর মূলত ক্লীব। মানুষ বিপরীতে এর। দিব্য ও ঐহ্যিক সঙ্গমের মিলিত স্রোত। বাধার প্রাচীর পেরুনো একা এক ইন্দ্রজাল। ‘ব্যক্তিগত’ কবিতায় দাবার ছকের মতো ঘরে বন্দি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে কবি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।
সাদাকালো—যদিও সাধ থাকে আসমানি রঙে, নীলে
মরীচিকা—ভাঁড়ারে জমা শুধু করুণার রসদ।
ভেতরে অনন্ত গতি—পায়ে তবু গতি নেই। সীমানা ব্যাপৃত
ছকবাঁধা এই আঁকানো ঘরে। চমৎকার এই চলাচল, বদ্ধ
পরিবেশে। দূরে বন্ধনমুক্তির ডাক।
এখানে ‘আঁকানো’ শব্দটি আসলে ‘আটকানো কিনা স্পষ্ট নয়। তাহলে অর্থ দুই রকম হতে পারে। আটকানো হলেই পূর্বাপর পঙক্তির সাথে মেলে। না হলে কবিতার সুর ভিন্ন দিকে যায়। ‘এভাবে জন্ম নিতে পারে একটি কবিতা’ নামক কবিতাটিতে কবি তাঁর কাব্যভাবনাকেও শব্দরূপ দান করেছেন। তিনি মনে করেন, ‘কবিতা কিছুই বলে না, হয়ে ওঠে।’ এই কথাটির মধ্যেই তাঁর কাব্যপ্রকরণ লুকিয়ে আছে। কবিতা আসলে কিছু বলে না, কিন্তু হয়ে ওঠে। কবিতাকে এখানে চিত্রার্পিত চিত্রের মতো কর্মবাচ্যের ভাষা নিয়ে থাকতে হয়; কবিতার কোনো কর্তৃবাচ্য নাই বলেই মনে করেন মামুন রশীদ।
‘১ আগস্ট ২০০০’ কবিতাটি বৈষ্ণব প্রেমের মতো বালিকাপ্রেমের অনুষঙ্গ নিয়ে সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ‘শব’ কবিতায় মৃত্যুর কথা প্রকাশিত হয়েছে মৃতদেহের রূপকের মধ্য দিয়ে। আমাদের যাপিত জীবনে মৃত্যু বলতে মৃতদেহকেই কল্পনা করি। কারণ মৃতদেহের চেয়ে মৃত্যুর জ্বলজ্যান্ত আর কোনো উপমা নেই। কিন্তু সুফিবাদ বা বৈষ্ণববাদ প্রেমের মিলনের মতো করে মৃত্যু দেখিয়েছে। কবি মামুন রশীদ এখানে মৃত্যুর ধারাবাহিকতা বোঝাতেই এ ধরনের উপস্থাপনরীতি বেছে নিয়েছেন।:
ফিরবে না। এইসব বাহকেরা ফিরে যাবে চেনা অধ্যায়ে,
আগুনের তাপ কমে এলে ওরা বিনিময়ে সংক্রামিত হবে
চক্রাকারে চার বেহারার কাঁধে।
যারা আজ শববাহক, তাদের মধ্যেই একজন কাল শব হবেন। একজন যুক্ত হবেন। আবার আরেকজন শববাহক শবে পরিণত হবেন। সংখ্যাটা ঠিক থাকবে। আর চক্রাকারে ঘুরতেও থাকবে শব আর শব বাহকেরা। ‘করতলে কার মুখ’ এবং ‘প্রিয়তমেষু’ কবিতায় প্রেমই মুখ্য। কিন্তু ‘প্রিয়তমেষু’ কবিতায় পুরুষের প্রেম ব্যাকরণে অসিদ্ধ বলেই ভাবিয়ে তোলে, তাহলে নারীপ্রেমে এখানে কে কথা বলে? কবি নাকি কবির প্রেমিকা? যদিও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কালকেতু আর ফুল্লরার অনুষঙ্গ আছে এখানে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ফুল্লরার মনের বাসনাই এখানে কালকেতুর প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।
কবিতা লেখা এক বিষয়। আর প্রকাশ এবং পাঠকের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন বিষয়। তিনটি কাজের অভিজ্ঞতা কবিকে হতাশায় পৌঁছে দেয় অথবা অহঙ্কারের চূড়ায় উত্তীর্ণ করে। মামুন রশীদ ‘আপাতত গ্রন্থের শেষ কবিতা’ নামক কবিতায় জানান, ‘প্রভু, আমি ছাড়া আর আমার আর কোনো পাঠক নেই।’ আবার শেষে বলেছেন, ‘তুমি ছাড়া আমার আর কোনো পাঠিকা নেই।’ কিন্তু কবিতাটিতে কবিতার বিষয়ের আড়ালে আছে জীবনরূপ কবিতার কথা। সেখানে জীবনপাঠের কথাই তিনি বলেছেন। এর প্রমাণ শেষ পঙক্তিটি: ‘ তোমার কাছেই জমা রেখেছিলাম আমাদের প্রস্তাবিত শিশুর হাসি।’
এই যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা আর উত্তরাধিকারের সুখকামনা। এখানেই লুকিয়ে আছে কবিতাটির চাবি। খুলতে হলে কবিতাটি আবার পড়তে হয়।
‘সমুদ্র রাখে না কিছুই’ কবিতায় দেখা যায় সমুদ্র শব্দ দিয়ে কবি অসীম সময়কে উপস্থাপন করেছেন। ‘রবীন্দ্রনাথ’ কবিতায় আমাদের যাপিত জীবনে রবীন্দ্রনাথের অনিবার্যতা উপলব্ধির সুর প্রবাহিত হয়েছে।
আমাদের আর্তনাদে, আমাদের ক্লান্তিহীন চলায়—
আমাদের অশ্রু স্রোতে, আমাদের জীর্ণ মলিনতায়
আমাদের তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে, বিরহের মরীচিকা দ্বীপে
নির্ভার নেশাতুর আলো।
‘মানুষের ভিড়ে’ কবিতায় কবির সংকোচ প্রকাশ পেয়েছে। নাগরিক জীবনে বিচিত্র মানুষের কাছে কবিদের যেতে হয়। সবার সাথে খাপ খেয়ে চলার লোক নন এই কবি। নিজেকে তিনি গুঁটিয়ে নেন। চোখ কান বন্ধ করে রাখেন। তখন বাইরের হাওয়াও ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।
নির্বাক, আরো নীরব হয়ে যাই
তবু বেদনার ভাষা মুখে
ফুটে ওঠে না
‘তোমাদের জনপদে’ কবিতার নামকরণে মনে হতে পারে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা। ভালোভাবে পড়লেই চোখে পড়ে এটি মূলত প্রেমের কবিতা। নতুন এবং নান্দনিক উপস্থাপনা অসাধারণ করে তুলেছে কবিতাটি। ‘অন্ধকারে’ কবিতায় মানবজীবনের নানা সীমাবদ্ধতায় এবং অসম্ভবতার কারণে বিবর্তনের গোপন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন কবি। এখানেও খাপ খেতে না পারার যন্ত্রণা উঠে এসেছে। ‘আজি হতে শতবর্ষ পরে’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মতো নিজের কবিতার অমরত্বের উচ্চাশা প্রকাশিত হয়েছে। নক্ষত্র মরে গেলে তার আলো কোটি কোটি বছর ধরে মহাকাশে আন্দোলিত হয়, এমন বর্ণনার মাধ্যমেই কবি নিজের সাহিত্যের ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেন। এই অমরত্ব নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন ‘আমাকেই ছেড়ে যায় সবাই, আমি নই’ কবিতায়।
নিরুদ্দেশে, দূরের কার্নিশে নিজেকে অমর, অক্ষয় করার
অপ্রাকৃত আনন্দে গা খুঁড়ে খুঁড়ে লেখা নাম, বেদনার
নীল ক্ষতে ধরে রাখি
কবিতাটির নামের ভেতর স্টিকারের মতো লুকিয়ে আছে নিঃসঙ্গতার করুণ বেদনা। নিঃসঙ্গতা আধুনিক কবিতার অতি ব্যবহৃত একটি প্রসঙ্গ। যতই ব্যবহৃত হোক, এখনো এটি মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। এটি এখনো অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূলসূত্র হয়ে আছে। বাংলা কবিতায় এই প্রসঙ্গটি প্রবেশ করার পর থেকে বিশাল গুরুত্বের সাথেই নতুন নতুনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। একঘেয়েমি বিষয়বস্তু হিসাবে না, উপস্থাপনার কারণে আসতে পারে। মামুন রশীদের ‘দুঃখ’ কবিতায় এই বিষয়টি আরো আকর্ষণীয় বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে।
পুরনো জুতার মত পুরনো বেদনা
যত পুরনো হয় তত বেশি স্বস্তি
এ কবিতায় হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, পুণ্ড্রনগরের প্রত্নইতিহাস উঠে এসেছে। এখানে আছে ইতিহাসচেতনা। তবে এই চেতনা তুলে ধরার কারণ কী? প্রয়োজনই বা কি? কবি তুলনা করে দেখিয়েছেন:
… কানে বাজতে থাকে প্রাচীন বৃষ্টির
প্রার্থনা— আর আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে, আত্মার
ঘনিষ্ঠতার মধ্যে হঠাৎ চমকে ওঠে বজ্রবিদ্যুৎ। তার
অন্তরঙ্গ আলোকচ্ছটার মধ্যে বর্ণময় হয়ে উঠতে
থাকে ক্লান্ত জীবন, ভুলভাবে বেঁচে থাকার দুঃখকথা।
হ্যা। কবির আত্মার আলোই কবিকে আত্মচেতনার পথ দেখায়। দেখিয়ে দেয় ভুলভাবে বেঁচে থাকার দুঃখগুলো কোথায় কেমন করে লেখা আছে।
চাণক্য বাড়ৈ
চাণক্যের কবিতায় নাগরিক জীবনের যন্ত্রণার নতুন স্কেচ আছে। যেন তার খাতা ভরেই আছে যন্ত্রণার স্থিরচিত্রে। ‘প্রকৃত ঈশ্বর’ কবিতায় দেখি, ‘করোটিতে প্রশ্নপিপাসা— অথচ বিস্ময় ছাড়া আর কোনো যতিচিহ্ন নেই।’ তাঁর কবিতায় আছে পাণিনী, চার্বাক, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কথা। সব কিছু ছাড়িয়ে আছে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা। ‘সমুদ্রসঙ্গম’ কবিতায় আছে ভৌগোলিক পৃথিবীর নানা দেশ, মহাদেশ, সমুদ্র আর মহাসাগরের তলদেশের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড, ল্যাব্রাডর, পেরু, ফকল্যান্ড, ভানিয়াতু, জাঞ্জিবার, বঙ্গোপসাগরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় কবি নিজেকে দাবি করেছেন জলমুগ্ধ জীব বলে। প্রথমোক্ত কবিতায় দেখেছি তাঁর কালগত ইতিহাস ভ্রমণ। আর পরের কবিতাটিতে দেখছি দেশগত ভৌগোলিক স্থানজুড়ে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার নির্যাস। সবশেষে কবিতাটি প্রেমের। কবি এই অভিজ্ঞার আলোকেই প্রেমিকার সামনের গিয়ে দাঁড়াবেন। লোনা ঢেউয়ের গর্জন তুলবেন।
‘এপিটাফ অথবা চুক্তিপত্র’ কবিতায় কবি মৃত্যুকে বলেছেন জ্যোতির্ময় পাখি। বুকের মাঝখান থেকে টুপ করে খুঁটে নেয় সুস্বাদু শস্যদানারূপ জীবন। মানবজীবন— বিশেষ করে পুরুষজীবন কেবলই ছায়ার মোহে জীবন আর মৃত্যুর চুক্তিনামায় রেখে যায় অজস্র স্বাক্ষর। কবিতাটি শুরু করেছেন এভাবে,
হয়তো এভাবে একদিন অনূদিত হবে শতাব্দীর নীরবতা— মৌনতা নামে
তোমাদের ভাষাবিজ্ঞানে যুক্ত হল নতুন অধ্যায়— আমি ওই শেওলা সবুজ
সমাধিতে ঘুমিয়ে গেলে তোমরা উদ্ধার কোরো তারাদের স্বরলিপি
কবি মৃত্যুপরবর্তী কালে আগ্রহী পাঠক, অনুসন্ধানী গবেষকের হাত দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্ম আবিষ্কার, পুনরাবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবেন। ‘অলৌকিক অশ্বারোহী’ কবিতায় কবি তাঁর স্বপ্নগুলোকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন। বলেছেন,
সবাই নক্ষত্রের মালিকানার কথা ভাবে, আমি তার আভাটুকু চাই—
কেউ কেউ বলে এ অসুখ কবিতাবাহিত— মেনে নিয়ে চলে যাই
যেদিকে মুখ করে ফুটে আছে রক্তজবাগুলো
এখানে কবি তাঁর সৃজনবেদনার কথাই বলেছেন। মাতৃপূর্ণতা যেমন অপরিমেয় বেদনার মধ্য দিয়ে, তেমনি কবির সৃজনবেদনাও সৃষ্টিকর্ম সার্থক করে তোলে। সেই বেদনা মেনে নিয়েই কবিতা যেন অশ্বারোহী হয়ে জাঞ্জিবার ভানিয়াতু ঘুরে বেড়ায়। জীবনানন্দ দাশের মতোই বিশ্বঘুরে বেড়ায়। কবির বেদনা কিন্তু এই অলৌকিক ভ্রমণে এগিয়ে যান নান্দনিকতার দিকেই— যেদিকে ফুটে আছে রক্তজবাগুলো।
‘আদিম কবিতা’য় নিজেকে আবিষ্কার করেছেন এক অস্থির সময় এবং অনিশ্চিত পরিবেশে। কবি ভুলে যান দিঙনির্ণয়ের পথ। তাই তিনি ইশারা খুঁজে বেড়ান, খুঁজে বেড়ান অনুবাদের ইঙ্গিত। লিখেছেন,
আমাকে নিয়ত লক্ষ্যচ্যুত করে এক দিকভ্রমের পাখি।
…
পতঙ্গতাড়িত যারা, তারাও জানে
আগুনআলিঙ্গন
আদিম আহ্বান আর এইসব ইশারার যথার্থ মানে
চাণক্যের একটি প্রিয় শব্দানুষঙ্গ অনুবাদ। এই শব্দটি তিনি অনেক কবিতায় অনেকভাবে লিখেছেন। যেমন, এ কবিতায় লিখেছেন, ‘আমি কেবল ইশারার অনুবাদ করে চলি
‘নাগলিঙ্গম’ কবিতাটি প্রেমের। প্রেমের ভেতর দিয়েই আসে প্রাচীন বাংলার রহস্যপুরাণ। প্রেমেই শেষ পর্যন্ত কবি বেঁচে থাকেন। আর বেঁচে থাকে তার কবিতা। ‘হৈমন্তিক’ এবং ‘উত্তর হেমন্ত’ কবিতায় প্রকৃতির ভেতর দিয়ে স্থাপিত হয়েছে জীবন্ত প্রিয়ার ভাস্কর্য। ‘হৈমন্তিক’এ লিখেছেন,
গভীর অরণ্যফেরত মাছরাঙা হেমন্তের চিঠি নিয়ে এসেছিল আমাদের গাঁয়ে
সুমিষ্ট আখের ক্ষেত ধরে যেতে যেতে অনুবাদ করেছিল কূলবতী নদীর ভাষা
একদিন জনে জনে তার সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা রটে গেল বলে ঝিঁঝিদের পাড়ায়
বসেছিল ঠুমরি খেয়ালের আসর
প্রকৃতিকে আমরা যেভাবে, যেরূপে দেখি কবি সেভাবে দেখবেন না। তাহলে কেমন করে দেখবেন? তিনি দৃশ্যমানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্যের ইশারাগুলো আবিষ্কার করেন। দেখা চোখের ভেতর দিয়েই অনুবাদ করে গ্রহণ করেন সেই প্রকৃতির ভাষা। দেখা আর অদেখার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে না পারলে কবিতা সার্থক হতে পারে না। ‘উত্তর হেমন্ত’ কবিতায় লিখেছেন,
নবাগত পরিযায়ী পাখিটিকে
দেখে অনুবাদক মাছরাঙা ভাবি… কোদাল কোপানো মেঘে
ছেয়ে গেল পুরোটা আকাশ
এখানে তিনি মাছরাঙাকে প্রকৃতির অপার রহস্যের অনুবাদক বলেছেন। এ কবিতায় ছাতিমের ফুল নস্টালজিয়াও সৃষ্টি করে। ‘স্কুলদিন’ কবিতায়ও আছে নস্টালজিয়া। স্মৃতিকাতরতা তাঁর নাগরিকজীবনের পূর্বজীবনের গ্রামের বালিকার প্রেমকথা।
‘নিশাচর আলোয় শহর’ কবিতায় নাগরিক রহস্যময়তা, বিমূঢ়তা কবির কাছে জাদুকরের মেলে ধরা হাতের তালুর মতো রহস্যপুরী বলে মনে হয়। ‘প্রশ্ন’ কবিতাটিও প্রেমের। স্মৃতিকাতরতা প্রাধান্য পেয়েছে। ‘আষাঢ়ের পঙ্ক্তিমালা’ কবিতাও তাই। তবে এখানে প্রেমের না-পাওয়ার বেদনা আর দূরতর কোনো ধারণা মূর্তিলাভ করেছে। বিড়ালের কাঠবিড়ালী খাওয়ার মধ্য দিয়ে কামনার মৃত্যুদৃশ্য অনুবাদ করেছেন কবি। এটি একেবারেই অভিনব এক শিল্পপ্রকরণ। এখানে বর্ষাঋতুর প্রাকৃতিক শক্তি কবিকে জাগিয়ে তোলে। বসন্ত আর বর্ষা এই দুই ঋতুতে বিরহ কেঁদে ওঠে। উত্তর ভারতের মহান কবি কালিদাস বসন্তের বিরহকে এক চিরন্তন কাব্যরূপ দিয়ে বিশ্বের আঙিনায় স্থাপিত করেছেন হাজার বছর আগেই। কিন্তু বাংলায় বর্ষার বিরহ বসন্তের বিরহের চেয়ে ভয়াবহ। সমীক্ষায় বলে এই ঋতুতে বাঙালির বিরহজনিত আত্মহত্যার পরিমাণ বেড়ে যায়। কারণ এই ঋতুর মেঘের ভেতর আছে রহস্য, আচ্ছন্নতার ভেতর আছে তীব্র এক দেশজ রোমান্টিকতা। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার কবিদের কাব্যের ‘বারোমাস্যা’ অংশে দেখা যায় সেই তীব্র এবং অমোঘ কাতররূপ। যতই ব্যবহৃত হোক এই ঋতুর কথা ফুরাবে না তার আয়োজন এবং প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আর কেউ এই বর্ষা নিয়ে লেখেননি। হাজার হাজার মাইল দূরে বসেও, তীব্র শীতের মধ্যেও তিনি সেই বাংলার বর্ষা নিয়েই কবিতা লিখেছেন। যেন তার ব্যক্তিগত এক বর্ষাঋতু সর্বদাই তিনি বহন করে চলেছেন।
চাণক্যের শীত নিয়েও একটি কবিতা আছে ‘সুদীর্ঘ শীতরাত্রি’। এ কবিতায় আছে পুরনোকে, অতীতকে অতিক্রম করে নতুন উচ্চারণ। শীত নিয়ে রবীন্দ্রপরবর্তী জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু এবং শামসুর রাহমানের কবিতা আছে। বাংলায় অল্পাধিক মাত্র তিন মাস শীত থাকে। এই সময়টা মানুষকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। কারণ মৃত্যুকে হিমশীতল ঘুমের মতো ধারণা করতে আমরা অভ্যস্ত। শরীরের তাপহ্রাস পেলে মৃত্যু আসে, এই ধারণা থেকেই আরোহ যুক্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে আসি যে, বাংলার প্রকৃতির উত্তাপ কমে এলে শীত আসে মৃত্যুর বার্তা নিয়ে। যদিও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে শীতের তীব্রতাই তাদের আবিষ্কারমুখী করে তুলেছে। আমাদের দেশে শীতে আছে আড়ষ্টতা। শীতের আড়ষ্টতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুই সবচেয়ে বেশি সফল এবং সার্থকভাবে কাব্যরূপ দিয়েছেন। চাণক্য বাড়ৈ শীতের ভেতর স্বপ্নমৃত্যুর ধারাবাহিকতা তুলে ধরেছেন। শীতের রাতগুলো দীর্ঘ, যেন ফুরাবে না, যেন অনন্ত এই বোধকে কবি নিজস্ব ভাষায় লিখেছেন, ‘আজ এইখানে যে হরিণীটি বধ হবে, শুনেছি পূর্বজন্মেও সে মরেছিল একই নিয়মে।’
সচেতন মানুষের কাছে মানবজন্মই সবচেয়ে রহস্যময়। এমনকি মৃত্যুর চেয়েও। মৃত্যুকে আমরা অজস্র ঘটনার ভেতর দিয়ে, উপমার ভেতর দিয়ে, উদাহরণের ভেতর দিয়ে এবং অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অবলোকন করি, তাই মৃত্যু ভীতিকর মনে হলেও অনিবার্য বলেই জানি। কিন্তু জন্ম কি অনিবার্য? এই প্রশ্নের উত্তর নাই। আমরা যারা পিতা হয়েছি সন্তানের মুখের দিকে চেয়েও কি বলতে পারি, আমরা ওর জন্যই প্রতীক্ষায় ছিলাম? এই যে সন্তান চোখের সামনে, সে আসলে কে? ওর সৃষ্টিই কি আমাদের যৌনতার পরিণাম? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। সেই মানব জন্মরহস্য নিয়ে লেখা কবিতা ‘জন্ম’। জন্মকে চাণক্য কীভাবে উপস্থাপন করেছেন দেখুন,
অনির্ণীত অন্ধকার থেকে উড়ে আসা গুচ্ছ গুচ্ছ আলোর ফুলকি,
তোমরাই প্রিয় বাল্যবন্ধু আমার— দিয়েছিলে অনন্ত আগুনসান্নিধ্যের
রাত—যদিও জানতাম তোমরা কেউ ছিলে না খসে পড়া তারা—
এমনকি তারাদের খুব কাছের আত্মীয় কোনো—তবু মুঠো ভরে
তোমাদের কুড়াতে চেয়েছি
কবির কাছে জন্মটা আসলে জোনাকজন্ম। আগেই তো বলেছেন গুচ্ছ গুচ্ছ আলোর ফুলকি। ফুলকি সৃষ্টির রূপটাই কবির কাছে জন্মদৃশ্য। ‘প্রতিতুলনা’ কবিতায় প্রেমের এক বিমূর্ত দৃশ্য আঁকার চেষ্টা করেছেন। প্রেম পুরনো হলে অন্য সব দৃশ্যের মতোই ধূসরতা লাভ করে, এটাই কি কবি তুলে ধরেছেন? এখানে প্রেম আর প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে। মাছরাঙার একটি শান্ত দৃশ্য দিয়ে কবিতাটি শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত নস্টালজিয়ার কাব্যরূপ হয়ে আছে কবিতাটি— ‘আমি, তুমি বিষয়ক শব্দাবলি নিয়ে তোমার বিমূর্ত মুখাবয়ব আঁকছি।’
‘কীর্তন’ এবং ‘রাগরাত্রি’ কবিতাদুটি চাণক্যের কবিতার সঙ্গীতময়তার পরিচয় দেয়। প্রথম কবিতাটিতে বাংলার বৈষ্ণব প্রেমের নানা উপাদানে কৃষ্ণকীর্তনের আবহ সৃষ্টি করে। সব শেষে রাধার কৃষ্ণবিরহে খোল করতাল কাঁদে। আর ‘রাগরাত্রি’ কবিতায় উত্তর ভারতের সঙ্গীতমূর্চ্ছনা সৃষ্টি করে। আর কী আশ্চর্য, সেখানে আছে সুফি সঙ্গীতের সুর। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের, খাজা বাবার আধ্যাত্মিক প্রেমের বিচিত্র বিস্তার। মেঘ,বিদ্যুৎ নিয়েই কিন্তু এই সুফি সঙ্গীতের ধারা। সবশেষে মনে হয় চাণক্যের কবিতার ধারণক্ষমতা অনেক।
মোহাম্মদ নূরুল হক
মোহাম্মদ নূরুল হক মূলত কবি। গদ্যেও তিনি সমান দক্ষ। কিন্তু কবিতায় তাঁকে গভীরভাবে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতায় আছে বঞ্চনা, আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণার শিল্পরূপ। ‘রোদের আঁচড়’ কবিতায় কবি দেখেছেন শামুকের মতো নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেও প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। যেভাবে শামুক আবার গুঁটিয়ে যায়। নূরুল হক পুনরায় গুঁটিয়ে যাননি। নতুন দিকের ইশারা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি পুরো বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করেন। তিনি অনুসন্ধান করেন, পতনের নীতি, ঘৃণার ইতিহাস। এ যেন পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরে দৌড়ে পালানো জনতার ভিড়ে অপার কৌতূহল আর পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় জানার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা। চূড়ায় ওঠার যাতনাই এখানে মুখ্য। কারণ সেখানে জায়গা কম। কবি কি তাহলে অল্পতে খুশি নন? বিষয়টা অন্যভাবে বোঝানো যায়, অল্প জায়গায় দ্বন্দ্ব পূর্ণতা লাভ করে না। তাও সত্য। তবে কবি দ্বন্দ্বেও যেতে আগ্রহী নন। তিনি সেখানে গেলে তৃষ্ণা এবং কাক্সক্ষা পূরণ করতে পারবেন না। রোদ যদি হয় সোনালি সম্ভাবনা, সেখানে আঁচড় লাগে। সম্পর্কের বেণী ধরে পতনের পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে গেলেই ইতিহাসে ধূলা জমে। বাতাসেও লেগে থাকে রোদের আঁচড়। আগেই তো বলা হয়েছে কবি পতন দেখেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন না। অপার কৌতূহলে সেই পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে চান। যে পাণ্ডুলিপি ইতিহাসের ধূলার আড়ালে লুকিয়ে আছে।
এই নাও সান্ধ্যনদী, সূর্য মরে গেলে দিয়ো মাতাল চুমুক
আমার পকেটভর্তি তৃষাতুর চৈত্রের আকাশ
মগজে স্লোগান তুলে জেগে থাকে রাতগুলো আলোর কাঙ্ক্ষায়।
‘স্রোতের নামতা’ কবিতায় আছে প্রেমতৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা আর অতৃপ্তির হাহাকার। স্রোতের নামতা না শেখার কারণে কবির তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই।
জ্বলন্ত সূর্যের ঠোঁটে চুম্বন এঁকেছি চণ্ডীদাস।
আয় রজকিনী ঘাটে— রসের দিঘিতে আমি ঢেউ
নদী নদী জল এনে— আয় তৃষ্ণা মেটাবি দিঘির।
‘এপ্রিলের রাত’ সাধারণত আমাদের দেশে সবচেয়ে উত্তপ্ত। এ সময়ও কবির প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিভা, দান ও অনুদান সব হিসাবে চলে আসে। কবির অতৃপ্তি প্রবল হয়। নিজের আয়ুকে বয়স্ক আর বয়সের সাথে তুলনা করেছেন বার বার। অবচেতনে রয়েছে মৃত্যুচিন্তা। যে চিন্তা মানুষকে হয়তো স্থবির করে দেয় অথবা গতিশীল করে তোলে। মৃত্যুভাবনাকে সামনে রেখে কাজ শুরু করলে তা দ্রুত সম্পন্ন হয়। জীবনের আয়ুকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু যদি মৃত্যুভাবনা স্বপ্নপূরণের কাজে লক্ষ্য হয় তখন হতাশা বেড়ে যায়। নূরুল হকের কবিতায় তাই দেখি হতাশা আর না পাওয়ার বেদনা। সব শেষে কবি বলেছেন, ‘তোমাকে পাই না কাছে, স্বপ্নে তবু ধরা দাও বুকে।’
‘লাল মাছি’ কবিতায় যেন কবির তৃষ্ণা কমে গেছে। অনেকটা নির্লিপ্ততা চলে এসেছে। কবিতার শেষে বলেছেন, “কাউকে চাই না আজ সূর্যকান্ত রাতের শয্যায়।” এর আগে তিনি বলেছেন,
আমাদের দক্ষিণের বারান্দায় নাকি বহুদিন
ঘুমিয়েছিল সম্ভ্রান্ত রাত
অথচ রাত্রির গানে কোনোদিন সুর সাধিনি
দক্ষিণের বারান্দা এখানে প্রেমের অভিসাররূপে চিত্রিত হয়েছে। কাছে পাওয়ার পরেও কবি তৃষ্ণা পূরণ করতে পারেননি বলেই এই নির্লিপ্ততা? বঞ্চনাকে পেছনে রেখেই কি কবি এ কবিতা লিখেছেন? বঞ্চনার পাণ্ডুলিপি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ‘জংলি কুসুম’ কবিতাটি। কোনো রাজকন্যা নয়, কোনো স্বর্গের দেবীকেও চাননি কবি। চেয়েছিলেন রক্তমাংসের একজন নারীকে। কাচের দেয়ালঘেরা এক পৃথিবীর ভেতর বাস করেও মনে হয়েছে এই বুঝি ছুঁই ছুইঁ কিন্তু আহারে মানব স্বপ্ন দেয়ালের ওপারেই থাকে। এর আগে কবিতার বুক বরাবর বুক কবি লিখেছেন,
যদি ভুল করে কোনো ভুলফুল ফোটে তোমাদের ছাদে
জেনে রেখো সে ভুল আমি
জেনে রেখো তোমার খোঁপায় ঠাঁই হলো না
তাই ফুটেছি অকালে— হৃদয়ের দাবি নিয়ে জংলি কুসুম।
কবিতাটির নামকরণের ভেতর লুকিয়ে আছে প্রবল আত্মগ্লানি। না পাওয়ার বেদনা মানুষকে নতুন পথ দেখায়, পরিস্থিতির নতুন ব্যাখ্যা দেয়, নতুন রূপকউপমার অলঙ্কারের ইশারা সৃষ্টি করে। হাহাকারের পরিণতি এই জংলি কুসুম। নিজেকেই তিনি এই নামে আখ্যায়িত করেছেন। তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চনা, নির্লিপ্ততা মোহাম্মদ নূরুল হকের মানসিকতার কয়েকটি পর্যায় দেখতে পেলাম। এর পরে কোন পরিণতি অপেক্ষা করছে? সেই অনিবার্য পরিণতি নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ‘যেভাবে সময় কাটে’ কবিতাটি। চরম এক অবস্থার বর্ণনা কবিতাটির শুরু থেকেই।
আমার রাতেরা নিদ্রাহীন, ঘুম গেছে স্বেচ্ছানির্বাসনে। দিনগুলো নির্বান্ধব— দৃষ্টিতে ধূসর দৃশ্য ভেসে ওঠে। সকালে বাজার থেকে কিনে আনি ব্যাগভর্তি মানুষের ঘৃণা।
কবির এই মানসিক অবস্থা মনে করিয়ে দেয় নাগরিক জীবনের প্রাথমিক যন্ত্রণার কথা। কেউ কাউকে এখানে সময় দিতে চায় না। সবাই নিজ নিজ সংঘ আর বন্ধুসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত। কবির নিঃসঙ্গতা এখানে কামড়ে ধরে। কেউ সময় দিতে পারে না। কবি স্বীকারোক্তিতে বলেন, ‘আমি কৃপাপ্রার্থী নই, তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চাই না। শুধু চাই একটু সময়।’
এ কবিতার ভেতর দিয়ে কবিকে পাওয়া যায় নাগরিক যন্ত্রণার জীবনে। অভিজ্ঞতার রাজ্যে একজন ফেরিওলা রূপে। নাগরিক জীবনের যন্ত্রণার রূপ বিচিত্র। প্রেম, কাম, পেশা, নিঃসঙ্গতা, আবাসন, বঞ্চনাসহ নানা ধরনের কষ্ট এখানে ভিড় করে। এগুলো নিয়েই নাগরিক কবিরা সারাজীবন লিখে যান। পেশাগত যন্ত্রণারও থাকে নানারূপ। কেউ একটা চাকরি পাওয়ার জন্য থাকে ব্যাকুল। কোনো রকম একটা চাকরি হলেই দিনগুলো একটা আকার লাভ করে। আবার কেউ চাকরি ছাড়তে পারলে যেন জেলখালাস হন। কারণ সেখানকার পচা পানিতে শ্বাস নেওয়া কষ্টকর। শ্রম এবং মর্যাদার বিষয়েও থাকে জটিলতা। কোনো কোনো কর্মসংস্থানে মেরুদহীনতাই কাম্য। কারণ সেখানে মেরুদ থাকলে প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের ইচ্ছামতো খাটাতে পারে না কর্তৃপক্ষ। কাজেই অমেরুদণ্ডী প্রাণী কেঁচোকেই লোকেরা সাধ করে গালভরা নাম দেয় ‘প্রকৃতির লাঙল।’ প্রতিষ্ঠানগুলোতেও তাই। অমেরুদণ্ডীরাই প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদনার পুরস্কারে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রমোশন, প্রণোদনাসহ নানাবিধ সুবিধা তাদেরই প্রাপ্য। এরাই প্রতিষ্ঠানের উর্বরাশক্তির উৎস। এসব বোধ নিয়েই কবিতা ‘ক্রীতদাসের ইতিকথা’। এখানে কে কত আগে খুলে নেবে নিজের মেরুদ এই প্রতিযোগিতা চলে।
মানুষেরা খুন করে মানুষের আশা, খুন করে আশ্বাসবিশ্বাস
এইসব মানুষের রমণগমনক্রোধ— সবই দাসের মতন।
সব শেষ পঙ্ক্তিতে জানান, আজকাল মানুষেরা ভালবাসে ক্রীতদাস হতে।
‘একটি আষাঢ়ে গল্প’ কবিতায় কতগুলো শব্দানুষঙ্গ জোড়া দিলেই অর্থ বের হয়ে আসে। যেমন, খুচরো আকাশ, মার্কেট, মেঘের কয়েন, শোপিস নক্ষত্র, সেলসগার্ল, ফার্স্টফুড এগুলো মিলে হয়ে যায় ‘আমার পকেট শূন্য’ শব্দবন্ধ। এর পরেও কবি বলেন, ‘আমি যেন মৃত বাঘ, ক্ষুধাহীন পড়ে আছি নীলহীন আকাশের জ্বলন্তগ্রীবায়। ’
‘প্রশ্নসিরিজ’ কবিতায় কবি আবার নাগরিক নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে প্রবেশ করেন রোমান্টিকতায়। মন ফিরে যায় গ্রামের হিজলে বনে আর নিশিডাকা গ্রামে। ‘সংশয়’ কবিতায় হাতাশার মাঝে মাঝে আকস্মিক আশাবাদী মনের জেগে ওঠার কথা লেখা হয়েছে। ‘সময়’ কবিতায় দেখি নাগরিক প্রেমের কথা। এতদিনে কবি যেন নাগরিকজীবনে একটু স্থিতিশীল হয়েছেন। এখানে সান্ধ্যআড্ডায় বন্ধুদের কোলাহলের কথা আছে। কবিতাটি মূলত রতিভাবের।
‘উদভ্রান্ত সন্ধ্যা’ কবিতায় নগরজীবনের আত্মপীড়ন আর ছাঁচেবন্দি হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। সহিষ্ণুতা আর সহনশীলতার নামে মানুষ যেভাবে ছাঁচের আকারে নিজে বিকৃত আকার ধারণ করে তাকেই কবি বলেছেন, ‘এতটা সহনশীল হতে গেলে মানুষে থাকে কে?’
এটাই অমানবিক পরিবেশের বর্ণনা। ‘আলোর কাঙ্ক্ষা’ কবিতায় দেখা যায় প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে বিদ্রোহের সম্ভাবনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ হয় না। কারণ কবি মনে করেন, ‘যত আলো কাঙ্কক্ষা করো—পাবে তার দ্বিগুণ আন্ধার।’
‘ব্যক্তিগত মেঘ পর্যটন’ কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনের চলার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো সত্যের উপমায় উপমিত হয়ে আছে। এ কবিতায় প্রবাদপ্রতিম সত্য উচ্চারণ আছে, ‘তবু সত্য প্রিয় নয় প্রিয় মোহন মিথ্যারা।’
দীর্ঘ কবিতা ‘উত্তরবাঁকের মেঘ’য় আবার কবিকে তার পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে ব্রিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ক্ষুদিরামের নাম উল্লেখ করেও কবি বলেন, ‘জেগে ওঠে সমকালে অতীতের দ্রোহী ক্ষুদিরাম।’
কবি প্রাণের ভেতর ইতিহাসের বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব অনুভব করেন। কিন্তু বিদ্রোহ করা হয়ে ওঠে না। হকের কবিতায় কতগুলো শব্দানুষঙ্গ ঘুরে ফিরে বারবার আসে। মাছি, লালমাছি, নীলমাছি, মাইল মাইল, পান করা, গেলাস গেলাস, নির্ঘুমতা ইত্যাদি। এগুলোর বৃত্তানুপ্রাসে কবির স্বভাব অনুমান করা মোটেই কঠিন না।
‘এইসব চবি এঁকে পান করি গেলাশে গেলাশে’ কবিতায় কবির একাতীত্ব শেষ পর্যন্ত অন্ধাকরে একা বসে থাকার ছবি আঁকে। ‘উপবিকল্প সম্পাদকীয়’ কবিতায় যেন এতদিনের মানসিক চাপ বিদ্রোহ হয়ে ফেটে পড়ে। কবির যেন এক আত্মচিৎকার এই কবিতা। এ যেন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মাওলানা ভাসানির সেই বিপুল উচ্চারণ ‘খামোশ’! কবিতাটি যে হঠাৎ ক্ষেপে ওটার তা প্রথম লাইনেই উল্লেখ করা হয়েছে।
নগরে এসেছি বলে
ভুলে যাইনি আজও সেই সমুদ্রের ডাক
কেউ লাঠি হাতে সামনে দাঁড়ালে
আজও নির্ভয়ে বলে দিতে পারি— কাউকে চুদি না।
এই বেপারোয়াপনা কিন্তু প্রায় দুই কোটি জনসংখ্যার এক বিশাল দুর্গের দ্বারে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ রেখে চিৎকার করার মতো। কারণ কবি সত্যিই কোনো বিদ্রোহ করেন না। বিপ্লব করেন না। পরিবর্তমান পরিস্থিতির চাপে পড়ে নিজেকেই পুনর্বিন্যাস করেন। ‘সম্ভ্রান্ত রাত্রির দীর্ঘশ্বাস’ কবিতায় দেখি যেন অনেক দিন পরে লালনের সন্ধানে নামেন। অনেক দিন ধরে একতারা হাতে নেননি। বাঙালি পুরুষের পথিকজীবনে বাউল পথ আর একতারাই নির্দেশকের কাজ করে। পেশাগত অনিশ্চয়তা, বিতৃষ্ণা আর তিক্ত অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দেয়, ‘শরীরের ক্ষুধা যত বাড়ে, তত কমে পাপপুণ্য ভয়।’
‘মধ্যরাতের ডায়েরি’ সিরিজের কবিতাগুলো নাগরিক জীবনের বৃত্তিগত যন্ত্রণার ফসল। প্রথমটিতে অতীতচারিতা বা স্মৃতিকাতরতা থাকলেও পরেরগুলোতে পেশাগত দায়, আর নিরানন্দের দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পেয়েছে। কৈশোরের স্মৃতি তাড়া করে। কোনো কিশোরীর স্মৃতি চোখজুড়ে নেমে আসে ক্লান্তির অবসরে। পত্রিকা অফিসে সাব এডিটর রাত জেগে কাজ করেন টেবিলে। তার চোখ ভুলে যায় স্বজনের মুখর রঙিন শৈশব। মধ্যরাতে উড়ে যেতে মনে চায় কিন্তু যাবেন কোথায়? পেশার কামড় ঘোড়ার কামড়ের মতো, দাঁত বসে যায় সহজে ছাড়ানো যায় না। মাইল মাইল পথ যেতে হবে। লাল অন্ধকার কেটে যেতে এগোতে হবে। রাত জেগে সংবাদ সম্পাদনার পরে বাকি রাতগুলো নির্ঘুম কাটে। তখনই শৈশব আর কৈশোরের স্মৃতির কামড় লাগে চোখে। ভীষণ এক দুঃসহ আর শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। এ যেন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান।
যে আমাকে এনে দেবে সাত শত তের নদী পার হয়ে প্রিয়তম ঘুম। কখনো ঘুমকাতুরে ছিলাম না, অথচ এখন ঘুমের জন্য ব্যাকুল। কতকাল ঘুমাই না, নির্ঘুম কাটাই যত মাতাল আন্ধার। সে কথা তুমিও জানো, তুমিও চেন সেব উদ্ভ্রান্ত— রাত্রির চিত্রকল্প।
মোহাম্মদ নূরুল হকের কবিতা ছন্দে এবং ছন্দহীনতায় সমুজ্জ্বল। তিনি সমকালের একজন চিত্রকর। তার কবিতায় মানুষের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের চিত্রভাষা নতুন ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে নিজস্ব ভাষিক প্রকরণে।
নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা কবিতা যা রচিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে বা সমালোচিত হয়েছে তার সবই যে মহাকালের পর্দাজুড়ে টিকে থাকবে এমনটি না হওয়াই স্বাভাবিক। এর মধ্যে অনেক লেখা মরা গাছের মতো শুকিয়ে থাকবে কিছুদিন তারপরে ঝরে যাবে। লেখার ধারা প্রবল স্রোত হয়ে এগিয়ে যাবে কিছুদূর গিয়ে নতুন চরে মাথা গুঁজে মরানদীর মতো নিস্তরঙ্গ হয়ে যাবে। তবে যা কিছু টিকে থাকবে তা নতুনত্ব নিয়েই থাকবে। পুরনোকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে এগোনো যাবে না। এখান থেকেই একদিন আবর্জনা সরিয়ে হিরার মতো জ্বলজ্বল করে উঠবে অমর কাব্য।
পড়তে পারেন: সমকালীন পাঁচ কবির কবিতা