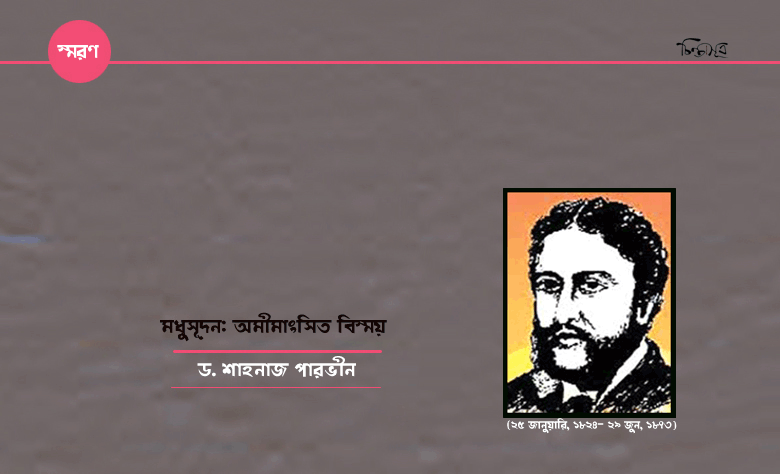 ইংরেজদের অধীনে ভারতবর্ষের সীমানা তখন ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর সিংহল, আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ, সিঙ্গাপুর, মালয় উপদীপ অঞ্চল জয় করে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আমহার্স্ট। ভারতের পূর্বাংশ দখলের পর ইংরেজ সৈন্যরা যখন আফগান দখলে ব্যস্ত, সেই কাছাকাছি সময়ে কবি মধুসূধন দত্ত অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর যশোর জেলার কেশবপুরের কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন দত্ত ছিলেন এক স্বতন্ত্র চেতনার কবি। এক অমীমাংসিত বিস্ময়। যে বিস্ময়ের আজও কোনো কাব্যিক মীমাংসা হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে তিনি কতটুকু অনতিক্রম্য হবেন, সেটাও গবেষণার ব্যাপার। বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিতে এক আধুনিক জীবনবোধ ও নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি, যা আজও খরস্রোতা নদীর মতোই বহমান।
ইংরেজদের অধীনে ভারতবর্ষের সীমানা তখন ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর সিংহল, আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ, সিঙ্গাপুর, মালয় উপদীপ অঞ্চল জয় করে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আমহার্স্ট। ভারতের পূর্বাংশ দখলের পর ইংরেজ সৈন্যরা যখন আফগান দখলে ব্যস্ত, সেই কাছাকাছি সময়ে কবি মধুসূধন দত্ত অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর যশোর জেলার কেশবপুরের কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন দত্ত ছিলেন এক স্বতন্ত্র চেতনার কবি। এক অমীমাংসিত বিস্ময়। যে বিস্ময়ের আজও কোনো কাব্যিক মীমাংসা হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে তিনি কতটুকু অনতিক্রম্য হবেন, সেটাও গবেষণার ব্যাপার। বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিতে এক আধুনিক জীবনবোধ ও নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি, যা আজও খরস্রোতা নদীর মতোই বহমান।
মধুসূদন দত্তের প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বশিক্ষায় কোনো ত্রুটি ছিল না। সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঠশালাতেই তার শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তীসময়ে কলকাতার হিন্দু কলেজ ও বিশপ কলেজে লেখাপড়া করেন। এ সময়েই তিনি পরিচিত হন দেশি-বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে। কলকাতার ছাত্রজীবনে তিনি আয়ত্ত করেছেন বারোটি ভাষা—বাংলা, ইংরেজি, ফারসি, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, ল্যাটিন, গ্রিক, হিব্রু, ফরাসি, জার্মান ও ইটালিয়ান।
এছাড়া শৈশবে রামায়ণ, মহাভারত ও চণ্ডীমঙ্গল থেকে নিয়েছেন গল্পরস এবং কলেজ জীবনে বায়রণ ও সেক্সপিয়র হয়ে উঠলেন তার প্রিয় কবি। এ সময়েই তিনি বিশ্ব সাহিত্যের প্রতি অদম্য স্পৃহায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো ও মিল্টনের কাব্যরসে তিনি দিনে দিনে ঋদ্ধ হয়ে উঠলেন। ওই সময়ে তার পঠিত দেশি-বিদেশি প্রায় সব সাহিত্যেই সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত এবং যুগযন্ত্রণা ছিল প্রায় অনুপস্থিত। বরং পৌরাণিক জীবনধারার শৈল্পিক কুশলতার নির্মান ছিল অগ্রগণ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তও সময়ের সেই সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বের হতে পারেননি। তিনি তার লেখনিতে দেশি-বিদেশি পুরাণের সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন। কিন্তু সেখানে ছিল এক ধরনের সুক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য বোধ, যা তাকে সবার চেয়ে আলাদা করেছে, অনন্য করেছে, একক সত্তা হতে সহায়তা করেছে। তিনি হাজার বছরের বাংলা কাব্যের ধর্মনির্ভর ধারার বিপরীতে প্রথম মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার শিল্পভাষ্য নির্মাণ করেছিলেন। জাগতিক মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর বিশ্বাস। তাই অধ্যয়ন, প্রজ্ঞা ও প্রতিভার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি হয়েছিলেন যুগস্রষ্টা।
মধুসূদনের অস্তিত্ব ও কৃতিত্ব প্রতিটি বাঙালি সাহিত্যানুরাগী সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে অনুভব করে। তাঁর নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, সনেট, ছন্দ, অলঙ্কার বিশিষ্ট পদ রচনারীতি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে যুগস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ আসন নিঃসংশয়ে দান করেছে। বিদেশি সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার থেকে দস্যুর মতো দুই হাত ভরে কত ঐশ্বর্য তিনি পেয়েছেন, লুটে এনে তাঁর শূন্য মাতৃভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছেন। বাংলা কাব্য সাহিত্যের গতি স্রোতকে সম্পূর্ণ নতুন এক খাতে তিনি বইয়ে দিয়েছেন, হিমালয়ের বক্ষ বিহারিণীর নির্ঝরিণীকে তিনি কালনাগিনী স্রোতস্বিনী জাহ্নবীতে পরিণত করেছেন। মধুসূদন বাংলা কাব্য জগতের ভগীরথ। ভগীরথ নির্দেশিত স্রোতপ্রবাহ যেমন জন্ম দিয়েছিল ভগীরথীর, তেমনি মধুসূদন জন্ম দিয়েছিলেন নতুন কালের, ভিন্ন প্রবাহের। এক অমীমাংসিত বিস্ময়ের। সেই প্রবাহের নতুন ধারার নতুন কালটিকে বলা হয় আধুনিক কাল। আধুনিক কালের বিপুল বিশাল এবং বিচিত্র সাহিত্য ধারার সংমিশ্রণে মধুসূদন সৃষ্টি করেন এক নতুন চেতনা।
বাংলা ভাষায় রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ [ দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রচিত এবং একই বছরের মে মাসে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের যাবতীয় ব্যয় বহন করেছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এই অর্থ ব্যয়ের পেছনে ছোট্ট একটি ঘটনা আমাদের জানা। অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার পর মধুসূদন দত্ত গভীরভাবেই বলেছিলেন, এটি ছন্দের উপযোগী ভাষা। তাঁর এ মন্তব্যকে কটাক্ষ করে যতীন্দ্রমোহন বলেছিলেন, বাংলাভাষা অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অমিত্রাক্ষর ছন্দে আপনি কোনো কাব্য রচনা করতে পারলে আমি তা নিজ ব্যয়ে ছাপিয়ে দেব। মধুসূদন এ মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে বলেছিলেন, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা। বস্তুত সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য ও শব্দ সম্পদই বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্ভব করেছে। শুধু মুখের ভাষায় জবাব দিয়েই চুপ থাকেননি তিনি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সাধনা, পাণ্ডিত্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে রচনা করেছিলেন তিলোত্তমাসম্ভভ কাব্য-এর প্রথমসর্গ। মহাকবি মধুসূদন দত্তও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সম্মান জানিয়ে তার নামেই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন। এ কাব্য বাংলা পয়ারের গতানুগতিক ভঙ্গির বিরুদ্ধে কাব্যিক প্রতিবাদ।
ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল অটল;
যেন উর্ধ্ববাহু, সদ্য, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী। নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
গ্রন্থের প্রথমেই এখানে ধবল গিরির যে বর্ণনা কবি এঁকেছেন, তার ঋজুতা তিনি রক্ষা করেছেন পুরোপুরি। বিশ্বনিয়ন্তার হাতে নির্মিত, তিল তিল করে যে সৌন্দর্য দিয়ে তার অবয়ব গঠিত, সেই সৌন্দর্যকে তিনি উপমার পরে উপমা গেঁথে সাজিয়েছেন। সৃষ্টির নানা উপকরণের সৌন্দর্য বর্ণনার মাধ্যমে তিনি তার শ্রষ্টাকে স্মরণ করেছেন। যে পৌরাণিক তিলোত্তমাকে উপলক্ষ করে দেবগণ অসুরমুক্ত স্বর্গ লাভ করেন তার পুক্সক্ষানুপুক্সক্ষ বর্ণনায় নিখুঁত করেছেন। ছন্দ ব্যবহারের নতুনত্বের পাশাপাশি এই ক্লাসিক কাহিনীর মধ্যে রোমান্টিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপানি? কবি, দেবি, তব পদম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ী!
তব কৃপা-মন্দর দানব- দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ- দেহ এ দাসেরে
যে কোন সৃষ্টিশীল কাজ করবার আগে আমাদের কাজটি যথার্থভাবে সম্পাদনের জন্য আমাদের শ্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি। তেমনি মহাকবি মাইকেলও তার বাগদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন। এটি মহাকাব্য রচনার একটি রীতি। মধুসূদন সেই রীতি অনুসরণ করেছেন।
কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চিন? যে দূর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
হে বিশ্ব বিনোদিনী দেবী তুমি বলো তোমার কি কোনো কাজ এ জগতে অসাধ্য আছে? তবে তুমি আবির্ভূত হও। তুমি আবির্ভূত হয়ে করি হৃদয় পদ্মাসনে অধিষ্ঠান কর। কল্পনা সুন্দরী, হৈমবতী, কিঙ্করী তোমার শ্বেতভূজে সঙ্গে আনো। এ দাসেরে যদি তুমি বর দাও তবে তোমার প্রাসাদের মাতঃধ্বনি, জয়োধ্বনি পুরো ভারতবর্ষ শুনতে পাবে। সত্যি কবির সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। কবির কণ্ঠ নিঃসৃত জয়োধ্বনি আজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে পুরো বিশ্বময় বিগলিত ধারায় প্রবাহিত।
সুন্দ ও উপসুন্দাসুর- মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে,—দোহে পতিপরায়ণা।
তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিফু, কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে;
তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে দেবতাদের হৃতস্বর্গ পুনরুদ্ধারের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। শক্তিমান দুই অসুর ভাতা সুন্দ ও উপসুন্দ। এরা সুরলোক থেকে দেবতাদের একসময় বিতাড়িত করে দেয়। রূপবতী তিলোত্তমার কুহকে দানব ভ্রাতৃদ্বয় পারষ্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করে। অতঃপর অসুরের দৌরাত্মমুক্ত স্বর্গলোক দেবতাদের হস্তগত হয়। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার পর তিনি বাংলা সাহিত্যের অমর মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য ১৮৬১ খ্রি. রচনা করেন।
মেঘনাদবধ কাব্য-এর গল্প নেওয়া হয়েছে রামায়ণ থেকে। রাম রাবণের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে এ কাব্যে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। রাম, লক্ষণ, সীতা, রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা সবাই পৌরাণিক চরিত্র। এরা কেউই সমকালীন নারী পুরষ নয়। মেঘনাদবধ মহাকাব্যের মাধ্যমে তিনি তাদেকে সমকালীন করার প্রয়াস পেয়েছেন।
মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেই তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। তৎকালীন যাপিত জীবনের বণার্ঢ্যতায় এ মহাকাব্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার স্রোত বয়ে গেছে। যদিও পরাধীন ভারতের দাসত্বের যন্ত্রণা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিলেন তারও আগে থেকেই। তাই বৃহৎ শক্তির অত্যাচারে জর্জরিত ক্ষুব্ধ রাবণ বঙ্গ সন্তানের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দেয় এ মহাকাব্যে। যে বঞ্চনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, সেই বঞ্চনা কি তার পিছু ছেড়েছিল? না সামাজিক ভাবে, না কাব্যিক ভাবে তিনি তাদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। বরং তার গাত্রবর্ণ এবং সংস্কৃতি তাকে খুব সুক্ষ্মভাবে তাদের থেকে পৃথক করেছিল। যদিও তিনি ছিলেন এক উচ্চবৃত্ত জমিদার পরিবারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী সন্তান। সমাজে প্রচলিত এই বৈষম্যের কারণেই একদিন বিশ্প কলেজের ভোজন কক্ষের গ্লাস প্লেট ভেঙেছিলেন। সবাই খ্রিস্টান। তবু শুধু ইউরোপীয়দের মদ দেওয়া হতো পানীয়রূপে। কিন্তু দেশীয় খ্রিস্টানরা তা থেকে ছিল বঞ্চিত। শুধু খ্রিস্টানই বা বলি কেন, তিনি তার ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনে পরাধীন ভারতের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আচরণেও আঘাত পেয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে তিনি অনার্য রাবণের হাতে আর্য রামের লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন।
প্রথম সংস্করণে এ কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল দুটি খণ্ডে (১৮৬১ খ্রি.)। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হলে তার কাব্য সৌন্দর্য ও ছন্দ নিয়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক সহৃদয় সমালোচনায় লিখেছিলেন—‘যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল, বর্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞানহয়, যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করূণারসে আদ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষস্থলে ধারণ করিবেন ইহার বিচিত্রতা কি?’
এই মহাকাব্যে কবি কখনো ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকীর পদতল থেকে পুষ্পহরণ করছেন, কখনও বা নতুন কুঞ্জ সৃষ্টি করে নতুন নতুন পুষ্পের বিস্তৃতি করছেন। এখানে ইন্দ্রজিৎ জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রী রাম চন্দ্রের যমপুরী দর্শন, পঞ্চবটি স্মরণ করে সরমার কাছে সীতার আক্ষেপ, লক্ষণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ, সর্বোপরি দেশ প্রেমের এক নিখুঁত চিত্র অপরূপ বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে—অনিসন্ধিৎসু পাঠক সমাজে যা আজও এক বিরল বিস্ময়।
ব্রজাঙ্গনা কাব্য গ্রন্থটি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। যদিও কাব্যগ্রন্থটি কবি মেঘনাদবধ কাব্য গ্রন্থ লিখবার আগেই লেখা শুরু করেন। ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হলে এ সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন—‘ইহা কৃষ্ণবিরহাতুরা রাধিকার বিলাপস্বরূপ কয়েকটি গীত। রচনা বেশ কোমল ও মধুর বোধ হইল। মাইকেলী ক্রিয়ার ভাগ ইহাতে অতি অল্পই আছে। কবি সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন: ব্রজাঙ্গনা কাব্য রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটি খণ্ডকাব্য। এখানে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলীর আধুনিক রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। এ কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে রাধিকার বিরহ যাতনার গান।’
কেউ কেউ ব্রজাঙ্গনা কাব্য কে সীমাবদ্ধভাবে গীতি কবিতা বললেও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন অন্যভাবে—‘বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য হেমবাবুর কবিতাবলী—ইহাই বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।’
ব্রজাঙ্গনা’র কবিতাগুলোর কাঠামো এবং শিল্পরূপ গ্রীক ওড হতে অভিন্ন। মধুসূদন সাহিত্যের যে ধারায় হাত দিয়েছেন তিনি সেই ধারার প্রচলিত কাঠামোর অভিনবত্বের গৌরবে ধন্য হয়েছেন। মধুসূদন একইসঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্য এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য-এর মতো দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সৃষ্টির সার্থক স্রষ্টা।মেঘনাদবধ কাব্যে দিগন্তভেদী রণভেরীর সুতীব্র নিনাদ আর ব্রজাঙ্গনার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত-মথিত সুমধুর বংশীধ্বনি সত্যিই বিস্ময়কর। বাঙালি সমাজের প্রতিভূ প্রেমিক কবির রাধাকে তিনি মানবিক করে এঁকেছেন। রাধা মানবী। বিরহ বিধুরা বাঙালি রমণীমাত্র। ব্রজাঙ্গনার মূল কথা ও সুর প্রেম- বিরহ, যদিও প্রকৃতি এর গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ। নিসর্গ চেতনার পরিচ্ছন্ন পরিচয় এতে ব্যপ্ত। কবি লিখেছেন:
কে ও বাজাইছে বাঁশী স্বজনি,
মৃদু, মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লেঅ মনে?
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?
ব্রজাঙ্গনাকে ভিন্নজনে ভিন্ন চোখে বিচার করলেও মানবীয় প্রেম ও মানবীয় মিলনাকুতিকে কেউ অস্বীকার করেন নি। বরং বৈষ্ণব প্রেম ধর্মের সাথে মিলেল চেয়ে অমিল বেশি। তাই এর পরিপ্রেক্ষিত সর্বজনীন ও সার্থক।
বীরাঙ্গনা কাব্য ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রচিত হয় এবং প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে। পত্রাকারে এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হলে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন—‘এখানিও অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিবদ্ধ। শকুন্তলা, তারা, রুক্সিণী, কেকয়ী প্রভৃতি ১১ জন অঙ্গনার দুষ্মন্ত, সোম, দারকানাথ, দশরথ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রিয়তমগণের নিকট লিখিত ১১ খানি পত্রিকা লইয়া এই কাব্য বিরচিত। এ কাব্যগ্রন্থের চরিত্রগুলোও পৌরাণিক। মানবিক নয়। বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম পত্রটি শকুন্তলার।’
শকুন্তলা তার জনক জননী কর্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়ায়, কম্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ—অতিথির যথাবিধি অতিথি সৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসাক্ত হন। পরে রাজা তাহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ধবিধানে পারণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত স্বরদরশ গমনান্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলঅ রাজ সমীপে এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।
পত্রের শুরুতেই কবি লিখেছিলেন
বন-নিবাসিনী দাসী নামে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
কবি বীরাঙ্গনা কাব্যে র কাহিনী ও চরিত্র আহরণ করেছেন রামায়ন ও মহাভারত এর আঙিনা হতে। ইটালির কবি ওভিদের হিরোইদস কাব্য মধুসূদন প্রেরণা অনুভব করেছিলেন হিরোইদস কাব্যের পত্রারীতি অনুসারে বীরাঙ্গনা কাব্যটি রচিত। শকুন্তলা, তারা, কৈকয়ী, সূর্পনখা, দ্রৌপদী, ঊর্বশী ইত্যাদি পৌরাণিক নারীকুল তাদের অন্তরলোকের গভীর তলদেশ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।
অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে বাংলা ভাষাকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা কাব্যে রচনা করেন সনেট। সনেট শব্দটির অর্থ ‘মৃদু ধ্বনি’। অল্প কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে সুর তুলে, আবেগের একটি শিখরকে স্পর্শ করার চেষ্টা থাকে বলেই চতুর্দশ পদীর এ নাম। বাংলা ‘চতুর্দশপদী’ এই নামের আড়ালে পঙক্তি সংখ্যার নির্দেশটুকু আছে। মূল তাৎপর্যের কোন ইশারা নেই। সনেটের রূপকল্প সম্পূর্ণরূপে রীতিবদ্ধ। পঙক্তির মত ছন্দও নির্দিষ্ট। এই ছন্দের হাত ধরে বাংলা নাটকের যথার্থ মুক্তি ঘটে। ইটালিতেই ‘সনেট’ কাব্যরূপের জন্ম। তবে প্রসার ঘটে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র। ইউরোপের বাইরেও সবখানে। ইটালির শ্রেষ্ট সনেট রচয়িতা দান্তে ও পেত্রার্ক। সনেটের মিলের যে সুত্রটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটা পেত্রার্কেরই পদ্ধতি। ইংল্যাণ্ডে বিখ্যাত সনেট রচয়িতাদের মধ্যে শেকস্পিয়র, মিল্টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।
সনেট একান্ত ভাবেই গীতিকাব্যধর্মী, ভাবগম্ভীর এবং ছন্দোবদ্ধ সত্ত্বেও আবেগচঞ্চল। বোধহয় তীব্র আবেগের বিস্তারকে সংক্ষিপ্ত আয়তনে নিয়ে আসার জন্যই এমন হয়। কিন্তু কোন বন্ধনই বড় কবির কাছে কোন বন্ধন নয়, বরং মুক্তিরই ক্ষেত্র। কারণ আমরা জানি, মাইকেল মধুসূদনের খ্যাতি শুধু সনেট প্রবর্তনের জন্য নয়, উঁচু দরের সনেট রচয়িতা হিসেবেও। তিনি এই ছন্দেই প্রথম রচনা করেন “তিলোত্তমাসম্ভব” (১৮৬০ খ্রি.) কাব্য এবং দীর্ঘ কাব্য সাধনা শেষে ‘সমাপ্তে’ নামক সনেটে চতুর্দ্দশপদী কবিতার সমাপ্তি টানেন। যদিও তিনি নাটক ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০ খ্রি.) লেখার সময় অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করেন।
তার সনেট সংখ্যা একশ’ আটটি। এই সনেট গুলোর মধ্যে একান্নটিতে তিনি ভাবের আবর্তন বিভাগ রক্ষা করেন নি এবং এই দিক থেকে মিল্টনের সঙ্গেই তার মিল বেশি। তাছাড়া পের্ত্রাক ও শেক্সপীয়রের প্রেম বর্ণনার আদর্শ মিল্টন যেমন ভেঙ্গে দিয়েছেন তেমনি মধুসূদনও নানা বিষয় নিয়ে সনেট লিখেছেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব তিনি তৎকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে সম্পূর্ণ নতুন কাব্যধারার প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা আজ তার জন্মের ১৮৯ বছর পরও আধুনিক এবং অনতিক্রম্য। তাই বাংলা সাহিত্য যতদিন থাকবে ততদিনই তিনি বর্তমান সময়ের মতই সাহিত্যাকাশের এক অমিমাংসিত বিস্ময় হয়ে আলোকজ্জ্বল পৃথিবীর কর্ণধার হয়ে জ্বলজ্বল করবেন।


