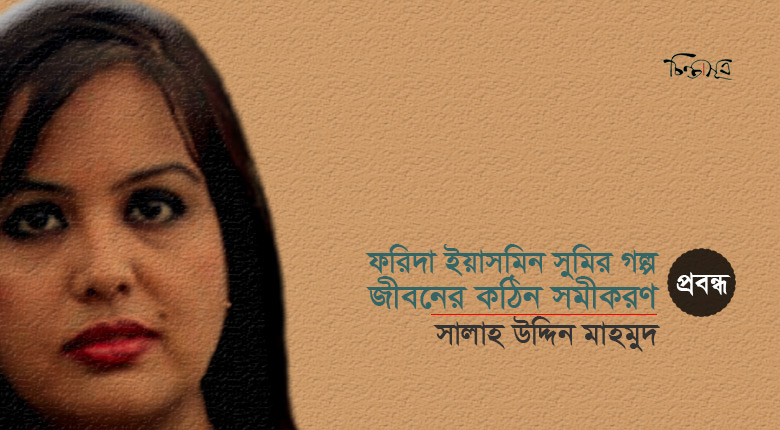 জীবনের কিছু গল্প থাকে, যা হৃদয়ের গভীরে দাগ কাটে। পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। নিজের না বলা কথাগুলো খুঁজে পায় মলাটবন্দি কাহিনিতে। ভাবনার অতলে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর এ কাজটি যিনি করেন; তিনি কথাশিল্পী। জীবনের যেকোনো কাহিনিকে শিল্পে রূপান্তর করাই তার কাজ। এ কাজ যিনি করতে পারেন; তিনি সফল। তার কথাশিল্প মানুষের অন্তরকে নাড়া দিতে বাধ্য। এমনই কিছু গল্প আমার চোখে পড়ে প্রথমত সাহিত্যের ওয়েবম্যাগ চিন্তাসূত্রের মাধ্যমে। তারপর হাতে পাই তিনটি গল্পগ্রন্থ। সেই লেখকের নাম ফরিদা ইয়াসমিন সুমি। ব্যক্তিগত অপরিচয়ের পরও যার গল্প আমাকে আকৃষ্ট করে। অনেক দিন ধরেই নির্মোহ একটি আলোচনার তাগাদা অনুভব করি। সে-সব অনুভূতি বা পাঠের বিশ্লেষণই তুলে ধরার চেষ্টা করবো এই প্রবন্ধে।
জীবনের কিছু গল্প থাকে, যা হৃদয়ের গভীরে দাগ কাটে। পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। নিজের না বলা কথাগুলো খুঁজে পায় মলাটবন্দি কাহিনিতে। ভাবনার অতলে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর এ কাজটি যিনি করেন; তিনি কথাশিল্পী। জীবনের যেকোনো কাহিনিকে শিল্পে রূপান্তর করাই তার কাজ। এ কাজ যিনি করতে পারেন; তিনি সফল। তার কথাশিল্প মানুষের অন্তরকে নাড়া দিতে বাধ্য। এমনই কিছু গল্প আমার চোখে পড়ে প্রথমত সাহিত্যের ওয়েবম্যাগ চিন্তাসূত্রের মাধ্যমে। তারপর হাতে পাই তিনটি গল্পগ্রন্থ। সেই লেখকের নাম ফরিদা ইয়াসমিন সুমি। ব্যক্তিগত অপরিচয়ের পরও যার গল্প আমাকে আকৃষ্ট করে। অনেক দিন ধরেই নির্মোহ একটি আলোচনার তাগাদা অনুভব করি। সে-সব অনুভূতি বা পাঠের বিশ্লেষণই তুলে ধরার চেষ্টা করবো এই প্রবন্ধে।
তার আগে সংক্ষেপে জেনে নেবো কথাশিল্পী ফরিদা ইয়াসমিন সুমি সম্পর্কে। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। আমি তার গল্পকার সত্তা নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করবো। নিজেও একজন গল্পকার হিসেবে তার গল্পের সঙ্গেই আমার পরিচয় বা ওঠাবসা। সমকালীন গল্পকাররা কী লিখছেন, কেন লিখছেন, কিভাবে লিখছেন—এসবের জবাব খুঁজতে গিয়েই আবিষ্কার করেছি তার গল্পের ধরন, নির্মাণকৌশল ও বৈশিষ্ট্য। গল্প পড়ার আগে তার জীবনী পড়ে নেওয়া আমার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। গল্পকারের জীবন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে গল্প পড়ে তৃপ্তি পাই না। তাই আগেই জেনেছি, এ গল্পকারের জন্ম ৪ অক্টোবর ১৯৭৪। জন্ম ঢাকায় হলেও বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামে। বাবা মো. জাকারিয়া, মা মাহমুদা বেগমের চার সন্তানের মধ্যে তিনি প্রথম। তিনি পেশায় প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।
ফরিদা ইয়াসমিন সুমির শিক্ষাজীবন কেটেছে চট্টগ্রামেই। নাসিরাবাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং সরকারি হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন ১৯৮৯ ও ১৯৯১ সালে। এরপর চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক সম্পন্ন করে যোগ দেন সরকারি চাকরিতে। পরে একই মেডিক্যাল কলেজ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি ‘ডিজিও’ ও ‘এমএস’ সম্পন্ন করেন। সুমি চিকিৎসাসেবা ও লেখালেখির পাশাপাশি আরও কিছু সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত আছেন। তিনি অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত কিশোরী ও নারীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দেন। এছাড়া প্রজনন-স্বাস্থ্য সচেতনতার উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ‘ইচ্ছেডানা’। বন্ধ্যাত্বসহ নারীদের অন্যান্য রোগের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন ‘জেনেসিস হেলথ অ্যান্ড ফার্টিলিটি কেয়ার’।
এখানেই শেষ নয়, তিনি ১৯৯৭ সালে ‘লাক্স-আনন্দবিচিত্রা ফটোসুন্দরী’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ‘ফটোসুন্দরী’ নির্বাচিত হন । স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল মঞ্চ ও টিভি নাটকে। অংশ নিয়েছেন বিজ্ঞাপনচিত্রে। এখনো ভালোবাসেন আবৃত্তি করতে। প্রকৌশলী স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে সাহিত্য সংসারেও সরব আছেন দীর্ঘদিন ধরে। এক ডজনের বেশি বই প্রকাশ হয়েছে তার। কবিতা, গল্প সংকলন ও প্রবন্ধ মিলিয়ে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চৌদ্দ। এরমধ্যে কবিতার বই দশটি, গল্পের বই তিনটি এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক বই লিখেছেন একটি। তার গল্পগ্রন্থসমূহ হচ্ছে—পাতা ফুল কাঁটা (২০১৮), যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের (২০১৯) এবং হাজার আয়নার ঘর (২০২০) । তিনি ইমদাদুল হক মিলনের ‘লীলা’ নাটকে অভিনয় করেছিলেন। যা প্রচারিত হয়েছিল চ্যানেল আইয়ের উদ্বোধনী নাটক হিসেবে। আর মিলনের ধারাবাহিক নাটক ‘মন হারাবার দিন’ও উল্লেখযোগ্য। যা প্রচারিত হয়েছিল এটিএন বাংলায়। সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসেবে বিশাল বাংলা সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬ এবং বাংলাদেশ কবিসভার (বাকস) বিশেষ সম্মাননা লাভ করেছেন।
ওটা করিয়ে রিপোর্টসহ যোগাযোগ করবেন।’ (জন্ম) এমন বিষয় মানব জীবনে জরুরিও বটে। এমনকি পাঠকের জন্য শিক্ষণীয়। ফলে একেবারে মন্দ নয়। তবে পাঠকের কাজে আসবে না, এমন কোনো বিষয় না আনাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছেন লেখক। বিচক্ষণতার পরিচয়ও দিয়েছেন তিনি।
এই যে তার জীবনে সম্পর্কে আমরা জানলাম, তারও বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে। যা আলোচনার মধ্যেই আপনারা জানতে পারবেন। কারণ কোনো মানুষই তার অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারেন না। কল্পনাও অনেকাংশে অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিনির্ভর হয়ে থাকে। আর একজন কথাকারের যাবতীয় কাহিনি উঠে আসে তার আশপাশ থেকেই। তাই তো দেখতে পাই, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার তিন বছর পর জন্ম নেওয়া লেখকের অনুভূতিতে মুক্তিযুদ্ধ মিশে আছে আবেগঘন হয়ে। তার গল্পে মুক্তিযুদ্ধও বিশিষ্টতা লাভ করে। যদিও দেশপ্রেমিক সব লেখকের কলমেই মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে। তবে তার গল্পে মুক্তিযোদ্ধার অন্তরের বাসনা সুতীব্রভাবে ফুটে ওঠে। গল্পের চরিত্র মাহবুবের ভাষায় বলতে হয়, ‘শান্ত হও মা। এ রকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা জরুরি। মনে রেখো, শুধু ময়দানে গিয়ে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করাই নয়, বরং পেছন থেকে তোমাদের সাহায্য, তোমাদের প্রেরণাও দেশকে স্বাধীন করতে ভীষণ প্রয়োজন। হায়েনাদের কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে প্রত্যেকের নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ববান হতে হবে।’ (সবুজ সোয়েটার) যুদ্ধ পরবর্তী দেশের ভয়াবহ তখন বুঝে না উঠলেও বড় হতে হতে তা অনুধাবন করেছেন লেখক। মুক্তিযোদ্ধাদের টগবগে চোখ দেখেছেন খুব কাছ থেকে। রাজনৈতিক উত্থান-পতন অবলোকন করেছেন গভীরভাবে। তার একটি প্রভাব তার লেখায় থাকাটাই স্বাভাবিক।
কখনো কখনো তার গল্পে দেখতে পাই জীবনের হাহাকার। নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প খুঁজে পাই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়। অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া সমাজে নারীর বঞ্ছনার আদি-অন্ত ফুটে ওঠে তার কলমের ডগায়। তার ভাষায় বলতে হয়, ‘মারটা সহনীয় হয়ে গেছে। সকালে একবার রাতে একবার। প্রতিদিনের খাদ্যাভাসের মতো। দুপুরে ঘরে ফেরে না বলে সে বেলাটা বেঁচে যায়। ওই সময়টায় ও পাড়ায় যায়। সেখানকার নিয়মিত খদ্দের। কাজে বেরিয়ে যাওয়া থেকে কাজ থেকে ফেরা পর্যন্ত এই সময়টুকু ওর নিজস্ব। দেড় কামরার ঘরটি গোছগাছ করে, হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে থাকে। কত কী যে ভাবে। বিষ কি ওর নিজেরই খাওয়া উচিত?’ (দোপাটি)। প্রতিনিয়ত বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হতে হতে মানুষের মনে এমন ভাবনার উদয় হওয়া মোটেই অবান্তর নয়। লেখকের সার্থকতা এখানেই যে, তিনি তা সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।
নাগরিক জীবনের পাশাপাশি এক অন্যরকম গ্রামীণ জীবন দেখতে পাই তার গল্পে। সেখানে দেখতে পাই মাটির গন্ধ মাখা গ্রাম। মাটিনির্ভর সেখানকার মানুষ। দেখা যায় সহজ-সরল কিংবা কুটিল-গরল নারী ও পুরুষ। সব মিলিয়ে ভিন্ন এক আবেশে কাছে টেনে নেয় পাঠককে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনা এমন, ‘বিবাগী হানিফ এখন পুরোপুরিই সংসারী। সময়মতো দোকানে যায়, বাজার-সওদা করে, নতুন মাল তোলে, মায়ের জন্য পান-সুপারি আনে, বউয়ের জন্য আনে কাঁচের চুড়ি, আলতা! দোকানের চেহারা ফিরতে সময় লাগে না। বেচাকেনা বাড়ে, ব্যবসা বড় হয়। পাওনাদারের দেনাও মিটতে থাকে একটু একটু করে। আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো নয় কুলসুমা। অন্যরা যখন অবসরে আড্ডা দেয়, গাঁয়ের বৌ-ঝিদের গিবত আর নিন্দায় ব্যস্ত থাকে, কুলসুমা তখন বাড়তি রোজগারের জন্য সেলাই মেশিনে কাজ করে, কাঁথা বানায়, বিছানার চাদরে ফুল তোলে। তবে মুখে হাসিটা লেগে থাকে সব সময়। কারও সঙ্গে কখনো ঝগড়া হয়েছে বলেও শোনেনি কেউ। হানিফের সঙ্গেই কুলসুমার যত গল্প, যত আহ্লাদ।’ (পয়মন্ত) এই দৃশ্যটুকুই যেন পুরো গল্পের প্রতিনিধিত্ব করে। জীবনের যাবতীয় ঝঞ্ঝা পেরিয়েও মানুষ উঠে দাঁড়াতে চায়, বাঁচার মতো বাঁচতে চায়। হানিফ ও কুলসুমা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আলাদা জগতেরও নয়।
আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, লেখকের জীবনীতে আমরা তার কর্মজীবন সম্পর্কেও জেনেছি। গল্প পড়তে গিয়েও দেখি, কর্মজীবনের বাস্তবতাও তুলে এনেছেন তার গল্পে। সেখানে ব্যবচ্ছেদের দীক্ষা পাবেন পাঠক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুটিনাটিও জানবেন। তার সঙ্গে আড়ালের গল্প। জীবনের ইচ্ছা বা অনুভূতির গল্প। লেখক যখন বলেন, ‘আজ চেম্বারে যাবে না রবিন। মাঝে মাঝেই এমন করে। মন না চাইলে কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। সিগারেট ধরায়। ঠোঁট গোল করে ধোঁয়া ছাড়ে। এই সময়গুলোতে রাত্রির কথা ভাবতে ইচ্ছে করে। একই মেডিক্যালে পড়েছে দু’জন। রবিন সি ব্যাচে আর রাত্রি ছিল ডি ব্যাচে। রাত্রিকে ওর প্রথম চোখে পড়ে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর। টিউটোরিয়াল ক্লাসে। প্রথম দিন দেখেই বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠেছিল।’ (হাজার আয়নার ঘর) কিংবা পেশাগত কাজের ভেতর থেকে গল্প তুলে এনে লেখক বলেন, লেখকের ভাষায়, ‘নেপাল ডোমের ছেলেটি নির্লিপ্ত চোখে সেদিকে চেয়ে বাদামের শাঁস মুখে পুরলো। এরকমটা নতুন কিছু নয়। এই দৃশ্য তার খুব চেনা।…মৃত্যুতেও আসলে কারাগার ঘোচে না মানুষের!’ (কারাগারে) এখানে এসে মনে হবে, হাসপাতালের লাশকাটা ঘরের একজন ডোমের জীবন থেকেও শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। বস্তুত জীবনের কোনো শিক্ষাই ফেলনা নয়। ফরিদা ইয়াসমিন সুমি যেহেতু পেশায় একজন চিকিৎসক। তাই তার গল্পে কৌশলে চিকিৎসা বিজ্ঞান এসে যায়। তা প্রাসঙ্গিক হতেই পারে। হয়েও ওঠে। গল্পের প্রয়োজনে, চরিত্রের প্রয়োজনে এসে যায়। লেখকের ভাষায় বলা যায়, ‘এবার ডাক্তার একটু কড়াভাবেই বললেন, বীর্য পরীক্ষার রিপোর্ট ছাড়া আপনার স্ত্রীকে কোনো চিকিৎসা দেওয়া যাবে না। ওটা করিয়ে রিপোর্টসহ যোগাযোগ করবেন।’ (জন্ম) এমন বিষয় মানব জীবনে জরুরিও বটে। এমনকি পাঠকের জন্য শিক্ষণীয়। ফলে একেবারে মন্দ নয়। তবে পাঠকের কাজে আসবে না, এমন কোনো বিষয় না আনাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছেন লেখক। বিচক্ষণতার পরিচয়ও দিয়েছেন তিনি।
তার গল্পের চরিত্ররা যেন আমাদের চির চেনা জন হয়ে ওঠেন। মনে হয় আমাদেরই প্রতিবেশী-স্বজন তারা। তাই তো মাহবুব, নেপাল ডোম, জয়গুন বিবি, কুলসুম, মনু, নীহারিকা, পিউ, হানিফ, কুলসুমা, ফজর আলী, শমসু, রবিন, রাত্রিদের আমরা দেখতে পাই আমাদেরই আশেপাশে। জীবন্ত হয়ে ওঠে একেকটি চরিত্র। লেখকের সার্থকতা এখানেই।
এছাড়া তার বেশকিছু গল্পে যৌনতা বা শারীরিক সম্পর্ক এসেছে। সেসব গল্পের প্রতিপাদ্যই হয়তো শরীরের ক্ষুধা বা চাহিদা। তবে তাকে অশ্লীল বলা যাবে না কোনোভাবেই। কারণ মানব জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তিনি শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। লেখকের ভাষায়, ‘সারাদিনে মণির প্রতি আকর্ষণ বোধ না করায় রাতে ওর পাশে ঘুমোতে যেতেও খুব বিরক্ত লাগত মাসুদের। মনের ইচ্চা ছাড়া যৌনজীবন যে বিভীষিকাময় তা হাড়ে হাড়ে টের পেল।’ (অবদমনের গল্প) এখানে আধুনিক বাস্তবতার শিল্পিত উপস্থাপন সত্যিই দারুণ। বর্তমান সময়ের যৌনতাকেন্দ্রিক মুখোশধারী কিছু চরিত্রের দারুণ সমন্বয় গল্পটিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। অন্যত্র লেখক বলেছেন, ‘বিয়ে আর সংসারের আশায় আশায় এভাবেই প্রতিনিয়ত লুট হতে থাকে মনুর মধু। সম্ভবত এই মনোভাবের কারণেই অনেক কিছুতে পারদর্শী হয়ে ওঠে মনু। ফলে যুবা, বৃদ্ধ, ছোকরা, যারাই ওর সংস্পর্শে আসে, সবাই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সুখ দিতে জানে মনু। মনু সুখ দিতে জানে।’ (মনুর মধু) ফলে এসব প্রসঙ্গকে কখনোই অশ্লীল মনে হয় না। বরং চরম বাস্তবতা হিসেবেই উপস্থাপিত হয় পাঠকের সামনে।
অপরদিকে নারীর চলাফেরার স্বাধীনতাকে আটকে দিতে চায় একটি শ্রেণী। তাই তো তাদের ধর্মীয় গোড়ামি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন লেখক। তিনি গল্পের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, আজ ফজর আলীর দিন। আজ তিনি আবার প্রমাণ করবেন, এইসব জঘন্যতম ঘটনার মূলে মূলত মেয়েদের বে-আব্রু চলাফেরা, বাড়ির বাইরে যাবার প্রবণতাই দায়ী। তাই তো ফজর আলীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, ‘এদের জ্ঞান দাও প্রভু। এদের চক্ষু খুলে দাও। মেয়েমানুষ যদি পুরুষদের দেখিয়ে দেখিয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করে, পুরুষের কী দোষ? এরকম কাজ-কারবার তো তখন হবেই! মিডা জিনিসত মাছি বইবু, ইয়ান স্বাভাবিক।’ (জিনা) ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধেও সঠিক বিচারের পরিবর্তে ফজর আলীরা নারীর চলাফেরাকেই দায়ী করে।
বলতে গেলে, কাহিনির সময় জ্ঞান, বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ—সব মিলিয়ে অনবদ্য হয়ে ওঠে সুমির হাতে। শুধু তা-ই নয়, তার গল্পের চরিত্ররা যেন আমাদের চির চেনা জন হয়ে ওঠেন। মনে হয় আমাদেরই প্রতিবেশী-স্বজন তারা। তাই তো মাহবুব, নেপাল ডোম, জয়গুন বিবি, কুলসুম, মনু, নীহারিকা, পিউ, হানিফ, কুলসুমা, ফজর আলী, শমসু, রবিন, রাত্রিদের আমরা দেখতে পাই আমাদেরই আশেপাশে। জীবন্ত হয়ে ওঠে একেকটি চরিত্র। লেখকের সার্থকতা এখানেই।
তবে যে কথা না বললেই নয়, তার প্রথমদিকের লেখায় বেশ কিছু দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। তার প্রথম গল্পের বই ‘পাতা ফুল কাঁটা’য় এমন কিছু অসঙ্গতি পাওয়া যায়। যেমন- তিনি ‘ঈর্ষা’ গল্পে এক পৃষ্ঠায় নায়িকার নাম (মিতি) লিখেছেন তেইশ বার। যে কারণে গল্পটি দুর্বল মনে হচ্ছে। পাঠ করতে গিয়ে শ্রুতিকটু লাগতে পারে। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে বিষয়টি তিনি ভেবে দেখবেন। এছাড়া কোনো কোনো গল্পে কাহিনির চেয়ে ব্যাখ্যা বেশি মনে হয়েছে। তখন পাঠকের মনে হবে, গল্প কই? যা পড়লাম; তা সবই তো ব্যাখ্যা। গল্প হবে এমন, যা পাঠকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে ছায়াছবির মতো। এছাড়া একই গ্রন্থে কয়েকটি অনুগল্প পেলাম। আবার দুটি বইয়ের ভূমিকায় একই লেখা লক্ষ্য করলাম। দুটি বইয়ের জন্য আলাদা ভূমিকা বা মুখবন্ধ থাকলে পাঠক উপকৃত হতে পারতো। এতটুকু সময় তিনি পাঠককে দিতেই পারতেন। আমার বিশ্বাস তিনি আরেকটু সচেতন হবে। একজন পাঠক হিসেবে আমি তার গল্পের বহুল পাঠ কামনা করছি।
আরও পড়ুন: ভান অথবা ॥ ফরিদা ইয়াসমিন সুমি

