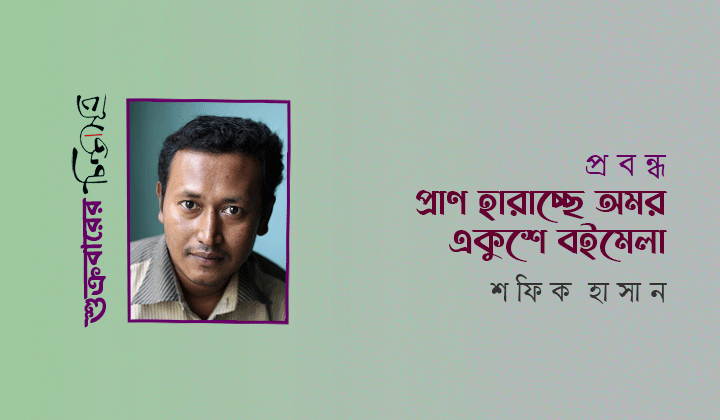অমর একুশে বইমেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাঙালি জাতির আবেগ-অনুভূতি। আত্মপরিচয়ের অহমিকাও যুক্ত এই মেলার সঙ্গে। ১৯৭২ সাল থেকে এর আবির্ভাব ও বিকাশ মুক্তধারার প্রাণপুরুষ প্রয়াত চিত্তরঞ্জন সাহার হাত ধরে। আশির দশক থেকে এই মেলা ক্রমশ খোলতাই হচ্ছে। পেয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ধীরে ধীরে বইমেলা সম্প্রসারিত হয়েছে টিএসসি থেকে দোয়েল চত্বরমুখী রাস্তার দুই পাশেও। এরপর তো পৌঁছে গেলো আরও বড় পরিসরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। যে উদ্যানের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই উদ্যানেই দিয়েছিলেন ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ। ৫২-র ভাষাশহীদ স্মরণে যে-মেলার সূচনা, সেটার সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে ৭১-এর গৌরবগাথার অনুষঙ্গ।
যে ভাষার দাবিতে এত আন্দোলন, সাগরসম রক্তক্ষয়—সেই ভাষায় লেখা বই বিকিকিনির সবচেয়ে বড় বাজার হয়ে উঠছে অমর একুশে বইমেলা। এই ‘বাজার’ সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের মননপরিসর, সংস্কৃতিচর্চাও কি বাড়ছে? আদতে আমরা কতটুকু ‘পাঠক’ হয়ে উঠছি। নতুন করে পাঠক সৃষ্টি হচ্ছে কি? বইমেলার হাত ধরে একুশের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কতটুকু শাণিত হয়ে উঠছি? সংস্কৃতি কি দাঁড়াতে পারছে শক্ত ভিতের ওপর? এখানটায় এসে কিঞ্চিত থমকে যেতে হয়। আমাদের বাজার বসেছে, বাৎসরিক ‘হাট’ পেয়েছি—সেই হাট-বাজারের পণ্যসামগ্রী কি যথাযথ পুষ্টিসমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর নাকি চোধধাঁধানো ‘চকচকে সোনা’! আমাদের মন ও মননের পুষ্টির জোগান যথাযথভাবে দিতে পারছে কি ‘একমাস উপলক্ষে’ প্রকাশিত বইগুলো? বই কেনা ও পড়ার মাঝেও রয়েছে যোজন যোজন দূরত্ব। তবে এটাও সত্য, বই না পড়লেও কেনাটা জরুরি। এতে লেখক বাঁচে, প্রকাশক টিকে থাকার রসদ পায়।
‘জাতির মননের প্রতীক’ স্লোগান যে বাংলা একাডেমির, সে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা মেধার বিকাশ ও মননচর্চায় কতটুকু ভূমিকা রাখতে সমর্থ হচ্ছে—এখন এমন প্রশ্নও সামনে হাজির হচ্ছে বারবার। বোধকরি এটা বিব্রতকর কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। প্রতিবছর বইমেলাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় বিপুল কর্মযজ্ঞ। নতুন-পুরোনো—সব শ্রেণীর প্রকাশকের জন্য বাংলা একাডেমির রয়েছে নির্ধারিত নীতিমালা। স্টল বরাদ্দ, স্টলপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আদতে কি তাই? এই নীতিমালা কতটুকু শেষপর্যন্ত পালন করা হয়! নাকি আগের বছরের ‘আমলনামা’র আলোকেই সবকিছু হয়ে যায়! বর্তমানে প্রকাশকদের স্টল নেওয়ার জন্য আবেদন করতে হয় অনলাইনে। সেখানে পূর্ববর্তী বছরে বরাদ্দপ্রাপ্ত স্টল ইউনিটের সংখ্যা উল্লেখ করতে হয়। নীতিমালার ‘অন্যতম অংশ এটাও। আবার প্রতি বছর প্রকাশিত নির্দিষ্ট সংখ্যক বইও লাগে। বজ্রকঠিন নীতিমালার বিপরীতে প্রকাশিত বই নেই, শর্ত পূরণের ধারে-কাছেও নেই এমন ব্যক্তিরাও তদবির/ লবিংয়ের জোরে স্টল বরাদ্দ পেয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে নীতিমালা হয়ে যায় ‘কেতাবি হিসাব’। বছরে ২৫টি নতুন বই প্রকাশের হিসাব দেখাতে হবে—এটা কতটুকু সঠিক ও সুবিবেচনাপ্রসূত! মন্দের ভালো বলা যেত, যদি সেটা যথাযথভাবে মানা হতো। একশ্রেণির প্রকাশক যেনতেনভাবে ২৫টি সংখ্যা মিলিয়ে দেন। সংখ্যার হিসাবে সিকি শতক পুস্তক/ পুস্তিকার সমাবেশ ঘটিয়ে দেওয়া হয়তো কঠিন কোনো বিষয় নয়। কিন্তু যে প্রকাশক নিজে বিনিয়োগ করে, সত্যিকারের বই প্রকাশ করেন তার পক্ষে গুনে গুনে ২৫টা বই কীভাবে প্রকাশ করা সম্ভব! অবশ্য পুরো প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে শুভঙ্করের ফাঁকির মতো। আইন তথা নীতিমালা হচ্ছে এমন জিনিস—চাইলে এর মাধ্যমে অপছন্দের কাউকে সহজে আটকে দেওয়া যাবে। স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্রটা লক্ষ করার মতো। নিয়মিত বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকাশকদের যেহেতু এখন আর বই জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই, বছরভর নতুন কোনো বই প্রকাশ না করেও তারা সহজেই বৈতরণী পাড়ি দিতে পারেন। তাই তো দেখা যায়, কেউ ১০০টি নতুন বই প্রকাশ করেও স্টল ইউনিট ২ থেকে ৩টির আবেদন করেও পাচ্ছেন না, আবার কেউ কেউ বই প্রকাশ না করেও তিন/ চারটি ইউনিট স্টল আঁকড়ে ধরে আছেন! এর অবনমন ঘটানোর ন্যূনতম সম্ভাবনা কিংবা আশঙ্কাও নেই। এসব হচ্ছে নীতিমালার ভেতরকার অসারতা, সিস্টেমের ভূত।
আবার একই প্রকাশক দুই নৌকায় পা দিচ্ছেন, এটা শেষপর্যন্ত কতটুকু শোভন, এর উপযোগিতাইবা কী—এটাও হতে পারে আলোচনার বিষয়বস্তু।
বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি একসময় যৌথভাবেই এসব বিষয় দেখভাল করত। আদালত কর্তৃক জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সামনে এসেছে দীর্ঘদিন একপ্রকার আড়ালে থাকা বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক সমিতি (বাপুস)। বাপুস যথাযথ তদারকি করতে পারছে কিনা, সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছে কিনা—পুরো বিষয়টাই সংশয়াচ্ছন্ন। সরাসরি প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত নন, এমন কারও পক্ষে এই সমিতির বর্তমান কার্যপরিধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা একপ্রকার কঠিনই।
বইমেলার পরিবেশের সঙ্গে এর স্টলবিন্যাস, প্যাভিলিয়ন সজ্জা, লিটল ম্যাগাজিন চত্বর, কফি, খাদ্যসামগ্রীর দোকান, ব্র্যাক ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং তথা বিকাশের তৎপরতা সমস্ত কিছুই জড়িত। পর্যাপ্ত পরিসর নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্যাভিলিয়নগুলো মেলাজুড়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব বরাবর স্থাপন করা জরুরি। কয়েক বছর যাবত প্যাভিলিয়নের নামে শুরু হয়েছে ‘ভিআইপি’ কালচার। সংশ্লিষ্ট প্রকাশক, লেখক বা ক্রেতা-পাঠক সবাই যেন সম্ভ্রান্ত শ্রেণির! এক শ্রেণির পাঠ্যবই নোট, গাইড ও বিসিএস গাইডের প্রকাশকও ‘প্যাভিলিয়ন কোটা’য় স্টল নিয়ে থাকেন।
মেলাজুড়েই সম্পাদনাহীন বইয়ের ছড়াছড়ি। একশ্রেণির লেখক যাচ্ছেতাই লিখছেন আবার আরেক শ্রেণির প্রকাশক নামের মুদ্রক সেসব দেদারসে ছেপে দিচ্ছেন। প্যাভিলিয়নের জৌলুস বেশি, ঝাঁকজমক ও জমকালো আয়োজন প্রায়ই নজর কাড়ে। কিন্তু প্যাভিলিয়ন দেওয়া প্রকাশকদেরও সব বই কি পাতে তোলা যায়? অন্যদের মতো তাদেরও অধিকাংশেরই নেই কোনো সম্পাদনা পর্ষদ। প্রতি বছর প্রকাশকদের সম্পাদনা পর্ষদ না থাকার বিষয়ে আক্ষেপ ঝরে পড়ে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর, কিন্তু প্রতিকার নেই। আক্ষেপে ভ্রূক্ষেপ করেন না কেউই! পাঠক বঞ্চিত হচ্ছে, ভুল ধারণা যাচ্ছে পাঠকের কাছে। প্রকৃত লেখক ও গ্রন্থানুরাগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এমন চাতুর্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে আয়োজকদের ভূমিকা কী হতে পারে, আয়োজক প্রতিষ্ঠান কি পারবে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে? কিংবা এটা তাদের এখতিয়ারের মধ্যে ফেলা যাবে! এখন যেমন লেখকদের সঙ্গে চুক্তিপত্রের নমুনা কপি জমা দিতে বাধ্য করছে, আগামীতে কি সম্পাদনার বিষয়টিও নিশ্চিত হতে চাইতে পারে? এসব দরকারি বিষয় খোঁচানোর আগে এটা নিশ্চিত করতে হবে—বছর বছর প্রকাশক বেড়ে চলেছে কেন? প্রকাশনা লাভজনক ব্যবসা নয়, মানুষ বই কেনে না, কিনলেও পড়ে না—এমন মর্সিয়ার মধ্যে প্রকাশকের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়ে চলা কি অস্বাভাবিক নয়? প্রকাশকরা যতই আহাজারি করেন, তাদের কারও কারও বিলাসী জীবন ঠিকই নজর কাড়ে। যিনি কর্মচারীর বেতন দিতে পারেন না বলে হাপিত্যেস করেন, তিনিও গাড়ি হাঁকিয়ে চলেন।
পেশাদার প্রকাশকের পাশাপাশি একশ্রেণির সৌখিন প্রকাশকের আবির্ভাব বরাবরই ছিল। সুরুচি কিংবা নিছক সখ থেকে কেউ কেউ প্রকাশনায় আসেন। সখ মিটে গেলে নীরবে প্রস্থানও ঘটে। সেই পশ্চাদপসরণের ইতিহাস অবশ্য কোথাও লেখা থাকে না। অল্প কয়েকজন প্রকাশকের নীরবে চলে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।
বইমেলা প্রকাশকদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার দাবি প্রকাশকরা জানিয়ে আসছেন দীর্ঘদিন যাবত। অন্যদিকে বাংলা একাডেমিও এটা হাতছাড়া করতে নারাজ। একুশের চেতনার সঙ্গে যে বইমেলার আবির্ভাব ও বিকাশ—রাষ্ট্রীয়ভাবে সেটার কাঠামো ধরে রাখার চিন্তা হয়তো স্বাভাবিক। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মাতৃভাষার দাবি, স্বাধিকার, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা। সে হিসেবে বইমেলাকে কুক্ষিগত করে রাখার দাবিটি হয়তো সঙ্গত। কিন্তু মাঝখানে নানাবিধ কেচ্ছা-কাণ্ডগুলো কি প্রত্যাশিত! বিশেষ করে ২০২৪ সালের বইমেলায় যে তুঘলকি খেল দেখা গেল, এটা ভবিষ্যতের জন্য বড় ‘ইতিহাস’ হয়ে থাকবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলা একাডেমি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও বাংলা একাডেমি পুরোপুরি স্বাধীন নয়। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ও কয়েক বছর যাবত চাচ্ছে নগ্নভাবে বাংলা একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে। এটা নিয়ে একটা চাপা ক্ষোভ, অসন্তোষ রয়েছে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে। কিন্তু ২০২৪ সালের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বনাম পূর্ত মন্ত্রণালয়ের যে নীরব লড়াই—তা কি কম লজ্জার! পূর্ত মন্ত্রণালয় বইমেলা আয়োজনের স্থান হিসেবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে ব্যবহার করতে দেবে না। সমাধান হিসেবে বলা হলো বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণসহ বাইরের রাস্তায় মেলার আয়োজন করতে। এতে না পোষালে চলে যেতে হবে পূর্বাচলে, উত্তরা পেরিয়ে নরসিংদীর কাছাকাছি! বাণিজ্য মেলা ও বইমেলাকে কি তবে নিয়ে আসা হবে একই সমান্তরালে? বইমেলার নেপথ্য ইতিহাস না জানলে কিংবা ভুলে গেলেই কেবল এমন হাস্যকর প্রস্তাব দিতে পারেন কেউ। কোনো প্রস্তাবই বাস্তবসম্মত নয়। দুটি সিদ্ধান্তের যে কোনো একটি বাস্তবায়ন করা মানে বইমেলাকে গলা টিপে হত্যা করা। কাজের পরিমাণ যখন কমে যায়, শূন্যস্থান পূরণ করতে বেড়ে যায় অকাজের সংখ্যা। পূর্ত মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মূলে কী আছে আমরা জানি না। তবে যে পূর্ত মন্ত্রণালয় বইমেলা আয়োজনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেই পূর্ত মন্ত্রণালয় দিয়ে আমরা কী করব! পূর্ত মন্ত্রণালয় জাতির জন্য বিশাল গহ্বর, সর্বনাশা গর্ত খুঁজতে চাচ্ছে কোন আকাক্সক্ষা থেকে!
অপরাপর বছরে যে সময়টাতে বইমেলার নির্মাণযজ্ঞ শেষ হয়, ২০২৪ সালে উভয় মন্ত্রণালয়ের রেষারেষির কারণে শেষদিকেই শুরু করতে হয়েছে নির্মাণকাজ। তাই তো মেলা শুরুর একসপ্তাহ যাবত থামেনি হাতুড়ি-পেরেকের ঠোকাঠুকি। শৌচাগার ব্যবস্থাপনায়ও নজিরবিহীন আলসেমি দেখা গেছে এবার। ফলে বেগ পেতে হয়েছে হাজার হাজার ক্রেতা-দর্শনার্থীকে, স্টল নির্মাণ শ্রমিকদের।
পাটা-পুতার ঘষাঘষিতে মরিচের দফা শেষ। একদিকে মুদ্রণসামগ্রীর উচ্চমূল্য, আবার বাংলা একাডেমিও স্টল ভাড়া বাবদ অস্বাভাবিক বেশি টাকা আদায় করছে। বিপুল বাণিজ্যের তোড়জোড় লক্ষ করা যায় এক্ষেত্রে। প্রতিটি প্যাভিলিয়ন থেকে কয়েক লাখ টাকা আদায়, ১ থেকে শুরু করে ৪ ইউনিট বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকাশকদের কাছ থেকে চড়া টাকা আদায়ের সংস্কৃতি চালু হয়েছে কয়েক বছর যাবত। বইমেলার কোথাও সুলভ মূল্যে তথা কম দামে চা পানের সুযোগ নেই। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের যেতে হয় মন্দির গেটের ঘুপচিতে। খাবার দোকানে বিরিয়ানিই সহজলভ্য, ডাল-ভাত, মাছ-ভাত বা সবজি-ভাত মেলে না। খাবারের দামও অস্বাভাবিক রকমের বেশি। কারণ বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ এসব স্টল ভাড়া আদায় করে লাখ টাকার অংকে। এসব দিক থেকে টাকা আদায়ের পরও বইমেলার স্পন্সর কোম্পানি থাকে। চারদিক থেকে পাওয়া টাকার হিসাব বাংলা একাডেমি কখনোই দেয় না। হিসাবে অস্বচ্ছতা, লুকোচুরি থেকে গেছে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত। স্পন্সর-করা প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকা নেওয়া হয়, সেই টাকা ব্যবহার হয় কী কাজে, তাও অজানা। বইমেলা ও বাণিজ্য মেলার তফাত কি ঘুচে আসছে ধীরে ধীরে! বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রকাশকরা তো বাণিজ্য করবেনই, সেটা তাদের অধিকার কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমিকে কেন ব্যবসা-বাণিজ্যের হালখাতা খুলে বসতে হবে!
বোধকরি ২০২৪ সালই ব্যতিক্রম, স্পন্সরহীন বইমেলার দেখা মিলছে। শুরুর দিকের সিদ্ধান্তহীনতা, অসামঞ্জস্যতার কারণেই বোধকরি এটা হিসাবের খাতায় যুক্ত হয়নি এবার। এবারের বইমেলায় প্রচারমাধ্যমের অনাগ্রহও লক্ষ করা যাচ্ছে। সবই কেমন যেন ঢিমেতালে, দায়সারাভাবে হচ্ছে, চলছে।
বইমেলার সুষ্ঠু পরিবেশের সঙ্গে স্টলবিন্যাসের বিষয়গুলোও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্যাভিলিয়ন কালচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন একশ্রেণীর (নিষিদ্ধ) নোট-গাইড বইয়ের প্রকাশক। গাইডবই থেকে অর্জিত বিপুল মুনাফার কিছুটা তারা ঢালছেন সৃজনশীল প্রকাশনায়। গাইড বইয়ের আছে অসম্মানের কলঙ্ক অন্যদিকে সৃজনশীল বইয়ে আছে সম্মানের পুষ্পাসন। কিন্তু সৃজনশীল পাঠক কোথায় পাব আমরা? এই পাঠকরা গাইড পড়েই তো নিজেদের সৃজনশীলতা নষ্ট করে ফেলছে। সৃজনশীল বই পড়তে লেখকের কল্পনাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাঠকের কল্পনাশক্তিও। মিলিত ধারায় পাঠক পিছিয়ে পড়লে তো মুশকিল! গোড়া কেটে দিয়ে আগায় জল ঢালার কী অর্থ থাকতে পারে! কম মেধাবীদের জন্য গাইড বইয়েরও দরকার আছে। আবার একই প্রকাশক দুই নৌকায় পা দিচ্ছেন, এটা শেষপর্যন্ত কতটুকু শোভন, এর উপযোগিতাইবা কী—এটাও হতে পারে আলোচনার বিষয়বস্তু।
বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ আশপাশের এলাকা ঘিরে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার কথা শোনা যাচ্ছে কয়েক বছর যাবত, চাই সেটারই সফল বাস্তবায়ন।
বইমেলায় প্রতি বছরই প্যাভিলিয়নের সংখ্যা বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রকাশকের সংখ্যা। পুরোনো প্রকাশকরা তো আছেনই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের স্ক্রিনশট থেকে শুরু করে স্টল নির্মাণের খুঁটি-ব্যানার, স্টল নম্বর সবকিছুই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করছেন প্রকাশকরা। ফেসবুকে রঙিন ছবি পোস্টানোর মচ্ছব যতটা চলে তার দুই শতাংশও যদি বইয়ের মান, বিষয়বস্তু, প্রয়োজনীয় সম্পাদনা বিষয়েও আলাপ হতো—পরিস্থিতি বোধকরি কিছুটা হলেও ভালো হতে পারত। গণহারে এমন ইঁদুরদৌড় কেন চলছে, আগে তো এত প্রচারকামিতা লক্ষ করা যায়নি! উত্তরটাও বোধকরি সহজ। ‘লেখক’ টানার একটি কৌশল হতে পারে এটা। ‘মুরগি লেখক’রা সবার আগে নিশ্চিত হতে চান, যেখানে পাণ্ডুলিপি দিচ্ছেন বইমেলায় তাদের স্টল থাকে কিনা। এটুকু নিশ্চিত করা গেলেই ‘ডিল’ করা সহজ হয়। এটা বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য হবে না—বর্তমানে বইমেলাকে টিকিয়ে রেখেছে মূলত কবিরা। নবীন-প্রবীণ যা-ই হোক না কেন। এরপরে রয়েছেন প্রবাসী লেখক, আমলা, ক্ষমতাবান মানুষ, সাবেক বড় কর্মকর্তা, সৌখিন লেখক, আমলা থেকে কামলার বউ কিংবা প্রেমিকা, ফেসবুকের স্ট্যাটাস লেখক… এরা। প্রকাশকের হাতে টাকা ও পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়ে তারা হয়তো নিজেদের উপকার করছেন, সামাজিক স্ট্যাটাস বাড়িয়ে নিচ্ছেন কিন্তু সামষ্টিকভাবে যে বইয়ের ব্যবসা, প্রকাশনার শিষ্টাচার তথা নীতি-নৈতিকতার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছেন এটা তারা যেমন উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না, তেমনি প্রকাশকরাও। খুব লজ্জা ও গ্লানি নিয়েই বলতে হয়—অধিকাংশ প্রকাশক পাণ্ডুলিপি পড়েন না, পড়লেও তারা জানেন কী ছাপছেন আদতে! আবার কেউ কেউ পাণ্ডুলিপি বোঝেনই না, নিরূপণ করতে পারেন না রচনার শক্তিময়তা কিংবা দুর্বলতা।
বইমেলা যত ঘনিয়ে আসে, প্রকাশক নামধারী একশ্রেণির মুদ্রকের জন্য ‘চানরাত’ আসে। কম-বেশি তিন মাসে করে নেন এক বছরের ব্যবসা। এরপর থাকে বিশেষ কিছু প্রজেক্টে বই ঢোকানোর (বিক্রির) তোড়জোড়। এই প্রক্রিয়াও জটিল, ধরাধরি, তোষামোদি, সিন্ডিকেট—কত কিছুই জড়িত এর সঙ্গে!
বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলা থাকাকালীন লিটল ম্যাগাজিন চত্বরটি ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। চমৎকার লেখক আড্ডা হতো। বর্ধমান হাউজের পাশে বয়রাতলা, কাঁঠালতলা ছিল যেন নতুন লেখক সৃষ্টির আঁতুড়ঘর। বৃক্ষমায়া ছাড়িয়ে বইমেলা যখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এলো, চরিত্র হারাতে শুরু করলো লিটল ম্যাগাজিন চত্বর। সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি দেখা গেলো, একেক বছর একেক জায়গায় বরাদ্দ হতে লাগলো চত্বরটির স্থান। বহেরাতলা-কাঁঠালতলা বলতেই যে চোখের সামনে ভেসে উঠতো লিটলম্যাগ চত্বরের দৃশ্য—সেটি আর রইলো না। প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যাও কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকছে। বর্তমানে লিটল ম্যাগাজিনের নামে মাসিক ম্যাগাজিন, সাহিত্যপত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকাও দেখা যাচ্ছে! ঠিকানাহীন লিটল ম্যাগাজিন চত্বর প্রতিবছর বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। সেই আড্ডা নেই, আড্ডার জায়গাও নেই। স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের উদ্ভাস নেই। লিটল ম্যাগাজিনকর্মীরা বিষয়টি প্রতিবছরই অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, আন্দোলনের ডাক দিচ্ছেন। এতটা অবহেলা লিটলম্যাগের প্রাপ্য ছিল না। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, পরিচালক থেকে শুরু করে অনেক কর্মকর্তাই লিটল ম্যাগাজিনে লিখেছেন, সম্পাদনাও করেছেন। তবু কেন এমন দুর্দশা?
ছোটকাগজ-বড়কাগজ দ্বন্দ্ব, সাহিত্যপত্রিকার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার বিষয়গুলো বরাবরই ছিল। তবে এটা সত্য, এখন বাছতে গেলে তেমন কোনো লিটল ম্যাগাজিন পাওয়া যাবে না। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তি-বন্দনার যেসব বালিশ-ম্যাগ প্রকাশিত হয়, তাতে আর যাই থাকুক আপামর পাঠকশ্রেণীর জন্য প্রয়োজনীয় রসদ থাকে না। থাকলেও সেটা এতই কম, হিসাবের মধ্যে আসে না। লিটল ম্যাগাজিন চত্বরের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, দ্রোহ ও বিপ্লবের অগ্নিশলাকাটিও প্রায় নিভু নিভু। একুশে বইমেলাও ধরে রাখতে পারছে না গৌরবময় অতীতের ধারাবাহিকতা। সবকিছু কেমন যেন ম্লান, ফিকে বলে ভ্রম হচ্ছে। এটা হতে পারে দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যাপার। বয়সজনিত চিত্তচাঞ্চল্যহীনতা।
তবু বইমেলা, তবু আনন্দের উদ্ভাস। হাজারো প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বইমেলা জেগে থাকুক, টিকে থাকুক, মাথা তুলুক শিরদাঁড়া উঁচু করে। তাই বলে স্থানান্তরের নামে সেটাকে ভাসানচর বা ঠেঙ্গারচরে পাঠানোর মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কিছুতেই চাই না। বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ আশপাশের এলাকা ঘিরে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার কথা শোনা যাচ্ছে কয়েক বছর যাবত, চাই সেটারই সফল বাস্তবায়ন। পাশাপাশি বইমেলার নীতিমালাও ঢেলে সাজানো জরুরি। নীতির নামে যেন নীতির বরখেলাপ না হয়, সমষ্টিগত মালাটা যেন অপাত্রে না যায়!