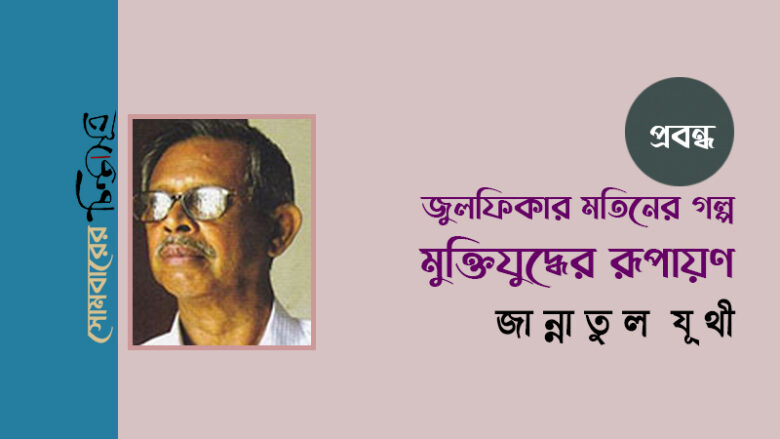জুলফিকার মতিনের কথাসাহিত্যের জগৎ বেশ বিস্তৃত। তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান পেয়েছে সমাজের ভেতরের প্রথাগত সংস্কার, মূল্যবোধ, অবক্ষয়, কুসংস্কার, পুরুষতন্ত্রের দাপট, প্রতিহিংসা, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মনস্তত্ত্ব, হৃদয়ের স্খলন, পীড়া, বিংশ শতাব্দীর নাগরিক যাতনা ও স্ববিরোধী বৈপরীত্য। তবে তাঁর গল্পে বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণপণে লড়েছেন তাই হৃদয়ের সেই রক্তক্ষরণ, যাতনা ও স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের ভালোলাগার সবটুকু দিয়ে গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন। যে গল্পের পরতে পরতে হারানোর বেদনা লুক্কায়িত। যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিকতা, লালসা ও নির্যাতনের ভয়াবহতা ছেঁয়ে আছে। “শেষ চিঠি”; “পূর্বজন্মের হত্যাকাণ্ড”; “সীমান্তিনী”; “খোঁজা”; “টেলিমেকাস”; “বন্দুক”; “মেয়াদ”; “প্রতিরূপ” প্রভৃতি প্রতিটি গল্পের প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ হলেও এর কাহিনি ও বুননকৌশল ভিন্ন। ভিন্ন স্বাদের এসব গল্পে মুক্তিযুদ্ধের বর্বরোচিত সময়কে ধারণ করেছেন গল্পকার। তাঁর গল্প সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন:
কয়েক দশকের গল্পচর্চায় জুলফিকার মতিন সমাজ দায়বোধের অঙ্গীকারে গল্পশরীরে যুক্ত করেন সমকালকে; সমকালের রাজনীতিকে। এক্ষেত্রে তাঁর গল্পে আছে বিদ্রুপের কষাঘাত; পরিহাসপ্রিয় জীবনের বিস্ময় ব্যাকুলতা আর জীবনরসিকের মগ্ন মূল্যায়ন। তবে তাঁর কথনে জীবনের দুর্মর আকুতি থেমে থাকে না কোথাও। মুক্তিযুদ্ধ, স্মৃতি-নস্ট্যালজিয়া, প্রেম চিরকালীন সম্পর্কসূত্রের মতো গেঁথে যায় গল্পের ছত্রে ছত্রে। দুরন্ত গতিময় কাহিনিভাষ্যে জীবনের যাবতীয় বাকবিতণ্ডায় এক রকমের উত্তেজনাতেই গল্পপাঠ শেষ হয়। সুনিপুণ এ ভাষ্যকারের লেখায় প্রান্তিক মানুষের পর্বটিও অনুচ্চ নয়। জানতে হয় প্রবৃত্তির খেলায়ও তিনি অকুণ্ঠ। সমাজজীবনের অন্ধকার দিকগুলোয় আলো পড়ে তাঁর গল্পে। অনেককিছু হয়ে ওঠে রহস্যময়, প্রশ্নবিদ্ধ। তবে শেষ পর্যন্ত জীবন একটা শ্রেয়োবোধেই উচ্চকিত তাঁর ভাষ্যে।১
প্রথম গল্প ‘‘শেষ চিঠি’’-তেই একজন মানুষের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট নির্মোহভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পকথক সত্তরের নির্বাচনে ভোট দিতে বাড়িতে যায়, তারপর আর ফেরা হয়নি ঢাকায়। গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতির সাহচর্য তাকে বেশ আমুদে করে তোলে সহজেই, খালাতো বোন তথা প্রেমিকা নীলার চিঠি নিরালায় বসে পড়তেই পায় অমলিন তৃপ্তি। এরই মধ্যে একদিন আসে ছাব্বিশে মার্চের সকাল। রেডিও অন করে দেখে কোনো সাড়া শব্দ নেই তাতে, ভাবে রেডিওটাও বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে অথচ ততক্ষণে নষ্ট হয়ে যায় তার স্বপ্নবিভোর কল্পনাময় পৃথিবীটা। খবর আসে পাকিস্তানিরা ঢাকা আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে হাজার হাজার মানুষকে। ঢাকা এখন মৃত্যুপুরী। জান নিয়ে সবাই পালাচ্ছে। তাদের অজপাড়া গাঁয়েও নেমেছে মানুষের ঢল। অনাগত আত্মীয়ের মতো মানুষ আর মানুষ। গল্পকথক বিচলিত হয়, সবাই আসে কিন্তু নীলার কোন খোঁজ নেই। বেশ কিছুদিন পর খালা-খালু তাদের বাড়িতে আসলেও সঙ্গে নীলা নেই। নীলা হারিয়ে গেছে বিষাক্ত সাপের নীলদংশনে। সেইসঙ্গে স্বপ্নের মৃত্যু। এমনি হাজারও স্বপ্নের বিসর্জনে অর্জিত মহান স্বাধীনতার গল্পই গেঁথেছেন অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক-গল্পকার। জুলফিকার মতিন তেমন একজন হয়েও অনন্য হয়েছেন তাঁর নির্মোহ বয়ানভঙ্গিতে। মতিনের আরেকটি বিশিষ্টতা হল তাঁর কাব্যিক ভাষাশৈলী। বাক্যগুলো গদ্যময় না করে তিনি কবিতার আদলে নির্মাণ করেছেন গল্পের শরীর। প্রতিটি গল্পই ভিন্ন তবে বাঁক শেষে মিলেছে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনিতে।
“শেষ চিঠি” গল্পে লেখক জুলফিকার মতিন দেখিয়েছেন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে কত মায়ের সন্তান অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কত স্বামী ও প্রেমিক তার স্ত্রী-প্রেমিকার সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি, কত নীলা তার প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধার এক বুক স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছেন এবং সবিশেষ কত মা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান তার প্রিয়জনের অপেক্ষায় বিনিদ্র রজনী পার করেছে। বুকের হাহাকার, আশাহত হওয়ার কষ্ট, যুদ্ধে একান্ত আপনজনকে হারিয়েও এদেশের সূর্য সন্তানেরা দেশমাতৃকার বুক থেকে উপড়ে ফেলেছে শত্রুর বিষদাঁত। “শেষ চিঠি” নীলার কাছ থেকে পাওয়া গল্পকথকের সংগৃহীত শেষ স্মৃতি। যে স্মৃতির পাতা খুলতেই নীলার সাহসী পদক্ষেপ পাঠকের সামনে উঠে এসেছে। নীলা ভয় পায়নি প্রাণের এমনকি সম্ভ্রমেরও। বরং নিজের প্রাণ দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেছে। “খালা এলেন। খালু এলেন। কিন্তু নীলা এল না। পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আর ফিরে আসেনি। এখনো মনের মধ্যে বাজে তার চিঠির শেষ কয়টি কথা, সত্যি বলছি, কালকে আমার মরতেও ভয় ছিল না।”২ নীলা মরতেও ভয় পায়নি কারণ নীলাদের মতো বীরেরাই এদেশ স্বাধীন করতে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের সম্মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে বীরদর্পে যাতে দেশমাতৃকার একচুল ক্ষতি পাষণ্ডরা করতে না পারে। নীলা এদেশের সূর্য সন্তান, যে প্রেমিকের নির্মল প্রেমকে উপেক্ষা করেছে দেশের জন্য। চিঠিতে নীলা জানিয়েছে তার মরতেও ভয় ছিল না। পাকবাহিনীর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার্থে এমন হাজারও নীলা নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা জানি, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পুরো বাংলাদেশই যুদ্ধ শিবিরে পরিণত হয়েছিল এবং মিলিটারিদের প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছিল নারী। তবু দমে যায়নি তারা বরং নীলার মতো অপার শক্তিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ছিনিয়ে এনেছে বিজয়ের লাল-সবুজ পতাকা।
জুলফিকার মতিনের অন্যতম গল্প “পূর্বজন্মের হত্যাকাণ্ড”। এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের জীবন বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা জানি, মানুষ স্বভাবতই হিংস্র, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ। সবসময় প্রতিবাদী হয় এমন কোনো কথা নেই। বরং নিজ স্বার্থ হাসিলে একটা শ্রেণি সর্বদা উদগ্রীব থাকে। যেমন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের দোসররা এদেশবাসীর ওপর নির্বিচারে হত্যা-ধর্ষণ চালিয়েছে। চালাতে সাহায্য করেছে। সম্পত্তি লুটপাট করেছে। আবার একটা বিশাল জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত মৃত্যু ভয় নিয়ে বেঁচে থেকেছে। গল্পের নায়ক সাখায়াৎ তেমনি একজন মানুষ। উচ্চশিক্ষিত এবং পাকিস্তানপন্থী হওয়ায় পাকিস্তানিদের হামলার সময়ে সে ভয়ে থতমত খেয়ে যায়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন তার বাড়িতে আসে তখন নিজের জীবনই তার কাছে প্রিয় মনে হয়েছে। কারণ সাখয়াতের মনে হয়েছে বিয়ে করলেই সে আবার সব ফিরে পাবে কিন্তু জীবন নয়। তাই মাথা নিচু করে থেকে নিজের প্রাণ রক্ষায় উদগ্রীব হয়েছে। স্ত্রী-সন্তানের প্রতি কোনো দায়িত্ব বোধের পরিচয় সে প্রদান করেনি বরং কাপুরষতার গ্লানি মাথায় নিয়ে বেঁচে থেকেছে। গল্পে পাই:
জেরিনা তাকায় সাখায়াতের দিকে। সাখায়াৎ তাকায় জেরিনার দিকে। সাখায়াৎ মাথা তোলে না। স্ত্রী আর সন্তানদের চেয়ে নিজের জীবন অনেক বড়। আর পৌরুষ, সে তো কেবল বিবাহ আর সন্তান উৎপাদন করার সময়।
জেরিনা বিব্রত মুখে তাকায়। লক্ষ্যহীনা। কত জিনিসই তো ঘরে রয়েছে। কিছুই চোখে পড়ে না। একটা ফ্লাগ। একটা কোরান শরিফ। পঁচিশে মাচের্র পরে তাও তো শুনেছে মূল্যহীন হয়ে গেছে ওদের কাছে। দরজায় আওয়জ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, খট খট খট!
বিন্দুমাত্র বিলম্ব হলে মুহূর্তেই বুঝি তা ভেঙে ফেলবে।
সামনে কাপুরুষ স্বামী। পাশে নাবালক ছেলেমেয়েরা। আর তো দেরি করা চলে না। ওদের জন্যে, কেবল কী ওদের জন্যে, তার নিজের জন্যেও এই কাপুরুষটাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। দ্রুত এগিয়ে দরজা খুলে দেয়, আইয়ে। মুঝে মালুম নেহি আপ আয়া হ্যায়। কোই কসুর হ্যায়? মাপ কিজিয়ে। আইয়ে, আপকি মেহেরবানি।৩
সাখয়াতের স্ত্রী জেরিনা সুশিক্ষিতা, গুণবতী-সাহসী। সাহস করেই পাকিস্তানী অফিসারের মুখোমুখি হয়। উর্দু ভাষার দক্ষতা দিয়ে প্রথমে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর তার শরীরটাকে ব্যবহার করে বর্ম হিসেবে। স্বামীর কাপুরষতাকে উপেক্ষা করে সে সন্তান, স্বামীকে রক্ষায় নিজের সম্ভ্রম লুটিয়ে দেয়। কোথাও গিয়ে মনে হয় জেরিনা শুধু প্রাণ বাঁচাতেই নিজের শরীর বিলিয়ে দেয়নি বরং কাপুরুষ স্বামীকে যথোচিত শাস্তিস্বরূপও সে পাকিস্তানী অফিসারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। যখন বাড়ির দরজায় পাকবাহিনী টোকা দেয় তখন সাখায়াৎ মুখ লুকিয়ে ছিল। স্ত্রী সন্তানের রক্ষায় পাকবাহিনীর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়নি। তখন সব বাধা উপেক্ষা করে জেরিনা তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। আর এর মধ্যে দিয়ে তার ভেতেরর দুটি সত্তা জেগে উঠেছে। প্রথমত সে স্বামী সাখায়ৎকে বোঝাতে চায় তার রূপের আগুনে অন্যকে কাবু করতে সক্ষম যেখানে তার স্বামী নির্বিকার। দ্বিতীয়ত মাতৃত্ব ও প্রেম। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা থেকেই সে নিজের সম্ভ্রম তুচ্ছ করে এগিয়ে গেছে। তার নাবালক সন্তানেরা যেন পৃথিবী থেকে সরে না যায় মা হিসেবে মহত্তম দায়িত্বই তাকে তখন বেশি ভাবিত করে।
নারীর সম্ভ্রমই তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। জীবন চলার পথে এই পুঁজিটুকু নারী কখনোই কোনকিছুর বিনিময়ে খোয়াতে চায় না। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি কখনো কখনো সবকিছু নির্বিকার করে দেয়। আর সেই নির্বিকারত্বের শিকার জেরিনা। যদিও শেষপর্যন্ত পাকবাহিনীর অফিসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নৈতিক ও অনৈতিকতার সংজ্ঞায় প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু যা একদিন তার ও সন্তানদের জীবন বাঁচিয়েছে পরবর্তীকালে সেটাই জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। স্বামীর প্রতি ধিক্কার থেকেই জেরিনা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। আর তার বিদ্রোহের রূপ ভিন্ন। জেরিনার বেঁচে থাকা অনেকটা মরা মাছের মতো ফ্যাকাসে। তবু জীবনের মায়া, সন্তানের দায় জেরিনাকে নতুন করে উপস্থাপন করে পাঠকের কাছে। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু তার চেয়ে আরও বড় যুদ্ধ হয়েছে ঘরে ঘরে। নারীর সম্ভ্রম লুটানোর মধ্যে দিয়ে। মায়ের সন্তানের মুখ চেয়ে বসে থাকার মধ্যে দিয়ে। স্বামীর হৃদয় ফাঁটা কান্নার মধ্যে দিয়ে। যুদ্ধ হয়েছে সর্বত্র। সাখায়াৎ তীব্র মানসিক যন্ত্রণা আর অন্তর্দহনে জ্বলতে থাকে। দুজনের মনো-মালিন্য তৈরি করে তীব্র ব্যবধান। ভালোবাসার জায়গাটা পূর্ণ হতে থাকে ঘৃণায়। সাখায়াৎ কাপুরুষ হিসেবেই বারবার জেরিনার কাছে উপস্থাপিত হয়। অথচ এতসবের ভেতর দিয়েও মানুষের আদিম বাসনা জেগে ওঠে। কাপুরুষ ও পৗরষ যন্ত্রণায় হাত বাড়ায় নারীর শরীরে কিন্তু সে নারী তো মরে গেছে বহুদিন আগে। জেরিনার মৃত্যু হয়েছে স্বামীর কাপুরুষতায়, পাকহানাদার বাহিনীর কাছে সম্ভ্রম লুটিয়ে, মায়ের পবিত্রতার! এই মৃত্যু দৈহিক নয় মানসিক। এজন্যই মুক্তিযুদ্ধ এক বিশাল-ব্যাপক জনযুদ্ধের অপর নাম। একসময় জেরিনা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে! তার তলপেট ফুলেফেঁপে উঠছে। পাকবাহিনীর জাওয়ান তাকে শেষপর্যন্ত আরেক বিষম বেদনা উপহার দিয়েছে। সাখায়াতের আঙুলের স্পর্শেও জেরিনার কোন উত্তেজনা নেই। বরফের মতো জমাট বেঁধেছে তার দেহ। স্বামীর কাপুরুষতা, অপারগতা ও মনোমালিন্য তাকে অন্য জগতের বাসিন্দা করে তুলেছে। মৃত মনকে সেখানে সাখায়াৎ খুঁজে পায় তার সাধ্য কী! গল্পকার জুলফিকার মতিন তুলে ধরেছেন এভাবে: “জেরিনা স্বপ্ন দেখে, সাখায়াৎ পাগল হয়ে গেছে। কিছুতেই আর সাখায়াতের বাম পাঁজর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে জেরিনা পড়েছে আকাশ আর মৃত্তিকায়, বক্ষপত্রে এবং মেঘপুঞ্জে।”৪
“সীমান্তিনী” গল্পটি কথাসাহিত্যিক জুলফিকার মতিনের এক ভিন্ন ঘরনার গল্প। এখানে যুদ্ধকালীন গ্রামের সাধারণ মানুষের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের কমাণ্ডার ছারোয়ার্দী। আর তার বাহিনীকে স্থান দেয় মতিজ্জল বুড়ো। ছরোয়ার্দীরা এখন দেশড় জনের একটি বৃহৎ বাহিনীতে রূপ নিয়েছে। তাই যেখানে সেখানে তারা রাত কাটাতে পারে না। কখন মিলিটারিদের নজরে পড়ে সেই ভয় তাদের সদা তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু বুড়ো মতিজ্জল প্রাকৃতিক কাজ সেরে ভিটার পূর্বদিকের প্রান্তে হঠাৎ দেখে সারি সারি মাথা। চেঁচিয়ে ওঠে মতিজ্জল বুড়ো। তখনই ছরোয়ার্দী দলবল নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু বুড়োর কৌতুহল নিয়ে মুক্তিবাহিনীর শঙ্কা সৃষ্টি হয়। তারা মতিজ্জল বুড়োকে রেখে যেতেও পারে না। কারণ মতিজ্জল তার বয়সের ভারত্বেই হোক বা সরলতার সুযোগেই হোক আর কারও সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর গ্রামে ঢোকার কথা বলে দিলে তারাই কোপানলে পড়বে! সেই ভয় ও শঙ্কা কাটাতে এবং মতিজ্জল বুড়োর কৌতুহল মেটাতে ছরোয়ার্দী বাহিনী অবস্থান করে তার বাড়িতে। ছরোয়ার্দী বাহিনী যদিও নিরাপত্তাহীন মনে করে নিজেদের তবু বুড়ো মতিজ্জল তাদের নিবৃত্ত করে। “এসে যখন পড়েছি, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ততো অপেক্ষা করতেই হবে। তুমি বরং খোঁজখবর নিয়ে এসো। মতিজ্জল বুড়ো বলে, পাগল নাহি? দুচার দিন জিরাও, তারপর তোমাদের যুদ্ধে তোমরা যাইয়ো বাপজানেরা।”৫
মতিজ্জল বুড়োর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু মতিজ্জল বুড়োর ছেলের ঘোর আপত্তি। এই আপত্তি আরও বৃদ্ধি পায় যখন দেখে মুক্তিযোদ্ধাদের কমাণ্ডার ছরোয়ার্দী তার সুন্দরী স্ত্রী টিয়ার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থেকেছে। তাদের চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব দেয়নি বরং দেশের আপামর জনসাধারণের কথা ভেবেছে। কমাণ্ডার ছরোয়ার্দী, হরমুজ, আওলাদ, মতিয়ারের মতো দেড়শ জনের বাহিনী নিয়ে তারা তাদের দিক থেকে শত্রুর মোকাবেলা করার চেষ্টা করে চলেছে। তবে যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন জনের সাহায্য নিয়েছে। তাদের বাড়িতে থেকেছে, খেয়েছে। কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতাও করেনি এমনটা নয়। যেমনটা করেছে মতিজ্জল বুড়োর ছেলে। সে নেকবর আলির কাছে পরামর্শ নিতে যায়। যে নেকবর আলি তাকে বুঝিয়েছিল- এসব যুদ্ধফুদ্ধ ভুয়া। ছেলে ছোকরারা ডাকাতি, চুরি করার জন্যই এসব করছে। গল্পকার তুলে ধরেছেন এভাবে:
কথা শুনে নেকবর আলির চোখতো চড়কগাছ, করছ কী? এ্যাহনো এ খবর ক্যাম্পে পৌঁছাও নাই। দেশের দুশমন-জাতির দুশমন। বাড়িতে থাকলে কি মা বোনের ইজ্জৎ থাকব। পরিণাম চিন্তা কর নাই?
ঠোঁট চাটে মতিজ্জল বুড়োর ছেলে, আমি কী করমু? নিজে আনল ।
-সর্ব্বনাশ! তোমার আব্বা নিজে ডাক্যা আনছে? এ কথা আর কারো কাছে কয়ো না। ফাঁসি অবো ফাঁসি। গাড়ির চাকায় বান্দ্যা রাস্তায় ছুটাব। তোমার বাপরে বুঝাও। আর এই কথা যদি মিলিটারি পায় তবে বেবাক গেরাম জালায়ে দিব। গেরামের সর্ব্বনাশ অবো। তোমার বাপজানরে বুঝাও।৬
মতিজ্জল বুড়োর ছেলে, নেকবর আলি পাকিস্তানের দোসর। তবে মতিজ্জল বুড়োর ছেলেকে নেকবর আলিই ভুল বুঝিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে কানপড়া দিয়েছে যার ফলে নেকবর আলির মনোকামনা পূর্ণ হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যত কথাসাহিত্যিক গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পাকিস্তানী দালালদের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। নেকবর আলির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সৈয়দ শামসুল হকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কাব্যনাট্যে মাতবর চরিত্রে, আনোয়ার পাশার রাইফেল রোটি আওরাত উপন্যাসের আবদুল মালেক ও আবদুল খালেকের চরিত্রে। আবদুল মালেক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, সমাজে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। স্বার্থপর এই ব্যক্তিটি পাকিস্তানের একনিষ্ঠ সেবক। প্রকৃতগত দিক দিয়ে তিনি একজন মিথ্যাবাদী ও ধুরন্ধর ব্যক্তি। তার ভাই ড. আবদুল খালেকও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী। তিনি তার ভাই আবদুল মালেকের চেয়েও বেশি ধুরন্ধর ও কপটচারী। আবদুল খালেক, মালেক, নেকবর আলি, মাতবর সবাই এক ধাঁচের। তারা নিজেদের স্বার্থে পাকিস্তানের দালালী করতে পিছপা হয়নি। কিন্তু টিয়া, মতিজ্জল বুড়োর মতো সাচ্চা মানুষের সংখ্যাই বেশি ছিল যার ফলে এদেশ শত্রুমুক্ত হয়। টিয়া নেকবর আলির কথা শুনেই বুঝতে পারে তার স্বামী কোথায় গেছে। দ্রুত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে অনুরোধ করে কিন্তু মিলিটারি ঠিকই এসেছিল। আর মিলিটারি টিয়াকে শেষ করে তবেই তাদের খায়েস মিটিয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কাব্যনাট্যের দৃশ্যপট চোখে ভেসে ওঠে। মাতবর নিজের জালে নিজেই ফেঁসেছে। শেষপর্যন্ত তার মেয়েকে নামমাত্র কোরআন শরীফে হাত দিয়ে পাকিস্তানী মিলিটারির হাতে তুলে দেয়। শেষমেশ মাতবরের মেয়ে ধুতরার বিষ পানে আত্মহুতি দেয়। আর শওকত ওসমান তাঁর দুই সৈনিক উপন্যাসে দেখিয়েছেন মখদুম মৃধার দালালীর চূড়ান্ত ফল। মৃধা কন্যা সাহেলী, চামেলীর ওপর নির্যাতনের চূড়ান্ত রূপ। পাকবাহিনীর দালালীর খপ্পরে পড়ে একসময় নিজের মেয়েদেরই সম্ভ্রম হারাতে হয়। সৈয়দ শামসুল হকের মাতবর, আনোয়ার পাশার আব্দুল মালেক ও আব্দুল খালেক, শওকত ওসমানের মখদুম মৃধা মুদ্রার একই পিঠ। তাদের দালালীর ধরণে কোন পার্থক্য নেই এবং চূড়ান্ত পরিণতিতেও সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে সর্বত্র নারীরাই ভুক্তভোগী:
চামেলী একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে থেমে গিয়েছিল। মেজর হাকিম তাকে তুলে তখন ঘাড়ে ফেলে নিয়েছে। সাহেলীর শুধু আর্তনাদ: বাপ্জান, বাপ্জান। আঁচড়-কামড়ের সুযোগ পাচ্ছিল না, সে শুধু পা ছুঁড়েছিল। ফৈয়াজ তাকে পাজাকোলা তুলে নিয়েছে। সাহেলীর দুই হাত এমনভাবে ঠাসা যে নাড়ার উপায় নেই। ফৈয়াজের মুখ থেকে ভরভর হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছিল। সাহেলীর ঠোঁটে বারবার চুম্বন-রত সে বলছিল, “চলো মেরি জান্। তোমকো রাত কা রাণী বানায়াংগা।”৭
যুদ্ধকালীন টিয়া, চামেলী, সাহেলী তথা এদেশের নারীদের ওপর বর্বরোচিত নিপীড়ন চালায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। মিলিটারিরা টিয়াকে বেইজ্জত করেছে তারপর তাকে মেরে রেখে যায়। মতিজ্জল বুড়োর ছেলের ষড়যন্ত্র তাকেই গ্রাস করে! মুক্তিযুদ্ধের গল্প হলেও লেখক জুলফিকার মতিন বিশেষভাবে মনস্তাত্ত্বিক ধারার প্রস্রবণ দেখিয়েছেন তাঁর “খোঁজা” গল্পে। একদল মুক্তিযোদ্ধা একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। উদ্দেশ্য কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়া। তাদের মধ্যে রয়েছে সাদেক, জ্যোতি, মন্টু, সোবহান, ইদ্রিস, জহুরুল, বাদল বিভিন্ন বয়সী ছেলে-মেয়ে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সারা দেশময় যখন ছড়িয়ে পড়েছে এবং শান্তি কমিটি ও দালাল বাহিনীর তৎপরতাকে উপেক্ষা করে তারা এখানে এসে উঠেছে। কিন্তু এখানে এসে বাদল আবিষ্কার করে এক অদ্ভুত সত্ত্বার। বাদল যাদের কখনও চোখেও দেখেনি সেই সত্ত্বাই তাকে বেশি ভাবিত করে। এই ভাবনার নেপথ্যে রয়েছে দেওয়ালে লেখা একটি বাক্য। যা তার হৃদয়ে গভীরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে,“ঔষধ খেতে হবে রবিবারে আর বৃহস্পতিবার।”৮ এই একটি বাক্যই অস্তিত্বহীন প্রাণের কোন সজল চোখের কল্পনা করে। যে গভীরতা তাকে মাতিয়ে তোলে, ভাবিয়ে তোলে। কোন সে জন যে কিনা তার প্রিয়জনের যত্নে, তাকে আগলে রাখতে এই মমতার স্পর্শ দেওয়ালে অঙ্কিত করেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর তাড়া খেয়ে বাদলদের মতোই এই পরিবারও হয়তো আরও একটু ঝঞ্জাটহীন আশ্রয়ে গেছে। বাদল, জহিরুল, সোবহান বিভিন্ন বয়সী ছেলে-মেয়ে, তারা মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরতা থেকে দেশবাসীর রক্ষার ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে। তবে “খোঁজা” গল্পের বিশেষত্ব নিহিত অন্যার্থে! গল্পকার জুলফিকার মতিন দেখিয়েছেন বাদল খুঁঁজে ফিরেছে সেই মমতাময়ীর মুখ। তিনি মাতা, পত্নী নাকি প্রিয়তম কেউ! বাদলের জিজ্ঞাসাই এখানে মুক্তিযুদ্ধের ভয়বহতাকে ছাপিয়ে হৃদয়কে আপ্লুত করে।
খেয়াঘাটের মাঝি হারান দাসের বাড়িতে এসেই প্রথমে আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধারা। সারাদিন লুকিয়ে থাকে সেখানে। এ সময় আরেকটি গ্রুপ অপারেশন চালায় নলকায়। ইউনিভার্সিটিতে পড়া জহরুলই এই বাহিনীর দলনেতা অগত্যা তারা উল্লাপাড়ায় নতুন আশ্রয়ে চলে আসে। এসে ওঠে পরিত্যক্ত পুরোনো জমিদার বাড়ি। মালিক লাপাত্তা। বাড়ির সঙ্গে লাগানো কালী মন্দিরের পুরোহিতই বাড়িটি দেখাশোনা করে। তবে বাদলের মনে ঘুরপাক খেতে থাকে কার লেখা ওটা। কে সে! “কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে যায়। পড়ে। ভাবতে চেষ্টা করে, কার ছিল এত ভুলো মন যার ঔষধ খাওয়ার কথাও মনে থাকত না।”৯ এই লেখাই বাড়িটির প্রতি বাদলের গভীর মমত্ব সৃষ্টি করে সেখানেই রাজাকারদের এলোপাথাড়ি লক্ষ্যহীন গুলি বাদলের পাঁজর ছেদ করে। তবু কষ্টের মধ্যে বাদলের মনে হয়, সে ওই মানবিক আত্মটাকে খুঁজে দেখতে পারবে।
জুলফিকার মতিন ‘‘খোঁজা’’ গল্পে যে অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা মুক্তিযুদ্ধের বেদনাকে আরও গভীরতর করে তোলে! ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ তার নিজ বসতি গড়ে তুলেছিল এই বাংলায় কিন্তু ধর্ম রক্ষার নামে সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম চালায় পাকবাহিনী। যার ফলে পড়ে থাকে ভিটেমাটি আর মানুষ হয়েছে উদ্বাস্তু, হয়েছে দেশান্তরি। জুলফিকার মতিনের গল্পের সেই মানবিক আত্মার নিবিড় যোগ লক্ষ করা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র “একটি তুলসী গাছের কাহিনি” গল্পের সঙ্গে। দেশভাগের ফলে একদল মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ওঠে। সেখানে তারা আবিষ্কার করে একটি তুলসী গাছ। পানির অভাবে শুষ্কপ্রায় গাছটি মরতে বসেছে। গাছটি উপড়ে ফেলা নিয়ে আগতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এরই মধ্যে দেখা যায় গাছটি চিরসজীব তরতাজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাদেরই মধ্যে কে বা কারা রমণীর সজল চোখ কল্পনা করে গাছটির পরিচর্যা শুরু করে! কাহিনির পার্থক্য থাকলেও হৃদয়ের আবেগ, আকুতি ও মানবিক আত্মা খোঁজার উদ্বেগটা একই। গল্পে পাই:
যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ-তুলসীগাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই, আকাশে যখন দিগন্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছল ছল করে ওঠে।১০
একটি তুলসী গাছের কাহিনির মোদাব্বের, এনায়েতের মতোই বাদলও মানবিক আত্মাটাকে খুঁজে ফেরে। পাঁজরে বিদ্ধ গুলিকে উপেক্ষা করে সে জীবনের সন্ধান করতে চায়। এখানেই গল্পকার হৃদয়ের সঙ্গে জীবনের যোগ দেখিয়েছেন। যে জীবন শত কষ্টেও হৃদয়কে উপেক্ষা করতে পারে না।
“টেলিমেকাস” গল্পেও লেখক মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি দিক উন্মোচন করেছেন। আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ দেশ মাতৃকার রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। টেলিমেকাস গল্পটির সূচনা হয়েছে টুটুলের গল্প শোনার আবদার এবং তার ছোট কাকুর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে। শেষপর্যন্ত টুটুলের ছোটকাকুর গল্পটি শেষ নাহলেও জুলফিকার মতিন তাঁর গল্পের ইতি টেনেছেন টেলিমেকাসের রহস্যময়তার মাধ্যমেই। টুটুলের ছোট কাকু এবং তার পিতার যুদ্ধে যাওয়া যেন গ্রিক বীর টেলিমেকাসেরই আরেক রূপান্তর। কিশোর টুটুল ছোটকাকুর কাছে গল্প শোনার আবদার করলেই তার কাকু টেলিমেকাসের গল্প বলতেন। কিন্তু সে গল্প আর শেষ হতো না। কাকু চলে যায় যুদ্ধে। কারণ পাকবাহিনীর মুহুর্মুহু আক্রমণে গোটা পূর্ব-পাকিস্তান তখন ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। গল্পকার সেই ভয়াবহতাকে রূপ দিয়েছেন এভাবে:
২৫ মার্চ রাত্রিতে হানাদার বাহিনী ঢাকাতে ট্যাঙ্ক নামিয়ে দেয়। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। জ্বালিয়ে দিয়েছে ঘরবাড়ি। এক রাত্রির ঐ নির্মম গণহত্যাতেই তারা সন্তুষ্ট হয়নি। দিনে দিনে বিস্তৃত হচ্ছে তাদের হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন আর অত্যাচারের মাত্রা। ঢাকা থেকে অসহায় নিরস্ত্র লোকজন প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। সেই পলায়নপর ভীতসন্ত্রস্ত মানুষদের পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছন দিক থেকে গুলি চালিয়ে পাখির মতো শিকার করতে শুরু করেছে। সে খবর ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সারা দেশ জুড়েই এক আতঙ্ক আর নিরাপত্তাহীনতাবোধ। পাশাপাশি শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে সে খবর। বাঙালি পুলিশ আর ই.পি.আর. বাহিনীর প্রতিরোধের কথাও লোকমুখে আর অজানা নেই কারও। নতুন প্রত্যাশা দানা বাঁধছে সবার মনে।১১
টেলিমেকাস গ্রিক বীর ইউলিসিস ও তার স্ত্রী পেনিলোপির সন্তান। টেলিমেকাস জ্ঞানদেবী এ্যথেনার স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন তার বাবা ইউলিসিসকে খুঁজে বের করার। তবে ধরণা করা হচ্ছিল ইউলিসিস ট্রয়ের যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার পথে মারা গেছে। সব দ্বিধা উপেক্ষা করে গ্রীক বীর টেলিমেকাস তার পিতৃদেব ইউলিসিসকে খুঁজতে বের হয়। টুটুলের ছোটকাকুর মৃত্যু সংবাদ পেয়েও টুটুলের বাবা কোনো এক অজানা বলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ভাইয়ের আত্মবলিদান তার মধ্যেও শক্তি সঞ্চার করে। যে কিনা টুটুলের মায়ের মুখের ওপর কথা বলে না তবু নীরব অবস্থানের মধ্যে দিয়ে তার অস্তিত্বকে জানিয়ে দেয়। জীবনের যুদ্ধ, অস্তিত্বের যুদ্ধ, টিকে থাকার লড়াই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সীমনা কোনকিছুই মানে না। তার ধরণ সর্বত্র এক। গ্রীক বীর টেলিমেকাস বাবাকে খোঁজার প্রত্যয়ে বের হয়েছিল আর টুটুলের বাবা তার আড়ষ্টতাকে উপেক্ষা করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য বেরিয়ে পড়ে। ভাইয়ের মৃত্যুর মহত্তম উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজেকেও তুলে ধরে। পাকবাহিনীর হাত থেকে বাংলাকে রক্ষার্থে এদেশের সূর্য সন্তানরা এক একজন টেলিমেকাস। তারা লড়েছে দেশের শত্রুকে প্রতিহত করতে। বাবা, ভাই, মা-বোনের জীবন ও সম্ভ্রম যারা হরণ করেছে তাদের পদাহত করতে। টুটুলের ভাষ্যে গল্পকার তুলে ধরেছেন:
[…] আর আম্মা হয়ে যান পাগলের মতো। তিনি বলেন, আমার কথা বাদই দাও। ছেলেমেয়েদের দেখছ না!
টুটুলের আব্বা বলেন, ওদের দেখতেই যাচ্ছি। ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্যই আমার যুদ্ধে যাওয়া প্রয়োজন। আমার কী হবে সেটা বড় কথা নয়। ওদের তো স্বাধীন দেশের নাগরিক করে মানুষ করতে হবে। টুটুল ভাবে, কোথা থেকে এত জোর পেলেন আব্বা। হয়তো সময়ই মানুষকে শক্তি জোগায়।১২
“বন্দুক” গল্পে শেষপর্যন্ত ফুটে উঠেছে এক হতভাগ্য পিতার হৃদয়ের জয়। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তাকে বন্দুক ধরতে বাধ্য করে। চৌধুরী সাহেবের দোনলা বন্দুক থাকলেও তিনি কখনও পাখি বা মানুষ মারার কাজে তা ব্যবহার করেননি। তবে প্রতিদিন বন্দুকটার পরিচর্যা করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তার কিশোর ছেলে সৌরভ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তাকে রজব আলী পাকবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। চৌধুরী সাহেবের ভাগ্নে খোরশেদই হৃদয়বিদারক এই খবরটি পৌঁছে দেয় মামা-মামির কাছে। একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে শোকে মুষড়ে পড়ে সৌরভের বাবা-মা। চৌধুরী সাহেব গ্রামের মান্যগণ্য ব্যক্তি হলেও পাকিস্তানের দোসরদের তোপের মুখে তাকে চুপসে থাকতে হয়। সৌরভের মতো অসংখ্য নিরীহ মানুষ হত্যা করেও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে দেশের মাথা হয়ে উঠে রজব আলীরা। বাবা মায়ের কোল থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে, নারীর সম্ভ্রমকে বিকিয়ে দিয়ে রজব আলী দেশ স্বাধীনের কুড়ি বছর পর নিজের পাওয়ার ও পজিশন নিয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে! সৌরভের মৃত্যুর জন্য, সাধারণ মানুষকে অকাতরে হত্যার জন্য দায়ী রজব আলীর বিচার যুদ্ধোত্তর দেশে হয়নি। তারা আইনের ফাঁক গলিয়ে, গা ঢাকা দিয়ে পার পেয়েছে। এবং দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের অংশীদারও হয়েছে। কিন্তু চৌধুরী সাহেবের পিতৃহৃদয় রজবকে ক্ষমা করতে পারেনি বিধায় তার জনসভায় শেষপর্যন্ত বন্দুকটাকে কাজে লাগিয়েছে। পিতৃত্বের দায়মুক্তি ঘটাতেই রাজাকার, আলবদর রজব আলীকে খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছে। গল্পকার জুলফিকার মতিন তীব্রতার সঙ্গে তাঁর গল্পে বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন এভাবে:
চৌধুরী সাহেব বলেন-তুমি আমার ছেলে সৌরভকে ধরিয়ে দিয়েছিলে না?
রজব আলী নিরুত্তর। ঘাম তার মুখে-নাকের উপর ।
গর্জে ওঠেন চৌধুরী সাহেব-তুমি রাজাকার ছিলে, তুমি আমার ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছে। তুমি তার মৃত্যুর কারণ। আর আজ ভোট কিনে দেশটাকে পাকিস্তান বানাতে এসেছ? কিসের গণতন্ত্র? কার গণতন্ত্র? কিসের ইলেকশান?
কথা বলতে বলতে তিনি তুলে ধরেন বন্দুক। একটু পিছিয়ে আসেন। গুলির শব্দ শোনা যায় দু’বার। দোনলা বন্দুকের দুটো নল থেকে বেরিয়ে আসে দুটো গুলি। এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় রজব আলীর বুকের ডান পাশ। বুকের বাম পাশ।১৩
যুদ্ধকালীন এদেশে রজব আলীদের সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু যুদ্ধোত্তর দেশে তারা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে। আজও স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ এর ভুক্তভোগী! দুর্নীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতার রেষারেষি সবই এর জের ধরে। রজব আলীদের দৌরাত্ম সম্পর্কে বুঝলেও জাতি নিশ্চুপ। তবে জুলপিকার মতিন তার গল্পে শাস্তি নিশ্চিত করেছেন। কালের গর্ভে বা পাঠকের হাতে রজব আলীর ভাগ্য ছেড়ে দেননি। বন্দুক গল্পে আরও একটি বিষয়ের ওপর নজর দিয়েছেন লেখক, বন্দুকের কারণেই চৌধুরী সাহেবের ওপর শান্তি কমিটির বিশেষ নজর পড়ে। তারা চৌধুরী সাহেবের বন্দুকটি তাদের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয় কিন্তু চৌধুরী সাহেব বন্দুকটি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দেওয়ার মনস্থির করেন। কারণ পাকবাহিনীর কাছে বন্দুকটি হস্তান্তর করলে তারা সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন করতেই তা ব্যবহার করবে! শেষমেশ স্থির করেন থানায় গিয়ে বন্দুক জমা দিয়ে আসবেন। কিন্তু হঠাৎ বন্দুক উধাও। আর তখনই চৌধুরী সাহেবের নজরে আসে সৌরভের প্রস্থান। এ নিয়ে তাদের মনে ভীতির সৃষ্টি হয়! পরবর্তীকালে খোরশেদই তাদের খবর দেয় পাকবাহিনী সৌরভকে মেরে ফেলেছে।
ইতোমধ্যে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যসহ জেনারেল নিয়াজী’র আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে মুক্ত হলো স্বদেশভূমি। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি এক অবিস্মরণীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা। যার জন্য জাতি জীবনপণ লড়াইয়ে নেমেছিল সম্পূর্ণ হলো তার অর্জন। স্বাধীনতা। স্বাধীনতা। স্বাধীনতা। আর তো লুকিয়ে লুকিয়ে গেরিলা জীবন বয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। খোরশেদ এসে আস্তানা গাড়ে কামারখন্দ থানায়। উড়িয়ে দেয় বাংলাদেশের পতাকা। সবুজের মধ্যে লাল। সবুজের শ্যামস্নিগ্ধ-শ্যামশ্রীর এই বাংলাদেশ-তার বুক লাল হয়ে আছে বাঙালির রক্তে। সেই রক্তের লাল ছোপ মেখে উদিত হচ্ছে নতুন সূর্য। একটি জাতি ওর চেয়ে আর কী বেশি দিতে পারে মুক্তির জন্য।
এই থানারই একটি ঘরে পাকিস্তানি আর্মিদের ফেলে যাওয়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সেগুলো একটি দুটি করে চেক করতে করতে তার ভেতরই খোরশেদ পেয়ে গেলো সৌরভের আনা চৌধুরী সাহেবের বন্দুক। বন্দুকটি দেখে সৌরভের কথা মনে করে অশ্রুতে ভরে যায় দুচোখ। সে সেটি তুলে নেয় পরম মমতায় ।
এবার তো আর সৌরভের মৃত্যু সংবাদ দেয়া ছাড়া তার কোনো উপায় নেই।১৪
“মেয়াদ” গল্পে জুলফিকার মতিন মানবতার বিপর্যয় দেখিয়েছেন। মানবিক বোধ যেখানে স্বার্থপর হওয়া থেকে বিরত রাখে আবার এই বোধের কারণে বিপদও ঘটতে পারে। মেয়াদ গল্পে এমনই এক কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র পার্থ। তার স্ত্রী রায়হানা এবং অবোধ শিশুকন্যা সোমা। পাথের্র অনুপস্থিতিতে সোমা ও রায়হানা টিভির সামনে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। এমন সময় দরজায় কড়াঘাত পড়তেই রায়হানা লক্ষ করে কেউ পার্থের নাম ধরে ডাকছে। রায়হানা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। পরক্ষণে আবার দরজার কড়াঘাতে রায়হানা শঙ্কিত হয়। মাঝে সুবিশাল দরজা থাকলেও অসহায়ত্বকে বুঝতে দেরি হয়নি রায়হানার তাই একসময় অনেক বাগবিতণ্ডার পর পার্থের দুই বন্ধু রউফ ও হামিদকে রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও ঘরে প্রবেশ করতে দেয় সে। কারণ মানবিকতাবোধ। যা না থাকলে মানুষ মনুষ্যত্বহীন নির্জীব প্রাণীতে রূপ নেয়। শরীরের প্রবল ক্ষত রউফকে খুব দুর্বল করে দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও মানবিক বোধের কারণে পার্থ রউফের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার চিকিৎসার পরই হামিদ নিরপদ আশ্রয়ে চলে যায়। রউফ সুস্থ হয়। ছোট্ট অবোধ শিশু সোমার সঙ্গে রউফের ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ পুলিশের আনাগোনা লক্ষ করে রউফ দ্রুত প্রস্থান করে। তবে বিপদ ঘনিয়ে আসে পার্থের ওপর। শকুন সবসময় মড়ার গন্ধ শুকেই কাছে আসে। তেমনই এদেশীয় শকুনেরা রউফের মতো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বেড়িয়েছে। কাঙ্ক্ষিত সমাধান না পেলে তাদের আশ্রয়দাতাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। দুজন নিরুপায় মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার ফল পাথের্র কারাগার বাস! লেখক জানিয়েছেন যার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। মানবিকবোধের বিসর্জন হয়েছে এভাবে:
অর্ধেকটা শুনেই ইন্সপেক্টার বলে, এত বড়া ছড়া? কে তোমাকে শিখিয়েছে, আম্মু?
সোমা বলে, রউফ কাকা। তুমিতো চেনো না তাকে। কতদিন আমাদের বাসায় ছিল। তার পায়ে না গুলি লেগেছিল?
কথা শুনে সোজা হয়ে বসে ইন্সপেক্টার কাবিল। এই খবরটা পেতেই তো খুঁজতে খুঁজতে এতদূর এসেছে। সে কথা তো আর এই বাচ্চা মেয়েটাকে বলা যায় না।
সেদিনই গ্রেপ্তার করা হয় পার্থকে। সেই থেকে সে জেলে। দুজন নিরুপায় লোককে আশ্রয় দিয়ে যে অপরাধ সে করেছিল তার শাস্তির মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। ১৫
“মেয়াদ” গল্পটিতে এসেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর জীবন-বাস্তবতার দিক। মূলত মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতির গতিবিধি, পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি। জুলফিকার মতিন অত্যন্ত সচেতন, বস্তুবাদী ও প্রত্যয়ী ব্যক্তি বিধায় তাঁর গল্পতেও এগুলো স্থান করে নিয়েছে। তাঁর এই গল্পটিতে সুস্পষ্টভাবেই তা বোঝা যায়। পার্থ তার কলেজ জীবনের বন্ধু ও তার সহযোগীকে আশ্রয় দান করে শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে এবং শাস্তিস্বরূপ কারাগারে নিক্ষেপিত হয়, অথচ যাদের আশ্রয় দিয়েছিল তারা ছিল মুক্তিযোদ্ধা এবং সামরিক বাহিনীর লোক। বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জাতীয় চার নেতা হত্যার পর দেশীয় রাজনীতিতে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির আবির্ভাবের ইঙ্গিত এ গল্পে সুস্পষ্ট। অথচ সে সময়ে সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব, রাজনীতি সচেতনতা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াহীন বাস্তবতা এ গল্পে সুন্দরভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।
জুলফিকার মতিনের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত আরেকটি গল্প “প্রতিরূপ”। এ গল্পেও মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র ফজল বৃদ্ধ। অভিজ্ঞতার ভারে নুয়ে পড়া ফজল ঘুরে ঘুরে সমাজটাকে দেখে। আর যৌবনকালে নিজের নানাবিধ অপরাধের কথা স্মরণ করে। মূলত ব্যক্তি হিসেবে সে খুব চরিত্রবান নয়। তার যৌবন ছিল পাপ-পঙ্কিলতায় পূর্ণ। কিন্তু এখন সেসবের জন্য তার অনুশোচনা রয়েছে এবং বর্তমানের প্রতি তার রয়েছে এক ধরনের ঘৃণাবোধ। তার দৃষ্টির ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর নানাবিধ চিত্র। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস। তবে রাজাকার, আলবদর শ্রেণি পাকিস্তানের দালালী করেছে সে সময়। শেষপর্যন্ত এই গল্পের কাহিনি গড়িয়েছে ভিন্ন এক স্রোতে। জয়নাল নামের এক ব্যক্তি ফজলকে অনেকটাই বাধ্য করে নিয়ে যায় একটা বাড়িতে। যাওয়ার সময়ে ফজলের বারবার মনে হয়েছে পতিতাবৃত্তির নতুন ধরন এসেছে নাকি! কিন্তু যখন নির্জন বাড়িতে শয্যাশায়ী অসুস্থ নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তখন ফজলের মধ্যে এক অন্য সত্তার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। জয়নালের ভাষ্য মুক্তিযুদ্ধকালীন ভয়াবহতার রূপ ফুটে উঠেছে এভাবে:
[…] অনেকদিন আগের কথা, পাকিস্তানি সৈন্যরা মেয়েটির উপর অত্যাচার করে। তার স্বামীকেও মেরে ফেলে। সেই থেকে স্মৃতিভ্রষ্ট কালেভদ্রে কখনো সম্বিত ফিরে আসে। সে তখন তার স্বামীকে দেখতে চায়। আমার কাজ হলো, তখন কাউকে ধরে নিয়ে আসা। যেমন আপনাকে এনেছি। ফজল বলেন-আমি তাহলে থাকি ।
লোকটি বলে-কোনো দরকার নেই। এরপর তো সে সব ভুলে যাবে। আবার কখন যে সে তার স্বামীকে দেখতে চাইবে, তার কী ঠিক আছে? আমি কি তাহলে তখন আসব? ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেন ফজল।
না, এ সুযোগ একজনকে মাত্র একবারই দেয়া হয়। ১৬
“শেষ চিঠি” গল্পে নীলার যে পরিণতি ‘‘প্রতিরূপ” গল্পে শয্যাশায়ী নারীর পরিণতি কিঞ্চিৎ কম নয়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কবলে পড়ে এদেশের মা-বোনেরা জীবন দিয়েছে, সম্ভ্রম হারিয়েছে। ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। জুলফিকার মতিন মুক্তিযুদ্ধের গল্প’তে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর ভয়বহতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পূর্বজন্মের হত্যকাণ্ড গল্পে জেরিনা ও সাখায়াতের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংকট যেমন স্থান পেয়েছে তেমনই উঠে এসেছে পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনি। সীমন্তিনী গল্পের টিয়া, খোঁজা গল্পের মানবিক আত্মার সন্ধান, টেলিমেকাস গল্পে টুটুলের কাকুর মৃত্যু ও টুটুলের বাবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ, বন্দুক গল্পে রাজাকার নিধনে চৌধুরী সাহেবের বন্দুকের সর্বোত্তম ব্যবহার, মেয়াদ গল্পের মানবিকবোধের বিপর্যয়-পার্থকে কারাগারে নিক্ষেপ প্রতিটি অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা। যুদ্ধ, বেদনা, গ্লানির ইতিহাসে পরিবৃত্ত প্রত্যেকটি গল্প। টিয়া, নীলা, শয্যাশায়ী মেয়েটি, জেরিনা, রায়হানা প্রত্যেকেই নির্যাতনের শিকার। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর বাস্তবতার সাক্ষী তারা। দেশমাতৃকার মতো তারাও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়েছে। আবার কারো কারো ভাগ্যে জুটেছে বীরাঙ্গনা আখ্যা। পাকবাহিনীর অত্যাচারে জেরিনা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলাদেশে তার সন্তানের কী পরিচয়? যুদ্ধশিশুই নয় কী! কিন্তু এ সমাজ-রাষ্টও কী এই অনাগত শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ দিতে সক্ষম হয়েছিল? এককথায় না। জাকির তালুকদারের কুরসিনামা উপন্যাসে বীরঙ্গনা পুত্র দুলালের জীবনের পরাজয়ই এর অন্তিম স্বাক্ষী। লোকলজ্জা ও কটুক্তি সহ্য করতে না পেরে দুলালের মা গলায় দড়ি দেয় এবং দুলালকে হতে হয় চরম দুর্দশার শিকার। ইতিহাসও যুদ্ধকালীন নারীর দুর্বিষহতার স্বাক্ষী দেয়। গবেষণায় পাওয়া যায়,
“২ নভেম্বর ১৯৭২ যুদ্ধ অপরাধ তদন্ত এজেন্সি কতৃক প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, পাকিস্তানিদেও নয় মাসব্যাপী ত্রাসের রাজত্বকালে বাংলাদেশে দুই লক্ষাধিক নারী নির্যাতিতা হযেছেন। সে সময়ের মানবতাবাদী গবেষক ড. জিওফ্রে ডেভিস বরেছেন, বাংলাদেশে ধর্ষণের ফলে প্রায় দু’লক্ষ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মধ্যে এক লক্ষ ৭০ হাজার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন। যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্থানীয় গ্রাম্য ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটান এবং বাকি ত্রিশ হাজারের মধ্যে অধিকাংশই সে সময় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।”১৭
বাঙালির জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধ একটি প্রাতিস্বিক বিষয়। প্রায় চব্বিশ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর আরেক অরাজকতার মধ্যে দিয়ে বাঙালিকে দিন যাপন করতে হয়। আর তখনই এ জাতি স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে শুরু করে। তবে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাক-হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার মুক্তিযুদ্ধেকে আরও বেগবান করে। এর মধ্যে দিয়ে জাতি এক বিভীষিকাময় ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়। আমরা জানি, এই যুদ্ধ যেমন স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তেমনই ছিনিয়ে নিয়েছে এদেশের লাখ লাখ সন্তানকে। নির্যাতন ও নিপীড়নের দ্বারা দুই লাখ মা- বোনের সম্ভ্রম হানি ঘটিয়েছে। ইতিহাসের এই নির্মম সত্যকে কালের স্বাক্ষী করতে কলম ধরেছেন এদেশের বোদ্ধা সমাজ। জুলফিকার মতিন এই কাতারেরই একজন। তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধের গল্প’গ্রন্থে ইতিহাসকে পুনর্জীবিত করেছেন। তাঁর “শেষচিঠি” গল্পের নীলা, “পূর্বজন্মের হত্যাকাণ্ড” গল্পের জেরিনা, “সীমান্তিনী” গল্পের টিয়া যুদ্ধকালীন নির্যাতিত নারীর প্রতিচ্ছবি। পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা থাকলেও তাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণের চিত্র একই। নীলা তার প্রিয়তমের জন্য দেশ-মা-মাটির ঋণস্বীকার করতে ভোলেনি। জেরিনা তার সন্তানের মঙ্গলকামনায় আত্মবলিদান করেছে। আর টিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাবাহিনীর প্রাণ রক্ষা করেছে। মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীর এই অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জাতির ইতিহাস রচিত হয়েছে। জুলফিকার মতিন ইতিহাসের এই মহত্তম অর্জন ও পাকবাহিনীর নির্মমতা সবই তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন।
তথ্যনির্দেশ
১. ড. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৭-২০১৫), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১১৫
২. জুলফিকার মতিন, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, আফসার ব্রাদার্স, ২০২০, পৃ. ১২
৩. তদেব, পৃ. ১৬
৪. তদেব, পৃ.২৫
৫. তদেব, পৃ.৩৪
৬. তদেব, পৃ. ৩৬
৭. শওকত ওসমান উপন্যাস সমগ্র-২, সময়, ঢাকা, ২০১২, পৃ.৩২৪
৮. জুলফিকার মতিন, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, পৃ. ৩৮
৯. তদেব, পৃ.৪১
১০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাসমগ্র, সলাউদ্দিন বইঘর, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৪২৩
১১. জুলফিকার মতিন, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, পৃ. ৫৩-৫৪
১২. তদেব, পৃ. ৫৭
১৩. তদেব, পৃ. ৬৬
১৪. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫
১৫. তদেব, পৃ. ৮১
১৬. তদেব, পৃ. ৯৬
১৭. শাহনাজ পারভিন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৬৩