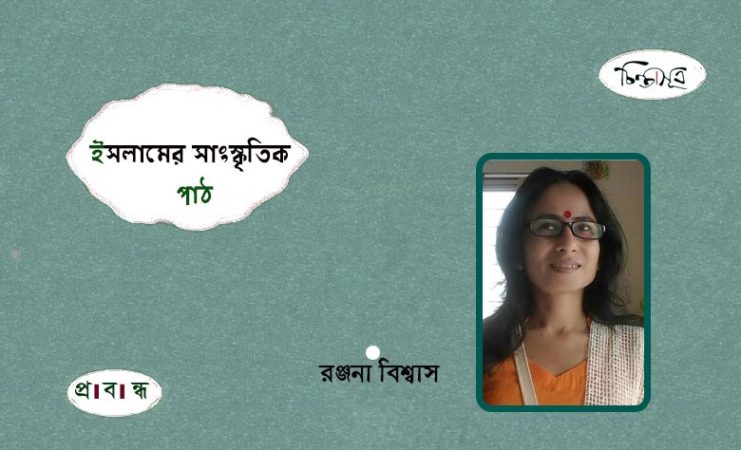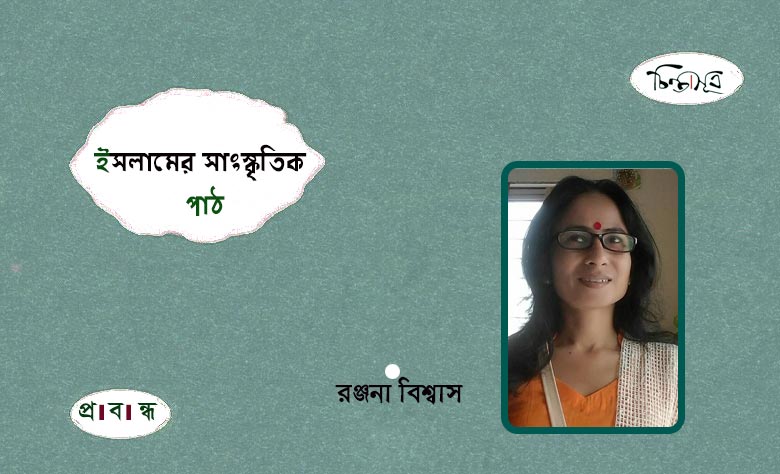 একটি একজন বাঙালি খ্রিস্টিয়ান এবং একজন আরবিন বা আরর্মেনিয় খ্রিস্টানের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের কোনো পার্থক্য না থাকলেও তাদের জীবন বোধ, সামাজিক আচারে মৌলিক পার্থক্য থেকেই যাবে। কেননা, একজন্য অস্ট্রিক অন্যজন সেমেটিক। এভাবে একজন নাইজেরীয় মুসলমানের সঙ্গে একজন কাজাখ মুসলমানেরও একইভাবে পার্থক্য লক্ষ করব আমরা। কারণ একজন নিগ্রয়েড অন্যজন ইউরোপয়েড, একজনের বাস মরুভূমির ভয়ানক গরমে, অন্যজনের বাস সাইবেরিয়ার বিপজ্জনক ঠাণ্ডায়। আর এভাবেই পৃথিবীজুড়ে জাতিতে জাতিতে তৈরি হয়েছে বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এ জন্যই আমরা যারা ঈশ্বর বা আল্লাহয় বিশ্বাস করি, তারা এই বৈচিত্র্যময় জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এর নির্মাতাকে মনে মনে সেজদা না করে থাকতে পারি না।
একটি একজন বাঙালি খ্রিস্টিয়ান এবং একজন আরবিন বা আরর্মেনিয় খ্রিস্টানের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের কোনো পার্থক্য না থাকলেও তাদের জীবন বোধ, সামাজিক আচারে মৌলিক পার্থক্য থেকেই যাবে। কেননা, একজন্য অস্ট্রিক অন্যজন সেমেটিক। এভাবে একজন নাইজেরীয় মুসলমানের সঙ্গে একজন কাজাখ মুসলমানেরও একইভাবে পার্থক্য লক্ষ করব আমরা। কারণ একজন নিগ্রয়েড অন্যজন ইউরোপয়েড, একজনের বাস মরুভূমির ভয়ানক গরমে, অন্যজনের বাস সাইবেরিয়ার বিপজ্জনক ঠাণ্ডায়। আর এভাবেই পৃথিবীজুড়ে জাতিতে জাতিতে তৈরি হয়েছে বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এ জন্যই আমরা যারা ঈশ্বর বা আল্লাহয় বিশ্বাস করি, তারা এই বৈচিত্র্যময় জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এর নির্মাতাকে মনে মনে সেজদা না করে থাকতে পারি না।
তাই যারা বলেন, ‘ধম্য চোখ বুজে মেনে চল’ নীতিতে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য বলতে হয়, ধর্মের যে ফিলোসফি, সে সম্পর্কে তাদের উন্নসিকতাই বিদ্যমান। ধর্মের ফিলোসফি মানেই একটি সমাজের অন্তর্গত বিশ্বাস ও কর্ম-প্রক্রিয়া, যা কালচারের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ খুব কম। তাই নৃবিজ্ঞানী ঞ্চক বলেন, ‘শ্যাডো সায়েন্স’। একজন হিন্দু যখন মাতৃকার্তির সামনে হাতজোড় করে প্রার্থনা করেন:
‘অসতো মা সদগময়/ তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মহমৃতংগময়।’
অর্থাৎ অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। তখন তার কী প্রত্যাশা আমরা দেখতে পাই! সে অন্ধকার থেকে আলোয় চেতে চাইছে, সে অমৃতের সন্ধান চাইছে। এই অমৃতের সন্ধান একজন রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পান, একজন লালন যেভাবে পান, একজন বুদ্ধ, যিশু, মুহাম্মদ যেভাবে পান বা কোপানিকাস গ্যালিলিও, এরিস্টটল যেভাবে পান, সেভাবে ধর্মের গুরুরা পান না, পান না একজন সাধারণ মানুষও।
এ জন্য মহামতি স্বামী বিবেকানন্দ যাত্রীদের তিন রকম কর্ম প্রক্রিয়ার যেকোনো একটিকে বেছে নিতে বলেন। লোকের জন্য জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানের পথ, একদল আর একদলের জন্য কর্মমার্গ ও অন্যটি হচ্ছে ভক্তিমার্গ। বলা বাহুল্য সমাজে ভক্তিমার্গের লোকই বেশি। আর এই সম্প্রদায়ের কারণেই একদিন স্বার্থান্বেষী ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘আমরা ধর্ম লাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টা রচিত সামগ্রী আমাদের মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষ আকর্ষণ করিয়া লয় যে ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন আমাদের সমাজের বাহিরেও আর কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে, সে কথা স্বীকার করিতে কষ্ট বোধ হয়।’ (ধর্ম, বুক ক্লাব, ঢাকা, ২০০৩; পৃ:৫)
কিন্তু হজরত মুহাম্মদ তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নিয়েছিলেন বলেই তিনি চেয়েছিলেন তার অনুসারীরা নেহাত ভক্তিমার্গে নয় জ্ঞান মার্গে বিচরণ করুক। আর তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘জ্ঞানার্জনের জন্য চীন দেশে যাও।’ সংস্কৃতির সংজ্ঞায় টাইলর ও মোতাহার হোসেন চৌধুরীও ‘জ্ঞান’কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাহলে সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সংঘাত কোথায়?
ধর্মসমাজ যেন ধর্মের স্থান দখল করতে না পারে, যেন আমাদের মমতা নিঃশেষে আকর্ষণ করে না নিতে পারে, তার জন্যই হজরত মুহাম্মদ চীন দেশে ‘জ্ঞান অর্জনের জন্য তার অনুসারীদের যেতে বলেছিলেন। না হলে আরবের সঙ্গে কী সম্পর্ক? ভৌগলিকভাবে চীনে যাওয়া আরবদের জন্য সহজসাধ্য নয়, এমনকি চীনের সংস্কৃতি আরবদের অনুকূলেও নয়; তাহলে? তবু তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মীর একটি দেশে কেন যেতে বললেন? হ্যাঁ বললেন, এজন্যই যে, আমাদের সমাজের বাইরে আর কোথাও ধর্মের স্থান আছে, জ্ঞানের জায়গা আছে। অহমিকা অজ্ঞানতা কুপণ্ডুকতার স্থান ইসলামে থাকতে পারে না বলেই এই নিদের্শ তিনি দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্রতর গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর বৃত্তের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার এই প্রয়াস যে যুগে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, ইউরোপ যা আঠারো শতকে বুঝতে পেরেছিল, তা ইসলাম বুঝতে পেরেছিল ৬ষ্ঠ শতকে।
সমস্ত মানুষের সমান প্রাপ্য—এই বোধ জাগ্রত করতে ও ধর্মকে সমাজের বা রাষ্ট্রের নয় ব্যক্তি মানুষের অন্তরের সৌন্দর্যে বিকশিত করতে বহু দার্শনিককে নির্যাতন ও মৃত্যুকে মেনে নিতে হয়েছে। অবশেষে মুক্তি এসেছে। এখন কথা হলো—যে ধর্মসম্প্রদায় ইউরোপীয়দের চেয়ে ১২০০ বছর আগে ঘোষণা করল—সমস্ত মানুষই এক জাতি। যে ধর্মসম্প্রদায়ের পতাকাতলে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণে কোণঠাসা নিম্নবর্ণের মানুষ আশ্রয় নিয়ে ছিল, সেই ধর্মসম্প্রদায় কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অজ্ঞতার দিকে। কত সহজেই আমরা এখন অন্যের মত আদেশ ও বিশ্বাসকে গলাটিপে হত্যা করে আস্ফালন করছি। আমাদের চিরস্থায়ী বিশ্বাসকে আবেগ দিয়ে আকঁড়ে ধরে একা বাঁচার স্বপ্ন দেখছি। অথচ চিন্তা দিয়ে একবার বিচার করতে চাইছি না, যে যে জায়গায় ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়, সেখানে নৌকাতে যাওয়া সম্ভব, কিংবা এই সময় মটর গাড়ি বা প্লেনেও যেতে বাধা নেই। এই যাওয়ার প্রক্রিয়াটাই তো সংস্কৃতি, এর বদল হয় কিন্তু উদ্দেশ্যটা তো ঠিকই থাকে। এখন পূর্বপুরুষগণ ঘোড়ায় গিয়েছেন বলে এই যুগে ওই ব্যবস্থাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে হবে এমন নয়।
রবিন্দ্রনাথ বলেন—‘মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং ঈশ্বর আছেন এই কথা পুরানতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নতুন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোন নতুন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, তাহারা পুরাতনকে তাহাদের জীবনের মধ্যে নতুন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নতুন করিয়া তুলিয়াছেন। নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সুষ্টি করে না—সেরূপ নতুনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নতুন করিয়া দেখিতে চাই।’ (ধর্ম প্রাগুক্ত; পৃ:৪৮)
স্তন্যপানরত শিশুর সঙ্গে মায়ের মূর্তি বা ছবি বা দৃশ্য নতুন নয়—পুরনো কিন্তু এক একজন শিল্পীর তুলির টান ও রঙের খেলায় সেই ছবি নতুন রূপে হাজির হয়, এখানেই শিল্পীর চিন্তা ও বোধের প্রকাশ; যা তাকে স্বতন্ত্র করে। বিষয় এক, ঘটনাও এক; কেবল প্রকাশের ধরন ভিন্ন। এই ভিন্নতাটাই কালচার। এ জন্য মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং তার ইহজগতের যাবতীয় কর্ম ও বিশ্বাসকে সম্মান জানাতে আমরা ব্যর্থ হলে, আমরা আমাদের আর এভাবে আমাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে নষ্ট করে দিতে পারি না। আমাদের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে, আর চিন্তা দিয়ে বিচার করতে হবে। আমাদের ক্ষুদ্রতার গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর গণ্ডির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমাদের সন্দেহ থাকতে হবে, প্রশ্ন থাকতে হবে। না হলে আমরা গতিহীন স্থবির হয়ে যাব।
কিন্তু আমরা যদি সহযোগী হই আর আমাদের মধ্যে যদি প্রেম থাকে, তাহলে পৃথিবীকে বানিয়ে বলতে পারি উদ্যান। এটি কোনো সরাইখানা নয়। এই উপলব্ধি থেকে আমরা জিহাদের পথে নয়, জ্ঞানের পথে, প্রেমের পথে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বিশ্বাসের পুরনো ফুলগুলোকে নতুন নতুন রঙে ও গন্ধে সাজিয়ে তুলতে সমর্থ হব। মত্ততা, উন্মাদনা পরিহার করে আমাদের আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া বোধশক্তিকে যদি জাগিয়ে তুলতে পারি, তা হলে আমরা কুপমণ্ডুকতা ধর্মব্যবসায়ীদের অসুস্থ রাজনীতি পরিহার করে আমাদের বিশ্বাস ও ধর্মকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারব।
আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি চূড়ান্তভাবে ধর্মবিশ্বাস নয়, বরং ধর্মে আনুগত্য প্রকাশের এক একটি প্রক্রিয়া, যাকে সমাজবিজ্ঞানে প্রথা বলে
ধর্ম তো সেই বটবৃক্ষের মতো, যেখানে রৌদ্রতপ্ত দেহ ও ক্লান্ত মন শান্তির জন্য আশ্রয় নেয়, কেউ জামা খুলে, কেউ শুয়ে বসে; কেউ হয়ত দু’দণ্ড দাঁড়িয়ে। শান্তি পাওয়ার জন্য এই যে, আশ্রিতের ভক্তির ধরন, নিবেদন করার প্রক্রিয়া, তাতে বটগাছের কী? কিংবা বটগাছের মালিকেরই বা কী? এই প্রক্রিয়াই কালচার। এই প্রক্রিয়ার কালে কালে দেশে দেশে বদল ঘটে, ঘটবেই। এ কারণেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে নৃবিজ্ঞানীরা জানান—‘ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও আকার ধারণ করিয়াছে। পারস্যে ইসলাম পারসীক রূপ ধারণ করিয়াছে, প্রাচীন পারস্যের (জরাতুষ্টীয়) ছাপ তাহাতে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হক। তদ্রূপ উত্তর আফ্রিকার ইসলাম; সেখানে মারাবিটদের ভক্তি ও আজ্ঞাপালন করায় ধর্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। যবদ্বীপে ইসলামি সমাজ প্রাচীন হিন্দু কৃষ্টির প্রভাব হইতে আজও মুক্ত হইতে পারে নাই। পশ্চিম এশিয়ার তুর্কিদের মধ্যে নৈষ্ঠিক সুন্নীমত প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের পুরাতন কৌমগত অনেক রীতি-নীতি আঁকড়াইয়া ছিল বা আছে।’ (ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (৩য় খন্ড) বর্মন পাবলিশেং হাউজ কলকাতা-১৯৪৬, পৃ: ১৭০)
আর তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি চূড়ান্তভাবে ধর্মবিশ্বাস নয়, বরং ধর্মে আনুগত্য প্রকাশের এক একটি প্রক্রিয়া, যাকে সমাজবিজ্ঞানে প্রথা বলে। এই প্রথাই ধর্ম বিশ্বাসীর কাছে একসময় ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে।
মানুষ তার অন্তরে যে বিশ্বাসই লালন করুক, এখানে যতই সে কট্টর হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে সাংস্কৃতিক লেনদেনটা কোনোকালে কোনো যুগেই বন্ধ হয়নি। আর একজ্যই মানুষের মধ্যে মানুষের বোঝাবুঝির সম্পর্কে তৈরি হয়েছে সহজেই। এই বোঝাপড়ার সম্পর্কটা তৈরি করতেই মুহম্মদ বলেছেন চীনে যেতে। আজ আমরা অন্য যেকোনো মতালম্বী মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অস্বীকার করছি, হিন্দুর আচার বলে যা কিছু প্রত্যাখ্যান করছি; কিংবা মুসলিমের আচার বলে যা কিছু আঁকড়ে ধরে নিজেদের সমাজ থেকে, বিশ্ব থেকে আলাদা করছি, সেই সব কিছুই আমরা যুগে যুগে কালে কালে কারও না কারও কাছ থেকে গ্রহণ করেছি, নিজেদের করে নিয়েছি।
ইতিহাস পাঠে জানা যায়—যেকোনো ধর্ম বিশ্বাসীর কাছে বিশ্বাসের ব্যাপারটি ছাড়াও একটি বিশেষ ধর্মীয় প্রথার প্রচলন থাকতে পারে। বাৎসায়নের কামসূত্রে দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত সুন্নত বা ত্বকচ্ছেদ সংস্কার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চানন তর্করত্ন বলেন—‘‘মুসলমানদের যেমন ‘সুন্নত ’ এই সূত্রেও সেইভাবের কর্ম্মের উল্লেখ আছে।’’ (ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রাগুক্ত: পৃ: ১৯৪)
তবে এই প্রথাটি মুসলিম সংস্কৃতি থেকে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা গ্রহণ করেনি বলে জানান ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। কেননা কচ্ছের ‘ভূজ’ নামক স্থানে যে তিনটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে, তা আরব ও ইহুদিদের স্মরণে কবরস্থানে প্রোথিত ছিল। আর সেগুলোর সময় কাল ১২৫ খ্রিস্টাব্দ। (প্রাগুক্ত: ১৯৫) অর্থাৎ এটি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা গ্রহণ করেছিল আরব ও ইহুদিদের কাছ থেকেই।
এদিকে অনেকেই মনে করে ‘ধুতি হিন্দুর পোশাক। কিন্তু জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখা গেছে—দক্ষিণ আরবের লোকেরা কোমরে জড়ানো আর হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরেন, যা ধুতির মতোই। সমাজ বিজ্ঞানীরা জানান, ‘ইজার’ পারসিকরা উত্তরের মেডীয়জাতির কাছ থেকে পরিধান করতে শেখে আর আরবরা পারসিকদের কাছ থেকে। সংস্কৃতে ‘ইজার’কে বলা হয় ‘চালনস’। মালয় দ্বীপে ইজার ‘চালনস’ নামে আজও পরিচিত। (প্রাগুক্ত: পৃ: ১৮২)
সমুদ্রগুপ্ত ও ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময় আবিষ্কৃত মুদ্রায় যে মূর্তি রয়েছে, তার পরনেও ‘ইজার‘ আছে বলে জানান ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এ জন্য আলবেরুনী ব্যঙ্গ করে বলেন, ‘হিন্দু অভিজাতেরা তখন ঢিলা পায়জামা পরিধান করে যে, তাহাদের পা দেখা যায় না। (প্রাগুক্ত: ১৮২)
হজরত মুহাম্মদের মধ্যে সৌর্হাদ্য প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন আইডিয়া আত্মস্থ করার যে দক্ষতা ছিল, তা তিনি তার সময় বিভিন্ন গোত্রের, সংস্কৃতির মানুষ ও জাতির কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। ‘তিনি যখন ইহুদি গোত্রগুলোর সঙ্গে বসবাস করছিলেন, সেই সময়ে জেরুজালেম টেম্পলকে তার নামাজ পড়ার দিকে তথা প্রথম কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (সাইমন সেবাগ মন্টিফিওরি, জেরুজালেমের ইতিহাস, অনু: মোহাম্মদ হাসান শরীফ মাসুম বিল্লাহ, চারদিক, ঢাকা-২০১৪, পৃ: ২৫০)। কিন্তু ইহুদিরা যখন তাকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে তখন তিনি কিবলা পরিবর্তন করে জেরুজালেম থেকে মক্কা করলেন (প্রাগুক্ত: পৃ: ২৬০)। তাই বলে তিনি ইহুদি সংস্কৃতি বিসর্জন দিতে পারেননি। সংস্কৃতির এই সক্ষমতা; আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা। তিনি শুক্রবার অর্থাৎ ইহুদিদের সাব্বাত ডে-তে প্রার্থনা করতেন, খৎনা যা ইহুদি প্রথা মেনে নিলেন, ইহুদিদের শুকর খাওয়া বর্জন করলেন, আবার প্রাচীন কপ্টিক বা আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান আম্মামে প্রচলিত সেজদা প্রথা গ্রহণ করলেন; খ্রিস্টানদের উপবাস পর্ব থেকে রোজা রাখার উৎসব গ্রহণ করলেন। ইসলাম আবির্ভাবের প্রাথমিক যুগে উসমানীয় ইহুদি, আর্মেনীয় ও আরব খ্রিস্টান ও মুসলমানরা পরত ফ্রক কোট বা সাদা স্যুট-এর সঙ্গে তাদের মাথায় শোভা পেত টারবুশ বা ফেজটুপি। মুসলিম আলেমরা পরত পাগড়ি ও জোব্বা। কোনো বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কিভাবে আরবের মুসলমানরা তাদের আনন্দ ভাগাভাগি করত, তা সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি বর্ণনা থেকেই আমরা জানতে পারি। তিনি বলেছেন, ‘রমজানের রোজার পর প্রাচীরগুলোর বাইরে সব ধর্মের লোকজন ভোজসভায় আপ্যায়িত হতোয়, সৌজন্য বিনিময় করত। নাগরদোলার ব্যবস্থা থাকত, ঘোড়দৌড় হতো, হকারেরা অশ্লীল পিপ-শো দেখাত, আরব মিষ্টি, বিশেষ ধরনের ফান, তুর্কি পিঠা বিক্রি করত। ইহুদীদের পুরিম পর্বে মুসলিম ও খ্রিস্টান আরবেরা ঐতিহ্যবাহী ইহুদি পোশাক পরত তিন ধর্মের লোকেরাই দামাস্কাস গেটের বাইরে ন্যায়পরায়ণ মাইমনের সমাধিতে (টম্ব অব সাইমন দ্য জাস্ট) ইহুদি পিকনিকে শরিক হতো। ইহুদিরা তাদের আরব প্রতিবেশীদের ম্যাটজা (বিশেষ ধরনের রুটি) উপহার দিত, পাসওভার সেদের ডিনারে দাওয়াত করত। বিনিময়ে আরবেরা উৎসবশেষে ইহুদিদের নতুন করে বানানো রুটি উপহার দিত। খৎনা করাত। মুসলিম প্রতিবেশীরা হজ করে ফিরে আসার পর ইহুদিরা তাদের জন্য পার্টির আয়োজন করত। আরব ও সেফার দিক ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।’ (প্রাগুক্ত: পৃ: ৫০০)
সেই সময় আরববিশ্বে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিল যে ‘মুসলমান বিজয়ীরা প্রথম দিকে খ্রিস্টানদের সঙ্গে তীর্থস্থানগুলো খুশিমনে ব্যবহার করত। দামাস্কাসে তারা কয়েক বছর সেই জন্য চার্চ যৌথ ভাবে ব্যবহার করে, উমাইয়া মসজিদে এখনো সেই জন দ্য ব্যপ্টিস্টের সমাধি রয়ে গেছে। জেরুজালেমের চার্চগুলো একত্রে ব্যবহারের কয়েকটি বর্ণনা দেখা যায়। নগরীর বাইরে ক্যাথিসমা চার্চে সত্যিই মুসলমানদের একটি মেরহাব ছিল। ওমরের কিংবদন্তির বিপরীতে মনে হচ্ছে, টেম্পল মাউন্টে জায়গা করার আগে মুসলমানেরা হলি যেপালচরের ভেতরে কিংবা বাইরে প্রথম নামাজ পঙ্গ ছিল।… বলা হয়ে থাকে, ইহুদিদের সঙ্গে খ্রিস্টানরাও মুসলিম সেনাবাহিনীতে ছিল’। (প্রাগুক্ত: পৃ: ২৬৬)
বাংলাদেশ বা ভারতের মুসলমানদের ক্ষেত্রেও সাম্প্রায়িক সম্প্রীতির মধ্যে এ রকম প্রাণের দরদের কোনো অভাব ছিল না কোনোকালে। তাই হিন্দুর সত্য নারায়ণ ঠাকুর মুসলমাননের সত্যপীর বলে শ্রদ্ধা পান। অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় মুসলমানের পীরকেন্দ্র আছে, যেখানে হিন্দু গিয়ে পূজা দেয় আর সাঁওতাল তাকে বং দেবতা মনে করে পূজা করে। (ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রাগুক্ত: পৃ: ১৭৮) কিন্তু কারও ধর্মবিশ্বাসে ঈশ্বর-বিশ্বাসে কোনো ফাটল লক্ষ করা যায় না। মানুষ কোনো যন্ত্র নয় যে, সে চিরকাল সিস্টেম মেনে চলতে পারবে কিংবা তা চাইবে। এ রকম হলে যে অভ্যস্ত এক অসাড় বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, প্রতি বসন্তে নতুন নতুন ফুল ফুটাইতে চাই না—আমরা ফুলগুলোকেই নতুন করে দেখতে চাই। ঠিক একইভাবে আমাদের বিশ্বাসের ঈশ্বরকেও আমরা নুতন করে, বিশেষভাবে, বিশেষ পদ্ধতিতে আপন করে পেতে চাইলে ক্ষতি কী! এ জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেন—‘সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্ম রক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষগণ্ডি আঁকিয়া একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে বন্ধ করে।’ অতএব জ্ঞান চর্চার সাহায্যে সংকীর্ণতা পরিহার না করলে আমরা বাঙালি হিসেবে তো বটেই, একটি বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবেও পৃথিবীতে টিকে থাকতে সমর্থ হব না।
আমাদের মনে রাখতে হবে—একজন মানুষ হিসেবে আমরা জীবন সম্পর্কে একটিমাত্র তত্ত্বগত পাঠগ্রহণ করতে পারি না। কেননা, আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে মানবীয় সত্তায় রূপান্তরিত করে বিশেষ এক সামাজিক সত্তা তৈরির দায়িত্ব রয়েছে আমাদের। তাই আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে যত দ্রুত আমরা একে অন্যের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্কে তৈরি করতে পারব, ততই আমরা সংঘাত এড়িয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যক্ষম হব। আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না—পৃথিবী আমাদের সরাইখানা নয়! এটি সব জাতির বাসস্থল।