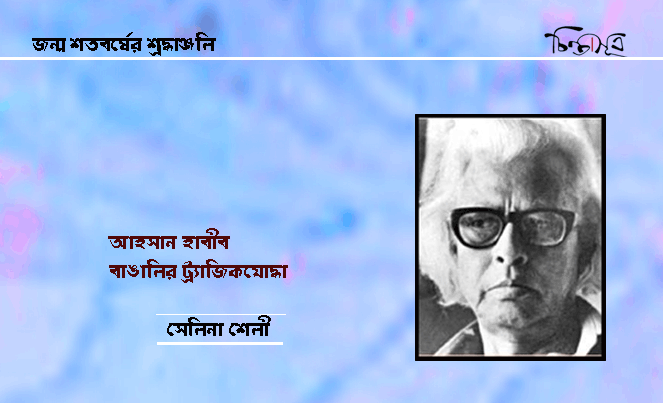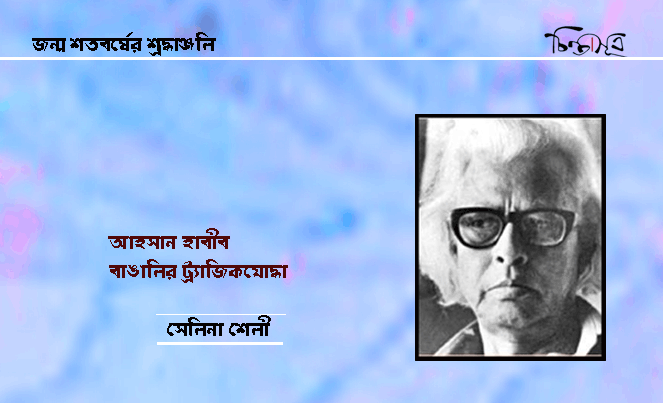 মনে পড়ে, ১৯৮৫ সালে আহসান হাবীব যখন হাসপাতালে, চাটগাঁয় আমরা কী ভীষণ উদ্বিগ্ন—নভেলটি চাখানায়, লালদিঘির তালসুপারি তলায়, বোসব্রাদার্সে। কবির মৃত্যুর (১০ জুলাই ৮৫) প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ক-এর কবিরা (ক নামে একটি কবিসংঘ ছিল চাটগাঁয়; সম্ভবত নামটি দিয়েছিলেন আসাদ মান্নান; সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এজাজ ইউসুফী, হাফিজ রশিদ খান, আবু মুসা চৌধুরীসহ অনেকে) কাপাসগোলা হাইস্কুল মিলনায়তনে একটি স্মরণানুষ্ঠান করি। এরপর দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর তাঁকে নিয়ে আর একটি অনুষ্ঠানও আমার নজরে পড়েনি। আজকের তরুণ কবিতাকর্মীরা আহসান হাবীবকে কতটুকু জানেন, সে বিষয়েও আমি সন্দিহান।
মনে পড়ে, ১৯৮৫ সালে আহসান হাবীব যখন হাসপাতালে, চাটগাঁয় আমরা কী ভীষণ উদ্বিগ্ন—নভেলটি চাখানায়, লালদিঘির তালসুপারি তলায়, বোসব্রাদার্সে। কবির মৃত্যুর (১০ জুলাই ৮৫) প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ক-এর কবিরা (ক নামে একটি কবিসংঘ ছিল চাটগাঁয়; সম্ভবত নামটি দিয়েছিলেন আসাদ মান্নান; সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এজাজ ইউসুফী, হাফিজ রশিদ খান, আবু মুসা চৌধুরীসহ অনেকে) কাপাসগোলা হাইস্কুল মিলনায়তনে একটি স্মরণানুষ্ঠান করি। এরপর দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর তাঁকে নিয়ে আর একটি অনুষ্ঠানও আমার নজরে পড়েনি। আজকের তরুণ কবিতাকর্মীরা আহসান হাবীবকে কতটুকু জানেন, সে বিষয়েও আমি সন্দিহান।
আহসান হাবীবের কবিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের তর্জমা। সামাজিক-রাষ্ট্রিক তথা মানবিক মূল্যবোধে তাঁর কবিতা নানাভাবে অণুরিত হয়েছে। বাংলা কবিতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে—ভারতের এক উত্তাল সময়ে—তাঁর আবির্ভাব। ভারত তখন বিক্ষুব্ধ, ভাঙছে, মত ও পথ বদলাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অস্থিরতা, হতাশা ও আশা তখন কবিদের মজ্জা ও মননে। স্বপ্ন অনেকটাই তিরোহিত। রক্ত ও মৃত্যুর পথ ধরে ১৩৫০-এর মন্বন্তরের ভয়াল রূপ, জয়নুলের ক্ষুধাদীর্ণ মৃত্যু-আকীর্ণ ছবির টান-টান রেখা কবিদেরও মানসপটে। মহামারি, নৈতিক অবক্ষয়, অবিশ্বাস চারিদিকে। নজরুল বাকরহিত, রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত। আর ‘পঞ্চপাণ্ডব’ নামে খ্যাত কবিরা বাইরের বিশ্বের হাতছানিতে নিমগ্ন। অন্যদিকে ইসলামি মূল্যবোধের কবিতার ধারা। এ রকম একটি সময় বাংলা কবিতাকে আপনার ঘরে ফিরিয়ে আনলেন তিনি। বাংলা কবিতা আবারও ফিরে পেল তার প্রাণ—তার গান, সুর, ঘরদোর, উঠোন, পুকুর, ঝিঁঝিঁপোকা, নদী, পাখি, নারী, বালক, রাখাল—সব। এই বিপুল মোড়ফেরানোর বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।
কবির কৃত্যে বা মননভাবনায় তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতা অনিবার্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যে পরিবারে তিনি লালিত হন, যে-সমাজে বা যে-সাংস্কৃতিক আবহে কবি বেড়ে ওঠেন, তারও প্রভাব অনিবার্য। কবি আহসান হাবীবে আমরা সেটি গভীরভাবেই প্রত্যক্ষ করি। কবির জীবনদর্শনে সেই আদর্শের বারুদই পোরা ছিল। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, অতৃপ্তি, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি তার মুল্যবোধটিকে তুলে এনেছিলেন। সেই সময়ের কবিতার গতিপ্রকৃতির একেবারেই বিপরীতে তিনি উঠে এসেছিলেন গভীর সংবেদনশীলতায়—মাটি ও মানুষের কথা নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে। কাব্যস্বরে সমকালীন কবিদের থেকে শুধু আলাদাই করননি নিজেকে, আশ্চর্যরকম সমাজ ও সময় মনস্ক, নিরুপদ্রব, শান্তশ্রী হয়ে উঠেছেন। ফলে নিবিড় অনুভূতিসম্পন্ন এক কবিকে চিনে নিতে দেরি হয়নি সচেতন পাঠকের। বাঙালি ভূখণ্ডের এক স্বাপ্নিক কবি হয়ে তিনি গ্রামবাংলার মিথ আর স্বপ্নপুরাণ বুনে গেছেন বাংলা কবিতায়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নতুন চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে কবিতা না-লিখলেও তাঁর কবিতায় শ্রেণিসচেতনতা প্রকট (যদিও সুকান্তের মতো বৈপ্লবিক ধারায় তা উৎসারিত নয়)।
অতি সাধারণ একটি পরিবারে তাঁর জন্ম। কবি আহসান হাবীবের জন্ম ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি। জন্মস্থান ও পৈতৃক আবাস বরিশালের শঙ্করপাশা গ্রামে। বাবা হামিজ উদ্দিন হাওলাদার, মা জমিলা খাতুন। পাঁচ ভাই ও চার বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আহসান হাবীব ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রকৃতিমগ্ন, নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকা এক আত্মকেন্দ্রিক বালক। ছাত্রজীবনেই তাঁর কবিতার হাতেখড়ি। প্রথম কবিতা ছাপা হয় পিরোজপুর সরকারি হাইস্কুল বার্ষিকীতে। কবিতার নাম ছিলো ‘মায়ের কবর পাড়ে কিশোর’। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ১৯৩৪ সালে, ভর্তি হন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে। এক পর্যায়ে বাবার ওপর রাগ করে ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে ভারতের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে পিরোজপুরের ইন্টারমিডিয়েট ১ম বর্ষ পাস করা একটি ছেলে কী অসীম সাহস আর দার্ঢ্য নিয়েই না সাহিত্যচর্চার জন্যে কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।
১৯৫০ সালে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে এসেই তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে সাহিত্যপাতা সম্পদনা শুরু করেন। আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ রাত্রিশেষ। প্রকাশসাল- ১৯৪৭ এ কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কমরেড পাবলিশার্স থেকে। এই বইয়ে খণ্ডিত ভারতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালিকে অখণ্ডরূপে ফিরে পেতে-চাওয়া এক কবিকে পাওয়া যায়:
নিবিড় রঙের আবরণ যে আভরণের তলে
এই পৃথিবীর কুৎসিত প্রাণহীন কামনায় জলে
প্রেমহীন সেই বন্ধুর দেশে নীড় বাঁধলাম তবু
এই মন আর এ মৃত্তিকার বিচ্ছেদ নাই কভু।
রাত্রিশেষের জটিল সেই দুঃস্বপ্নের সমাপ্তিতে নতুন দেশের স্বপ্নবোনা যে ভূখণ্ড তিনি পেয়েছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার বাংলা’ নজরুলের ‘বাংলাদেশ’ অথবা জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’ ছিল না। তাই ওই যুগসন্ধিক্ষণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সেতুবন্ধন রচনা ছিল তাঁর কাঙ্ক্ষা—
রাত্রিশেষ
কুয়াশার ক্লান্ত মুক সীতের সকাল
পাতার ঝরোকা খুলে ডানা জাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল।
(শীতের সকাল: ছায়া হরিণ)
আহসান হাবীব এক নিভৃতিচারী কবির নাম।
অনেকে তাঁকে ‘মৃদুভাষী’ কবি বলে উল্লেখ করেছেন, যা কবির অপছন্দ ছিলো। জীবনের শেষ ধাপে এসে এক গদ্যে তিনি বলেছিলেন—‘আজ আমি বলি, অহংকার করেই বলছি, পরাক্রান্ত ক্ষুধাকে আমি কবিতার ওপরে হুকুম চালাতে দেইনি। ফিরে যাইনি পিরোজপুর অথবা শঙ্করপাশায়, আপন বিবরে। তবে এই সময়ে ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারি—ক্ষুধাই সেই হননকারী শত্রু যে মানব জীবন থেকে উপকরণ গ্রুণ করে, তাকে কবিতাহীন নরকে অনবরত আছড়াতে থাকে। আরো বুঝতে পারি, এই অনিবার্য ক্ষুধা মানুষই তৈরি করে- মানুষের মধ্যে। এবং এই সময় থেকেই কবিতা আমার আক্রান্ত হতে থাকে ক্ষুধার হাতে। তার অর্থ কবিতা তাঁর চরিত্র বদলাতে থাকে। ক্ষুধার সেই রাজ্যে কবিতা কিছু বলার দায়িত্ব নিতে থাকে। প্রথম কাব্য গ্রন্থ রাত্রিশেষ তৈরি হতে থাকে এই পরিবেশে। বণ্টনবৈষম্য, সামাজিক অসাম্য, পরাধীনতা, স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং মহাযুদ্ধের দায় এই সবই সমগ্র রাত্রিশেষের উপজীব্য। উত্তরতিরিশ কবিতার সমাজসচেতন অধ্যায়ে নিজের সংলগ্নতা আমি এভাবেই এই সময়ে আবিষ্কার করি।’
আহসান হাবীব একজন স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনার কবি ছিলেন। কোনো রকম কূপমণ্ডূকতা সামাজিক ধর্মীয় বা নৈতিক অবক্ষয়কে যেমন ব্যক্তি জীবনে তেমনি কাব্যেও তিনি স্থান দেননি। তাঁর কবিতাই সেই সাক্ষ্য বহন করে:
আমি তো এখন আপনার প্রজা নই,
আর তো আপনার মাখা তামাক খাই না।
নিজে মাখি নিজে খাই কোথাও যাই না
এখন হয়েছি নিজ স্বাধীন।
কবি যে সময়ের চেয়ে কত বেশি অগ্রসর ছিলেন তা আরও গবেষণার দাবি রাখে ।আজীবন আপসহীন এই কবি– সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে যে কারুর মন্দ কবিতা যেমন নির্দ্বিধায় ফেলে দিতেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের সঙ্গে কোনোভাবেই আপস করতেন না। মানুষের আদর্শিক দিকটি নানা কৌশলে জেনে নিতেন।অনেকেই তাঁর কবিতায় নেতিবাচক সময়-সমাজের চিত্র দেখে তাঁকে হতাশাবাদী কবি বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আহসান হাবীব নিজেই লিখেছেন—‘আমি বুঝি না যেখানে হেরে যাওয়ার পালা, সেখানে খামোখা জিতিয়ে দিয়ে আত্মপ্রতারণায় কী লাভ? আমরা কী মনে রাখতে পারি না, এই হারাই সমাপ্তি নয়। বরং জয়ের ইঙ্গিত এখানেই আমরা কি মনে রাখব না, বার বার হেরে গিয়ে জয়ের যে নেশা আমাদের বিষণ্ণতাকে ক্রমান্বয়ে নতুন নির্মাণের কৌশল জোগায় তারই নাম জীবন।
আমি তো মনে করি, বিষণ্নতার যে বঞ্চনার ফলে সেই বঞ্চনাকে এ বিষণ্নতার মাধ্যমেই জীবনকে স্পষ্ট করে তুলি না কেন? বিষণ্নতাই আমার বঞ্চিত জীবনকে নিরাবরণ করে, নগ্ন করে তুলুক,প্রখর হয়ে উঠুক বিষণ্নতা, বঞ্চনা জ্বলে জ্বলে উঠুক।’ তারপর ক্রমান্বয়ে ‘ছায়া হরিণ’, ‘সারা দুপুর’, ‘আশায় বসতি’, ‘মেঘ বলে চৈত্রে যাবো’, ‘দুই হাতে দুই আদিম পাথর’ ও ‘প্রেমের কবিতা’।
শ্রেণীবৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্তজীবনের কৃত্রিমতা এবং উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু যৌবনের যন্ত্রণা—এসবই আজ পর্যন্ত আমার কবিতার বিষয়বস্তু। সুধীজনদের কেউ কেউ বলেন, বলতে-বলতে চালু হয়ে গেছে, আহসান হাবীব মৃদুভাষী কবি। কবিতায় মৃদুভাষিতা কী জিনিস, আমি কিন্তু বুঝি না। ভালো কবিতা আর মন্দ কবিতা বুঝি, সার্থক রচনা আর অসার্থক রচনা বুঝি।
কবি আহসান হাবীবের ৮টি কাব্যগ্রন্থ, ৪টি শিশুকিশোরপাঠ্য ছড়ার বই, তিনটি উপন্যাসসহ মোট ৩০টি গ্রন্থ রয়েছে। একমাত্র শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘বিদীর্ণ দর্পণে মুখ’—এর ফ্ল্যাপেই কবি তাঁর নিজস্ব কিছু বক্তব্য (ওপরে অংশত উদ্ধৃত) ছাপিয়েছেন। এছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থের ফ্ল্যাপেই কবি তাঁর কোনে পরিচিতি বা ফটোগ্রাফ ব্যবহার করেননি। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই চাকরি যাওয়া আর পাওয়ার দোটানায় কেটেছে তাঁর। তবু কোনো লোভ বা অনৈতিকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। যারা তাঁকে জানেন, সবাই একবাক্যে কবির নৈতিক সৌন্দর্য ও পরিশুদ্ধ মার্জিত ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছেন। জীবনে ও কাব্যে তিনি অত্যন্ত সতর্ক মানুষ ছিলেন। যখন তিনি সম্পাদক, খ্যাতিমানদের দুর্বল লেখা নাকচ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ নিয়ে কারও-কারও সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও সাহিত্যের বিচারে তিনি কখনো ছাড় দিতেন না। দৈনিক বাংলার সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনাকালে, শেষ পর্যায়ে, কবি নাসির আহমেদ তাঁর সহকারী ছিলেন। নাসির আহমেদ তাঁর এক গদ্যে জানান, ‘সম্পাদক হিসেবে কতোটা সুবিবেচক ছিলেন তিনি, তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। মফস্বলের সম্ভাবনাময় লেখকদের লেখা যেন ফাইলচাপা পড়ে না—থাকে, সেজন্য তিনি দৈনিক বাংলায় তাঁর দফতরে পৃথক ফাইলে তাদের লেখাসংরক্ষণ ও প্রতি সপ্তাহে প্রেসে পাঠাবার আগে একবার ওই ফাইল থেকে লেখা বিবেচনা করতেন। এ দৃষ্টান্ত এদেশের সাহিত্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রায় বিরল। ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো লেখার গুণাগুণ বিচারে তাঁকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না।
কবি আহসান হাবীব মানুষকে বড়বেশি শ্রদ্ধা করতেন। ভালোবাসতেন এই বাংলার সব কিছুই। তবে জীবনানন্দের মতো ‘আবার আসিব ফিরে’ বলেননি; বরং প্রতিবাদ করেছেন এই বাংলা ছেড়ে যেতে—‘তবে কেন যাবো, কেন যাবো স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ বিভূঁয়ে?’ আত্মপ্রচারবিমুখ এই কবি চিন্তাচেতনায় ছিলেন আধুনিক ঋদ্ধ রুচিবোধসম্পন্ন—নির্মোহ। কৈশোরের ছেড়ে আসা গ্রামকে তাঁর প্রায় সব কাব্যগ্রন্থেই লালন করেছেন। এই বাংলার পুথি, পুরাণ, মেলা, মেলার পুতুল, ভাটিয়ালি, কাজেম বয়াতি, রাখাল বালক নেহাল উদ্দিন, পাখির পায়ের দাগ, নদী, বাঁশবাগান, ফুল, নারী, নিশিরাত, সব কিছুই তাঁকে স্পর্শ করেছে। নিজেকে জানতেন এই মাটির পুত্র হিসেবে। কবি তাঁর ভেতকার বালকটিকে কখনো রাখাল, কখনো রোদকুড়োনো ছেলে, কখনো স্কুলযাত্রী, এমনকী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেও দেখিয়েছেন। প্রতিটি কবিতা অসংখ্য টুকরো-টুকরো দৃশ্য পরম্পরায় গাঁথা। লোকজীবনের কথ্যভঙ্গি এবং ছন্দটিও তাঁর অনায়াসসাধ্য ছিল। ব্যাপক জীবনের শান্ত অথচ নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারা ধরা পড়ে তাঁর কোনো কোনো কবিতায়:
রোদবৃষ্টিতে মাখামাখি আকাশের নিচে সন্ধ্যা
আসে এক সময়
এক সময় রাত নামে
স্বপ্ন আরো গভীর হয়ে যায় চাঁদ এবং
নক্ষত্রের ভেজা গায়ে।
রাত বাড়তে থাকে
হাতের মুঠোয় একটি মৃদু টংকার স্বপ্নময়
খালেক নিকিরের চেতনা জুড়ে
সেই তারই স্বপ্ন স্রোত। অবিরত অবিরল
ঘুঘু কাঁঠাল পাতা নিম কিংবা নিশিন্দা
এরকম কোন স্বপ্ন
আপাতত খালেক নিকিরের নেই
না ঘুমে না জাগরণে
(আহবান: আহসান হাবীব)
কবিমাত্রই স্বাপ্নিক। কাহলিল জিবরান আর গান্ধী যেমন স্বপ্নকে এক উচ্চতর বাস্তব (Higher reality) ভাবতেন, অথবা মার্কেজ যেমন স্বপ্নকে জীবনের ছোট অংশ বলে মনে করতেন, সে রকম নয়—স্বপ্ন জাগরণেই আহসান হাবীব বাস করতেন শাশ্বত বাংলার প্রতিটি অনুষঙ্গে:
আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকী সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল, জামরুল, সাক্ষী
পূবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থিরদৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো আগন্তুক নই।
কবি এ-ও জানতেন, একদিন তিনি এই সুন্দর দেশে থাকবেন না। যদিও সেই নির্মমতাকে মেনে নিতে কষ্ট হয় কবির। কেননা:
শৈশবে এই পাথর খণ্ডে বসে
আমি সূর্যাস্ত দেখতাম
রাখাল এই পথে ফিরতো
আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতো
…
এই বিকেল আমার সঙ্গে যাবে না
তবে কেন যাবো?
কেন যাবো স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ বিভূঁয়ে
অন্ধকারে?
প্রস্তুতি বড় কষ্টের।
আমার কোন প্রস্তুতি নেই।
প্রস্তুতি বড় কষ্টের
আমার কোনো প্রস্তুতি নেই।
প্রকট মৃত্যু চেতনাগন্ধী কবিতার মধ্য দিয়েই কবি চলে গেলেন। একেবারে প্রস্তুতিহীন ভাবেই, রেখে গেলেন কবিতার যে অমিত শস্যভাণ্ডার, তা আগলে রাখার দায়িত্বে তো আমাদেরই। আমরা, যারা কবিতাকে, দেশকে, মাকে ভালোবাসি।