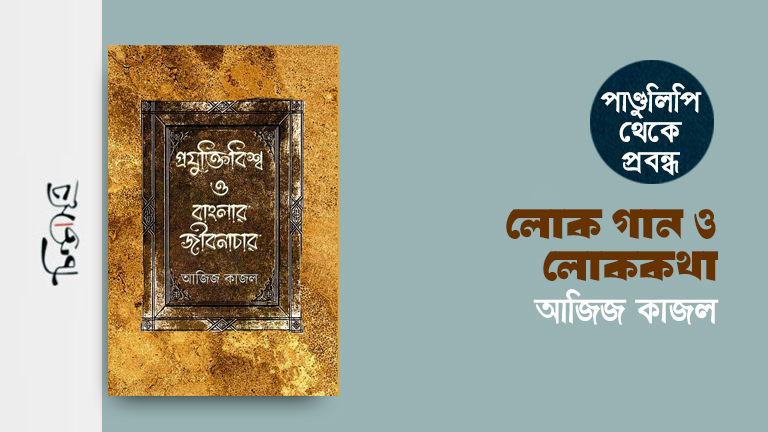০১.
পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা সংসার ধর্ম পালন করেও এক ধরনের নিরুপদ্রব বৈরাগ্য জীবন পছন্দ করেন।দেশ কাল পাত্রভেদে কিছুটা ভিন্ন হলেও একটি জায়গায় তাদের মিল বা সমতা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। অনেকটা স্রোতের বিপরীতে এদের অবস্থান। তারা কারো ক্ষতি সাধন করে না। অপ্রত্যাশিত জুটঝামেলাও পছন্দ করেন না। কিন্তু মাঝেমধ্যে নিজের অভিরুচি, অভ্যাস ও আচরণের একটা প্রতিফলন ঠিকই ঘটিয়ে দেন। ভাটি-বাংলার ভূগোল ও পরিপার্শ্ব দ্বারা প্রভাবিত (স্থান-কাল-পাত্রভেদে) এমন কিছু মানুষের উপস্থিতি আমাদের চোখে পড়ে। এরা গ্রামের বিয়েশাদী, গায়েহলুদ, আকিকা, খতনা, মেজবানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে হাঁটখোলা, দোকান পাঠে অপ্রত্যাশিত আসর জমিয়ে বসেন। কেউ করেন ধর্মগীত। কেউ করেন গান। কেউ ঢোল বাজান। কেউ একতারা, দু’তারা, কেউ হারমোনিয়াম! কেউ হঁলাগান, মজাদার কৌতুকে মানুষের ভেতরের আবেগ ও কৌতূহলে পুরো পরিবেশ জমিয়ে রাখেন। তাদের আছে আলাদা একটি জগত ও শিল্পক্ষুধা। আসর জমানোর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে অভ্যাসবশত তারা কখনো পুকুর ঘাটে, নদীর পাড়ে, জমিনের আলপথের নিভৃত কোনে বিড়বিড় করে—এভাবে জোর গলায় তাদের প্রতিদিনের চাহিদা, চর্চা ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটান।
বাংলাদেশের এমন কোন গঞ্জগ্রাম নেই, যেখানে এমন মানুষের উপস্থিতি কমবেশি চোখে পড়ে না। অন্যদিকে শহরের নাগরিক রুচির (কেতাদুরস্ত) বিপরীত পরিবেশেও এদের দেখা মেলে। ভর দুপুর, বিকাল, সান্ধ্য বা গভীর রাতে, রেলের রাস্তা ঘেঁষে, ঝুপড়ি চা’র দোকানে অথবা কোলাহল ছাড়া নির্জন কোন স্থানে, এমন কতিপয় শিল্পীর দেখা ঠিকই পাওয়া যায়। চোখের সচেতন দৃষ্টি ও সংবেদন থাকলে আমাদের আশেপাশেই আছে এদের অবস্থান।
এ ধরনের সংবেদনশীল মানুষকে ভুলবশত অনেকে মাথানষ্ট বলেও তাচ্ছিল্য করতে দ্বিধা করেন না। আসলে এরা হচ্ছে আমাদের ভাটি বাংলার আবহাওয়া ও মৃত্তিকা গঠিত আবেগের বরপুত্র। যারা সম্পূর্ণ ন্যাচারাল—ঐতিহ্যলগ্ন ও প্রকৃতিগত। বাংলার নানা লোক আচার ও বংশ-পরম্পরার ধারক ও বাহক। এদের মনের ভেতরের সংবেদনগুলো সম্পূর্ণ প্রকৃতি প্রাপ্ত ও অর্থবহ। জগত সংসারের গূঢ় তাত্ত্বিক হাওয়ার সবচেয়ে সংবেদন সুর ও বচনটি তাদের হৃদয় ও মস্তিকের ভেতরেই আগে প্রবাহিত হয়।এইসব মানুষ সংসারে বা সমাজে এমন কিছু মন্তব্য বা আকর কথা বলেন;অনেক সময় পাশে থাকা সহধর্মীনিটি এবং কাছের মানুষগুলো তন্ময় বা অভিভূত হয়ে পড়েন। এরা একটি দুর্লভ বা বিপন্ন গোষ্ঠি। এদের মূল্যায়ন করার জন্য আলাদা অঞ্চলের মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন পড়ে। ঘরের বা নিজঘাটার মানুষ তাদের চিনতে পারেন না। অথবা চিনলেও তার সেই শ্রেষ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে মরণোত্তরে। আঞ্চলিক বাক্যে একটা কথা প্রচলিত আছে, ঘরের গরু ঘাঁটার খের (ঘাস বা বিছুলি) খায় না।
আঠারো শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার হিন্দু সমাজে কবিওয়ালা ও মুসলিম সমাজে শায়েরের উদ্ভব ঘটে। এই প্রাতিষ্ঠানিক নাম-গন্ধের বাইরেও অনেক মানুষ স্ব স্ব ধর্মের প্রতিনিধিত্বসহ স্বনামে-বেনামে শতো শতো বচন, গান, কথামালা তৈরি করে চলেছেন। উদাহরণ হিসেবে ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অথবা ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় কদাচিৎ কিছু সংবাদে(কতিপয় মানুষের) এমন কিছু বিষয় আমাদের চোখে পড়ে।
বিশ্ব-মুলুক ছাড়িয়ে বাংলা মূলুকের আনাচে কানাচে এখনো ছড়িয়ে আছে মাইকেল জ্যাকসনের ভক্ত। ঝালমুড়ি, ভাঙারি, পান-সিগারেটের ক্ষুদে পেশা থেকে শুরু করে কেতাদুরস্ত স্মার্ট পেশার মানুষ পর্যন্ত সবাই জ্যাকসনকে (তার ভিন্ন রকম উপস্থাপনাকে বাংলার লোকজ গান, স্টাইল, ভঙ্গির আদলে) সমন্বয় করে নিজের পেশাকে অন্যরকম লাভের উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। মাইকেল জ্যাকসনের মতো বিশ্ব সংস্কৃতির এমন কিছু নক্ষত্র, উজ্জ্বল প্রদীপকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই পৃথিবীবাসীর।
রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাক ব্যবস্থা, জেলা, মহকুমার থানাসহ এইসব শব্দবন্ধের (যান্ত্রিক বিকাশের) বড়ো প্রতিনিধিত্বকরে, ব্রিটিশরা কলকাতা কেন্দ্রিক নগরায়নের পত্তন ঘটায়। এর মধ্য দিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়। এবং ধীরে ধীরে তা সর্বত্র উভয় বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়ে।ইউরোপীয় শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি-প্রভাবিত ধারার বিপরীতে বাংলার প্রান্তিক সমাজেও আরেকটি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা নানাভাবে বিকাশমান ছিলো। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ যারা, তারাও এই প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি। ধর্মবোধ ও জীবনবোধে, চেতনে অবচেতনে তারাও একটি স্বকীয় মানবিক ধারার প্রতিনিধি বলে ধরে নেওয়া যায়। এ বিষয়ে যতীন সরকার এর ভাবনা-প্রত্যয়টি অর্থবহ বলে মনে হয়—’তাদের নিজস্ব ধর্মবোধে শাস্ত্রীয় হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্মের হুবহু অনুসৃতি ছিলো না। তাদের ঈশ্বর বিশ্বাসও শাস্ত্রীয় ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে পৃথক। ঈশ্বরকে ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁরা মানবদেহের মধ্যেই উপলব্ধি করেছেন। যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে’—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে তার সবই আছে মানবদেহের ভেতরে—এটিই তাঁদের ধর্মবোধ ও জীবনবোধের ভিত্তি।” অর্থাৎ চেতনে অবচেতনে মনরে মন চলো বৃন্দাবন—এই প্রত্যয়, বিশ্বাস ও মোহে তারা প্রতিনিয়ত জগত সংসারে বিচরণ (সংহত ও সংযতভাবেও) করছেন।
বাংলাদেশের লোক সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক নামের মধ্যে আছে বাউল, গম্ভীরা, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কবিগান, কীর্তন, গাজন, ভাদুগান, ঝুমুর গান, ঘেঁটু গান, জারি গান, সারি গান, বারোমাসি ইত্যাদি। এছাড়াও পয়ার, পাঁচালি,টপ্পাধুয়া, হঁলা, হামদ্, নাত, নতুন-পুরনো বাংলা-উর্দু-হিন্দি সিনেমার গান থেকে শুরু করে অঞ্চলভিত্তিক নানা লোকগান, বচন ও হরেক রকমের বৈচিত্র্যময় কথাশিল্প কমবেশি তারা গলায় ধারণ করে। এর মধ্যে অনেক গান ও কথা অঞ্চলভিত্তিক ও প্রকৃতিলগ্ন। ফলে এই কথামালা বাগানগুলো এক নিবিঢ় মায়ার বন্ধনে পুরো পাড়া-মহল্লায় যেন বিস্তৃত থাকতো। অঞ্চলভেদে, সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন; ধর্মীয় পুরাণ গাঁথা থেকেশুরু করে শিক্ষা-রুচি, খাওয়া-দাওয়া-চলাফেরা ও অভ্যাসভেদে একটি এলাকার জন মানসের মনস্তত্ত্বের ওপর ভর করে এইসব আয়োজন চলতো।
বিশেষজ্ঞ মতে পাকিস্তান জন্মের পরপর কবিগানের যে লোকায়ত ধারা সেটি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অথবা নিজস্ব প্রচেষ্টায় তা ক্ষীণ হয়ে আসলেও নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত, ঘন-প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব প্রভাবিত ভাটি বাংলার মানুষের আবেগে (ধীরে হলেও নানাভাবে নানা প্রকরণে) তা চলমান আছে। আসলে দরগা সিন্নী-মানত, পীর-মাজার বিশ্বাসীসহ শতো সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যায়ন, আমাদের রক্তের পূর্ব বৈশিষ্ট্য ও সংকরায়নের পরিচয় বহন করে। এই দেশে লালন, হাসন, শাহ আব্দুল করিম, রাধা রমণ, আসকর আলী পণ্ডিত থেকে শুরু মাইজভাণ্ডার—পুরো বাংলাদেশের অধ্যাত্ম এবং আধ্যাত্ম সাধনার ধারাকে একটি (অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু অবস্থা ছাড়া) পারস্পরিক সহাবস্থানের মধ্যে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।
“অ হালার চান গলার মালা”, “কি দু:খ দি গেলা মোরে”, “কইলজার ভিতর গাঁথি রাইক্কুম তুঁয়ারে”, “অরে আমার ময়না পাখি চিনোনি তারে”, ” মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে”, ওকি গাড়িয়াল ভাই” গান—ইত্যাদি ধারার গানগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক মাটিজাত-ঐতিহ্যের অন্যতম শক্তিশালী উদাহরণ। যা নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়িয়ে পুরো বাংলাদেশ তথা (বহির্বিশ্বসহ) বিভিন্ন জেলা উপজেলায়, পাড়া-মহল্লা গঞ্জগ্রামে খুবই জনপ্রিয় ও পরিচিত—বর্তমান মিডিয়ায় নতুন করে নতুন সুরে অথবা রিমিক্স ঢঙের প্রচারে নতুনত্ব পাওয়ায় গানগুলো এখন লোক মুখে দারুণভাবে চলমান আছে।
প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষের মনের যে শিল্পক্ষুধা তা তার পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু-নির্ধারিত। এ বিষয়ে কালজয়ী মনোবিদ ফ্রয়েডএর কথা বলা যায়। মানুষের মনকে তিনি ২টি ভাগে ভাগ করেছেন। ১ হচ্ছে সচেতন স্তর (Conscious mind) ২. অবচেতন স্তর (Unconscious mind)। সচেতন স্তরের পাশাপাশি অবচেতনে স্তরে মানুষের মনে এমন কিছু বিষয় মজ্জাগত থাকে যা আমরা নিজেরাও জানি না। এই স্তরে মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাসমূহ অবস্থান করে। যা উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে সমতা আছে। দুনিয়াতে কেউ পাখির আওয়াজ ভালো বুঝে, কেউ নদীর কলকল ধ্বনি, কেউ সাগরের উত্তাল ধ্বনি, কেউ আকাশের বিশালতা, কেউ পাহাড়ের মৌনতা ভালো বুঝে—কিছু মানুষের অনুভূতির দরোজায় এই ধ্বনি বা আওয়াজগুলো একটু অন্যরকম অনুরণন তৈরি করে। জগত সংসারের উল্লেখিত মানুষগুলোও এমন, যারা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অথবা তাদের বুঝতে চাই না।
পুঁজিবাদী বিশ্ব মোটা দাগে সবাইকে শারীরিক, মানসিক ও কাঠামোগত দিক দিয়ে একটা ফ্রেমে নিয়ে আসছে। ফলেপৃথিবীর বৈচিত্র্যায়নের বহমান অনেক সৌন্দর্য আমাদের কাছে নিতান্তই ঠুনকো আর মামুলি ব্যাপার হয়ে আছে; চেতনে-অবচেতনে বিষয়গুলো আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যাই অথবা না-পছন্দ করি। যদিও মিডিয়া এখানে প্রবল দানবীয় শক্তির বড়ো ভূমিকাটুকু পালন করে আছে। ডিজিটাল ভার্সনে সবকিছু কে একদম নিখুঁত! করে দেখার বাতিক—এটাও একটা বড়ো রোগ বা দোষ। মাটি বিমুখ থাকা বা মাটিলগ্ন বিষয়গুলো উপেক্ষা করাই যেন সহজ ও স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পশ্চিমা বিশ্বের (শতো-হাওয়ার মিক্স) অনেক কিছুর মাঝে ঢালাও করে হারিয়ে না গিয়ে বিষয়গুলোর প্রতিও আমাদের নজর দিতে হবে।
০২.
“আউল বাউল লালনের দেশে মাইকেল জ্যাকসন আইলোরে আরে সবার মাথা খাইলোরে”… শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদীর কণ্ঠে গাওয়া এই গান [১৯৮৬ তে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ঢাকা-৮৬’র একটি গান] একসময় বাংলাদেশ বেতার ছায়াছবির গানের আসরে প্রচুর শুনা যেতো। বিশ্বসংস্কৃতির সমান্তরালে বাংলা সংস্কৃতিতে মাইকেল যখন জুরালো ভূমিকা পালন করতে শুরু করলো, বাংলা সংস্কৃতি ডুবতে বসেছে বলে সুধীমহলের অনেকের কাছে বড়ো আক্ষেপ ছিলো। আমাদের সংস্কৃতি তবুও পারে নি বাইরের এই জ্যাকসনকে অস্বীকার করতে। বিশ্ব-মুলুক ছাড়িয়ে বাংলা মূলুকের আনাচে কানাচে এখনো ছড়িয়ে আছে মাইকেল জ্যাকসনের ভক্ত। ঝালমুড়ি, ভাঙারি, পান-সিগারেটের ক্ষুদে পেশা থেকে শুরু করে কেতাদুরস্ত স্মার্ট পেশার মানুষ পর্যন্ত সবাই জ্যাকসনকে (তার ভিন্ন রকম উপস্থাপনাকে বাংলার লোকজ গান, স্টাইল, ভঙ্গির আদলে) সমন্বয় করে নিজের পেশাকে অন্যরকম লাভের উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। মাইকেল জ্যাকসনের মতো বিশ্ব সংস্কৃতির এমন কিছু নক্ষত্র, উজ্জ্বল প্রদীপকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই পৃথিবীবাসীর।
মাইকেল জেকসনের হাত ধরে, পুরো বিশ্ব পেল কালজয়ী বড় নৃত্যশিল্পী ও গায়ক। বড় ড্যান্সার। মোটাদাগে বলা যায়, কুংফুতে ব্রুসলি।শরিরী সৌন্দর্যে আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার, জেমস বন্ড অথবা সত্যজিৎ এর মতো কালজয়ী মহান শিল্পীর কথা। এরা বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রত্যেকটি আর্টে বড় রকমের ছাপ ফেলেছেন। স্ব স্ব ক্ষেত্রে এরকম বহু শিল্পীর নিজস্ব স্টাইল, উপস্থাপন কৌশলের নান্দনিকতার হাত ধরে, পুরো বিশ্বেও বড় একটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের হাওয়া এখনও বিরাজমান আছে, থাকবে যা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
বাউল ধারার ইমেজ এবং আবহে-যেমন নগরে এসে নগর বাউল হয়েছে। এবং অনেকেই নাগরিক মেজাজ কে ধারণ করে নিজের শেকড়, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মেলানোর চেষ্টা করছেন। যা ইতিবাচক বলা যায়। তাই বাউলিপনা শতো রঙে থাকলেও মাটিজাত সংস্কৃতির এই কাণ্ড উপড়ে ফেলা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তার ভেতরের রস ঠিকই মাটির সাথে মিশে থাকে। বাংলার লোকগান এবং লোক কথার ক্ষেত্রেও যা সত্য।
…কালজয়ী মার্কস, সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও চার্লস ডারউইনকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না। সময়ের চেয়ে এগিয়ে এই মানুষেরা, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং উপলব্ধিকে পুরো বিশ্ব-মানুষের চিরন্তন অনুভূতি, সংবেদন, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের সাথে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এখানেই তারা সেরা। এখানেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।
১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন এর “অরিজিন অব স্পিসিস” প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিবর্তন তত্ত্বে নতুন চিন্তা পুরো বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলো।ঠিক এরপরেই ১৮৬১ সালে আমরা পেয়েছি—আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ সম্পন্ন বিশ্বজয়ী বাঙালি প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি উপনিষদ এর মধ্য দিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের (বস্তুগত চেতনা, অধ্যাত্ম, আধ্যাত্মসহ) স্পিরিচুয়ালিজমকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এবং চরম রোমান্টিকতায় রবীন্দ্রনাথ নানা প্রকরণে ইউরোপীয় রোমান্টিসিজম (রোমান্টিক আন্দোলন) এর অন্যতম এক্টিভিস্ট ওইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং এস টি কোলরিজসহ অনেকের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন।
বিষয়গুলো বলার আলাদা কারণ হলো ম্যাটেরিয়ালিজম (ইউরোপের আলোকিত বস্তুবাদ ও যান্ত্রিক জীবনের সাথে মিলিয়ে যে ম্যাটেরিয়ালিজম) আর স্পিরিচুয়ালিজমকে (প্রাচ্যের অধ্যাত্ম আর আধ্যাত্মের সাথে মিলিয়ে যে স্পিরিচুয়ালিজম) বুঝার জন্য। অর্থাৎ এতকিছুর মাঝেও কেউ তার ঘরের আঙিনা, পরিবেশ-পরিপার্শ্ব কে অস্বীকার করতে পারেন নি। হুমায়ুন আজাদ যেমন “আধুনিক বাংলা কবিতা”র উল্লেখযোগ্য সংকলনে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েও যেমন তাকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। অনেক লেখায় তিনি নানা প্রকরণের রবীন্দ্রনাথ এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তিরিশের ধী-সম্পন্ন শক্তিশালী প্রতিনিধি পঞ্চপাণ্ডব’র বেলায়ও যা সত্য। রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় লোক সাহিত্য, লোক গান, এবং লোকজ ধারার প্রতিও প্রবল আগ্রহী ছিলেন। সুধীমহলে লালন এবং হাসনরজা তার কল্যাণে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতসহ দেশাত্ববোধক অনেক গানেও তিনি ভাটি-বাংলার লোকজ আবহকে ধারণ করেছেন।
আমাদের বঙ্গে ইউরোপীয় কেতাদুরস্ত সাহিত্যের ভাণ্ড যখন আলগা করি, তখন পল্লীকবি জসীম উদ্ দীন কে আমরা অস্বীকার করি। শিল্পসাহিত্যে তার অবদানকে খাটো করে দেখি। “জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দু’খান সরু,গা খানি তার শাওন মাসের যেমন তমালতরু” বাংলার সবুজ কচিশ্রেষ্ঠ এমন লাউয়ের সবুজ বর্ণনা কী অসাধারণ! এই একটা লাইন থেকেই তৈরি হতে পারে গাঁওবান্ধব কতো সুন্দর কবিতা। এই মানসিক দৈন্য থেকেইতো আমরা আদর্শ পল্লীগ্রামকে অজপাড়া গাঁ বলে তাচ্ছিল্য করি। জসীম উদ্ দীনের কবিতায় পুঁথিসাহিত্য, লোককথা এবং লোকসঙ্গীতের প্রভাব ছিলো। বিশেষ করে কবিতার উপমা-উৎপ্রেক্ষাগুলো তিনি সবুজ ধানের সামান্য দুলুনি থেকেও বুনতে পারতেন। যার অস্তিমজ্জায় ছিলো সরল নিসর্গ-প্রভাবিত গ্রাম বাংলার অকৃত্রিম রূপ।
সাহিত্যে যখন রবীন্দ্র যুগ এবং নাগরিক সাহিত্যের দাপট চলমান, তখন এর সম্পূর্ণ বিপরীতে আরেকটি ধারাও কিন্তুসজীব ও চলমান ছিলো। যেটি সম্পূর্ণ ভূমিলগ্ন।সৃজনে মননে কেতাদুরস্ত সাহিত্যের চেয়ে এটি কম ঋদ্ধ ছিলো না। এমন শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বশীল শিল্পীদের অন্যতম হলেন হরিচরণ আচার্য, মুকুন্দ দাস, রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত সহ অনেকে। ক্রমান্বয়ে এই মৃন্ময় অথচ ধী-পথে হেঁটেছেন (অনেক শিল্পী ও কারিগর) আসকর আলী পণ্ডিত, গগন হরকরা, রাধা রমণ, উকিল মুন্সী, রমেশ শীল, জালাল উদ্দীন খাঁ, বিনয় বাঁশী, ফণী বড়ুয়া, এম এন আখতার, কুদ্দুস বয়াতী, কাঙ্গালিনী সুফিয়া, মমতাজ, শফী মণ্ডল, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, আব্দুল গফুর হালী, সৈয়দ মহিউদ্দিন, বুলবুল আক্তার, সিরাজুল ইসলাম আজাদসহ আরও অনেকেই। ময়মনসিংহ গীতিকার অনেক- গুলো পালা, কিংবদন্তি ও লোক কাহিনীর সাথে চট্টগ্রামের ভেলুয়া সুন্দরী পালা কে যেমন আমরা ঠিকই সামগ্রিক ভাবে মিলিয়ে নিতে পারি। সময় পরম্পরায় উল্লেখিত শিল্পী ও কারিগরদের বেলাতেও যা সমূহ সত্য বলে প্রতীয়মান করা যায়। কেউ গানে, কেউ সুরে, কেউ কথার ধ্রুপদি শক্তিতে একেকজন (কালের নিরিখে তাদের সময়ে তারা) একেকটা চিহ্ন বা দাগ লাগিয়ে দিয়েছেন। তাদের উৎপাদিত সুর, স্বর, শব্দব্রহ্ম’র উৎস এতই গভীরে প্রোথিত যে এদের বৈচিত্র্যায়নকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত লোকগান, লোকধ্যান, লোক কথা, লোক চিন্তার সৃজন ও মননের বিশাল ভাণ্ডারে, (লালন, হাছন, শাহ আব্দুল করিমের মতো বড়ো ফিগারের পাশাপাশি) এই মেধাবী শিল্পীদেরও প্রত্যেকটি জায়গায় রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। উল্লেখিত আর্টিস্টের মূলভাব কে আশ্রয় করে বাংলার আনাচে কানাচে বিভিন্ন ধারার আঞ্চলিক তথা লোকগান, লোক কথার বাজার এখনো সর্বত্র বিরাজমান।
নাগরিক অভিজাত শিক্ষিতের হাতে উল্লেখিত শিল্পী মহোদয়গণ কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান নি। এবং নিজেদের হীন-ম্মন্যতায় তাদের কবিনা বলে কবিওয়ালা/কবিয়াল দিয়ে এখনো ওয়ালা বা আল্ প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। তাদের প্রতি এমন অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য বিষয়ে যতীনসরকার এর প্রবল আত্মবিশ্বাসী আক্ষেপ ও বচনটি যথার্থ বলেই মনে হয়। তিনি বলেছেন—”আসলে শিক্ষিত নাগরিক মানুষেরা সহজে তাদের শিক্ষাভিমান ত্যাগ করতে পারে না, এক ধরনের উন্নাসিক ও উঁচু কপালে মনোবৃত্তির বৃত্তাবদ্ধ হয়ে থাকতেই তারা স্বস্তি বোধকরেন। তাদের পরিমণ্ডলের বাইরে কার মানুষদের কৃতিকে যখন স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন, তখনো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রাণপন চেষ্টা তারা করে যান”। যতীন সরকার, “বাংলা কবিতার মূলধারা ও নজরুল” গ্রন্থ’র ‘বাংলা কবিতার মূলধারা ও জালাল উদ্দীন খা’ গদ্য থেকে”]। এ বিষয়ে আরেকটি আক্ষেপ বা উদাহরণ আমি নিজেও যোগ করতে চাই। আমাদের লালনসহ অনেক বড়ো শিল্পীদের কৃতি ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বিষয়ে জানার জন্য সুদূর বাইরের দেশ থেকে অনেক ভ্রমণপিপাসু, কবি, লেখক শিক্ষার্থী বাংলাদেশে এসেছে, আসছে। তারা আমাদের হাঁটে, মাঠে ঘাটে যাচ্ছে।
কৃষক সমাজের সাথে মিশছে। লালনের মানবিক দর্শন কে বুঝার চেষ্টা করছে। তার মরমী দর্শন কে বহুমুখী দৃষ্টি-কোণ থেকে উপলব্ধি করছে, গবেষণা করছে, পিএইচডি করছে। আর আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সামান্য ডিগ্রিধারী (তথাগত শিং গজালেই) হলেই নিজেকে মাটি থেকে আলগা করে ফেলি। আগ্রাসী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাপনায়, এটাই এখন আমাদের ধর্ম। শৈশবের খেলার সাথী, ধাত্রী মা, পড়শী-স্বজন, দুধমাতা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল মানুষটিকে অবজ্ঞা করার একটা যোগ্যতা মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলি। যা মোটেই কাম্য নয়। অথচ আমরা বুঝি না প্রকৃত মানুষ হিসেবে এখানেই আমাদের বড়ো পরাজয়।
আমরা ঘরের কর্ম কাজের লোক দিয়ে করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত বিশ্বের মানুষেরা এতো অর্থবিত্তের মালিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের কাজ নিজেরা করতেই বেশি অভ্যস্ত। ফলে এই কায়িক শ্রম তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক সুস্থ রাখে।ভালো রাখে। আত্মবিশ্বাসী করে।আমাদের মতো কার্বোহাই-ড্রেট প্রধান খাবারে অভ্যস্ত বড়ো ভুঁড়িওয়ালাও তারা নয়। এ বিষয়ে সামান্য ভাবার বা উপলব্ধির ভ্রক্ষেপটুকু পর্যন্ত আমাদের নেই। আমাদের সীমাহীন দৈন্য এখানে। তেমনি বলা বলা যায়, নিজের সুন্দর ও সৌন্দর্যের চেয়ে বহিরাগত সুন্দর ও সৌন্দর্য আমাদের কাছে বড়ো। এছাড়াও ঘোর আলস্য, আরামপ্রিয়তা, পরচর্চা, পরনির্ভরতাও নিজেকে চেনার পথকে রুদ্ধ করেছে। বহিরাগত কেউ যখন আমাদের মূল্যায়ন করে, তখনই নিজের সুন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায়।তখনই পাশের ঘরের মানুষ এবং আঙিনাটি আমার কাছে ফর্সা ও সুন্দর হয়ে ওঠে। উল্লেখিত লোক শিল্পী, লোক গান, লোক কথার বেলাতেও যা সত্য।
বাউল ধারার ইমেজ এবং আবহে-যেমন নগরে এসে নগর বাউল হয়েছে। এবং অনেকেই নাগরিক মেজাজ কে ধারণ করে নিজের শেকড়, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মেলানোর চেষ্টা করছেন। যা ইতিবাচক বলা যায়। তাই বাউলিপনা শতো রঙে থাকলেও মাটিজাত সংস্কৃতির এই কাণ্ড উপড়ে ফেলা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তার ভেতরের রস ঠিকই মাটির সাথে মিশে থাকে। বাংলার লোকগান এবং লোক কথার ক্ষেত্রেও যা সত্য।
এক পল্লীকবি জসীম উদ্দীন মাঝখানে ছিলো বলেই জীবনানন্দ দাশ, আল মাহমুদ, ওমর আলীসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কবিকে আমরা আলাদা স্বরে চিহ্নিত করতে পারি। উল্লেখিত কবিগণ তাদের নিজস্বতা দিয়ে বাংলা কবিতার লোকজ ধারাকে নানা শব্দে, বাক্যে, ফর্মে ভেঙেছেন। তাদের ভাষার স্মার্টনেস ও নিজস্ব আইডেনটিটি রচনায় জসীম উদ্দীনকে বড়ো সহায়ক শক্তি হিসেবে পাওয়া যায়।