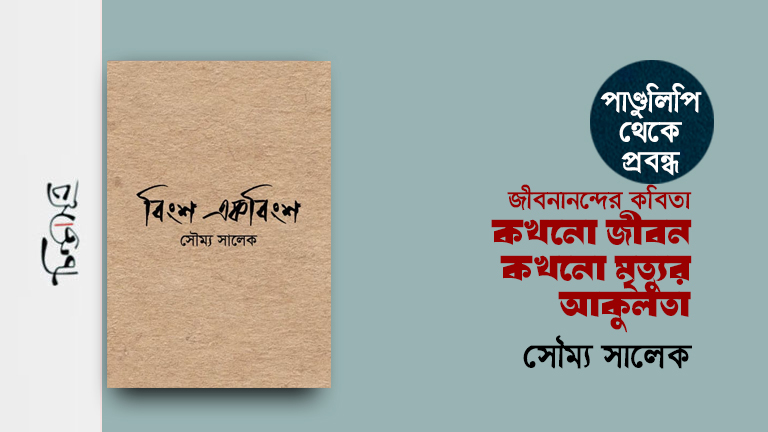জীবন-মৃত্যুর উত্তেজনা এবং আশঙ্কার সমষ্টি মানবজীবন। জীবন সৃষ্টি ও সম্ভাবনার দিকে অগ্রগামী হলেও তার পরতে পরতে রয়েছে মৃত্যুর অশনি সংকেত। মৃত্যুর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আগুয়ান হলেও জীবন সর্বদাই উচ্ছলতা ও উন্মাদনার আশ্রয়ে মানুষকে তার স্বপ্নের পথে এগুতে প্ররোচিত করে। এই প্ররোচনা কেবল তাদের জন্যই শুভ কিছু বয়ে আনে না, যারা জীবনের সংগ্রামশীলতা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে কিংবা বিপন্নতা ও অবক্ষয় যাদের হৃদয়ে গভীরভাবে আসন নিয়েছে। সামাজিক পরিপার্শ্বগত সংকটই কেবল কাউকে জীবন বিমুখ করে না, তার অন্তরীণ—‘বিপন্ন বিস্ময়’—বোধও নতুন নতুন সংকটের ঘূর্ণাবর্তে জীবনের সার সম্পর্কে নানাবিধ চৈতন্যে তার সক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করে এবং সে সমুলে বিষণ্নতায় মুসড়ে পড়ে। অবশ্য এই সংকট অত্যন্ত বিরল এবং কেবল ভাবনাশীল হৃদয় এর অন্যতম শিকার!
জীবনানন্দ দাশ এই অন্তরীণ চেতনাজাত বিপন্নতার বিশ্লেষক এবং তার যাপিত জীবনও যে সেই সংকটে মজ্জমান ছিল তা বোধ করতে আমাদের খুব বেশি ঘামতে হয় না। হৃদয় খুড়ে খুড়ে এই প্রত্ন-প্রাচীন চৈতন্যকে আমাদের সামনে সবচেয়ে বাস্তব করে তুলেছেন জীবনানন্দ, এর আগে যে কেউ আত্মপীড়নের এসব একান্ত সংক্রমনকে দৃশ্যমান কারেন নি তা নয় কিন্তু সেসব ছিল বিক্ষিপ্ত ও গীতভাষ্যের অন্তরালে আবৃত। জীবনানন্দের নতুন বাক্বিন্যাসে, শব্দের অভিনব প্রয়োগে, আধুনিক মনস্বী-হৃদয়ের এই সংকট হয়েছে মূর্তমান, যা তার চিন্তা ও ভাষ্যকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য।
জীবনানন্দের অসংখ্য কবিতার মধ্যে বিচিত্র বীক্ষায় জীবন-মৃত্যুর উন্মুলতা, সমস্বর ও সহাবস্থান নানা রেখায় উপস্থাপিত হয়েছে। এই রচনায় আমাদের উদ্দিষ্ট পটভুমি তাঁর ‘জীবন’ শিরোনামের কবিতাগুচ্ছ, যা ধূসর পাণ্ডুলিপি—কাব্যে পত্রস্থ।
মৃত্যু ও মৃতের বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তাশীলদের রয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অভিমত। বস্তুগত অবস্থানের বিলোপ ব্যতীত মানুষ যেমন কিছু বোধ করতে পারে না, সেই অবস্থার বিষয়ে দর্শনেরও স্পষ্ট কোনও অভিন্ন ভাষ্য নেই। এটি দর্শনের স্থায়ী সমস্যার একটি। প্রাচীন দর্শনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব সক্রেটিসের বক্তব্য হচ্ছে : ‘হয় মৃত্যু একটি স্বপ্নহীন চিরস্থায়ী ঘুম, নয় নতুন আরেকটি জীবনের সূচনা।’ মৃত্যু মানুষের সমুহ বিনাশ করতে পারে না; বিশেষত তার মানবিক প্রতিষ্ঠা, চিন্তা এবং উপহারকে, যা লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে সংরক্ষণ করে থাকে। একটি মানুষ যে পথে কখনও গমন করেনি, এমন পথে গিয়েও সে বোধ করে, কবে যেন সে একেবার এ পথে চলেছিল অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম চৈতন্যে সে তার পূর্বপুরুষের স্মৃতিকে বহন করে চলেছে যা তার এই অচেনা পথ-ভ্রমণের বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, তার সামনে আবছায়া-ধোঁয়াশা তৈরি করছে! জীবন কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতার মধ্যেই এমন অভীক্ষার মুখোমুখী হয়ে আমাদের ভাবনা এক অবাক প্রশ্নবোধে চমকে উঠবে।
‘সে কোন প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে!
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ-
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে!
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে—তার সাথে সেও আছে জেগে!’
উদ্দিষ্ট কবিতাগুচ্ছে আমরা একই সমবায়ে জীবন ও মৃত্যুর সমুত্থানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। জীবনের অনাকাক্সিক্ষত সমাপ্তিও যে মানুষকে তার পথচলা থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং জীবনের সম্ভাবনা যে মৃত্যুর চেয়ে প্রবল তা প্রত্যক্ষ করি কবির প্রাণবন্ত উচ্চারণে। স্বপ্ন ও কামনার শক্তি যেখানে বীর্যবান সেখানে ফলন আসবেই :
‘নতুন বীজের গন্ধ ভরে দেয় আমাদের মন
এই শক্তি-একদিন হয়তোবা ফলিবে ফসল!
এরই জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভরে অলক্ষিত আকাশের তল!
দুরন্ত চিতার মতো গতি তার—বিদ্যুতের মতো সে চঞ্চল!’
‘রবার্ট ফ্রস্টকে দেখতে যাওয়া’-শীর্ষক অক্তাবিত্ত পাস-এর রচনায় ফ্রস্টের একটি ভাষ্য ছিল এমন : ‘আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে থাকে জীবনকে হারাবার সম্ভাবনা। প্রতিটি মুহূর্ত বয়ে চলে মুত্যুর ঝুঁকি। প্রত্যেক তূর্ণকাল বিকল্পের আধার।’ জীবনের প্রতি মুহূর্তে বিকল্প কিংবা বৈচিত্র্যের পাশাপাশি রয়েছে মৃত্যুর অনিশ্চিত হাতছানি। তবু দেহ অবশ হবার আগ পর্যন্তও মানুষ জীবনের প্রতি উন্মুখ, জীবনের দিকেই প্রাণ ফেলে :
‘মুখে রক্ত ওঠে-তবু কমে কই বুকের সাহস!
যেতে হবে—কে এসে চুলের ঝুঁটি টেনে লয় জোরে!
শরীরের আগে কবে ঝরে যায় হৃদয়ের রস!
তবু চলে—মৃত্যুর ঠোঁটের মতো দেহ যার হয় নি অবশ!’
দুই.
আমরা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিন্তা, ভাষ্য বা বক্তব্যকে চিত্ররূপে খুঁজে পাই। এত বিপুল বৈচিত্রময় চিত্রকল্প বাংলা কবিতায় আর কারো মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে প্রথম দিকেই ‘চিত্ররূপময়’ বললেও আমরা আশ্চার্য হয়ে দেখি তার সার্বিক কবিতার দৃশ্যপটেই এই চিত্ররূপময়তার বিপুল সমাহার। এত দৃশ্যকল্প তিনি কোথায় পেয়েছেন ? এমন প্রশ্ন হতে পারে। আসলে মানুষের জীবন এবং তার পরিপার্শ্বের মধ্যেই এর নিবিড় অবস্থিতি, কবি তার নিরীক্ষণে-উৎখননে সেসব শিল্পবস্তুকে উদ্ভাবন করেন, উপস্থাপন করেন। জনৈক ফরাসি লেখক বলেছেন, ‘রূপকল্পকে খুঁজে পেতে হয় না, তারা দৃশ্যমানই থাকে।’ জীবন কবিতাগুচ্ছে এমন কতক দুর্দান্ত দৃশ্যকল্প বিরচিত, এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় দুটো কাব্য-দৃশ্য উপস্থাপন করছি।
ক.
যেখানে আসে নি চাষা কোনদিন কাস্তে হাতে লয়ে
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে
নিরাশার মতো ফেঁপে চোখ বুজে পলাতক হয়ে
প্রেমের মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছি শেষে!
খ.
বনের পাতার মতো কুয়াশায় হলুদ না হতে
হেমন্ত আসার আগে হিম হয়ে পড়ে গেছি ঝরে!
মৃত্যু ও বিষণ্নতা প্রকাশে কবি এই কবিতাগুচ্ছেও ব্যবহার কারেছেন তার পরিচিত প্রিয় শব্দাবলি, যার স্বত:স্ফূর্ত প্রয়োগ কবিতার নিহিতার্থকে সহজ করে তুলেছে। নক্ষত্র, ধূপ, হাড়, শাদা হাত, হিম, হেমন্ত, ভূত, গুহা, গহ্বর, আকাক্সক্ষা কিংবা আস্বাদ এসব শব্দগুচ্ছের অবস্থান কিংবা শব্দভাষ্য যে দিকে ধাবমান কেবল সেই মৃত্যুময়তা বা নাস্তিবোধই এককভাবে এই কবিতাগুচ্ছের অন্তরগত সুর নয় বরং এর বিপরীতে জীবনের প্রতি চিরায়ত আকর্ষণই কিছু কবিতায় মুখ্য মনে হয়েছে। পৃথিবীতে মৃত্যু, হতাশা ও বিষণ্নতার বিপরীতে রয়েছে আশা-আকাক্সক্ষা ও সম্ভাবনার সহাবস্থান আর ভালো-মন্দের এই সমন্বয়-সুষমাই কবিকে বারবার পৃথিবীর পথে ডেকেছে।
‘পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা-হতাশা
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন!
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন!’
মৃত্যুর বিষয়ে মানুষের ভীতির শেষ না থাকলেও জীবনের ‘দশদিক-সম্ভাবনা’ আর ‘মৃত্যুর অনিশ্চয়তা’ এ দুয়ের অবস্থান ও বস্তুগত বিশ্লেষণ মানুষকে অনেকবেশি জীবনমুখী করে। জীবনের দশদিকব্যাপী বিচ্ছিন্নতা কিংবা অন্ধকারের মাঝেও মৃত্যুযাত্রী পথিক শেষবার অন্তরের আগুন জ্বালিয়েও কিছুটা চলতে চায়, গন্তব্যে পৌঁছাতে চায়। জীবনের প্রতি মানুষের এই আগ্রাসী পক্ষপাতকে আমরা ’জীবন’-কবিতাগুচ্ছের দ্বাদশ কবিতায় এভাবে দেখতে পাই :
‘শীত রাত বাড়ে আরো নক্ষত্রেরা যেতেছে হারায়ে—
ছাইয়ে যে আগুন ছিল সেই সবও হয়ে যায় ছাই!
তবুও আরেকবার সব ভস্মে অন্তরের আগুন ধরাই।’
মানুষের সবশেষ অবলম্বন তার অন্তরের স্পৃহা বা প্রাণশক্তি, সেটিকে অল্পকতক লোক ব্যতীত সকলে জীবনের জন্য কিংবা জীবনের স্বার্থে প্রয়োগ করে থাকে।
তিন.
প্রত্যেক কবিই তার নিজের মতো করে বলতে চান, সেটি অবশ্য তার কর্তব্যও কিন্তু প্রত্যেক কবির লেখা নিজস্বতা অর্জন করতে পারে না। যারা আগে জন্মেছেন তাদের থেকে নতুন কাব্যশৈলিতে নতুন প্রকারণে নতুন অলংকারে সবাই পঙ্ক্তি সাজাতে পারেন না। যারা পারেন তারাই সংশ্লিষ্ট কালের প্রতিভূরূপে আদৃত হয়ে থাকেন। জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যের এমনই এক অগ্রগণ্য কবিপ্রতিভা যিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের থেকে নিজেকে সযত্নে স্বাতন্ত্র্য দিতে পেয়েছেন এবং পরবর্তী সময়কালও তাঁর লিখনশৈলী দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এই স্বাতন্ত্র্য তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ- ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’তে এসে, পরবর্তী সব কবিতাও সেই নিজস্বতার পথে দারুণভাবে সচল থেকেছে। তাঁর এই নিজস্বতা যেমন কবিতার বাক্য-রচনার দিক থেকে তেমনি চিন্তার দিক থেকেও। নৈরাশ্য, নিসর্গবোধ, বিচ্ছিন্নতা, প্রকৃতিপ্রেম, স্তব্ধতা, আচ্ছন্নতা ও পরিভ্রমণশীলতা তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে থাকলেও এসব উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রবল ও প্রাণবন্তভাবে উঠে এসেছে জীবনানন্দের কবিতায়।
শিল্পী ভ্যান গখের চিত্রে হলুদ রঙের যে স্বপ্নময়তা, তাতে নিসর্গরচনার যে অনুপম পরিক্ষেত্র সৃজিত হয়েছে; জীবনানন্দের কবিতায় ‘হলুদ’ প্রায়শই সেই একই মর্মে স্বর তোলেনি, তাঁর কবিতায় ‘হলুদ’ এসেছে মৃত্যু ও ক্ষয়ে যাবার বর্ণ-অনুষঙ্গরূপে:
‘যে পাতা সবুজ ছিল তবুও হলুদ হতে হয়
শীতের হাড়ের হাত আজও তারে যায় নাই ছুঁয়ে—
যে মুখ যুবার ছিল, তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়—
হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায়—পড়ে যায় নুয়ে’
যারা অনেক বেশি আত্মমুখী—ব্যর্থতা, ক্লেদ, জরা ও মৃত্যুর অপছায়া তাদের জীবনকেই দ্রুত গ্রাস করে, হতাশার আগ্রাসন দ্রুত তাদের মুষড়ে ফেলে, তখন তারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা ছাড়া ভিন্ন দিশা খুঁজে পায় না। এরা তারাই যারা সমুদ্র, পাহাড় ও নিসর্গ-সুন্দরকে দেখা থেকে অকারণে নিজেদের হৃদয়কে বঞ্চিত রেখেছে, তারা যদি সৃষ্টির বিপুল তরঙ্গকে অবলোকন করতো তাহলে এত দ্রুত তাদের প্রাণশক্তি ফুরাতো না। কবির বর্ণনা এই সত্যের দিকই যেন আমাদের আহ্বান করে :
‘বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁঁচড়ায়-করে প্রাণপণ—
এই নক্ষত্রের তলে একবার তারা যদি আসে—
রাত্রিরে দেখিয়া যায় একবার সমুদ্রের পারের আকাশে!’
মানব হৃদয়ে আকাক্সক্ষার শেষ নেই। একটি প্রাপ্তি তার হৃদয়কে নতুন কোন চাওয়ার প্রতি আকাক্সক্ষী করে তোলে। দেখা যায় সব সাধারণ চাওয়া পূরণের পর মানুষ কখনও কখনও অদ্ভূত কাণ্ড করে বসে, যাকে বিকৃতিও বলা চলে, এসব আসলে অত্যধিক চাওয়ার ফল। অপরিমিত চাওয়া এবং একে একে সব পূর্ণতার পরও মানুষ অদ্ভূত কারণে বিপন্নতা বোধ করতে পারে, এই নাস্তিবোধের আসলে পরিত্রাণ নেই। এমন অদ্ভূত উত্তুঙ্গতার মাঝে পৃথিবীতে অনেক আগ্রাসী স্বপ্নচারীকে আত্মঘাতী হতে দেখা গেছে। আকাক্সক্ষার, ভালোবাসার যে কোনও সীমা-পরিসীমা নেই এবং এটি যে বস্তু-নিরপেক্ষ এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অনেক রয়েছে। সব ভালোবাসার অনুভূতি যার হৃদয়গত সে তো মুত্যুকেও দ্রুত কাছে পেতে চাইবে যদিও মৃত্যুর অনুভূতি ব্যাখ্যাতীত কেননা ভোগকারী তার অনুভূতি জানাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এখানে আমরা সপ্তদশ নম্বর কবিতাটির শেষাংশ পাঠ করতে চাই:
‘জেগে জেগে যা জেনেছ—জেনেছ তা—জেগে জেনেছ তা—
নতুন জানিবে কিছু হয়তোবা ঘুমের চোখে সে!
সব ভালোবাসা যার বোঝা হল—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে!’
মৃত্যুর মাধ্যমে ব্যক্তি তার অবস্থান হারায় পৃথিবী থেকে। প্রিয় যারা তার পরিপার্শ্বে ভালোবাসার আঁচল বিছিয়েছিল এতোদিন; তার আকাক্সক্ষা রয়ে যায় যেন তারা সেসব স্মৃতিকে ধরে রাখে, যা ছিল মধুময় যদিও তা আজ হাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে পলকা ধূয়ার আবরণে। মানুষের কামনা, যেখানে সে সুস্থির আশ্রয় মনে করে তা যেন জীবনে থাকে, মরণের পরেও রয়। মানুষের এই গোপন আর্তিই ধ্বনিত হয়েছে এই কবিতায় :
‘যে-ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক
যে ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমানো গন্ধের মতো স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিও, প্রিয়া!’
জীবনে জরা আছে, বিষাদ ও বিমূর্ত অন্ধকার আছে এবং সবশেষে মৃত্যু আছে তবু মানুষের সবকিছু হতাশার কাছে পরাভূত নয়; মুক্তি আছে, আনন্দ আছে, মিলন ও স্ফূর্তি আছে পৃথিবীতে, যা মানুষের প্রতিদিনের পালে প্রেরণার হাওয়া দিয়ে যায়। শীতের নদীতে ভাসা মৃত-জোনাকির মত চরম ব্যাহত-বিধ্বস্ত নয় সবকিছু। ত্রিশতম কবিতার কয়েক ছত্র তুলে ধরছি :
‘যেমন নিস্তব্ধ শান্ত নিমীলিত শূন্য মনে হয়—
তেমন আস্বাদ এক কিংবা সেই স্বাদহীনতার
সাথে একবার হবে মুখোমুখি সব পরিচয়!
শীতের নদীর বুকের মৃত জোনাকির মুখ তবু সব নয়!’
মানুষের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব বড় আপেক্ষিক এবং অমীমাংসিত। তাই কবি প্রশ্ন রাখেন—
‘মানুষ চেয়েছে কিবা? পেয়েছে কি ?—কিছু পেয়েছে কি!
হয়ত পায় নি কিছু—যা পেয়েছে, তাও গেছে খসে
অবহেলা করে করে কিংবা তার নক্ষত্রের দোষে—’
সবশেষে মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়, সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং তার জীবনের হিসেব-নিকাশ অসহায়ভাবে অনিষ্পন্ন থেকে যায়। এখানে কবির উচ্চারণ এমন :
‘শরীর ছিঁড়িয়া গেছে—হৃদয় পড়িয়া গেছে ধসে!
অন্ধকার কথা কয়- আকাশের তারা কথা কয়
তারপর, সব গতি থেমে যায়—মুছে যায় শক্তির-বিস্ময়!’
বিশতম কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশ এক অবাক লোকের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন, যার কাছে কেউ আসে নি, যাকে কেউ চেনে নি কিংবা যাকে নিয়ে কেই মেতে উঠেনি কখনও। এটা আসলে অভূতসম্ভব কেননা কবি কোন বিজন প্রান্তে অবস্থানকারী কারও তথ্য এখানে উত্থাপন করেন নি। এটি ব্যক্তির একান্ত মুহূর্তের নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি। তার প্রকৃত পরিচয় কেউ যাচে নি কিংবা নিজেই সে তাকে ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম হয়েছে বারবার। কবিতাটির প্রথমাংশ তুলে ধরছি, পাঠে বাকীটা পাঠকের অনুধাবনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।
‘কিংবা কেউ কোনদিন দেখে নাই—চেনে নি আমারে!
সকালবেলার আলো ছিল যার সন্ধ্যার মতন
চকিত ভূতের মতো নদী আর পাহাড়ের ধারে
ইশারায় ভূত ডেকে জীবনের সব আয়োজন
আরম্ভ সে করেছিল! কোনদিন কোনো লোকজন
তার কাছে আসে নাই—আকাক্সক্ষার কবরের পরে
পুবের হাওয়ার মতো এসেছে সে হঠাৎ কখন!’
সংগ্রামশীলতার মুখর পাটভূমিতেও মানুষ তার বাস্তবতাকে ছেড়ে অনেকসময় স্বপ্নের দিকে ধেয়ে চলে; সে বিচ্যুত হয়, ব্যথিত হয়, আক্রান্ত হয় কিন্তু তবু সে সার্বিকভাবে সরে আসে না। ‘যাতবার মন ছিঁড়ে গেছে, হয়েছে দেহের মতো হৃদয় আহত’—তবু সে পরম কামনা নিয়ে টিকে থাকে জীবনের মাঠে। প্রত্যাশার প্রদীপ ও সময়ের অপঘাতের দ্বি-বিধ এই চক্রেপথে সে ছুটে চলে জীবন-মৃত্যুর দ্বৈরথে। এই দ্বৈরথ, সচল ও সমাজবদ্ধ মানুষের চরম বাস্তবতা। কেউ দেখুক বা না-দেখুক মানবমঞ্চের কুশিলবদের এই ক্রীড়া কবি প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর একান্ত পরিজ্ঞানে:
‘একবার মৃত্যু লয়ে—একবার জীবনেরে লয়ে
ঘূর্ণির মতন বয়ে যে বাতাস ছেঁড়ে—তার মতো গেছি বয়ে!’
ছিঁড়ে-ফুঁড়ে, বেদনায়, অস্থিরতায়, উন্মুলতায় জীবনের গতি চলে অনিবার আকাক্সক্ষার অভিমুখে, তারসাথে মৃত্যু চলে চক্রছায়া ফেলে। জীবনজুড়ে মৃত্যুর অপছায়া থাকলেও এটি ব্যক্তিকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না বরং তার বিমর্ষতা এবং বিপন্ন-বোধই মৃত্যুর মতো এসে তাকে গ্রাস করে এবং প্রকৃত মৃত্যুর পথে তাকে এগিয়ে দেয়। আকাক্সক্ষা পূরণের জন্য কেউ জীবনের দিকে ছুটে আবার কেউ অভিনব বস্তু-নিচয়ের অন্বেষায় মৃত্যুমুখী হয়; জীবন ও মৃত্যুর এই সম্ভাবনাই কবি জীবনানন্দ দাশ দারুণ কাব্যকীর্তিতে তাঁর ‘জীবন’- কবিতাগুচ্ছে প্রাণবন্ত ভাষা দিয়েছেন।
গ্রন্থনির্দেশ:
১. কবিতাসমগ্র/ জীবনানন্দ দাশ
২. বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ/ সম্পাদনা: মোজাফফর হোসেন
৩. সক্রেটিস-এর শেষ দিনগুলি/ প্লেটো, অনুবাদ মোস্তফা মীর