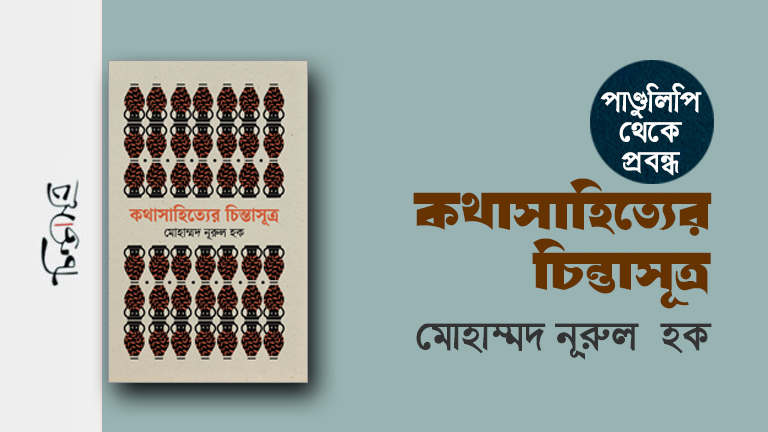কথাসাহিত্যিকের মনের ভাব প্রকাশের জন্য থাকে প্রধানত দুটি দিক। একটি তাঁর কল্পনাশক্তি, অন্যটি অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা। উভয়দিকের সম্মিলনেই তিনি সৃষ্টি করেন কথাসাহিত্য। কথাশিল্পীকে কেবল কাহিনির পর কাহিনি সাজালেই চলে না, সেই আখ্যানকে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য চরিত্র ও পরিবেশ তৈরি করতে হয়। মূলত চরিত্রগুলোর আন্তঃসম্পর্ক ও তাদের কার্যকারণ সম্পর্কের ওপরই নির্ভর করে কাহিনির পরিণতি। চরিত্রশূন্য কাহিনি যেমন অসম্ভব, তেমনি কাহিনি-বিযুক্ত চরিত্রও স্থবির পর্বতের মতো নিশ্চল-মূর্তি। চরিত্রের অভাবে কাহিনি জন-প্রাণহীন উত্তপ্ত বালুকাবিস্তীর্ণ মরুভূমি মাত্র। কিন্তু অনেকানেক চরিত্রের ভিড় ও কাহিনির ঘনঘটাও কোনো আখ্যানকে সার্থকউপন্যাস বা ছোটগল্পে রূপ দিতে পারে না।
কাহিনি-চরিত্রের পাশাপাশি সংলাপ-পরিবেশ-সময়চেতনা ও লেখকের স্বকীয় ভাষাশৈলীও সার্থক উপন্যাস-ছোটগল্পের অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে। এরপরও কোনো কাহিনি সার্থক-বিশ্বস্ত উপন্যাস বা ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারে না। এজন্য দরকার হয়, লেখকের সতর্ক ও সচেতন জীবনদর্শন।
গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে কথক কখনো কখনো স্বয়ং, কখনো কখনো কোনো চরিত্রের ভেতর দিয়ে জীবনদর্শন প্রকাশ করেন। এজন্য কখনো কখনো চরিত্রের ক্রিয়াপ্রণালির ভেতর দিয়ে, কখনো কখনো ঘটনাপ্রবাহের অন্তসলিলে নিজের জীবনদৃষ্টি তুলে ধরেন। লেখকের সমগ্র জীবনবোধ, সংসারকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, স্বকীয় স্বপ্নের সতর্ক বাস্তবায়ন প্রচেষ্টাভিন্ন কোনো আখ্যান সার্থক উপন্যাস বা ছোটগল্পে রূপ নিতে পারে না। অর্থাৎ কথাশিল্পী যে উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প সৃষ্টি করেন, সেখানে থাকে তার মৌলিক কল্পনা ও চিন্তাসূত্র। তার চিন্তার সূত্রটি একইসঙ্গে সুদৃঢ় ও সূক্ষè হতে হয়। কল্পনা-চিন্তাসূত্র তৈরিতে তাঁকে মহাভারতের অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজ হতে হয়। তাঁর চিন্তার রেখা একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্রকে অঙ্কিত হবে। সেই রেখা কখনো ধীরে ধীরে বৃত্ত তৈরিতে সমাপ্তি টানবে, কখনো এঁকে-বেঁকে চলে যাবে বহুদূর পর্যন্ত সমান্তরাল রেললাইনের মতোই। সেই সমান্তরাল রেখা যেখানে থামবে, সেখানেই উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে যেমন লেখকের পূর্বপ্রস্তুতিময় একটি গতি থাকবে, ছোটগল্পে তেমনটি না-ও থাকতে পারে। ছোটগল্পের শুরু যেমন আকস্মিক হতে পারে, তেমনি সমাপ্তিতেও আকস্মিকতা বিদ্যমান থাকতে পারে। বিপরীতে উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনে যেমন বিশেষ আয়োজন-প্রস্তুতির প্রয়োজন, তেমনি সমাপ্তিতেও পরিপূর্ণ তৃপ্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখন পর্যন্ত এই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত সমস্ত উপন্যাসের শুরু ও সমাপ্তি মোটামুটি এমনই। ব্যতিক্রম এখনো দেখা যায়নি। দূর ভবিষ্যতে উপন্যাসের কাঠামোগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠলে, তখন শুরু ও সমাপ্তিতেও নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটবে।
উপন্যাসের কাহিনি নির্মান, ঘটনা বর্ণন, চরিত্র সৃষ্টি ও সংলাপ রচনায় লেখককে বিশেষ কল্পনা-চিন্তার আশ্রয় নিতে হয়। উপন্যাসকে তার পূর্ববর্তী প্রকরণ কাব্য-মহাকাব্য-নাটক-উপাখ্যান থেকে স্বতন্ত্র চরিত্র নিয়েই উপস্থিত হতে হয়। এর পেছনে সুস্পষ্ট কারণও রয়েছে এই প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর উপন্যাসের শিল্পরূপ গ্রন্থের ‘তিনটি উপাদান’ অধ্যায়ে বলেছেন,
উপন্যাস তখনই শিল্পকলাগতভাবে মধ্যযুগীয় উপাখ্যান ও কিংবদন্তী কিংবা নাটক অথবা মহাকাব্য থেকে একটা পৃথক সত্তা নিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বেরি এল, যখন এর তিনটি উপাদান অজস্র ভাষিতার মাধ্যমে একটি চিরায়তিক শিল্পরূপ গড়ার আয়োজন সম্পন্ন করলো। এই তিনটি উপাদানের একটি বিস্তৃত বাস্তব; দ্বিতীয়টি মানব-মানবীর দ্বিতীয়জন অথবা বহুজন সম্পর্ক-সম্পন্ন সুদূর প্রসারী ব্যক্তিকতা; তৃতীয়টি লোকগদ্যের ভাণ্ডার থেকে মানব-মানবীর অভিব্যক্তির যাবতীয় ভাষা বের করে আনা।১
এখন প্রশ্ন হলো—বিস্তৃত বাস্তব কী? কিভাবে বাস্তবকে বিস্তৃত করে তুলতে হয়? এই প্রশ্নের সরল উত্তর খোঁজার চেয়ে উপন্যাস লেখকের প্রজ্ঞা ও চিন্তাসূত্রের অনুসন্ধানের ওপর জোর দেওয়া উচিত। কারণ যা বাস্তব, তা সংকীর্ণ ও বিস্তৃত; এই ভাবে ভাগ হতে পারে না। তবে, পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বাস্তবের স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে। একপক্ষের কাছে যা বাস্তব, আরেক পক্ষের কাছে তা-ই হয়ে উঠতে পারে অলীক। এই বাস্তবতা ও অলীক দর্শনের ঘটনা নির্ভর করে লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা, তাঁর পরিবেশগত ধারণা, প্রজ্ঞা, কল্পনা ও চিন্তাসূত্রের ওপর। অর্থাৎ জড়বাদী ও যুক্তিবাদীর কাছে যা বাস্তব, ভাববাদীর কাছে তা কল্পনারও অতীত হতে পারে। আবার ভাববাদীর বিশ্বাসের অলিন্দে যা স্বর্গীয় শোভা, বস্তুবাদীর কষ্টিপাথরের ঘর্ষণে তা-ই অন্তসারশূন্য। এভাবে দেখলে বিষয়টি দর্শন-ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রকাশ করে। উপন্যাসিকের কাজ এই দ্বন্দ্ব থেকে তাঁর নিজস্ব বাস্তব আবিষ্কার করা; আর সেই বাস্তবকেই বিস্তৃত করে তোলা।
মানব-মানবীর সুদূর প্রসারী ‘ব্যক্তিকতা’র চিত্রায়ণের মাধ্যমেই ঔপন্যাসিকের রুচি ও মর্জির স্বরূপ প্রকাশিত হয়। একইসঙ্গে ‘লোকগদ্যের ভাণ্ডার থেকে মানব-মানবীর অভিব্যক্তির যাবতীয় ভাষা’ বের করে আনাও কথাশিল্পীর কর্তব্য। অর্থাৎ ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তির অভিব্যক্তির ভাষা আবিষ্কার ঔপন্যাসিকের অন্যতম দায়। এই তিন কর্মসিদ্ধিতে যে উপন্যাসিক যতটা নৈপুণ্য দেখাতে পারেন, তিনি ততটাই ভাষাভিত্তিক জীবনশিল্পী হিসেবে সার্থক হতে পারে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বিষবৃক্ষ(১৮৭৩) মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)-এর বিষাদ-সিন্ধু (১৮৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর চোখের বালি (১৯০৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)-এর পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৫), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)-এর ক্রীতদাসের হাসি(১৯৬২) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)-এর লালসালু (১৯৪৮), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)-এর তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)-এর প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)-এর খোয়াবনামা (১৯৯৬)। এসব উপন্যাসে লেখকেরা তাদের চিন্তা-কল্পনা-অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রজ্ঞার ছাপ রেখেছেন। লেখকের জীবনদর্শনের কথা বলার আগে উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয়-আশয় কী হতে পারে—তার নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে এ-ও বলে নেওয়া ভালো—ছোটগল্পের সাক্ষাৎপূর্ববর্তী কথাসাহিত্য হলো উপন্যাস। ফলে উপন্যাস ও ছোটগল্পের কথাসূত্র একসঙ্গেই আলোচনার দাবি রাখে। এই নিবন্ধে সেই প্রচেষ্টাই থাকবে।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আদিপুরুষ। মূলত তাঁর হাতেই আধুনিক ও সফল উপন্যাসের সৃষ্টি। একথা স্বীকৃতি যে, ‘‘বিষবৃক্ষ’ বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম শিল্পসম্মত মনস্তত্ত্বমূলক ‘নভেল’।”২
বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কল্পনা ও চিন্তাসূত্রের সূক্ষèতম প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর চিন্তার সুতোকে সূঁচের ছিদ্রে প্রবেশ করাননি। বরং সূচাগ্রে রেখেই কাঁথা বুননের মতো উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টি করেছেন নগেন্দ্র, কুন্দ নন্দিনী, রোহিণী ও গোবিন্দলালের মতো চরিত্রগুলো। কাহিনির বিস্তৃত বাস্তবার দিকে যাওয়া এই নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য লেখকের চিন্তাসূত্র কিভাবে উপন্যাসের কাহিনিবিন্যাস, চরিত্রনির্মাণ, পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ রচনা ও কাহিনির পরিণতিতে তাঁর ভূমিকা কী থাকে। এই উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে চিন্তাসূত্র কাজ করেছে, তা মোটেও সরল কিংবা একরৈখিক ছিল না। তাঁর চিন্তাসূত্র ছিল শতভাগ বঙ্কিম—শতভাগ জটিল। এই উপন্যাসে তিনি বিধবাবিবাহের কুফল দেখাতে চেয়েছেন। বিধবাবিবাহের মধ্যে তিনি পুণ্য সমাজ ও মানবজাতির জন্য কোনো মঙ্গলসূত্র আবিষ্কার করেননি। বরং বিধবাবিবাহের মধ্যে বঙ্কিম দেখেছেন পাপ। এই পাপের পরিণতি হিসেবে দেখিয়েছেন সংসারে অশান্তি। আর শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন মৃত্যুদণ্ড। অর্থাৎ তিনি দেখিয়েছেন ‘বিধবাবিবাহ পাপ’ আর এই পাপের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। একই পরিণতি তিনি দেখিয়েছেন কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের রোহিনীর ক্ষেত্রেও। বঙ্কিম ইচ্ছা করেই কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীকে কোনো কুমার পুরুষ কিংবা বিপত্নিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেন না, বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই সতীনের সংসারে পাঠান। এর মাধ্যমে তিনি বিধবার পুনঃবিবাহের ভেতর দেখান তাদের লোভী ও চরিত্রহীনা হিসেবে দেখানোর হীন চেষ্টা করেন।
বঙ্কিমচিন্তার সূত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, তিনি যতটা কথাশিল্পী তারও বেশি লোকশিক্ষক-ধর্মপ্রচারক। তাঁর আদর্শ এতই সনাতনপন্থী যে, ধর্মের বাণী শোনানো ও নৈতিকশিক্ষা দানই মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নিজের কথা প্রবন্ধে বলেননি। ধর্মীয় রীতি-নৈতিকতা শেখানোর জন্য ‘ঈশপের গল্প’ ও ‘পঞ্চতন্ত্রের মন্ত্রের’ মতো গল্পের ছলে হিতোপদেশ দিতে চেয়ছেন। এজন্য তিনি উপন্যাসকেই উত্তম মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন। সে অনুযায়ী নিজের বক্তব্য, ধর্মীয়নৈতিক আচারনিষ্ঠার শিক্ষা সমাজনকে তিনি দিতে চেয়েছেন। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি রস অপেক্ষা নীতি, হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা পাপ-পুণ্যকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছৈন। তাই তিনি মানবশিল্পী হতে পারেননি, হয়েছে ধর্মপ্রচারক-নীতিবাদী।৩
একই পরিণতির দেখা মেলে তাঁর উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালি ও চতুরঙ্গ উপন্যাসের বিধবা চরিত্রের জীবনেও। এই দুই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাসূত্র বঙ্কিম রূপ নিয়ে বঙ্কিমের চিন্তার সমুদ্রে গিয়ে লীন হয়েছে। ফলে চোখের বালির বিনোদিনীকে পুনঃবিবাহের স্বপ্ন দেখার অপরাধে তীর্থে চলে যেতে হয়। আর চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনীকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। তবে বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শগত মিল থাকলেও কৌশলগত পার্থক্য রয়েছে।
বঙ্কিম যেভাবে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেভাবে নেননি। কিন্তু বিধবা বিবাহকে রবীন্দ্রনাথও ভালো চোখে দেখেছেন তেমন প্রমাণ দেননি। চোখের বালিতে বিনোদিনীকে রূপ দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, রুচি দিয়েছেন। তার বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সে বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী করেননি। অকালে তাকে বিধা বানিয়েছেন। সেই বিধবার মনে প্রেম দিয়েছেন, ঈর্ষা দিয়েছেন। সেই ঈর্ষার আগুনে আশালতা-মহেন্দ্রের জীবনে ঝড় তুলেছেন। […] বিহারী যখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সে তখন তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সংসারের সাধ জাগার পরও স্বপ্ন পূরণ হলো না।৪
বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কাহিনি বর্ণনা, পটভূমি রচনা, চরিত্র সৃষ্টির অন্তর্গত মাহাত্ম্য অভিন্ন। তাঁরা বিধবাবিবাহ প্রশ্নে উভয়েই একই পথের প্রবক্তা ও অনুসারী। ধর্মীয়, সামাজিক শৃঙ্খলার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা মানব জীবনের কামনা-বাসনাকে স্বীকৃতি দিতে অনীহ। উভয়ের চিন্তাসূত্রই এখানে অভিন্ন রেখায় গ্রন্থিত, অভিন্ন গতিপথে প্রবাহিত।
আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলা উপন্যাসের একজন স্বতন্ত্র কুশীলব। তাঁর তেইশ নম্বর তৈলচিত্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই উপন্যাসেরপ্রধান অনুষঙ্গ শিল্পীর জীবন-যাপন, চিন্তা ও কল্পনাবিশ্ব। এতে লেখক দেখিয়েছেন, মানুষ নিজেকে শিল্পের স্রষ্টা হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। সঙ্গে নিজে হয়ে ওটে সমঝদার। আরও একটি বিষয় এই উপন্যাসে পরিষ্কার করেছেন লেখক, সেটি হলো—মানুষই মানুষকে শাসন করে, শোষণ করে, অত্যাচার করে। যুগের পর যুগ মানুষই মানুষকে দাস-ক্রীতদাস বানিয়ে রাখে। বাইরে থেকে কোনো শক্তি এসে তাকে শাসন করে না, শোষণও না। এমনকী কোনো প্রাণী কিংবা শক্তি এসে মানবজাতিকে কোনো রকম সহযোগিতাও কখনো করে না। মানুষই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা।
শব্দের ব্যবহার, কাহিনির বর্ণনায় একটি বিষয়ই পরিস্ফূট হয়েছে, সেটি হলো শিল্পীর চিন্তাসূত্র। কথাশিল্পী কী চিন্তা করেন, তার প্রকাশ কিভাবে তিনি করেন, সেই কৌশলের সুলুক-সন্ধান করতে হলে চিত্রশিল্পীর মনোজগতের খবর আগে বের করে আনতে হবে। সেই কাজটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জাহেদের পর্যবেক্ষণ দিয়ে লেখক প্রকাশ করেছেন। মানুষের সাধারণ কর্মচিন্তার বিপরীতে এই উপন্যাসে ভিন্নচিন্তাসূত্র আবিষ্কার করেছেন লেখক। সমাত্মজীবনী কিংবা পুরো সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের সুবিধা-অসুবিধা, মঙ্গল-অমঙ্গল বিষয়ে এখানে লেখক চিন্তিত নন। তিনিব্যক্তিবিশেষের জীবনচিত্র ও তার পারিপার্শ্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এরকারণ প্রধান চরিত্র জাহেদের জবানিতে জানিয়েছেন। জাহিদ বলছে,
সব মানবের শিরোমণি যাঁরা তাঁরা আমার নমস্য কিন্তু একজনের ছোট্টহৃদয়ের সবটুকু অধিকার করে বেঁচে থাকাই আমার লক্ষ্য। কালের অতল গর্ভে তলিয়ে যাব, হারিয়ে যাব। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। কিন্তু তবু যাওয়ার বেলায় আমার ঠোঁটে থাকবে বিজয়ীর হাসি। এবং এটাই আমার বিদ্রোহ, এটাই আমার বিপ্লব। হাওয়ার ওপর ভেসে বেড়ানো নয়, বসুন্ধরার দৃঢ় ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে কাজ করা। পুরাতন দুর্গকে ভেঙে নতুন প্রাসাদ গড়ে তোলার এই একমাত্র পথ। অন্যথায় আত্মধ্বংসই হবে সার।৫
বহুর নায়ক হওয়ার পরিবর্তে একজনের আরাধ্য হয়ে ওঠার সাধনা প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ। কারণ নায়ককে ভাবতে হয়, তার সমাজ, দেশ, সর্বোপরি কল্যাণকামী বিশ্বের কথাও। আলাউদ্দিন আল আজাদ সেই প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তিনি একজন নারীর হৃদয়ে ঠাঁই পাওয়ার বাসনাকে সব মানবের শিরোমণি হওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। কথাসাহিত্যের চিন্তাসূত্র এখানে এসে যেন ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। আদতে তা নয়। এক নারী, যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে, তার মনে ভালোবাসার সৌধ নির্মাণ করা আর বিপদসংকুল সমগ্রবিশ্বকে শান্তির কপোতে পরিণত করা একই অর্থ বহন করে। ফলে দৃশ্যত লেখক কেবল একজন নারীবিশেষের হৃদয় জয়ের কথা বললেও নেপথ্যে সমগ্র মানবজাতির মনে আস্থা-বিশ্বাস স্থাপনেরই বীজ বপন করেছেন এই উপন্যাসে।
বাংলা কথাসাহিত্যের আরেক গুরুত্বপূর্ণ লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)। লাল সালু (১৯৪৮) তাঁর সময়ের সবচেয়ে আলোচিত সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। আর এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি পুরনো কবরকে মাজার ঘোষণা দিয়ে মহব্বতনগরের ধর্মান্ধ বাসিন্দাদের বোকা বানিয়ে মজিদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্রীয় সংঘটিত ঘটনা। মজিদ গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত বাসিন্দাদের মনে মাজারকেন্দ্রিক ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আকাক্সক্ষার বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের সবাইকে ধর্মান্ধতার সুতোয় বেঁধে নিয়ন্ত্রণ করে। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, মহব্বত নগরে প্রবেশ করেই প্রথমে গ্রামের মাতুব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে উপস্থিত হয়। সেখানে সাধারণ অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত গ্রামবাসীর ধর্মানুভূতিকে পুঁজি করে উপস্থিত সবাকেই ‘জাহেল’, ‘বেএলেম’, ‘আনপাড়াহ্’ বলে বকে। তার অভিযোগ, মোদাচ্ছের পীরের মতো একজন কামেল পীরের মাজারকে গ্রামবাসী অযত্নে-অবহেলা ফেলে রেখে মহাপাপ করেছে। তার কথা শুনে উপস্থিত গ্রামবাসীর সঙ্গে সঙ্গে মোড়ল খালেক ব্যাপারীওলজ্জায় মাথা হেঁট করে রাখে। এই সুযোগে মজিদ আরও জানায়, সে গারো পাহাড়ে খুব শান্তিতে ছিল, কিন্তু এখানে সে ছুটে এসেছে দৈবস্বপ্নের কারণে। এরপর মজিদের পরিকল্পনা ও গ্রামবাসীদের পরিশ্রমে শুরু হলো জঙ্গল পরিষ্কার করা।
একসময় কবরটি লালসালু কাপড়ে ঢেকে যায়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন আসা শুরু করে। তাদের দান করা টাকা-পয়সায় শুরু হয় মজিদের জীবিকার নতুন পথ। অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি সমাজের ওপর মজিদ তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেখিয়েছেন সমাজের ওপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেয়েও মানুষের জীবনে বড় চ্যালেঞ্জ টিকে থাকা। সেই টিকে থাকার জন্য মানুষকে সংসারে ক্রমাগত সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তাকে সংগ্রাম করে জীবনে টিকে থাকতে হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর লাল সালু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদের ভেতর টিকে থাকার জন্য ‘সমাজমান্য’ কৌশল আরোপ করেছেন। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজে একজন মানুষ নিজেকে সবার চেয়ে ক্ষমতাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রায় বিনা পরিশ্রমে যে কৌশলের আশ্রয় নেই, তারই একটি হলো ধর্ম ব্যবসা। আর ধর্মব্যবসায়ের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র হলো মাজার ব্যবসা। মজিদ সেই মাজার ব্যবসাকে তার উপার্জনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। এই মাজারের কল্পিত পীরের আশীর্বাদের লোভ ও অভিশাপের ভয় দেখিয়ে মজিদ সমাজের দশ জনের ওপর কর্তৃত্ব আরোপ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেই জীবিকা নির্বাহের পথকে সচল রাখতে সেই মাজারের কল্পিত অসীম ক্ষমতার ভীতি সঞ্চার করে নিজের স্ত্রীর মনে। তার স্ত্রী যখন তাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মান্য করে, তখন গ্রামের আর দশজন তার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস দেখায় না।
মজিদ গ্রামবাসীর ওপর তার দ্বিতীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করে বাপ-বেটাকে একসঙ্গে খৎনা করিয়ে। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আরেকটি উদাহরণ তাহের-কাদেরের বাবা-মায়ের ঝগড়ার ফলে তাদের ওপর তার আরোপিত শাস্তি। মজিদ ছোট ছোট অথচ গভীর ইঙ্গিতবাহী এসব কর্মযজ্ঞের ভেতর দিয়ে সমাজের ওপর তার কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তার এই কর্তৃত্বের পেছনে ‘মাছের পিঠের মতো’ কল্পিত পীরের মাজারই একমাত্র শক্তি।
মজিদের গ্রামীণ রাজনীতির আরেকটি কৌশলের পরিচয় মেলে হঠাৎ পাশের গ্রাম আওয়ালপুরে এক বয়স্ক পীরের আগমনে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ ওই পীরের পুরানো মুরিদ। সেখানেই ওই পীর উঠেছে। উর্দু ভাষায় সুন্দর ওয়াজ করে। তার কথাবার্তায় আওয়ালপুরের বাসিন্দারা মুগ্ধ। খবর পেয়েছে মজিদ সে বৃদ্ধ পীরকে গ্রামছাড়া করতে নিজেই আওয়ালপুরে উপস্থিত হয়। কিন্তু গ্রামছাড়া করতে না পারলেও সেখানে ওই পীরের মুরিদদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার ভেতর দিয়ে মজিদ মহব্বতনগরের বাসিন্দাদের ওপর নিজের কর্তৃত্বের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তোলে।
মজিদ গ্রামবাসীর ওপর তৃতীয় বার কর্তত্ব স্থাপন করে খালেক ব্যাপারিকে দিয়ে তার প্রথম স্ত্রী আমেনাকে তালাক দিতে বাধ্য করিয়ে। গ্রামবাসীর ওপর সবচেয়ে বড় আধিপত্য বিস্তার করে আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মাধ্যমে।
মানুষকে কিংকর্তব্যবিমুঢ় করে দিয়ে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কৌশল মজিদের মজ্জাগত। গ্রামীণ রাজনীতিতে এই কৌশল বেশ ফলদায়কও বটে। মজিদ তার কৌশল পুরো গ্রামবাসীর সঙ্গেই প্রয়োগ করে। স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী প্রমাণ করা, খালেক ব্যাপারি স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করা, আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ভেস্তে দেওয়া, কাদের-তাহেরের বাপকে গ্রামছাড়া করা ও বাপ-বেটাকে একসঙ্গে খৎনা করানোর মধ্য দিয়ে মজিদ যেভাবে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, সেটি গ্রামীণ রাজনীতিরই অংশ।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেখিয়েছেন, মানুষ মাত্রই টিকে থাকার চেষ্টা করে। কখনো অন্যকে ঠকিয়ে, কখনো অন্যকে পরাজিত করে, কখনো বা নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য উপার্জনের পথ খুঁজে নেয়। উপার্জনের ব্যবস্থা হলে মানুষ সমাজে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়। মজিদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ প্রসঙ্গে হায়াৎ মামুদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য,
‘লালসালু’ উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য উত্ত পারের নষ্ট হৃদয় খুলে দেখানো কিংবা গ্রামীণ বাংলায় পীরবাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নেওয়া-এমন ব্যাখ্যায় আমার যুক্তিবোধ সায় দেয় না। মজিদের ভণ্ডামি আমাদের সমর্থন পায় না ঠিকই, কিন্তু আমাদের ঘৃণা তার দিকে ছুটে যায় না; কারণ দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব তার প্রবঞ্চনাকে ক্ষমার্হ করে তাকে আমাদেরই মতো সাধারণ ও দুঃখদীর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করে এবং তার অ-সুখ যে জীবনের অর্থহীনতাকে বুঝতে-বুঝতে অর্থ খুঁঁজে পাওয়ার সিসিফাস-শ্রম-তা লেখক আমাদের বুঝতে দেন, তার জন্য এক অব্যাখ্যেয় গোপন কষ্টও ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে আমাদের মনে।৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবন ও সমাজ চিত্রণে বিশেষ কৌশলী ভূমিকা নিয়েছেন লাল সালু উপন্যাসে। এই বিশেষ কৌশল তাঁর অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পেও তিনি প্রয়োগ করেছেন। বিশেষ কৌশলের অংশ হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানুষকে দুই ভাগে দেখেছেন। প্রথম শ্রেণী বিত্তশালী——ধর্মের জোরে, ক্ষমতার জোরে—অর্থের জোরে, পেশীশক্তিতে তারা বলিয়ান। বৃহৎ সমাজ-রাষ্ট্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র উপাসনালয় হয়ে পরিবারেও এই শ্রেণীর দৌরাত্ম্য-আদিপত্য বিরাজমান। দ্বিতীয় শ্রেণী দরিদ্র-নিরীহ—তারা যেমন ঐশীধর্মের ব্যাপারে উদাসীন, তেমনি ক্ষমতাবানদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ-অনীহ। সমাজে নিত্য এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব চলে। প্রথম শ্রেণী সংখ্যায় অত্যল্প হলেও দরিদ্র-নিরীহ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর তাদেরই কর্তৃত্ব চলে। সমাজ-রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড যেমন তাদের হাতে থাকে, তেমনি ধর্মের বিধিবিধানও তাদের করায়ত্ত। ফলে দুনিয়ার ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের ভার যেমন তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করে, তেমনি পরকালের স্বর্গ-নরকের সনদ দেওয়ারও স্বঘোষিত আধিকারীক তারা। ফলে পাপ-পুণ্য-ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে সর্বকালে-সর্বদেশে-সর্ব সমাজে বিচারের কাঠগড়ায় কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীকে দাঁড়াতে হয়। জবাবদিহিও করতে হয় তাদেরই।
লাল সালু উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত আকারে মূল্যায়নে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,
মজিদের আর্থিক অব্স্থা ভালো; বিয়ে করেছে; স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে দেয়নি, বরং বানিয়ে নিয়েছে মসজিদ; পাশের গ্রামের পীর সাহেবের প্রতিপত্তি ঠেকিয়েছে; ঐ পীর সাহেবের ওপর যে ভক্তি দেখিয়েছিল, সে-ই আমেনা বিবিকে তালাকও দিইয়েছে খালেক ব্যাপারিকে দিয়ে। ৭
বাস্তবিক পক্ষেই মজিদ চরিত্রের ভেতর গ্রামীণ রাজনীতির এক কৌশলী সত্তার উপস্থিতি প্রগাঢ়ভাবে উপস্থিত। লাল সালু উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেখিয়েছেন, গ্রামে সাধারণ মানুষকে বশে আনতে হলে দুটি বিষয়কে আশ্রয় করতে হয়। একটি ক্ষমতা, যেটা রাজনীতিকের জন্য সহজ; অন্যটি ধর্মানুভূতি জাগিয়ে তোলা, যেটি সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের ওপর সহজেই প্রয়োগ করা যায়। মজিদ চরিত্রে এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মজিদ এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই সমাজে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে। ক্ষমতাবানদের সে রাজনৈতিক কৌশলে পরাস্ত করেছে, তার জন্য সে আগে মুরিদ বানিয়েছে মোড়ল খালেক ব্যাপারিকে। আর ক্ষমতাহীনদের ধর্মানুভূতির অস্ত্র দিয়ে কাবু করেছে। তার জন্য সে লাল সালু আবৃত মাজারকে আশ্রয় করেছে। এখানেই মজিদ চরিত্রের সার্থকতা, এখানেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তার সমাজসংস্কার ও সামাজিক অসঙ্গতি শনাক্তির সূত্রের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।
বাংলা উপন্যাসের আরেকজন কুশীলব শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)। তাঁর প্রদোষে প্রাকৃতজন, দক্ষিণায়নের দিন আঙ্গিক-প্রকরণের দিক থেকে বাংলা উপন্যাসের সফল উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দলিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। প্রদোষে প্রাকৃতজন উপন্যাসে লেখক যেভাবে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমণ মুহূর্তের বর্ণনা করেছেন, সঙ্গে এনেছেন শিল্পীর মনস্তত্ত্ব ও রাজনৈতিক চেতনা, সেভাবে দক্ষিণায়নের দিনেও রাজনীতি ও মানুষের মনস্তত্ত্ব গুরুত্ব পেয়েছে। আর দলিল উপন্যাসে স্বৈরশাসকের শাসনকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসবাদ ঢুকে পড়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়ে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় সূচিত হয়েছিল, তারও চিত্র আঁকা হয়েছে।
উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও লেখক থেকে লেখকের চিন্তাসূত্র সংক্রমিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। এরও চেযে বড় কথা, উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেও লেখকরা ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের যে ছবি আঁকেন,তাতে বাস্তব বিশ্বের রাজনীতি, ধর্মীয় ও সমাজের প্রচলিত প্রথাকে শতভাগ উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ বিপরীত কিংনা নতুন সৌধ নির্মাণ করেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের সঙ্গে পরবর্তী গল্পকারদের গল্পের যে মিল-অমিল, তার নেপথ্যেও ক্রিয়াশীল রয়েছে কথা বলার চিন্তাসূত্র। রবীন্দ্রগল্পে নর-নারীর সম্পর্ক, সামাজিক ঘটনাবলি, অধ্যাত্মচেতনা যেভাবে এসেছে, তাঁর পরবর্তী কথাশিল্পী চারুচন্দ্র মজুমদারের গল্পেও প্রায় একইভাবে এসেছে। পরবর্তী গল্পলেখক বিষয় বৈচিত্র্যের নিরীক্ষা করলেও আঙ্গিক-প্রকরণে তেমন পরিবর্তন আনেননি বললে অত্যুক্তি হবে না।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে চারুচন্দ্র মজুমদার, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় হয়ে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পর্যন্ত; প্রত্যেক লেখকের চিন্তাসূত্রের যেখানে মিল, সেটি মানবতা। তারা মানুষের জীবনচিত্রই এঁকেছেন, কেউ সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন, কেউ সমাজের কাছে নিজে সপে দিয়েছেন। আবার সমাজের সনাতন রীতি ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ নিস্পৃহ থেকেছেন। তবে, প্রত্যেকেই সমাজের ছবিই এঁকেছেন। সামাজিক চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্য একেকজনের একেক রকম হতে পারে কিন্তু যুগযন্ত্রণাকে তুলে ধরার ক্সেত্রে সবার চিন্তাসূত্র একবিন্দুতে এসে মিলেছে। তা হলো, মানুষের যাপিত জীবনের অকৃত্রিম ছবি অঙ্কন।
তথ্যসূত্র
১। রণেশ দাশগুপ্ত, রচনাসমগ্র, (সম্পাদক: সৌমিত্র শেখর) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ.১০
২। দেবীপদ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের কথা, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১২১
৩। মোহাম্মদ নূরুল হক, বাংলা উপন্যাসে বিধবা: বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ, বাংলানামা,ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ৫২-২৩
৪। তদেব, পৃ. ৬৯
৫। আলাউদ্দিন আল আজাদ, তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস), গতিধারা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৭১
৬। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, উপন্যাসসমগ্র, (ভূমিকা) হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, প্রতীক, ঢাকা, মে, ২০১৪,
৭। আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, অবসর, ঢাকা, ২০০১, পৃ. পৃষ্ঠা. ৫৬,
কথাসাহিত্যের চিন্তাসূত্র
প্রকাশক: জলধি
মূল্য: ৩০০ টাকা
স্টল নম্বর ১৯২-১৯৩