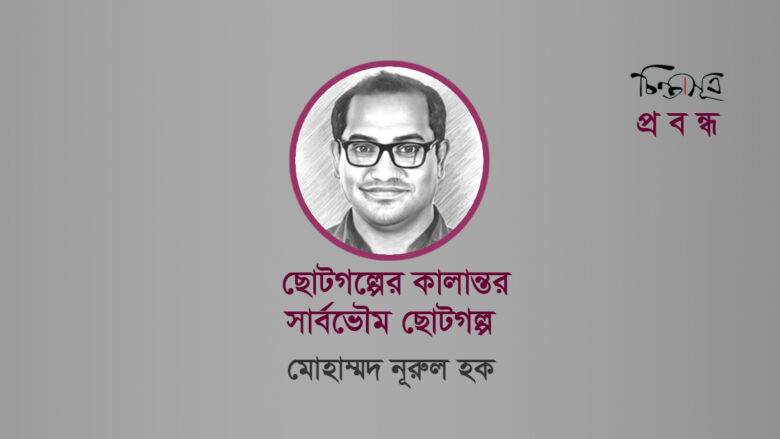ছোটগল্পের রূপ কী হবে—তা নিয়ে লেখকদের প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোটগল্প কেমন হবে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পবিষয়ক ছোট সংজ্ঞাটি আজকের গল্পকারদের কাছে আর মান্যতা পায় না। হয়তো একারণে নিরীক্ষার নামে আজকের লেখকেরা গল্পকে গল্পহীন করে তুলছেন। ছোটগল্প আজ বহুরৈখিকতার নামে শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়ছে। ছোটগল্পের মৌল গুণ একরৈখিকতা; পূর্ণতা নিটোল গল্প বুননে। গল্পের ভেতর অনাবশ্যক বিবরণ উপস্থাপন, গল্পের শিল্পগুণ যতটা ক্ষুণ্ন করে, ততধিক ক্ষুণ্ন করে পাঠকের মনোযোগ। ননফিকশনের বিবরণ চর্চায় গল্পকার নিজের পাণ্ডিত্য, নিরীক্ষাপ্রবণতার স্বাক্ষর হয়তো রাখেন, কিন্তু সে স্বাক্ষর গল্পের পক্ষে সহায়ক না হয়ে পাঠবিমুখ করার কারণ হয়ে ওঠে।
ছোটগল্প কেবল লেখকের কল্পনাপ্রসূত কাহিনির ঘনঘটা? আন্তন চেখভ, কিংবা রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো গল্প পাঠ শেষেও দেখা যায়, গল্পের উদ্দেশ্য নিছক কোনো কাহিনি বুননের নৈপুণ্য উজিয়ে মহত্তর কোনো শিল্প হয়ে ওঠেনি। যে কাহিনি গ্রামের কোনো প্রখর স্মৃতিধর প্রবীণের মুখেও শোনা যায়, তার জন্য দীক্ষিত মানুষের সযত্ন প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। এসব গল্পের বিষয় মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য আচরণের পরম্পরা। কখনো কখনো আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নির্বাচিত ঘটনাও গল্পের শরীর ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিয়ামক হয়ে ওঠে। ভিন্ন ধরনের গল্পও রয়েছে। সেসব গল্পে মনভোলানো কথার ফুলঝুরি ছাড়াও নতুন নতুন চিন্তার বীজও লুকিয়ে থাকে। এ ধরনের গল্প পাঠ শেষে পাঠকের চিন্তার ভরকেন্দ্রে পরিবর্তনের ঢেউ জাগে। কোনো কোনো ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কের জটখোলাও পাঠকের অভিরুচির মধ্যে পড়ে। তখন একই গল্পের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এসব গল্পে কাহিনির চেয়ে, কাহিনির সূত্র, চরিত্রের আচরণের চেয়ে চরিত্রের অবদমন প্রধান ভূমিকা পালন করে। গল্পের ক্যানভাসজুড়ে চরিত্রগুলো আপন মহিমার ঔজ্জ্বল্য ছড়াতে সক্ষম। গল্পকার যখন কোনো গল্পের বিষয়কে চরিত্রের আচরণ ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলেন, তখন পাঠক স্বাধীনভাবে চরিত্র নির্বাচনের সুযোগ পান। ব্যাপারটা অনেকটা চিত্রকলার মতোই। ছবি যেমন নিজে কথা বলে না, দর্শককে দিয়ে বলিয়ে নেয়, তেমনি এসব গল্পের চরিত্রগুলো নিজে কথা না বললেও পাঠক সেসব চরিত্রের ভেতর আপন স্বভাবের স্পর্শও অনুভব করেন। এ ধরনের গল্পে পাঠকও একটি অধ্যায়। যেখানে পাঠকের অনুধ্যান আর চরিত্রের নৈপুণ্য ঐকান্তিক হয়ে ওঠে। গল্পের ভেতর বুদ্ধির মুক্তি ঘটে, চরিত্র যখন সংস্কারমুক্তচিত্তে আত্ম-উদ্বোধনের ছাড়পত্র লাভ করে। তার জন্য লেখকের ভূমিকা ষোলোআনা। লেখকের স্বভাবই তার সৃষ্ট চরিত্রের আচরণে প্রকাশ পায়। সঙ্গত কারণে দীক্ষিত লেখক চরিত্র সৃষ্টির সময় কোনো একটি বিশেষ চরিত্রের প্রতি পক্ষপাত দেখান না।
কিন্তু একথাও সব সময় সত্য নয়—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলোর স্বভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোনো কোনো চরিত্রের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাঁর ক্ষেত্রে বিশেষ চরিত্রের প্রতি দুর্বলতা মেনে নেওয়া যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের উন্মেষ; অনেকাংশে বিকাশও। কিন্তু উত্তরকালের কোনো দীক্ষিত লেখকের ভেতর সে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেলে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’ একজন কাবুলিওয়ালার বণিক মনোবৃত্তির সঙ্গে পিতৃস্নেহের যুগল আচরণের মনস্তাত্ত্বিক কাহিনি। আবার ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পেও সে মানবিক প্রেম মুখ্য। পার্থক্য ‘কাবুলিওয়ালা’র প্রেম আত্মজার প্রতি, ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে পোস্টমাস্টারের প্রতি ছোট্টবালিকা রতনের প্রেম? ফলে ‘কাবুলিওয়ালা যে যুক্তিসঙ্গত বিশ্বস্ততা অর্জন করে ‘পোস্টমাস্টার’ তা পারে না। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পের নায়ক প্রতি সন্ধ্যায় কোন অমোঘ আকর্ষণে ঘরে ফেরেন? সেটা বাস্তবতার নিরিখে কতটা গ্রহণযোগ্য? গল্পকে সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে হবে? রূপকথা বলার দিন সে কবেই শেষ! আজকের দিনে, চাঁদের দেশের চরকাবুড়ির সুতাকাটার কাহিনি কেউ শোনেন? চাঁদ অধরা যতদিন ছিল, ততদিন মানুষের কাছে এর মর্যাদা ছিল ভিন্ন ধরনের। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ মানুষের গবেষণার বিষয় হয়ে থাকেনি কেবল, হয়ে উঠেছে ভ্রমণের স্থানও। সঙ্গত কারণে চাঁদ নিয়ে কল্পকাহিনি বুননের রুচি অচল হয়ে পড়েছে। রূপকথা বলার যুগ যেমন অস্ত গেছে, তেমনি সময় হয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতার। বিজ্ঞান নয়—বিজ্ঞানসম্মত; দর্শন নয়—দর্শনময় গল্প বলার সময় এখন। ঐশীধর্মের পরিবর্তে মানবধর্ম, রাজনীতি নয়, রাজনীতিনিষ্ঠ গল্প বলার যুগ আজ। সুতরাং আজকের গল্পে ভাবালুতা পরিত্যাজ্য।
শরৎচন্দ্রের ভাবালুতাসর্বস্ব গল্প আজকের যুগে অচল। অচল কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগন্ধী ধারাও। চরিত্রের হয়ে লেখকের ওকালতিও এখন চলে না। বিশেষ চরিত্রের প্রতি স্রষ্টার বিশেষ পক্ষপাত পাঠককে বিব্রত করে। পাঠক অসহায় বোধ করেন স্রষ্টার পক্ষপাতিত্বে। তবু তাঁর ‘মহেশ’-এর মানবিক বোধ এবং সর্বপ্রাণের প্রতি সমান সম্মানই এ গল্পকে কালোত্তীর্ণ হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাই শরৎচন্দ্রীয় গল্পের স্থানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মনস্তাত্ত্বিক গল্প পাঠকের আরাধ্য হয়ে ওঠে। ভাবালুতাসর্বস্ব গল্পের জায়গা দখল করে মনোবিশ্লেষণাত্মক গল্প। সেখানেও সমস্যা থেকে যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘নয়নচারা’ মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমুর ক্ষুধার্ত জীবনের এক মর্মস্পর্শী কাহিনি। গল্পকার এ গল্পে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে এত বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন যে, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে পাঠকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা হলেও সমরেশ বসুর ‘আদাব’ গল্পটিও সর্বজনীনবোধকে আশ্রয় করে রচিত। যেখানে মানবপ্রেমই বড়। কোনো ধর্মীয় পরিচয় নয়, প্রবল সংশয়ের ভেতরও মানুষ মানুষকে চিনতে শেখে। বিশ্বাস করে, একজনের সংকটে অন্যজন ব্যথিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর ‘রজনী হল উতলা’য় কথক তার হবু স্ত্রীর কাছে তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতিচারণা করছেন। সে গল্প স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় না, শুরু হয় অনুরুদ্ধ হয়ে। কিন্তু শেষ হয় পথের সমাপ্তিতে। যে কথক রাতের পর রাত, আশ্রিতের কন্যাদের দেহসম্ভোগ করে পরিচয় না জেনে, সে কথকের জন্য পাঠক মনে করুণা জাগে কতটুকু? কতটুকুই বা ঘৃণা জাগে? তবে গল্পের শ্রোতা নীলিমা গল্প শুনে কি কিছুটা বিব্রত বোধ করে? হয়তো করে, অন্ধকারে বসে থাকে বলে কথকতা টের পায় না।
রাসু আর কালীর শারীরিক মিলনে ধর্ম কিংবা সামাজিক বিধি কোনোটায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কারণ ঘটনাটা একটা স্বাভাবিক পরিণতির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেও ঘটেছে লোকচক্ষুর আড়ালে।
শওকত ওসমানের ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পের বিষয়বস্তু সামান্য। কিন্তু সে সামান্য বিষয়কেই আসামান্য দরদ দিয়ে বুনেছেন। সৌদামিনী মালো একজন তেজোদীপ্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন নারী। তার স্বামী বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন, জগদীশ মালো। নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে সৌদামিনী ছাড়া তার উত্তরাধিকার থাকে না। বিশাল ভূসম্পত্তির প্রতি নিকটাত্মীয় মনোরঞ্জন মালোর দৃষ্টি পড়ে। সে সম্পত্তি রক্ষা ও মাতৃহৃদয়ের হাহাকার মেটানোর জন্য সৌদামিনী একটি ছেলে দত্তক নেয়। এতেই ক্ষেপে ওঠে সমাজের ধর্মরক্ষাকারী সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতিপালন ক্ষত্রিয়ের ঘরে? তারা মেনে নিতে পারে না। ফলে সৌদামিনীকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। সেখানে সৌদামিনী নিজেই এক বিস্ময়কর তথ্য ফাঁস করে। ছেলেটি হিন্দু নয়, মুসলমান। দত্তক হরিদাস তার মুসলমানিত্বের পরিচয় জানতে পেরে শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগী হয়। সৌদামিনী এবার ভেঙে পড়ে। হয়ে পড়ে দিশাহারা। যে সম্পত্তির জন্য এত লাঞ্ছনা, সেই সম্পত্তি গীর্জাকে দান করে নিজেও ধর্মান্তরিত হয়। তাতেও তার শেষ রক্ষা হয় না। অপ্রকৃতিস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। উপাসনালয়গুলো মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে, মানুষের বিপদে সান্ত্বনাও দিতে পারে না। সৌদামিনীর সম্পত্তি ওঠে নিলামে। সেখানে কথক শোনে সৌদামিনীর সংগ্রামমুখর জীবনের ইতিকথা। গল্পে সম্পত্তির প্রতি লোলুপ মানুষের হীন মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট। শওকত ওসমান নিপুণ কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজের লোভী মানুষের পরধন লোলুপতার চিত্র। সম্পত্তির প্রতি সাধারণ মানুষেরই যে কেবল অন্যায় লোভ রয়েছে তা নয়, উপাসনালয়গুলোরও রয়েছে লালসা। সৌদামিনী নিকটাত্মীয় মনোরঞ্জনের লোভ থেকে সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিজের অবদমনকেও সহ্য করেছেন। ধর্মান্তরিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন গির্জায়, সেখানে অবদমনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি আর নিজের জীবন সবই হারালেন। জনব্রাদার সৌদামিনীকে ধর্মান্তরিত হতে প্রথমে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু গোপনে ধর্মান্তরিত হওয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন করে রাখেন। সঙ্গত কারণে লেখক শওকত ওসমান বিষয়টিকে ব্যঙ্গ করেন, ‘নৌকা ঠেলে দিয়ে বেয়াই কে আজ না গেলে নয়, বলে থেকে যেতে বলা’। সৌদামিনীর সম্পত্তি, সম্ভ্রম, আর সম্মান রক্ষার কোনো সম্ভাবনাই যখন হিন্দু সমাজে অবশিষ্ট নেই, তখন ব্রাদার জনকেই শেষ আশ্রয়দাতা বলে মনে হয়। অথই সমুদ্রে অসহায় মানুষ খড়কুটো ধরেও শেষবারের মতো টিকে থাকতে চায়, সৌদামিনীও চেয়েছেন। কিন্তু রক্ষকই যেখানে ভক্ষক সেখানে সে সম্ভাবনা অলীক। এ সুরই বেজে উঠেছে এ গল্পে।
হাসান হাফিজুর রহমান অনেক গল্প লিখেছেন। নানা কারণে তার গল্পকার খ্যাতি অর্জিত হয়নি। কিন্তু তার ‘আরো দুটি মৃত্যু’ গল্পটি বাংলা ভাষা কেন বিশ্বসাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর সমান্তরালে পথ চলার সামর্থ্য রাখে। ‘নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ’গামী রাত্রির ট্রেনের কয়েকজন যাত্রীর ভ্রমণকালীন একটি মানবিক ঘটনার গল্প। গল্পের চরিত্র সংখ্যা চার। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ, একজন মাঝবয়সী নারী; অন্যজন নয়-দশ বছরের একটি মেয়ে। আর শেষজন গল্পের কথক। মূল গল্পে কথকের কোনো ভূমিকা নেই। যা আছে তা কেবল কিংকর্তব্যবিমূঢ় দর্শকের। সেখানে প্রসববেদনা উদ্ভূত এক নারীর অন্তিম মুহূর্তের চিত্র আঁকা হয়েছে। শেষপর্যন্ত নানা উৎকণ্ঠায় আর ভয়ের ভেতরই অন্তঃসত্ত্বা নারীটির মৃত্যু ঘটে, ছোট মেয়েটির আর্তচিৎকারে পরিচয় মেলে, মৃতা আর বয়স্ক পুরুষ ভাসুর-ছোটবউ সম্পর্ক। মৃত্যু ঘটে এক নারীর, সঙ্গে অনাগত শিশুরও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—মানুষকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।
অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত ওসমান, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, বুলবন ওসমান, সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে নিুবর্গের মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবি উন্মোচিত হতে থাকে। ফলে পাঠক দেখতে পায়, তাঁদের গল্পে একটি নতুন প্রত্যয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানবিকতার প্রশ্নে, গল্পের ভেতর গল্প পাঠের আনন্দে পাঠক স্বস্তিবোধ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নিুবর্গের মানুষের জীবনযাত্রা চিত্রিত হলে সেখানে দেখা যায়, নিম্নবর্গের মানুষ অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সংগ্রামী; কিছুটা দ্রোহীও। মানিকের গল্পের চরিত্রগুলো বাস্তবপন্থী, বিভূতিভূষণের গল্পের চরিত্রগুলো ভাবুক। তারাশঙ্করের গল্পের চরিত্রগুলোর ভেতর এ দুয়ের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত। আলাউদ্দিন আল আজাদ উচ্চবিত্তের জীবনচক্রে যেমন ডুবুরি, তেমনি নিুবিত্তেরও। তার ‘ঠাণ্ডাভাত’, ‘ঈশ্বরের পলায়ন’, ‘একহাজার একরাত্রি’ ও ‘বৃষ্টি’ সে সাক্ষ্যই বহন করে। শওকত ওসমান ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের অন্বয়সাধন করে একধরনের বিমিশ্র অনুভূতিসম্পন্ন গল্প বুনেছেন। অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে সমকালীন সমাজবাস্তবতার রূঢ়চিত্র প্রতিফলিত। তিনি লিখেছেন, ‘মানুষ’, জমিরুদ্দিনের মৃত্যুবিবরণ’, ‘আনন্দের মৃত্যু’, ‘প্রাচীন বংশের নিঃস্বসন্তান’-এর মতো কয়েকটি ছোটগল্প। ‘প্রাচীনবংশের নিঃস্বসন্তান’ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন কী করে একজন মানুষ সব হারাতে হারাতেও হারায় না। কী করে একজন মানুষ সুযোগের অভাবেই অনৈতিকতার দিকে যেতে সাহস পায় না। সুযোগ এসে গেলে তথাকথিত সৎ মানুষও কী করে অসৎ হয়ে ওঠে, তার নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে এ গল্পে। এ গল্প একরৈখিক। বহুরৈখিকতার নামে গল্পহীন প্রলাপে পর্যবসিত হয়নি। সৈয়দ শামসুল হকের আর একটি অসাধারণ গল্প ‘মানুষ’। এক চাকরিচ্যুত সাজাপ্রাপ্ত মানুষের সঙ্গে তার দীর্ঘ পুরনো শত্রুর একরাতের আকস্মিক সাক্ষাতের গল্প এটি। কথক যার জন্য চাকরি হারিয়ে কারাবরণ করে, ঝড়ের রাতে একই স্থানে তারই সঙ্গে দেখা। কথক সব ভুলে লোকটির সঙ্গে কথা বলার কাক্সক্ষা পোষণ করলেও লোকটি সমাজব্যবস্থায় প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের আচরণের কথা মনে করে কথককে বিশ্বাস করতে পারে না। তাই কথকের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে জীবনবাজি রেখে পথে নেমে পড়াকেই শ্রেয় মনে করে।
বনফুলের ‘অদ্বিতীয়া’ গল্পটি খুব সাধারণ গল্প। বনফুলের স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ রসবোধ এ গল্পে উপস্থিত। ঘটনাটা অসামান্য ও পরিহাসপূর্ণ। কথকের শ্যালিকা কথককে চিঠি দিয়ে জানায়, কথকের স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় মারা গেছেন। বাচ্চাদের মানুষ করার জন্য কথককে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে। কথকও শ্যালিকার যুক্তি অকাট্য মেনে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। কিন্তু বাসরঘরে ঢুকেই নিজের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ পেয়ে লজ্জা পান—সেখানে তারই স্ত্রী তার পাঁচ সন্তান পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে। এ গল্পের ভেতর পুরুষসমাজকে যেমন তিরস্কার করা হয়েছে, তেমনি নারীর চাতুর্যও প্রকাশিত হয়েছে। আবদুল গাফ্্ফার চৌধুরী’র ‘মাসকাটাল’ শ্রমজীবী মানুষের ক্রমপরিবর্তমান পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে না পারার গল্প। একদিকে সাধারণ মানুষের সেবা, অন্যদিকে খেটে খাওয়া মানুষের রুটিরুজির পথ রুদ্ধ হওয়ার কষ্ট। মূল চরিত্র ছিটু মাঝি। মাসকাটাল নদীর বুকে নৌকা বেয়ে তিনপুরুষ ধরে জীবনযাপন করে আসা মাঝি। এ নদীতে যখন জমিরুদ্দিন মৃধা ইঞ্জিনচালিত লঞ্চ নামানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ছিটুমাঝি, রমিজ, হামিদ, রসিদ মেনে নিতে পারে না। সঙ্গত কারণে ছিটু মাঝি স্বগতোক্তি করে, ‘মানুষের ভাত মেরে একি মেসিন চালাবার যন্তররে বাবা’। লঞ্চ নদীতে নামানোর জন্য অনুরোধ করার জন্য লঞ্চের মালিক মৃধার বাড়িতে সবাই উপস্থিত। মৃধা সমাজের গণ্যমান্য, কথা বলার ঢংও তেমন। ফলে লঞ্চ নামানোর বিরুদ্ধে যার ক্ষোভ সবচেয়ে বেশি, সে ছিটুমাঝির বড় ছেলে আজিজের বেকারত্ব নিয়েই মৃধা প্রশ্ন তোলেন। তাকে দেখা করারও প্রস্তাব দেন। রসিদের কাছে মৃধার যুক্তি নিষ্ঠুর বলেই মনে হয়, তাই সে ক্ষোভের কথা প্রকাশই করে দেয়, ‘লঞ্চ না চললে দেশের কেউ মারা যাবে না, কিন্তু চললে আমরা দুশো আড়াইশো নাইয়া সকলে একযোগে যে মারা পড়বো মৃর্ধা সাহেব’। এ ক্ষোভমিশ্রিত উক্তির ভেতর নিঃস্বপ্রায় মানুষের আর্তনাদ শোনা যায়, সত্য; কিন্তু স্বার্থপরতাও আছে। আছে শ্রেণীচেতনাও। কম খরচে নিরাপদে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য নৌকার চেয়ে লঞ্চই উত্তম। এসত্য নাবিকরা বোঝেও, নিজের স্বার্থে সে সত্য মেনে নিতে অনীহ। এর পর লঞ্চবিরোধী ছিটুমাঝিরই বড় ছেলে আজিজকে লঞ্চের চাকরি দেওয়া হয়। ছিটুমাঝি বিষয়টা মেনে নিতে পারে না, তার সঙ্গী হয় ছেলে গনি। পিতা-পুত্র দু জনে আবার নদীতে না ভাসায়। ছেলে গনির ভেতরই ছিটুমাঝি নিজের যৌবনের রূপ দেখতে পায়। পরোপকারিতার প্রশ্নে গনি যে পিতা ছিটুমাঝিরই এক ভিন্ন সংস্করণ। ছিটুমাঝি তার প্রথম ছেলে সিরাজকে মাসকাটাল নদীতে হারিয়েছিলেন এক ঝড়ের রাতে। বৈঠা বাইতে গিয়ে হঠাৎ সিরাজ নদীতে পড়ে যায়। তার আর্তচিৎকার শুনেও ছিটুমাঝি ছেলেকে উদ্ধার না করে দু আরোহীর জীবন বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।
সম্পূর্ণ গল্পটির পরিপূর্ণতা টানটান উত্তেজনায়। কোথাও ঝুলে পড়ে না। গল্পের শেষে দেখা যায়, যে লঞ্চ বৈঠাচালিত নৌকার মাঝিমাল্লার অন্ন সংস্থানের প্রধান অন্তরায়, সে লঞ্চের সংকটময় সময়ে ছিটুমাঝির ছোট ছেলে গনি দাঁড় বেয়ে বিপদাপন্ন মানুষকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে যায়। যে মানবিক গুণ সমাজের উঁচু তলার মানুষ জমিরুদ্দিন মৃধার নেই, সে মানবিক গুণ নিম্নবর্গের সুবিধা বঞ্চিত, শোষিত গনির রয়েছে। তাই যে লঞ্চ তার অভুক্ত থাকার কারণ হয়ে ওঠে, সে লঞ্চ উদ্ধার করায় গনির ব্রত। ‘আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর/ আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়ায় যে মোরে করেছে পর’ মন্ত্রে উজ্জ্বীবিত হতে দেখা যায গনি ও ছিটুমাঝিকে। মানুষের বিপদে মানুষই এগিয়ে আসে। উঁচু তলার শোষক শ্রেণী মানুষের অন্ন কেড়ে নিয়ে সুখী, নিম্নবর্গের মানুষ পরোপকারেই তৃপ্ত। আবদুল গাফফার চৌধুরী এ গল্পে মানবিকবোধের সঙ্গে পাশবিক আচরণের সাংঘর্ষিক সম্পর্ককে ফুটিয়ে তুলেছেন। উঁচু তলার মানুষ, দেশসেবার নামে আপন স্বার্থসিদ্ধির পথ খোঁজেন, নিম্নবর্গের মানুষ নিজের স্বার্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে স্বগোত্রের স্বার্থচিন্তাও করেন। অনেক সময় আপন স্বার্থচিন্তাও ত্যাগ করেন।
আল মাহমুদের ‘কালো নৌকা’, ‘পানকৌড়ির রক্ত’, ‘জলবেশ্যা’ তিনটি গল্পই সমাত্মীয়। ‘কালো নৌকা’য় প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ স্পষ্ট। গল্পের চরিত্র সংখ্যা পাঁচ। রাসু জলদাস, তার ছেলে দামোদর, পুত্রবধূ কালী, প্রতিবেশিীনী শ্যামা আর অধীর জলদাস। ছেলে দামোরের সলিলসমাধির পর বৌ কালী অপ্রকৃতিস্থ। যখন-তখন দিগম্বর হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো তার স্বভাব। শ্যামার পরিচর্যায় কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে ঘরমুখো হয়। একদিন একা ঘরে দিগম্বর অবস্থায় রাসু কালীকে দেখে। তার শরীরের ঘাম মুছে দেয়। কিন্তু নিজে থাকে স্বাভাবিক। সেটা সামাজিক ভীতি হয়তো। দিনের শেষে রাসু অধির জলদাসের দোকান থেকে মদ খায়। নিজের ভেতরে জেগে ওঠে আদিম প্রবৃত্তি। কালীকে খুঁজতে বের হয়। পেয়েও যায়। নিজের ডেরায় দিগম্বর পেয়েও যে কালীর শরীর নিয়ে মেতে উঠতে সংকোচবোধ ছিল, অন্যের কোষায় কালীকে একা বস্ত্রহীনা পেয়ে আহ্বান করে। আহ্বানের ভাষাও কামার্ত আর পরম নির্ভরতার। যখন রাসু কালীকে মৃত স্ত্রীর সতীর নামে আহ্বান করে, ‘তুই সতী, তুই সতী—তোর বুকে সতীর গন্ধ। তুই সতী হয়ে যা কালী’। তখন কালীও শ্বশুরের আলিঙ্গনে টের পায় মৃতস্বামী দামোদরের স্পর্শ। তাই রাসুর শক্তবাহুর পেষণে কালী একবার শুধু অস্পষ্টভাবে আওয়াজ তুলে উচ্চারণ করলো, ‘দামোদর’। গল্প এখানেই শেষ। পরবর্তী অংশ তাদের আদিম আর মৌল প্রবৃত্তির ছন্দে দুলে ওঠা নৌকা আর সমুদ্রের মিলিত আলোড়নের বর্ণনা। এ গল্পে আল মাহমুদ দেখিয়েছেন, ভরা যৌবনে বৈধব্যের যন্ত্রণায় একজন নারী বাকরহিত হয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। অবদমন মানুষকে মানসিক ভারসাম্যহীন করে তোলে। রাসু আর কালীর শারীরিক মিলনে ধর্ম কিংবা সামাজিক বিধি কোনোটায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কারণ ঘটনাটা একটা স্বাভাবিক পরিণতির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেও ঘটেছে লোকচক্ষুর আড়ালে।
লেখকসৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে পাঠক স্বাধীনভাবে চরিত্র নির্বাচন করার সুযোগ না পেলে সেখানে পাঠক গল্প পাঠ শেষে কিছুটা হলেও মর্মপীড়ায় ভোগেন।
হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প। এ গল্পে সামাজিক অবক্ষয়, দারিদ্র্য, নীতিবোধ, নৈতিকতার স্খলনকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। মানুষের দেহই হয়ে ওঠে মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন। শরীরই হয়ে ওঠে জীবনদাতা। তাই পিতা হয়েও আত্মজার শরীরের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের জন্য খদ্দেরের অপেক্ষা করতে হয়। এ মানবেতর জীবনের কদর্য দিকটি চিত্রায়ণের জন্যই এ গল্পটি নিত্যপাঠ্য ও স্মরণযোগ্য। তার ‘শকুন’ গল্পটি বেশি ব্যঞ্জনাময়। এ গল্পে দেখানো হয়েছে একদল গ্রাম্য কিশোর, হঠাৎ সুদখোর, মহাজনপ্রতিম একটি শকুন তাদের সামনে এসে পড়েছে। শকুনটি কোথাও উড়ে যেতে পারছে না। সমাজের বিভিন্ন স্তরের গৃহস্থঘরের সন্তান এরা। কিন্তু কোনোভাবেই শ্রেণীসচেতন নয়। তার শ্রেণী শত্র“ খতম করার শিক্ষাও তারা পায়নি। তবু কী এক জিঘাংসা যেন পেয়ে বসে তাদের। শকুনটিকে কিশোরের দল পালক খসিয়ে, দৌড়িয়ে ক্লান্ত করে তোলে। এক সময় শকুনটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। গল্পটি খুব সাদামাটা। কিন্তু শেষ দিকে শকুনটা মৃত্যুর সময় যে বমি করে, সেখানে মহাজনদের ঘৃণ্য ভূমিকা আর কৃতকর্মের ফল স্পষ্ট হয়। শকুনটির পাশে একটি বেওয়ারিশ শিশুর লাশ ঘিরে আরও আরও শকুন উš§ত্তের মতো নেমে আসে। গল্পের শেষদিকে মৃতশিশুর মাতৃপরিচয় ‘ই কাজটো ক্যা করলো গো?’ বলে যে নারী-পুরুষের ভিড় জমে ওঠে, তারা টের পায় না ঠিক; কিন্তু পাঠক বুঝে ফেলে, ‘শুধু কাদু শেখের বিধবা বোনকে দেখা যায় না। সে অসুস্থ। দিনের চওড়া আলোয় তাকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে’ বলে। মৃত শিশুর লাশ আর শকুনের লাশের পাশাপাশি শকুনের বমি করার মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। সুদখোর মহাজন, কিংবা সমাজপতির অন্যায় আচরণ সহজে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। কেবল বিশেষ মুহূর্তেই তা প্রকাশিত হয়। তাদের লাম্পট্যের ফল প্রকাশ পায় অবৈধ সঙ্গমজনিত কারণে সন্তান গর্ভধারণে নয়, সন্তান প্রসবে। শকুন যেমন যা-ই ভক্ষণ করুক, যতক্ষণ তার উদরে আছে ততক্ষণ প্রমাণ অসম্ভব; বমি করলেই সপ্রমাণ; তেমনি লাম্পট্যেরও। এ পর্বে উঠে আসে আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘মাতৃহননের নান্দীপাঠ’। কেন্দ্রীয় চরিত্র আতিকুল্লাহ। নিজের মাকে হত্যা করার কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ক্রমাগত যুক্তিতর্কের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। বিধবা মা, যখন আতিকুল্লাহকে অতি স্নেহে আগলে রাখতে চান, তখন আতিকুল্লাহ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। আবার মা যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করার উপায় বের করে নেন, তখনও আতিকুল্লাহ সহ্য করতে পারেন না। মানবজীবনের এই এক ভয়াবহ দিক। নিজে যে অভাব পূরণ করতে পারে না, সে অভাব কেউ পূরণ করে দিলেও মানবমন সহজে মেনে নিতে চায় না। সন্তান মাকে সঙ্গ দিতে পারে, সাময়িক কষ্ট দূরও করতে পারে। কিন্তু শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন মায়ের জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ সন্তানের পক্ষে অসম্ভব। সে ক্ষুধা নিবারণের জন্য সন্তানের পিতা ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে বৈধ কি অবৈধ কোনোভাবেই জৈবিক সম্পর্ক রক্ষাকে সন্তান সহজে গ্রহণ করতে অনীহ। তাই সন্তানের চোখে পিতা ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে মায়ের জৈবিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে দণ্ডনীয়। এখানে মায়ের চাহিদার চেয়ে সন্তানের সামাজিক মর্যাদা, একক কর্তৃত্বই বড় হয়ে ওঠে। গল্পকে শেষ পর্যন্ত গল্প হয়ে উঠতে হয়। নিরীক্ষার নামে চিন্তার জড়ভরত যেমন গ্রাহ্য হয় না, তেমনি আবেগের তারল্য মান্যতা পায় না। সুতরাং গল্পকারকে নির্বাচন করে নিতে হয়, কীভাবে তার গল্প তিনি বুনবেন। কখন প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করবেন, কখন সান্ধ্যভাষা ব্যবহার করবেন, সে দায়ও তার। এ সময়ে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালখণ্ডে দেশত্যাগী মানুষের নাড়ির টানও গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে। আপনমৃত্তিকা ছেড়ে যারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের জীবনবেদ আর মৃত্তিকার প্রতি টান নিয়ে রফিকুর রশীদ লিখেছেন ‘মাটির ঘ্রাণ’। এ গল্পে মাটির টানে ছুটে আসা, অর্চনা ও বাংলাদেশের কালামের মধ্যকার সম্পর্ক ও পারিবারিক অবস্থান ও সম্পর্ক নিয়ে একটি অন্তর্ভেদী বিবরণ রয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনার ধর্ষণের ফলে যে মানবপিণ্ড অর্চনার জীবনে কলঙ্ক হয়ে আসে, সে মাটিতে পুঁতে রাখা অবাঞ্ছিত মানবপিণ্ডের টানেই অর্চনা বাংলাদেশে ফিরে আসে। কী সে অমোঘ টান! এমন মানবিক প্রেম ব্যতিক্রম। তারই বর্ণনা রয়েছে এ গল্পে।
প্রকৃত কথাশিল্পী জীবনশিল্পী; সাধন-সূত্রই তাঁর বাকবিভূতি নির্মাণের পথে সহায়ক হয়ে ওঠে। সে সঙ্গে শিল্পীর আত্মপ্রক্ষেপণ ও স্বাধিকারপ্রমত্তস্বভাব তার শিল্পকর্মের নির্গলিতার্থকে উপলব্ধি ও বোঝার পক্ষে উদ্বোধন-সূত্র হিসেবে কাজ করে। এ জন্য তাকে প্রাণপাত করতে হয় না। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে গল্পের কাহিনি বিন্যাস, সংলাপ রচনা, চরিত্র নির্বাচনে লেখকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, অভিরুচি ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ছোটগল্পের লেখক খুব সহজেই গল্পের ভেতর সন্তর্পণে নিজের ছায়া অঙ্কন করে রাখেন। না এ ছায়া অঙ্কনের বিষয়কে কোনোভাবেই মনোবিকারের বিশেষ স্তরে পর্যবসিত করা যাবে না। কারণ মনোবিকলনের ক্ষেত্রে যে যে নিয়ামক অনিবার্য হয়ে ওঠে, গল্পের বুননশৈলীতে সে নিয়ামকগুলো আপাতত অবান্তর হয়ে যায়। মনোবিকলনের ফলে শিল্পীর অবচেতন মনে একটি বিশেষ দৃশ্য, ঘটনা ও মানসিক স্তরের বিকার ঘটে মাত্র; তাতে সচেতন মনের পূর্ণ সম্মতি থাকে না। অন্যদিকে গল্পের ভেতর মানবজীবনের গূঢ়ৈষার উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিশেষ শ্রেণিবিন্যাস। সে হিসেবে গল্পকার মাত্রই সমাজচিন্তক। সমাজের ভালো-মন্দের বিভিন্ন দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণও তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সমাজস্থ মানুষের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও পেশাগত জীবনের বহুকৌণিক দিক সমাজচিন্তকের ভাবনার বিষয়। এ অর্থে ছোটগল্পকারও একজন নিখাদ সমাজচিন্তক। সুতরাং তার গল্পের ভেতর সমাজের একটি বাস্তবসম্মত ধারণা ও প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। সে প্রতিচ্ছবিতে কোনো রঙ লাগানো থাকে না। তবে রঙের প্রলেপ থাকে। সে প্রলেপে প্রহসন নয় সহানুভূতিই মুখ্য। মনিরা কায়েস গল্প লিখতে বসে, কেবল কল্পনার ফানুস উড়িয়ে মনোবিকার প্রকাশ করেন না। মানুষের আচরণ ও অভ্যাসের যৌক্তিক পরম্পরারও উন্মোচনও করেন। সেখানে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানবিক সংকটকে প্রকাশ করে, একটি বিশাল ক্যানভাসে চিত্রায়িত করেন। যে ক্যানভাস ধারণ করতে পারে প্রান্তবর্তী মানুষের আচরণগত সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য ও অসহায়তার সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, আত্মবিকলন ও আত্মউদ্বোধনও। মানুষের বাহ্যিক আচরণের চেয়ে মনস্তত্ত্বের দিকেই আলোকসম্পাত করার পক্ষপাতী তিনি। তাই তার গল্পের নাম ‘মাটিপুরাণ পালা’। মানবিক গূঢ়ৈষাকে অস্বীকার না করে, কেবল দেখার কাক্সক্ষাকে চরিতার্থ করার ভেতর যে বিপুল ফাঁকি লুকায়িত—সে সত্যকে প্রকাশ করে একজন শেকড়চ্যুত যুবকের তুমুল মনোবিকারকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন এ গল্পে। কেবল কল্পনার ফানুস নয়, অভ্যাস ও আচরণের মধ্যে যে সাংঘর্ষিক সম্পর্ক তৈরি হয়, সে সম্পর্কের সূত্র যে মানবিক সংকটের জন্ম, তা-ই এ গল্পে প্রকাশিত। শেকড়বিচ্ছিন্ন তারিক সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর অসুস্থতার কথা সাময়িক ভুলে ধনী বন্ধুর পানের উৎসবে যোগ দেয়, বন্ধুপত্নীর খোলা গলার কামনা দেখার জন্য। সে কামনার ইশারায় দগ্ধ হয়, কিন্তু কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন হয় না সে উৎসব থেকে। বরং গভীর রাতে ভাড়া বাড়িতে ফিরে গিয়েই জানতে পারে তার স্ত্রী সাবিহা হাসপাতালে। হাসপাতালের জন্ম নেওয়া সন্তানের ‘জন্মফুল’ মাটি চাপা দেওয়া নিয়ে তারিক অকস্মাৎ শেকড়সন্ধানী হয়ে ওঠে। তার মনে হয় তার সন্তানের জন্মফুল তার নিজস্ব বাড়িতেই হওয়া উচিত। না হলে তার সন্তান নাড়ির টান অনুভব করবে কীভাবে? নাড়ি ছেঁড়া যে জন্মফুল সে ‘জন্মফুল’ যেখানে গ্রথিত থাকবে সে মানবসন্তান স্বভাবতই সেখানে থাকার কিংবা যাওয়ার কাক্সক্ষা পোষণ করবে।
নাজিব ওয়াদুদের ‘আবাদ’ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারী ও ফসলিক্ষেতের জš§দানের যোগ্যতাকে অভিন্ন সমতলে বিবেচনা করার এক অব্যর্থ শিল্পরুচির পরিচয় এ গল্প। এ গল্পের মূল চরিত্র জগলু। নিম্নবর্গের মানুষ। রূপাকে ভালোবাসে—বলা হয় না। বলার আগেই জগলু চলে যায় জেলে। ততদিনে রূপা বিবাহিতা। কিন্তু বন্ধ্যা হওয়ার অপরাধে সংসার ভাঙে। জগলু জেল থেকে ছাড়া পায়। ফিরে আসে গ্রামে। আবার দেখা হয় রূপার সঙ্গে। রূপা বন্ধ্যা—একথা জগলু মানতে পারে না। রুক্ষজমিতে পরিচর্যার জোরে যে জগলু ফসল ফলাতে পারে, সে জগলু রূপাকে বন্ধ্যা বলে স্বীকার করতে চায় না। তাই জগলুর বিয়ের প্রস্তাবে যখন রূপা যখন তার বাপকে বলে, ‘অখে ঠগাবে ক্যানে? আমি বাঞ্জা তুমি জানো না? আমি বাঞ্জা গো মাঝির ব্যাটা’, তখন জগলু ক্রোধে ফেটে পড়ে, ‘কুন শালা বুলে এই কথা?’। সফল চাষির কাছে বন্ধ্যাজমির অস্তিত্ব যেমন অকল্পনীয়, তেমনি বন্ধ্যা নারীরও। একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে যারা চিরকাল নিজের সুবিধা আদায় করে এসেছে, তাদের প্রতি এ গল্প সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবাদ। এ গল্পের চরিত্রগুলো যেমন বিশ্বস্ততা অর্জনে সমর্থ, তেমনি কাহিনিও স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছে। ফলে গল্পটি নিছক কাহিনি হয়ে থাকেনি—হয়ে উঠেছে কয়েকজন মানুষের যাপিতজীবনের চিত্রও।
আবু ইসহাকের ‘জোঁক’ শোষকের প্রতি বিদ্রƒপাত্মক ভাষায় ও কৌশলে লিখিত। আবু বকর সিদ্দিকের ‘ফজরালি হেঁটে যায়’, হাসনাত আবদুল হাইয়ের, ‘নবাবের তলোয়ার’, জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের, ‘আমৃত্যু, আজীবন’, মাহমুদুল হকের, ‘কালো মাফলার’, কায়েস আহমদের ‘মহাকালের খাড়া’, ‘নচিকেতাগণ’ কালোত্তীর্ণ হওয়ার সব মাত্রাই পূরণ করেছে। হরিশংকর জলদাসের ‘শোধ’ গল্পের বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র। আকিমুন রহমান-এর ‘উদ্বাস্তু’ আত্ম-পরিচয় সংকটাপন্ন মানুষের জীবনের মনোযাতনা প্রকাশিত। আহমদ মোস্তফা কামালের ‘অশ্রু অথবা রক্তপাতের গল্প’ সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অস্থিরতার বিষয় ফুটে উঠেছে। মঈনুল আহসান সাবেরের ‘কবেজ লেঠেল’ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লিখিত। তবে এ গল্পে কেবল মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ই প্রধান নয়, সঙ্গে উঠে এসেছে কবেজ লেঠেলের আত্মআবিষ্কারের প্রসঙ্গও। শুভবোধ ও ন্যায়বোধের প্রশ্নে সমাজের চিহ্নিত দাগি আসামির বিবেক জেগে ওঠে। তারই প্রমাণ কবেজ। কবেজ কেবল আকমল প্রধানের প্রতিদ্বন্দ্বী রমজান শেখকে খুন করে না, খুন করে দেশের শত্র“কে। রমজান শেখের খুনের সংবাদে আকমল প্রধান উল্লসিত হয়ে কবেজকে যখন বলে, ‘কী নিবি তুই কবেজ, ট্যাকা এইনই দেই, জমি লিখ্যা দেই? তখন কবেজ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে, ‘কী দিবা তুমি? আমি তো হেরে ট্যাকা বা জমির লাইগ্যা খুন করি নাই।’ তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবেজ আকমল প্রধানের শত্র“কে নয়, দেশদ্রোহীকে খুন করে। আকমল প্রধানের শত্রুকে খুন করলে সে আকমল প্রধানের দান প্রত্যাখ্যান করত না। যে দেশের শত্রু খুন করে সে কার কাছে তার পারিশ্রমিক নেবে? দেশ তো তারও। ফলে খুনের জন্য কোনো কিছুই আকমল প্রধানের কাছ থেকে গ্রহণ করতে অনীহ।
ব্যক্তিগত দুঃখবোধকে নৈর্ব্যক্তিকতায় উন্নীত করার পক্ষে কেউ কেউ ব্যক্তিবিশেষের মনোবিকার ও ভিন্ন ঘরানার যৌনবিকারের চিত্র এঁকে গল্পকে সীমিত পাঠকের জন্য নির্দিষ্ট পরিসর নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। গ্রামীণ জনপদের আর্থিক নিরালম্ব শিক্ষিত যুবকের জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কা এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের নিরাপদ মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের যে চিত্র মহীবুল আজিজ ‘মাছের মা’ গল্পে আঁকেন, সে গল্পের নায়ক গৃহশিক্ষক আখলাক নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় উন্নীত হয় গল্পকারের বুননশৈলীতে। লেখক দারিদ্র্যপীড়িত বেকার যুবকের যৌনক্ষুধা মেটানোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশলকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। শিশুছাত্রীকে ধর্ষণের জন্য তাকে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করে আখলাক। প্রস্তুত করে তার মস্তিস্কের কোষে সাঁতার শেখানোর। এর জন্য মাছের অনবরত আরামদায়ক বেদনার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে মর্মে বিশ্বাস চালিয়ে দেয়ার বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি নির্মাণের দক্ষতা দেখিয়েছেন গল্পকার। ফলে জলের নিচের কলাকৌশলকে শিশুছাত্রীর মনে মাছের কর্মকাণ্ড হিসেবে ছায়াপাত করে। যৌনতার প্রসঙ্গ গল্পের মৌল অনুষঙ্গ হয়েছে রাজীব নূরের ‘নহ মাতা, নত কন্যা’ গল্পটিও ব্যতিক্রম। এ গল্পে মিথ ও উপকথার আবহ তৈরি করে চাচা ও ভ্রাতুষ্পুত্রির যৌন সম্পর্ককে একটি যুক্তিনিষ্ঠ আবহের দিকে পরিণতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে তাদের সামাজিক বিবেচনায় আপাতত অনৈতিকতাও গ্রাহ্যতা পায়, ঘটনার পরম্পরা ও আকস্মিকতায়। লেখকের বিশ্বাস, কর্মবিশ্ব ও আচরণের সঙ্গে গল্পের চরিত্রগুলোর বিশ্বাস, কর্মবিশ্ব ও আচরণের পরিচয় না থাকলে লেখকের চিন্তার কোনো গহন অঞ্চলই স্বচ্ছ ও স্বয়ম্ভু হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় না। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনায় বাংলা কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলোকে অনেকটা অসহায় ও লেখকের করুণাপ্রার্থী হতে দেখা যায়। চরিত্রগুলো প্রায় আপন যোগ্যতা বলে বিকশিত হয় না। এর কারণ লেখকের অনবধানতা? না কি নায়ক-খলনায়ক সৃষ্টিতে লেখকের ব্যক্তিগত ও সচেতন পক্ষপাত এর জন্য দায়ী? জীবনের ভাঁড়ারে প্রচুর অভিজ্ঞতা জমা না থাকলে ব্যক্তিগত অভিরুচিতেও অনেক সময় সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন চরিত্র বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে পাঠক নিজেকে অসহায় বোধ করেন কেবল।
লেখকসৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে পাঠক স্বাধীনভাবে চরিত্র নির্বাচন করার সুযোগ না পেলে সেখানে পাঠক গল্প পাঠ শেষে কিছুটা হলেও মর্মপীড়ায় ভোগেন। কালের বিবর্তনে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে যে পরিমাণ রুচির পরিবর্তন হয়, সে পরিমাণ দূরদর্শিতা লেখক দেখাতে না পারলে গল্পের নির্দিষ্টকালের বিবরণ থেকে চিরকালীন ব্যঞ্জনার স্মারক হয়ে উঠতে পারে কতটুকু?