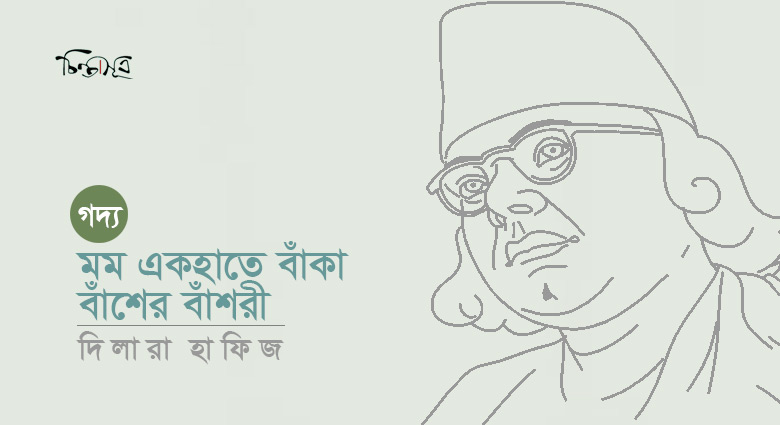 বাংলা ভাষার অন্যতম অসাম্প্রদায়িক-অনন্য-অসাধারণ এক কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬)।
বাংলা ভাষার অন্যতম অসাম্প্রদায়িক-অনন্য-অসাধারণ এক কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬)।
তিনি বাঙালির জাতীয় কবি। বিশ্বমানবতার কবি।
অখণ্ড ভারতবর্ষের শোষিত ও বঞ্চিত জনারণ্যে তিনি অনন্য ও অদ্বিতীয় এক কাব্যপ্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিলেন জাতির বন্ধ্যাকালে। এ কারণে কাব্যযাত্রার শুরুতেই হাতে তুলে নিয়েছিলেন অগ্নির বীণা। কোমল সুরের বীণা, যে অগ্নির দ্রোহে-বিদ্রোহে এবং প্রতিবাদেও বেজে ওঠে তুমুল রাগিণীতে—বাংলা ভাষার কাব্যজগতে সেই নতুন অভিজ্ঞতাও তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন কাব্যপিপাসুদের। দ্রোহী, বিদ্রোহী, প্রেমিক ও প্রেম পূজারি কবি হিসেবে ভূষিত হয়েছেন জীবদ্দশায়।
তার সমকালে তিনি আপামর জনগণের কাছে অবিশ্বাস্য রকম জনপ্রিয় কবি। তিনি প্রথম হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যেমন ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তেমনি সমালোচিত হয়েছেন যুক্তিহীনভাবে। হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য ব্যবহারেও তিনি পথিকৃত। এককথায় বলা যায়, নজরুল যুগ-সচেতন মানবতাবাদী কবি। এ সব কথা মোটামুটি সবাই জানে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমার অনুভূতি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলবো।
নজরুল শুধু জাতীয় কবি নন, তিনি আমারও কবি। আমি কিভাবে তাকে পাই কাছে, মনের সুশোভিত জ্যোৎস্নালোকে, বিরহের গিরিখাদে, কখনো সুফিবাদের প্রেমে, ভক্তিতে, শোকে-দুঃখে, দ্রোহে-বিদ্রোহে কখনো আবার অপ্রেমেও পাই তাকে। পাই উৎসবে-ব্যসনে বিচিত্র অনুভূতির অনুরণনে। এত বিচিত্র রূপে কখনো কোনো কবি ধরা দেননি আগে।
কণ্টক মুকুট শোভায় সুসজ্জিত এই কবি যুদ্ধ-বিগ্রহে, স্বাধীনতায়, ঐতিহ্যের ব্যবহারে, সংগীতের সুর মাধুর্যে আমার নমস্য। যার ‘এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য’। প্রেমিক ও বিপ্লবী এই কবির অঙ্গীকার যেন এদেশের বঞ্চিত, শোষিত জনেরই অঙ্গীকার।
সর্বার্থেই উৎসব হলো এক ধরনের অঙ্গীকার। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উৎসব, পালা-পার্বণ এসেছে সেই অঙ্গীকারের বোধ থেকেই। ছোট বেলায় যখনই রোজার শেষে আমাদের বাড়ির সামনের হালোটে দাঁড়িয়ে, কখনো কারও কাঁধে চড়ে পশ্চিম দিকের বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে বহু কাঙ্ক্ষিত ঈদের চিকন বাঁকা চাঁদকে দেখতে পেতাম, সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে আতস-বাজি-বন্দুকের শব্দে শ্রবন্দ্রিয় মাতিয়ে তুলতো। ঘরে ফিরে সেই বাল্যকালে প্রথম প্রথম রেডিওতে, পরে অবশ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ’—গানটি যখন বাজতে শুনতাম—মনে হতো আমি এক অপার আনন্দ সরোবরে ভেসে যাচ্ছি পানা ফুলের মতো। গানের সঙ্গে বাজনায় মাতাল করা আনন্দের পারদ যেন ধা করে বেড়ে তা আকাশ-বাতাস-পাতাল মাড়িয়ে ছোট্ট শিশুর মনেও ঝুমঝুমি বাজাতো।
এখনো এই বয়সে গানটি বাজার সঙ্গে সঙ্গে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ভেতরে যত কষ্টই থাকুক, তবু মনে হয়, আনন্দধারা বহিছেভুবনে। পৃথিবীর পর্ণকুটির জুড়ে যেন আনন্দ নেমে আসছে, তার সুবাস পৌঁছে যায় সব শ্রেণীর মানুষের ঘর-দোর ছেড়ে বহির্বাটিতেও।
ইদানীং খুব ভাবি, কবি কাজী নজরুল ইসলাম যদি এই গানটি না লিখতেন ঈদ-উল-ফিতরের এই ঈদ এবং ঈদের চাঁদকে নিয়ে, তাহলে কত না অসম্পূর্ণ থাকতো আমাদের ঈদের হাসি-গানের এমন আনন্দধারা। কবি নিজে মুসলমান না হলে কোনোদিন এই গানটি লিখতে পারতেন? এই প্রশ্নও জেগেছে মনে।
নিশ্চয় না।
কারণ, রোজার তিরিশ অথবা উনত্রিশ দিনের সিয়াম সাধনায় ইতি টেনে শেষ রোজার ইফতারির পর পরেই প্রথম চাঁদ দেখার যে আনন্দাবেগের উৎসধারা গানটির অন্তরার মধ্যে নিহিত আছে, সেই আপ্লুত আবেগে অবগাহন যে না করেছে, তার পক্ষে কখনো এই গান লেখা সম্ভব হতো না বলেই মনে করি আমি। জনজীবনের একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে মাটির মানুষের কাছে আকাশের একফালি চাঁদ এত কাঙ্ক্ষিত, এত মনোরম ও আশা জাগানিয়া হতে পারে, তা কাজী নজরুল ইসলামের আগে কেউ এমন শব্দে-বন্ধে-ছন্দে ধরতে পারেননি। এ জন্যেই বোধ করি এই উৎসব-সংগীত রচনার জন্যে কাজী নজরুল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। যথার্থই আমরা হাত বাড়িয়েছি জাতীয় কবির কাছে। এ আমার একান্তই ব্যক্তিগত বিবেচনাপ্রসূত অনুভূতির প্রকাশ মাত্র।
যে কারণে পৃথিবীজুড়ে মানবতাবিরোধী যত প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণের নাগপাশ বিরাজমান ছিল, সে সবের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার।
তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়, ধর্মীয় রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিষ অতীতে যেমন ছিল, আজও তেমন প্রবলভাবেই বিশ্বজুড়ে বর্তমান। কিন্তু তিনি কখনো ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মেলাননি। সেজন্যে তার কবিতায় আমরা হিন্দু-মুসলিম মিথ ও ঐতিহ্যের সাবলীল ব্যবহার লক্ষ করি ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাসহ অনেক রচনায়। বাংলা কাব্য সাহিত্যেকাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্য রচনার জন্যে প্রথম কারাবরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।
এ কথাটিও উল্লেখ্য, তার সময়ে তার ওপর মুসুলমান সমাজের রক্ষণশীল অংশ ক্রোধে কতটা ক্ষিপ্ত হলে বলতে পেরেছে, ‘নরাধম ইসলামের মানে জানে কী? নরাধম নাস্তিকদিগকেও পরাজিত করেছে।’ অথচ জাতীয়ভাবে সাংস্কৃতিক জগতে ইসলাম ধর্মকে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি, তা অতিক্রম করা কখনো সম্ভব নয়।
বিশ্বজুড়ে ধর্মের নামে মানুষে মানুষে শ্রেষ্ঠত্বের যে লড়াই, তা পরিণামে ডেকে এনেছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। সেই পৃথিবীর কোথাও আর কোনো নিরাপদ জায়গা নেই, যেখানে বাস করে কেউ বলতে পারবে আমার আয়ুতক বাঁচবো আমি। অহেতুক কেউ মেরে ফেলবে না আমাকে। ধর্মের বিষবাষ্পে এতটাই বিষায়িত এই মায়াবী পৃথিবী। নিরাপদে বেঁচে থাকার সেই গ্যারাণ্টি এখন পৃথিবীর কোথাও নেই।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বারো বছর পরে হিরোশিমা নাগাসাকিতে এক সাংবাদিক গিয়ে আট থেকে দশ বছরের শিশুদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। প্রশ্ন ছিল বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও? ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার? অধিকাংশের জবাব ছিল, আমি বেঁচে থাকার গ্যারাণ্টি চাই। বলাই বাহুল্য, কবিরা দ্রষ্টা, তারা ভবিষ্যৎ দেখতে পান। এজন্যেই এতকাল আগে নজরুল ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এভাবে কবিতায় বলতে পেরেছিলেন:
কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম-নেশা,
ধ্বংস করেছি ধর্ম যাজকী পেশা।
ভাঙি মন্দির ভাঙি মসজিদ
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সংগীত—
এক মানবের একই রক্ত মেশা
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।
অন্যত্র যখন বলেন, ‘মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান’, তখন মনে হয়, অবশ্যই মনে হবে, যিনি একাধারে কবি, দ্রোহী-বিদ্রোহী, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ ও সৈনিক। সব পরিচয় ছাপিয়ে তখন বড় হয়ে দেখা দেয় তার বিশ্ব মানবতার বোধ ও বোধি। যে কারণে পৃথিবীজুড়ে মানবতাবিরোধী যত প্রকার অন্যায়, অবিচার, শোষণের নাগপাশ বিরাজমান ছিল, সে সবের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার।
এজন্যে নিজের সম্পর্কে কত সহজে বলতে পেরেছেন, ‘আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।’ কণ্টক মুকুট পরা এই কবির জন্যেই আমরা বাঙালি জাতীয় পরিচয়ে পেয়েছি আমাদের রণসংগীত।
ধর্মীয়ভাবে প্রত্যেক মুসলমানের মনে এবাদতের পীঠস্থান হিসেবে পবিত্র কাবাগৃহের প্রতি রয়েছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। সেই রূপককে অস্তিবাদী নজরুল ব্যবহার করেছেন একেবারেই নতুন আঙ্গিকে।
‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল/ চলরে চলরে চল…।’ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মনে প্রাণে ছিল তারই গান, কবিতা। বিস্ময়করভাবে স্বাধীনতার প্রেরণা লাভেও আমরা হাত বাড়িয়েছে তারই কাছে। বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে ও পরিশেষে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নজরুলের গান, তার শিকলভাঙার জ্বালাময়ী স্বরগ্রাম, সংগ্রামী বাঙালির জাতীয় চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছে সমধিক। মুক্তির সে লড়াইয়ে যোদ্ধাদের শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে নজরুলের কবিতাই। এভাবেই তিনি ফুলের জলসা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছেন।
যেকোনো যুদ্ধ মানেই ধ্বংস অবধারিত, সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে নব সৃষ্টির যে আনন্দ, নব সূর্যালোকে নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাতলে অধিষ্ঠিত দেখতে পাওয়ার যে গৌরব—তা তো মুক্তিযোদ্ধাদের জয়বাংলা ধ্বনির মধ্যেই চুপটি করে ঘুমিয়েছিল। সে ইতিহাস কে না ভালো জানেন?
নজরুল ইসলাম নিজে যুদ্ধে গিয়েছেন, আক্ষরিক অর্থে সরাসরি যুদ্ধে যাওয়ার আবেগ সব কবির থাকে না। আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধই তার প্রমাণ। সারাদেশে কবি তো ছিলেন শতাধিক। কিন্তু কলম ছুড়ে ফেলে দেশ-মাতৃকার প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে দেখি রফিক আজাদ, মাহবুব সাদিক, বুলবুল খান মাহবুব, মাহবুব হাসানসহ হাতেগোনা কয়েকজন কবিকে। সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন খুব কম-সংখ্যক কবি-কথাসাহিত্যিক।
বিশ্বের পটভূমিতে কাজী নজরুল ইসলামের রয়েছে মহাযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে সম্মুখযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার যে অনুপ্রেরণা, সেই অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধিতে ধারণ করেই, তিনি এমন একটি যুদ্ধ-সংগীত রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, যা আমাদের জাতীয় জীবনের পরম পাওয়া বলে মানি।
তার ‘মহররম’ কবিতাটি বাঙালি মুসলমানের মনে কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার অনবদ্য শোকাবহ স্মৃতির প্রতীক হয়ে আজও মানুষের অন্তরে অতীত শোকের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে নতুন করে। ফোরাত নদীর কূলে দাঁড়িয়ে এক ফোঁটা পানির জন্যে যে হাহাকার, অস্তিত্বের যে সংকট, তাকে তিনি তুলে ধরেছেন প্রকৃতির অসামান্য আন্তরিক নীলিমায়, ‘নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া/ আ’ম্মা! লাল তেরি, লাল কিয়া খুনিয়া!’
এমনকি একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত শোককেও তিনি নৈর্ব্যক্তিক করে তুলেছেন সুর লহরীর ভেতর দিয়ে। অবাক হতে হয় শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যর পরে শোকাচ্ছন্ন কবি যখন বলেন:
ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি…
অথবা ‘শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়’—এই গানের কথা ও সম্মোহিনী সুরের ভেতর দিয়ে কবির হৃদয় বিদীর্ণ করা শোকের যে হাহাকার ফুটে উঠেছে, তা শ্রোতামাত্রের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায় অনায়াসে। তখন তা কেবল কবির ব্যক্তিগত শোকে সীমাবদ্ধ থাকে না। সব বিস্ময়ের সীমারেখা অতিক্রম করে সর্ব সাধারণের শোকে পরিণত হয়ে যায়।
এখানেই সংগীত সম্রাট তিনি।
মানুষের অসহায়ত্ব ও সৃষ্টির রহস্য জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, বিনাশ এমনকি মানবজীবনের পরিণতি নিয়ে স্রষ্টার বিস্ময়কর খেয়ালিপনাকে অস্তিবাদী নজরুল অনুভব করেন মরমি সুফি-সাধকের মতো। ভক্ত হৃদয়ের গভীর এক উপলব্ধি থেকেই তিনি বলতে পারেন:
খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে
হে বিরাট শিশু আনমনে
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুলখেলা
নিরজনে প্রভু, নিরজনে।
কিংবা
লাইলী তোমার এসেছে ফিরিয়া / মজনু গো আঁখি খোলো
প্রেমপিয়াসী এই কবির প্রেমের প্রতি যে দুর্নিবার আকর্ষণ ও তার বিরহ-কাতরতা; দুই-ই প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে তার সংগীতে।
একইভাবে ইসলামি গজল রচনায়ও রয়েছে তার বিশেষত্ব। ‘কারো মনে তুমি দিও না আঘাত, সে আঘাত লাগে কাবার ঘরে।’ অর্থাৎ মানুষের মনের মধ্যেই বাস করেন সেই প্রতীকী ঈশ্বর বা খোদা। তাকে আঘাত করলে, সে আঘাত অবশ্যই পবিত্র কাবা গৃহে আঘাত করার মতোই ব্যাপার হবে। ধর্মীয়ভাবে প্রত্যেক মুসলমানের মনে এবাদতের পীঠস্থান হিসেবে পবিত্র কাবাগৃহের প্রতি রয়েছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। সেই রূপককে অস্তিবাদী নজরুল ব্যবহার করেছেন একেবারেই নতুন আঙ্গিকে।
আমার দিক-নির্দেশনাহীন কাব্যজীবনের যাত্রাপথের প্রথম দিকে নজরুলের অনুকরণে বেশ কিছু কবিতা লিখে খাতাভরে ফেলেছিলাম। চেষ্টা করেছি নজরুলের মতো হতে। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে জানার পরে কেন যেন মনে হলো আমাকে যেতে হবে আমার সমকালে, নিজ অস্তিত্বের শেকড় খুঁজে নিতে নিজস্ব আয়নায়। তবে কবি-মাত্রই একথা স্বীকার করবেন, আমাদের অগ্রজ সব কবি বাস করেন আমাদের হৃদয়ের জ্যোৎস্নালোকে। তাদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা আমাদের নিরুদ্দেশ কাব্যযাত্রায়।

