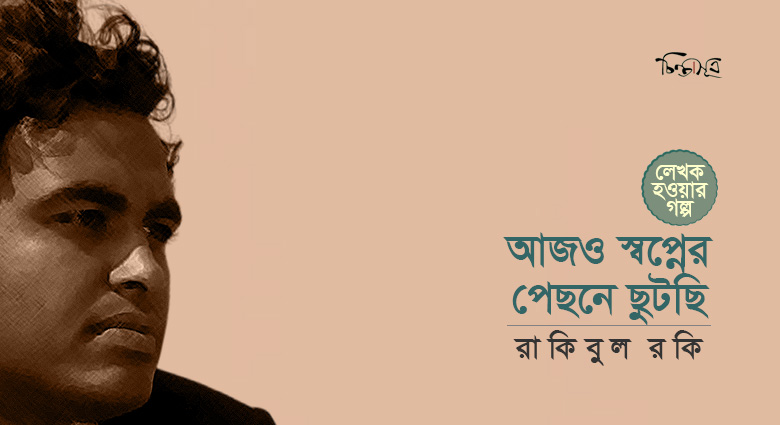 ০১.
০১.
শুনতে কি চাও তুমি সেই অদ্ভুত বেসুরো সুর
ফিরে পেতে চাও কি সেই আনচান করা দুপুর
:অঞ্জন দত্ত
ভর দুপুর। বাইরে সোনালি সোনালি রোদ। খাটে, ফ্লোরে বিছানা পাতা হয়েছে। বিছানা বলতে পাটির বিছানা। তখন গরমের সময় পাটি বিছানো হতো। শীতে চাদর। এখন তো বারো মাস চাদর। অতীতের মতো পাটি বোধহয় হারিয়ে গেলো বাঙালির জীবন থেকে। দুপুরের ভাত খাওয়া হয়েছে ঘণ্টা খানেক হয়েছে কি হয়নি, ভাতঘুমের জন্য এই শয্যা। মা-খালা সবাই ঘুমিয়ে আছে। আমি বোধহয় বড়খালার সঙ্গে নিচে শুয়েছি। বড়খালাকে আমরা বলি, আম্মা। মাকে মা। নানি বাড়িতে কি তখন কোনো অনুষ্ঠান ছিল? মনে নেই। শুধু মনে আছে, দুপুরে আমি পাটিতে শুয়ে আছি। পাশে সবাই ঘুমে। ঘুম নেই চোখে আমার। নিজের মনে গড়াচ্ছি। আর আপন মনে কথা বলে যাচ্ছি। বলছি, রোকনুজ্জামান খানের ‘হাসি’ ছড়াটি। পুরোটা তো পারি না। বড় জোর চার লাইন। কিন্তু একলা শুয়ে শুয়ে আর কী বলবো? ছড়াটির জানা অংশের সঙ্গে তাই আবোলতাবোল লাইন বসিয়ে টেনেই নিচ্ছি।
এটা আজ থেকে কত বছর আগের কথা? প্রায় তিন দশক তো হবেই। যতটুকু মনে পড়ে, বয়স তখন পাঁচ পেরিয়েছে কি পেরোয়নি। আচ্ছা, এত ছোটবেলার কথা কি মানুষের মনে থাকে? বিশেষ করে আমার মতো বেভুল মানুষের? জানি না। আটাশি সালের বন্যার কিছু কিছু দৃশ্য আমার কাছে এখনো জীবন্ত। অথচ হিসাব করে দেখেছি, আমার বয়স তখন মেরে কেটে তিন। কিন্তু দৃশ্যগুলো এখনো ফটোগ্রাফের মতো আমার চোখে ভেসে ওঠে। ভেসে উঠে সেই দুপুরের ছবি। সত্যিই কি এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল? নাকি সবটাই আমার উর্বরমস্তিষ্কের কল্পনা। যাই হোক, আমার মনে হয়, কথা বানানোর স্বভাব সেই ছোট বেলা থেকেই ছিল। আসলে বানিয়ে বলার স্বভাব প্রতিটি বাচ্চারই থাকে। সেটা তেমন কোনো কিছু না। তবু আমার মনে হয়, সেই সুদূর শৈশবেই একটি বীজ রোপণ হয়েছিল আমার মধ্যে; কিছু কথা নিজের মতো করে বলতে হবে।
০২.
আমি হব সকাল বেলার পাখি
: কাজী নজরুল ইসলাম
ছোট তেঁতুল গাছের মতো ছেলেবেলার কথা আরেকটু বলি। দুটো স্বপ্নের কথা খুব মনে পড়ে। আরও কিছু স্বপ্নের কথা মনে আছে, তবে এ দুটো বিশেষ। একটি স্বপ্ন, আমরা অনেকে ছোট একটি রুমে বসে আছি। তখন কিসের একটি শব্দ ভেসে এলো। আমি ভয়ে জড়োসড়ো সেই স্বপ্নের মাঝেই, চারপাশে অনেকেই আছে। তবু আমি ভয় পাচ্ছি। কী এক অদ্ভুত শব্দ। এই শব্দটি জাগরণেও আমাকে অনেক দিন কাঁপিয়েছে। পরে অবশ্য শব্দটির রহস্য উদ্ঘাটন করেছি। আমাদের বাড়িটি ছিল কাশীপুর কাউন্সিল অফিসের কাছেই। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ রাস্তার পাশেই ছিল আমাদের তিনতলা দালান। নাকি সাড়ে তিনতলা! আমরা কোথাও গেলে ফিরে আসার সময় রিকশাঅলাকে বলতাম, কাশীপুর কাউন্সিল অফিস, তিনতলা দালানের সামনে নামবো। অনেক সময় নতুন কাউকে বাড়িতে আসতে বললে মজা করে বলতাম, পঞ্চবটি থেকে মুক্তারপুর পর্যন্ত রাস্তার পাশে একটাই তিনতলা দালান, ভুলের কোনো আশঙ্কা নেই। (জানি না, সেই বলাতে কোনো অহঙ্কার ছিল কি না। যদিও বুকে হাত দিয়ে এখনো বলতে পারি, কোনো বিষয়েই আমার কোনো অহঙ্কার নেই, ছিল না। তারপরেও কি কথাটি অহঙ্কারের মতো শোনাতো? এজন্যই কি এখন বাড়ির পাশে লিখতে হয় ‘ছিল’? মানে এখন নেই।) রাস্তাটি উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে গেছে। রাস্তার পূর্বপাশে আমাদের বাড়ি। বাড়ি বলতে দালান আর কী। পশ্চিম পাশে নদী। আমার বলতাম, গাঙ। আসলে শাখা নদী। হয়তো শাখা নদীও না। কারণ সেই গাঙের পর ছিল চর। চরের পরে বুড়িগঙ্গা। ঢাকা সদরঘাট থেকে আসা বরিশালগামী লঞ্চগুলো এখান দিয়েই যেতো। ছাদে দাঁড়ালে দেখা যেতো লঞ্চগুলো। দেখা যেতো মুন্সীগঞ্জের কমলাঘাট। তখন লঞ্চকে বলতাম জাহাজ। এই জাহাজের ভেঁপু ভেসে আসতো আমাদের জানালা অবধি। বিশেষ করে রাতে। তা শুনেই আমি ভয়ে কাঁপতাম।
দ্বিতীয় স্বপ্নটি যখন দেখি, তখন মনে হয় ক্লাস টু’তে পড়ি। বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছি। কে যেন এসে বললো, ওই যে সকাল বেলার পাখি! আমরা পাখিকে আরও ভালো করে দেখার জন্য ছুটলাম। আসলে চড়ুই, টিয়ের মতো আমি ভেবেছিলাম ‘সকাল বেলার পাখি’ বুঝি কোনো পাখির নাম। স্বপ্নের মধ্যে সেই পাখির পেছনে ছোটা শুরু করলাম, সেই সকাল বেলার পাখির পেছনে এখনো ছুটছি, ছুটছি স্বপ্নের পেছনে পেছনে। এই সকাল বেলার পাখি, এই স্বপ্ন, আমার লেখালেখি। একটি ভালো লেখার জন্য জীবনবাজি রেখে ছুটছি। ছুটবো।
০৩.
সকাল নয়, তবু আমার
প্রথম দেখার ছটফটানি
দুপুর নয়, তবু আমার
দুপুরবেলার প্রিয় তামাশা
ছিল না নদী, তবুও নদী
পেরিয়ে আসি তোমার কাছে
তুমি ছিলে না তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা!
:সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
মেহেদী আর আমি প্রায় নদীর পাশে বসে হিসেব করতাম। হিসাব করে দেখতাম, আমাদের বড় লেখক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে কারণে আমরা এই ধরনের রায় দিয়েছিলাম, তা হলো, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সত্যজিৎ সবারই পারিবারিকভাবে একটা লেখালেখি, সংস্কৃতিচর্চার ঐতিহ্য ছিল। আমাদের তা কানাকড়িও নেই। যদিও আমি ছোটবেলা থেকে অগাধ বিত্তের মাঝে বড় হয়েছি, তারপরও বলতে হয়, আমার বংশে আমি প্রথম অনার্স পাস। এমএ পাস। এর একটা কারণ ছিল। সংসারের যে সচ্ছলতা আমি দেখেছি, সেটা পুরোটাই আমার বাবার উপার্জনে। দাদার কাছ থেকে তেমন কিছু তিনি পাননি। কারণ তার ছোটবেলাতেই দাদা মারা গিয়েছিলেন। ফলে বাধ্য হয়েই বাংলা সিনেমার মতো সংসারের বড় ছেলে হিসেবে বড় একটি পরিবারের জোয়াল তার কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। এছাড়া আমাদের এলাকার পরিবেশ ঠিক পড়ালেখার অনুকূল ছিল না। এর ছোট্ট একটি চিত্র আমি একটু পরেই দেবো।
যাই হোক, মেহেদীর অবস্থাও অনেকটা আমার মতোই ছিল। বংশঠিকুজি খুঁজলে মনে হয় না কাউকে পাওয়া যাবে, সৃজনশীলতার সঙ্গে জড়িত ছিল। এই যে নিরাশা, তারপরও আমরা একদিন বাজি ধরেছিলাম লিখবোই।
এখন যদি মারা যাই, লেখাটা শেষ করতে পারব না। শেষ পর্যন্ত আমি কী বলতে চেয়েছিলাম, কাউকে তা বলতে পারব না। তাই আমার উপলব্ধি হলো, বেঁচে থাকতে হবে। যেভাবেই হোক।
আবার ছোটবেলার কথায় আসি।
সেই যে স্কুলে ভর্তি হয়েছি কি হয়নি সেই সময়ের পর এমন কোনো ঘটনা আর মনে পড়ে না, যার সঙ্গে ভবিষ্যতে যে লেখার চেষ্টা করেই জীবন পার করবো, তার সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্লাস সেভেনে ওঠার আগে লেখার ভূত তখনো ঘাড়ে চাপেনি, তবে আউট পড়াশোনা শুরু হওয়ার পরিচর্যাটা শুরু হচ্ছিল। সেটা পরে বলবো। আগে লেখা কিভাবে শুরু হলো, সেই ঘটনা বলি। তার আগে বলি, নব্বইয়ের দশক ছিল রোমান্টিক সিনেমার যুগ। শাবনাজ-নাইম, সালমান শাহ-শাবনুর, ওমর সানী-মৌসুমীর জয়জয়কার। তখন বিনোদনের জন্য পুরো পরিবার দল বেঁধে সিনেমা হলে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। এছাড়া ভিসিআরে নিত্যনতুন হিন্দি সিনেমা তো ছিলই। ফলে হাই স্কুলে পা দিতে দেরি, মনে প্রেম প্রেম ভাব আসতে দেরি হতো না।
অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, আমাদের যুগে থ্রি-র ছেলেমেয়েও প্রেমে পড়তো। সেভেন এইটের স্টুডেন্ট তো রীতিমতো লায়েক। নানানজনের প্রেমের সাথে আমার লেখার কী সম্পর্ক? প্রশ্ন হতে পারে। কারণ আমি ছিলাম বড়লোকের শান্তশিষ্ট, গোবর গণেশ সন্তান। নম্র। ভদ্র। পাড়ার ছেলের সাথে মিশি না। খেলতে যাই না। সারাদিন মায়ের আঁচল তলে থাকি। স্কুলে যাই, যাই না। সকাল সন্ধ্যা পড়তে বসি। যদিও তেমন মনোযোগ নেই। কোনো রকমে সব সাবজেক্টে পাশ করে উপরের ক্লাসে প্রমোশন পাই। ঝগড়াঝাটি, মারামারির রেকর্ড নেই। একা একা ছাদে বসে, পরিচিত কয়েক জনের সাথে আড্ডা দিয়ে দিন কেটে যায়। যদিও আমাদের সেই জীবন এখনকার মতো ফ্ল্যাটবন্দি জীবন ছিল না। রাজ্যের লোক বিকেলে ছাদে সময় কাটানোর জন্য চলে আসতো।
আত্মীয় না, কিন্তু একই মহল্লার হওয়ায় অনেকেই ফিতার ক্যাসেট ভাড়া করে নিয়ে আসতো দেখার জন্য। এমনও দেখা গেছে, পরিচিত কোন লোক এসে আমাদের ঘরে শুয়ে শুয়ে সিনেমা দেখছে। একা থাকার পরও যুগের বাতাস এসে আমার বদ্ধ মনের ঘরেও টোকা দিতো। প্রেম মানেই তো কবিতা। দেখতাম, স্কুল নাইন টেনে পড়া মুরব্বিরা প্রেমের কবিতা লেখার চেষ্টা করত। মিলটিল দিতো লাইন শেষে। আমি পড়ে অবাক হতাম। মনে হলো, আমিও লেখার চেষ্টা করি তো! আফসোস, মাথায় কিছুই আসতো না। কিছুই লিখতে পারতাম না। এই যে না পারা, এই না পারার কারণেই আমি চেষ্টা করতাম, যা এখনো অব্যাহত আছে। আর যারা লিখতে কামিয়াব হয়েছিল, তাদের লেখার ওইখানেই কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটেছিল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমিও প্রেমে পড়ি। মনে মনে। কাউকে সে কথা বলার সাহস বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না। যার প্রেমে পড়েছি, তাকে বলা তো বহুৎ দূর কি বাৎ! শুধু তাই নয়, অনার্সে ওঠার আগে অপরিচিত কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি কি না, সন্দেহ আছে। তবে অনার্সে ওঠার পর সেটা নিশ্চয় সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছিলাম। কারণ অনার্সে যখন ভর্তি হই, তখন ৭২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৫০ জনই ছিল মেয়ে।
এখনো যদিও অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ইতস্তত করি। স্বাভাবিক হতে পারি না। তবে পরিচিত গণ্ডির মধ্যে আমি থাকলে অনেকের কথা না বললেও চলে।
এখন ওই যে, কারও সঙ্গে মিশতে পারি না, মন খুলে কথা বলতে পারি না, হৃদয়ের কথা কেউ শোনার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল না। এজন্যই লেখার কাছে আত্মসমর্পণ। তবে যত সহজভাবে বললাম, বিষয়টা মনে হয়, তত সহজ না। লেখার প্রতি ঝুঁকে পড়ার আরও কিছু কারণ নিশ্চয় ছিল। এর একটি হলো, যাদের লেখা ছাপা হতো, পড়তাম, তারা ছিল আমার কাছে নক্ষত্র। সিনেমার নায়ক নায়িকাও আমাকে ততটা আকর্ষণ করতো না, যতটা একজন লেখক বা কবি করত। একটা মানুষ একটা কবিতা বা গল্প লিখেছে, সে লেখাটি কত মানুষ পড়ছে। এটা ভাবতেই আমার কাছে রোমাঞ্চ লাগতো। মনে হতো তারচেয়ে সুখী শক্তিমান আর কে হতে পারে?
এছাড়া শৈশবে মৃত্যুচিন্তা আমাকে খুব তাড়া করতো। যখনই মনে হতো আমি মরে যাওয়ার পর কেউ আমার কথা মনে রাখবে না, ভুলে যাবে, তখন খুব খারাপ লাগতো। প্রশ্ন হতে পারে, ছোটবেলায় মৃত্যু নিয়ে এত দার্শনিক চিন্তা এল কিভাবে? এর কারণ খুবই সহজ। এখনো দেখবেন, পাড়ামহল্লার মসজিদগুলোতে কিছু পোলাপানের সমাগম ঘটে। তারা নিয়মিত নামাজ কালাম করে। আমিও একসময় ওই রকম ছিলাম। মসজিদে যেতাম। হুজুরদের বয়ান শুনতাম। নিশ্চয় স্বীকার করবেন, হুজুররা মানুষের মনকে দুর্বল করার জন্য, ধর্মের পথে মতি ফেরানোর জন্য মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী আজাবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ওখান থেকেই মৃত্যু চিন্তা, বলা ভালো মৃত্যুভয় আমার মাঝে ঢুকেছিল। তখন মনে হতো, ইশ, আমি যদি ভালো কিছু লিখতে পারি, তাহলে মৃত্যুর পরও হয়তো নামটা থেকেও যেতে পারে। যদিও আমার লেখালেখির পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আমার এক শিক্ষকের। তার কথাই এখন বলব।
০৪.
সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।
: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পড়ি তখন ক্লাস থ্রি-তে। সকাল সন্ধ্যা নানিবাড়িতে রাখা লজিংমাস্টারের কাছে পড়তে বসি ছোটমামা, খালার সঙ্গে। আমাদের বাড়ি থেকে নানি বাড়ি যেতে ছিল পাঁচ সাত মিনিটের পথ। রাতে অনেক সময় নানি বাড়িই থাকি। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা-বিস্কিট খেয়ে বাংলা ঘরে পড়তে যাই। পড়া শেষে বাড়ি ফিরে আসি।
বাড়িতে বিকেলে পড়ার জন্য একজন স্যার ঠিক করা হলো। প্রথম দিন স্যার এলেন। কথাবার্তা বেশি বললেন না। চেহারা দেখতে ছিল তখন বিটিভিতে প্রচারিত ‘দ্য সোর্ড অব টিপু সুলতান’ সিরিয়ালের নাম ভূমিকায় অভিনয় করা টিপু সুলতানের মতো। কিন্তু পরদিন থেকে স্যার ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। পড়াতেন। খুবই ভালো পড়াতেন। তারচেয়ে বেশি কথা বলতেন। তার সেই কথাই খুলে দিয়েছিল আমার কাছে এক নতুন দুয়ার। মূলত স্যারের কথায় অনুপ্রাণিত হয়েই আমার লেখালেখির জগৎ, তারচেয়ে বড় কথা বইয়ের জগতে পদার্পণ। ২০২১ সালের বইমেলায় প্রকাশিত আমার অনূদিত বই ‘দ্য পাওয়ার অব ইয়োর সাবকনশাস মাইন্ড’ স্যারকেই উৎসর্গ করেছি। উৎসর্গ পাতার লেখাটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি।
খন্দকার আজিম
শ্রদ্ধাস্পদেষু
আমাদের গ্রামের মানুষের আকাশ ছিল সীমাবদ্ধ। রঙিন টিভি কেনা, শাওয়ারের নিচে গোসল করা, পাকা দালান তোলা পর্যন্তই ছিল তাদের স্বপ্নের দৌড়। তিনবেলা পেট ভরে খাবার খাওয়া, পরিষ্কার জামা-কাপড় পড়া, সপ্তাহে সিনেমা দেখাই ছিল তাদের জীবন। সুখ।
তখন বই বলতে বুঝতাম স্কুলের পাঠ্য বই, কিছু ধর্মীয় জীবনী। যেগুলোকে আদব করে বলতাম, কিতাব। কিতাব ধরার অনুমতি সবার ছিল না। এলাকার খুব কম লোকই কলেজে পড়তো তখন। শৈশবে স্থানীয় কাউকে দেখিনি, যিনি বিশ^বিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়িয়েছেন। ইউনিভার্সিটি শব্দটি শিখেছিলাম, শব্দার্থ জানার জন্য।
তখন একজন শিক্ষক বাড়িতে পড়াতে এলেন। যতটা পড়াতেন, তার চেয়ে বেশি গল্পের ঝুড়ি খুলে বসতেন আমাদের সামনে। কত কবিতাই না তাঁর কণ্ঠস্থ! ‘বিষাদ সিন্ধু’ থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করতেন। শুনতে শুনতে ঘোর লেগে যেতো। চনমন করে উঠতো রক্ত। তিনি যদি এভাবে না বলতেন, না শোনাতেন, হয়তো ক্লাস এইট পাশ করার আগে ‘বিষাদ সিন্ধু’ পড়ে শেষ করা সম্ভব হতো না।
স্যার বলতেন, ‘দশটি কবিতা পড়লে একটি কবিতা লেখা যায়। দশটি বই পড়লে একটি বই লেখা যায়।’
একবার স্যারের কাছে চেয়েছিলাম ভূতের বই। দিলেন শরৎচন্দ্র। ‘বড়দিদি’। পড়ি। রেখে দেই। কিছু দিন পর আবার পড়ি। কয়েক পৃষ্ঠার পড়ার পর আবার রেখে দেই। এভাবে রেখে দিতে দিতে একদিন পুরো বই পড়া হয়ে যায়। একবার পড়ার পর আবার পড়ি সেই বই। এভাবে কয়েকবার পড়া হয়ে যায় ‘বড় দিদি।’
কী আনন্দ! মনে হলো এতদিনে মনের মতো পৃথিবী খুঁজে পেলাম। সেভেনে পড়ি তখন। সে-ই শুরু। বই সংগ্রহ করা সহজ ছিল না তখন আমাদের পক্ষে। তারপরও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবার আগেই যে বঙ্কিমের সব উপন্যাস পড়া শেষ হয়ে গেল, সে তো স্যারের জন্যেই। স্যার যদি পড়ার নেশাটা ঠিক মতো না ধরিয়ে দিতেন, তাহলে কি ওই বয়সে বঙ্কিমী ভাষা গলধঃকরণ সহজ হতো? সহজ উত্তর, না।
আজও হাসি মুখে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে স্বপ্নের পেছনে ছুটে চলছি, এই বীজ তো স্যারই বুনে দিয়েছিলেন সেই শৈশবে। দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন স্রোতের বিরুদ্ধে। তাই বেড়ে উঠেছি নিজের মতো। স্যারের সেই অপরিশোধ্য এই ঋণের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।
বইয়ের নেশা এরপর থেকে তীব্র আকার ধারণ করলো। কিন্তু হাতের কাছে যথেষ্ট বই নেই। এর ওর কাছে এনে, টুকটাক বই কিনে বই পড়তাম। তখন একটি বই-ই বারবার পড়তাম বইয়ের অভাবে। বলে রাখা ভালো আজিম স্যারের কাছে থ্রি থেকে সেভেন পর্যন্ত পড়েছিলাম। তবে বইয়ের নেশাটা ঠিক মতো ধরে সে সেভেনেই। এর আগে পড়ার আগ্রহ রাক্ষস-খোক্কসের গল্পেই সীমাবদ্ধ ছিল। নাইনে এসে বর্ষার নতুন জলের মতো কবিতার দেখা দেয়। এর আগে কিছু ছোটগল্পও লিখেছিলাম। তো কবিতার তখন ভর মৌসুম আমার। আসলে কবিতা না বলে পদ্য বলাই ভালো। বলা বাহুল্য এইসব লেখার বেশির ভাগ পদ্যের বিষয়ই প্রেম। কোনো এক বা একাধিক দয়িতাকে কাছে পাবার তীব্র আকুলতা। না পাওয়ার প্রচণ্ড দুঃখ। অঙ্ক কিংবা হিসাববিজ্ঞানের নিউজপ্রিন্ট খাতা অঙ্কের বদলে ভরে উঠেছে কাঁচা পদ্যে।
এখানে একটা বিষয়, ঠিক এই সময়টাতেই পরিবারে নানা ধরনের বিপর্যয় শুরু হচ্ছে। একটা বলি। বাবার ব্যবসার এমনই ভরাডুবি হয় যে এক সময় বাস্তুভিটাও বিক্রি করতে হয়। এক সময় যেখানে আমাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া থাকতো, সেখানে আমরাই হয়ে গেলাম ভাড়াটিয়া। একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল, আমাদের এক ভাড়াটিয়া মাসান্তে ভাড়া দেই, দিচ্ছি বলে দুই বছর পার করে দিয়েছিল। কী অবিশ্বাস্য ঘটনা তাই না? কিন্তু তাই হয়েছিল। সেই আমরা যখন ভাড়াটিয়া হয়ে যাই, তখন এমনও সময় এসেছে, মাসের চার তারিখ হয়েছে অথচ ভাড়া যোগাড় হয়নি। তাই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছি, কেননা পাঁচ তারিখ সকাল হতেই বাড়িওয়ালার ম্যানেজার ভাড়ার রশিদ নিয়ে দরজায় হাজির হবে। যদি বলি ভাড়াটা পরে নিয়েন, তাহলে অকথ্য বাক্যবোমায় চারপাশ কাঁপিয়ে তুলবে। তবে সেই দিন গেছে।
২০০৪ থেকে ২০১৪ জীবনে নানা উত্থানপতন এসেছে। ভেবেছিলাম, এই সময়ের কথাগুলোই বিস্তারিত লিখব। এই সময়টাতেই সিদ্ধান্ত নেই, লিখব। যা হয় হোক। কিন্তু এত ঘটনা, এত উপলব্ধি লিখতে গেলে সাতকাহন হয়ে যাবে। এই সময়টাতে কতবার যে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, কত আনন্দ পেয়েছি- বলে শেষ করা যাবে না। এগুলোই আমার জীবনের পরম সঞ্চয়। এই যে এক সময় এলাকার সবচেয়ে আলিশান বাড়ির মালিক থাকার সুখ আবার মস্ত পৃথিবীর এক হাত জায়গাকে নিজের বলতে না পারার বেদনাকে আমি ঈশ^রের আশীর্বাদই মনে করি। আল্লাহ আমাকে জীবনের নানান দিক দেখিয়েছেন। পুড়িয়ে পুড়িয়ে তৈরি করে তুলেছেন। তাই আজ বলি, মৃত্যু কোনো সমাধান না। গতকাল যদি আমি মারা যেতাম, আজকের সুন্দর সকালটা দেখতে পেতাম না। আমি বিশ্বাস করি, গতকালের চেয়ে আজকে কিছুটা হলেও এগিয়েছি। সমৃদ্ধ হয়েছি। সেটা সুনামে কি বদনামে, কিংবা অভিজ্ঞতায়। এগিয়েছি তো। এখন যদি মারা যাই, লেখাটা শেষ করতে পারব না। শেষ পর্যন্ত আমি কী বলতে চেয়েছিলাম, কাউকে তা বলতে পারব না। তাই আমার উপলব্ধি হলো, বেঁচে থাকতে হবে। যেভাবেই হোক।
০৫.
যদি বেঁচে যাই একদিন আরও
লিখব।
: শামসুর রাহমান
কবিতা লিখতে শুরু করার পর একটি আকাক্সক্ষা তীব্র আকারে দেখা দিলো, সেটি ছাপার অক্ষরে দেখা। আমার জন্য যা ছিল খুবই কঠিন। লেখা পাঠানো বা পত্রিকা অফিসে যাওয়া, আমার কাছে অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার। আমি এখনো একটি বিষয় খুব মিস করি, সত্তর, আশি বা নব্বই দশকের সাহিত্যিকেরা বিভিন্ন সাহিত্য সম্পাদকের দপ্তরের বসে আড্ডা দেওয়ার যে অভিজ্ঞতা তাদের ঝুলিতে আছে, আমার সে ঝুলিটা এখনো শূন্য। এখনো আমি মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি না। কারও সামনে স্বাভাবিক হতে পারি না। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে, কেমন আছেন বলার পর কথা খুঁজে পাই না। অথচ এ আমারই ছাপার অক্ষরে নিজের নাম, লেখা দেখার কী ব্যাকুলতা! প্রথম লেখাটি ছাপা হয় সম্ভবত ২০০৩ বা ২০০৪ সালে। এরপর ট্যাপ চুয়ে টিপ টিপ পানি পড়ার মতো এখানে সেখানে কিছু লেখা ছাপা হতে শুরু করলো।
লিখছি। কিছু হয় না হয়তো। তাও লিখছি। লিখবো। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগপর্যন্ত লিখতে চাই। ছুটতে চাই স্বপ্নের পেছনে।
শুভাকাঙ্ক্ষীদের অমত সত্ত্বেও বাংলায় অনার্সে ভর্তি হই। বাংলা অনার্সে ভর্তি হওয়ার সাহসটা খন্দকার আজিম স্যারই দিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, সাহিত্য করতে গেলে আগে তো ব্যাপারটা বুঝতে হবে। তাই বাংলায় অনার্সে ভর্তি হওয়া। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। কারণ ব্যাকরণে আমার চিরকালই ভ্যাবাচেকা অবস্থা। স্যার অভয় দিলেন, সেকেন্ড ক্লাস একটু খাটলেই পাওয়া যায়। সমস্যা হবে। তবে বাংলায় ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরোধিতার কারণ হলো, তখন আমাদের বাড়ি বিক্রি হয় হয়, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সেই অবস্থায় এমন কিছু পড়া যেন তার ওপর ভর করে ছাত্র পড়িয়ে দুটো টাকা উপার্জন করা যায়। তা সত্ত্বেও বাংলাতেই ভর্তি হই আমি। বাংলায় ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্তটা যে ভুল ছিল না পরে তা প্রমাণিত হয়।
যাই হোক, অনার্সে ভর্তি হবার কিছুদিনের মধ্যেই একটি দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। সবাই মিলে প্রতি মাসে চাঁদা দিয়ে ‘লিটল মেঘ’ নামে ছোট একটা পত্রিকা করতাম। ‘লিটল মেঘে’র সম্পাদক ছিলেন বর্তমানের তরুণ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, গীতিকার ইশতিয়াক আহমেদ। তখন পত্রিকার পাঠকদের পাতায় লিখতাম। লিখতাম ছোটদের পাতায়। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমি গদ্য-পদ্য সমান তালেই লিখতে চেষ্টা করেছি। শুরু থেকেই। তবে অনার্সে ভর্তি হবার আগে গল্প বা উপন্যাস (একটি উপন্যাস লিখেছিলাম ইন্টার পরীক্ষা দেওয়ার পর রেজাল্ট হওয়ার আগের অবসর সময়ের মধ্যে। সময়দেবী আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে সেটি লুপ্ত করে দিয়ে।) লিখলেও প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হই অনার্সে ওঠার পর।
লিখতে এসে যা করলাম, নিজের নামটা বদলে দিলাম। ২০১১ সালের পর নামটিতে আরেক দফা সার্জারি করি। সেই নামটিই এখন বহন করে চলেছি। ২০১৫ সালে প্রথম বই বের হয়। কবিতার। ওই বছর আমাদের সম্পাদনায় একটি শিশু সংকলনও প্রকাশিত হয়। মুজিবুল হক কবীর এবং খালেদ হোসাইনের সঙ্গে যৌথভাবে বইটি সম্পাদনা করি। তারা দুজনই আমার শ্রদ্ধেয়। নমস্য। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তাদের নামের সঙ্গে সত্যি সত্যিই একটি বইয়ের কভারে আমার নাম যাবে। তাদের সঙ্গে কাজ করেই আমি খুশি ছিলাম। এ কথা বলেছিলামও। তাদের দুজনকে ব্যক্তি হিসেবে চেনার আগে তাদের লেখা পড়েছি। দুজনই আমার শিক্ষকতুল্য। তাই প্রথমবার যখন একই সঙ্গে দুটো বই বের হলো, তাদের মতো ব্যক্তির সঙ্গে আমার নাম ছাপা হলো, এটা ছিল বড়ই আনন্দের।
তারপর একে একে চৌদ্দটি বই বের হলো। লিখে যাচ্ছি। হয়তো কিছু হয় না। তবু নিজের মতো করে লিখছি। আরও লিখতে চাই। প্রচুর লিখতে চাই। চাই, অনেক বই বের হোক আমার। জানি, মানুষকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি বইই যথেষ্ট। কিন্তু আমার যে তত প্রতিভা নেই। এক্ষেত্রে মুজতবা আলীর একটা কথা আমি মান্য করি। তার কথাটা ছিল এমন, কেউ হয়তো দশটা বই লিখেছে, তারমধ্যে একটি ভালো হয়েছে। এখন তিনি যদি নয়টি খারাপ বই না লিখতেন, তাহলে একটি ভালো বই তো পাওয়া যেতো না। (অনেক আগে পড়েছিলাম, হাতের কাছে বই নেই। নিজের মতো করে মূল কথাটা বললাম।) মান্নান সৈয়দ যে বলেছিলেন, ‘লেখারাম লিখে যা।’ আমি তাই করতে চাচ্ছি।
আসলে লেখা আমার আশ্রয়। অবলম্বন। বর্ম। সংসারে থেকেও আমি সন্ন্যাসী। সমাজে থেকেও অসামাজিক। পৃথিবীর অন্য কোনো কাজের সঙ্গেই আমি খাপ খাওয়াতে পারি না। তাই লিখতে চাই। যদিও দারুণ আলস্যে আমার দিন কেটে যায়। কিন্তু সবসময় জাগরণে, এমনকি কখনো কখনো ঘুমেও আমার মাথায় ভ্রমরের মতো লেখা গুনগুন করে। পড়া ও লেখার চেয়ে কিছুই আমার প্রিয় নয়। সবসময় লেখা নিয়ে থাকতে চাই, এজন্য ভাঙাচোরা ইংরেজি জ্ঞান নিয়েও অনুবাদ করার চেষ্টা করছি। ‘কবিতা কেন কবিতা’ শিরোনামে সুজিত সরকারের একটি প্রবন্ধ পড়ে প্রথম অনুবাদের কথা মাথায় আসে। ভাবলাম, সত্যিই তো যদি নিজের মাথায় ভাব না আসে, তাহলে তো অনুবাদ নিয়ে থাকা যাবে, লেখালেখির সঙ্গে থাকা হবে তাও।
লিখছি। কিছু হয় না হয়তো। তাও লিখছি। লিখবো। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগপর্যন্ত লিখতে চাই। ছুটতে চাই স্বপ্নের পেছনে।

