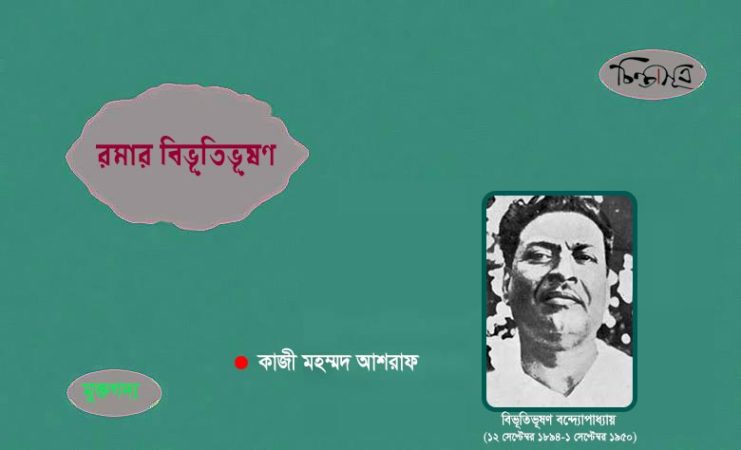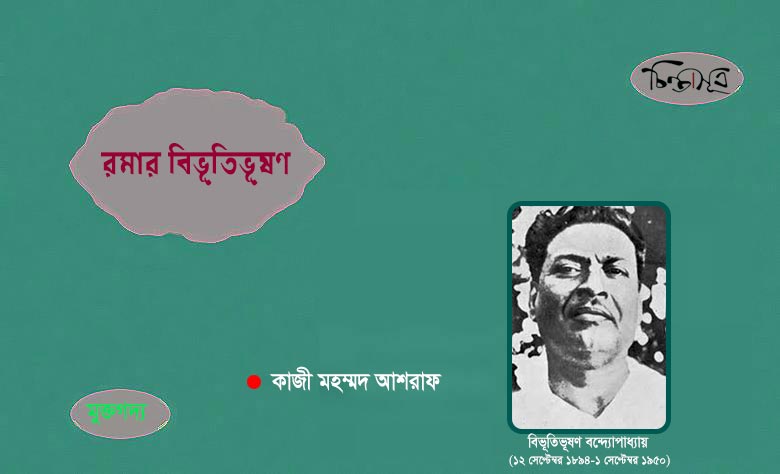
আমরা যখন ইছামতীতে নাইতে যাই, ঘুরি তার পাড়ে পাড়ে, বাবলার নুয়ে পড়প শাখা যেখানে জল ছোঁয় ছোঁয়, ঝরে পড়া বাবলার ফুল যেখানে তীরের মতো ছুটে চলে ইছামতীর ঘোলাজলের বুকের ওপর দিয়ে। সজল হলুদ ফুলগুলি, ভাটির দিকে চলতে থাকে স্রোতের সঙ্গে। পাড়ে দাঁড়িয়ে কি সুন্দর যে লাগে! (আমার স্বামী বিভূতিভূষণ: রমা বন্দ্যোপাধ্যায়)
চল্লিশোর্ধ্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ষোড়শী রমাবন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এভাবেই বনে-বাদাড়ে নিসর্গের নিবিড় আলিঙ্গনে হারিয়ে যেতেন। অপু-দুর্গার আদি সংস্করণের সাক্ষাৎ ঘটে রমার এ বর্ণনায়। অবশ্য ততদিনে তার ‘পথের পাঁচালী’ প্রকাশিত, অপু-দুর্গাও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিভূতিভূষণ নানা জায়গায় স্নান করতে ভালোবাসতেন। নিত্য নতুন ঘাট আবিষ্কার করতে তার ছিল গভীর আনন্দ। বেড়াতে বেরিয়ে নতুন ঘাট আবিষ্কার করে আসতেন, তার পরে রমাকে নিয়ে যেতেন সে সব ঘাটে স্নান করতে। এভাবে দুয়েকবার বিপদেও পড়েছেন। একবার তাদের ইছামতীর কুঠির মাঠ ছাড়িয়ে এক নির্জন বনতলে বিভূতি স্নান করতে নামান রমাকে। সেখানে কী সব কাঁথা-মাদুর আধাপচা, আধশুকনো দেখা যাচ্ছিল নলখাগড়ার বনের ভেতর। বিভূতির অবশ্য নলখাগড়ার বন দেখেই খুব পছন্দ হয়— ভেতরে কী আছে না আছে তা জানতেন না। জানলেও ক্ষতির ভয় তার ছিল না। গ্রামের মমহিলার সব সময় বলত—‘কল্যাণীর সন্তান বাঁচবে কী? ও বিভূতির সঙ্গে অপথে- বিপথে ঘুরে বেড়ায় সকাল-সন্ধ্যা। অপদেবতার দৃষ্টি পড়ে না ওরকম করলে?’
বিভূতভূষণ প্রথম স্ত্রী গৌরীর মৃত্যুর প্রায় দুই যুগ পরে রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। তাদের পরিচয় জহয়েছিল অনেকটা নাটকীয়ভাবে। রমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন। বদলির সুবাদে আগের বছর তারা বনগ্রামে এসে উঠেছেন। রমার বয়স তখন পনেরো। পড়াশোনা ছিল ভালো। বিভূতিভূষণের যে এগ্রামেই বাড়ি তা তারা জানতেন না। এ সময় বিভূতিভূষণের বোন জাহ্নবী স্নান করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। এ ঘটনায় বনগ্রাম এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল। তখন মামীদের কাছে বিস্তারিত জানতে পান রমা। ঠিকানা সংগ্রহ করে ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে রমা একদিন বিভূতিভূষণকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। এভাবেই তাদের পরিচয় এবং সখ্য। পরের বছর ১৯৪০ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা ১৩৪৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় বিভূতিভূষণের বয়স ৪৬ বছর আর রমার ১৬ বছর। তাদের দাম্পত্য ছিল প্রায় এগারো বছরের। তাদের একমাত্র সন্তান ছিল বাবলু।
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণমূলক রচনাটি পড়ে মনে হয় তাদের অসম বয়সী দাম্পত্যজীবন ছিল ঈর্ষণীয় সুখের, অপার আনন্দের। যেকোনও পুরুষ লেখকের মনে তীব্র এক আশা জেগে উঠবে, মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীও যেন এমন একটি স্মৃতিকথা রচনা করেন।
বিভূতিভূষণ ছিলেন সহজ, সরল আর বিশ্বাসী মানুষ। ক্ষুদ্র ঘাসপাতা থেকে শুরু করে বিশাল মানবজীবন, সভ্যতা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি ছিল গভীর বিশ্বাস। বিয়ের ঘটনায় তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। রমাকে বলেছিলেন, ‘আমার জীবনে আবার বিবাহ? আমার নিজেরই কেমন আশ্চর্য লাগছে! এ জীবনের লীলাকে আমাদের সার্থক করে তুলতে হবে। পুণ্যে, দানে, ধ্যানে ঘরকন্যার কাজে। কতবার আমার জীবনের এই গভীর অন্ধকার খাদটার কথা ভেবেছি। তুমি শান্ত প্রদীপের শিখা নিয়ে আলো জ্বালিয়ে সেই অন্ধকার দূর করতে এসেছ কল্যাণী।’
মাঝখানের প্রায় দুই যুগের নিঃসঙ্গ দিনগুলোর কথা বাসর রাতে রমাকে শুনিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। দুহাতের অঞ্জলিতে রমার আনত মুখটা তুলে ধরে বলেছেন, ‘বস কল্যাণী। আজ আমার অনেক কথা মনে পড়ছে, বিগত দিনের বহু কথা। আজ যদি বাবা-মা থাকতেন, আজ যদি জাহ্নবী থাকতো!’ এর পরে বলেন অনেক কথা, যা জীবনে কারও কাছে বলতে পারেননি। এমনই লাজুক ছিলেন তিনি। বলেন, ‘আজকে তোমাকে পেলাম কল্যাণী, যার কাছে আমার এ জীবনের সকল সঞ্চিত কথা মেলে ধরতে পারব।’
বড় নিঃসঙ্গ, বড় বন্ধুহীন কেটেছে বিভূতিভূষণের জীবন। জীবনের ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, আর সুখ-দুঃখের বোঝা হালকা করার জন্য, নির্দ্বিধায় জীভনের নিভৃত কথাটি খুলে বলবেন এমন কোনো আত্মার আত্মীয় তার ছিল না। তাদের বাড়িতে তার নিজের একটি মাটির ঘর ছিল। তিনি আদর করে ঘরটির নাম রেখেছিলেন ‘শ্যামলী’। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের দেখাদেখি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের থাকার ঘরটিরও এ নাম ছিল। বিভূতিভূষণের ঘরটির কপাট ছিল না। আসবাব বলতে বাবার আমলের একটা চৌকি ছিল শুধু। বৃষ্টির ছাঁট আসত, বর্ষাকালে দিনে-রাতে গরু-ছাগল এসে ঢুকত; একসঙ্গে রাত্রিযাপন করতে হতো। কেউ ছিল না সে ঘর ঝাড়ু দেওয়ার, প্রদীপ জ্বালানোর। লেখালেখির কাগজ-কলম পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি একটা সুটকেসে রেখে নিরাপত্তার জন্য অন্য এক বাড়িতে রাখতেন। একদিন সেই বাড়ির লোকজন তার সুটকেস আর একমাত্র জামাটা উঠোনে ছুড়ে ফেলে দ্যায়। তাদের অভিযোগ, তিনি আচার-বিচার মানেন না, কে যত্ন করে রাখবে এসব!
এসব কথা শুনে রমার চোখের পানি ছলছল করত। ছোটবেলার কথা, স্কুল-কলেজে পড়ার সময়কার নানা ঘটনা বলতেন বিভূতিভূষণ। শৈশবে তিনি স্কুলে ভর্তি হতে চেয়ে মায়ের কাছে আবদার করেছিলেন। অভাবের সংসার, টাকা পাবেন কোথায়! সেই বাচ্চা মানুষ দুদিন না খেয়ে দাবি নিয়ে থাকার পরে তার মায়ের কোমরের রুপোর গোট বন্ধক রেখে সাতটাকা পেয়ে সে টাকা দিয়ে স্কুলে ভর্তি করানো হয়। প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করতে দশ মাইল হাঁটতে হতো। কখনও শুধু নুন-ভাত খেয়ে, কখনও না খেয়ে। কলকাতার কলেজ জীবনেও মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকতে হতো। একটামাত্র ধুতি ছিল। এক পয়সায় কেনা সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকোবার অপেক্ষায় ছেঁড়া ত্যানা পরে বসে থাকতে হতো। এসময় তিনি প্রথম বিয়ে করেন— অনেকটা কষ্ট দূর করার জন্যেই। কিন্তু অর্থাভাব দূর হয় নি। বিএ পরীক্ষার আগে ফরম ফিলাপ করার সময় হাতে টাকা ছিল না। পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করেছেন— টাকা সংগ্রহ করতে পারেন নি। একেবারে শেষদিন ক্লার্ক জানান তার নামে টাকা জমা হয়ে গেছে, দ্রুত ফরম ফিলাপ করে দিতে হবে। তার ধারণা, সে টাকা দিয়েছিলেন পিতৃতুল্য শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
অতীত জীবনের এসব কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন রমা। শুনতে শুনতে তার চোখের পাত ভিজে যেত। কষ্ট হতো। গভীর মমতায় ছেয়ে যেত মন প্রাণ। অসম বয়সী স্বামী কিন্তু বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণকে অনেক বেশি ভালো লাগত। দু’জনে দু’জনের প্রতি আরও গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন।
এক সময় বিভূতিভূষণ স্কুলের ছেলেমেয়েদের পয়সা দিতেন ‘বাবা’ ডাক শোনার জন্য। কিন্তু বোন জাহ্নবীর সন্তান পালনের কষ্ট দেখে, পরে অনীহ হয়ে পড়েন। জাহ্নবীর ছোট মেয়ে অসুস্থ হয়ে অনেক কষ্ট পেয়ে মারা যায়। এ দুঃখজনক ঘটনাটি ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ উপন্যাসে জিতুর বউদির ছোটমেয়ে হিসেবে তুলে ধরেছেন। এ ঘটনার পর তিনি শিশুদেরকে ভালোবাসতে ভুলে যান। সন্তানের কথা বললে তিনি বলতেন, ‘ছেলেপুলে নেই তো নেই। ওসব ঝঞ্ঝাট চেয়ো না। ও ভারী ফ্যাসাদ। এই তো বেশ আছি দুজনে। যখন যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছি, যা হয় খাচ্ছি, ছেলেপুলে হলে পারবে তুমি যেতে?’
বিয়ের পর থেকেই বিভূতিভূষণ রমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটশিলা, বনগ্রাম, দার্জিলিং, বার্নপুর নানা জায়গায় বেড়াতে যান। নানা সাহিত্যসভায় রমাকে নিয়ে যান। বিভিন্ন সাহিত্যিকের বাড়ি যান, সেখানেও রমা তার ছায়াসঙ্গী। গল্পের প্লট খুঁজতে কোথাও গেলেন— সঙ্গে আছেন রমা। এমন ছির মানিকজোড়।
রমা বন্দ্যোাধ্যায়ের ধারণা লেখকেরা খুব একটা কাল্পনিক ধারণা নিয়ে কিছুই লেখেন না। চারপাশের প্রত্যহের ঘটনা নিয়েই লেখেন। চোখের দেখা ঘটনাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরার ক্ষমতা তাদের আছে। তার চোখের সামনের ঘটনা নিয়েই ‘মেঘমল্লার’, ‘সঞ্চয়’, ‘তুচ্ছ’ প্রভৃতি গল্প লিখেছেন বিভূতিভূষণ। রমা স্বামীর অনুগামিনী হয়ে ঘুরে ফিরে এসব সাহিত্যকর্মের সৃষ্টির সাক্ষী হয়ে আছেন।
তবে বাবলুর জন্মের পর রমার ঘোরাফেরা কমে যায়। বিভূতিভূষণও সংষারী হয়ে ওঠেন। এবার তিনি শিশুর পরিচর্যা নিয়ে যত্নবান হয়ে ওঠেন। বাচ্চা এত কম খাচ্ছে কেন, বয়স অনুসারে আরও বেশি খাওয়াতে হবে। কীভাবে মানুষ করতে হবে এসব ভাবনা প্রকাশ করতেন। একবার বিরাট এক ল্যাকটোজেনের কৌটো কিনে আনেন। এভাবে বাবলু হয়ে ওঠে তার নতুন সঙ্গী। ট্রেন দেখাতে নিয়ে যেতেন। বাবলু কোনদিন কী করে তা বিভিন্ন বইয়ের কোনায়, খাতায় লিখে রাখেন, ‘বাবলু বড় ভালো’ কিংবা ‘বাবলু আজ ডিম খেয়েছে’ এমন সব কথা।
বিভূতিভূষণ দরিদ্র ছিলেন কিন্তু কৃপণ ছিলেন না। রমা জানান তাদের বিয়ের আগে তো বটেই পরেও অনেক দুঃস্থ লোক সাহায্যের জন তার স্বামীর কাছে আসত। গোপন দানের কথা বিভূতিভূষণ চেপে গেছেন কিন্তু সাহায্যপ্রার্থী কিংবা সাহায্যপ্রাপ্তরা উপযাচক হয়ে এসব জানাতেন। দারিদ্র্য সম্পর্কে তার নিজের একটা আদর্শগত ধারণা ছিল নজরুলের মতো। তার ধারণা, একটু টানাটানির ভেতর মানুষ হওয়অ ভালো। তাতে মানুষের মনের ক্ষুধা বাড়ে। দেখবার, শুনবার, উপভোগ করবার আগ্রহ তীব্রভাবে জাগে। বৃহত্তর জীবনের পথে সেই আগ্রহ তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যার এই অভাববোধ থাকে না, তার জীবন অসম্পূর্ণ, একপেশে।
বিস্ময় এবং মুগ্ধতা সম্পর্কেও বিভূতিভূষণের নিজস্ব দর্শন ছিল। তার মতে, জীভন চলার পথে কোনও কিছু থেকেই যে লোক বিস্মিত হয় না, অন্তরের দিক থেকে সে মৃত। জীবনের মুগ্ধ হওয়ার মস্ত বড় জিনিস বিস্ময়।
বিস্ময় এবং মুগ্ধতাবোধ বিভূতিভূষণের জীবন দর্শন। এ দর্শনে তিনি নিজেও অন্যকে বিস্মিত এবং মুগ্ধ করে রাখতেন। শেষ জীবনের প্রায় এগারো বছর রমা তাকে কাছে পেয়েছিলেন, তাতেই তিনি শিশুর সারল্য আর জীবনের সহজতা দেখে পাগলের মতো মুগ্ধ হয়েছিলেন। হবেন না কেন, ছেলেমানুষীকে সযত্নে লালন করতেন যে! একবার তার সুটকেস খুলে রমাকে ডাকলেন, ‘কল্যাণী দেখে যাও’ বলে। হাতের কাজ অসমাপ্ত রেখে রমা কাছে গিয়ে বসলে তিনি সুটকেস থেকে রমার বিয়ের আগের একটা শাড়ির এক টুকরো কাপড় বের করে বললেন, ‘দেখ, কত যত্ন করে এটা রেখে দিয়েছি।’ এর পরে স্মৃতিচারণ আর রমার গুণ ও সৌন্দর্যের অনেক প্রশংসা করেন। পরে প্রগাঢ়স্বরে বলেন— ‘তুমি আমার সকল জিনিস এমনি করে রাখবে কল্যাণী, যখন আমি থাকব না।’
ছোট্ট সামান্য এক টুকরো সামান্য স্মৃতি অসীম ভালোবাসার স্মারক হয়ে থাকত বিভূতিভূষণের কাছে। এটা দারিদ্র্যজনিত ক্ষুদ্রতা নয় বরং সীমার ভেতর অসীমকে ধারণ করার চেষ্টা। অনেকে বলেন, অত্যন্ত কৃপণ গরিব ঘরের ছেলে ছিলেন, কিছুই দেখার শোনার সুযোগ হয়নি। তাদের ধারণা বিভূতিভূষণ একেবারে অনধিুনিক ছিলেন। রমার মতে. এ ধারণা ভুল। বিভূতিভূষণ যৌবনে খেলাত ঘোষ স্টেটে চাকরি নেন। সেখানের রমার মাতামহও চাকরি করতেন। ওই কোম্পানি ছিল টাকা বনানোর জায়গা। তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য দেখেছেন, চাকচিক্য তাকে বিচলিত করতে পারে নি। বরং টাকা ধার দিয়েছেন কিন্তু ফেরত না পেয়ে আফসোস করেন নি। পত্রিকা অফিস থেকে পাওয়া অনেক চেক তোশকের নিচে জমে উঠত, ভেঙে খরচ করারও আগ্রহ থাকত না। সঙ্গলাভ করেছেন বহু জ্ঞানী ও গুণীর। দেশ-বিদেশের শিল্প-সাহিত্যের সর্বশেষ তথ্যও তার কাছে আসত।
বিভূতিভূষণের স্বভাব-চরিত্র অনেকটা তার পিতার মতো। তিনি ছিলেন ভ্রমণপিপাসু অস্থির চিত্তের মানুষ। কিছুটা উদাসীন। তার ছায়া অবলম্বনে সৃষ্টি হরিহর। আবার বিভূতিভূষণের চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে তার সৃষ্ট অনেক চরিত্রের। অপু তো বটেই। দুর্গাও তার নিজের ছায়া থেকে তৈরি। দুর্গার মুখের অতিপরিচিত একটি সংলাপ ‘মিষ্টি যেন গুড়’ বিভূতির নিজেরই। যে কোনও পাকা ফলের এমনকি তেঁতুলের স্বাদ বর্ণনা করতেও তিনি এ কথা বলতেন।
বিভূতিভূষণর ছেলেমানুষীর ভেতরেও গভীর আত্মদর্শন ছিল। তিনি সাধারণত লিখতেন দিনের বেলায়। খুব প্রয়োজন না হলে রাতে লিখতেন না। রাত্রিটুকু রেখে দিতেন শুধু গল্প করার জন্য। সন্ধ্যা হলে হারিকেন হাতে যেতেন প্রতিবেশী এক কাকার বাড়ি। একদিন তিনি যেতে পারেননি— জরুরি লেখা লিখতে হচ্ছে। হঠাৎ শোনা গেল, সে কাকা দলবল নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বকছেন। ‘কেমন তালেবর হয়েছ তুমি, ধরাকে সরা জ্ঞান কর। লঘু-গুরু মানো না। আমি বুড়ো মানুষ আমাকেই তোমার কাছে আসতে হল।’
বিভূতিভূষণ ঘরের ভেতর থেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কাকা শুনছেন না। রমা খুব কষ্ট পেয়ে কেঁদে ফেললেন। বিভূতি বললেন, ‘আজকাল বাড়ি বয়ে অভিভাবক কেউ আর আমাকে বকতে আসেন না ছেলেবেলার মতো। কিন্তু আমার মনটা তৃষিত হয়ে থাকে কেউ আমাকে ছোট ভেবে শাসন করুক সেই জন্য।’ তিনি মনে করতেন সবাই সম্মান-শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে প্রশংসা করে, ভালো বলে স্তুতি করে। তিনি ভালো এ স্তুতি শুনতে শুনতে একঘেয়েমি লাগত। জীবনকে এভাবে তিনি কত দিক থেকে অবলোকন করতেন, এখানেই তারর মহিমা। বড় মানুষ হতে হলে, উঁচু মাপের শিল্পী হতে হলে জীবনকে এভাবেই নানা দিক থেকে রহস্যভেদ করতে হয়।
১৩৮৬ সনের নববর্ষ সংখ্যা ‘অমৃত’ পত্রিকায় রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আমার স্বামী বিভূতিভূষণ’ রচনাটি প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৯৬ সনে বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত ‘বিভূতি-স্মৃতি’ গ্রন্থে স্থান পায়। ৩৪ পৃষ্ঠায় এ স্মৃতিকথায় রমার চোখে দেখা এক বিভূতিভূষণকে চেনা যায় যিনি প্রেমিক স্বামী ও পিতা এ তিন পরিচয়ে পরিচিত। বাইরে যিনি মহান কথাসাহিত্যিক, ‘পথের পাঁচালী’র স্র্রষ্টা। এ রচনার গুণ এখানেই যে বিভূতিভূষণের সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রভূমি কীভাবে জগতের আলোয় আলোকিত হতো তা জানা যাচ্ছে। আবার জগৎকে মুগ্ধ করার কোন রহস্যের আলো ছিল তার ব্যক্তিত্ব-চরিত্র এবং সৃষ্টিতে, তারও প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।
বিভূতিভূষণ এক মানবিক বিভূতির নাম।