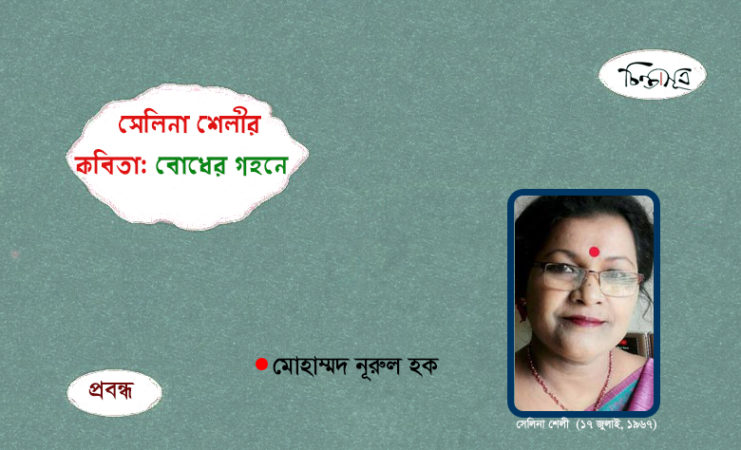স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার ইতিহাসে চাতুর্যহীন আলোড়নে কবিতাকে স্বয়ম্ভূ শিল্পে পরিণত করার পক্ষে যে কজন কবি নিরন্তর পরিচর্যার ভেতর দিয়ে এগিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সেলিনা শেলীও একজন। তাঁর কবিতা শরীরবৃত্তীয় অনুষঙ্গকে অবলম্বন করে, বিশ্ববীক্ষায় উত্তরণের পথে অশরীরী হয়ে ওঠে। সমকালীন রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে পুরাণকে একীভূত করে নতুনতর চেতনার উদ্বোধনে চিত্রকল্প ও উপমার ক্ষেত্রে দূরাগত বংশীবাদকের সুরের মতো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতা মূলত মানবচিন্তার ভরকেন্দ্রে, হৃদয়ের অলিন্দে আলোড়ন-সম্ভব শিল্পিত উচ্চারণ। সেলিনা শেলী কবিতায় কেবল হৃদয়াবেগের স্রোতে ভেসে যেতে চাননি, হতে চাননি বাক্চাতুর্যপূর্ণ কবিতার বুদ্ধিবৃত্তিক রূপকারও। কারণ কবি বুদ্ধির সৌকর্যের চেয়ে প্রজ্ঞার অনুশাসনকেই বেশি সমীহ করেন। চাতুর্যের অহমিকার চেয়ে সততার নির্বুদ্ধিতাকেই শ্রেয় মনে হয় তাঁর। সে ক্ষেত্রে কোনো রকম আপসকামিতা তাঁর লক্ষ্য নয়।
তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘অন্ধকার হে অন্তর্গত’। এ কাব্যের প্রতিটি কবিতাই ব্যক্তিগত আবেগ-উপলব্ধি ও চরাচরের নানা সঙ্গ-অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত। ‘প্রিয়তমা নীল কিশোরী’ কবিতায় মানবজীবনের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে যে অসঙ্গতি তা-ই ফুটিয়ে তুলেছেন স্বরবৃত্তের ধীরলয়ে। পঙ্ক্তি ভেঙে নতুন পঙ্ক্তি গঠন করার কারণে স্বরবৃত্তের চাপল্যের স্থানে এসেছে বৈদগ্ধের ছাপ। আবার অন্ত্যমিল পরিহার করায় চটুল ভঙ্গির স্থান দখল করেছে গাম্ভীর্য।
উসকে দিয়ে সলতেখানি
রোদ ছড়ালে চোখে চোখে
বিষণ্নতা—রোদের জালে
ধরতে গিয়ে রূপচাঁদা মাছ
দেখলে শেষে আটকে আছে
চন্দ্রবোড়া ত্রিভঙ্গিতে।
(প্রিয়তমা নীল কিশোরী: অন্ধকার হে অন্তর্গত)
ত্রিভঙ্গিতে ঝুলে থাকা চন্দ্রবোড়ার যে চিত্রকল্প, তা জীবন ছেঁকে আনা উপলব্ধির নির্যাস। মানবতার যে তিলকরেখা মানবজাতিকে দেবদেবীর মহিমার ওপরে অধিষ্ঠিত করেছে, সেটি সংশয়বাদী চেতনা। সে সংশয় যার ভেতর নেই, সে পরিপূর্ণ মানুষ হয় কী করে? অপার সংশয় ও ভুলের সুযোগেই চন্দ্রবোড়ার প্রতীকে মানুষ ভুল জিনিসকেই আসল ভেবে সাময়িক তৃপ্তির হাসি দেয়। কিন্তু বিভ্রান্তির মেঘ কেটে গেলে মানুষ সহসা সচকিত হয়ে ওঠে এবং পুনরায় আপন সৃষ্টিকর্মে নিবিষ্ট মনে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করে।
‘মৃত্যু’, ‘নেতিবাচক’, ‘স্মৃতির ভেতর বৃষ্টিপাত’, ‘সজারু’, ‘নিঃসঙ্গতা’, ‘ছয়দিন লোহার খাটে’, ‘সময়’, ‘দুর্বোধ্য অন্তরাল,’ ‘সুপ্রিয় গর্ভিনী’ কবিতায় ব্যক্তি মানুষের অসহায়তা, নিঃসঙ্গতা, মনোবিকলনসহ অন্তর্গত চেতনার রূপ এঁকেছেন। ‘ব্ল্যাক রেইন’ কবিতায় দেখি কবি হয়ে উঠেছেন একজন অসহিষ্ণু ও প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ।
ব্ল্যাক রেইনে পুড়ছে মেধা
মন-মানস ও এই বসুধা
আমার কিছুই ভাল্লাগে না
আমার কিছুই ভাল্লাগে না
ও বায়ান্ন আয় ফিরে আয়
আমার কিছুই ভাল্লাগে না
ও একাত্তর আয় ফিরে আয়।
(ব্ল্যাক রেইন : অন্ধকার হে অন্তর্গত)
এ অসহিষ্ণুতা আধুনিক কবির প্রবণতা সত্য; কিন্তু প্রতিশোধ-স্পৃহা কতটা মানবিক?
যাপিতজীবনের নানা অনুষঙ্গ যেমন কবিতার অন্তরাত্মা গঠনে ভূমিকা পালন করে, তেমনি বহু ঘটনাও সে কবিতার শরীর গঠনে সহায়ক হয়ে ওঠে। ‘অবিনশ্বর যৌবন শুধু’ কবিতায় একটি চিরকালীন উক্তি আছে। যে উক্তি মানবজীবনের শ্রেণীভেদকে কটাক্ষ করে পরম দার্ঢ্যে ও চরম ঔদার্যে। ‘অবিনশ্বর যৌবন শুধু’ কবিতার মূল বিষয় অনেকটা রাবীন্দ্রিক। কিন্তু ‘সবার জন্য থাকে না কফিন চিতা’, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওই আবহ ম্লান হয়ে যায়। ‘আত্মগত-১’ কবিতায় ‘একখ- রাত ঝুলে আছে তোমার চোখে’ পাঠান্তে যে দৃশ্য ভেসে ওঠে সেটি চিত্রকল্পের মদিরা? ক্লান্তি? রোমান্স? যে অর্থে রাত্রি পূর্ণ যৌবনের একটি রোমান্সকর অধ্যায়কে আলোকসম্পাত করে, সে অর্থে রাত্রি কারও বিনিদ্রার কারণও হয় কখনো কখনো? না হলে অনতিবিলম্বে আবার প্রশ্ন কেন, ‘কার জন্য জমিয়েছ আঁধার এমন?’
এভাবে কবিতায় ব্যবহৃত একটি শব্দ বাগার্থকে ছাড়িয়ে বহুরৈখিক অর্থ ধারণ করে। আক্ষরিক অর্থের স্থানে ব্যঞ্জনাই কবিতার অনিবার্য অলঙ্কার হয়ে ওঠে। ‘ঘৃণা’ কবিতায় এসে জীবনের কর্মযজ্ঞের ভেতর স্মৃতি, ক্লান্তি আর স্বপ্নভঙ্গের বিষয়াবলিও সমান গুরুত্বে বিবেচ্য হয়ে উঠেছে।
পলকা হাওয়ায় উড়ছে বিষণ্নতা
এক দুপুরের সূর্য ঢাকা মেঘৰ
তোমার ভেতর এখন অন্য মনপপ
আমার ভেতর আমার সমর্পণ।
তবু ডালা খুলছে বিপন্নতা
কেমন করে থামাই স্মৃতির বেগ?
(ঘৃণা : অন্ধকার হে অন্তর্গত)
কবি নিজেকেই যেন প্রশ্ন করেন, যখন চরাচরের যাবতীয় দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরালে পরিবর্তন ঘটে, সে সঙ্গে একে অন্যের ভেতর নিজেকে বিলীন করে দেয়, তখন ব্যক্তি মানুষের অস্থিরতা বেড়ে চললে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে ঝলসে ওঠা স্মৃতির গতিবেগও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। এভাবেই অবসাদে নুয়ে পড়া মানুষের মনস্তত্ত্ব উপলব্ধির সূত্রবীজ হয়ে ওঠে কোনো কোনো মুহূর্তের বিশেষ কোনো স্মৃতিরও?
দ্বিতীয় কাব্য ‘নিভে আসে সূর্য সকাল’। প্রথম কবিতার নাম ‘বর্ষাগমন’। বর্ষার একটি বিশেষ মুহূর্তে মানবমনে যে চাঞ্চল্যের বেগ আসে সে অনুভূতিকে একটি বিশেষ তাৎপর্যে ধারণ করার চেষ্টা আছে এ কবিতায়।
বৃষ্টির সয়লাব স্রোতে ঝমঝম ঝাঁঝর
পিছলে কাদা-জলে কেটেছে অঙ্গুলি
বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে ধবল পাঁজর
আঁচলে টুপটাপ ঝরে আকাশ-আধুলী।
(বর্ষাগমন: নিভে আসে সূর্য সকাল)
বৃষ্টির সঙ্গে আধুলির তুলনায় উৎপ্রেক্ষার উৎপত্তি হয় সত্য; কিন্তু শেষপর্যন্ত চিত্রকল্পেই তার স্বস্তি ও উত্তরণ। সেলিনা শেলীর কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি শব্দকে অভিধান থেকে তুলে আনেন না। বরং দিনানুদিনের ভাষা-ই তাঁর কবিতায় রূপান্তরিত। এভাবে তিনি সমকালের সাধারণ বিষয়কেও কবিতা করে তুলতে জানেন। এ পর্বে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘দেখবো তোমার স্বপ্ন দহন’। এ কবিতায় মানবমনের নানা স্তরবিন্যাসকে একই সমান্তরালে বিচার করে আরাধ্য মানুষের সঙ্গে অভিমানের একটি সম্পর্ক রচনা করা হয়েছে, যেখানে স্বপ্নকে অমর ও মহিমান্বিতরূপে দেখেছেন কবি। ‘পরিচয়’ কবিতায় প্রথাগত ধর্মের প্রতি সংশয়ের প্রশ্নকে অনিবার্য করে তুলেছেন। সেখানে বাউল দর্শনের সঙ্গে কবিকল্পনা ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রসঙ্গকে অভিন্নার্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সুফিবাদের সঙ্গে এর খুব একটা মিল না থাকলেও সাংঘর্ষিক সম্পর্কও নেই তেমন। বিশেষত, লালনের সঙ্গে ধর্মভিত্তিক চেতনাটুকুর অন্বয় থাকলেও যেখানে এসে কবি বলছেন, ‘না মুসলিম না হিন্দু/ মানুষ কিনা তাও বোঝা গেলোনা’ সেখানে বাউল দর্শনের বিশেষত, লালন দর্শনের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।
‘ফেরা’ কবিতায় একজন বিশ্বনাগরিকের প্রতিচ্ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে মনোযাতনাকেও শৈল্পিক করে তুলেছেন কবি। সেখানে যখন তিনি উচ্চারণ করেন, ‘নিজেকে কিশোরী করে শার্ট খুলে উড়াবি আকাশে’ তখন স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের অবসিত মানসিকতার বিপরীতে বিলসিত ইচ্ছার বরমাল্য হয়ে ওঠে চিত্রকল্পময় পঙ্ক্তিটি। ‘যখন বিভীষণ বড়ই ভীষণ’ কবিতায় সামাজিক মূল্যবোধের প্রশ্নে সংস্কারাচ্ছন্ন দেবতানির্ভর সমাজব্যবস্থায় মানুষ যতই সভ্য হওয়ার ভান করুক, উপরিতলে; কিন্তু কবি উপলব্ধি করেন, ভেতরে ভেতরে প্রণয়ের মুদ্রা ছোঁড়ে পুরোহিত-সমাজ।
বাসনার পরিসমাপ্তি কখন ঘটে? প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির সামঞ্জস্য না ঘটলে কাক্সক্ষাপীড়িত মানুষের মনে চাঞ্চল্যের গতি বেগ পায়। সেখানে মনোবিকলনও অনেকাংশে প্রতিদিনের আচরণীয় বিষয়ে পরিণত হয়।
বাতাসের কানে, কানে কানে আমি
বলেছিলাম গতরাত্রে
ওরে হাওয়া শোন, কিশোরী তো নই
কাঁচুলি পরেছি গাত্রে।
(হাওয়ায় হাওয়ায়: নিভে আসে সূর্য সকাল)
উপর্যুক্ত পাঠোদ্ধারে ইচ্ছার অবদমনের সংকীর্ণ বৃত্ত ভেঙে বের হয়ে আসার কাক্সক্ষা প্রকাশিত। এ কাক্সক্ষা প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীলতার সকল অঞ্চলে জড়িত মানুষের।
চণ্ডীদাসের ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’, বাণীর প্রতিধ্বনি আবহমান বাংলা কবিতার সাধকগণ যুগযুগ ধরে করে আসছেন। আলোচ্য কবিও এর ব্যতিক্রম নন। গ্রন্থবিহীন ধর্মমানি কবিতায় নশ্বর পৃথিবীর নৈরাশ্যমূলক দৃশ্য ও দৃশ্যের নানা জটিল পরিক্রমা দেখে বিচলিত কবি। ফলে তাঁর কণ্ঠ ভেদ করে বের হয়ে আসে এমতো উচ্চারণ:
রেহেলে তোলা আত্মমগ্ন যন্ত্রণা নেই
ঈশ্বরকে মুক্তি দিলাম।
অবশেষে মানুষ হলাম।
(গ্রন্থবিহীন ধর্মমানি: নিভে আসে সূর্য সকাল)
যে সর্বশক্তিমানের প্রতি ভক্তিতে অধিকাংশই আচ্ছন্ন, সে ঈশ্বরকে তার কর্মযজ্ঞের বিবর থেকে এভাবে মুক্তি দেওয়া সম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব; সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্নদের পক্ষে কোনো কালেও সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর এ দ্বিতীয় কাব্যের নাম পড়ে মনে খটকা লাগে ‘নিভে আসে সূর্য সকাল’ কেন? তাহলে কবি কি নৈরাজ্যের জয়গান গাওয়ার মানসে এ কাব্য লিখেছেন? কিন্তু পুরো কাব্য পাঠে মনের সংশয় কাটে, কারণ পুরো কাব্যে ছড়িয়ে রয়েছে সৌন্দর্য ও আনন্দের এবং প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতিময় শব্দসমবায়। তাহলে এমতো নামাঙ্কনের সার্থকতা কী?
তার তৃতীয় কাব্য ‘চিতাচৈতন্যের গান’। এ কাব্য পূর্ববর্তী কাব্য দুটির অসংযত আবেগের স্থানে প্রগাঢ় অনুভূতিকে প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে বাকসংহতি ও বৈদগ্ধের স্বাক্ষর। পূর্ববর্তী কাব্য দুটিতে কবি ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে বাজাতে বাজাতে ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তায়ও আচ্ছন্ন ছিলেন। চিন্তার প্রাথমিক ও মধ্যম স্তরে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। সেখানে যুক্তির অনুশাসনকে গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু ‘চিতাচৈতন্যের গান’-এ এসে কবি যেন অনেকটা সমাজমুখী ও রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠেছেন। কবি উপলব্ধি করতে প্রাণিত হয়েছেন, যে সাহিত্য সমাজ ও মানুষের কাজে আসে না, সে সাহিত্য দীর্ঘায়ু হতে পারে না।
মানুষের তৈরি পৃথিবীতে বাস করে অলীক দেবতার গুণগানে সময় ব্যয় করাকে কবি ঘৃণার্হ করে তুলেছেন। তাই কবি মানবসভ্যতার যেকোনো অমঙ্গলজনক কর্মযজ্ঞের জন্য অলৌকিক কোনো শক্তিকে দোষারোপ করেন না। বরং আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রকে দায়ী করেন। ‘যাবে কি বেদনার বাড়ি ফের’ কবিতায় পাঠকের সামনে একটি অমোঘ সত্য হাজির করেন, ‘মনে রেখো, সিডরের ত্রাণে ভরা রণতরী ওরা/ যতটুকু হাত, দ্যাখো, নখ বড় তারও চেয়ে বেশি’। এ সত্য চিরন্তন। চিরকালই আধিপত্যবাদী শক্তি দুর্বলের ওপর সাহায্যের হাত বাড়ানোর আড়ালে লোভের ফাঁদও পেতে রাখে। যেমন গ্রামাঞ্চলে সমাজপতি মোড়ল, শহরের বহুতল ভবনের বাসিন্দা অভিজাত শ্রেণীর কামুক হাত এগিয়ে আসে অসহায় কোনো রমণীর দিকে।
‘চিরকাল বানান ভুল’, ‘অভিমান’, ‘জীবিকার তালু বেয়ে’, ‘ব্ল্যাকহোল’, ‘বেদনার বাড়ি’, ‘আত্মনিপীড়ন’, ‘ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি’, ‘শরীরযাপন’, ‘উচ্ছ্বাসী আবাহ’, ‘নপুংসক’, ‘রক্তের নুন থেকে তুলে আনি আলো’ ইত্যাদি কবিতায় যেমন ব্যক্তিমনের রক্তক্ষরণের নিবিড় পর্যবেক্ষণ রয়েছে, তেমনি রয়েছে অন্তর্গত ভুবন নির্মাণেরও নৈপুণ্য। গভীর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে সেলিনা শেলী লিরিকেই স্বাচ্ছন্দ্য।
নৈঃসঙ্গ মৃদঙ্গ বাজে দিগন্তের গাঁয়ে-চরাচরে
ভেতরে কি আছে কেউ? কে আছে ভেতরে?
শূন্যতার মেঘভারে অন্ধকার কাঁদে একা একা
স্ফটিক কাঁচুলি পরে জেগে থাকে নক্ষত্রবালিকা।
যতটা হরিৎ জানি, তার চেয়ে বেশি ঝরাপাতা
মাপজোক শেষ হলে পড়ে থাকে কবিতার খাতা
(সকলি শূন্য হে: চিতাচৈতন্যের গান)যে প্রেম রেখেছো জমা নোনা ছাদঘরে
চলো তাকে নিয়ে যাই মরণোত্তরে
উড়ে এসে দূরে বসে ড্রাইকেক মেঘ
যে তোমাকে নিতে চায় দিগন্তের গাঁয়ে
পারানির কড়িগুলো বাঁধো তার পায়ে
এ রতি-আরতি খেলা শিব-পার্বতীর
(ছাদঘর-২: চিতাচৈতন্যের গান)
উপর্যুক্ত পাঠোদ্ধারের প্রথম উদাহরণটি প্রচলিত অর্থেও একটি সার্থক লিরিক। কিন্তু দ্বিতীয়টি কি সে রকম কোনো লিরিক? এমন অমিল ও কূটাভাসে পূর্ণ পঙ্ক্তিগুচ্ছের আয়োজন কি লিরিক হতে পারে? প্রশ্ন আরও হতে পারে। কিন্তু লিরিক কোনো দৃশ্যগ্রাহ্য সমিল পঙ্ক্তিমাত্রই নয়। লিরিকের অন্তর্গত সুরই হলো এর প্রাণ। সে প্রাণ স্পষ্ট হয়ে আছে দ্বিতীয় উদাহরণেও। প্রথম উদাহরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কবিতার একটি অন্তর্গত সাদৃশ্য রয়েছে। ‘সোনার তরী’ কবিতায় শেষ আর্তনাদ, ‘ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই’, আর ‘সকলি শূন্য হে’ কবিতায়, ‘যতটা হরিৎ জানি, তার চেয়ে বেশি ঝরাপাতা/ মাপজোক শেষ হলে পড়ে থাকে কবিতার খাতা’ একই অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ সৃষ্টি যখন স্রষ্টার মহিমাকে ছাড়িয়ে যায় স্রষ্টার অস্তিত্ব সেখানে ম্লান হয়ে যায়। আবার স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, সে সম্পর্কের একটি প্রচ্ছন্ন ভাবও রয়েছে এ কবিতায়। দ্বিতীয় উদাহরণের ‘যে তোমাকে নিতে চায় দিগন্তের গাঁয়ে/ পারানির কড়িগুলো বাঁধো তার পায়ে’, পঙক্তি পড়ে মনে পড়ে যেতে পারে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘উটপাখী’ কবিতার সে পরার্থপরতার অমোঘ উচ্চারণ, ‘অতএব এসো আমরা সন্ধি করে/ প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি;/ তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,/ তোমাকে বন্ধু আমি লোকায়তে বাঁধি’। দুই যুগের দুই যুগসারথির উপলব্ধির অভিন্ন রূপ পাঠকের মনে ধাঁধার জš§ দেয় না, বিমোহিত করে। কী করে সম্ভব মহৎ কবিতে কবিতে এমন ভাবনার সমান্তরাল বিনিময়? কিংবা জসীমউদ্দীনের ‘আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর/ আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর’-এর মতো পরার্থপরতার সে অজর বাণীও সেই সঙ্গে স্মরণ করে নিতে পারি। এখানে প্রভাবের প্রসঙ্গ অবান্তর। এটি কোনো প্রভাবজনিত বিষয় নয়। এটি নিশ্চতরূপে বোধের সাদৃশ্য, চিন্তার ঐক্য, সুরের ঐকতান এবং চেতনার অভিন্ন রূপ।
তাঁর কবিতা উচ্চকণ্ঠের নয়, নিম্নকণ্ঠের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সংরাগ থাকা সত্ত্বেও ব্যঙ্গকবিতায় পর্যবসিত হয়ে যায় না। আবার অলস মস্তিষ্কেও তার একটি মৃদু সুর তোলে। সে সুর তাঁকে উদ্দীপিত করে না, বরং শান্ত ও সৌম্য রূপ নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে প্রান্তর ও প্রান্তের নানা দৃশ্য দেখে সে স্নিগ্ধতায় আকণ্ঠ ডুব দিয়ে থাকতে প্রলুব্ধ করে। সেখানে আকস্মিক উত্তেজনায় কেঁপে ওঠার মতো ব্যাপার ঘটে না। কোনো উচ্চকিত বিষয়ও সেখানে তাৎপর্য ধারণ করে না।
বিষয়ভাবনায় সেলিনা শেলী রবীন্দ্রনাথের মননসঙ্গী। বিশ্বচরাচরের যা-কিছু কবিমনে আলোড়ন তুলতে সক্ষম, তার সবই কবিতার রসায়ন হয়ে উঠতে পারে। চিন্তার জটাজালে তিনি বিভ্রান্ত নন। স্বচ্ছতা ও বোধের অধিগম্য প্রকাশ প্রকরণই তাঁর আদর্শ। চিত্রকল্পে তিনি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। চিত্রকল্পকে দৃষ্টির স্নিগ্ধতায় উপস্থাপন করেন না। বোধের অলিন্দেই তাঁর উৎসারণ। এদিক থেকে তাঁর কবিতা দৃষ্টিকে ঘোলা করে না, মনকে আলোড়িত করে। বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজে নিছক চিন্তার তারল্যপূর্ণ কথার গুঞ্জন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। হয়তো তাই কবিতাবিমুখ মানুষের কাছে আজ কবিতা দুর্বোধ্য ও জটিল। এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতাকে দুর্বোধ্য বলতে চান, তাঁদেরও আলোচ্য কবির কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনার সুযোগ নেই। তাঁর কবিতার ব্যাখ্যা কখনোই একরৈখিক হয়ে ওঠে না। উত্তরাধুনিক কবিতার প্রবণতাও সে সাক্ষ্য বহন করে। এ অর্থে তাঁর কবিতা উত্তরাধুনিকও। আবার পরাবাস্তব চিত্রও তাঁর কবিতায় সংক্রমিত, সে অর্থে তাঁর কবিতা পরাবাস্তবও। এত সব তত্ত্ব ও মতবাদের ভিড় উজিয়ে সাদা কথায়, সেলিনা শেলীর কবিতা চিন্তার ভরকেন্দ্রে একটি চিন্তনরেখা এবং কল্পনার অলিন্দে মৃদু ঢেউ তোলা একগুচ্ছ রোদের কণা, যা থেকে ঠিকরে বের হয় প্রতিদিনের প্রথম সূর্যোদয়ের আলোকচ্ছটা।