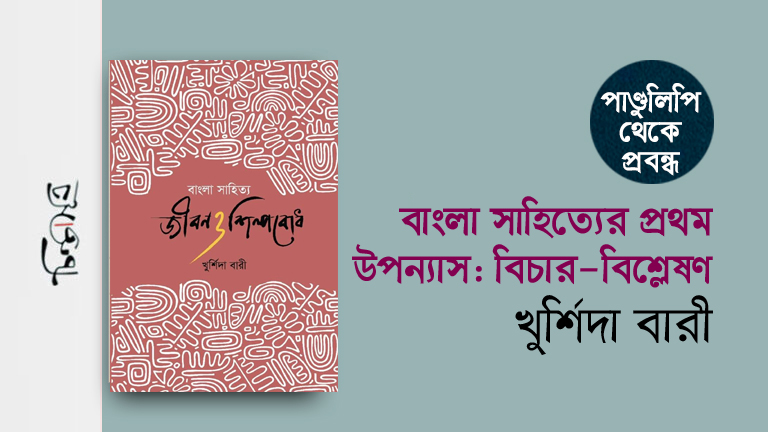বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে আলালের ঘরে দুলাল স্বীকৃত। আলালের ঘরে দুলাল-এর আগে প্রকাশিত হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্সের ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ও একবছর পরে প্রকাশিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের বিজয়-বসন্ত প্রথম উপন্যাস হিসেবে কেন মর্যাদা লাভ করেনি, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে।
রচনাকালের দিক দিয়ে হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্সের ফুলমণি ও করুণার বিবরণ প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরে দুলাল-এর আগে প্রকাশিত। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে। আলালের ঘরে দুলাল প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। আর কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের বিজয়-বসন্ত প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। এইদিক বিবেচনা করলে ফুলমণি ও করুণার বিবরণ অগ্রাধিকার পায় এবং পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের গৌরব হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্সের প্রাপ্য।
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ উপন্যাসে হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্স কয়েকটি খ্রিষ্টান ধর্মান্তরিত বাঙালি পরিবারের জীবনযাত্রার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। ম্যুলেন্সের ভাষা কেরীর কথোপকথন ও বাইবেলের অনুবাদের মিশ্রিত রূপ। এতে দেশীয় নিম্নশ্রেণির লোকের কথ্যরীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের সাথে সাথে খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থের বৈদিশিকপন্থী বাগ্ধারার প্রচুর সংমিশ্রণ দেখা যায়। ম্যুলেন্স ফুলমণি ও করুণার গার্হস্থ্যজীবনের বিপরীতমুখী চিত্র অঙ্কন করেছেন। ফুলমণি মনে প্রাণে খ্রিষ্টধর্মানুরাগী। তার স্বামী ও ছেলেমেয়েরাও অনিন্দ্যনীয় চরিত্রের অধিকারী ও তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক সহৃদয়পূর্ণ এবং একই আদর্শের অনুসারী। পক্ষান্তরে করুণা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও এতে তার আস্থা নেই। তার স্বামী অন্যাসক্ত, মাতাল ও দায়িত্বহীন। তার দুই ছেলে-মেয়ের মধ্যে এক ছেলে চোর, অন্য একজন কুপথগামী হতে হতে সৎসংসর্গের প্রভাবে পাপের কবলমুক্ত। করুণা নিজে আত্মসম্মানহীন, ইতর, কলহপ্রবণ। শেষ পর্যন্ত লেখিকার আন্তরিক চেষ্টায় খ্রিষ্টধর্মের জীবনীর পৌণঃপুনিক প্রচারে ও তার জ্যেষ্ঠ্য পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে তার মনে আত্মগ্লানির আগুন জ¦লে ওঠে এবং তার চরিত্র সংশোধিত হয়।
প্যারীচাঁদের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার কয়েক বছর আগে ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর মুদ্রণ সমাপ্ত হয়। দেশীয় খ্রিষ্টান স্কুলে এটি পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচারিত হয়েছিল। খ্রিষ্টান পরিবার সংক্রান্ত ঘটনাই প্রধান হওয়ায় বাঙালি পাঠক সমাজে এর বিশেষ প্রচার হয়নি এবং লেখিকা সম্বন্ধেও কেউ কৌতুহলী হননি। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে, ম্যুলেন্স অতি চমৎকার বাংলা ভাষা আয়ত্ত করলেও উপন্যাস বা কথাশিল্পের সাথে বিশেষ পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এই নিরস দীর্ঘ কাহিনি কোনোদিক থেকেই হিন্দু পাঠকসমাজের কাছে চিত্তাকর্ষক হতে পারেনি। তার তুলনায় কিছু পরে লেখা প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল সরস কাহিনি সৃষ্টিতে অনেক বেশি সার্থক হতে পেরেছে। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনির স্ফূরণ হলেও তার শিল্পলক্ষণ নামমাত্র। তাই আলালের ঘরে দুলাল-ই প্রথম বাংলা উপন্যাসের গৌরব শিরে ধারণ করে আছে। তাছাড়া ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ম্যুলেন্সের মৌলিক রচনাও নয়, একটি ইংরেজি গ্রন্থের মর্মানুবাদ।
কলকাতার সমকালীন সমাজচিত্র আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থের বিষয়বস্তু। উচ্চবিত্ত ঘরের আদুরে সন্তান মতিলালের পদস্খলন ও শেষে সৎপথে ফিরে আসা উপন্যাসটির মূল প্রসঙ্গ। ঘটনাগুলো মতিলালকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ঠকচাচা নামক চরিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। কাহিনির উত্থান-পতনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গেছে ঠকচাচা’র হাতে। সুকুমার সেন মনে করেন, ‘কিন্তু ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে প্রধানত ঠকচাচার দ্বারা। সেদিক দিয়ে দেখিলে ঠকচাচাই আসল নায়ক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম অমর চরিত্র ঠকচাচা।’
বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সরল ও সতেজ কথ্যভাষা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তনের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। এদিক দিয়ে তিনি তীক্ষè মননশক্তি ও স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস রচনার জন্য যতটা না হোক, ভাষা-সংস্কার প্রচেষ্টার জন্যই বিশেষভাবে তিনি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিষয়ে উপযোগিতা অনুসারে এই কথ্যভাষায় মাত্রাভেদ ও তারতম্য নির্ধারণ করার মতো সচেতন মন তাঁর ছিল।
উপন্যাসের সব লক্ষণের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ছয়টি বৈশিষ্ট্য: কাহিনি, চরিত্র, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বাস্তবতা ও স্থানীয় পরিবেশ, সংলাপ, ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন। প্যারীচাঁদ মিত্র কাহিনি গ্রন্থনে (উপন্যাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত) খানিকটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কলকাতার সমাজের উচ্ছৃখলতা ও অনাচার বর্ণনায় তিনি যে ধরনের সরস কৌতুকরীতি ব্যবহার করেছেন, তার জন্যই তিনি অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছেন। তা না হলে চরিত্রসৃষ্টি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণÑ এসবের বিশেষ কোন পরিচয় তাঁর উপন্যাস থেকে পাওয়া যায় না। সুনীতি, চারিত্রিক আদর্শ ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের নীতি ও আদর্শ প্রচারে তাঁর ঝোঁক এত বেশি ছিল যে, এর কাহিনি বা চরিত্রে কথাসাহিত্যের লক্ষণ ফুটে উঠতে পারেনি। তাঁর চরিত্রগুলো হয় পুরোপুরি সৎ, আর না হয় ষোল আনা ঠক-প্রবঞ্চক। এরকম একপেশে চরিত্র উপন্যাসের আবহাওয়াকে বড় কৃত্রিম করে তোলে। নীতিমার্গীয় লেখক প্যারীচাঁদের অধিকাংশ চরিত্রের এই হলো মারত্মক ত্রুটি। কিন্তু দু-চারটি খলচরিত্র তাঁর হাতে চমৎকার খুলেছে। বাবুরাম বাবু, ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, মতিলালÑ এই চরিত্রগুলো অধিকাংশ সময়ের ‘টাইপ’ ধরনের হলেও সরসতা ও কৌতুকের দ্বারা লেখক তাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। প্যারীচাঁদ আদর্শবাদী মহৎ চরিত্রের চেয়ে বক্রচরিত্রেই অধিকতর তৃপ্তি বোধ করতেন। তাই বাস্তবতার সঙ্গে সরসতা কৌতুকের সঙ্গে ব্যঙ্গ তাঁর রচনা ও চরিত্রাঙ্কনে একটা স্থায়ী গৌরব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতা ও শহরতলীর চিত্র এই উপন্যাসে আশ্চর্য নিপুণতার সাথে চিত্রিত হয়েছে। প্যারীচাঁদের যা কিছু গৌরব তা শুধু আলালের জন্যই। আলালের হালকা চালের কলকাতার ভাষা ‘আলালী ভাষা’ নামে পরিচিত। প্যারীচাঁদ মনে করতেন, এই চলিতঘেষা আধা সাধুভাষা, যাতে বহু স্থলে চলিত-সাধু-অসাধু উপভাষার বিচিত্র জগাখিচুড়ি তৈরি হয়েছে। এই ভাষাই নাকি কথাসাহিত্যের আদর্শ ভাষা। বিদ্যাসাগরীয় ক্লাসিক-ঘেষা গম্ভীর বাক্রীতি ঠিক উপন্যাসে উপযোগী নয়। বিদ্যাসাগরীয় পরিচ্ছন্নতা ও ক্লাসিক গাম্ভীর্য এবং আলালী সরসতার সমন্বয়ের ভাষাই কথাসাহিত্যের যথার্থ বাক্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা-খনি হাতে নিয়ে কথাসাহিত্যের উপল-ঊষর ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এবং রসের ধারা বইয়ে দেন। তবে একথা ঠিক, প্যারীচাঁদ সর্বপ্রথম সহজ মানুষের দুষ্টু, খল চরিত্রের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়ে উপন্যাসের বাস্তবতার পথ তৈরি করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিতভাবে যা বলেছেন তার উচ্ছ্বাসটুকু বাদ দিলে প্যারীচাঁদের সমগ্র সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত মনে হবে:
তিনিই সর্বপ্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা করতে হয় না। তিনিই সর্বপ্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালাদেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।
প্যারীচাঁদের ভাষারীতির দৃষ্টান্ত:
১. ভবানীবাবু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠতে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন। লঙ্গি বাবুদের বরাবার মিছরি খাইয়া মুখ খারাপ হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগবে কেন? সুতরাং তাহারা ক্রমে ২ ছটকে পড়িতে লাগিল। [মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়]
২. বাবুরামবাবু চৌ গোঁপপা নাকে তিলক—কাস্তাপেড়ে ধুতি পড়া—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মতো— কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—এতগাল পান—ইতস্তত বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন, ওরে হরে! শীঘ্র বালি বাইতে হইবে, দুইচার পয়সার একখানা চলতি পানসি ভাড়া কর তো! বড় মানুষের খানসামার মধ্যে বে-আদব হয়। হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড, ভাত খেয়ে বস্তেছিনু—ডাকা-ডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেছি।… চল্তি পানসি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—একি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা? [আলালের ঘরের দুলাল]
এই ভাষা পুরোপুরি চলিত ভাষা নয়, মূল ঠাট-টা সাধুভাষার ছাঁদ অনুসরণ করেছে, কিন্তু লেখক নাটকীয় প্রয়োজনে ভাষাকে তীর্যক ও চরিত্রানুরূপ রূপ দিয়েছেন। অবশ্য অনেক সময় চলিত ও সাধুভাষার সংমিশ্রণও করে ফেলেছেন, যেটা সেকালের প্রায় সকল বাঙালি লেখকের মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছিল। অন্তত রবীন্দ্রনাথের পূর্বপর্যন্ত বাঙালি কথাসাহিত্যিকেরা সাধু ও চলিতরীতির বর্ণনা ও সংলাপের পার্থক্য সম্বন্ধে সবসময়ে সচেতন থাকতেন না। যাই হোক, প্যারীচাঁদের উল্লেখিত দৃষ্টান্ত দুটি যে সহজে সরল ও চলতি জীবনের উপযোগী তাতে কোন সন্দেহ নেই।
তবে, প্যারীচাঁদ অবলম্বিত ভাষারীতি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হলেও এর ন্যূনতা এবং দুর্বলতা বিষয়েও আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর ভাষা অনেকের দ্বারা সমকালে প্রশংসিত হলেও একালে আমরা যখন ভাষারীতির বিশুদ্ধতার বিষয়ে বেশি সচেতনতা লাভ করেছি তখন প্যারীচাঁদের ভাষারীতিতে সামঞ্জস্যতার অভাবকে কিছুটা পীড়াদায়ক বলেই মনে হয়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় (২য় খণ্ড) গ্রন্থে এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন:
প্যারীচাঁদ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সাধুরীতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে তৎসম শব্দের পরিবর্তে প্রচুর দেশী-বিদেশী শব্দের, বাঙলা বিশিষ্ট বাগভঙ্গি এবং কথোপকথনের মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে, এর ফলে বহু স্থলেই সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটেছে এবং পরিমিতি বোধের অভাব ঘটেছে। প্যারীচাঁদ সাধু ভাষার কাঠামোতে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেন এবং চলিত ভাষার শক্তি পরীক্ষা করেন। মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে ভাষায় আমাদিগের সচারাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।
কিন্তু বাস্তবে উনি অপর সকল গ্রন্থ, এমনকি উপন্যাসেও সাধুরীতির ব্যবহার করেছেন। ‘মদ খাওয়া বড় দায়’ গ্রন্থের ভাষাও সাধুরীতির অনুসারী। প্যারীচাঁদের ভাষা বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুটি চরমপন্থী অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্যের গঠনে সাধুরীতির ব্যবহার করতে গিয়েও প্যারীচাঁদ অনেক সময়ই রীতি লঙ্ঘন করেছেন, ফলে তা কখনো আদর্শ ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। তবে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট প্রাণশক্তির আবিষ্কারে তিনি যে তৎপর ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা বাগধারা, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বিত এবং বাগরীতির ব্যবহারে।
উপন্যাসের কাহিনি-নির্মাণে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সমাজের বিভিন্ন খণ্ডচিত্রগুলো নিপুণ দক্ষতার সাথে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া সেসময়ের সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার রচনারীতির ধারা থেকে বের হয়ে এসে প্রথমে চলিতরীতিতে সাহিত্যরচনা প্রশংসার দাবি রাখে। সক্রিয় সত্তায় ভাস্বর এই সাহিত্যকর্মে তিনি শিল্পনৈপুণ্য ও রচনাশৈলী প্রদর্শন করেছেন তা পরবর্তীতে আধুনিক উপন্যাসের পথকে মসৃণ করেছে।
১৮৫৯ সালে প্রকাশি বিজয়-বসন্ত করুণ রসে সিক্ত নারী-অনুকূল কথাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর মধ্যে একটা সম্মিলিত কাব্যাভাস রয়েছে বলে গদ্যটি যে সুপাঠ্য এবং গতি-বাক্যে মসৃণ, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। এতে করে যথার্থ অনুমান করা যায়, বিজয়-বসন্ত যথার্থই পদ্য থেকে গদ্যে রূপান্তরিত হয়েছে।
জয়পুর রাজ্যের রাজা জয়ের দুই পুত্র বিজয় ও বসন্ত। ছোটবেলায় মা মারা যায়। দাসী শান্তার কাছে তারা বড় হতে থাকে। একদিন বিমাতার মিথ্যা অপবাদের শিকার হয়ে রাজা কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু মন্ত্রী কৌশলে তাদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। যেতে যেতে তারা সেখান থেকে দৈবক্রমে চলে যায়, দুই ভাই আলাদা হয়ে যায়। অনেক দুঃখ-কষ্ট-মানসিক পীড়ন শেষে দুই ভাই দুজনকে ফিরে পায়। পরে নিজ রাজ্যেও ফিরে আসে।
জনপ্রিয়তার দিক থেকে আলালের ঘরের দুলাল থেকে বিজয়-বসন্ত এগিয়ে কিনা সে দাবি হুট করে উড়িয়ে দেয়া যায় না। জনপ্রিয়তার তুঙ্গ বলতে যা বোঝায় সে সমৃদ্ধিকে কাঙালের বিজয়-বসন্ত যে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল, সে কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বিজয়-বসন্ত এক সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. শ্রেণির পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। বিজয়-বসন্ত’র প্রভাব অনুকরণে সমকাল ও উত্তরকালে বেশ কয়েকটি পুস্তক রচিত হয়, এর মধ্যে নাটক বা যাত্রাপালায় রূপান্তরিত রসরাজ অমৃতলাল বসু’র (১৮৫৩-১৯২৯) নাটক ‘বিজয়-বসন্ত’ এবং পাংশা থানার ভাতশালিনী’র মতিলাল রায় প্রণীত ‘বিজয়চণ্ডী’ (কলিকাতা, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) গীতাভিনয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। ‘বিজয়চণ্ডী’র বিজ্ঞাপননামীয় ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন:
কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার প্রণীত বিজয়-বসন্ত নামক করুণরসপূর্ণ সুললিত কাব্যের অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।
বিজয়-বসন্ত বিশেষ সমাদর ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জানা যায়, এই গ্রন্থের কুড়িটিরও অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নিতান্ত শিশুপাঠ্য বর্ণবিষয়াদি ভিন্ন অন্য কোনও বাংলা গ্রন্থের এরূপ বহুলপ্রচার হয়নি এবং পল্লিবাসী সাহিত্যসেবকের কোনও গ্রন্থ এরূপ সমাদার লাভ করেনি। (কাঙাল হরিনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রের সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৩: ২২)
এতে করে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিজয়-বসন্ত কাঙাল হরিনাথের কি অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তির পরিচয় পেয়েছিল। তার শৈল্পিক প্রতিভার এই বিচ্ছুরণ এইসব যথাযথ কারণেই ‘নীতিগর্ভ অপূর্ব উপাখ্যান’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ১৮৫৯ (১০ পৌষ ১৭৮১ শক) সালে কলকাতার শ্রী লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং থেকে সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে যে বিজয়-বসন্ত প্রকাশিত হয়েছিল তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১০৫।
কাঙাল হরিনাথের মৃত্যুর প্রকাশিত বিজয়-বসন্ত গ্রন্থের কোনো এক সংস্করণের নিবদনে রায়বাহাদুর জলধর সেন জানিয়েছেন:
কাঙাল হরিনাথ বিজয়-বসন্ত নামক সর্ব্বজন পরিচিত উপন্যাসের ত্রয়োদশ সংস্করণ অনেকদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়া গেলেও এতদিন নানা অসুবিধায় তাহার আর সংস্করণ হয় নাই। কিন্তু এখন অনেকেই কাঙালের বিজয়-বসন্ত পাঠ করিবার জন্য অত্যাধিক আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি এই পুস্তকখানির পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করিয়াছি এবং পূর্ববর্ত্তী কয়েকটি সংস্করণের অসাবধানতাবশত যে সমস্ত ভ্রম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।
কাঙাল সর্ব্ব বিষয়েই কাঙাল ছিলেন, তাঁহার যেরূপ বাহ্যপরিপাট্যের দিকে দৃষ্টি ছিল না, তাঁহার গ্রন্থাবলিও তেমনই যেমন তেমনভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। কিন্তু এখন ত আর সেদিন নাই; এমন ভাল জিনিষেরও বাহ্যশোভাবর্ধন করিতে হয়। তাই আমরা এবার বিজয়-বসন্ত এই নূতন সংস্করণে ভাল কাগজ দিয়াছি, ছাপা ভাল করিবার চেষ্টা করিয়াছি স্মলপইকা না দিয়া পইকা দিয়াছি। আরও এক কাজ করিয়াছি, শুনি, এখন ছবি না দিলে বই কাটে না, তাই এই পুস্তকে তিনখানি ছবি দিয়াছি। যে পুস্তকের তেরটি সংস্করণ বিনা বিজ্ঞাপনে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার এই নূতন সংস্করণও কাটবে বলে আমার বিশ্বাস। (কুমারখালী, ১লা অশ্বিন, ১৩২১, শ্রী জলধর সেন)
এইসব আলোচনায়, উদ্ধৃতিতে, বিশ্লেষণে বিজয়-বসন্ত’র জনপ্রিয়তা, চাহিদা, সাহিত্যমূল্য নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯) ছিলেন কাঙাল হরিনাথের সাহিত্য-সাগরেদ এবং গুণমুগ্ধ কাছের মানুষ। তিনি বিজয়-বসন্ত বিষয়ে উপর্যুক্ত মন্তব্য ব্যক্ত করেছিলেন ১৩২১ সনে। কিন্তু তারও একযুগ আগে, ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হরিনাথ গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে জলধর সেন ভূমিকায় লিখেছিলেন:
যখন দয়ার সাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সুললিত বাঙালা গদ্যে পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন, সেই সময়ে নদীয়া জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বিজয়-বসন্ত রচনা করেন। হরিনাথ ইংরেজি জানিতেন না। ইংরেজি গ্রন্থের কোনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পুস্তক লেখা তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি প্রতিভাবলে সেই সময়ে বিজয়-বসন্ত প্রকাশিত করিয়া পাঠক সমাজের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলিতে কি তাঁহার এই পুস্তকে এক শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে মৌলিকতা, মধুরতা ও প্রকৃত কাব্যগুণে যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছিল।
জলধর সেনের এই লেখাটির মনোভাব এবং একই পুস্তক বিষয়ে এর একযুগ আগে লেখা ‘নিবেদন’ এর মনোভাব লক্ষ করলে স্পষ্টতই অনুভব করা যায় যে, তার পুস্তকধারণা এবং ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ পেয়েছিল।
বিজয়-বসন্ত’র বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বলার সাথে তৎকালীন সমসাময়িকতার সাথে প্রয়োজনীয় আধুনিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল যার জন্য বইটি সবশ্রেণির পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। সে আমলেই বিশটি সংস্করণ প্রকাশ হয়েছিল। সততার প্রশ্নে অনুমান করা যায়, সেই আমলে সংস্করণ বলতে আদর্শ নির্দেশিত সংখ্যক বই নিয়েই এক একটি সংস্করণ। সে আমলে ১২৫০ সংখ্যায় এক সংস্করণ হতো বলে জানা যায়। অর্থাৎ ২০ সংস্করণে কম করে ২৫০০০ কপি বই। বর্তমানের তুলনায় তখন বাঙালির বইবাজারের পরিধি ছিল অনেক সংকুচিত। সে তুলনায় শতাধিক বছর আগে বিজয়-বসন্ত’র কুড়িটি সংস্করণ মুদ্রিত হওয়া নিশ্চয়ই যাই-তাই ব্যাপার ছিল না। নিতান্ত শিশুপাঠ্যের মতো ঘরে ঘরে না হলেও এই বই ব্যাপক বিক্রির সামগ্রী হতে পেরেছিল তা সত্য এবং বিস্ময় উদ্রেগকারী। জানা যায় এর প্রথম সংস্করণের একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।
আসলেও এই গ্রন্থে যে স্ত্রীশিক্ষা, নারীভাবনা, সমাজবাস্তবতা এবং প্রত্যাশা ও স্বপ্ন নির্মাণের সৃজনশীলতার সাহিত্যবৈভব চয়িত হয়েছে, তা রচনা হিসেবে এবং রচয়িতা হিসেবে যথাক্রমে বিজয়-বসন্ত ও কাঙাল হরিনাথ মজুমদার আবশ্যিকভাবে প্রশংসার দাবিদার। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র বা কারণ রয়েছে এই উপন্যাসে, যা না থাকলে বা যাকে সামান্য বৈমূর্তে উপস্থাপন করলে একে নিঃসন্দেহে শিশুসাহিত্য পর্যায়ে ফেলা যেত। শিক্ষাবিদ, লেখক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক এবং ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের (বোম্বাই) সভাপতি রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮০-১৯৬১) বিজয়-বসন্ত’র মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, ‘গ্রন্থখানিকে যথার্থ শিশুসাহিত্যভুক্ত করার পক্ষে কয়েকটি আপত্তি থাকলেও বাংলার শিশুপাঠ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানিকে প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।’
এর আগে বলা হয়েছে, আলোচ্য বিজয়-বসন্ত প্রভাবিত এবং সেটি অনুকরণ করে সমকালে ও উত্তরকালে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, অমৃতলাল বসুর ‘বিজয়-বসন্ত’ (নাটক), মতিলাল রায়ের ‘বিজয়চণ্ডী’ ইত্যাদি। অসমর্থিতসূত্রে আরেকটি তথ্য জানা যায় যে, ছায়াছবির নির্বাক যুগে কাঙাল হরিনাথের এই গ্রন্থের কাহিনি অবলম্বনে ‘বিমাতা’ নামক একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এটিও একটি উল্লেখযোগ্যসূচক যে, বিজয়-বসন্ত এতোটাই জনপ্রিয় এবং ব্যাপক নন্দিত হয়েছিল যে, তার কাহিনি নিয়ে কেবল নাটক, যাত্রাপালাই রচিত হয়নি, সাথে সাথে সিনেমাও তৈরি হয়েছিল।
কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের উপন্যাস বিজয়-বসন্ত সাহিত্যবিচারে একটি প্রাঞ্জল এবং সাধারণ কাজ। কিন্তু এর রচনাকাল, রচয়িতা এবং সেই অনাগ্রসর সময়ে তার বিবেচিত বিষয়কে গভীর বীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের এই রচনা সৃষ্টি নিদর্শন হিসাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, উপন্যাসশিল্পের ঊষাকালে এর উন্মেষ ঘটেছিল।
আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থটির আগে না পরে প্রকাশিত হয়েছে, এই নিয়ে নানারকম মতামত আছে। আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থটিকে প্রায় সব পণ্ডিতই বাংলা সাহিত্যে ‘প্রথম পূর্ণাবয়ব’ উপন্যাস হিসেবে দাবি করেছেন এবং এর চরিত্রচিত্রণ দক্ষতা, কাহিনি বুননকৌশলসহ ব্যবহৃত ভাষাশৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, আলালের প্রশংসা করার মত অনেককিছুই আছে; যা সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী রচনাগুলোতে নেই। সেই কালে এবং পরিবেশে রচিত গ্রন্থটি নিশ্চয়ই এটি ফুল-চন্দন পাওয়ার যোগ্য। আলালের আগে কোন গ্রন্থটি এতটা আঙ্গিক-বিচারে সুসজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। গ্রন্থটি প্রথমে ১৮৫৪ সালে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে উপন্যাসটি পণ্ডিতদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলে সবাই স্বীকার করে নেন।
কিন্তু আলালের ঘরের দুলালকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করতে আপত্তি জানিয়েছেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি মনে করেন, কুষ্টিয়ার কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার প্রণীত বিজয়-বসন্ত বাংলার প্রথম উপন্যাস। শাস্ত্রী মহাশয় হরিনাথ মজুমদারের বিজয়-বসন্ত সম্পর্কে বলেছিলেন:
কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত ‘বিজয়-বসন্ত’ ও টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বাঙ্গারার প্রথম উপন্যাস। তন্মধ্যে বিজয়-বসন্ত তৎকালে প্রচলিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতিবহুল বাঙ্গালে লিখিত। (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং; পৃ ১৩১)
ধর্তব্য হলো, শিবনাথ শাস্ত্রী অন্য কারো মতো এককভাবে বিজয়-বসন্তকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে দাবি করেননি। কারণ হলো বিজয়-বসন্ত প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৫৯ সালে। পক্ষান্তরে আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৮ সালে। প্রকাশকাল হিসেব করলে হ্যানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্সের ফুলমণি ও করুণার বিবরণ প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা পায়। দীর্ঘ আখ্যান রূপকথার ঢঙে রচিত বিজয়-বসন্ত উপন্যাস হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। পণ্ডিতেরা তাই এটিকে উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নন।
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ গ্রন্থটি আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থের আগে প্রকাশিত হয়েও যে কারণে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি; ঠিক একই কারণে বিজয়-বসন্ত গ্রন্থটি আলালের ঘরের দুলাল-এর একবছর পরে প্রকাশিত হয়েও গুণগত মানে উন্নত না হওয়ায় প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা পায়নি। বিজয়-বসন্ত গুণগত মানে আলালের ঘরের দুলাল-এর চেয়ে উন্নতমানসম্পন্ন হলে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা লাভের সুযোগ বা সম্ভাবনা ছিল।
উপন্যাসের বিষয়বস্তু, সংলাপ, চারিত্র্যবিচার, সমাজ-সমকাল, অর্থনৈতিক অবস্থা, লেখকের দর্শন ও ভাষাশৈলীÑ এসবের বিচারে আলোচ্য তিনটি উপন্যাস ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, আলালের ঘরের দুলাল ও বিজয়-বসন্ত-এর কোনোটিই পরিপূর্ণ সার্থক উপন্যাস হিসেবে মর্যাদা লাভ করেনি। কিন্তু তারপরও উপন্যাসের বিভিন্ন গুণবিচারে ত সকল সাহিত্যবোদ্ধা ও পণ্ডিতেরা আলালের ঘরের দুলালকে অপেক্ষাকৃত এগিয়ে রেখেছেন। সেকারণে এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদায় স্বীকৃত হতে পেরেছে।