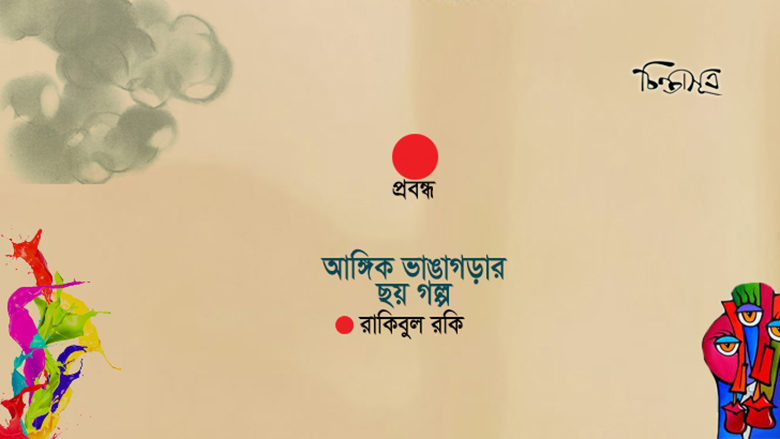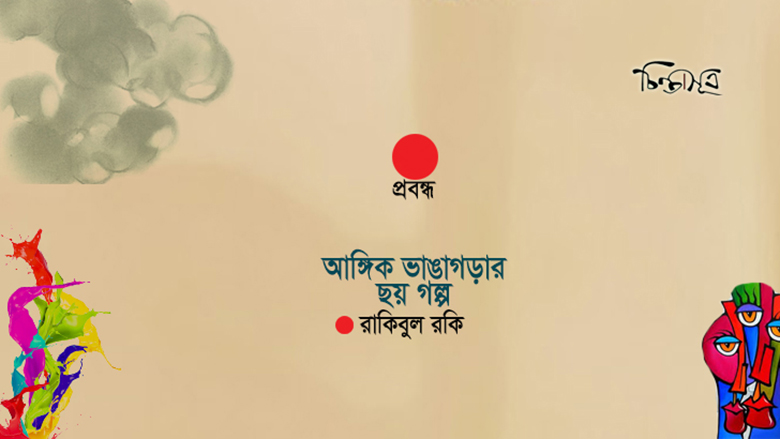 হুমায়ূন আহমেদ একদিন মুহম্মদ জাফর ইকবালের কাছে গিয়ে বললেন, পৃথিবীর সব গল্প বলা হয়ে গেছে। তখনো দু’জনের কেউই লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেননি। মুহম্মদ জাফর ইকবাল তার এক লেখায় ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন। উল্লেখ করার কারণ তার মতে, পৃথিবীর সব গল্প কখনো বলে শেষ করা সম্ভব নয়। সেটা তিনি তার লেখায় প্রমাণ করে দেখিছেনও। বইটি এই মুহূর্তে হাতের কাছে না থাকায় লেখার কোনো অংশ উদ্ধৃত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমাদের জীবনের যে নিত্যনতুন ঘটনা ‘প্রত্যহ যেতেছে ভাসি’, তা লিখে শেষ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলি, সবাই ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পে অনেক কিছুই আছে। তবে মি-টু নেই। বর্তমানে যে ‘মি-টু’ নামের যে মুভমেন্ট বা আন্দোলন পৃথিবীতে ঝড় তুলছে, একবছর আগেও বিষয়টি কেউ চিন্তা করেনি। ফলে আজকের গল্পতেই বিষয়টি উঠে আসবে, গতকাল এই গল্প বলা কখনোই সম্ভব ছিল না।
হুমায়ূন আহমেদ একদিন মুহম্মদ জাফর ইকবালের কাছে গিয়ে বললেন, পৃথিবীর সব গল্প বলা হয়ে গেছে। তখনো দু’জনের কেউই লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেননি। মুহম্মদ জাফর ইকবাল তার এক লেখায় ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন। উল্লেখ করার কারণ তার মতে, পৃথিবীর সব গল্প কখনো বলে শেষ করা সম্ভব নয়। সেটা তিনি তার লেখায় প্রমাণ করে দেখিছেনও। বইটি এই মুহূর্তে হাতের কাছে না থাকায় লেখার কোনো অংশ উদ্ধৃত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমাদের জীবনের যে নিত্যনতুন ঘটনা ‘প্রত্যহ যেতেছে ভাসি’, তা লিখে শেষ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলি, সবাই ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পে অনেক কিছুই আছে। তবে মি-টু নেই। বর্তমানে যে ‘মি-টু’ নামের যে মুভমেন্ট বা আন্দোলন পৃথিবীতে ঝড় তুলছে, একবছর আগেও বিষয়টি কেউ চিন্তা করেনি। ফলে আজকের গল্পতেই বিষয়টি উঠে আসবে, গতকাল এই গল্প বলা কখনোই সম্ভব ছিল না।
কথাগুলো বলার কারণ সমকালীন গল্পের গুরুত্ব সবসময় অন্যরকম। যদিও সমকালীন শব্দটি কিছুটা গোলমেলে। তারপরেও বলা যায়, বর্তমান সময়ের নতুন লেখকরা কী ভাবছে? কিভাবে ভাবে ভাবছে এবং সেটার প্রকাশ কেমন, তা জানার জন্য সমকালীন গল্পের গুরুত্ব অন্যরকম।
ওয়েবম্যাগ ‘চিন্তাসূত্র’ সমকালীন গল্প শিরোনামে নতুন আঠারো গল্প প্রকাশের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মধ্যে ছয়টি গল্প ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।
গল্পগুলো হলো:
সম্মিলিত মৃত্যুর পর ॥ সুবন্ত যায়েদ
ইন্টারভিউ ॥ শিল্পী নাজনীন
বৃত্ত ॥ সানাউল্লাহ সাগর
কয়েদি নম্বর-৩৩২ ॥ শারমিন রহমান
কানার হাটবাজার ॥ হুসাইন হানিফ
লালবেজি ॥ শীলা বৃষ্টি
প্রকাশিত ছয়টি গল্পই বিষয়-বৈচিত্র্যে, চরিত্র নির্মাণে, আঙ্গিক ও প্রকরণে আলাদা। গল্পগুলো পর্যালোচনা করলেই বিষয়গুলো অনুধাবন করা যাবে।
বর্তমানে আমাদের সাহিত্যের বিষয় শহরকেন্দ্রিক হলেও একসময় তা গ্রামের জল-হাওয়াতেই বিকশিত হয়েছে। শারমিন রহমান গ্রামের মানুষের জীবন-যাপনকেই তার লেখার উপজীব্য করেছেন সবসময়। ‘কয়েদি নম্বর৩৩২’ গল্পটি গ্রামের একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীর আত্মকথন।
বকুল অনেকদিন পর তার বাপের বাড়িতে নায়র আসে। বিয়ের পর তার স্বামী তাকে বাবার বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছিল। অনেক বছর চলে যাওয়ার পর যখন বকুলের স্বামী বকুলকে বাবার বাড়ি যাওয়ার কথা বলে, বকুল তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। কিন্তু বাড়ি এসেই বকুল হোঁচট খায়, যখন সে তার বাবার মুখে জানতে পারে, তার স্বামী আতিক কিছুদিন আগেই এ বাড়িতে এসে একসপ্তাহের মতো থেকে গেছে। যা বকুল জানতো না। তবে বকুলের জন্য আরও চমক বাকি ছিল। এক রাত পার হওয়ার আগেই বকুলের পৃথিবী এলোমেলো হয়ে যায়। ঘরের বাইরে ঝগড়ার শব্দ শুনে এসে দেখে ছোট বোন পারুল মায়ের পা ধরে কাঁদছে। আর মা তাকে বকেই যাচ্ছে। আতিকও সেখানে উপস্থিত। সে কখন এসেছে, বকুল তা জানতো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বকুল বুঝতে পারে এসব ঘটনার নেপথ্য কারণ। পারুলের বিয়ে হয়নি। কিন্তু সে সন্তানসম্ভবা। সে সন্তানের বাবা আর কেউ নয়, বকুলের বকুলেরই স্বামী আতিক। পারুল বকুলকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দৌড়ে এসে বকুলকে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। কারণ পারুলের ধারণা, আতিক আর তার মিলনের মাঝে একমাত্র বাধা বকুল। বকুলের বাবা ও আতিক অনেক কষ্ট করেও পারুলের হাত থেকে বকুলকে উদ্ধার করতে পারে না। একপর্যায়ে বকুলের বাবা পারুলকে জোরে ধাক্কা দিলে পারুল কাঠের আলমারির ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে মারা যায়। এরপরই আমরা দেখতে পাই, পারুলের মৃত্যুর জন্য নির্দোষ বকুলকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। বকুলের পনেরো বছরের জেল হয়। নির্ধারিত মেয়াদের আগেই ভালো আচরণের কারণে বকুলকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণাও হয়। কিন্তু এই মুক্তি বকুলের কাছে হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর। তার মনে হতে থাকে সে জেল থেকে মুক্তি পেলে আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে। তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কারণ আতিক ও বকুলের মা বকুলকে পারুলের হত্যাকারী হিসেবে শনাক্ত করেছিল। তাই শেষপর্যন্ত বকুল জেলখানার ছোট্ট মুক্তি পাওয়া থেকে জীবন থেকে মুক্তির পথই বেছে নেয়।
গল্পকার ভিন্ন এক আঙ্গিকে গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘খয়েরি রঙের ডায়েরিটা বন্ধ করে জেলার সাহেব নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। চোখ বেয়ে নামা নোনা জলের ধারা বয়ে চললো। টেবিলে রাখা সাদা কালো ডোরা কাটা পোষাকটা ভিজতে লাগল, ঝাপসা চোখে জেলার তাকিয়ে আছে, জ্বলজ্বল করছে সেলাই করা ৩৩২ নম্বর।’
লেখক আমাদের জন্য কিছু ধাঁধা রেখে দিয়েছেন। যেমন, বকুলের পরিণতি কী হয়েছিল? বকুল কি আত্মহত্যা করেছে, না বাড়ি ফিরে গিয়েছে? এই ধাঁধার সূত্র অবশ্য লেখক দিয়েছেন। এক. বকুলের ডায়েরিতে পুরো গল্পটি পড়ছিলেন জেলার সাহেব। জেলারের কাছে ডায়েরি এলো কিভাবে? বকুল রেখে গেছে অথবা বকুল মারা গেছে। তবে এ জেলারের চোখের পানি আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহজ করে দেয় যে, বকুলের পরিণতি কী হয়েছিল!
তবে আরেকটি প্রশ্নের সমাধান আমাদের কাছে অনির্ণীতই থেকে যায় যে, বকুলের সৎ-মা কেন বকুলের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছিল? সেটা কি তার নিজের স্বামীকে বাঁচাতে, নাকি আতিকের ভয়ে?
শারমিন রহমানের গল্পের ভাষা বেশ ঝরঝরে। সুখপাঠ্য। চরিত্রগুলো অল্পকথায় ভালোভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে ‘কয়েদি নম্বর ৩৩২’ পড়ার পর এর চরিত্র, সংলাপ মনে দাগ কাটার চেয়ে এর বিষয় অর্থাৎ পরকীয়ার বিষবাষ্প মানুষের জীবনকে কিভাবে ধ্বংস করে দেয়, তাই আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়।
সানাউল্লাহ সাগরের ‘বৃত্ত’ গল্পে নির্দিষ্ট কোনো কাহিনী নেই। উত্তর-আধুনিক যুগে গল্পহীন গল্পের যে ধারা ‘বৃত্ত’ তারই সমগোত্রীয়। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, গল্পের প্রচলিত ফর্ম ভেঙে সানাউল্লাহ সাগর নিজের মতো করে গল্প বলেছেন। এ গল্প ব্যাষ্টিক জীবনের, আবার হতে পারে সামষ্টিক জীবনেরও। তবে কোন সে জীবন? সচ্ছল, স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীন, সব পাওয়া জীবনের গল্প? না। বৈরী জীবন, বৈরী সময়ের আলেখ্য এই গল্প। যে জীবন সর্বদাই পিছিয়ে পড়ে। যে জীবন অচেনা পৃথিবীতে বেড়ে ওঠে। আমাদের পরম্পরাহীন স্বপ্নের মতো যে জীবন। কবি আবুল হাসান যেমন বলেছেন, ‘আমার কেবলই রাত হয়ে যায়’, সেই অন্ধকারে পিছিয়ে পড়া জীবনের গল্প এই ‘বৃত্ত’। এই জীবন কার জীবন? কাদের জীবন? অথবা আমি যে শুরুতে বলেছি, এই জীবন সামষ্টিক জীবনের, সে জীবন কাদের? এ জীবন আমার হয়তো আপনার, নয়তো জুলেখার কিংবা জয়নবের মার।
সংলাপহীন এ গল্পে লেখক আত্মকথনের মতো নিজেই নিজেকে অথবা আমাদের এ গল্প শুনিয়েছেন। গল্পের ভাষা কাব্যাক্রান্ত। উপমা,। বিশেষণের ছড়াছড়ি। পড়তে পড়তে কখনো মনে হয় কবিতা পড়ছি। গল্পের যেকোনো জায়গা থেকে নিয়ে দুটো উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে।
ক.
আমাদের সকালগুলো বন্দিমুখের মতো আমাদের পকেটেই থাকে। পকেটের মধ্যে নিয়ে আমরা সারাদিন ঘুরে বেড়াই। দিন শেষে তাদের ক্ষুধা পেলে আমরা অন্ধকার খেয়ে ফেলি। ভাগাভাগি করে খাই। তারা কিছু কম আর আমরা কিছুটা বেশি। আমরা বুঝতে পারি আমরা আবার প্রতারিত হচ্ছি। মনে মনে খুশি হই। শেষ সময়ও আমরা প্রতারিত হওয়ার যোগ্যতা রাখি!খ.
প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে ঘুম এলো। তার হাতে প্রাইমারির বুড়ো হেড মাষ্টারের মতো লম্বা একটা বেত। আমরা তার চোখে তাকাতে পারছি না। তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সকালের ঘুম, দুপুরের ঘুম, আবার অনিয়ম ঘুম শিল্পসম্মত ঘুম। কিন্তু তার ঘুম! হয়তো আমাদের মতো তারও কোনো নিজস্ব ঘুম নেই। তাকে আমাদের প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। আমরা কোনো প্রশ্নই করি না। আমরা আমাদের মধ্যে ডুবতে থাকি। ডুবে যেতেই থাকি। বেত মহোদয় চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে বসে যান। আমরা তার মাথায় উঠে যাচ্ছি। আমরা হাসি হাসি মুখ থেকে তাকেও খুলে নিয়ে যাচ্ছি। পালাচ্ছি। ঘুম থেকে পালাচ্ছি। সেখানে সকালে কিংবা বিকালের কোনো হিসেব নেই। সেখানে অস্থিরতার তুমুল চাষবাস হয়। অথবা সেখানে আমরা কিংবা ঘুম কেউ আর বেঁচে নেই। আমরা ভাগ হতে থাকি। আমি, তুমি ও সে ভাগ হয়ে তিনটি স্বপ্নে ছড়িয়ে যাই। ইচ্ছে করি যার যার আঁকবো অথবা তিনটি গল্প বানাবো। অথবা কোনো কিছুই না প্রত্যেকে আলাদা আলাদা অথচ এক হয়েই হাঁটবো দৌড়াবো আবার চরিত্রও হয়ে উঠবো।
সাধারণত কাব্যিকতা গল্পের রস ক্ষুণ্ন করলেও এই গল্পের মূল শক্তি ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ নয়, এর কাব্যিকতা। সানাউল্লাহ সাগর ছোট ছোট বাক্যে তার গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। ফলে গদ্যভাষার কোথাও শ্লথ হয়ে পড়েনি। তবে লেখকের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পাঠককে পড়া থামিয়ে থামিয়ে ভাবতে হবে বৈকি!
‘ইন্টারভিউ’ গল্পে শিল্পী নাজনীন কাহিনীর মূল চরিত্র মৃদুলের কয়েকঘণ্টার ঘটনা ফোকাস করেছেন। মৃদুল। একের পর ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু কোথাও চাকরি হচ্ছে না। কারণ মামা-চাচা না থাকলে যা হয়, ঘটনা তেমনেই। তার কোথাও চাকরি না পাওয়ার কারণে প্রেমিকা তনিমার অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে গেছে। তারপরও তনিমা তার বরকে বলে-কয়ে বিভিন্ন জায়াগায় তদবির করায় মৃদুলের চাকরির জন্য। তারপর মৃদুলের ভাগ্যে শিকেয় ছিঁড়েনি। মৃদুল অবশ্য ঠিক বেকারও নয়। সে মফস্বলের ননএমপিও একটি কলেজে বেগার খাটে। সে চাকরিটিও হয়েছিল ঘুষের বিনিময়ে। ওহ, হ্যাঁ, গল্পকার কলেজের কাজকে বেগার খাটা-ই বলেছেন। এ বলার মাঝে কোনো অতিকথন কিংবা সত্যের অপলাপ নেই। একান্তই সত্য। সমাজে এখনো স্কুল কলেজের চাকরিটাকে অনেকে ঠিক চাকরি মনে করেন না। যাই হোক, এবার মৃদুলে মাকে অনেক বলেকয়ে ধান বিক্রির টাকা নিয়ে ঢাকায় এলেও ইন্টারভিউ দেওয়ার পরই বুঝে যায়, এবারের চাকরিটাও তার হবে না। বিষণ্ন মনোরথে মৃদুল এসে বাংলা মোটরের ফুটওভার ব্রিজের নিচে দাঁড়ায়, তখন এক দেহপসারিনীর আহ্বান আসে তার কাছে। মৃদুলের সঙ্গে পতিতার কথাবার্তার অংশটি বেশ আকর্ষণীয়। পতিতা চলে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃদুল ছিনতাইকারীদের হাতে পড়ে মোবাইল, টাকাপয়সা খোয়ায়। কপর্দকশূন্য অবস্থায় এক বন্ধুর কথা মনে হলেও সে শেষপর্যন্ত বন্ধুর বাসায় যায় না, বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর আচরণ তার প্রতি কেমন হবে, সেই কথা ভেবে। শেষপর্যন্ত সে রাতটা পার্কে শুয়ে কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তার মধ্যে যে মধ্যবিত্তীয় আবেগ, সে আবেগ তার ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তোলে।
শিল্পী নাজনীন আমাদের অতিপরিচিত একটি চরিত্রকে তার গল্পের বিষয় করেছেন। তার দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, অপ্রাপ্তি আমাদের খুবই চেনা। বর্তমানে ননএমপিও শিক্ষকের জীবন একটি অভিশপ্ত জীবন। লেখক পরম মমতায় সে চরিত্র তুলে ধরেছেন তার গল্পে। ফলে আমাদের মনেও মৃদুলের জন্য মমতা সঞ্চারিত হয়। মৃদুল হয়ে উঠে আমাদের একান্ত আপনজন। তার দুর্ভাগ্য যেন আমাদেরই দুর্ভাগ্য। গল্পের শেষে যখন লেখক সমাপ্তি টানেন এভাবে, ‘হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মৃদুল। কী একটু ভাবে। তারপর ঢুকে পড়ে দ্বিধাহীন। পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে টান হয়ে। শওকত আর তার বউয়ের বিরক্ত মুখের চেয়ে এই ভালো। কাত হয়ে শুয়ে মাথার নিচে পুরনো রঙচটা ব্যাগটা রেখে ঘুমোনোর চেষ্টা করে সে। কুকুরটা অদূরে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। একটুকরো বাসি পাউরুটির কৃতজ্ঞতায় মৃদুলের মাথার দিকে সতর্ক প্রহরীর ভূমিকায় ঝিমোয়।’
এই যে মৃদুলের হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানো, এই ঘুরে দাঁড়ানো যেন আমাদেরই ঘুরে দাঁড়ানো। এই ব্যক্তিত্বটুকু, জিদটুকু আমাদেরই। মূলত পুরো গল্পটি দাঁড়িয়ে আছে এই সমাপ্তির ওপরই। গল্পটি যদি অন্যভাবে সমাপ্ত হতো, তাহলে যে নিঃসন্দেহে গল্পটি ব্যর্থ হতো বলা যায়।
মাদ্রাসায় ধর্মীয় (ইসলাম) শিক্ষা দেওয়া হয় বিধায় অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে বাঙালির কাছে গুরুত্ব একটু অন্য রকম। আলাদা। মাদ্রাসার শিক্ষক, যারা সমাজের হুজুর হিসেবে পরিচিত, মানুষ তাদের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি ভেবে সম্মান করে। ধর্ম এখনো মানুষের কাছে খুবই সংবেদনশীল একটি ব্যাপার। তাই, এই হুজুররা যেহেতু বর্তমানে ইসলামি শিক্ষা প্রচার, প্রসারে নিয়োজিত, সেক্ষেত্রে তাদেরও বিশেষ একটি শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হয় সমাজে। আমরা ‘লালসালু’ উপন্যাসে দেখেছি, ধর্মকে ব্যবহার করে সহায়সম্বলহীন মজিদ কিভাবে মহব্বত নগরের সমাজপতি খালেক ব্যাপারির চেয়ে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষককে বিকৃত আচার আচরণের ফলে হুজুরদের সম্মান আর আগের জায়গায় নেই। মাদ্রাসার ছাত্রদের ওপর নির্যাতন, বিকৃত যৌন লালসা তাদের ভূমিকাকে করে তুলেছে প্রশ্নবিদ্ধ। হুসাইন হানিফের ‘কানার হাটবাজার’ গল্পটি মাদ্রাসার শিক্ষকদের এই কীর্তিকলাকে নিয়ে লিখিত।
সমকালীন গল্পই একদিন চিরকালীন হয়ে উঠে তার প্রসাদগুণে। তবু আজকের ধ্যান ধারণা, উপলব্ধির প্রতিফলন এই ছোটগল্প। জীবনের নানা বাঁক, সমাজবাস্তবতা, মনস্ততত্ত্ব, গল্প বয়নের কৌশল, ফর্মভাঙার চেষ্টা, নতুন ভাবে গল্প বলার টেকনিক গল্পগুলোতে দেখতে পাই।
‘কানার হাটবাজার’ ক্যাটালগিং গল্প। উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্পে কথক শিক্ষকের হাতে প্রহৃত হয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, তার এই মারখাওয়া শুধু মুখ বুঝে না খেয়ে কিভাবে খেলে হুজুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হতো। হুসাইন হানিফের লেখক সত্তা পরিহাসপ্রবণ। গল্পে উইটের ব্যবহার তার একটি শক্তিশালী দিক। পাঠক এতে আনন্দিত হয় কিন্তু যার দিকে লক্ষ করে তীর ছোড়া হয়, তার হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় হতে দেরি হয় না।
হুসাইন হানিফের গল্পটি একটি সাহসী গল্প। কারণ চারিদিকে ধর্মান্ধতা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, এ ধরনের গল্প লেখার জন্য সাহসের দরকার বৈকি!
গল্পের শুরুতে দেখি তিনি লিখেছেন, ‘ইশ্ বেয়াদবি হয়ে গেছে! হুজুরের সাথে এরকম বেয়াদবি আর করা যাবে না। এটা আমার জন্য উচিত হয় নি। আমার উচিত ছিল নিজেকে হুজুরের হাতে সঁপে দেওয়া। যত বেত্রাঘাত করতে পারেন। কিন্তু না, আমি কিচ্ছু করলাম না। চুপচাপ হুজুরের পবিত্র হাতে মার খেয়ে চললাম। টু শব্দটিও করলাম না। একটু নড়লাম চড়লামও না।
আহা! কী ভালো হুজুরটা! তার সাথে আমার এমন করা উচিত হয়নি। গুরু তো! উস্তাদ। পিতৃপ্রতীম। বেচতে পারবেন, কিনতেও পারবেন। অথচ তিনি মারলেন আর আমি সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেলাম। মেরেছেন ঠিক করেছেন। কোরানই পড়া দরকার। চল্লিশ মিনিট কেন চল্লিশ বছর লাগাতার পড়তে বললেও সেটা করাই আমার উচিত। কেননা আমি ছাত্র। ক্রীতদাস। তার চে’ অধম। মানুষ হওয়ার যোগ্য না। মানুষ হওয়ার জন্যই মা বাবা মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন। বলেছেন, যেভাবেই হোক মানুষ বানাবেন।’
গল্পকার শুধু মাদ্রাসার শিক্ষকদেরই এক হাত তুলে নেননি, আমাদের বাবা-মা ধ্যানধারণা, সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতিও প্রশ্ন তুলেছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বক্তব্য বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে পড়েছে, যেমন তিনি লিখেছেন, ‘হুজুররা তো নবীর ওয়ারিশ। তার উত্তরাধিকারী। নবীর মলমূত্র সুবাসিত হলে, ভক্ষণ করলে জাহান্নাম হারাম হবে। তাহলে আমাদের ছোট ছোট নবীরা, যাদের আমরা হুজুর বলে চিনি, তারা তো নবীই—নবীরই ওয়ারিশ—তাদের থেকে যা বের হবে সেটাও তো নবীর মতোই হওয়া উচিত।’
ইসলাম ধর্মের কোথাও এমনটা লেখা নেই যে, ‘নবীর মলমূত্র সুবাসিত হলে, ভক্ষণ করলে জাহান্নাম হারাম হবে।’
এর ফলে দুটো ব্যাপার হতে পারে, এক. মানুষের ধর্মানুভূতি আহত হতে পারে। দুই. যারা এই বাক্যের অসারতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, তারা এটাকে সত্যি ভেবে বিভ্রান্ত হতে পারে।
একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, লেখকের কাজ মূল্যবোধ তৈরি করা, প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে ফেলা। কিন্তু কখনোই মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেওয়া নয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করা নয়।
সুবন্ত যায়েদ নিরীক্ষাধর্মী গল্পকার। বর্তমানে গল্পের প্রচলিত ফর্ম ভেঙে গল্প লেখার যে প্রবণতা শুরু হয়েছে, সুবন্ত সেই ধারার প্রতি বিশ্বস্ত। ‘সম্মিলিত মৃত্যুর পর’ তেমনি একটি গল্প। মানুষের একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, অন্তর্দহন, পোড়ন, পীড়ন, পরাজয়, বঞ্চনা গল্পের মূল উপজীব্য। এই গল্পে গল্পের অংশ সামান্যই। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়া এক যুবক বনে চাকরি নিয়ে চলে যায়। সেখানে তার মনের যে ভাব, অনুভূতি লেখক তা উত্তম পুরুষে বর্ণনা করেছেন। গল্প কথক ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে প্রকৃতি-প্রাণীর কথা শোনাতে গিয়ে হরিণ ও ইলিশ মাছের মিথটি নৈপুণ্যের সঙ্গে গল্পে জুড়ে দিয়েছেন। এর সমাপ্তি টেনেছেন নতুন এক অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে। তিনি লিখেছেন, ‘মানুষ এই স্বাদু মাছ খেতে গিয়ে দেখলো পিঠের ওপর দিয়ে খয়েরি মাংস। হরিণ ইলিশকে স্মৃতি রাখতে বলেছিল বলে হয়তো তাই, মানুষ গল্প বানালো, একদা এক হরিণ আর ইলিশ দৌড় প্রতিযোগিতা দিলো এই শর্তে, যে হারবে সে খানিকটা মাংস কেটে পুরস্কার দেবে বিজয়ীকে। তারপর প্রতিযোগিতা হলো আর হরিণ হারলো বলে খানিকটা মাংস কেটে পুরস্কার দিলো ইলিশকে। ইলিশের পিঠের এই খয়েরি মাংস হলো আদতে হরিণের।’
তবে লেখক এই মিথকে নতুন ব্যঞ্জনা দান করলেন এর পরের অংশ জুড়ে দিয়ে, ‘গল্প আসলে এটা ছিল না। গল্প হবে মূলত প্রতিযোগিতা হয়েছিল তিনজনের। একটি রূপালি ইলিশ, ধূসর হরিণ আর একজন মানুষের। কিন্তু প্রতিযোগিতায় জিতে গেলো ইলিশ আর হরিণ। জনপদবাসী তাই হরিণ আর ইলিশের প্রতিযোগিতার গল্প বললো কিন্তু মানুষের পরাজয়ের কথা কেউ জানলো না।’ কারণ ‘তার জীবন আসলে মানুষের ছিল না।’
মূলত গল্পটি একজন মানুষের আড়ালে আধুনিক যুগে ব্যর্থ মানুষের গল্প। যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে। আধুনিক সভ্যতা যার আশ্রয়টুকু কেড়ে নিচ্ছে। সে শেকড়চ্যুত প্রকৃতির সন্তানের মনোলোকের উদ্ভাসন এই গল্প।
সুবন্ত যায়েদ গল্পটিকে ছয়টি অংশ ভাগ করেছেন। ‘এক’, ‘দুই’, ‘গল্প এক-এর অংশ’, ‘গল্প দুয়ের অংশ’, ‘গল্প এক-এর বাকি অংশ’, ‘এক ও দুয়ের সমাপ্তি’—এ ছয়টি উপশিরোনামে। গল্পটি লেখক টানা বর্ণনা করে গেছেন। হরিণ ও ইলিশের একটি সংলাপ বাদে কোনো সংলাপ নেই। সুবন্ত যায়েদের এ গল্পের একটি লক্ষণীয় দিক হলো, তিনি গল্পের চেয়ে প্রতিটি বাক্যকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বেশি মনোযোগী। তার গদ্যও সানাউল্লাহ সাগরেরমতো কাব্যভারাক্রান্ত। যেমন, তিনি লিখেছেন,
মানুষের জন্য আমার কোনো সময় নাই।
কারণ, আমি অন্ধ তবু দৃষ্টি দৃষ্টি খেলা খেলি না।
কারণ, মনের ভেতরে আমার কোনো দৃশ্যপাপ আসে না।
কারণ, আমি প্রেমিক নই তবু ভালোবাসার ইতিহাস সমাজে প্রতিষ্ঠা করি না।
কারণ, যোনি ও শিশ্নপ্রধান সমাজে আমি কোনো টিপসই দেই না।
এর রকম আরও বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে একটি কথা অনাবশ্যক হলেও বলা যায়, গদ্যভাষা কাব্যিক না হয়ে যদি কাব্যভারাক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে গল্পের রসগ্রহণে কিছুটা ঘাটতি পড়ে বৈকি। আর এ কথাটিকে ‘অনাবশ্যক’ বলার কারণ হলো, লেখকরুচি অবশ্যই তার নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে যাবে। জনমতানুযায়ী তার রুচি বা স্টাইল বদলানোর কোনো প্রয়োজন নেই।
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে যেতে পরিণতিতে পৌঁছেছে ‘লালবেজি’ গল্পটি। পাঠক এক বিন্দু থেকে শুরু যেতে যেতে যখন গল্পটি পাঠ শেষ করেন, তখন খেয়াল করেন তিনি পৌঁছে গেছেন অন্য কোনো বিন্দুতে। শীলাবৃষ্টি পাঠককে বুঝতেই দেন না গল্পটি কোথায় গিয়ে শেষ হবে। আমাদের অনিশ্চিত জীবনের মতোই তার গল্পের ভুবন।
‘লালবেজি’ একটি মহল্লার বা এলাকার গল্প। এ গল্পের কোনো বা কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। এলাকার বিভিন্ন মানুষের সমাত্মজীবনীই এ গল্পের প্রাণ।
গল্পটি শুরু হয় মোস্তফা মিয়ার টিভির দেখার ঘটনার মধ্য দিয়ে। গুণবতী গ্রাম থেকে আগত এক ছেলেকে তিন হাজার টাকা সাহায্য করে তিনি টিভিতে সংবাদ দেখতে বসেছেন। কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত ছেলেটি বাড়ি থেকে থেকে বের হবার দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ছেলেটি মিনিছাদরূপী সানসেডের দরজাকে বের হবার দরজা মনে করে রওনা দিলে সে দশ ফুট ওপর থেকে পড়ে জ্ঞান হারায়। এ নিয়ে মহল্লায় হৈচৈ শুরু হয়। ছেলেটিকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ছেলেটির মা এসে মরা কান্না জুড়ে দেয়। আশঙ্কা তৈরি হয় ছেলেটি মারা গেলে মোস্তফা মিয়াকেই পরিবারসুদ্ধ জেলে যেতে হবে। মোস্তফা মিয়ার বড় ছেলে এলাকার উঠতি মাস্তান সুমন এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সানশেড থেকে পড়ে যাওয়া মিজান নামের ছেলেটি মারা যায়, তাহলে যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য সে হাসপাতালে তার বন্ধুবান্ধব এনে হাজির করে, বড় নেতাদেরও ফোন দিয়ে রাখে। বুক চাপড়ে, গলা ফাটিয়ে কান্নারত মিজানের মাকে ধমকায়। বলে,
‘এইচ্যা চিল্লান কিল্লাই? চিল্লাইলে কি আন্নের হোলা ভালা অই যাইবনি? না মনে কইচ্যেন ইয়েন বাংলা সিনেমা, আন্নের চিল্লানির ম্যাজিকে আন্নের হোলা উডি বইব!’
এইবার একটু থেমে মহিলাকে নকল করে গলা ফাটায় সুমন, ‘মারিয়ালাইসে রে! মারিয়ালাইসে রে! কী কইতেন চান? আন্নের হোলারে কি আন্ডা ধাক্কা দি নি নীচে হালাই দিসি নি? হোলার হকেটেত্তুন যেই তিন হাজার টেয়া হামাইলছেন, হিয়েনো তো আঁর বাপের টেয়া। হেতের হিছে অনতরি ছ হাজার টেয়া খরচ অইসে, আরও অইব, আর আব্বায় টেয়া খরচ কইত্যে কি ওনা-হানা করের?’
‘মারিয়ালাইসে রে! মারিয়ালাইসে রে!’—এবার ভেংচি কেটে ওঠে সুমন, ‘হ্যাতে কন! হ্যাতে ভিপি জামাল, না লোডা-শাকিল্যা? আন্ডা এলাকা দখল কইত্যো আইছে? হেতেরে মারি আন্ডা কী লাভ? না কি আন্নের হোলায় আঁর বাপের সম্পত্তির ওয়ারিশ!’
চোখে লালমরিচের রঙ আর গলায় তার ঝাঁজ তুলে তর্জনি উঁচিয়ে এইবার মহিলাকে শাসায় সুমন, ‘আর একটা আওয়াজ বাইর কইরবেন তো আব্বারে লই সোজা বাইর অই যামু হাসপাতালেত্তুন!’
তখন মহিলা শান্ত হয়। মোস্তফা মিয়ার বুকও নিজের বখাটে ছেলেকে নিয়ে গর্বে ফুলে ওঠে। মিজানের পেছনে মোস্তফা মিয়ার আরও কিছু টাকা খরচ হলেও মিজান একপর্যায়ে সেরে ওঠে। গল্পের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ মিজানের ঘটনা নিয়ে শেষ হয়। পাশাপাশি লেখক আমাদের মোস্তফা মিয়ার স্ত্রী, দুই কন্যা, কাজের মেয়ের পরিচয়, বৈশিষ্ট্যসহ আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ সুমনের জবানিতে তার পরিচয়, কাজকর্ম, বন্ধুবান্ধবের কথা, বোনের কথা বিবৃত হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে আবার স্বয়ং গল্পকার কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এখানে তিনি ছাদের ওপর সেতু ও তার প্রতিবেশী ছবি আপার বৈকালিক আড্ডার চিত্র তুলে ধরেন। এমন সময় তারা আকস্মিক এক ঘটনার মুখোমুখি হন। বাড়ির সামনের পথ দিয়ে তারা রানাকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখে। রানা সুমনের বন্ধু। সুমন রানার বোন ঝিলিকের রূপমুগ্ধ। এদিকে, ছবি আপার মনেও রানার জন্য কিছুটা দুর্বলতা আছে। কিছুক্ষণ পরই রানা যেদিকে গিয়েছে, সে দিকে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। ছাদে আড্ডারত সেতু, ছবি কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, রানার আবার কিছু হলো না তো! দেখা যায়, রানা সে গোলাগুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু লেখক এরপরই গল্পের মোড় ঘুরিয়ে রানার মাকে গল্পের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলেন। দেখা যায়, রানা মারা যাওয়ার চৌদ্দ দিন যেতে না যেতেই তার মা পুত্রশোক ভুলে গিয়ে কটকটে হলুদ শাড়ি পরে কোহিনূরের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে হাজির হন। গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে আমরা জানতে পারি পুরো গল্পটা সেতুর ডায়েরি থেকে তার স্বামী পারভেজ পড়ছিল। গল্পকার রানার মাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেই গল্পটির সমাপ্তি টানেন।
শীলা বৃষ্টির সেন্স অব হিউমারের প্রশংসা করতেই হয়। তিনি খুব অল্প শব্দেই চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেক খুঁটিনাটি উঠে এসেছে। যা একজন গল্পকারের শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সংলাপ নির্মাণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলোর মুখে আঞ্চলিক সংলাপ উপভোগ্য। তবে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের ভাষা হওয়ায় কোথাও কোথাও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদটি সুমনের জবানিতে বলা হয়েছে। ফলে পুরোটাই আঞ্চলিক ভাষায় লেখা হয়েছে। যা গল্পের রস কিছুটা ক্ষুণ্ন করেছে। এছাড়া গল্পে ঘটনার উলম্ফনের কারণে পাঠকের কাছে তা রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে শেষের দিকে মনে হয়েছে গল্পকার শহীদুল জহির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত।
সমকালীন গল্পই একদিন চিরকালীন হয়ে ওঠে তার প্রসাদগুণে। তবু আজকের ধ্যান ধারণা, উপলব্ধির প্রতিফলন এই ছোটগল্প। জীবনের নানা বাঁক, সমাজবাস্তবতা, মনস্ততত্ত্ব, গল্প বয়নের কৌশল, ফর্মভাঙার চেষ্টা, নতুন ভাবে গল্প বলার টেকনিক গল্পগুলোতে দেখতে পাই। সমকালীন গল্পের আয়োজন করার জন্য ‘চিন্তাসূত্র’কে আবারও ধন্যবাদ। এই নবীন সমকালীন গল্পকারগণ একদিন চিরকালীন সাহিত্যের পথের পথিক হবেন, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।