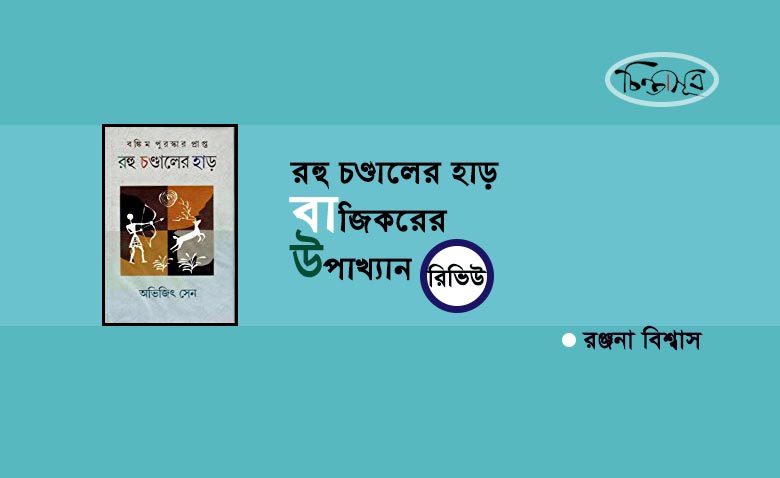 প্রাচীন যুগে তো নয়ই, মধ্যযুগের চল ছিল না উপন্যাসের। কিন্তু সে যুগেও কাহিনী বা আখ্যান নির্মিতি লক্ষ করার মতো। সেই সব আখ্যান যদিও দেবতা আর রাজ-রাজড়াদের স্তুতিবহুল ছিল, তবু নিম্নবর্গের পরিচয় চর্যাপদ থেকেই লক্ষ করা যায়। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, অন্ত্যজ জীবনকে অস্বীকার করে কোনো মঙ্গলকাব্য রচিত না হলেও অন্ত্যজ জীবনকে আশ্রয় করে বলা চলে অন্ত্যজ জীবনকে সাহিত্যের ভরকেন্দ্রে স্থাপন করে অন্ত্যজ মানুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় বিধৃত হয়নি সে যুগে। হতদরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষ ধর্মযুগের আবির্ভাবের পর যাদের স্থান নির্দিষ্ট হয় গ্রামের ত্রি-সীমানার বাইরে সমাজের প্রান্তে; শশ্মান ঘাটের পাশে, তাদের পরাজয়, তাদের ট্রাজেডি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছিল অনেক পরে। এর আগে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রই বলি আর রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিভূতিভূষণই বলি কারও উপন্যাসে নিম্নবর্গের যুগযন্ত্রণা টের পাই না। এখানে নিখিলেশ, গোরা ও সত্যচরণের অভিজ্ঞতাকে শানিত করেছে ‘ঘরে-বাইরে’র নিচুতলার মানুষ পঞ্চু; ‘গোরা’র চরঘোষ পুরের নিম্নবর্ণের নাপিত আর ‘আরন্যকে’র অনার্য মানুষগুলো। সেই বিচার উপন্যাসগুলো বহিরাগতদের অভিজ্ঞতার উপন্যাস হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার ‘গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস’ গ্রন্থে ‘ঘরে-বাইরে’র পঞ্চু সম্পর্কে বলেন, ‘পঞ্চু প্রসঙ্গ কেবল নিখিলেশের আত্মকথাতেই পাই। স্থিতধী নিখিলেশ ভারতবর্ষের সমাজ-রাজনীতির অর্ন্তগঠনটাকে যেভাবে নিতে চাইছিল, সেখানে পঞ্চুর মতো দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষের কথা না থাকলে নিখিলেশর আত্মসন্ধান অসম্পূর্ণই থেকে যেত। কিন্তু সেই পঞ্চু বা তার শ্রেনীর পরিনাম ঔপন্যাসিকের অবিষ্ট নয়।’
প্রাচীন যুগে তো নয়ই, মধ্যযুগের চল ছিল না উপন্যাসের। কিন্তু সে যুগেও কাহিনী বা আখ্যান নির্মিতি লক্ষ করার মতো। সেই সব আখ্যান যদিও দেবতা আর রাজ-রাজড়াদের স্তুতিবহুল ছিল, তবু নিম্নবর্গের পরিচয় চর্যাপদ থেকেই লক্ষ করা যায়। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, অন্ত্যজ জীবনকে অস্বীকার করে কোনো মঙ্গলকাব্য রচিত না হলেও অন্ত্যজ জীবনকে আশ্রয় করে বলা চলে অন্ত্যজ জীবনকে সাহিত্যের ভরকেন্দ্রে স্থাপন করে অন্ত্যজ মানুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় বিধৃত হয়নি সে যুগে। হতদরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষ ধর্মযুগের আবির্ভাবের পর যাদের স্থান নির্দিষ্ট হয় গ্রামের ত্রি-সীমানার বাইরে সমাজের প্রান্তে; শশ্মান ঘাটের পাশে, তাদের পরাজয়, তাদের ট্রাজেডি আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছিল অনেক পরে। এর আগে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রই বলি আর রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিভূতিভূষণই বলি কারও উপন্যাসে নিম্নবর্গের যুগযন্ত্রণা টের পাই না। এখানে নিখিলেশ, গোরা ও সত্যচরণের অভিজ্ঞতাকে শানিত করেছে ‘ঘরে-বাইরে’র নিচুতলার মানুষ পঞ্চু; ‘গোরা’র চরঘোষ পুরের নিম্নবর্ণের নাপিত আর ‘আরন্যকে’র অনার্য মানুষগুলো। সেই বিচার উপন্যাসগুলো বহিরাগতদের অভিজ্ঞতার উপন্যাস হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার ‘গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস’ গ্রন্থে ‘ঘরে-বাইরে’র পঞ্চু সম্পর্কে বলেন, ‘পঞ্চু প্রসঙ্গ কেবল নিখিলেশের আত্মকথাতেই পাই। স্থিতধী নিখিলেশ ভারতবর্ষের সমাজ-রাজনীতির অর্ন্তগঠনটাকে যেভাবে নিতে চাইছিল, সেখানে পঞ্চুর মতো দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষের কথা না থাকলে নিখিলেশর আত্মসন্ধান অসম্পূর্ণই থেকে যেত। কিন্তু সেই পঞ্চু বা তার শ্রেনীর পরিনাম ঔপন্যাসিকের অবিষ্ট নয়।’
এই একই কথা খাটে অন্যগুলোর বেলায়ও। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের কথা বলার সময় যখন এলো, তখন দেহোপজীবীনিরাও হয়ে উঠলো শুদ্ধ প্রতচারিনী; বনওয়ার স্বপ্ন দেখতে সাহস পেল, শিবের কাছে সেও প্রার্থনা করে-‘শিবো হে..কুল দিয়ো। আর করালী হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। নিতাই হয়ে উঠতে চায় কবি। নিম্নবর্গের মানুষের মোটামুটি সামগ্রিক পরিচয় উঠে আসতে শুরু করে কল্লোলের পথ বেয়ে নিম্নবর্গের মধ্যে একেবারে প্রান্তিক নিম্নবর্গ যারা, তারাও বাদ যায়নি। প্রান্তিক নিম্নবর্গ কারা? প্রশ্নটা ভিষণভাবেই নাড়া দেয় আমাদের। নিম্নবর্গের মধ্যে যে নারী, নিম্নবর্গের মধ্যে যে নিম্নে আছে সেই তো!
এ পর্যায় ‘কবি’তে আছে দেহোপজীবিনী; ‘নাগিন কন্যার কাহিনী’তে আছে-বেদেনী (নাগিনকন্যা)। নিম্নবর্গমানুষের বঞ্চনা, রিক্ততা তার শোষণের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে একটি সমাজ বা দেশের কতটুকু পরিচয় আমরা পেতে পারি? তার জন্যই তারাশঙ্কর থেকে শুরু হয়েছিল এক ভিন্ন অভিযাত্রা। এই যাত্রায় আছেন অদ্বৈত মল্লবর্মন, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রফুল্ল রায়, সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, অভিজিৎ সেনসহ অনেকেই।
অবহেলিত ছিন্নমূল মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর। ‘বেদে জনগোষ্ঠী’র জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করে তিনি বাংলাসাহিত্যে বেদে জনগোষ্ঠীর এক অন্যতম আত্মীয় হয়ে উঠলেন। শুধু তারাশঙ্করই নন-বেদে জনগোষ্ঠীর একটি প্রধান উপশাখা বাজিকরদের নিয়ে অভিজিৎ সেন রচনা করলেন তার প্রথম উপন্যাস-‘রহু চণ্ডালের হাড়’। ভাসমান যাযাবর জনগোষ্ঠী জিপসীকে নিয়ে বিশ্বের প্রধান লেখক সম্ভবত George Borrow-ই। জিপসীদের ইতিহাস, জীবন যাত্র, নৃতত্ত্ব খুব সম্ভবত এর আগে কেউ এত খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেনি। বাংলা সাহিত্যে সেই যাযাবর শ্রেণী উঠে এসেছে তারাশঙ্কর ও অভিজিৎ সেনের রচনায় ইতিহাস ও নৃতত্ত্বসহই।
সে বিচারে আমরা এই দুজনকে George Borrow-এর যোগ্য উত্তরসূরি বলতে পারি। তবে নৃতত্ত্বও যেভাবে, যে নির্দিষ্ট নিয়মে কোনো জাতির বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে, সাহিত্যে সেই নৃতত্ত্বের ব্যাখ্যা আশা করা অনুচিত। কেননা সাহিত্যে কোনো জনজাতির সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব যেভাবে উপস্থাপিত হয়, তা বাস্তবের অভিজ্ঞতার সীমানা ছাড়িয়ে কল্পনার জগতে আশ্রয় লাভ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এজন্যই বলা হয় ‘সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যে তফাৎ বিস্তর’। কিন্তু তা হলেও সত্য খোঁজার বিভিন্ন পথ যেমন আছে, তেমনি নিষ্পত্তি বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পথও কিন্তু ভিন্ন নয়। যে পথেই হাটা যাক না কেন জনজাতির প্রশ্নে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে নৃতত্ত্বের হাত ধরতেই হয়। তবে এ কথা মানতেই হচ্ছে, নৃতত্ত্ব যেমন সত্য বের করে আনতে উৎসাহী, তেমনি সাহিত্যেও। তবে এই দুইয়ের খানিক তফাৎ পথচলায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। কিন্তু যতই তফাৎ থাকুক, সাহিত্যিক যেমন দ্বারস্থ হন নৃতত্ত্বের, তেমনি নৃতাত্ত্বিবিদদেরও সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। আর এ কারণেই বাজিকর জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান তাই আজ অভিজিৎ সেনের ‘রহুচণ্ডালের হাড়ের’।
ঔপন্যাসিক তার উপন্যাসকে ইতিহাসের পটভূমিতে স্থাপন করে সমকালীন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেও তার উপন্যাসের ইতিহাস চেতনা এবং ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চেতনা এক নয়। ঐতিহাসিকেরা যে ইতিহাসে সাধারণ মানুষকে দাঁড় করাতে পরেন না, ঔপন্যাসিকেরা সেই সব সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের অলিখিত ইতিহাসই লিখে থাকেন। সেই রকমেই রহুচণ্ডালের হাড়ে রচিত হয়েছে রহু, দনু, পীতেম ও ধন্ধুদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা-দুর্ঘটনার আদ্যোপান্ত।
রহু ও তার উত্তরসূরিদের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা, তাদের স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-দৈন্য ও সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাসে। শেকড়বিহীন যাযাবর গোষ্ঠীর থিতু হওয়ার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যায় রহু চণ্ডালের হাড়। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসে সাঁওতালরা। তারা জমির স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে যায় বার বার। দ্বন্দ-সংঘাত তাদের টেনে নিয়ে আসে পুবে আরো পুবে। কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কখনো মানবসৃষ্ট সমস্যা তাদের দিশাহারা করে দেয়। মানুষ যখন সান্ত্বনা খোঁজে ভগবানের কাছে, আল্লার কাছে; তখন বাজিকরেরা তাকিয়ে থাকে অতীতের পানে। কেননা তাদের তো কোনো আশ্রয় নেই, না ভগবান, না আল্লা না যিশুর কাছে। রহুই তাদের আরাধ্য। তাদের পিতৃপুরুষ। রহু কি করে নানি?—লুবিনি বলে।
জবাব আসে, ‘রহু বাজিকরদের দেখে।’ তারা সান্ত্বনা খুঁজেছে কেবল রহুর হাড়ের কাছে। ‘বিগামাই কালীমাই, কি ওলামাই?’—সেও তো শুধু পথের সংগ্রহ তার বেশি কিছু নয়।
বাজিকরদের নির্দিষ্ট কোনো জাত নাইে, ধর্ম নেই। পারগানা লক্ষন সোরেনকে পীতেম বলেছিল—’বাজিকর কোন জাত নয়’। পীতেমের উত্তরসূরি শারিবা দেড়শ বছর পরেও একইভাবে বলেছে, তার দোস্ত হানিফকে, আমরা বাজিকর হানিফ ভাই।
বাজিকর কোনো জাত নয়।
তবে হামারদের জাত নাই।
গরু খাও?
খাই
হারাম, শুয়োর?
খাই।
তাজ্জব! তুমি হারাম নিশা কাটাই দিলা হে! এমন মানুষও এদেশে আছে, যার কোনো জাত নাই?
এই জাতের প্রশ্নে বাজিকররা বার বার মৌন থেকেছে। লাল মিয়া মহিম বাবুর কাছে বেকুব হয়েছে ইয়াসিন। ধম্মোকম্মো কী করো?
‘অভিজ্ঞ ব্যক্তিটি দলের মানুষের কাছে বেকুব হয়ে যায় এদিকে ওদিকে তাকায়। ফলে তারা বেজাতবরে অবাক হয়। ধর্মহীনদের সাথে ন্যায় নীতির দরকার পড়ে না বলে ভাদুধান কাটার আগেই ইয়াসীন আর রূপা বাজিকরের জমি বেহাত হয়। তবু খোদার কাছে গোলামের মায়ের মতো বাজিকররা নালিশ করে না। বলে না-‘খোদাতালা নাই’, ‘খোদাতালা নাই’ কিংবা আমার কোনো নালিশ নাই’ বলার মধ্য দিয়ে রমজান যেটুকু বুক পোড়ানো অভিমান দেখায়, তাও বাজিকরের করে না। ‘নমনকুড়ির বানের মতো সর্বনাশ বাজিকরের আর কী হয়েছে? তবু কোনো বাজিকর রমনী আকাশের দিকে তাকিয়ে গোলামের মায়ের মতো কাউকে গাল পারেনি।” তারা সান্ত্বনা খুঁজেছে সেই অতীতের কাছে। রহু চণ্ডালের হাড়ের কাছে।
রহু চণ্ডালের হাড়’ এ সাধারণ মানুষের অলিখিত ইতিহাসের সন্ধান যেমন মেলে, তেমনি ভৌগোলিক সম্প্রসারণও নজরে আসে। বাজিকরদের কোনো স্থিতি নেই। গোরখপুর থেকে আরও পুবে পাঁচবিবি পর্যন্ত তাদের কেবল স্থানবদল হয়। প্রতিবারই তাদের মনে হয়, এটা তাদের দেশ, এই তো তাদের স্বপ্নের নিকানো উঠান। কিন্তু হায়। সেই স্বপ্ন প্রতিবারই অধরা থেকে যায় দনু পীতেম কিংবা লুবিনিদের কাছে। লুবিনি তার নাতি শারিবাকে বলে ‘কুথায় হারাই গেল গোরখপুর?’ গোরখপুর বাজিকরদের আদি নিবাস, সেখানে যর্যরা নামে এক পবিত্র নদী বয়ে যায়। কিন্তু সেই নদীর সন্ধান তাদের মেলে না। ‘পথে পথে ফিরা বাজিকরের কুত্তা ভুকে, জানোয়ার চিল্লায়। পুরনিয়া, কাটিহার, কিশনগঞ্চ, দিনাজপুর, রঙপুর, ফির মালদা, রহুর ঘোড়ার অক্তের দাগ…’ বাজিকরদের মাথার ওপর সূর্য জ্বলে, শীতের হিমঝরে, বর্ষার জল পড়ে বাজিকরদের গায়ের সুন্দর রঙ তামার বর্ণ পায়, তবু তারা থিতু হতে পারে না। না রাজমহলে না পাঁচ বিবিতে। ঘুরতে ঘুরতে তাদের ভাষা বদলায় বেশবাস বদলায়, তবু তারা শান্তি পায় না, স্বস্তি পায় না। তারা কেবল পুবে সরে আসে। কে জানে পুবে যেখানে আশা জাগানিয়া সূর্য ওঠে, আকাঙ্ক্ষার সেই সূর্যটার সন্ধান তারা কোনো কালে পাবে কি না।
‘রহুচণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসটিতে বিধৃত হয়েছে যাযাবর জনগোষ্ঠীর বাজিকর সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের গল্প, যা দেড়শো বছরের বাজিকরদের নিজস্ব ইতিহাস। উপন্যাসটিতে বাজিকররা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লষণে বাজিকররা বেদে বা বাদিয়াদের একটি পেশা ভিত্তিক প্রধান উপ-শাখা।
বেদে বা বাদিয়া জনগোষ্ঠীকে জেমস ওয়াইজ সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো: ১. বেবাজীয়। ২.বাজিকর ৩. মাল ৪. মিরশ্চিকার ৫. সাপুড়িয়া ৬. সান্দার ও ৭. রসিয়া। আবার ভারত কোষ বেদে বা বাদিয়া জনগোষ্ঠীকে যে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছে, বাজিকর তাদের মধ্যে একটি। আর বাংলাদেশে যে বেদে জনগোষ্ঠী আছে, আমরা তাদের পেশার ভিত্তিতে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করেছি। তার মধ্যে বাজিকর অন্যতম। ভারত কোষে বেদে সম্প্রদায় শীর্ষক লেখা থেকে জানা যায় যে ‘বেদেরা ভানুমতির খেলা ও শারীরিক কসরৎ’ করে জীবিকা নির্বাহ করে।
বাজিকররা ভেল্কিবাজি করে, ১০০ টাকার নোট ৫০০ টাকা করে। হাত দেখে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার মতো কাজ করে এরা উপার্জন করে। আবদুল হক তাদের সম্পর্কে বলেন ‘‘তাদের পুরুষদের পেশা হলো ম্যাজিক ও শারীরিক কসরৎ দেখানো। আর মেয়েদের পেশা হলো জরিবুটি বিক্রি করা। ওই গোত্রটি সুনামগঞ্জ মহকুমার ‘বাজিকর’ গোত্র নামে খ্যাত।… এরা মুসলমান হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতির অনুসারী।” (আব্দুল হক রচনাবলি, পৃ. ৪১০)।
এডওয়ার্ড. ই. ডাল্টন বেদেদের বাজিকর সম্প্রদায়ের একটি শাখা বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ মংচিৎ ছিলো উল্টোটা। কেননা বেদে এর অর্থ -ই হলো যাযাবর জাতি। বাজিকর এই যাযাবর জাতির একটি উপ-শাখা। বাজিকররা যে বেদে, তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়টি ফুটে উঠেছে ‘রহু চণ্ডালের হাড়ে’। বাদিয়া হলো ভারতের যাযাবর শ্রেণী। উপন্যাসটিতে বেদে শব্দটির পরিবর্তে বাদিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
লুবিনিকে পীতেম যখন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক শনিবারের ভূমিকম্পের ইতিহাস শোনায়, তখন সে বলে, ‘বাউদিয়া বাজিকর পিছনে যা ফেলে যায়, তা জানোয়ারের বিষ্ঠা, কে তার কথা স্মরণ করে?’ তার আগে সে নিজেদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সভ্য মানুষদের সম্পর্কে বলে, ‘মানুষ চায় বাউদিয়া বাউদিয়াই থাকুক-বাজিকর বাজিকরই থাকুক।’ এই পরিচয় আর একটু স্পষ্ট হয় সালমা ও পীতেমের ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতায়। যখন সালমা পীতেমকে বলে, ‘গেরস্থ হওয়ার মানে বাঁধা জানোয়ার’, তখন সালমা জানতে চায়,
তবুও তুই বাঁধা জানোয়ার হওয়ার কথা ভাবছিস?
ভাবছি।
কেন?
বাজিকর বাদিয়ার দিন বোধহয় শেষ হয়ে আসলো।. এই পরিচয় সালমা বেশ দম্ভের সঙ্গে জানিয়েছিল দারোগাকে। পীতেমের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল—‘কী করবে একে? মারবে? মারো, তোমার ক্ষমতা দেখি? দেখো, দারোগাবাবু, আমরা বাদিয়াজাত, আসমানের দেবতা আমাদের সহায় থাকে।’
বাজিকররা যে বাদিয়া বা বেদিয়া এ কথা লেখকও অকপটে স্বীকার করেন উপন্যাসের এক স্থানে সাংবাদিক বয়ানে। ‘রূপার যাযাবর রক্তের আকস্মিক ক্রোধ ঝলসে ওঠে। একজন তার হাতে খুন হয়। তারপরই আড়ালের চিরকালে ভয়ার্ত মার খাওয়া বেদিয়া সারা দুনিয়াব্যাপী অন্ধকার দেখে।’ আর খেদে আক্ষেপে জামির বলে, ‘বাজিকরের বেটারা, তুমরা বাদিয়া বটে, কিন্তু সি কথা এখন বিসোরন হই যাও।’ বাজিকর সম্প্রদায়টি যে বেদিয়া বা বেদে জনগোষ্ঠীর একটি শ্রেণী তার প্রমাণ এই স্বীকারোক্তি ছাড়াও উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যেতে দেখি।
বেদে জনগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো—এরা কৃষি কাজকে ঘৃণার চোখে দেখে। এরা বীজবপন করে না। ফসলও ফলায় না। বাজিকররাও এর ব্যতিক্রম নয়—‘কৃষিকর্ম বাজিকররা কোনো দিন করেনি।’ তাই বাজিকর পীতেম লক্ষণ সোরেনের যুক্তি অগ্রাহ্য করে। লক্ষন সোরেন যখন বলে, ‘পুরুষ মানুষের যেমন একজন মেয়ে মানুষ চাই-ই, তেমনি সব মানুষেরই জমিও চাই। শুনে পীতেম বলে তারপর তোমাদের মতো মালিকের বাঁধা গোলাম হই আর কি! ওর মধ্যে বাজিকর যায় না।’ বাজিকররা জমির যে কিছু বোঝে না তা পরিষ্কার করেছিল দয়ারাম। ‘আঃ হাহা হা মজা তো ওই খানেই। তোমরা বাদিয়া লোক, জমির ব্যাপারে কিছুই বোঝো না। বাদিয়া বা বেদে জনগোষ্ঠী জমির সঙ্গে কখনো সম্পর্ক পাতে না, পাততে জানে না। কারণ তাদের রক্তে ঘুরে বেড়াবার নেশা।’ শারিবাকে তাই লুবিনি বলে, ‘বাজিকর পাটক্ষেত নিড়াতে জানে না, মার খায়। বাজিকর হাল মই দিতে জানে না, মার খায়।’
তাহলে বাজিকরের পেশা কী! ‘বাজিকর বানর নাচায়, ভাল্লুক নাচায়’—জামির বলে,—‘ কাজ পালে কাজ করো না, না পেলে বান্দর লাচাবা, রহু চণ্ডালের হাড় দিয়া ভেলকি দেখবা।’ রহু চণ্ডালের হাড়ে দেখি ঢোলকে বাড়ি পড়ে। বাজিকরের মুখে ধারালো শব্দের বাক্য বের হয়—‘হাই দেখো রহু চণ্ডালের হাড়ের কিসমৎ। সত্যের গুল্লি ডবল হ মিথ্যার গুল্লি চইল্যো যা-হা, এই দেখো ডবল, ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ…’
পনেরো হাত উঁচু দিয়ে দড়িতে আবলীলায় হেঁটে যায় বাজিকর যুবতী, দড়িতে দোল খায়, হাতের পায়ের ভঙ্গি করে। নিচে ঢোলক বাজে, চটুল গান হয়। বাজিকররা বানরের বাচ্চাকে খেলা শিখায়। আর ‘ঢোলকের চামড়ায় কাঠি পড়ে। রহু চণ্ডালের হাড়ে তেল সিদুঁর লাগে, অন্যভ্যস্ত পায়ে টান টান দড়ির ওপরে হেটে যায় বাজিকর বালিকা।’ বাজিকর বাদিয়ার এই-ই হলো পেশা।
উপেক্ষিত মানুষদের নিয়ে লেখা উপন্যাসে লোকজীবনের যে ইতিহাস, তাতে ব্যক্তির প্রেম রোমান্স, জীবন-জীবিকা; সবখানেই থাকে নানা শৃঙ্খলা-শাসন। ব্যক্তিসত্তার ওপর জয়ী হয় গোষ্ঠীসত্তা। বাজিকরের ঘর-গৃহস্থালির প্রতি টান আছে। তাদেরও ব্যক্তিগত সঞ্চয় আছে। তবু তাদের অস্তিত্ব গোষ্ঠীতে। তাই ঝালোদী মেয়ে পাখিকে ভালোবাসলেও সোজন গোষ্ঠীরহিতের কথা চিন্তা করে পাখিকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে। তবু শেষ রক্ষা হয় না।
এ উপন্যাসে রহু বাজিকরদের কল্পিত আদিপুরুষ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নয়। তাদের বোধের মধ্যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এক দলপতির ভূমিকা নিয়ে বেঁচে থাকে সে। দেড়শ বছর ধরে দনু থেকে শারিবা পর্যন্ত পাঁচপুরুষের পায়ের নিচে মাটি পাওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু তা রহুর কালেও যেমন ভেঙে গিয়েছিল, শারিবার কালেও ভেঙে গেছে। চলতে চলতে তারা অন্যগোষ্ঠীর পাশে এসেও নিজেদের নিরাপদ রাখতে পারেনি। অনুপ্রবেশ করেছে অন্যবর্ণের ভ্রষ্টাচার, প্রবেশ করেছে উচ্চবর্ণের রাজনীতি আর ক্ষমতার প্রভাব। ভেঙে গেছে গোষ্ঠী। গোষ্ঠীজীবন-ভিত্তিক উপন্যাসের এটাই ট্রাজেডি।
গোষ্ঠীর মধ্য যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তীব্র হয়ে ওঠে, তখনই গেষ্ঠী ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বান্দ্বিকতাই গোষ্ঠীজীবন-ভিত্তিক উপন্যাসের চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এখানে চরিত্রের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ নয়, প্রাধান্য পায় তার সমূহ-চেতনা। বাংলাদেশে খুব কমই এ জাতীয় গোষ্ঠীচেতনা-ভিত্তিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। অথচ এ জাতীয় উপন্যাসের পাতা থেকে আমরা ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।
উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠীজীবন-ভিত্তিক উপন্যাসগুলো মূলত ভাঙনের আখ্যান; যেমন, তারাতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘ব্যাধখণ্ড’, সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’, সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’, সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’, প্রফুল্ল রায়ের ‘পূর্ব পার্বতী’ ইত্যাদি। ‘রহুচণ্ডালের হাড়ে’র গোষ্ঠীর ভাঙনও বিচিত্র কিছু নয়।


