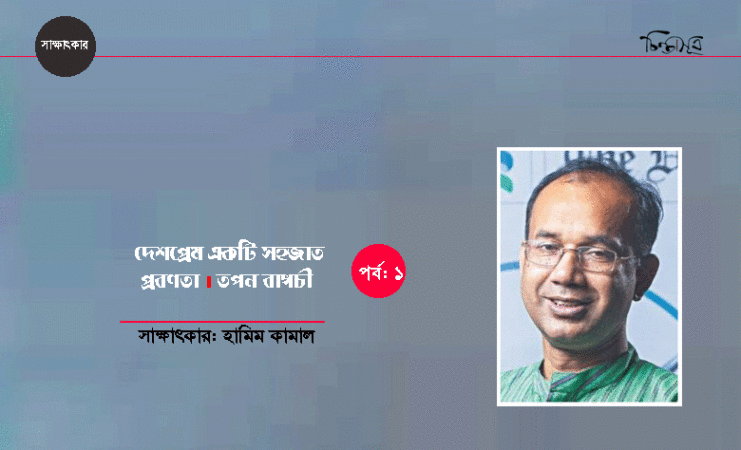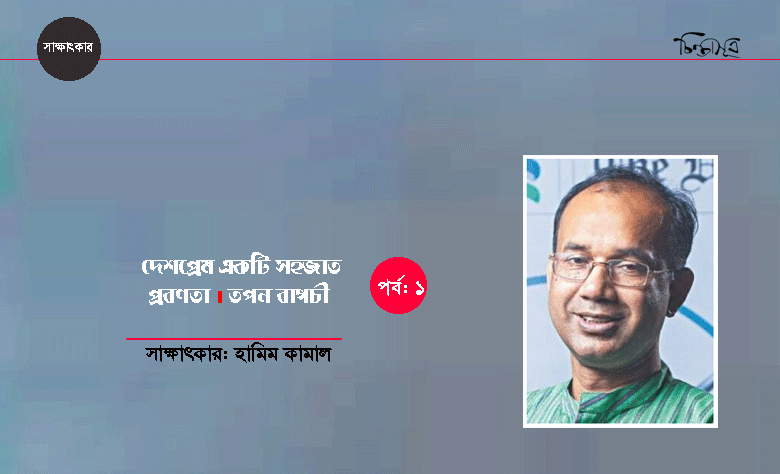তপন বাগচী—একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তিনি ১৯৬৮ সালের জন্ম ২৩ অক্টোবর মাদারীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা তুষ্টচরণ বাগচী; মা জ্যোতির্ময়ী বাগচী। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় এমএ ও পিএইচডি করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ: শ্মশানেই শুনি শঙ্খধ্বনি, কেতকীর প্রতি পক্ষপাত, অন্তহীন ক্ষতের গভীরে, সকল নদীর নাম গঙ্গা ছিল। প্রবন্ধগ্রন্থ: সাহিত্যের এদিক-সেদিক, সাহিত্যের কাছে-দূরে, চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, লোকসংস্কৃতির কতিপয় পাঠ, বাংলাদেশের যাত্রাগান : জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ : চন্দ্রাহত অভিমান, নির্বাচন সাংবাদিকতা, নজরুলের কবিতায় শব্দালঙ্কার, তৃণমূল সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশ। পুরস্কার ও স্বীকৃতি: সাংস্কৃতিক খবর পদক (কলকাতা, ২০১৩), মাইকেল মধুসূদন পদক (২০১২), লিটল ম্যাগাজিন মঞ্চ সংবর্ধনা (নদীয়া ২০১০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য পুরস্কার (২০০৯), কবি বাবু ফরিদী সাহিত্য পুরস্কার (২০০৯), মাদারীপুর সুহৃদ পর্ষদ সম্মাননা (২০০৯), ফরিদপুর সাহিত্য পরিষদ সম্মাননা (২০০৯), মহাদিগন্ত সাহিত্য পুরস্কার (কলকাতা ২০০৮), এম নূরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরস্কার (২০০৮), জেমকন সাহিত্য পুরস্কার (২০০৮), অমলেন্দু বিশ্বাস স্মৃতি পদক (২০০৮), জসীমউদ্দীন গবেষণা পুরস্কার (১৯৯৬), মুনীর চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১)।
দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করার পর বর্তমানে বাংলা একাডেমির গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের উপপরিচালক। সম্প্রতি সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, দর্শন বিষয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন তরুণ কথাসাহিত্যিক হামিম কামাল। আজ প্রকাশিত হলো প্রথম পর্ব]
হামিম কামাল: সৃজনের ভুবনে তো অনেকদিন ধরে হাঁটছেন তপন দা। প্রথম প্রেম কোনটি?
তপন বাগচী: সৃজনশীলতার দিকে আসলে আট দশজন লেখকের মতো, আরও যদি বলি বাঙালি লেখকের মতো, কবিতা দিয়েই প্রেম শুরু হয়, লেখার ক্ষেত্রে। আমি লক্ষ করেছি যে, আমাদের বড় কথাসাহিত্যিদের কথাও যদি বলি, হয়ত যৌবনে এক দুই লাইন কবিতাও তাঁরা লিখেছেন। আমার শুরুটাও হয়েছিল ও রকম, কবিতা পড়তে গিয়ে, বা পাঠ্যবইয়ে কবিতা পড়তে গিয়ে। কবিতার দোলাটা আমায় খুব টানতো। একটি গদ্য পড়ে আমি হয়তো কিছু শিখেছি, কিন্তু তা আমার লাইন বাই লাইন মনে থাকতো না, সামান্য কিছু মেসেজ হয়ত মনে থাকতো। একটা গল্প হয়তো পড়েছি, এর লার্নিংটা মনে থাকতো। কিন্তু একটা কবিতা যখন পড়তাম, এর প্রতিটি লাইন, প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি উপমা আমাকে টানতো। একসময় মনে হতো জীবিত কেউ বুঝি এরকম লিখতে পারে না, অর্থাৎ কবিরা বুঝি এসময়ের কেউ না। তারা হয়ত অন্য জায়গা থেকে এসেছে, অহি নাজিলের মতো করে লিখে যায়। তখন নিজে লেখার কথা ভাবিনি, কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যেতাম।
যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি, একদিন বাড়িতে খুব বিরক্ত করছিলাম দুপুরবেলায়। ভাদ্রমাস হবে তখন। তো, বাবা আমার জ্বালাতন থেকে রেহাই পেতে ঘাটে বাঁধা একটা নৌকায় তুলে পুকুরের মাঝখানের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, ‘শোন, জসীমউদ্দীন কবিতা লিখতো, জয়নুল আবেদীন ছবি আঁকতো। হয় কবিতা লিখবি, নয় ছবি আঁকবি। এরপর তোকে বাড়িতে আনব।’ নৌকার পাটাতনে একটি খাতা আর একটি পেন্সিল দিয়ে দিলেন। তো একরকম জিদের বসে আমার পরিচিত জসীমউদ্দীনের এক কবিতায় কিছু শব্দ বদল করে লিখে ওটাই বাবার কাছে দিয়েছিলাম। বাবা আমার চুরিটা ধরতে পারলেন। কিন্তু খুব আনন্দিতও হলেন। আমি যে জসীমউদ্দীনের কবিতার কিছু শব্দ বদল করে একরকম নতুন কিছু দাঁড় করিয়েছি এটা তাকে আনন্দ দিয়েছিল। তিনি বললেন, কবিতা লিখলে তুই পারবি। এরপর একটা খাতা বের করে দেখান। অবাক হয়ে দেখি, তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।
এরপর আমার দাদু, মানে আমার বাবার যিনি বাবা, তার কথা শুনে আমি খুব আনন্দ পেতাম। ধরো, আমার বাবা বাড়ি আসবেন। খুব দূরে চাকরি করতেন। তো যেদিন বাড়ি আসবেন, সেদিন আমরা খুব আনন্দে থাকতাম। তার আসার খবরটা দিতেন দাদু। এভাবে দিতেন, বলতেন, ‘বাজারে গেছিলাম, বাতাস পাইলাম, তোর বাবা আসবে।’ এই ‘বাতাস পাইলাম’ শব্দটা খুব টানতো। বলতে পারতেন, খবর পেলাম, বার্তা পেলাম, হয়তো কারও সঙ্গে দেখা হলো যে বাবাকে কোথাও দেখেছে যে আসছেন, দাদুকে দেখে জানিয়েছেন, তো দাদু কথাটা বললেন এভাবে। ছোটবেলায় আমি অলঙ্কারিক শব্দ, উপমায় বলা, একটু ব্যঞ্জনাময় শব্দ এসবের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতাম।
এদিকে আমার দাদু, আর ওদিকে মামার বাড়িতে থাকতে আমার নানী, দিদিমা বলতাম, ওনার নাম সুহাসিনী। মজার মজার ছড়া বলতেন, গল্প করতেন। এবং এমন কিছু শব্দ তার মুখ থেকে আসতো যে আমি মুগ্ধ হয়ে থাকতাম, মানুষ এতো সুন্দর করে কথা বলতে পারে? যেমন একদিন বললাম, আচ্ছা দিদিমা, ‘তোমার বিয়ে হয়েছিল কবে? কোন বয়েসে?’ তো তিনি খুব মজা করে বললেন, ‘তখন আমি এককলস জল নিতে পারতাম না।’ একটা প্রতীক ব্যবহার করলেন। তার বয়েসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। একটি মেয়ে, সে এক কলস জল ভরে আনতে পারে না, এ বয়েসে তার বিয়ে হয়েছে। সরাসরি আট বছর বা নয় বছরে বিয়ে হয়েছিল বললে যতটা আমার মনে থাকতো, তার চেয়ে বেশি আমার মনে রইলো এসব। কারণ তিনি চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এগুলো তো কবিতাই। সাধারণ মানুষের মুখে-মুখে রচিত সাধারণ কবিতা!
তখন থেকে এ ধরনের শব্দের প্রতি, বাকভঙ্গির প্রতি আমার টান হয়। পথ দিয়ে যেতে যেতে আমি এ ধরনের শব্দ খুঁজতাম, মানুষ কী বলছে, হাটফেরত মানুষ কী বলছে, এসব আমি খুঁজতাম।
একদিন আমার স্কুলশিক্ষক অনিলকৃষ্ণ দত্ত বললেন, তোমরা একটা দেয়ালপত্রিকা তো করতে পারো। বেশ, তা তো করাই যায়। কিন্তু দেয়াল পত্রিকায় লিখবে কে? একে বলি, তাকে বলি। আমার দুই অগ্রজ, তাঁদের নাম আজও মনে আছে, একজন রমেশ চন্দ্র গাইন, আরেকজন স্বপন কুমার কীর্তনিয়া, তাঁরা দুটি কবিতা দিলেন। স্যারও কবিতা দিলেন। আমি মনে করলাম, একটা লিখি না কেন! এইতো, শুরু হয়ে গেল। লেখাটাও আমার মনে আছে। আমি এক বৃষ্টির রাতে জেগে বসেছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি কি একা জেগে আছি? পুরো বাড়ির কেউ জেগে নেই, সবাই শুয়ে পড়েছে। আমি একা হারিকেন জ্বালিয়ে পড়ছি, বাইরে বৃষ্টি। তো এমন সময় আমি একাই জেগে আছি কিনা, এমন প্রশ্ন মনে জাগলে উত্তর পেলাম, না আমার সঙ্গে সঙ্গে যে বৃষ্টি জেগে আছে। কবিতার শেষের দুটি লাইনটা এমন ছিল- ‘বৃষ্টি আমার পড়ার সাথী বাদল ঝরা রাতে/ না ঘুমিয়ে তাই জেগে রয় আমার সাথে সাথে’। বৃষ্টি আমার সঙ্গে জেগে রয়, এই যে এক ছবি। আর সে আমার সাথী, তার ওপর আমি ব্যক্তিত্ব আরোপ করলাম, পারসোনিফিকেশন করলাম, এটা তাৎক্ষণিকভাবে হয়ে গেল এবং আমার ওই স্যার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, তোমার কবিতাটা তো খুব সুন্দর হয়েছে! এখন বুঝি, ওটা আসলে কবিতা হয়নি, বড়জোর একটা ছড়ার মর্যাদা হয়তো দেওয়া যায়। কিন্তু ওটাই আমার প্রকাশযোগ্য প্রথম লেখা ছিল। এরপর আমি আর ফিরিনি, লিখতে শুরু করি।
এরপর ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে এসে স্থানীয় পত্রিকায় লিখেছি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, ঈদের দিনে, পূজোর দিনে, মানে উপলক্ষের কিছু কবিতা লিখেছি। সাপ্তাহিক আল মোয়াজ্জিন, অর্থসাপ্তাহিক বাংলাসংবাদ, সাপ্তাহিক আলমিজান পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এসব। কলেজে একটা দেয়ালপত্রিকাও বের করেছিলাম। আমাদের প্রাণিবিদ্যার ম্যাডাম নূরজাহান বেগমকে নিয়ে একটা ব্যঙ্গ ছড়া লিখেছিলাম। তিনি ছাত্রদের ‘আপনি’ করে বলতেন। এটা আমি মানতে পারতাম। তিনি সুন্দর করে পড়াতেন। কিন্তু খিটখিটে মেজাজের ছিলেন। তাঁকে নিয়ে লিখলাম, ‘খিটখিটে এক আপনি-ম্যাডাম, আপনি বলেন ডাকেন/ ব্যাঙের ছবি আঁকতে গিয়ে মশার ছবি আঁকেন’। ম্যাডাম তো এই ছড়া শুনে রেগেমেগে টঙ। কিন্তু ছড়াকারের নাম তো জানেন না। ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে ডাক পড়ল আমার। বললাম যে ম্যাডাম, ‘আমার কাছে ডাকে এসেছে। এটা যে আপনাকে নিয়ে বুঝতে পারিনি।’ নইলে আপনার হাতে প্র্যাকটিক্যাল আছে জেনেও এই লেখা প্রকাশ করতাম না, আপা। ভুল হয়ে গেছে, আপা, ক্ষমা চাই।’ আপা হেসে উঠলেন। বললেন, ‘যাই হোক, ছড়াটা ভাল হয়েছে। যাও তুমি। ক্লাসের পড়ালেখা ঠিকমতো করো।’ আমার আনন্দ আর ধরে না। আপা আমাকে ‘আপনি’ নয়, ‘তুমি’ সম্বোধন করেছেন? ছড়া লিখে আপার মন বদলাতে পেরেছি। কিন্তু আপাকে আর বলা হয়ে ওঠেনি যে ছড়াটি আমিই লিখেছিলাম। আপা কোথায় আছেন, জানি না। কিন্তু তাঁর ওই স্বীকৃতি আমার পরবর্তী জীবনে বেশ আশীর্বাদ হয়ে ফলেছে। আজকে সেই আপাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।
পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বুঝতে পেরেছি যে যা কিছু এতদিন লিখেছি এসব আমার একবারেই অনুশীলনের পর্যায়ের। এর সঙ্গে আমার কবিতার পঠন-পাঠন যুক্ত নয়। তখন সংবাদের সাহিত্যপাতা, একতার সাহিত্যপাতা, এসব পাতায় যে কবিতাগুলো ছাপা হতো, দেখতাম আমার পুরনো ধারণার সঙ্গে মেলে না। কারণ আমি তো জসীমউদ্দীন পড়ে আসা লোক, নজরুল-রবীন্দ্রনাথ পড়ে আসা লোক। তখন তো আমি জীবনানন্দ দাশকে পাইনি। শামসুর রাহমানকে পাইনি, বুদ্ধদেব বসুকে পাইনি। এদের পাঠের পর আমি আধুনিক ধাঁচের কবিতা লিখতে শুরু করি।
কবিতা নিয়েই দীর্ঘদিন ছিলাম, একটা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর করতে এসে লিখতে হয়েছে। সাহিত্য বাসরে ছড়া কম পড়ছে। দুটো ছড়া লিখে দিতাম, তাৎক্ষণিকভাবে। কখনও মনে হলো, গল্প কম আছে, পরের সপ্তাহে একটা গল্প লিখে ফেললাম। এভাবে আমার শিশুতোষ লেখার পরিমাণ বাড়তে থাকে।
তখন আমাদের দেশে প্রচুর স্মরণিকা বেরোত। পয়লা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, এ দিনগুলোকে সামনে রেখে এগুলো বেরোতো। আমাদের জগন্নাথ হল থেকে চারটা-পাঁচটা স্মরণিকা বেরোত। এগুলোতে পাতা ভরানোর জন্য আমাকে প্রবন্ধ লিখতে হতো। নামে-বেনামে লিখতে হতো। তো ছড়া দিয়ে শুরু হলেও আস্তে আস্তে আমার লেখার গণ্ডি ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধে পৌঁছে গেল। উপন্যাসও লিখেছিলাম, এখনো অপ্রকাশিত। জেমকন সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলাম আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির জন্য। এখনো আস্থা তৈরি হয়নি বলে প্রকাশ করিনি। তিনটি নাটকও লিখেছিলাম ছাত্রজীবনে। ডাকসু এক প্রতিযোগিতায় নাটক আহ্বান করেছিল। এর আগে এ নিয়ে একটা কর্মশালা করেছিল। তেরোটি হল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ছাব্বিশ জনের নাটক জমা পড়েছিল, ওরা পাঁচটিকে নাটকের মর্যাদা দিয়েছিল। আমার নাটক ছিল তাতে। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অশোক কর্মকার তখন ডাকসুর সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক। তাঁর আগ্রহে নাটক জমা দিয়েছিলাম। মানসম্মত বিবেচনায় সনদও পেয়েছিলাম।
তো ওই অর্থে সাহিত্যেক সব শাখাতেই অল্পবিস্তর বিচরণ ঘটেছে। তবে মূল প্রেমটা থেকে গেছে কবিতার সঙ্গে এবং আমি অন্য যেসব শাখা নিয়ে লিখেছি, আমি মনে করি ওসব আমার কবিতাচিন্তারই একটা সম্প্রসারিত রূপ।
হামিম কামাল: তো তপনদা, দেখা যাচ্ছে পারিবারিক বলয় থেকে উপকরণ নিয়ে পুষ্ট হয়ে, পরে বিভিন্ন বলয়ে আপনি নিজেতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রতিটি বলয়ই একটা সময় নিয়ে অগণিত পরিপার্শ্বকে ঘিরে, অসংখ্য মানুষকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। আরও এককভাবে বলতে গেলে, যে শাখাতেই লিখেছেন, চরিত্র ও উদ্দেশ্য মূলত মানুষ। লেখারশিল্প আর এর সঙ্গে মানুষের সংশ্লিষ্টতা- এটা আপনার ভাবনায় কোন পথে, কী উপায়ে গুরুত্ব পায়। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় মানুষের বোঝার ক্ষমতার যে সীমা, তাকে ধরার চেষ্টা- এসব নিয়ে কী ভাবেন? লেখায় কিভাবে এর প্রতিফলন ঘটান। এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের এ কৌশল আপনি কিভাবে অর্জন করেছেন।
তপন বাগচী: আমি মনে করি, সেটাই গ্রহণযোগ্য সাহিত্য যেটা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এটা সম্ভব না হলে তা সফলতার দিকে যায় বলে আমার মনে হয় না। আরেকটি বিষয় হলো, ক্লাস সিক্স-সেভেন থেকে আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। রাজনীতি করার কারণে আমি মানুষের সঙ্গে মিশেছি, মিটিং-মিছিল করেছি, গোপন সভা করেছি- কী করে মানুষের ভাগ্য বদলানো যায়, মৌলিক অধিকারগুলো কী করে আদায় করা যায়, কী করে ওদের সংঘবদ্ধ করা যায়, এসব নিয়ে কাজ করেছি। যে কারণে মানুষকে পাঠ করার সুযোগ হয়েছে।
তখন ১৯৮০ সাল, আমি ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের স্কুলের মাঠে ‘লেনিন যাত্রাপালা’ হলো, অমলেন্দু বিশ্বাসের। তখন মণি সিংহের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটে, তিনি আমাদের এলাকায় গিয়েছিলেন, জনসভায়। এলাকায় সাম্যবাদের দীক্ষা আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের এলাকায় কয়েকজন ত্যাগী নেতা ছিলেন, মৃণালকান্তি বারুণী, সন্তোষ ব্যানার্জী, আবদুল মোতালেব মিয়া, গোপাল সরকার এঁদের সংস্পর্শে এসে বামপন্থী একটা চিন্তা আমার ভেতর গড়ে উঠেছিল। তো, আমি ভাবলাম, ‘লেনিন যাত্রাপালা’ এ গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ দেখবে? আমি পরেরদিন এদের অনেককে জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখলা। উত্তরে বোঝা গেল, লেনিনের গোটা শিক্ষাটা তারা হয়তো ওভাবে নিতে পারেনি, কিন্তু অমলেন্দুর অভিনয় তাদের ভালো লেগেছে। তারা এটা বুঝেছে, যে পৃথিবীতে একজন লোক এসেছিল, যে এ সমাজটায় সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এ বার্তাটা কিন্তু ওরা নিতে পেরেছে। শুধু শিক্ষিত হলেই হয় না, দেশপ্রেমের সহজাত প্রবণতা ওদের মধ্যে ছিল। দেশপ্রেম একটা সহজাত প্রবণতা। কেউ যদি দেশের বিরুদ্ধে যায়, সেটা কোনো না কোনো কার্যকারণের প্রত্যাঘাত। সাধারণ প্রবণতা দেশকে, মাটিকে, মাকে, মানুষকে ভালোবাসা। তখন মনে হলো, লেনিনের মতো কঠিন একটি বিষয়, মাইকেল মধুসুদনের মতো কঠিন একটি বিষয়, এমনকি হিটলার যাত্রাপালা- সেটিও মানুষ গ্রহণ করেছে। অমলেন্দু বিশ্বাসের অভিনয়েই হিটলার যাত্রাপালা হয়েছিল। এটি গ্রামের সাধারণ মানুষ নিয়েছে। অবাক হতাম, ভাবতাম, আজকাল কি এটা দেখবে কেউ?
চলবে…